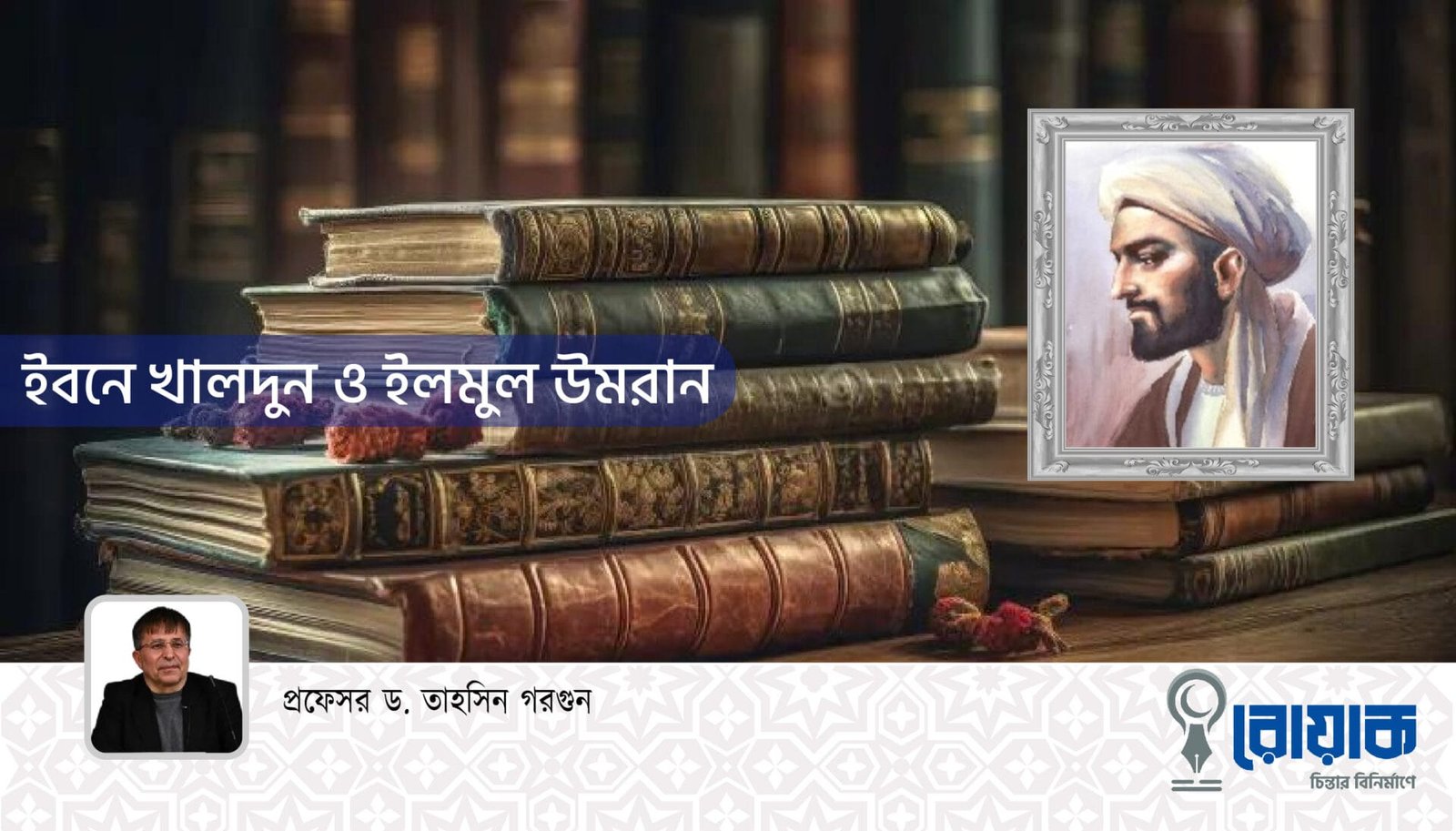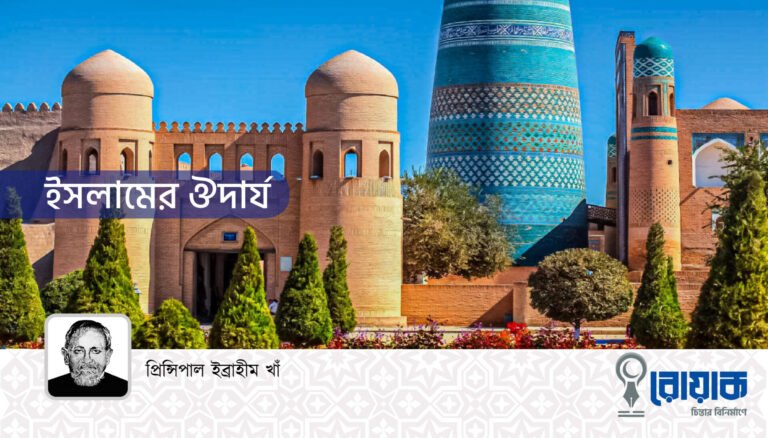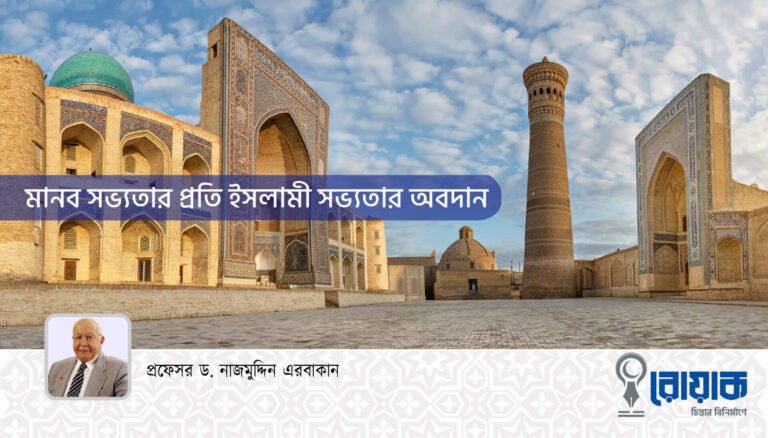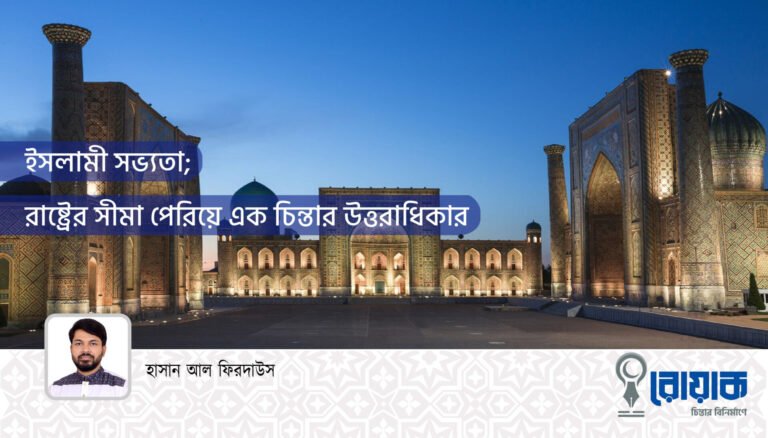এ প্রবন্ধে যে সব বিষয় নিয়ে আলোচনা করবো, শুরুতেই তা সংক্ষেপে তুলে ধরতে চাই,
১. ইবনে খালদুনের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি।
২. ইবনে খালদুনের ইলমুল উমরান কী?
৩. সমাজবিজ্ঞান বা Sociology কী?
৪. ইলমুল উমরান ও সমাজবিজ্ঞানের মধ্যকার সম্পর্ক কেমন হতে পারে?
৫. ইবনে খালদুন বর্তমান দুনিয়ার প্রেক্ষিতে কতটা প্রাসঙ্গিক এবং আমরা তাঁর নিকট থেকে কীভাবে উপকৃত হতে পারি?
আমাদের সামনে প্রথমেই যে প্রশ্নটি এসে দাঁড়ায়, তা হলো ইবনে খালদুন তাঁর মুকাদ্দিমায় যে থিওরিগুলো দিয়েছেন, সেগুলোকে আমরা সমাজবিজ্ঞান বা Sociology নামে অভিহিত করতে পারি কিনা? এ প্রশ্নটিকে আগে সুস্পষ্ট করার জন্য বর্তমান বিশ্বের প্রায় সকল বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞান (Sociology) বিভাগের পাঠ্য বই হিসেবে পঠিত এন্থনি গিডেন্সের লেখা Sociology নামক বইটি নিয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করতে চাই।
আগে দেখা যাক এন্থনি গিডেন্স সমাজবিজ্ঞানকে (Sociology) কীভাবে সংজ্ঞায়িত করেছেন। তাঁর মতে,
“Sociology is the scientific study of human social life, groups and societies. It is a dazzling and compelling enterprise, as its subject matter is our own behavior as social beings. The scope of sociology is extremely wide, ranging from the analysis of passing encounters between individuals on the street to the investigation of crime, international relations and global forms of terrorism.”
অর্থাৎ, সমাজ এবং সমাজের প্রতিষ্ঠানাদির বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিই হচ্ছে সমাজবিজ্ঞান। সমাজের মৌলিক উপাদান এবং সামাজিক জীব হিসেবে আমাদের আচরণকে বিশ্লেষণ করাই হচ্ছে সমাজবিজ্ঞানের কাজ। যার দরুণ এটি বেশ সমৃদ্ধ এবং প্রাসঙ্গিক একটি বিষয়। সমাজবিজ্ঞানের পরিধি অনেক বিস্তৃত। যেমন, দুজন পথচারীর সাময়িক বিবাদের বিশ্লেষণ থেকে নিয়ে বিশ্বব্যাপী অপরাধ, সন্ত্রাসবাদ, মানুষের জীবনাচরণ এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্ক নিয়ে বিশ্লেষণধর্মী সময়োপযোগী আলাপন উপস্থাপন করাই হচ্ছে সমাজবিজ্ঞানের নিত্যদিনের কাজ।
ইবনে খালদুন তাঁর নিজের তৈরিকৃত ডিসিপ্লিন ইলমুল উমরানকে এভাবে সংজ্ঞায়িত করেছেন-
“انه لما كانت حقيقة التاريخ انه خبر عن الإجتماع الإنساني الذي هو عمران العالم ، وما يعرض لطبيعة ذالك العمران من الأحوال”
“ইলমুল উমরান হলো এমন জ্ঞান যা বিশ্বজগতের উমরানের সাথে সম্পর্কিত মানুষের সমাজ এবং প্রকৃতির দাবি অনুসারে তার মধ্যে সৃষ্ট অবস্থাসমূহ এবং সে সকল অবস্থার আবশ্যিক ফলাফল হিসেবে ইতিহাস এবং ইতিহাসের হাকীকতকে বিষয়বস্তু হিসেবে গণ্য করে থাকে।”
আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, এন্থনি গিডেন্সের প্রদত্ত সমাজবিজ্ঞানের সংজ্ঞা এবং ইবনে খালদুনের ইলমুল উমরানের সংজ্ঞার মধ্যে কতগুলো মৌলিক পার্থক্য রয়েছে।
প্রথমত, ইলমুল উমরানের মধ্যে ইতিহাস বড় একটি ফ্যাক্টর।
দ্বিতীয়ত, ইবনে খালদুনের মতে, সমাজ বলতে মানবসমাজ বুঝানো হয়, সে ক্ষেত্রে মানুষের একত্রে বসবাসের বিষয়টি মানুষের স্বাধীন ইচ্ছার উপর ছেড়ে দেওয়া হয়নি। ইবনে খালদুন মানুষের সামাজিক জীবনকে স্বীয় ইচ্ছাধীন কোনো বিষয় নয়, বরং অত্যাবশ্যকীয় (Imperative) একটি বিষয় হিসেবে দেখে থাকেন। মানবসমাজকে অত্যাবশ্যকীয় (Imperative) একটি বিষয় হিসেবে দেখার অর্থ হলো এ বিষয়টিকে একটি মেটাফিজিক্যাল বিষয় হিসেবে দেখা কিংবা অন্টোলজিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করা। তাহলে আমরা এ কথা বলতে পারি, সমাজকে অন্টোলজিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করা ইলমুল উমরানের মূল বিষয়।
অপরদিকে সমাজবিজ্ঞান (Sociology) সমাজকে একটি মওজুদ বা বিদ্যমান বিষয় হিসেবে দেখে। বর্তমান সময়ের সমাজবিজ্ঞান এ মওজুদ বা বিদ্যমান সমাজের বিভিন্ন ধরনের বৈশিষ্ট্য ও অবস্থাকে বিশ্লেষণ করে।
এখানে আমরা যে মৌলিক পার্থক্যটি দেখতে পাই, তা হলো, সমাজবিজ্ঞানের (Sociology) ক্ষেত্রে ইতিহাস কোনো বিবেচ্য বিষয় নয়। এটি শুধুমাত্র মওজুদ বা বিদ্যমান সমাজকে ব্যাখ্যা করে।
অপরদিকে ইলমুল উমরান মানুষকে ও সমাজকে ঐতিহাসিক একটি অস্তিত্ব হিসেবে গ্রহণ করে। ঐতিহাসিক একটি অস্তিত্ব হিসেবে গ্রহণ করার কারণে সে অস্তিত্বটি একটি প্রক্রিয়ার মধ্যে কীভাবে তার অস্তিত্বকে ধারাবাহিক রাখে সে বিষয়কে বিশ্লেষণ করে থাকে। এজন্য ইলমুল উমরানের ক্ষেত্রে ‘সময়’ এর ব্যপারটি অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ।
যেমন, এ বিষয়টিকে সুস্পষ্ট করে তুলে ধরার জন্য আমাদেরকে মুকাদ্দিমার সূচিপত্র ও এন্থনি গিডেন্সের Sociology বইয়ের সূচিপত্রকে তুলনামূলকভাবে নিরীক্ষণ করতে হবে। এ তুলনামূলক নিরীক্ষণের মাধ্যমে আমরা এক্ষেত্রে সুস্পষ্ট একটি ধারণা পাব।
প্রথমেই যদি এন্থনি গিডেন্সের Sociology বইয়ের সূচিপত্রের দিকে তাকাই, তাহলে দেখতে পাই, তিনি প্রথমেই ‘সমাজবিজ্ঞান (Sociology) কী’ এ বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন। পরবর্তী অধ্যায়ে তিনি বিশ্বায়ন (Globalization) নিয়ে আলোচনা করেছেন। তারপরের অধ্যায়সমূহে তিনি সমাজবিদ্যাগত প্রশ্ন ও উত্তর (Asking and Answering Sociological Questions), সমাজবিজ্ঞানে তাত্ত্বিক চিন্তা (Theoretical Thinking in Sociology), সামাজিক যোগাযোগ ও দৈনন্দিন জীবন (Social Interaction and Everyday Life), সামাজিকীকরণ, জীবনযাত্রা ও বার্ধক্য (Socialization, Life-Course and Ageing), পরিবার ও ব্যক্তিগত সম্পর্কসমূহ (Families and Intimate Relationships), স্বাস্থ্য, অসুস্থতা ও অক্ষমতা (Health, Illness and Disability), স্তরবিন্যাস ও শ্রেণি (Stratification and Class) দরিদ্রতা, সামাজিক বাধা ও সমাজ কল্যাণ (Poverty, Social Exclusion and Welfare), বৈশ্বিক বৈষম্য (Global Inequality), লিঙ্গ ও যৌনতা (Sexuality and Gender), বর্ণ, জাতিভুক্ত ও অভিবাসন (Race, Ethnicity and Migration), আধুনিক সমাজে ধর্ম (Religion in Modern Society), গণমাধ্যম (The Media), প্রতিষ্ঠান/সংগঠন ও বিস্তৃতি/নেটওয়ার্ক (Organization and Networks), শিক্ষা (Education), অর্থনৈতিক জীবন ও কর্ম (Work and Economic Life) অপরাধ ও বিচ্যুতি (Crime and Deviance) রাজনীতি, সরকার ও সন্ত্রাসবাদ (Politics, Government and Terrorism), নগর ও নাগরিক অবস্থান (Cities and Urban Spaces), পরিবেশ ও ঝুঁকি (The Environment and Risk) নিয়ে আলোচনা করেছেন।
আধুনিক সমাজবিজ্ঞানে সাধারণত এ সকল বিষয় নিয়েই আলোচনা করা হয়।
কিন্তু ইবনে খালদুনের মুকাদ্দিমার দিকে যদি লক্ষ্য করি, তাহলে দেখবো, এর প্রথম অধ্যায়ে তিনি যে বিষয়টি তুলে ধরেছেন, তা হলো একটি জীবসত্তা হিসেবে মানুষ কীভাবে অন্য মানুষের সাথে বসবাস করছে, মানুষের মৌলিকত্বের সাথে এ বিষয়টির সম্পর্ক কী এবং মূলগত দিক থেকে মানুষের ইচ্ছার সাথে সম্পৃক্ত না হয়েও কীভাবে এটি সমাজে বাস্তবায়িত হচ্ছে। এবং মানুষ কর্তৃক বসবাসকৃত সমাজের এ ব্যবস্থাপনাটি কার্য ও কারণের সম্বন্ধের (Causality Order) মাধ্যমে তুলে ধরার অর্থ হলো এ বিষয়টিকে অন্টোলজিক্যাল দৃষ্টিকোণ থেকে তুলে ধরা। সমাজকে অন্টোলজিক্যাল দৃষ্টিকোণ থেকে তুলে ধরে সমাজ কীভাবে অস্তিত্ব ও বিকাশ লাভ করে, সে বিষয়টিকেও তিনি উপস্থাপন করেছেন।
পরবর্তীতে তিনি সমাজ মূলগতভাবে যেমন, ঠিক সেভাবেই বিকশিত হওয়ার জন্য অপরিহার্য শর্ত হিসেবে দুটি ভিন্ন উপাদানকে উল্লেখ করেছেন। সেগুলোর মধ্যে প্রথমটি হলো; ‘মানুষ যদি এমন একটি আচরণের মধ্যে থাকে যে, আমি যদি আমার নিকটবর্তীজনকে রক্ষা করতে না পারি, তাহলে আমি নিজেও আমার নিজের অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখতে পারবো না’। সমাজের মানুষ যদি এ ধরনের সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্যরে আলোকে তাদের সমাজকে গড়ে না তুলে, তাহলে তারা একত্রে বসবাস করতে পারবে না। যেমন, মানবশিশু খুবই দুর্বল ও অসহায় হিসেবে জন্মগ্রহণ করে। সমাজ যদি তাকে বড় হওয়ার জন্য ও বেঁচে/টিকে থাকার জন্য সাহায্য না করে, তাহলে তার পক্ষে বেঁচে থাকা সম্ভবপর নয়। এক অর্থে ইবনে খালদুন এ বিষয়টিকে এভাবে তুলে ধরেছেন, আল্লাহ মানুষকে একটি প্রজাতি হিসেবে সৃষ্টি করেছেন এবং মানুষ যেন এভাবে টিকে থাকতে পারে এজন্য তার নিয়ন্ত্রণের বাইরে আল্লাহ তায়ালা একটি ‘অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার নীতি’ দান করেছেন। সে নীতিটি হলো মানুষজন মুসলিম হোক বা না হোক, তারা যেন একটি প্রজাতি হিসেবে নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে পারে, সেভাবেই একে অপরকে রক্ষা করে থাকে। এ বিষয়টি হলো মানুষের সমাজজীবনের পর্যায়, এটি পরবর্তীতে পর্যায় থেকে পর্যায়ক্রমে অতিবাহিত হতে থাকে। অর্থাৎ, আসাবিয়্যাত হলো মানুষের জীবনকে সমাজবদ্ধভাবে পরিচালনা করার প্রথম ধাপ।
দ্বিতীয়টি হলো, একটি সমাজ হিসেবে মানুষের টিকে থাকা বা বেঁচে থাকার জন্য পরিবেশকেও মানুষের বাসোপযোগী হতে হবে। পরিবেশ যদি মানুষের বসবাসের উপযোগী না হয়, তাহলে মানুষের পক্ষে সেখানে বেঁচে থাকা সম্ভবপর নয়। যার কারণে মরুভূমিতেও উমরান গড়ে উঠবে না, আবার বরফাচ্ছাদিত অঞ্চলেও উমরান গড়ে উঠবে না।
এ দুটি মূলনীতি উমরানের জন্য অপরিহার্য।
মানুষের একসাথে বসবাস করার জন্য এ দুটি মূলনীতির সাথে ইবনে খালদুন তৃতীয় একটি মূলনীতি যুক্ত করেন। তিনি বলেন, যদি কোনো কওম বা গোত্রের নিকট কোনো পয়গাম্বর আসে, তাহলে সে পয়গাম্বরের উম্মতের মধ্যে এমন একটি শক্তিশালী চেতনা থাকতে হবে, যে চেতনার বলে তারা উম্মতের সকলকে রক্ষা করার জন্য আপ্রাণ প্রচেষ্টা চালাবে। আর সে প্রচেষ্টা হতে হবে এমন, যেমনটা একজন মা তার সন্তানকে রক্ষা করার জন্য করে থাকেন।
ফলশ্রুতিতে সামাজিক অস্তিত্বের তৃতীয় মেটাফিজিক্যাল মূলনীতিটি হলো ‘নবুওয়ত’। এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষ করে ইবনে খালদুনকে নিয়ে যারা কথা বলেন, তারা জ্ঞাতসারে হোক কিংবা অজ্ঞাতসারে হোক এ বিষয়টিকে উপেক্ষা করে থাকেন। এ ‘নবুওয়ত’ এর মাধ্যমে সৃষ্ট আসাবিয়্যাত রক্ত সম্পর্কীয় আসাবিয়্যাতকে সম্পূর্ণ রূপান্তরিত করে নতুনভাবে সংজ্ঞায়িত করে থাকে। তাঁর এ সংজ্ঞায়নের মাধ্যমে একইসাথে একজন পয়গাম্বরকে ইত্তিবা বা অনুসরণকারীদের মাধ্যমে সম্পূর্ণ ভিন্ন একটি সমাজিক ব্যবস্থাপনা গড়ে উঠে।
ইবনে খালদুন তাঁর মুকাদ্দিমার প্রথম অধ্যায়ে সাধারণভাবে আল-উমরানুল বাশারীর মধ্যে ইমাম ফখরুদ্দিন রাযীর রচিত গ্রন্থ “আল-মাবাহিসুল মাশরিকিয়্যা” এর মেটাফজিক্যাল পদ্ধতিকে সমাজের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেছেন। এ বিষয়টি সম্পর্কে অবহিত থাকা অতীব জরুরী।
এরপর দ্বিতীয় অধ্যায়ে তিনি ‘উমরান আল হাদারী’ ও ‘উমরান আল বাদাবী’ নিয়ে আলোচনা করেছেন। এ অধ্যায়ে তিনি মানুষের জীবনপদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করেছেন এবং দুটি মৌলিক ক্যাটাগরিকে পরস্পর থেকে পৃথকভাবে তুলে ধরেছেন। সে মৌলিক ক্যাটাগরির মধ্যে একটি হলো সে সময়ে মানুষ যাযাবর হিসেবে বসবাস করত। বিশেষত যারা গ্রামীণ জীবনধারায় অভ্যস্ত ছিলো। তাদের যাযাবর হিসেবে বসবাস করার অর্থ আবার এ নয় যে, তাদের মধ্যে কোনো ধরনের ব্যবস্থাপনা ছিল না। তাদেরও একটি ব্যবস্থাপনা ছিল, ইবনে খালদুন যেটিকে ‘উমরান আল বাদাবী’ হিসেবে নামকরণ করেছেন। অপরদিকে শহরে বসবাসকারীগণ, যেটিকে তিনি ‘উমরান আল হাদারী’ হিসেবে নামকরণ করেছেন। তিনি উল্লেখ করেছেন যে, সত্যিকারের উমরান অবশ্যই শহরের মধ্যে বিকশিত উমরান। এরপর তিনি ‘উমরান আল হাদারী’ নিয়ে আলোচনা করেন এবং এর পূর্বশর্তসমূহ কী কী সেগুলো নিয়েও আলোচনা করেন।
এক অর্থে বলতে গেলে এন্থনি গিডেন্স তাঁর Sociology নামক গ্রন্থে যে সকল বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন, তার প্রায় সকল বিষয় নিয়েই ইবনে খালদুন তাঁর মুকাদ্দিমার এ অধ্যায়ে আলোচনা করেছেন। তৃতীয় অধ্যায়ে তিনি রাজনীতির সাথে সম্পর্কিত বিষয়সমূহ আংশিকভাবে আলোচনা করেছেন।
তবে এন্থনি গিডেন্স সমাজবিজ্ঞান (Sociology) হিসেবে যে সকল বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন, সে বিষয়গুলোকে ইবনে খালদুনের মুকাদ্দিমার ইলমুল উমরানের মধ্যকার একটি অধ্যায় হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে।
এখন পর্যন্ত আমরা যে আলোচনা করলাম, তা থেকে বুঝতে পারি যে, বর্তমানে সমাজবিজ্ঞান বলতে যা বুঝায়, তা ইবনে খালদুনের সমাজবিজ্ঞানের তত্ত্বের নিকটে খুবই সামান্য। ইবনে খালদুন সমাজবিজ্ঞানের যে তত্ত্ব দিয়েছেন তা অনেক বিস্তৃত ও ব্যাপক। বর্তমান সময়ে যে বিষয়কে সমাজবিজ্ঞান নামে অভিহিত করা হয়, সেটিকে ইবনে খালদুনের ইলমুল উমরানের মধ্যে একটি অধ্যায়ের সমতুল্য হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে।
এরপর ইবনে খালদুন আরেকটু অগ্রসর হয়ে পরবর্তী ধাপে মানুষের একত্রে বসবাস করার ফলে সৃষ্ট ব্যবস্থাপনাসমূহ নিয়ে আলোচনা করেছেন। মানুষের তৈরি রাষ্ট্রকে ইবনে খালদুন দুভাগে বিভক্ত করেছেন। একটি হলো ‘মুলক’ অপরটি হলো ‘খেলাফত’।
ইবনে খালদুনের মতে, মুলক (Kingdom) হলো এমন জনগোষ্ঠী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রব্যবস্থা, যাদের নিকটে কোনো পয়গাম্বর আসেনি।
আর খেলাফত হলো সে রাষ্ট্রব্যবস্থা, যা একজন পয়গাম্বরের অনুসারীগণ যখন সে পয়গাম্বরের সাথে সম্পর্ক ঠিক রেখে কোনো আইনী ও রাষ্ট্রব্যবস্থা গড়ে তুলে।
এ দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে, মূলকের ক্ষেত্রে আকলী ও আমলী (প্রায়গিক) হিকমত প্রযোজ্য, আর খেলাফতের ক্ষেত্রে শরয়ী হিকমত প্রযোজ্য।
এক স্থানে ইবনে খালদুন বলেন, “আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁর আদেশকে ‘মুলক’ এর মাধ্যমে পরিপূর্ণ করেন, তবে এটি এমন সমাজের জন্য প্রযোজ্য, যে সমাজে পয়গাম্বর আসেননি কিংবা যে সমাজ পয়গাম্বরের সাথে কোনো সম্পর্ক স্থাপন করতে পারেনি কিংবা সম্পর্ককে বিছিন্ন করে ফেলেছে।”
চতুর্থ অধ্যায়ে তিনি শহর ও শহরের জীবন নিয়ে আলোচনা করেছেন। শহরের জীবনের বিষয়টি আসলে আমাদেরকে মনে রাখতে হবে, শহরের জীবন ধারা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ।
আল ফারাবীর ভাষায়, “মানুষ আখলাকী কামালিয়াত (পরিপূর্ণতা) মূলত শহরের মাধ্যমে লাভ করে থাকে।”
কেননা, একজন মানুষ যত বেশি ও যত ধরনের মানুষের সাথে মিশে, সে নিজেকে তত বেশি বিকশিত করতে পারে। এজন্য যদি প্রশ্ন করা হয় যে, ইনসানে কামিল কোথায় খুঁজে পাব, তাহলে আমি জবাবে বলব সবচেয়ে বড় ইনসানে কামিল বড় বড় শহরের মধ্যে পাওয়া যায়, গ্রামগঞ্জে কিংবা গুহার ভেতরে ইনসানে কামিল খুঁজে পাওয়া সম্ভব নয়।
যে ব্যক্তি সমাজ থেকে নিজেকে বিছিন্ন করে গুহার মধ্যে বসবাস করে, তার আখলাকী শ্রেষ্ঠত্ব তো কারো পক্ষে জানা সম্ভব নয়। অনুরূপভাবে গ্রামে বসবাসকারী মানুষের সুযোগও সীমাবদ্ধ।
অপরদিকে এমন এক ব্যক্তির কথা চিন্তা করুন, যার অঢেল সম্পদ রয়েছে এবং সে রাজনৈতিকভাবে অনেক বড় শক্তির নিয়ন্ত্রক কিংবা এমন একজন সেনাপতির কথাই ধরুন, যে অনেক বড় একটি বাহিনী নিয়ন্ত্রণ করে। এ ধরনের মানুষেরা যখন তাদের ক্ষমতা প্রয়োগ করে কাজ করে থাকে, তখন এমন অনেক সময় তাদের সামনে আসে, যখন তাদের পক্ষে আদালত ও আখলাকের মূলনীতিসমূহ মেনে চলা অনেক কঠিন হয়ে পড়ে। কিন্তু যদি তারা সে কঠিন অবস্থাতেও আখলাক ও আদালতের নীতিকে বিসর্জন না দেয়, তবে তখন সে অনুপাতে তাদের আখলাকী পূর্ণতা ফুটে উঠবে।
অনেক হাদীসেও আদিল বাদশাহ ও সৎ ব্যবসায়ীদের মর্যাদার কথা উল্লেখ করা হয়েছে।
ফলশ্রুতিতে যদি ইবনে খালদুনের দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে পর্যালোচনা করি, তাহলে দেখতে পাই, যদি কোনো ব্যক্তি এ কথা বলে, আমার ভুল করার সম্ভাবনা রয়েছে এজন্য আমি রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিষয়াদীর সাথে সম্পৃক্ত না হয়ে শুধু নিজেকে রক্ষা করার জন্য একাকী বসবাস করে সেখানে আমার আখলাকী শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করবো, এমন ব্যক্তির এ আখলাকী সন্ধানের খুব বেশি মূল্য নেই।
সত্যিকার মারেফত হলো অনেক বড় বড় পদে থেকেও নিজেকে আখলাক ও আদালতের মূলনীতির আলোকে পরিচালিত করা।
ইবনে খালদুন তাঁর মুকাদ্দিমার চতুর্থ অধ্যায়ে শহর সম্পর্কে অনেক ভিন্ন ভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন। তবে এখানে বিষয়টি শুধুমাত্র শহরের সোশিওলজির সাথে সম্পর্কিত নয়, শহরের সাথে বিভিন্নভাবে সম্পর্কিত আরও অনেক বিষয় তিনি এখানে আলোকপাত করেছেন।
মুকাদ্দিমার পঞ্চম অধ্যায় হলো জীবিকা সংক্রান্ত অধ্যায়। এ অধ্যায়ে তিনি জীবিকা অর্জনের উপায়, শিল্প-কৌশল এবং তৎসমুদয়ে ক্রিয়াশীল বিচিত্র অবস্থা ও সমস্যাবলি নিয়ে আলোচনা করেছেন। আর এ সকল বিষয় সরাসরি অর্থনীতির সাথে সম্পৃক্ত। এ অধ্যায়ে তিনি অর্থনীতি সংক্রান্ত এত অসাধারণ মূলনীতি বর্ণনা করেছেন, যার কারণে শুধুমাত্র মুসলমানগণই নন, অনেক অমুসলিম অর্থনীতিবিদও ইবনে খালদুনকে অর্থনীতির জনক হিসেবে বিবেচনা করে থাকেন। পাশ্চাত্যের যে সকল অর্থনীতিবিদগণ ইবনে খালদুনকে অর্থনীতির জনক হিসেবে বিবেচনা করেন, তাঁরা ছোটখাট কোনো অর্থনীতিবিদ নন। তাদের মধ্যে অনেক বিখ্যাত অর্থনীতিবিদগণও রয়েছেন।
ইবনে খালদুন অর্থনীতিকে ইলমুল উমরানের গুরুত্বপূর্ণ একটি অংশ হিসেবে দেখে থাকেন এবং স্থায়ী মূলনীতিসমূহের উপর ভিত্তি করে যে বিষয়সমূহ পরিবর্তিত হয়েছে, সে বিষয়সমূহকে বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করেছেন।
এখানে ইবনে খালদুনের দৃষ্টিভঙ্গির সাথে প্রচলিত সমাজবিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গির মূল পার্থক্য হলো সমাজবিজ্ঞানে শুধুমাত্র পদ্ধতিগত ক্ষেত্রে অপরিবর্তনীয় বিষয়সমূহকে অনুসন্ধান করা হয়ে থাকে। কেননা, সমাজবিজ্ঞান সমাজের উৎপত্তির ফলে সৃষ্ট একেবারে মৌলিক ও অপরিবর্তনীয় বিষয়সমূহ নিয়ে গবেষণা করে না । এর মূল কারণ হলো সমাজবিজ্ঞান স্থায়ী কিংবা অপরিবর্তনীয় কোনো কিছুর অস্তিত্বে বিশ্বাস করে না। সমাজবিজ্ঞানীরা বর্তমানে বিদ্যমান সমাজসমূহের জীবনধারার মধ্যে তুলনামূলকভাবে পরিবর্তনীয় ও অপেক্ষাকৃত কম পরিবর্তনীয় বিষয়কে পরস্পর সম্পর্কিত করে এদের লিপিবদ্ধ করার চেষ্টা করে থাকেন।
অপরদিকে ইবনে খালদুনের দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে স্বতন্ত্র পর্যায়সমূহ রয়েছে।
প্রথমটি হলো, সমগ্র মানবতা ও সমাজের অস্তিত্বের মূলকে গঠনকারী মূলনীতিসমূহকে ইবনে খালদুন অপরিবর্তনীয় ও চিরন্তন হিসেবে উল্লেখ করেছেন। ফলশ্রুতিতে এ দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে, বিশেষ করে সমাজবিজ্ঞান ও সাধারণভাবে সমাজবিজ্ঞানের সাথে সম্পর্কিত যত বিষয় রয়েছে, সকল বিষয়ের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ইবনে খালদুনের দৃষ্টিভঙ্গি স্বতন্ত্র।
দ্বিতীয়টি হলো, তিনি চিরন্তন বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ত থেকে অপেক্ষাকৃত কম পরিবর্তনীয় ও অধিক পরিবর্তনীয় বিষয়কে পরস্পর থেকে পৃথক করেন। এগুলোকে পৃথক করার পর এদেরকে একটিকে অপরটির সাথে সম্পৃক্ত করে বিশ্লেষণ করেন।
মুকাদ্দিমার সর্বশেষ অধ্যায় হলো জ্ঞান সম্পর্কিত। এ অধ্যায়টি একইসাথে জ্ঞানের ইতিহাস ও জ্ঞানের দর্শন সম্পর্কিত একটি অধ্যায়। শুধু তাই নয়, একদিক থেকে দেখলে এ অধ্যায়কে জ্ঞানের এনসাইক্লোপিডিয়া বলা যায়। ইবনে খালদুন এ অধ্যায়ে সমগ্র মানবতার উদ্ভাবিত জ্ঞান নিয়ে আলোচনা করেছেন। একইসাথে তিনি এ অধ্যায়ে জ্ঞান অর্জনের পন্থা সম্পর্কেও আলোচনা করেছেন এবং এ সম্পর্কে একটি সমালোচনামূলক দৃষ্টিভঙ্গি পেশ করেছেন।
এ অধ্যায়কে পর্যালোচনা করলে আমরা দেখতে পাই, এখানে ইবনে খালদুন চার পর্যায়ের ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি দাঁড় করিয়েছেন।
- মানুষ সমাজবদ্ধভাবে বসবাস করার কারণে যেখানেই মানুষ রয়েছে সেখানেই সমাজ রয়েছে। সেটি বাদাবী (গ্রাম্য) কিংবা হাদারী (শহুরে) যে কোনোটি হতে পারে। এর অর্থ হলো এটি একটি মুভমেন্ট পয়েন্ট।
- তাদের অস্তিত্ব কীভাবে সম্ভবপর হলো এটিকে বুঝার জন্য সহায়ক মূলনীতি সংক্রান্ত বিষয়।
- এ সকল বিষয়কে কীভাবে জানা যাবে এ সংক্রান্ত প্রশ্ন।
- আমরা এ সকল বিষয় সম্পর্কে কীভাবে জানি সে পন্থাকে নিয়ে সমালোচনামূলক দৃষ্টিভঙ্গি। এটি অনেক বড় একটি দৃষ্টিকোণ। এ সকল দৃষ্টিভঙ্গিকে সামনে রেখে ইবনে খালদুন তাঁর মুকাদ্দিমার সর্বশেষ অধ্যায়কে দাঁড় করিয়েছেন।
এ সকল বিষয়কে সামনে রাখলে দেখতে পাই, বর্তমান সময়ে সমাজবিজ্ঞানে যে সকল বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়ে থাকে, ইবনে খালদুন তাঁর মুকাদ্দিমায় সে সকল বিষয় নিয়েও আলোচনা করেছেন। তবে এ সকল বিষয় নিয়ে আলোচনা করার সময় স্বাভাবিকভাবেই তিনি যে সমাজে বসবাস করেছেন সে সমাজের অবস্থা তুলে ধরেছেন। সে সময়ে যেহেতু তিনি অনেক বড় বড় রাষ্ট্রের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে দায়িত্বপালন করেছেন, সেজন্য সে সকল রাষ্ট্রের বিভিন্ন বিষয়কেও তিনি বিবেচনায় নিয়ে আলোচনা করেছেন।
এ সকল বিষয় নিয়ে আলোচনা করার সময় তিনি যেটিকে মূল ভিত্তি হিসেবে ধরেছেন, সেটি হলো ইমাম ফখরুদ্দিন রাযীর মেটাফিজিক্স। তিনি রাযীর মেটাফিজিক্যাল তত্ত্বের উপর ভিত্তি করে এ সকল বিষয় নিয়ে গবেষণা করেছেন, শ্রেণিবিন্যাস করেছেন এবং লিপিবদ্ধ করেছেন।
অপরদিক থেকে দুটি বিষয়কে তিনি পৃথকভাবে তুলে ধরেন,
- চিরন্তন বা অপরিবর্তনীয়।
- ঐতিহাসিক কারণে অপেক্ষাকৃত কম বা বেশি পরিবর্তনীয়।
যদিও আমি আমার এ আলোচনায় এন্থনি গিডেন্সের রচিত বইকে কেন্দ্র করে আলোচনা করেছি, তবে বর্তমানে সমাজবিজ্ঞান একটি নয়। অঞ্চলভেদে ভিন্ন ভিন্ন সমাজবিজ্ঞান বা Sociology রয়েছে। যেমন জার্মান সোশিওলজি রয়েছে। যেমন, ম্যাক্স ওয়েবার জার্মান সোশিওলজিকে যেভাবে তুলে ধরেছেন, সেটির ধারণা ব্রিটিশদের সোশিওলজি থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। অপরদিক থেকে ফরাসি সমাজবিজ্ঞানী এমিলে দ্যুর্খায়েমের সমাজবিজ্ঞান যদি দেখি, তাহলে দেখতে পাই, জার্মান ও ব্রিটিশ সোশিওলজি থেকে ফ্রান্সের সোশিওলজি সম্পূর্ণ ভিন্ন। Marcel Mauss, Levi Strauss-সহ আরও অনেক ফরাসি সমাজবিজ্ঞানীর দিকে যদি তাকাই, তাহলেও দেখতে পাই, তাঁদের সমাজচিন্তা সম্পূর্ণ ভিন্ন।
অনুরূপভাবে, Social Theory-র নামে কিংবা সিস্টেম থিওরি হিসেবে গৃহীত অনেক তত্ত্ব রয়েছে, সেগুলোও আবার সম্পূর্ণ ভিন্ন। এছাড়াও মার্কসবাদীদের তৈরি করা সমাজতত্ত্বগুলোও সম্পূর্ণ ভিন্ন। এ কারণে আমরা এ কথা বলতে পারি যে, বর্তমান সময়ে সমাজবিজ্ঞান বুঝালে শুধুমাত্র নির্দিষ্ট কোনো একটি সমাজবিজ্ঞান নয়, বরং ভিন্ন ভিন্ন সমাজবিজ্ঞানকে বুঝানো হয়। এগুলোর মধ্যে শুধু যে বিষয়টি অভিন্ন সেটি হলো এদের নাম একই, কিন্তু এদের মধ্যে খুব বেশি মিল নেই।
এর কারণ হলো ফ্রান্সের সোশিওলজি ফ্রান্সের সমাজকে মূলভিত্তি হিসেবে ধরে গবেষণা করেছে এবং সমাজ সম্পর্কিত সকল প্রশ্নের উত্তর ফরাসি সমাজের উপর ভিত্তি করে দেওয়ার চেষ্টা করেছে।
জার্মান সোশিওলজি জার্মান সমাজকে মূলভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করে এবং সেটির আলোকে তাদের সমাজবিজ্ঞান গঠন করে থাকে। ব্রিটিশরা ইংল্যান্ডের সমাজকে মূলভিত্তি হিসেবে ধরে ও আমেরিকান সমাজবিজ্ঞানীরা আমেরিকার সমাজকে মূলভিত্তি হিসেবে ধরে সে আলোকে তাদের সমাজবিজ্ঞানকে গড়ে তুলেছেন।
এখানেই ইবনে খালদুন থেকে আমাদের যে বিষয়টি শিখতে হবে সেটি আমরা খুঁজে পাই। ইবনে খালদুন আরব, তুর্কি, বারবার (আফ্রিকান) ও ফ্রাঙ্কদের সমাজবিজ্ঞানকে পরস্পরের চেয়ে ভিন্ন বলে অভিহিত করেন না। তাঁর মতে, সকল মানুষের জন্য ও সমাজের জন্যই প্রযোজ্য, এমন একটি বিষয় রয়েছে। সে বিষয়টি হলো সকল মানুষ সমাজবদ্ধভাবে বসবাস করে, আর এ সমাজবদ্ধভাবে বসবাস করার মধ্যে একটি সংহতি বা আসাবিয়্যাত রয়েছে। আসাবিয়্যাত বা সংহতি ছাড়া সমাজবদ্ধভাবে বসবাস করা সম্ভব নয়।
এখানে লক্ষ্য করুন, সকল সমাজের জন্য প্রযোজ্য এমন একটি মূলনীতির কথা তিনি এখানে আলোচনা করছেন, সেটি হলো ‘আসাবিয়্যাত’।
ইবনে খালদুন দ্বিতীয় যে বিষয়টির প্রতি গুরুত্বারোপ করেন, তা হলো একটি সমাজের বৈশিষ্ট্য সে সমাজের ভৌগলিক অবস্থানের উপর নির্ভরশীল, বিশেষ করে এটি পরিবেশের সাথে সম্পর্কিত। ফলশ্রুতিতে সে পরিবেশকেও বিবেচনায় নিলে আমরা দেখতে পাই, ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন ধারার সমাজ গড়ে উঠে।
তৃতীয় বিষয় হলো, যদি মানুষগণ কোনো একজন পয়গাম্বরের অনুসরণ করে, তাহলে রক্তের সম্পর্ক এবং আঞ্চলিকতার সম্পর্কও ছিন্ন করে সে পয়গাম্বরের অনুসারীদের মধ্যে একটি ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক গড়ে উঠে ও সে পয়গাম্বরের দেখানো পন্থার আলোকে একটি ব্যবস্থা গড়ে উঠে। আর সে সময়ে ইন্দোনেশিয়াতে বসবাসকারী মুসলমানদের সাথে মরক্কো, সাইবেরিয়া, আফ্রিকা ও মধ্য এশিয়াতে বসবাসকারী মুসলমানদের ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক গড়ে উঠে এবং তারা একই লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে একটি সভ্যতা বিনির্মাণের জন্য চেষ্টা করে। এখানে একটি বিষয় লক্ষ্য করুন, ভিন্ন ভিন্ন পরিবেশ ও অঞ্চল হওয়া সত্ত্বেও একজন পয়গাম্বরের অনুসরণের ফলে তাদের মধ্যে খুব শক্তিশালী একটি আসাবিয়াত (সংহতি) গড়ে উঠতে পারে।
এ দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে, বর্তমান সময়ে যদি আমরা সমাজ নিয়ে গবেষণা করতে চাই তাহলে প্রথমেই যে কাজটি করতে হবে সেটি হলো পয়গাম্বররের অনুসরণকারী উম্মাহকে তথা মুসলিম উম্মাহকে একটি অভিন্ন জাতিসত্তা হিসেবে গ্রহণ করতে হবে। এরপর এর নিচে উপবিভাগ হিসেবে বিভিন্ন অঞ্চলের মুসলমানদের মধ্যে যে ভিন্নতা রয়েছে সেটি তুলে ধরতে হবে। আরব উপদ্বীপে বসবাসকারী মুসলমানদের ভিন্নতা, উত্তর আফ্রিকাতে বসবাসকারী মুসলমানদের ভিন্নতা, মধ্য এশিয়া ও বলকান অঞ্চলের মুসলমানদের ভিন্নতাকে তুলে ধরতে হবে। এগুলা একইসাথে এক, আবার একইসাথে এদের মধ্যে ভিন্নতাও রয়েছে। এটিকে আমরা ওয়াহদাতের মধ্যে কাসরাত (একের মাঝে বহুত্ব) বলে অভিহিত করতে পারি।
এখন যদি রাশিয়ার কথা চিন্তা করি, রাশিয়ার সমাজ কোন মূলনীতিগুলোর উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এ প্রশ্নও আমাদেরকে করতে হবে। যেমন রাশিয়া যখন সোভিয়েত ইউনিয়ন হিসেবে ছিল, তখন তারা নিজেদেরকে কম্যুনিস্ট হিসেবে দাবি করত। তবে এর পেছনে রাশিয়ার জাতীয়তাবাদ খুবই শক্তিশালী একটি ফ্যাক্টর ছিলো এবং তারা অন্যান্য অঞ্চলকে রাশিয়ার মধ্যে আত্মীকরণ করার জন্য চেষ্টা চালিয়েছে, তবে এক্ষেত্রে তারা সফল হতে পারেনি। কিন্তু এখন তারা রাশিয়ান জাতীয়তাবাদের সাথে অর্থোডক্সিয়া ধর্মবিশ্বাসকে একত্রিত করে নতুন করে একটি শক্তি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে।
অনুরূপভাবে যদি ইউরোপীয় ইউনিয়নের দিকে তাকাই, তাহলে দেখতে পাই, সেখানে অর্থোডক্স, ক্যাথলিক ও প্রোটেস্ট্যান্ট খ্রিস্টানরা রয়েছে। এরা কেউ কাউকেই পছন্দ করে না। দেশ হিসেবে দেখলে ইউরোপীয় ইউনিয়নে ফ্রান্স, ইতালি, স্পেন ও জার্মানি রয়েছে। ব্রিটেনও ছিল ইতিপূর্বে। কিন্তু এদের মধ্যে অভিন্ন কোনো কিছু না থাকা সত্ত্বেও, পঞ্চাশ বছর আগেও এরা একে অপরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার পরেও শুধুমাত্র রাজনৈতিক একটি প্রকল্পের অংশ হিসেবে অর্থনৈতিক কারণে একক একটি রাষ্ট্রে পরিণত হওয়ার চেষ্টা করছে এবং একটি অভিন্ন সমাজ গঠনের জন্য চেষ্টা চালাচ্ছে।
আমরা যখন বাইরে থেকে দেখি, তখন আমাদের মনে একটি প্রশ্ন আসে, সেটি হলো এরা কি আদৌ সফল হতে পারবে? আমরা এটি চাই যে তারা সফল হোক, দুনিয়ার সকল মানুষ তাদের মানবিক মর্যাদা নিয়ে আদালত ও শান্তির মধ্যে বসবাস করুক, কেউ কারোর উপর অত্যাচারের স্টীমরোলার পরিচালনা না করুক।
কিন্তু যদি বাস্ততার নিরিখে বিবেচনা করি, তাহলে কী দেখি? তাহলে দেখতে পাই যে, সমগ্র ইউরোপীয় ইউনিয়ন আজ কঠিন সংকটের সম্মুখীন। কেন? কারণ তাদের মধ্যে আসাবিয়্যাত নেই।
এখন বর্তমান সময়ে আমরা ইলমুল উমরানকে কীভাবে ব্যবহার করবো? আমি মনে করি এ নামে ব্যবহার করতে কোনো সমস্যা নেই। তবুও যদি এটিকে আমাদের তরুণ প্রজন্মের নিকট সহজভাবে তুলে ধরতে চাই, তাহলে আমরা একে ‘ইলমুল মাদানী’ (সভ্যতা সংক্রান্ত জ্ঞান) হিসেবে অভিহিত করতে পারি।
আমরা দেখতে পাই যে, ইলমুল উমরান বা ইলমুল মাদানী’র মধ্যে একইসাথে বিশ্বাস রয়েছে, আখলাক রয়েছে, রাজনীতি রয়েছে, আইন রয়েছে, একইসাথে সমাজ ও সমাজবিজ্ঞান রয়েছে, একইসাথে সামাজিক মনস্তত্ত্ব, সাইকোলজি, মেটাফিজিক্স রয়েছে, এক অর্থে বলতে গেলে এর মধ্যে সকল কিছুই রয়েছে। এ বিষয়টিকে যদি বিবেচনায় নেই, তাহলে দেখতে পাই, ইবনে খালদুনের মুকাদ্দিমা আমাদেরকে এ সকল বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে সাহায্য করে।
ইবনে খালদুন ও ইলমুল উমরান নিয়ে আলোচনা করার পর এ কথা অনায়াসেই বলা যায় যে, ইবনে খালদুনকে শুধুমাত্র একজন সমাজবিজ্ঞানী হিসেবে আখ্যায়িত করা একজন মানুষকে শুধুমাত্র তাঁর কোনো একটি অঙ্গের নামে নামকরণ করার শামিল। যেমন মানুষের চোখ আছে, এখন তাকে শুধুমাত্র চোখ বলে ডাকা কি সমীচীন হবে? মানুষের কান আছে, এখন যদি কেউ তাকে কান বলে ডাকে, তাহলে কেমন হবে? এটি মোটেই ঠিক হবে না।
– একইভাবে ইবনে খালদুনকে অর্থনীতিবিদ বললেও ইবনে খালদুনের পরিচয়কে অসম্পূর্ণ করে রাখা হবে।
– ইবনে খালদুনকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানী বলার অর্থ হলো তাঁকে অসম্পূর্ণভাবে তুলে ধরা।
– ইবনে খালদুনকে শুধুমাত্র দার্শনিক বলে আখ্যায়িত করাও তাঁর প্রতি অবিচার করার শামিল।
তাহলে আমরা ইবনে খালদুনকে কী নামে ডাকব? তাঁকে আমরা তাঁর রাখা নামেই ডাকব। সে নামটি কী? সেটি হলো, তিনি হলেন ‘ইলমুল উমরানের প্রতিষ্ঠাতা’।
আর ‘ইলমুল উমরান’কে বর্তমান ভাষায় আমরা ‘ইলমুল মাদানী’ বা ‘সভ্যতা সংক্রান্ত জ্ঞান’ বলে অভিহিত করতে পারি। ইবনে খালদুন একইসাথে একটি সভ্যতা কীভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়, কীভাবে তার অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখে, একটি সভ্যতা কোন ধরণের সংকটে নিপতিত হতে পারে এ সকল বিষয়কেও অসাধারণভাবে তুলে ধরেছেন। আর সভ্যতা সংক্রান্ত সকল বিষয়কে এভাবে বর্ণনা করার কারণে ইবনে খালদুন থেকে আমাদের অনেক কিছু শেখার আছে। কেননা আমরা ইসলামী সভ্যতার পুনর্জাগরণ চাই। আমরা যেহেতু ইসলামী সভ্যতার পুনর্জাগরণ চাই, তাই আমাদের অবশ্যই ইবনে খালদুনের মুখাপেক্ষী হতে হবে।
তবে একটি বিষয় না বললেই নয়, ইবনে খালদুনকে বুঝার ক্ষেত্রে একটি বড় সংকট রয়েছে, অনেকেই তাঁকে না বুঝেই তাঁর ব্যাপারে অপবাদ দিয়ে থাকে। তাঁর কথার উদ্দেশ্য এবং মর্মকে বুঝার পরিবর্তে যদি তাঁকে শাব্দিকভাবে বুঝার চেষ্টা করা হয়, তাহলে তাঁকে বুঝার জন্য বর্তমান সময়ে তাঁর শব্দসমূহই সবচেয়ে বড় বাধা হয়ে দাঁড়াবে। এ কারণে আক্ষরিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে যদি ইবনে খালদুনকে বুঝার চেষ্টা করা হয়, তাহলে মুকাদ্দিমার লাইনসমূহই ইবনে খালদুনকে বুঝার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় প্রতিবন্ধক হিসেবে কাজ করবে।
তাহলে কী করতে হবে?
ইবনে খালদুনের লেখাকে পড়তে হবে, তবে তাকে শুধু আক্ষরিকভাবেই নয় বরং বর্তমান সময় ও তাঁর সাথে সম্পর্ক সৃষ্টি করতে হবে এবং এক্ষেত্রে আমাদেরকে সফল হতে হবে।
ইবনে খালদুন তাঁর মুকাদ্দিমার মাধ্যমে যে কাজটি করেছেন সেটিকে আমরা সোশ্যাল অন্টোলজি নামে অভিহিত করতে পারি। আর ইবনে খালদুনের সবচেয়ে বড় সফলতা হলো এ সোশ্যাল অন্টোলজি সৃষ্টি করতে পারা। সোশ্যাল অন্টোলজি সৃষ্টি করার দৃষ্টিকোণ থেকেও সত্যিকারার্থেই জ্ঞানের ইতিহাসে এর কোনো তুলনা নেই। যদিও ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে পাশ্চাত্যের কিছু চিন্তাবিদ কিছু কিছু কাজ করেছেন যেগুলোকে সোশ্যাল অন্টোলজি হিসেবে আখ্যায়িত করা যায়। অনুরূপভাবে বিংশ শতাব্দীতেও কিছু দার্শনিক এরকম কিছু করার চেষ্টা করেছেন কিন্তু তাঁদের সংখ্যা হাতেগোনা কয়েকজন মাত্র। তবে এদের কেউই ইবনে খালদুনের মত এক্ষেত্রে এত গভীর ও সামগ্রিক কোনো কিছু করতে পারেননি। যার কারণে ইবনে খালদুনের সাথে তাঁদের কোনো তুলনাই চলে না।
ইবনে খালদুনের এ সোশ্যাল অন্টোলজির মূল কাঠামোটি কী?
এ বিষয় সম্পর্কে ইবনে খালদুন প্রথম যে বিষয়টি উল্লেখ করেন সেটি হলো মানুষ মূলসত্তাগত দিক থেকে দুর্বল একটি সৃষ্টি এবং অন্যের উপর নির্ভরশীল এক সৃষ্টজীব। এ বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আমরা সকলেই এমন। আর সবচেয়ে নির্ভরশীল ব্যক্তি হলো সে, যার অবস্থান সমাজে সবচেয়ে উপরে।
যেমন ধরুন, আপনি এমন একটি দেশের প্রেসিডেন্ট, যে দেশের জনসংখ্যা ১০ কোটি। এর অর্থ হলো আপনি একজন প্রেসিডেন্ট হিসেবে সে দেশের ১০ কোটি মানুষের উপর নির্ভরশীল। তারা আপনাকে তাদের সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা দিয়েছেন বলেই আপনি শক্তিশালী। কিন্তু যদি তারা আপনার প্রতি তাদের সমর্থন প্রত্যাহার করে নেয়, পরের দিন আপনি সাধারণ একজন নাগরিক ছাড়া আর কিছু নন। মানুষের মূল বৈশিষ্ট্য হলো মানুষ মূলসত্তাগত দিক থেকে দুর্বল এবং অন্যের মুখাপেক্ষী।
দ্বিতীয় যে বিষয়টি তিনি উল্লেখ করেন, তা হলো মানুষ তার নিজের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য অন্য মানুষের সাথে কথা ও কাজের ক্ষেত্রে পারস্পারিক সহযোগিতার চুক্তি করতে বাধ্য।
তৃতীয় বিষয়টি হলো, যারা কথা ও কাজের ক্ষেত্রে পারস্পারিক সহযোগিতার চুক্তি করে, তারা সুযোগ ও সম্ভাবনার আলোকে একটি সিস্টেম বা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করে থাকে। একটি নিজাম বা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা ছাড়া নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখা সম্ভবপর নয়। সকল মানুষই এমন।
চতুর্থ বিষয়টি হলো, কথা ও কাজের ক্ষেত্রে পারস্পরিক সহযোগিতার যে চুক্তি, সে চুক্তির ভিত্তিতে গড়ে উঠা প্রতিটি ব্যবস্থা (প্রতিষ্ঠান) একটি শক্তির বহিঃপ্রকাশ ঘটায় এবং একটি সমাজের মূল সে সমাজকে গঠনকারী মানুষগণের একে অপরকে সাহায্য ও সমর্থনের ক্ষেত্রে যে শক্তি, সে শক্তির সাথে সম্পর্কিত। পারস্পরিক সাহায্য-সহযোগিতা ও সমর্থনের দিক থেকে মানুষ যত বেশি শক্তিশালী, তাদের বসবাসকৃত সে সমাজও তত বেশি শক্তিশালী।
পঞ্চম বিষয়টি হলো, হাতে যে শক্তি আছে, তা যত বেশি ব্যবহার করা হবে, তত বেশি বৃদ্ধি পাবে ও বড় হবে। এ বিষয়টিও খুবই গুরুত্বপূর্ণ।
সর্বশেষ বিষয় হলো প্রতিটি শক্তিরই একটি সীমা ও শেষ রয়েছে। সীমায় উপনীত হওয়া কিংবা উদ্দেশ্যে উপনীত হওয়া প্রতিটি শক্তিই ধীরে ধীরে দুর্বল হয়ে পড়ে এবং তার স্থান অন্য শক্তির নিকট ছেড়ে দেয়।
ইবনে খালদুনের এ সোশ্যাল অন্টোলজির মূল ফ্রেমটির তৃতীয় বিষয়টির অর্থাৎ যারা কথা ও কাজের ক্ষেত্রে পারস্পরিক সহযোগিতার চুক্তি করে, তারা সুযোগ ও সম্ভাবনার আলোকে একটি সিস্টেম বা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করে থাকে এ প্রশ্নের জবাব সমাজবিজ্ঞান দেওয়ার চেষ্টা করে। সমাজবিজ্ঞান শুধু এ কাজটিই করে থাকে।
কিন্তু ইবনে খালদুনের সামগ্রিক ব্যবস্থার মধ্যে এটি শুধুমাত্র একটি বিষয়, এছাড়া আর অন্য কিছু নয়।
এখন বর্তমান সময়ে আসা যাক। ইবনে খালদুন আমাদের বর্তমান সময়ের জন্য কী বলেন? বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর বিভিন্ন অনুষদে সমাজবিজ্ঞান পড়ানো হয়। সে সকল অনুষদের সমাজবিজ্ঞান বিভাগের দিকে যদি তাকান, তাহলে দেখতে পাবেন, সেখানে ঐ সমাজের কোনো কিছু নিয়ে গবেষণা করা হয় না। যেমন, পাকিস্তান বলেন, তুরস্ক বলেন, মিসর বলেন কিংবা বাংলাদেশ বলেন, এ সকল দেশের সমাজবিজ্ঞান বিভাগে নিজেদের দেশের সমাজ নিয়ে গবেষণা হয় না। যেমন, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ ইউরোপের যে সকল ধারা অনুসরণ করেন, সাধারণত সে সকল ধারার থিওরিকেই বেশি প্রাধান্য দিয়ে থাকেন। যেমন, যদি কেউ জার্মান ভাষা জেনে থাকেন, তাহলে তিনি জার্মান চিন্তাবিদগণ জার্মান সমাজকে সামনে রেখে যে সকল থিওরি দিয়েছেন, সে সকল থিওরীকেই শিক্ষার্থীদেরকে শিখান।
আর যারা ইংরেজি জানেন, তারা আমেরিকা কিংবা ইংল্যান্ডের সমাজবিজ্ঞানের থিওরিকে শিক্ষার্থীদেরকে শিখিয়ে থাকেন এবং আমেরিকার সমাজকে সমাজবিজ্ঞান হিসেবে তুলে ধরেন। একইভাবে যারা ফ্রেঞ্চ জানেন, তারাও ফ্রান্সের সমাজকে সমাজবিজ্ঞান হিসেবে তাদের শিক্ষার্থীদের সামনে তুলে ধরেন।
এখন কথা হলো বাংলাদেশের সমাজে জন্মগ্রহণকারী বাংলাদেশী যুবকগণ কি সমাজবিজ্ঞান বিভাগসমূহে তাদের নিজেদের সমাজ ও দেশ সম্পর্কে জানার সুযোগ পায়?
এর জবাব হলো, না, পায় না!
একবার চিন্তা করে দেখুন তো, এটি কত মারাত্মক একটি বিষয়!
শুধুমাত্র সমাজবিজ্ঞানই নয়, সকল বিভাগের ক্ষেত্রে এ একই কথা প্রযোজ্য। যারা অর্থনীতি পড়ে, তারা তাদের নিজেদের অর্থনীতি সম্পর্কে কতটুকু ওয়াকিবহাল?
তাহলে ইবনে খালদুন আমাদেরকে মূল যে বিষয়টি শিক্ষা দিয়ে থাকেন, সে বিষয়টি হলো আমরা যদি সমাজবিজ্ঞান তৈরি করতে চাই, তাহলে আমাদের নিজেদের সমাজকে মূলভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করে সমাজবিজ্ঞান তৈরি করতে হবে। সমাজবিজ্ঞান সংক্রান্ত গবেষণার ক্ষেত্রে আমাদের সমাজকে একইসাথে জ্ঞানের বিষয় ও জ্ঞানের উৎস হিসেবে তৈরি করতে হবে। যদি আমরা আমাদের সমাজকে একইসাথে জ্ঞানের বিষয় ও জ্ঞানের উৎস হিসেবে তৈরি করতে পারি, তাহলে হয়তোবা আমরা আমাদের সমাজের উপর ভিত্তি করে এমন এমন সব থিওরী সৃষ্টি করতে সক্ষম হব, যেগুলো দেখে জার্মানি, ফ্রান্স, ইংল্যান্ড ও আমেরিকা তাদের সমাজকে সমালোচনার দৃষ্টিতে দেখার সুযোগ পাবে। পরবর্তীতে তারা নিজেদেরকে পুনর্গঠন করতে পারবে। এটি হয়তো অনেকের কাছে কল্পনাপ্রসূত হতে পারে, কিন্তু এটি মোটেই অসম্ভব নয়। অতীতে তারা মূলত আমাদের সমাজ থেকেই শিখেছে, এখনো যদি আমরা এক্ষেত্রে সফল হতে পারি, তাহলে তারা আমাদের নিকট থেকেই শিখবে। কারণ আমরাই হলাম বিশ্ববিবেক।
এ বিষয়টিকে বিবেচনায় নিয়ে সমাজবিজ্ঞান সংক্রান্ত যত বিষয় রয়েছে সকল বিষয়ের ক্ষেত্রে আমাদের সমাজকে সামনে রেখে তত্ত্ব (থিওরী) ও মডেল দাঁড় করাতে হবে।
আর আমাদের সমাজ কী?
আমাদের সমাজ হলো মুসলিম সমাজ। আমাদের সমাজ ইসলামী সভ্যতা ও মুসলিম উম্মাহর একটি বড় অংশ। এখন যদি আমাদের দৃষ্টিভঙ্গিকে আরেকটু বিস্তৃত করি, তাহলে আমাদের যারা সমাজবিজ্ঞান পড়ে, তাদের মৌলিক দায়িত্ব হলো মুসলিম উম্মাহর মধ্যকার ঐক্যকে কীভাবে সুদৃঢ় করা যায়, কীভাবে মুসলমানদের মধ্যকার কথা ও কাজের ক্ষেত্রে পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধি করা যায় এ সকল বিষয় নিয়ে গবেষণা করা।
ইনশাআল্লাহ, আমরা ধীরে ধীরে ইবনে খালদুন যেদিকে ইঙ্গিত করেছেন, সে দিক বিবেচনায় রেখে আমাদের সমাজবিজ্ঞানকে নতুন করে গড়ে তুলব। নতুন করে সমগ্র মানবতা আমাদেরকে দেখে নিজেদের ভুলভ্রান্তি সংশোধন করে নিবে। আর আমি বিশ্বাস করি, সেদিন খুব বেশি দূরে নয়।
অনুবাদ : বুরহান উদ্দিন আজাদ।