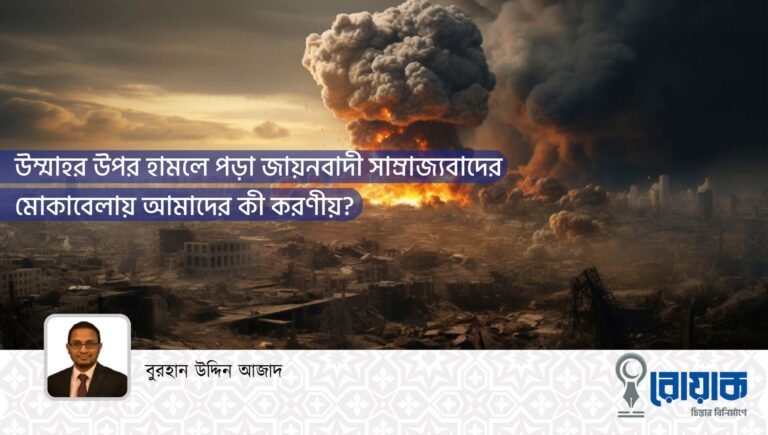এক.
মনে করুন, আপনি একজন প্রফেশনাল ফোটোগ্রাফার। দামী একটা ক্যামেরা নিয়ে ঢুঁ মারছেন উত্তরের কৃষিনির্ভর কোনো একটি গ্রামের মেঠোপথ ধরে। থেকে থেকে ক্লিক-ক্লিক শব্দ তুলে ভরে যাচ্ছে আপনার ক্যামেরার মেমোরি। ইতি-উতি তাকিয়ে পছন্দমাফিক কম্পোজিশন খুঁজছেন আপনি।
সবেমাত্র ভোরের আলো ফুটতে শুরু করেছে তখন। দূরদিগন্তে সূর্য উঁকি দিচ্ছে, গাছ বা কৃষিক্ষেত-এর পেছন থেকে বেরিয়ে আসছে রক্তিম বা কমলা-রং। রক্তিম সে আলোয় ডানা মেলে ক্ষুধার্ত পেটে পাখিরা তাদের নীড় ছাড়তে শুরু করেছে, চতুর্দিকে কান-জুড়ানোর পাখির কলকাকলি। ঘাস ও পাতার ডগায় জমে থাকা শিশিরবিন্দুগুলো ভোরের আলোয় মুক্তোর মতো ঝলমল করছে। সূর্য-গাছ-পাখি-কৃষিক্ষেত—সৌন্দর্যের অপরূপ লীলাভূমি। ন্যাচার-ফোটোগ্রাফির জন্য একেবারে উপযুক্ত এক সময়। মনের আনন্দে ছবি তুলেই যাচ্ছেন আপনি। প্রতিটি ছবি যেনো পূর্বের ছবির সৌন্দর্যকেও ছাপিয়ে যাচ্ছে।
হঠাৎ-ই আপনার চোখ পড়লো দূরের এক মেঠোপথে। একজন কৃষক তার কাঁধে করে ভার বয়ে নিয়ে চলছেন তার নিজস্ব গন্তব্যে। দু’পাশে ঝুলছে কোনো এক শস্যে পরিপূর্ণ দু’টি ডালা। আপনার এবং আপনার অবজেক্টের (কৃষক) মাঝে রয়েছে বেশ বড়সড় একটা কৃষিজমি; সে জমির পাতা ও ঘাসের উপরের তরল বিন্দুগুলো আলোর বিচ্ছুরণ ঘটাচ্ছে। ছবির জন্য একেবারে দারুণ মুহূর্ত। ক্যামেরাটা চোখের সামনে তুলে একাধারে অনেকগুলো ছবি তুললেন। চোখ থেকে আপনার প্রিয় যন্ত্রটি নামিয়ে ছবিগুলো দেখলেন, স্যাটিসফাইড।
এবার তাহলে ফেরার পালা। ফিরলেন বাসায়। বেছে বেছে দুয়েকটা ছবি সযত্নে রেখে দিলেন। এমনকি জাতীয় পর্যায়ে পুরষ্কারও বাগিয়ে আনলেন কৃষকের সেই ছবিটি দিয়ে।
কিন্তু, আমার মনে আপনার জন্য কিছু প্রশ্ন আছে।
আপনি কি একবারও সেই কৃষকের নিকট গিয়ে তার দৈনন্দিন জীবন নিয়ে প্রশ্ন করেছেন?
লেন্সের সহায়তায় যে মানুষটার প্রতিকৃতির জন্য আপনি পুরস্কার পর্যন্ত জয় করলেন, সেই কৃষকের মনেও কি তখন এতোটা সুখ ছিলো?
সে কি তার পরিশ্রম আর ফলানো শস্যের যথাযথ মূল্য পাচ্ছে?
আপনি যে ছবিটি দিয়ে গ্রাম বাংলার সৌন্দর্য ফুটিয়ে তুলে প্রশংসা কুড়াচ্ছেন, সেখানে সেই কৃষক কি আদৌ ভালো আছেন?
গ্রাম-বাংলার সৌন্দর্যই যাদের জন্য, তারাই যদি ভালো না থাকে, তাহলে আপনার এই ছবি তার কী উপকারে আসবে?
আপনার ছবিটা কি তাহলে বাস্তবতা-বিবর্জিত হলো না?
অন্যর দুর্দশাকে সুন্দর দ্বারা পরিবর্তন করে সেটাকে ভুলভাবে উপস্থাপন করাটা কি অন্যায় না?
উত্তরগুলো জানা খুবই জরুরি। কারণ, গ্রাম-বাংলার অপরূপ সৌন্দর্যের বুলি আওড়িয়ে প্রতিবছর এমন অসংখ্য ছবি তোলা হচ্ছে। ভুল বার্তা দিয়ে আকৃষ্ট করা হচ্ছে মানুষ ও পর্যটকদের। লক্ষ লক্ষ মানুষ উত্তরের এমন এলাকাগুলোয় এসে ভ্রমণ করছে—নিজ খরচ, আত্মীয়-স্বজন বা বন্ধু-বান্ধবের মাধ্যমে। নিজেদের সমস্ত দুঃখ-দুর্দশা-মনোকষ্ট প্রকৃতির কাছে ন্যস্ত করে প্রকৃতির সৌন্দর্যকে তার স্থানে বদল করে নিয়ে খুশিমনে তারা বাড়ি ফিরছে।
কিন্তু, যারা এই প্রকৃতিকে এমন পরম যত্নে আগলে রেখেছে, যাদের সহায়তায় ফলে আত্মিক প্রশান্তির এমন অসাধারণ এক পরিবেশ উপভোগ করছে সবাই, যাদের হাড়-ভাঙা খাটুনি ও পরিশ্রমের ফল হিসেবে একেবারে তাজা ও টাটকা শস্য পাচ্ছি আমরা, একবারও কি তাদের নিয়ে আমরা প্রশ্ন করেছি যে, তারা কেমন আছে? কী খাচ্ছে? দৈনন্দিন জীবন কেমন? সাধারণ খরচের ন্যূনতম অর্থও আসে কোথা থেকে? ফসল কাটার পরমুহূর্তে তাদের অনুভূতি কী? তারা কি তাদের পরিশ্রম ও ফসলের ন্যায্য মূল্য পায়? তাদের জন্য রাষ্ট্রীয় পর্যায় থেকে কী কী সুবিধা দেওয়া হচ্ছে? নাকি অর্থ বরাদ্দের নামে সব লুটেপুটে খাওয়া হচ্ছে?
এগুলো গেলো কৃষক বা চাষীর ক্ষেত্রগুলোতে উদিত হওয়া কিছু প্রশ্ন। আবার শস্যের ক্ষেত্রেও এমনই কিছু প্রশ্নের উদয় হয়। যেমন, একই পেশায় নিয়োজিত থাকার পরেও পূর্বের প্রজন্মের তুলনায় এই প্রজন্মের গড়-বয়স কমছে কেন? একই জমির একই শস্য কেন আমাদেরকে পূর্বের মতো শক্তি সঞ্চয় করতে সহায়ক হচ্ছে না? কেন কৃষকেরা প্রতিনিয়তই শ্বাসকষ্টের রোগী হচ্ছে এবং সে সংখ্যাটা কেন উত্তরোত্তর বেড়েই চলছে? রাসায়নিক সার বা রাসায়নিক ঔষধের পরিমাণ কেন বৃদ্ধি পাচ্ছে প্রতিনিয়ত? এতো পরিমাণ রাসায়নিক সার বা রাসায়নিক ঔষধ দেবার পরেও কেন শস্যে পোকামাকড়ের উপদ্রব কমে না?
প্রশ্নগুলো উত্তর জানা জরুরি। শুধু প্রশ্ন করে বিশৃঙ্খল অবস্থার সৃষ্টি করার কোনো অর্থই হয় না। বিপরীতে যৌক্তিক প্রতিটি প্রশ্নের জন্য প্রয়োজন যৌক্তিক ব্যাখ্যা। নতুবা বুঝতে হবে, কোথাও না কোথাও বড় ধরনের কোনো ঘাপলা রয়েছে। আর সেসবের সমাধানও করতে হবে।
চলুন, তাহলে এবার এসব সৌন্দর্যের পেছনে লুকিয়ে থাকা অন্ধকার জগতটাকে উন্মোচন করি। একটু দেখে আসি বাংলার কৃষকেরা কেমন আছেন! জেনে আসি তাঁদের উৎপাদিত ফসলগুলো কতটুকু স্বাস্থ্যসম্মত! বর্তমান এই বিশ্বব্যবস্থাপনার কাছে তাঁরা কতোটুকু জিম্মি! রাষ্ট্রের কাছে তাঁরা কতোটুকু অসহায়! কতোটা দুর্বিষহ তাঁদের দৈনন্দিন জীবন!
দুই.
প্রথমেই একটু নজর দেই একজন কৃষকদের দৈনন্দিন জীবনের দিকে।
“আধুনিকতা”র বর্তমান এই সময়েও একজন কৃষকের দৈনন্দিন জীবনটা খুবই দুর্বিষহ। ঠাণ্ডায় কাঁপতে কাঁপতে বা ঘামে ভেজা একটা শরীর নিয়ে একদম ভোরে জেগে ওঠে সাধারণ একজন কৃষক। বাসায় থাকে না পর্যাপ্ত পরিমাণের খাবার। যতটুকু থাকে, তা দিয়ে সকাল-দুপুরের খাবারের বন্দোবস্ত করতে হবে। অতএব, দু’মুঠো চিড়ে-গুড় খেয়ে কৃষির সরঞ্জামাদি নিয়ে সকালে বের হয় জমির উদ্দেশ্যে।
সকাল-দুপুর কাটে জমিতেই। মাঝে একটু দুবেলা খাওয়ার জন্য কাজ থেকে অবসর নিতে হয়। বাসা থেকেই বাটিতে করে খাবার পৌঁছে দেওয়া হয় জমিতেই। দুপুরে খাওয়ার পর হয়তো কোনো এক গাছের নিচে ক্ষণিকের জন্য বিশ্রাম নেয়। এভাবেই কাটে বিকেল পর্যন্ত। বিকেলের দিকে টুকটাক কিছু সবজি নিয়ে বাজারের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয় একজন কৃষক।
সবজি বিক্রি শেষে যতটুকু বা আয় হয়, তা নিয়ে পরেরদিনের খাবারের জন্য চাল-ডাল কেনা হয়। আবার যেসব সবজি সকালে বিক্রি করতে হয়, সেসব সবজি দিনের শুরুতে নির্দিষ্ট বড় একটি হাটে বিক্রি করে সে অর্থ দিয়ে আগামী কিছুদিনের খাবারের জন্য বাজার করে নিয়ে আসে অর্থকষ্টে দিনাতিপাত করা একজন কৃষক।
দিনভর একটানা হাড়ভাঙা খাটুনির পর সন্ধ্যার পরে পরিবারের সকলের সাথে কথা বলার সুযোগ হয় একজন কৃষকের। সেসময়টাতেই খোঁজ নেয় সে পরিবারের বাকী সদস্যদের। অর্থাভাবে সন্তানদের সে দিতে পারে না পর্যাপ্ত শিক্ষার উপকরণ। আবার, বাহ্যিক বেশভূষার কারণে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে গিয়েও প্রতিনিয়ত সে হয় নিগৃহীতের শিকার। অর্থাভাবে বাধ্য হয়ে কৃষকরা তাদের সন্তানদেরকে ভর্তি করিয়ে দেয় সরকারি বিদ্যালয়গুলোতে। কিন্তু, এসব প্রতিষ্ঠানে পড়াশোনার মান যে কতোটা তলানিতে গিয়ে ঠেকেছে, তার ভয়াবহ সমীকরণ আমরা পত্রিকার পাতা থেকে শুরু করে একজন শিক্ষার্থীর মুখেও শুনি।
এই গেলো এক অবস্থার কৃষকদের জীবন। আরেক অবস্থার কৃষকদের জীবনটাও এমন। তবে, বিভিন্ন মৌসুমে ফলিত ফসল, যেমন–চাল, গম বা আলু নিজেদের জন্যই রেখে দেয় পরের মৌসুমে পুনরায় ফসল ঘরে তোলার আগ পর্যন্ত। সে সময় পর্যন্ত শুধু এই ফসলটুকুই তাদের খাবারের একমাত্র সম্বল।
এদের আয়ের সময়ই থাকে মাত্র তিনটে। রবি, খরিপ-১ ও খরিপ-২, অর্থাৎ, একমাত্র ফসল ঘরে তোলার সময়ই বাজারে বিক্রি করে যে আয় হয়, সে আয় দিয়েই তাদের পরের মৌসুমের শেষ পর্যন্ত চলতে হয়। এরা আবার সবজি বিক্রি না করে লম্বা সময়ের ফসলের পেছনে নজর দেয়। সকাল-সন্ধ্যায় তাদের জীবনটাও পূর্বের অবস্থার কৃষকদের মতোই।
এখানে দু’ধরনের কৃষকদের কথা তুলে ধরা হলো। একদল শুধু দীর্ঘকালীন সময়ের ফসলগুলো নির্দিষ্ট সময়ে বিক্রি করে, আরেকদল প্রতিনিয়ত স্বল্পকালীন টাটকা সবজি বিক্রি করে। তবে, এরা যে আবার দীর্ঘকালীন ফসল ফলায় না, বিষয়টা তেমনও না। অথবা, যারা শুধু নির্দিষ্ট সময়ে ফসল বিক্রি করে, তারা যে আবার একেবারেই সবজি ফলায় না, সেটাও না। কিন্তু, এখন প্রশ্ন হলো, স্বল্পকালীন হোক বা দীর্ঘকালীন, কৃষকরা কি তাদের কষ্ট, পরিশ্রম ও ফসলের ন্যায্যমূল্য পায়?
মুদ্রাস্ফীতির এই সময়ে গত কয়েকবছর ধরেই টেলিভিশন-পত্রিকায় কৃষকদের আন্দোলন বা বিক্ষোভের ঘটনা আমরা শুনে আসছি। ফসল কাটার পর ন্যায্যমূল্য না পেয়ে সড়কে ফসল ফেলে বিক্ষোভ বা অবরোধ করা গত কয়েক বছরের একেবারে সাধারণ একটি বিষয়ে পরিণত হয়েছে।
জমি চাষ থেকে শুরু করে বীজ ক্রয়, বীজ বপণ, পরবর্তী পরিচর্যা, সেচ প্রদান, কয়েকধাপে রাসায়নিক সার দেওয়া, আগাছা নির্মূল, ফসল কাটা ও মাড়াই করা এবং পরিশেষে বাজারজাত করা—দীর্ঘ একটা প্রক্রিয়ার মাধ্যমে একজন কৃষক তার ফসলের মুখ দেখতে পায়। কিন্তু, এই প্রক্রিয়ার প্রতিটা পর্যায়েই এখন যে পরিমাণ অর্থ ব্যয় হয়, একজন কৃষক তার ফসল বিক্রি করে লাভ তো দূরে থাক, ব্যয়িত অর্থই সে এখন তুলতে পারে না।
এই ন্যায্যমূল্যটুকু না পাওয়ার অন্যতম একটি কারণ হলো মধ্যস্বত্বভোগী একটি দল। সরকার কর্তৃক প্রজ্ঞাপন জারি করা হলেও তাদের জন্য কৃষকরা নির্দিষ্ট সে দামের চেয়ে অনেক কম দামে বিক্রি করতে বাধ্য হয়। কেননা, এতো পরিমাণ ফসল হয়তো তাকে এদামেই বিক্রি করতে হবে নতুবা তার ফসলগুলো পঁচে নষ্ট হয়ে যাবে।
এখন, একজন কৃষক যদি ৩-৫ মাস টানা পরিশ্রমের পর তার ব্যয়িত অর্থই তুলতে না পারে, তাহলে সে কীসের উপর ভিত্তি করে কৃষিকাজ চালু রাখবে? এদের মধ্যে যাদের সামর্থ্য রয়েছে, কৃষিকাজ ছেড়ে তারা ইতোমধ্যে শহরমুখী হয়ে শিল্প-কারখানার সাথে সম্পর্কিত কর্মসংস্থানের দিকে ঝুঁকছে। আর যাদের সামর্থ্য নেই, তাদের অবস্থা প্রতিনিয়তই অবনতির দিকে যাচ্ছে। আমাদের সামনে প্রতিবছর দারিদ্র্যের যে হার উপস্থাপন করা হয়, তা যে পুরোটাই সাজানো একটি মিথ্যা, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।
অর্থাৎ, অর্থনৈতিক দিক থেকে গ্রাম-বাংলার প্রতিটি কৃষকই চরম দারিদ্রের মাঝে দিনাতিপাত করে। কোনো দুর্ঘটনায় যদি তাদের আকস্মিকভাবে অর্থের প্রয়োজন হয়ে পড়ে, তখন তাদের একমাত্র সম্বল হয় গ্রামীণ ব্যাংকগুলো। সেখান থেকে নির্দিষ্ট একটি সুদের হারে টাকা তুলে এনে সে খরচ বহন করে। একারণেই গ্রামের এমন কোনো কৃষক নেই, যে এমন ঋণের জালে আবদ্ধ না, এসব সুদভিত্তিক প্রতিষ্ঠানের কাছে জিম্মি না।
শোনা যায়, প্রতিবছরই রাষ্ট্রীয় পর্যায় থেকে এসব দরিদ্র কৃষকদের জন্য ভর্তুকি হিসেবে বড় অঙ্কের অর্থ বরাদ্দ দেওয়া হয়। কিন্তু, তার ১০-২০%-ও যদি তাদের কাছে পৌঁছাতো, তাহলে দৈনন্দিন খাবারের ক্ষেত্রে অন্তত টানাপোড়েনে থাকতে হতো না একটি কৃষক পরিবারের। তাহলে টাকাগুলো যায় কোথায়? উত্তরটা হয়তো সকলেরই জানা, কিন্তু মুখ খোলার সামর্থ্য নেই গ্রাম্য কোনো চেয়ারম্যান বা মেম্বারেরও।
এমনকি, দেশের আর্থিক অবস্থার অবনতির কারণে যখন আইএমএফ-এর নিকট থেকে “আর্থিক সাহায্য”-এর নামে চড়া সুদে ঋণ চাওয়া হয়, আইএমএফ তখন শর্ত দেয় যে, এই “আর্থিক সাহায্য” তখনই দেওয়া হবে, যখন দেশের কৃষি সেক্টরে ভর্তুকির পরিমাণ কমিয়ে দেওয়া হবে।
বিষয়টা অদ্ভুত না? আমরা “আর্থিক সাহায্য”-এর নামে চড়া সুদে ঋণ নিতে গেলে দেশের অভ্যন্তরীণ একটা বিষয়ে কেন সে শর্ত দেবে? তাহলে কি বৈশ্বিকভাবেই কৃষিকে কোণঠাসা করা হচ্ছে? নাকি মানবসভ্যতাকে কুক্ষিগত করার একটা মাধ্যম হিসেবে কৃষিকে ব্যবহার করা হচ্ছে? বিষয়টার তাহলে শুরু ও শেষ কোথায়? মধ্যস্বত্বভোগীদের সাথে কি বৈদেশিক কোনো সংস্থার যোগসূত্র আছে? গ্রামীণ ব্যাংকগুলোর এমন চড়া সুদে ঋণ দিয়ে পুরো একটা সমাজকে জিম্মি করার অর্থ কী তাহলে? এনজিও প্রতিষ্ঠানগুলোর উদ্দেশ্য কী আসলে?
তিন.
এবার তাহলে কৃষিপণ্যের দিকে নজর দেওয়া যাক।
আজ থেকে একযুগ আগেও চাষের জন্য প্রায় ৯০% কৃষক নিজেরাই বীজ সংরক্ষণ করতো। এতে যে ফলন খারাপ হতো, তা-ও নয়। সবসময় প্রায় একই পরিমাণের ফসল পেতো। এজন্য তারা বলে দিতে পারতো অমুক জমিতে এই বীজে এতো পরিমাণ ফলন হবে। কিন্তু, মাত্র একযুগের ব্যবধানে কৃষকের নিজ বাড়িতে সংরক্ষণ করা বীজের ফলন প্রায় অর্ধেকে নেমে এসেছে। ফলে, বাধ্য হয়ে কৃষকদেরকে আজ প্যাকেটজাত বীজ এবং হাইব্রিড বীজের দিকে ঝুঁকতে হচ্ছে।
এর অন্যতম একটি কারণ হলো, জমিতে রাসায়নিক সার ব্যবহার করা। কীটনাশক ব্যবহারের মাত্রা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাওয়ার সাথে সাথে জমির উর্বরতা ক্রমান্বয়ে কমতে থাকে। একপর্যায়ে গিয়ে বাড়িতে সংরক্ষণ করা বীজগুলো রাসায়নিক সার মিশ্রিত মাটির সাথে অভিযোজন করতে পারে না। ফলে, ফলনের পরিমাণ উত্তরোত্তর কমতে থাকে। তখন কৃষক বাধ্য হয় প্যাকেটজাত বীজ এবং হাইব্রিড বীজের দিকে ঝুঁকতে।
তবে, প্যাকেটজাত বীজ বা হাইব্রিড বীজের পাশাপাশি রাসায়নিক সার ব্যবহার করার পরেও কেন তাহলে জমির উর্বরতা কমছে? ফসলের ফলন বেশি হলেও কেন সে ফসলকে খেয়ে পূর্বের মতো শক্তি অর্জন করা সম্ভব হয় না? গ্রাম্য পরিবেশে বেড়ে ওঠা একজন যুবকের কেন এখন শ্বাসপ্রশ্বাসের সমস্যা হচ্ছে? বিষয়গুলো কি তাহলে প্যাকেটজাত বীজ, হাইব্রিড বীজ বা পাশাপাশি রাসায়নিক সারের কোনোভাবে সম্পৃক্ত?
প্রথমেই আসি প্যাকেটজাত বীজ বা হাইব্রিড বীজের বিষয়ে। মূলত, হাইব্রিড বীজ ফসলের উৎপাদন বাড়ালেও উৎপাদনের বিভিন্ন ধাপে উচ্চমাত্রায় কীটনাশক, সেচ ও সার ব্যবহার করার প্রয়োজন পরে। অন্যদিকে, বাড়িতে সংরক্ষণ করা বীজগুলো পরবর্তী বছরে একই পরিমাণল ফসল এবং পণ্য উৎপাদন করে বা তারচেয়েও কম করে, তাই কৃষক প্রতি বছর নতুন বীজ কিনতে বাধ্য হয়। প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার তাড়নায় কৃষক প্রতি বছর হাইব্রিড বীজের পিছনে টাকা খরচ করছে। এভাবেই মূলত ধ্বংসাত্মক এই বৃত্তটির উদ্ভব হয়েছে।
এবার আসি রাসায়নিক সারের বিষয়। মূলত, রাসায়নিক সারের পুরো অংশটাই বিষাক্ত। রাসায়নিক সারের মাধ্যমে বা কীটনাশক ব্যবহার করে ফসলের যে পরিমাণ উপকার করা হচ্ছে, তারচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে মানুষরা। কৃষকরা এসব সার বা কীটনাশক স্প্রে-র মতো ব্যবহার করার সময় তাদের নাক, মুখ ও রোমকূপে প্রবেশ করে তাদের শারীরিক ক্ষতি করছে। পাশাপাশি, এসব ফসল খেয়ে মানুষের মাঝে হৃদরোগ, শ্বাসকষ্ট এবং ক্যান্সারের মতো রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটছে।
কিন্তু, এসব কীটনাশক বা রাসায়নিক সার স্লো-পয়জন বা দীর্ঘস্থায়ী বিষ হওয়ায় আমরা এর প্রভাব তাৎক্ষণিকভাবে বুঝতে পারি না, এর প্রভাবটা মানুষের দৃষ্টিগোচর হয় নির্দিষ্ট একটা বয়সে গিয়ে। তবে, এসব খাবার খেয়ে শরীর দুর্বল লাগা বা শরীরে মেদ জমার বিষয়টা কিন্তু আমরা আবার ঠিকই অনুভব করতে বা বুঝতে পারি।
এরচেয়েও আশ্চর্যজনক বিষয় হলো, যে কোম্পানিগুলো হাইব্রিড জাতের বীজ উৎপাদন করে বাজারজাত করে, তারাই আবার সেসব বীজের কীটনাশকও উৎপাদন করে। এমনকি, এসব কোম্পানিই আবার মানুষের জন্য ঔষধও উৎপাদন করে থাকে। সেসব কোম্পানির মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটা হলো, Cargill-কারগিল, DuPont-ডুপন্ট, Pioneer-পাইওনিয়র, Bayar-বায়ার, Monsanto-মনসান্টো, Syngenta-সিনজেনটা, BASF-বাসফ ও Hayera-হায়েরা।
অতএব, বর্তমান প্রেক্ষাপট বিবেচনা করে এটা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, তারাই বীজের মাঝে অপ্রতিরোধ্য সব কীট এবং মানুষের বিভিন্ন রোগের ডিএনএ প্রবেশ করিয়ে দেয়। ফলশ্রুতিতে, কৃষক বা চাষীরা ঐসব রোগের কীটনাশকই খুঁজে বেরায় এবং পরিশেষে, মানুষের রোগের ক্ষেত্রেও তাদের নিকটই যেতে হয়। অর্থাৎ, সামগ্রিকভাবে সম্পূর্ণ একটা জাতি এসব কোম্পানির কাছে নিঃশর্তভাবে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হচ্ছে।
আবার, আশির দশকে সবুজ বিপ্লব শুরু হলে হাইব্রিড জাতের বীজ উৎপাদন ব্যবহারের প্রতি জোর দেওয়া হয়। এরপর নব্বইয়ের দশকে “জাতীয় বীজ সংরক্ষণ কেন্দ্র”-এর চিন্তাভাবনা শুরু হয়। বিশ্বের সমস্ত দেশ থেকে বীজগুলো নিজেদের আয়ত্তে রাখার জন্যে সাম্রাজ্যবাদী দেশ ও তাদের সংগঠনগুলো নতুন পরিকল্পনা করে। তারা জাতীয় বীজ সংরক্ষণ কেন্দ্রগুলোর থেকে বীজ হাতিয়ে নেয়ার জন্যে আন্তর্জাতিক বীজ সংরক্ষণ কেন্দ্র খোলার পরিকল্পনা গ্রহণ করে এবং তারই ধারাবাহিকতায় রকেফেলার ফাউন্ডেশন, গেটস ফাউন্ডেশনসহ এরকম সাম্রাজ্যবাদী সংগঠনগুলো নরওয়ের সভালবার্ড (Svalbard) দ্বীপে আন্তর্জাতিক বীজ সংরক্ষণ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করার সিদ্ধান্ত নেয়।
এটি সভালবার্ড (Svalbard) দ্বীপে করার কারণ এখানে প্রচুর বরফ থাকে এবং এমনভাবে তৈরি করা হয় যাতে এতে প্রাকৃতিক দুর্যোগ আঘাত না করতে পারে। এই কারণগুলোকে প্রচারণার মাধ্যম হিসেবে নিয়ে তারা বিশ্বের বিভিন্ন দেশকে বুঝাতে সক্ষম হয় যে কেন এরকম একটি আন্তর্জাতিক বীজ সংরক্ষণ কেন্দ্রের দরকার। এভাবে বুঝিয়ে কিংবা ক্ষেত্র বিশেষে চাপ প্রয়োগ করে বিশ্বের অনেক দেশ থেকেই তারা বীজ সংরক্ষণ করে আসছে।
এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য একটা ঘটনা হলো, ২০০৩ সালে আমেরিকার ইরাক আক্রমণের পর তাদের জাতীয় বীজ সংরক্ষণাগার থেকে অনেক বীজের নমুনা হারিয়ে যায়, যা আজও পাওয়া যায়নি! সেগুলো কোথায় গেছে, তার হদিসও কেউ দিতে পারেনি। এমনকি, সিরিয়ার সংকট তৈরি হওয়ার পর স্বয়ং সভালবার্ড থেকেও কিছু সিরিয়ান বীজ হারিয়ে যায়!
কৃষি ও খাদ্যের মাধ্যমে যে আমাদেরকে আমাদের অজান্তেই শোষণ করা হচ্ছে, তার একটা উদাহরণ পাওয়া যায় আমেরিকার সাবেক প্রেসিডেন্ট ও যায়নবাদীদের অন্যতম হোতা হেনরি কিসিঞ্জারের একটি উক্তির মাঝে,
❝যদি আপনি তেল নিয়ন্ত্রণ করেন, তবে আপনি দেশ নিয়ন্ত্রণ করতে পারবেন, যদি আপনি খাদ্য নিয়ন্ত্রণ করেন, তবে আপনি বিশ্ব নিয়ন্ত্রণ করতে পারবেন। আর এই খাদ্যকে নিয়ন্ত্রণ করতে হলে অবশ্যই আপনাকে এর মূল উপাদান বীজকে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে।❞
সে আলোকে এটা বলাই যায় যে, কোনো দেশের উপর অবরোধ আরোপ করতে হলে শুধুমাত্র বীজের উপর অবরোধ করেই তাদের সহজে কাবু করা সম্ভব হবে।
তাহলে আশা করি, একজন পাঠক হিসেবে হেনরি কিসিঞ্জার-এর মন্তব্য, নরওয়ের বিখ্যাত সভালবার্ড বীজ সংরক্ষণাগার আর হাইব্রিড জাতের বীজ উৎপাদন—এগুলোর মধ্যকার সম্পর্ক নির্ণয় করতে পেরেছেন।
অতএব, আইএমএফ-এর ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে কৃষিতে ভর্তুকি কম দেওয়ার শর্ত, গ্রামীণ ব্যাংকগুলোর চড়া সুদে ঋণ প্রদান করে কৃষকশ্রেণিকে জিম্মি করা বা মধ্যস্বত্বভোগীদের একচেটিয়া ব্যবসার পেছনের রহস্যগুলো তাহলে এবার একটু হলেও খোলাসা হয়েছে বলে আশা করি।
চার.
সাধারণত কোনো কিছুর সমালোচনা করলে নিশ্চায়ই কোনো কিছুর সাথে তুলনা করেই সমালোচনা করা হয়। অর্থাৎ, সমালোচনার অবশ্যই একটা ভিত্তি থাকে। বাংলা অঞ্চলে কৃষি ও কৃষকের বর্তমান অবস্থাটা সমালোচনামূলকভাবে সামগ্রিক যে বিষয়টা তুলে ধরা হলো, তারও একটা ঐতিহাসিক ভিত্তি রয়েছে। সেটি হলো, ইসলামী সভ্যতায় বাংলা অঞ্চলে কৃষির ঐতিহাসিক সাফল্যগাঁথা। তাহলে বর্তমানে আমাদের অবস্থা এতোটা শোচনীয় কেন? এর উত্তর জানতে হলে আগে পশ্চিমাদের দর্শন নিয়ে একটু জানা প্রয়োজন।
শোষণ ও সাম্রাজ্যবাদের হোতা এবং জায়নবাদের পৃষ্ঠপোষক পশ্চিমাদের দর্শনই হলো মানুষকে মানুষ মনে না করা। এর প্রমাণ পাওয়া যায় কথায়, আচরণ এবং দর্শনে। যেমন,
- ০১. শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে পাশ্চাত্যের ধারণা হলো, “আমি সাদা, তাই আমি তোমার চেয়ে শ্রেষ্ঠ। আমি ইউরোপীয়, তাই আমি তোমার চেয়ে শ্রেষ্ঠ। আমার জন্ম আমেরিকায়, তাই আমি তোমার চেয়ে শ্রেষ্ঠ।”
- ০২. ইউরোপীয়দের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিশ্বাস হলো, “ইউরোপীয়দের ন্যায় যোগ্যতাসম্পন্ন অন্য কোনো জাতির অস্তিত্ব নেই।”
- ০৩. বর্ণবাদী সাম্রাজ্যবাদের মূল দর্শনই হলো শক্তির মাধ্যমে আধিপত্য বিস্তার। ডারউইনের ‘সার্ভাইভাল অব দ্য ফিটেস্ট’ তত্ত্বও এ শক্তির আধিপত্যের ধারণারই ফলাফল। তারা ব্যতীত বাকীরা ধ্বংস হয়ে যাবে-এটিই তাদের নিয়তি।
- ০৪. আমরা সকলেই জানি, বর্তমান পৃথিবী জায়নবাদীদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। সেই জায়নবাদী ইহুদীদের অন্যতম নাথান রথচাইল্ড একবার বলেছিলেন,
❝সাম্রাজ্য পরিচালনা করার জন্য কে রাজা হলো তা আমার দেখার বিষয় নয়, আমার দেখার বিষয় হলো টাকা বা অর্থ। সত্যিকারের শাসক মূলত সে-ই, যার অর্থ আছে।❞ - ০৫. চার্চিল আমাদের ভারতীয় উপমহাদেশে গণহত্যা চালিয়েছে। আমাদের গম, চাল খাদ্য সঙ্কট দূর করার জন্য যথেষ্ট ছিলো। কিন্তু তারা আমাদের এ সকল খাদ্যদ্রব্য লুট করে নিয়ে যাওয়ার কারণে ৪.৩০ মিলিয়ন বাঙালী খাদ্যাভাবে মৃত্যুবরণ করে। দুর্ভিক্ষের বিষয়ে চার্চিলকে জিজ্ঞেস করা হলে চার্চিল জবাব দেন,
❝তারা যদি এত সন্তান জন্ম না দিতো, তাহলে তো এত মৃত্যুবরণ করতো না!❞
নিজেদেরকে এমন শ্রেষ্ঠ মনে করার কারণেই ভারত উপমহাদেশে এসে তারা শোষণ, লুটপাট ও হত্যাযজ্ঞ চালাতে দ্বিধাবোধ করেনি। নিজেদের এমন দর্শনের কারণেই পরিকল্পিতভাবে ভারতীয় উপমহাদেশকে শাসনের নামে শোষণ ও আয়ের উৎস হিসেবে ব্যবহার করেছে।
ব্রিটিশদের শোষণের ভয়াবহতা এতোই ছিলো যে, সঠিক ইতিহাস ঘাটলে দেখা যাবে, ১৭৭১ সালের দুর্ভিক্ষের পূর্বে বাংলাদেশের রাজস্ব (১৭৬৮ সালে) ছিলো ১ কোটি ৫২ লক্ষ ৪ হাজার ৮ শত ৫৬ টাকা। কিন্তু, এই ভয়াবহ দুর্ভিক্ষে এ’অঞ্চলের এক তৃতীয়াংশ মানুষ মৃত্যুবরণ করার পরও ১৭৭১ সালে রাজস্ব বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ১ কোটি ৫৭ লক্ষ ২৫ হাজার ৫ শত ৭৬ টাকায়। একটু চিন্তা করলেই আমরা এই আগ্রাসনের ভয়াবহতা উপলব্ধি করতে পারব। তাদের শাসনের মাত্র কয়েক বছরের মাথায় জনগণ এ ধরণের দুর্ভিক্ষের কবলে পড়ে।
“বাংলায় বিপ্লব প্রচেষ্টা” নামক গ্রন্থে হেমাচন্দ্র কান্নগো বলেন, এই জমিদাররা প্রতি একরে এতো বেশি খাজনা এবং জুলুমপূর্ণ কর আরোপ করা শুরু করে, যা ছিলো সম্পূর্ণ বে-আইনী। কৃষকদের কাছ থেকে আদায়কৃত খাজনার পরিমাণ, সরকারকে প্রদান করা অর্থের চেয়ে ৫ গুণ বেশি ছিলো। অর্থাৎ সরকারকে দেওয়ার মধ্যে দিয়েই যেধরণের ভয়াবহ দুর্ভিক্ষে ও অর্থনীতির ধস নেমে আসে, জুলুমের শিকার হতে থাকে তার থেকে ৫ গুণ বেশি খাজনা এ’সব জমিদাররা আদায় করতে শুরু করে। এদিকে ব্রিটিশরা ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির মাধ্যমে তাদের ভূমির রাজস্ব আরও বাড়িয়ে দেয়। নির্ধারিত যে রাজস্ব ছিল তার থেকে আরও বৃদ্ধি করে ১ কোটি ৫৭ লক্ষ থেকে ২ কোটি ৬৮ লক্ষ টাকা অর্থাৎ ৩৩ লক্ষ পাউন্ড রাজস্ব আয় বাড়িয়ে দেয়। ফলে নতুন এক ভয়াবহ আগ্রাসনের দ্বার উন্মোচিত হয়।
মেমোরেন্টাম অন দি পার্লামেন্ট সেটেলমেন্টের ৪০ নং পৃষ্ঠায় উল্লেখ আছে, তাদেরই এজেন্ট সেন্সেস কমিশনার স্যার টমাস মন্ড্রোর মতে, ১৮৪২ সালে উপমহাদেশে ভূমিহীন কৃষকের কোনো অস্তিত্ব ছিলো না। কিন্তু ১৮৭২ সালে অর্থাৎ ৩০ বছরের ব্যবধানে আমাদের ভূমিহীন কৃষকের সংখ্যা দাঁড়ায় ৭৫ লক্ষে। এই সংখ্যা ক্রমাগত বৃদ্ধি লাভ করতে করতে ১৯৩১ সালে দেখা যায়, সেন্সেস অনুসারে আমাদের ভারতীয় উপমহাদেশের এবং বাংলা অঞ্চলের কৃষকদের মধ্যে ৭০ ভাগ জনগণই ভূমিহীন কৃষকে পরিণত হয়েছে। বাকী যে ৩০% এর ভূমির মালিকানা ছিলো, খোঁজ করলে দেখা যাবে, তাদের মধ্যে সত্যিকারের মালিকানা ছিলো নিতান্তই হাতে গোনা কয়েকজনেরই। অধিকাংশই ছিলো জমিদার কিংবা ব্রিটিশদের তৈরিকৃত এজেন্ট। এরা মূলত লুণ্ঠনের কাজেই ব্যবহৃত হতো। ১৯২১ সাল থেকে শুরু করে ১৯৩১ সাল পর্যন্ত এই এক দশকে জমিদার এবং খাজনাভোগী শ্রেণির সংখ্যাও বৃদ্ধি পায়। অর্থাৎ তারা জুলুমকে আরও বেশি ত্বরান্বিত করতে, তাদের শোষণের মাত্রা আরও বেশি বাড়িয়ে দিতে তাদের এজেন্টদের সংখ্যা আরও বেশি বৃদ্ধি করতে থারে যা দশ বছরের ব্যবধানে ৬২ গুণ বৃদ্ধি পায়।
এস. কে চ্যাটার্জীর বইয়ের একটি রিপোর্ট অনুযায়ী, ১৮০২ সাল থেকে ১৮৫৪ সাল পর্যন্ত ৫৩ বছরে মোট দুর্ভিক্ষের সংখ্যা ছিল ১৩ এবং এইসব দুর্ভিক্ষের মৃত্যুর সংখ্যা ছিল ৫০ লক্ষেরও অধিক। কিন্তু, ব্রিটিশরা নিজেদের শোষণের ফল সহজপন্থায় নিয়ে যাওয়ার জন্য এবং ৪ কোটি সমপরিমাণ মানুষের প্রায় ৬ মাসের খাদ্য ও সব শিল্পের কাঁচামালের চাহিদা পূরণের জন্য রেলপথের স্থাপত্য নির্মাণ শুরু হওয়ার পর ১৮৬০ থেকে ১৮৭৯ পর্যন্ত এই ২০ বছরে দুর্ভিক্ষের সংখ্যা ১৬ এবং মৃত্যুর সংখ্যা ছিল প্রায় দুই কোটি। উপমহাদেশের কৃষকদের সেচ ব্যবস্থা থেকে শুরু করে জমিজমা, বিভিন্ন সম্পদ, মাঠ, ঘর-বাড়ি নষ্ট করে তার উপর দিয়ে রেলপথ বসায় এবং দেখানো হয় তারা অনেক পরিকল্পিত, উন্নত ও সংরক্ষিত উপায়ে উন্নয়ন করছে। অথচ এই স্থাপনার ক্ষেত্রে তারা মোটেও জনগণ এবং কৃষকদের বাস্তবিক অবস্থার দিকে নজর দেয়নি। তারা নজর দিয়েছিলো তাদের লুণ্ঠনের দিকেই, লুণ্ঠন তরান্বিত হওয়ার পন্থার দিকেই। এক্ষেত্রে একটি বিষয় উল্লেখ করা আবশ্যক, তাদের তৈরিকৃত রিপোর্ট অনুযায়ী যদি অফিসিয়ালি মৃত্যু ও দুর্ভিক্ষের সংখ্যা এটা হয়, তাহলে বুঝাই যাচ্ছে তা নির্দিষ্ট কিছু অঞ্চলের। প্রতিটি প্রত্যন্ত অঞ্চলের গ্রামগুলির অবস্থা তাহলে কি হয়েছিলো? ২০ বছরের ব্যবধানে যদি কোটি কোটি লোক মারা যায়, তাহলে সত্যিকার বাস্তবিক অবস্থা কি হয়েছিলো? উপমহাদেশে যার ফল আমরা আজও ভোগ করছি।
যাইহোক, এভাবেই তারা ভারতের সবেচেয়ে বৃহৎ অর্থনৈতিক শক্তি কৃষিকেই ধ্বংস করে দিয়েছে। তাহলে কৃষিতে বৃটিশ ঔপনিবেশিক শাসনামল এবং তার পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সময়ের তুলনা করলেই বিষয়টা আরো সুস্পষ্ট হয়ে যাবে। একজন কৃষকের দৈনন্দিন জীবন এবং কৃষিপণ্য ও কৃষির সামগ্রিক অবস্থা মাত্রই তুলে ধরা হয়েছে। পাশাপাশি, পশ্চিমাদের মনোভাবটাও আমাদের নিকট সুস্পষ্ট হয়েছে এবং এদেশের কৃষির প্রতি তাদের ‘সুমহান’ কৃতকর্মের বিষয়ও তুলে ধরা হয়েছে। অতএব, তাদের নিয়ে আর বেশি আলোচনা করার প্রয়োজন নেই। সেহেতু, এবার একটু ইসলামী সভ্যতায় বাংলা অঞ্চলে কৃষির ঐতিহাসিক সাফল্যগাঁথা-দিকে নজর দেওয়া যাক।
দিল্লি সালতানাতের সময় যতদিন বাংলা তার অধীনস্থ ছিলো, ততোদিন সালতানাতের সবেচেয়ে বেশি পরিমাণ অর্থের যোগান দেওয়া হতো এই বাংলা থেকে। মুঘল আমলে এই বাংলাই সমগ্র বিশ্বের ২৫-২৯% জিডিপি নিয়ন্ত্রণ করতো। বাংলার এই অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির কারণটা ছিলো কৃষির প্রাচুর্য। বাংলার মাটি ছিলো যেমন উর্বর, এর আবহাওয়াও ছিলো তেমনি উপযোগী।
বাংলায় যে পরিমাণ শস্য উৎপাদন হতো, প্রায় ৫০-৬০টি দেশে সেসব রপ্তানি করা হতো। মুসলিমরাই ছিলো চিনির উদ্ভাবক, কেননা এই অঞ্চলে যে পরিমাণ আখের চাষ হতো, তা আর কোথাও হতো না। এমনকি, আজকে সারা বিশ্বে প্রচলিত মশলাপাতির প্রায় ৭০-৭৫%-ই এই ভারতীয় উপমহাদেশে আবিষ্কৃত। মুঘল আমলের মশলাগুলো আজও সমানভাবে সমাদৃত।
বাদশাহ আলমগীরের সময় বাংলার কৃষি সর্বোচ্চ অবস্থানে পৌঁছে। মীর জুমলা (১৫৯১- ১৬৬৩) এবং শায়েস্তা খাঁর (১৬৬৪-১৬৭৮, ১৬৮০-১৬৮৮) আমলে উৎপাদন ছিল সর্বোচ্চ। নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য ছিল সর্বাধিক সস্তা। টাকায় আট মণ চা পাওয়া যেত। এ’সময় বাংলা অঞ্চল অর্থনৈতিক দিক থেকে সমৃদ্ধির সর্বোচ্চ শিখরে পৌঁছে।
এই বাংলা অঞ্চল নদীমাতৃক হওয়ায় বাংলার নদীর মাছগুলোর জন্য প্রায় ৫০টিরও অধিক অঞ্চল থেকে বাণিজ্য করতে আসতো। যেহেতু এই অঞ্চলের পাশেই রয়েছে সুবিশাল সমুদ্র, আবার সে সময়ের বাণিজ্যের সবচেয়ে বড় মাধ্যম সমুদ্রপথ হওয়ায় এই বাংলা সমগ্র বিশ্বের সাথে বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপন করতে পেরেছিলো। বার্থেমা ও বাবুর্সা ১৬ শতকে এই অঞ্চল ভ্রমণ করে বলেন,
❝এখানকার মানুষেরা প্রতিটি শহরকেই একেকটি বন্দর হিসেবে গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছে।❞
এভাবেই বাংলা অঞ্চল এভাবেই সমগ্র বিশ্বের নিকট পরিচিত হয়ে ওঠে। ব্যবসায়ী থেকে শুরু করে ভ্রমণপিপাসুরা বাংলার প্রতি আগ্রহী হয়ে ওঠে। শুধু যে কৃষিতেই বাংলা অঞ্চল সমৃদ্ধশালী ছিলো, তা নয়। বরং, নান্দনিক সৌন্দর্যের আধার ছিলো এই বাংলা অঞ্চল। সামগ্রিকভাবে কয়েকজনের কয়েকটি বক্তব্য শোনা যাক।
- ০১. ইবনে বতুতা—
❝নদী পথে মিশরের নীল নদের মতো ডানে-বামে ছিলো অসংখ্য চাকা, উদ্যানরাজী এবং গ্রামের পর গ্রাম। আমরা গ্রাম ও উদ্যানরাজীর মধ্য দিয়ে ১৫ দিনের মতো চলেছি। আমাদের মনে হয়েছে আমরা একটি সাজানো উদ্যানের মধ্যে দিয়ে চলেছি।❞ - ০২. একজন চীনা দূত—
❝এর অঞ্চলে ভূমি এতটাই উর্বর এবং এর উৎপাদন এতই বেশি যে, একই জমিতে প্রতি বছর দুই থেকে তিন ধরণের ফসল তারা পায়। কোনো রকম যত্ন না করেও অঞ্চলের ভূমি থেকে কৃষকরা তাদের চাহিদার থেকেও বেশি ফসল উৎপাদন করতে পারে।❞ - ০৩. আবুল ফজল—
❝বাংলার মাটি এতো বেশি উর্বর ছিলো যে, একই জমিতে বছরে তিনটি ফসল উৎপন্ন হতো। যদি এই অঞ্চলের চালের প্রত্যেক প্রকার থেকে একটি করে শস্যকণা সংগ্রহ করা হতো তাহলে একটি কলস ভরে উঠতো।❞
এরপর,
আমরা দ্রব্যমূল্যের ক্রয় ক্ষমতার দিকে তাকালে লক্ষ্য করি, সে সময়ের সবকিছু বিদেশে রপ্তানি হওয়া এবং বৈদেশিক অর্থ উপার্জনের ফলে ও রাষ্ট্রীয় নানাবিধ আখলাকী উদ্যোগের ফলে প্রতিটি পণ্যই অত্যন্ত সস্তা দরে পাওয়া যেতো। বিষয়গুলো নিয়ে ইউরোপীয় লেখকগণ বিকৃতভাবে উল্লেখ করলেও দেখা যায়, দ্রব্যমূল্য ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে ছিলো। যার ফলে সবাই নিজ চাহিদা মতো খাবার ক্রয় করতে পারতেন। এমনকি ক্রয় করার পরেও তাদের কাছে অর্থ উদ্ধৃত থেকে যেতো। এজন্যই ইবনে বতুতা মন্তব্য করেন পৃথিবীর কোথাও তিনি এমন একটি দেশ দেখেননি যেখানে জিনিসপত্র বাংলা অঞ্চলের মতো এতো সস্তায় বিক্রি হয়। তিনি দেখেন যে এ দেশ চালে পরিপূর্ণ ও ভালো এবং পুষ্টিকর খাদ্যদ্রব্যে ভরপুর।
১৬৪০ সালে বাংলাদেশের এ অঞ্চলে ভ্রমণ করে সিবাস্তিয়ান মাররিক বলেন, প্রত্যেক বাজারে বা শহরে খাদ্যদ্রব্য ও নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস ও শিল্পজাত দ্রব্য, সুতির বস্ত্র প্রভৃতির প্রাচুর্য এতো বেশি ও সস্তা ছিল যে মাত্র একটি বাজার থেকে এসব জিনিসপত্র অল্প দামে ক্রয়পূর্বক জাহাজ বোঝাই করে নেওয়া যেতো। যার ফলে ব্যবসায়ীগণ এ অঞ্চলের সাথেই ব্যবসা করতে সর্বদা প্রচেষ্টা চালাতো। এ অঞ্চলের মানুষ ব্যাপক হারে উৎপাদন করে তাদের অর্থনৈতিক স্বাবলম্বিতা অর্জন করতো।
এছাড়াও তিনি মন্তব্য করেন, শহরগুলিতে বিশেষ করে খাদ্যদ্রব্যের ক্ষেত্রে মূল্য এতটাই সাধ্যের মধ্যে ছিলো যে তিনি দিনে কয়েকবার আহার করতে প্রলুব্ধ হতেন। ইবনে বতুতা অনেকগুলো দ্রব্যের বর্ণনা দেন। যেমন–মাত্র ৮ দিরহামে ৮০ রাতল ধান পাওয়া যেতো। ১ রৌপ্য দিনারে ২৫ রাতল চাল পাওয়া যেতো। ১ আনা ৯ পাইয়ে বর্তমান ওজনের ১ মণ চাল পাওয়া যেতো। এভাবে প্রতিটি পণ্যই এ অঞ্চলের মানুষদের কাছে অনেক সস্তা ছিলো। যার ফলে এ’অঞ্চলের মানুষ যতটুকু আয় করতেন ততটুকু দিয়ে তারা তাদের খাদ্য, বস্তু কেনার পরেও তাদের আয়ের একটি বড় অংশ উদ্বৃত্ত থাকতো।
সে আমলে জনসংখ্যার তুলনায় কর্মসংস্থান অনেক বেশি ছিলো। পাশাপাশি মুসলমানদের রাষ্ট্রব্যবস্থা, শিক্ষাব্যবস্থা ও সাংস্কৃতিক বলয়ের কারণে মানুষ অনেক বেশি পরিশ্রমী হয়ে উঠে। নারী-পুরুষ সকলেই তাদের স্ব-স্ব জায়গা থেকে সাধ্যমতো পরিশ্রম করে। যার ফলে শক্তিশালী অর্থনৈতিক অবস্থান, কৃষির ভিত্তি, বস্ত্র বা সব ক্ষেত্রে বিশাল এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধিত হয়। এর মধ্য দিয়ে মুসলমানদের আখলাকী এবং রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে সুনির্দিষ্ট একটি শ্রমনীতি প্রতিষ্ঠা করা হয়। আর শ্রমনীতির দিকে যদি আমরা লক্ষ্য করি তাহলে দেখবো, একজন শ্রমিক যে পরিমাণ পারিশ্রমিক পেতেন তার তিন ভাগের এক ভাগ দিয়ে তার বাৎসরিক অন্ন-বস্ত্রের চাহিদা মিটে যেতো।
যেমন, মুঘল সালতানাতের সময়কালে শ্রমিকদের যে মজুরি নির্ধারিত ছিলো সেটি লক্ষ্য করলে দেখা যায়, দৈনিক মজুরি হিসেবে তৎকালীন সময়ে একজন শ্রমিক দুই দম আয় করতেন। তাহলে তার মাসে আয় হতো ৬০ দম অর্থাৎ বছরে তার আয় হতো আঠারো টাকার সমান। জীবন ধারণের নিমিত্তে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম এতোটাই ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে ছিল যে, ইবনে বতুতা বলেন তার জনৈক বন্ধু আল মাসুদী বাংলা অঞ্চলের একজন নাগরিক যিনি বছরে আয় করেন ১৮ টাকা। কিন্তু তার বছরে খাদ্যদ্রব্য, বস্ত্র ক্রয় করতে ব্যয় হয় ৮ দিরহাম বা ১ টাকা। পারিবারিক অন্যান্য সদস্যের চাহিদা এবং খাদ্য-বস্ত্র সব মিলিয়ে তার আয়ের তিন ভাগের দুইভাগ খরচ হতো। আর এক ভাগ থেকে যেত। কারও কারও ক্ষেত্রে ১ ভাগ ব্যয় হতো আর বাকি দুই ভাগই উদ্বৃত্ত হিসেবে থেকে যেতো। আবার তিনি বলেন, অনেকের সারা বছর ২ বা ৩ টাকার বেশি প্রয়োজন পড়তো না। ফলে ১৫ টাকার মতো উদ্বৃত্ত থেকে যেতো। এসব উদ্বৃত্ত টাকা সেই সময়ের মুসলমানদেরকে ওয়াকফ, দান, সাদাকাহ, যাকাতের দিকে ব্যাপকভাবে ধাবিত করে।
মুসলিমরা তাদের এই বাৎসরিক উদ্বৃত্ত সম্পদের একটি অংশ এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলে প্রেরণ করতো। বিভিন্ন দরিদ্র অঞ্চল, দুর্ভিক্ষকবলিত অঞ্চল, যুদ্ধবিগ্রহ সংঘটিত হয়েছে এমন অঞ্চলে মুসলমানরা তাদের সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিত। রাষ্ট্র, শিক্ষা, চিকিৎসা সব ক্ষেত্রে অনেক বেশি বাজেট দিতে পারতো। যার কারণে বলা হয় ইসলামী সভ্যতার ১২শত বছরের শাসনামল ছিল পুরো পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত একটি ন্যায়ভিত্তিক শাসনামল। গোটা দুনিয়াতে হত দরিদ্র খুঁজে পাওয়া, অনাহারী মানুষ খুঁজে পাওয়া ছিল দুষ্কর। আমাদের উপমহাদেশের মুসলিম সালতানাত তথা ইসলামী সভ্যতা যে এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন তার একটি উদাহরণ হচ্ছে ৭ শত বছরে আমাদের অর্থনৈতিক জিডিপি ছিলো ২৯%। অর্থাৎ যাকাত নেওয়ার লোক খুঁজে পাওয়া দুষ্কর ছিল। ইসলামী সভ্যতার এ অঞ্চলে সেই বিশাল অর্থনীতির বর্তমান অবস্থা কেমন? সে ব্যাপারে আমরা কতটুকুই বা অবগত?
অথচ, বর্তমানে দেখা যায় সম্পূর্ণ ভিন্ন পরিস্থিতি। হাল আমলের গ্রামাঞ্চলের কৃষকরা, নারীরা এবং তাদের সন্তানেরা পাচ্ছে না তাদের সঠিক চিকিৎসা, শিক্ষা এবং সব ধরণের অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। পাশাপাশি গ্রামীণ ক্ষুদ্র শিল্প, কুটির শিল্প আজ ধ্বংসের দিকে ধাবিত হচ্ছে। যার ফলে বেকারত্ব বাড়ছে। শহর থেকে গ্রামমুখী হওয়া লক্ষ লক্ষ মানুষ সেখানে এক ভয়াবহ অবস্থার সৃষ্টি করছে। যতটুকুই বা খাদ্য পাচ্ছে সেটুকুও ভেজাল মিশ্রিত। এগুলো খেয়ে রোগগ্রস্ত হওয়ার পরেও পাচ্ছে না সঠিক চিকিৎসা। চিকিৎসা পেলেও যে ঔষধ আমরা ভক্ষণ করি তা সেই একই চক্রের ফসল।
কথিত যে নয়া ব্যবস্থা তারা প্রতিষ্ঠিত করেছে এ থেকে বেরিয়ে আসার কোনো বিকল্প নেই। নতুন বাংলাদেশ গড়ার কোনো বিকল্প নেই। তাই সঠিক উপলব্ধি, সচেতনতা তৈরি ব্যতীত মুক্তির পথ খোঁজা আকাশকুসুম কল্পনা। শুধু বীজ, খাদ্য ও ওষুধ নয় প্রত্যেকটি সেক্টর-ই আজ পুরোপুরি বিদেশি কোম্পানির হাতে বন্দি। প্রফেসর নাজমুদ্দিন এরবাকানের ভাষায়, “আমরা সবাই যায়নবাদের কারাগারে বন্দী, সেখানে আমরা কতিপয় অবাধ্য কয়েদি। কিন্তু দিন শেষে সবাই কয়েদী।”
মুক্তি জন্য নতুন বিশ্বব্যবস্থার প্রস্তাবনার আলোকে সামনে অগ্রসর হয়ে নতুন বাংলাদেশ তথা হারানো ঐতিহ্যের বিনির্মাণ করতে হবে। আমরা বিশ্বাস করি, পূর্বের সেই সোনালী ঐতিহ্যের আলোকে যদি আমরা কাজ করি তাহলে ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি সম্ভব। কেননা আগের সেই খনিজ সম্পদ, জমি, বনাঞ্চল, কৃষক, মানব সম্পদ, নদী, সমুদ্র এখনও বিদ্যমান।
পাঁচ. অন্তিম রেখা
মূলত এতক্ষণ যে আলোচনা করা হলো, তা ছিলো, ইতিহাসের আলোকে বর্তমান কৃষি ও কৃষকের সরেজমিন পর্যালোচনা। সম্পূর্ণ বিষয়ের পেছনে উৎসাহ ও উদ্দীপনা জাগিয়েছে সময়ের শ্রেষ্ঠ পত্রিকা—জ্ঞানের পুনর্জাগরণ ও নবধারার কাগজ “মিহওয়ার”।
ইতিহাসকে সামনে রেখে ঐতিহাসিক সাফল্যগাঁথা এবং বর্তমান সময়ের কৃষি ও কৃষকের চরম দুরবস্থার মধ্যকার বিষয়ের অসাধারণ পর্যালোচনা তুলে ধরা হয়েছে মিহওয়ার পত্রিকার দ্বিতীয় ও তৃতীয় সংখ্যায়।
পত্রিকাটির দ্বিতীয় সংখ্যায় এসেছে ইসলামী চিন্তা ও গবেষণা ইন্সটিটিউট-এর সম্মানিত প্রেসিডেন্ট তরুণ কৃষিবিদ শ্রদ্ধেয় আশিকুর রহমান সৈকত-এর লেখা “কৃষিব্যবস্থা ও বীজঃ যায়নবাদীদের হাতের মুঠোয় মানবসভ্যতার ভবিষ্যৎ” শীর্ষক প্রবন্ধটি।
এবং তৃতীয় সংখ্যায় এসেছে ইসলামী চিন্তা ও গবেষণা ইন্সটিটিউট-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং ত্রৈমাসিক মিহওয়ার পত্রিকার সম্পাদক তরুণ চিন্তক হাসান আল ফিরদাউস-এর লেখা “বাংলা অঞ্চলে কৃষি ও খাদ্যব্যবস্থা : প্রেক্ষিতে ইসলামী সভ্যতা” শীর্ষক প্রবন্ধটি।
দ্বিতীয় ও তৃতীয় সংখ্যায় লিখিত প্রবন্ধ দু’টি অধ্যয়নের পরেই জানার আগ্রহ এবং বাস্তব অভিজ্ঞতা লাভের জন্যই একেবারে সরেজমিনে যাওয়া এবং কৃষকদের সাথে সময় অতিবাহিত করে তাদের জীবন সম্পর্কে অবহিত হওয়া।
এই আলোচনায় মূলত তত্ত্বের আলোকে বর্তমান সময়ের কৃষি ও কৃষকের চরম দুরবস্থার সত্যতা তুলে ধরার প্রচেষ্টা করা হয়েছে। তত্ত্বের পাশাপাশি তথ্যের জন্য উক্ত প্রবন্ধ দু’টি পড়ে অনুধাবন করার অনুরোধ রইলো।