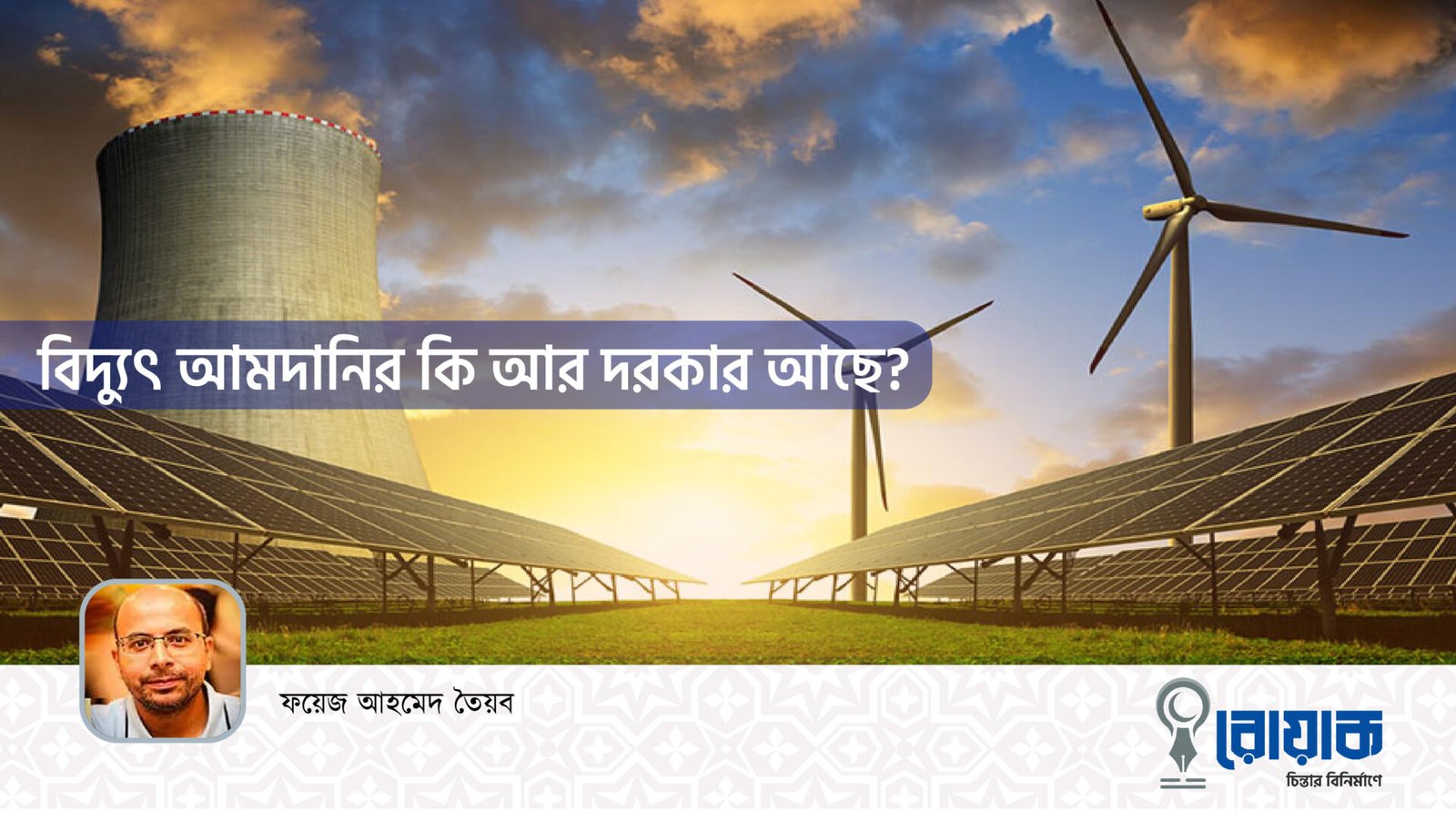কাগজে–কলমে ২১ হাজার ২৩৯ মেগাওয়াট হলেও বাংলাদেশের প্রকৃত বিদ্যুৎ উৎপাদন সক্ষমতা ২০ হাজার ৭৪৮ মেগাওয়াট। তবে সর্বোচ্চ বিদ্যুৎ উৎপাদনের রেকর্ড ১২ হাজার ৮৯৩ মেগাওয়াট (বিপিডিবি, জানুয়ারি-২০২১)। তার মধ্যে নবায়নযোগ্য বিদ্যুৎ ৭৫০ মেগাওয়াট, এটি প্রকৃত উৎপাদন সক্ষমতার মাত্র ৩ দশমিক ৬ শতাংশ। বিদ্যুতের মহাপরিকল্পনা পিএসএমপি ২০১৬ অনুযায়ী ২০২১ সালের মধ্যেই মোট সক্ষমতার অন্তত ১০ শতাংশ নবায়নযোগ্য বিদ্যুৎ থেকে আসার কথা। টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট এসডিজি ৭–এর অন্যতম শর্ত, ব্যবহৃত বিদ্যুতের ১২ শতাংশ নবায়নযোগ্য উৎস থেকে আসতে হবে। বাংলাদেশ এলডিসি উত্তরণের শক্তিশালী প্রার্থী। তাই নিম্নমধ্য আয়ের দেশের মোট ব্যবহৃত বিদ্যুতের ১৭ শতাংশ নবায়নযোগ্য হতে হবে, এই শর্ত তার মানা উচিত। কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে নবায়নযোগ্য বিদ্যুৎ উৎপাদনের স্থানীয় ও বৈশ্বিক উভয় লক্ষ্যমাত্রা থেকেই বেশ পিছিয়ে আছে বাংলাদেশ।
সবুজ বিদ্যুতের রোডম্যাপ
২০৪১ সালের প্লাটিনাম জয়ন্তীতে নবায়নযোগ্য জ্বালানির অনুপাত কী হবে, তা নিয়ে সুস্পষ্ট কোনো মহাপরিকল্পনা নেই। তবে পিএসএমপি ২০১৬ কিছু সম্ভাব্য দিকনির্দেশনা দিয়েছে। স্রেডা ও ইউএনডিপির গবেষণা প্রতিবেদন বলছে, জমি স্বল্পতা সত্ত্বেও সৌর বিদ্যুতায়নের আওতায় ২০৪১ সালের মধ্যে প্রায় ২০ হাজার মেগাওয়াট সবুজ বিদ্যুৎ উৎপাদন সম্ভব। একটি উচ্চ ক্ষমতার সৌর স্থাপনা মডেলে এই সক্ষমতা ৩০ হাজার মেগাওয়াট পর্যন্ত বাড়ানো সম্ভব। ছোট ও মাঝারি আইপিপি সৌরশক্তি কেন্দ্র, ইউটিলিটি সোলার, এপিজেড-এসইপিজেড, শিল্প–ছাদ-অফিস-শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, মিনি সৌর গ্রিড, সেচ, সোলার হোম, সোলার চার্জিং স্টেশন, কাপ্তাই লেক, ডেলটা প্ল্যান, যমুনা-পদ্মা-তিস্তা-মেঘনা রিভার বেসিন রিস্টোরেশান অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট প্রকল্পের ভূমি, হাওর এবং সুবিস্তৃত উপকূলকেন্দ্রিক সমন্বিত সৌর মহাপ্রকল্প নিয়ে এটা করা সম্ভব। অর্থাৎ শুধু মধ্য পর্যায়ের বিনিয়োগ করেই ২০৪১ সালের মধ্যে সবুজ বিদ্যুতের স্থানীয় এবং বৈশ্বিক লক্ষ্যমাত্রা অর্জন সম্ভব।
সম্ভাবনা বনাম বাস্তবতা
বাংলাদেশে সৌরবিদ্যুতের আলাপ উঠলেই জমি স্বল্পতার প্রসঙ্গ ওঠে। ভাসানচর, চরফ্যাশন, ভোলা, বরিশাল-নোয়াখালী-চট্টগ্রাম অঞ্চলের বিচ্ছিন্ন দ্বীপগুলোতে বিকল্প হিসেবে সৌর-বায়ুবিদ্যুতের সমন্বয়ে নবায়নযোগ্য বিদ্যুৎ উৎপাদন মডেল দাঁড় করানো যায়। এই অঞ্চলে সৌর এবং বায়ুশক্তির সম্ভাবনা দেশের অপরাপর অঞ্চলের চেয়ে ভালো। দেশের অন্যত্র বায়ুপ্রবাহজনিত সমস্যা থাকলেও উপকূল ও চরাঞ্চলে গড় বায়ুপ্রবাহ ধীরবায়ুপ্রবাহী টারবাইনের জন্য যথেষ্ট। বায়ুবিদ্যুতের পাইলট প্রকল্পটি যে সফল না তার আদত কারণ কিন্তু স্থাপনার ত্রুটি ও দুর্নীতি। উপকূল ও চরাঞ্চলে বায়ুবিদ্যুৎ নিয়ে দোটানা, তাই অনুচিত।
সৌরবিদ্যুতে জমি স্বল্পতার সমস্যা আছে, এ কথা সত্য, তবে বিকল্প স্থানীয় সমাধানও আছে। এগুলোকে কাজে লাগানোর সর্বোচ্চ চেষ্টা করা দরকার। সৌরশক্তির মজুত সক্ষমতা বাড়াতে স্থানীয়ভাবে মানসম্পন্ন ব্যাটারি উৎপাদন বা আমদানি করতে হবে। উচ্চমান কনভারটার ও ডিসি সামগ্রীও সহজলভ্য করা দরকার। ভবিষ্যতে বৃহৎ পরিসরের বিদ্যুৎ স্টোরেজ নিয়ে ভাবতে হবে। মনে রাখতে হবে সৌর স্টোরেজে লিথিয়াম-আয়ন ব্যাটারিই একমাত্র বিকল্প নয়, আছে ফ্লো-ব্যাটারি, আয়ন-সল্ট-ওয়াটার ব্যাটারি, গ্রাভিটি স্টোরেজ।
জলবিদ্যুতের কতটা সবুজ?
১০০ বছর ধরে জলবিদ্যুৎ নবায়নযোগ্য বিদ্যুতের বৃহত্তম বৈশ্বিক উৎস। তবে আধুনিক গবেষণা বলছে, জলবিদ্যুৎ পুরোপুরি সবুজ নয়। বিস্তৃত অঞ্চলের প্রতিবেশ এতে নষ্ট হয়। বৃহৎ নির্মাণযজ্ঞে কার্বন ডাই–অক্সাইডসহ অপরাপর গ্রিনহাউস গ্যাস উৎপন্ন হয়। গবেষণা সংস্থা এনার্জি মিনিটের মতে, বর্তমান বিশ্বের ২৩ শতাংশ এনথ্রোপোজেনিক মিথেন উৎপাদনের জন্য দায়ী বিভিন্ন জলবিদ্যুৎ প্রকল্প। কার্বন ডাই-অক্সাইডের চেয়েও মিথেন ৩০ গুণ বেশি ক্ষতিকর গ্রিনহাউস গ্যাস। ‘নেপালের জলবিদ্যুৎ খাতের চ্যালেঞ্জ ও সুবিধার মূল্যায়ন’ নামক গবেষণা প্রবন্ধে শর্মা তেজস্বী বলেছেন, হিমালয়ান নদীগুলোর বেশির ভাগ জলবিদ্যুৎকেন্দ্রই অতি মাত্রায় ভাঙন, পলিপতন ও অবক্ষেপে পড়ে, সংকুচিত হয় জলাধারের ক্ষমতা ও জীবনকাল। জলবিদ্যুৎকেন্দ্রের হাত ধরে বন্যার শঙ্কাও আছে। একটি জলবিদ্যুৎ বাঁধের জলাধার ভরাটে কয়েক বছর লেগে যায়, এই সময়ে জলপ্রবাহ সংকুচিত হয়ে ভাটির পরিবেশ ও প্রতিবেশ বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। তদুপরি পলিবাহিত নদীতে বাঁধ ভাটিতে পলিপড়া কমায়, পরিণতিতে জমির উর্বরতা হ্রাস করে, বিঘ্নিত হয় বদ্বীপায়ন প্রক্রিয়া।
জলবিদ্যুৎ আমদানি
বাংলাদেশে নন-নিউক্লিয়ার নবায়নযোগ্য বা সবুজ বিদ্যুতের কথা উঠলেই ভারত থেকে ‘সস্তা ও দূষণহীন’ জলবিদ্যুৎ আমদানির পরামর্শ আসে। বস্তুত ভারতের অরুণাচলে পরিকল্পিত ১৫৪টি জলবিদ্যুৎ বাঁধ বহুপক্ষীয় ভূরাজনৈতিক ঝুঁকি তৈরি করবে। এগুলো চীনকে ব্রহ্মপুত্রের ওপর অতি বৃহৎ জলবিদ্যুৎ প্রকল্প করার বৈধতা দেবে। তিব্বতের বিদ্যুৎ ঘাটতি কমাতে ব্রহ্মপুত্রের পানিসম্পদ ব্যবহার করে চারটি বৃহৎ বাঁধ তৈরির পরিকল্পনা আগে থেকেই চীনের আছে। বাংলাদেশে বহমান যমুনা-ব্রহ্মপুত্রে পানির বড় অংশ আসে অরুণাচল ও আসামের বিপুল মৌসুমি বৃষ্টি থেকে। তাই ভারতের বাঁধ শুধু জলবিদ্যুৎ প্রকল্পেই সীমাবদ্ধ থাকবে না, বরং জলাধার ভরাট ও আন্তসংযোগের মতো বিষয়ও এতে যুক্ত হবে। জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের পাশাপাশি আন্তনদী সংযোগ প্রকল্পের বৃহৎ লক্ষ্য হচ্ছে উদ্বৃত্ত অঞ্চল থেকে ঘাটতি অঞ্চলের দিকে খাবার ও সেচের পানি প্রবাহিত করা।
‘ব্রহ্মপুত্র অববাহিকার পানি সম্পদ প্রতিযোগিতা: চীন, ভারত ও বাংলাদেশ’ নামক গবেষণা প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ভারতের পানি প্রত্যাহারে বাংলাদেশ যে হুমকির মুখে পড়েছে, তিব্বতে চীনা বাঁধ নির্মাণ ভারতকে সেই উদ্বেগের মধ্যেই ফেলে দিয়েছে। বিভিন্ন চীনা বিশ্লেষণে বলা হয়েছে, ভারতের জল প্রত্যাহার ভাটির প্রতিবেশীর ওপর মারাত্মক অর্থনৈতিক এবং পরিবেশগত প্রভাব ফেলতে পারে। সিএনএকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে একজন চীনা বিশেষজ্ঞ বলেছেন, ভারতীয় প্রত্যাহার পরিকল্পনাগুলো বাংলাদেশের স্বার্থের ক্ষতি করতে পারে, তাই কিছু বলার অধিকার বাংলাদেশের রয়েছে। মোদ্দা কথা হচ্ছে, উজানে চীনের উন্নয়ন উদ্যোগের সমালোচনার ক্ষেত্রে দ্বৈত-নীতি প্রয়োগ করছে ভারত।
ব্রহ্মপুত্র অববাহিকায় ভারতের সীমানা মার্জিনাল (জনসংখ্যার ৩ ও ভূমির ৬ শতাংশ)। অপেক্ষাকৃত কম জনবহুল এই অঞ্চল চীনা ভূমির ৩ শতাংশ। অন্যদিকে ব্রহ্মপুত্র বেসিন বাংলাদেশের ভূমির ২৭ শতাংশ। এখানে বাস করে জনসংখ্যার ৭০ শতাংশ। বর্তমানে ব্রহ্মপুত্র অববাহিকায় বাংলাদেশের সেচ চাহিদার অন্তত ২৫ শতাংশ পানি ঘাটতি রয়েছে, প্রায় ৫ কিলোমিটার প্রস্থের যমুনা চলমান শুষ্ক মৌসুমে ৭০০ মিটারে নেমে এসেছে। সব মিলে চীন ও ভারতের জলবিদ্যুৎ প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে ব্রহ্মপুত্র-যমুনায় চরম পানি সংকট দেখা দেবে। এটি বাংলাদেশের গ্রীষ্মকালীন স্বাদু পানির প্রধান উৎস। এ অবস্থায় অরুণাচলকেন্দ্রিক জলবিদ্যুৎ আমদানিতে বাংলাদেশের অংশ নেওয়াটা মোটেই সমীচীন হবে না।
যেহেতু ভারতে কয়লা উৎপাদিত বিদ্যুতের উদ্বৃত্ত রয়েছে এবং বৈশ্বিক নবায়নযোগ্য বিদ্যুতের লক্ষ্য অর্জনে ভারত সৌর ও বায়ুবিদ্যুতে ব্যাপক বিনিয়োগ করছে, তাই অরুণাচলের অতি খরুচে জলবিদ্যুৎ আদতে ভারতের প্রয়োজন নেই, দরকার আসলে পানি প্রত্যাহার। বাংলাদেশ যদি বিদ্যুৎ করিডরের অনুমতি দেয়, তবে ব্রহ্মপুত্র (যমুনা) নদ ও এর শাখা নদের ওপর পরিকল্পিত ১৫৪ জলবিদ্যুৎ প্রকল্প অর্থনৈতিকভাবে কার্যকর হয়ে আন্তনদী সংযোগ প্রকল্পকে এগিয়ে নেবে। আশঙ্কা হয়, এই প্রক্রিয়া ভাটির ব্রহ্মপুত্র (যমুনা) নদীটিকে ধীরে ধীরে হত্যা করবে। তদুপরি এই বাঁধগুলোর অনেকগুলো জলাধার হিসেবে কাজ করবে এবং ভবিষ্যতে চ্যানেল দিয়ে পরস্পর সংযুক্ত করা হবে। উদাহরণস্বরূপ, মানস-শঙ্কোশ-তিস্তা-গঙ্গা সংযোগ প্রকল্পের মাধ্যমে ইতিমধ্যেই যমুনা নদীর শাখা নদী মানস এবং শঙ্কোশের পানি সরিয়ে নেওয়ার মহাপরিকল্পনা করা হয়েছে (ইন্ডিয়া ওয়াটার পোর্টাল ডট ওআরজি/ন্যাশনাল-রিভার-লিংকিং-প্রজেক্ট)। মোটকথা, নবায়নযোগ্য বিদ্যুতের নামে বাংলাদেশের কোনোভাবেই জলবিদ্যুৎ আমদানির ফাঁদে পড়া যাবে না।
সর্বোচ্চ কতটুকু বিদ্যুৎ আমদানি করা যাবে?
‘হাইড্রো-ইলেকট্রিক পাওয়ার ইভাকুয়েশান মাস্টারপ্ল্যান অব অরুণাচল’ রিপোর্ট অনুসারে ছয়টি সাত হাজার ও একটি ছয় হাজার মেগাওয়াট জলবিদ্যুৎকেন্দ্র থেকে ৮০০ কেভি হাই ভোল্টেজ সঞ্চালন লাইনের জন্য বাংলাদেশের ভূমি দরকার। এ থেকেই বোঝা যায় যে বাংলাদেশে জলবিদ্যুৎ রপ্তানির প্রস্তাবের মূল আসলে বিদ্যুৎ করিডর। যেখানে বাংলাদেশে সড়ক প্রশস্ত করার কিংবা সৌরবিদ্যুতের জমিস্বল্পতা বহুল আলোচিত, সেখানে সাতটি হাই ভোল্টেজ সঞ্চালন লাইনের ভূমি বরাদ্দ পুরোপুরি অবাস্তব। ইতিমধ্যেই বিপিডিপি-পিজিসিবি-পল্লী বিদ্যুতের সঞ্চালন লাইনের জন্য অধিগ্রহণ করা জমি নিয়ে শত শত মামলা রয়েছে।
গ্রীষ্মকালীন চাহিদা আমলে নিয়েই বর্তমানে বাংলাদেশের স্থাপিত বিদ্যুৎ সক্ষমতার প্রায় ৫৯ শতাংশ অলস। বিপিডিবি হিসাবে ২০৩০ সালে অন্তত ১৫ হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন সক্ষমতা অলস থাকবে। ফলে ১৮তম জেএসসি মিটিংয়ে ২০৩০ পর্যন্ত বিদ্যুৎ আমদানির প্রয়োজন নেই বলেই সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। পিএসএমপি ২০১৬ তে দেশের জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিত করে মোট ব্যবহৃত বিদ্যুতের সর্বোচ্চ ১৫ শতাংশ আমদানির নির্দেশনা দেওয়া আছে। বর্তমানে ভারত থেকে ১১৬০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ আমদানি করছে বাংলাদেশ, আরও ১৬০০ মেগাওয়াট আমদানির নতুন চুক্তি হয়েছে। আমদানি বিদ্যুৎ রেকর্ড উৎপাদনের ২১ শতাংশ ছাড়িয়ে যাচ্ছে। কৌশলগত জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিত রাখতে তাই নতুন আমদানির সুযোগ নেই।
তাহলে করনীয় কী? যেহেতু ভারত ও চীন সৌর বিদ্যুতায়নে খুবই আশাব্যঞ্জক অবস্থান তৈরি করেছে, তাই দেশ দুটোর সঙ্গে সৌর বিদ্যুতায়নের দ্বিপক্ষীয়/বহুপক্ষীয় বিনিয়োগ মডেল তৈরি করা যেতে পারে। সবদিক বিবেচনায় তাই সৌরবিদ্যুতই বাংলাদেশের টেকসই জ্বালানির ভবিষ্যৎ। সৌরবিদ্যুৎ বিক্রির অবকাঠামো তৈরি করা গেলে ‘নগর সৌরবাড়ি বিপ্লব’ হবে। অন্যদিকে সর্বোচ্চ ঘনবসতির দেশে বায়ুবিদ্যুতের প্রসার চাই। সীমিত আকারে জিও-থার্মাল, উপকূলীয় বায়ুবিদ্যুৎ, সমুদ্রশক্তি নিয়েও কাজ করা উচিত। পাশাপাশি কার্বন ট্যাক্স চালু করে বিকল্প স্থানীয় সবুজ বিদ্যুৎ উৎপাদনে করপোরেট প্রণোদনাও সময়ের চাহিদা।