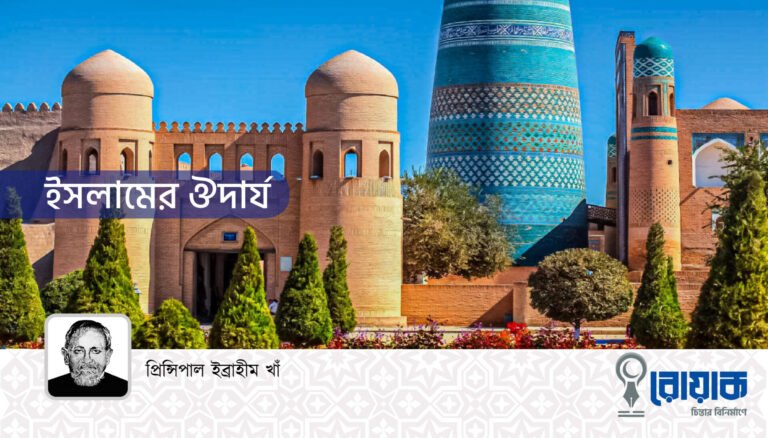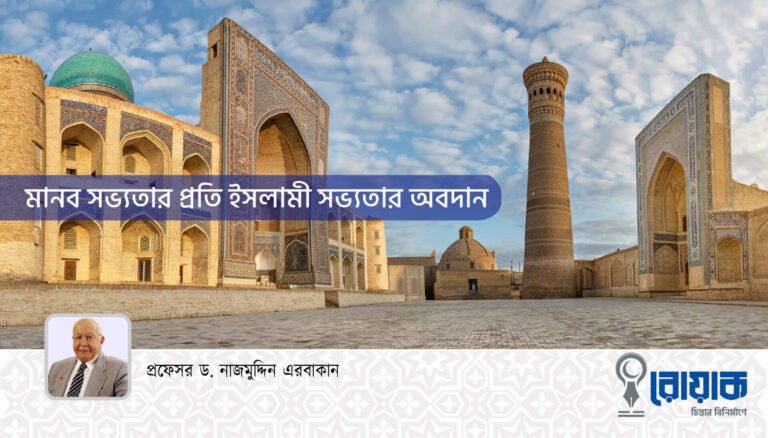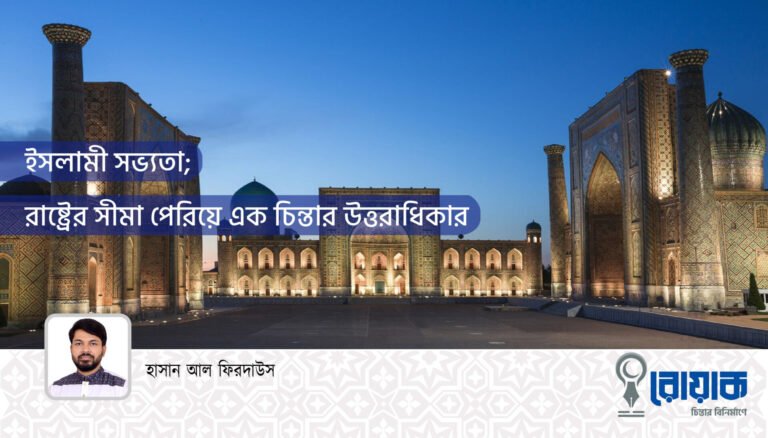“কোন দলটি উত্তম, যারা আল্লাহর ভয় ও সন্তুষ্টির উপর তাদের ভবনের ভিত্তি স্থাপন করেছিলো তারা, নাকি তারা-যারা একটি পতনোন্মুখ পাহাড়ের কিনারায় তা স্থাপন করেছিলো, যা তাদের সাথে নিয়ে জাহান্নামের আগুনে পড়ে গিয়েছিল?”
ইসলামী আইন অথবা সুপ্রতিষ্ঠিত ঐতিহাসিক ইসলামী অনুশীলনের উপর ভিত্তি করে কিছু অনন্য ইসলামী প্রতিষ্ঠান রয়েছে, যেগুলো একটি ইসলামী সমাজ বা রাষ্ট্রের মধ্যে অর্থনৈতিক কাঠামোর উপর শক্তিশালী প্রভাব ফেলে। ইতিহাসের নানা ঘাত-প্রতিঘাতে এ প্রতিষ্ঠানগুলোর অনেকগুলোই বিলুপ্ত বা প্রান্তিক হয়ে পড়ে। আধুনিককালের সকল সমাজকে একই পথ অনুসরণের ধারণার কারণে ইসলামী ঐতিহ্যগুলো শুধুমাত্র ঐতিহাসিক মূল্য রাখে, বর্তমানের জন্য সেগুলো ভিত্তিহীন প্রমাণিত হয়। ইসলামী বিশ্বে ইসলামী প্রতিষ্ঠানগুলোর আত্মশক্তি পুনরুদ্ধার এবং তাদের পুনরুজ্জীবিত করার জন্য সক্রিয় প্রচেষ্টা চলছে। উপরে উদ্ধৃত কোরআনের আয়াত থেকে স্পষ্ট যে, প্রতিষ্ঠানগুলো প্রতিষ্ঠার পিছনের উদ্দেশ্যটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠানগুলোকে সমসাময়িক চাহিদার সাথে খাপ খাওয়ানো বা আধুনিক চাহিদা পূরণের পাশাপাশি ইসলামী শরীয়তের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নতুন প্রতিষ্ঠান তৈরি করার চ্যালেঞ্জও রয়েছে। চ্যালেঞ্জটি হলো, ইসলামী আদর্শ ও লক্ষ্যের মধ্যে টানাপোড়েন এবং ঔপনিবেশিক/আধুনিক/ইসলামী কাঠামোর মধ্যে বিদ্যমান অসামঞ্জস্য যা সারা বিশ্বে ইসলামী আন্দোলনকে উৎসাহিত করে তোলে। সামনে আমি ইসলামী আর্থিক প্রতিষ্ঠান, বীমা, ওয়াকফ (ট্রাস্ট বা এনডাউমেন্ট), হিসবাহ বা বাজার নিয়ন্ত্রণ এবং পরিবেশ সুরক্ষাকে পৃথক পৃথক বিভাগে আলোচনা করবো।
ইসলামী আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ
ইসলামে সুদের উপর স্পষ্ট নিষেধাজ্ঞা এবং আধুনিক পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে সুদ-ভিত্তিক লেনদেনের কেন্দ্রিকতার পরিপ্রেক্ষিতে একটি ইসলামী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বাস্তবায়নে প্রথম বাস্তব চ্যালেঞ্জ হলো সুদের বিকল্পের বিকাশ। এই বিষয়ে সাহিত্যের একটি বিশাল ভাণ্ডার আছে; সিদ্দিকীর (২০০৪) একটি সাম্প্রতিক জরিপে যা উঠে এসেছে। আমি এ সমস্যা সমাধানের তিনটি ভিত্তি নিয়ে নিচে আলোচনা করছি,
- প্রথম ভিত্তি,
সমস্যা থেকে বেরিয়ে আসার সহজ উপায় হলো এই যুক্তি দেওয়া যে, আধুনিক ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থায় যে সুদ প্রচলিত তা কোরআনে নিষিদ্ধ সুদের মতো নয়। এই পথটি খ্রিস্টান ও ইহুদিদের দ্বারা বেছে নেওয়া পথের সমতুল্য, একাধিক প্রচেষ্টা সত্তে¡ও সংখ্যাগরিষ্ঠ আলেমগণ এটিকে অস্বীকার করেছেন। মুসলমানরা বিশ্বাস করে যে, কোরআন হলো আল্লাহর নাযিলকৃত বাণী এবং হাদীসে ধারণ করা ঐতিহ্যগুলো মৌলিকভাবে সঠিক। জোন্স (১৯৮৯) দেখান যে সুদের উপর বিধিনিষেধের পুনঃব্যাখ্যা আক্ষরিক না হয়ে রূপক হিসেবে খ্রিস্টান বিশ্বের স্বার্থকে বৈধ করার একটি মৌলিক পদক্ষেপ ছিলো।
- দ্বিতীয় ভিত্তি,
দ্বিতীয় ভিত্তি হলো, বিদ্যমান আধুনিক প্রতিষ্ঠানের সমতুল্য এমন প্রতিষ্ঠান খুঁজে বের করা, যা ইসলামী শরীয়ত মোতাবেক পরিচালিত হয়। এটি সবচেয়ে জনপ্রিয় মাধ্যম হওয়ায় আরও বিস্তারিত আলোচনার দাবী রাখে। এম.এন. আইয়ুব (২০০২) এবং জাহের ও হাসান (২০০১) কীভাবে সুদ ছাড়াই কাজ করতে পারে এমন ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করা যায়, সে বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেন। এবিষয়ে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ রেফারেন্স বই হলো IIBI (১৯৯২) কর্তৃক প্রকাশিত The Encyclopedia of Islamic Banking and Insurance। ইকবাল এবং খান (২০০৪) ‘ফিনান্সিয়াল ইঞ্জিনিয়ারিং’ এর মাধ্যমে এমন আর্থিক প্রতিষ্ঠানের নকশা তুলে ধরেন, যা পশ্চিমা প্রতিষ্ঠানের কার্যাবলি পূরণ করে এবং শরীয়ত মোতাবেক পরিচালিত হবে। সুদ এবং সুদের সাথে সম্পর্কিত নৈতিক বিপর্যয় রোধে খ্রীস্টানদের গৃহীত পন্থার সাথে এ নকশার বিস্তর ফারাক রয়েছে; জোনস(১৯৮৯)।
- তৃতীয় ভিত্তি,
তৃতীয় একদল লেখক বিশ্বাস করেন যে, ইসলামী প্রতিষ্ঠানগুলো বিদ্যমান পুঁজিবাদী কাঠামো থেকে আমূল আলাদা এবং এই ধরনের কাঠামো প্রতিষ্ঠার জন্য একটি বিপ্লবের প্রয়োজন; উদাহরণস্বরূপ দেখুন, আনসারি (২০০০), তাসিন (২০০১) এবং ভাদিল্লো। প্রকৃতপক্ষে, অধিকাংশ মুসলিম চিন্তাবিদগণ এবিষয়ে একমত যে, মুসলিম প্রতিষ্ঠানগুলো একইধরণের অমুসলিম প্রতিষ্ঠানগুলো থেকে আমূল আলাদা, কিন্তু রূপান্তরের জন্য উপযুক্ত কৌশল নিয়ে তাদের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। দ্বিতীয় পথটি (আগের অনুচ্ছেদে আলোচনা করা হয়েছে) হলো বিবর্তনীয় পরিবর্তন এবং বিদ্যমান পশ্চিমা আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও অনুশীলনে পরিবর্তন সাধনের একটি উপায়, যাতে ইসলামী শরীয়তের গুরুতর লঙ্ঘন থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যায় এবং একটি ইসলামী ব্যবস্থার মতো অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে তোলার সূচনা হয়। হাফিজ এবং আল-হাসান (২০০৬) এর মতো বিপ্লবী পদ্ধতির সমর্থকরা অবশ্য বিশ্বাস করেন যে, এই ধরণের পদ্ধতিগুলো বাস্তবে কার্যকরী নয় এবং আদর্শ পদ্ধতির সাথে আপোষ করার ফলে ইসলামের বিপ্লবী চেতনা দুর্বল হয়ে যাবে।
তৃতীয় পদ্ধতির প্রাথমিক ধারণা এবং ইসলামী বীমার ক্ষেত্রে এর প্রয়োগ গাজী এবং অন্যদের গবেষণাপত্রের (১৯৯২) তৃতীয় অধ্যায়ের ভূমিকায় সবচেয়ে স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। তিনি জোর দিয়ে বলেন, পুঁজিবাদী প্রতিষ্ঠানের প্রতিলিপি বা পরিবর্তন করার পরিবর্তে একটি প্রতিষ্ঠান কোন উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করবে সে দৃষ্টিকোণ থেকে চিন্তা করা উচিত। যদি এই উদ্দেশ্য ইসলামের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়, তাহলে তা অর্জনের জন্য ইসলামী বিধানের সাথে সামঞ্জস্য রেখে একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে হবে। মিরাখোর (২০০৭) ঐতিহাসিক প্রমাণ সরবরাহ করেন, যা পরামর্শ দেয় যে, ঐতিহ্যবাহী ইসলামী প্রতিষ্ঠানগুলোর উপযুক্ত পরিবর্তন একই ধরণের পশ্চিমা প্রতিষ্ঠানগুলোর চেয়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন উপায়ে বেশ দক্ষতার সাথে কাঙ্খিত উদ্দেশ্য সম্পাদন করতে পারে।
আধুনিক পুঁজিবাদী আর্থিক ব্যবস্থাগুলো শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে বিকশিত হয়েছে এবং আজ ব্যাক্তিগত ও সরকারী উভয়ক্ষেত্রের প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে পারস্পরিক সহায়তাকারী একটি ব্যবস্থা তৈরি করেছে। যেমনটি অনেক লেখক উল্লেখ করেছেন যে, মুসলিম সংস্কারকগণ একটি বড় অসুবিধার সম্মুখীন হন, কেননা আর্থিক ব্যবস্থা হলো একটি সমন্বিত ও সুসংহত কাঠামো, এবং একটি ইসলামী ব্যবস্থার জন্য টুকরো টুকরো পরিবর্তন রচনা, পরিচালনা ও বাস্তবায়ন করা বেশ কঠিন। ট্রাস্ট ও জনসাধারণের স্বার্থের উপর ভিত্তি করে সুদমুক্ত একটি ইসলামী ব্যবস্থা দ্বারা বিদ্যমান ব্যবস্থার প্রতিস্থাপন একটি কঠিন কাজ, এর জন্য একই সাথে বিভিন্ন ফ্রন্টে পরিবর্তন এবং হস্তক্ষেপ প্রয়োজন।
কেন্দ্রীয় ব্যাংক, বাণিজ্যিক ব্যাংক, অর্থ উৎপাদন ও ব্যবস্থাপনা, স্টক এক্সচেঞ্জ, সরকারী অর্থ ও ঋণ পরিচালনা, বন্ধক, সুদভিত্তিক উপকরণ ছাড়াই স্থিতিশীল আয়ের ধারা সৃষ্টি এবং অন্যান্য ভোক্তা ঋণের জন্য প্রস্তাবনা নিয়ে প্রচুর পরিমাণে লেখালেখি (এবং অনেক বিতর্ক) রয়েছে। বিদ্যমান পুঁজিবাদী উপকরণের বিকল্প প্রস্তাব করা হয়েছে এবং বাস্তবায়ন করা হয়েছে। সবচেয়ে সাম্প্রতিক উদাহরণ হলো সুকুক (বন্ডের একটি ইজারা এবং বাই-ব্যাক বিকল্প), যা একটি তাত্তি¡ক প্রস্তাব থেকে খুব অল্প সময়ের মধ্যে ইসলামী অর্থের বৃহত্তম উৎসগুলোর একটিতে পরিণত হয়েছে। প্রাসঙ্গিক সাহিত্য জরিপ করার পরিবর্তে আমরা উপরে উল্লিখিত তৃতীয় ভিত্তি অনুসরণ করি এবং আর্থিক সমস্যার ইসলামী সমাধানের মূলনীতিগুলো এবং বর্তমান পুঁজিবাদী সমস্যাগুলোর থেকে কীভাবে সেগুলো আলাদাÑতা নিয়ে আলোচনা করি। প্রথমত, একটি আর্থিক ব্যবস্থার অন্তর্নিহিত ভিত্তি নিয়ে আলোচনা, দ্বিতীয়ত জনগণের আমানতের নিরাপত্তা প্রদানের উপায় এবং তৃতীয়ত কীভাবে সেই আমানতগুলো ব্যবহার করা যেতে পারে তা নিয়ে আলোচনার চেষ্টা করেছি।
আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ভিত্তি
একটি ইসলামী অর্থনীতিতে আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো কীভাবে গঠন করা হবে, তা দেখার জন্য আমাদের অবশ্যই এই ধারণাটির উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে হবে যে, চ‚ড়ান্ত অর্থে অর্থ হলো একটি মাধ্যম বা উপায়, যা একটি ইসলামী অর্থনীতির কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে। এটি পুঁজির অন্তহীন সঞ্চয় ধারণার বিপরীত, যা পুঁজিবাদের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে এবং যার মধ্যে অর্থে উপার্জনের প্রাথমিক উদ্দেশ্য হলো, আরও অর্থ উপার্জন করা। ইসলামের দাবি হলো, মানুষের জীবন, তার সম্পদ ও সকল প্রচেষ্টা আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য হওয়া উচিত। কোরআনে আল্লাহর সন্তুষ্টি ও পরকালের সাফল্যের জন্য অর্থ ব্যয় করার বিষয়াদি নিয়ে অসংখ্য উপদেশ রয়েছে (কোরআন ২৮:৭৭) এবং মূল্যবান সামাজিক প্রকল্পের জন্য অর্থ ব্যয় করার উপর জোর দেওয়া হয়েছে। সহযোগিতা ও আস্থার উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত একটি সমাজে ব্যক্তিরা ন্যূনতম সঞ্চয় ও ব্যক্তিগত সম্পদের উপর নির্ভর করতে পারে, কেননা তারা তাদের বিপদের সময় অন্যদের সহায়তা লাভ করতে পারে। অনেক ইসলামী বিধান এই ধরনের সহযোগিতার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে; উদাহরণস্বরূপ, অপরিচিত ব্যক্তিরা আতিথেয়তা লাভের অধিকারী। একটি সাম্প্রতিক উদাহরণ হলো, ম্যালকম এক্স (১৯৬৫,পৃ. ২১৩) তার ভ্রমণ অভিজ্ঞতায় লিখেছেন যে, “আমেরিকাতে আমার অভিজ্ঞতা আমাকে এই বিশ্বাসের দিকে পরিচালিত করেছে যে শ্বেতাঙ্গ এবং অ-শ্বেতাঙ্গের মধ্যে কখনও একতা এবং ভ্রাতৃত্বের চেতনার অস্তিত্ব থাকতে পারে না…।”
সহযোগিতা ও বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করে একটি আর্থিক ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠা করার ধারণার উপর সাধারণ আপত্তি হলো, এটি শুধুমাত্র ছোটো কোনো সম্প্রদায়ের মধ্যেই সম্ভব, যেখানে ব্যক্তিগত সম্পর্কগুলো সহজেই টিকিয়ে রাখা যায়। ভৌগলিকভাবে ব্যাপকভাবে লেনদেন ছড়িয়ে থাকা বৃহৎ জনসংখ্যার মধ্যে এটা নিশ্চিত করা হয় যে, শুধুমাত্র আধুনিক বেনামী এবং চুক্তিভিত্তিক প্রতিষ্ঠানগুলো কাজ করতে পারে। যাইহোক, এই মতের বিপরীতে যথেষ্ট দলিল রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, লোপেজ (১৯৭৬) দেখান যে ‘বাণিজ্যিক বিপ্লব’ এর (৯৫০-১৩৫০ খ্রিস্টাব্দ) যুগে তৎকালীন পরিচিত বিশ্ব জুড়ে অবাধে শরীয়ত সমর্থিত ‘আর্থিক ঝুঁকি ভাগাভাগি’ পদ্ধতি দ্বারা সমর্থিত বাণিজ্য সচল ছিলো, যার বিকাশ হয়েছিলো মুসলিম দেশগুলোতে। মিরাখোর (২০০৭) উল্লেখ করেছেন যে, সুদভিত্তিক চুক্তির চেয়ে এই পদ্ধতিগুলোর জন্য বেশি আস্থার প্রয়োজন এবং পরামর্শ দেন যে, ক্রুসেড, মোঙ্গোল আক্রমণ ও বিউবোনিক প্লেগ দ্বারা বাণিজ্য ব্যবস্থায় যে আঘাত আসে, তা মানুষের বিশ্বাসকে নষ্ট করে দেয় এবং পরবর্তীতে ব্যবসার প্রভাবশালী পন্থা হিসেবে সুদভিত্তিক লেনদেন উদ্ভবের দিকে পরিচালিত করে। আমাদের উদ্দেশ্যের জন্য, আমরা লক্ষ্য করি যে ইতিহাস আমানত ও পারস্পরিক সহযোগিতার ইসলামী প্রক্রিয়ার উপর ভিত্তি করে একটি বিশ্ব অর্থনীতির বিকাশের সম্ভাবনাকে প্রমাণ করে, যদিও সমসাময়িক বিশ্ব অর্থনীতিতে এগুলো পরিকল্পনা এবং প্রয়োগের ক্ষেত্রে অনেক অসুবিধা সৃষ্টি করে।
সঞ্চয়
উপরে আলোচিত কিছু উদ্দেশ্য পূরণের জন্য আমাদের ঐতিহাসিক প্রতিষ্ঠান আমানত-কে পুনরুজ্জীবিত ও আধুনিকীকরণ করতে হবে। আগেকার যুগে মানুষ বিশ্বস্ত লোকদের কাছে নিজেদের সম্পদ আমানত রাখতো। আমাদের ‘দারুল আমানত’ এর মতো একটি প্রতিষ্ঠান দরকার, যা নিরাপদে আমানত রাখার কাজটি সম্পন্ন করবে। এটি আধুনিক ব্যাংকগুলোর অন্যতম প্রধান কাজ, যা অবশ্য মুনাফাভিত্তিক। আমাদের দার আল-আমানাহ সম্পূর্ণ ভিন্ন ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হবে। এর একটি প্রাথমিক কাজ হবে আমানতকারীদের আমানতের মূল্য সংরক্ষণ করা। আধুনিক সময়ে এর জন্য নতুন কিছু উদ্ভাবন প্রয়োজন, যেহেতু কাগজের টাকা আগের সময়ের সোনার সমতুল্য নয়। এমন হতে পারে যে, আমানতকারীকে একটি সীমাবদ্ধ সম্ভাবনার অনুমতি দেওয়া হবে, যার মাধ্যমে আমানতের মূল্য একটি সম্মত সূচক অনুসারে সংরক্ষণ করা যেতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, আমানতগুলো স্থিতিশীলতার জন্য অপ্টিমাইজ করা মুদ্রার একটি বান্ডিলে সংরক্ষণ করা যেতে পারে, বা ভোগ্যপণ্যের স্থানীয় সূচীযুক্ত ঝুড়ি আকারে, বা আরও নির্দিষ্টভাবে ভবিষ্যতের বিশেষ প্রয়োজন, যেমন শিশুদের শিক্ষার ব্যয়ভারের জন্য চুক্তি করা যেতে পারে। কিছু মুসলমানের দ্বারা ব্যাংক-সুদের পক্ষে দেওয়া মূল যুক্তিটি হলো আমানতের প্রকৃত মূল্য হ্রাস করার জন্য মুদ্রাস্ফীতির প্রবণতা। প্রস্তাবিত ধরণের একটি প্রতিষ্ঠান সুদের আশ্রয় না নিয়ে এই সমস্যাটি কাটিয়ে উঠতে পারে।
সামাজিকভাবে লাভজনক প্রকল্পের জন্য আমানতের ব্যবহার
আধুনিক ব্যাংকগুলোর একটি দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো উদ্বৃত্ত অর্থ জমা করা এবং তা বিনিয়োগের জন্য ব্যবহার করা। প্রতিষ্ঠান এবং (সাধারণত কিছু পরিমাণে) আমানতকারী উভয়ের সুবিধার জন্য সঞ্চয়ের মূল্য বাড়ানোর উদ্দেশ্যে এগুলো তৈরি করা হয়েছে; সামগ্রিকভাবে, যে উপায়ে তহবিল বিনিয়োগ করা হয়, তা ব্যাঙ্কের ব্যক্তিগত উদ্বেগ হিসেবে বিবেচিত হয়। এ ব্যবস্থাটি সম্পদের ঘনত্ব বৃদ্ধির দিকে পরিচালিত করে।
এর পরিবর্তে আমাদের দারুল আমানত মানুষ ও সমাজের কল্যাণে বিনিয়োগ করতে পারে, সামাজিক সমস্যাগুলোকে মোকাবেলা করতে এবং সম্পদের ইসলাম প্রদর্শিত প্রবাহমানতার দিকে পরিচালিত করে। এই প্রতিষ্ঠানের একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ হবে সামাজিক কল্যাণের জন্য সর্বোত্তম সুযোগ সন্ধান করা (এর আমানতকারীদের পক্ষে) এবং এই ধরনের সুযোগগুলোতে বিনিয়োগ করা। শুরুতে, যদি কোনো প্রতিষ্ঠানের কাছে জমাকৃত সম্পদের উপর যাকাত ধার্য করা যায়, তাহলে এ পরিমাণ সম্পদ দাতব্য কাজে ব্যবহারের জন্য সে দায়ী থাকবে। উপরন্তু, যথেষ্ট পরিমাণে সম্পদ কর্জে হাসানা (দাতব্য উদ্দেশ্যে তৈরি একটি সুদ-মুক্ত ঋণ) হিসেবে ব্যবহারযোগ্য থাকবে, ঠিক যেমন প্রচলিত ব্যাংকগুলো রিজার্ভ/তারল্যের একটি ক্ষুদ্রাংশ থেকে অর্জন করতে পারে। এই ধরনের ব্যবহার অবশ্যই আমানতকারীদের সম্মতিতে হতে হবে। যাইহোক, ইসলামের ইতিহাসে এই ধরনের অসংখ্য ঘটনা এবং নজির রয়েছে।
উপরে যেমনটা উল্লেখ করা হয়েছে, দরিদ্রদের সাহায্য করা এবং সমাজের কল্যাণের জন্য কাজ করা কেবল মুসলমানদের দায়িত্বই নয়, তারা এটি করার সর্বোত্তম সুযোগগুলো সন্ধান করার জন্য একে অপরের সাথে প্রতিযোগিতা করতে উৎসাহিত হয়। ঠিক যেমন আধুনিক ব্যাঙ্কগুলো এই দুনিয়ায় সবচেয়ে লাভজনক বিনিয়োগের সুযোগগুলো সন্ধান করে, তেমনি দারুল আমানত পরকালে সর্বোত্তম বিনিয়োগের সন্ধান করবে (সমর্থনের জন্য সর্বোত্তম সামাজিক কারণ)। একটি গুরুত্বপূর্ণ বিনিয়োগ হতে পারে মানুষকে জীবিকা নির্বাহের জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতা অর্জনের ব্যবস্থা করা; যেহেতু এ ধরণের বিনিয়োগের একটি দীর্ঘমেয়াদী ফলাফল আছে।
মুসলিমরা যুক্তি-তর্ক দিয়ে এ ধারণা পেশ করেছেন যে, ইসলামী ব্যাংকগুলোর সামাজিক দায়বদ্ধতা রয়েছে এবং কেউ কেউ এটিকে আদর্শবাদী, আবেগী এবং অবাস্তব বলে সমালোচনা করেছেন। প্রকৃতপক্ষে, এ ধরণের কার্য সম্পাদনকারী বড় বড় ফাউন্ডেশন এবং দাতব্য সংস্থা ইতোমধ্যেই সারা বিশ্বে বিদ্যমান, যদিও মূলত সেগুলো আর্থিক প্রতিষ্ঠান। ইসলামী নীতির একটি পুনর্বিন্যাস প্রয়োজন, যা এই প্রেরণা ও অনুশীলনগুলোকে কেন্দ্রীয় ও আধুনিক ব্যাংকিং অনুশীলনকে প্রান্তিক করে তুলবে। উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় মানুষ ও সামাজিক পুঁজির গুরুত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বিশ্বব্যাংক (২০০৬) দেখায় যে, মানুষের দক্ষতা হলো জাতীয় সম্পদের প্রধান উপাদান; আরও বলে যে, উপরে প্রস্তাবিত ধরণের প্রতিষ্ঠানগুলো প্রচলিত উন্নয়ন কৌশলগুলোর চেয়ে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে আরও দক্ষতার সাথে এগিয়ে নিতে পারে। অধিকন্তু, কাহফ (২০০০) এবং হক্সটার ও অন্যদের (২০০২) গবেষণায় উপস্থাপিত ঐতিহাসিক প্রমাণগুলো পরামর্শ দেয় যে, এ ধরণের কার্যকলাপ অতীতে ইসলামী সমাজে ব্যক্তিগত ও প্রাতিষ্ঠানিক উভয় পর্যায়ে ব্যাপকভাবে ঘটেছে। ইসলামী চেতনার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নতুন ধরনের প্রতিষ্ঠান তৈরি করার জন্য ইসলামী চেতনা ব্যবহার করার সম্ভাবনা মালয়েশিয়ায় তাবুং হাজি দ্বারা ব্যাপক সফলভাবে চিত্রিত হয়েছে, যা মুসলমানদের হজ্জ পালন ও এই উদ্দেশ্যে সঞ্চয়-এ উদ্বুদ্ধ করে; বিস্তারিত জানার জন্য ওজঞও (১৯৯৫) দেখুন।
বিনিয়োগ এবং ব্যবসায়িক অর্থ
পশ্চিমা আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর মূল উদ্দেশ্য হলো বিনিয়োগকারী/আমানতকারীদের অর্থকে আরও অর্থোপার্জনের জন্য ব্যবহার করা। বিপরীতে, ইসলামী আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে অবশ্যই ইসলামী শরীয়ত (অর্থ সংগ্রহ, বিনিয়োগ এবং ব্যয়ের প্রক্রিয়ায়) এবং চেতনার (কাক্সিক্ষত সামাজিক লক্ষ্য, সহমর্মিতা, সম্প্রীতি এবং সহযোগিতার প্রচারে) সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হতে হবে। সুদ এবং প্রতিযোগিতার নীতিগুলো যা পশ্চিমা আর্থিক ব্যবস্থাগুলোর ভিত্তি, তা সহযোগিতা ও সম্প্রীতির বিকাশের জন্য প্রতিক‚ল। বিশেষত, উপরে শুরু হওয়া সুদের আলোচনাকে আরও বিকাশের জন্য, নিচে আরো দুটি যুক্তি তুলে ধরা হলো, যা ইসলামী মূলনীতির সাথে সুদের দ্ব›দ্বকে সুস্পষ্ট করে তোলে। যথা :
প্রথমত,
বিনিয়োগ ক্রিয়াকলাপগুলো অবশ্যই কিছু অংশীদারিত্বের উপর ভিত্তি করে হতে হবে, যার অনেকগুলো রূপ এবং প্রকরণ সম্ভব। এ অংশীদারিত্ব নিছক আর্থিক নয়; অংশীদারদের ব্যবসার ভাগ্য ভাগাভাগি করে নিতে হয়। এইভাবে, শাইলকের আইনী চুক্তির প্রয়োগ নিয়ে মুসলমানদের কোনো সমস্যা নেই, বরং কষ্টের সময়ে অ্যান্টোনিওর জন্য তার মধ্যে যে সহানুভূতির অভাব দেখা গিয়েছিলো, তা মুসলমানদের চেতনার সাথে সাংঘর্ষিক। সুদভিত্তিক চুক্তিগুলো ইসলামী চেতনার পরিপন্থী। কারণ সেখানে ব্যবসায়িক ফলাফল নির্বিশেষে ঋণদাতাকে পরিশোধ করতে হয়, প্রয়োজনে জামানত থেকে তার শরীরের ও মাংসের পাউন্ড তুলে নেয়। আধুনিক সময়ে বন্ধকগুলোর ফোরক্লোজারের সময় একই ধরণের কাজ করে, যেখানে বড় ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলো কৃষক এবং বাড়ির মালিকদের আর্থিক বিপর্যয়ের সুবিধা নেয়। সুদভিত্তিক লেনদেন অন্যের ভাগ্যের প্রতি উদাসীনতা বাড়ায় এবং তা সহযোগিতা ও সম্প্রদায়ের অনুভূতির বিকাশের জন্য ক্ষতিকর।
দ্বিতীয়ত,
হালাল হওয়ার জন্য উপার্জন অবশ্যই উৎপাদনশীল কার্যকলাপ বা বাস্তব পরিষেবার উপর ভিত্তি করে করা উচিত। একজনের প্রয়োজনের বাইরে আর্থিক সম্পদের মালিকানা কোনো উৎপাদনশীল কার্যকলাপ নয়। যাইহোক, উদ্যোগ-যার মধ্যে বিচার-মিমাংসা, ভালো ব্যবসার সুযোগ নির্বাচন এবং এই ধরনের নির্বাচনের সাথে সম্পৃক্ত ঝুঁকি নেওয়া জড়িত-একটি উৎপাদনশীল কার্যকলাপ। এভাবে প্রকৃত পণ্য এবং পরিষেবাকে কেন্দ্র করে নির্মিত ন্যায়-ভিত্তিক লেনদেন ইসলামে অনুমোদিত, নিখাদ আর্থিক লেনদেনগুলো নয়; এ ইসলামী চেতনা আধুনিক ব্যাংকিংয়ের চেতনার সাথে সরাসরি সাংঘর্ষিক, যেখানে প্রকৃত লেনদেনে ব্যাঙ্কের জড়িত হওয়া প্রায়শই আইনীভাবে নিষিদ্ধ-ব্যাংক শুধুমাত্র একটি বিশুদ্ধ আর্থিক মধ্যস্থতাকারী হিসেবে কাজ করতে পারে। যদিও প্রচলিত ব্যাংকগুলোকে ইসলামী উদ্দেশ্যগুলোর সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়া যায় না, কিছু পশ্চিমা প্রতিষ্ঠান ইসলামী আইনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং তাই এগুলোকে ইসলামী অর্থনীতির মডেল হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে। বৃহৎ বিনিয়োগকারীদের বর্তমান বিনিয়োগ ব্যাংকে ব্যবহৃত কিছু কৌশল এবং উদ্যোগ কাজে আসে এবং তাই এগুলো অনুকরণ করা যেতে পারে। কারণ, এক্ষেত্রে বিনিয়োগকারীর দ্বারা ঝুঁকি ভাগাভাগি করে নেয়া হয়, যা মূলত ইসলামী শরীয়ত মেনে চলে। ছোটো থেকে মাঝারি বিনিয়োগকারীদের বিনিয়োগের ক্ষেত্রে মিউচুয়াল ফান্ড বিনিয়োগের ক্ষেত্রে তহবিলের একটি উপযুক্ত উৎস হতে পারে। বর্তমান পশ্চিমা আর্থিক উপকরণগুলোকে ইসলামী শরীয়তের দাবির সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়ার ক্ষেত্রে প্রচুর প্রায়োগিক সমস্যা দেখা দেয়; এর একটি সহজবোধ্য সারাংশের জন্য উসমানির (২০০০) লেখাটি দেখা যেতে পারে।
তাকাফুল (বীমা)
আতিকুজ্জাফর খান (২০০৫) এর মতে, ইউরোপ এবং উসমানী খেলাফতের মধ্যে বাণিজ্যিক যোগাযোগের ফলে মুসলমানরা প্রথম বীমা অনুশীলন সম্পর্কে সচেতন হয়েছিলো। আমি অনুমান করি যে, ব্যক্তিগত এবং ব্যবসায়িক উভয় জীবনেই সমবায়ের অনুশীলন বীমার প্রয়োজনীয়তাকে উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস করে। এ কারণেই ৪/১০ এবং ৮/১৪ শতকের মধ্যে বৈশ্বিক বাণিজ্যে ইসলামী আধিপত্যের সময় ব্যাপক আন্তর্জাতিক বাণিজ্য থাকা সত্তে¡ও বীমার প্রয়োজন বা বীমা প্রবর্তন হয়নি। বীমার অনুমতি সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে ইসলামী শরীয়ত প্রণেতারা সাধারণত নেতিবাচক উত্তর দিয়েছেন। উদাহরণস্বরূপ, আতিকুজ্জাফর খান (২০০৫) বিংশ শতাব্দীতে বীমা সংক্রান্ত মুসলিম চিন্তাবিদদের সম্মিলিত রায়ের ইতিহাস দিয়েছেন। যদিও তারা বীমার উপযোগিতাকে স্বীকার করেছে, তারা দেখতে পেয়েছে যে, এটি বিভিন্ন কারণে ইসলামী আইনের সাথে সাংঘর্ষিক।
প্রথমত, একটি বীমা চুক্তিতে যাবার (প্রাপ্ত পণ্য বা প্রদত্ত মূল্য সম্পর্কে অনিশ্চয়তা) থাকে; ক্ষতির ক্ষেত্রে একটি বড় অংকের পাওনা পরিশোধ হতে পারে, কিন্তু ক্ষতি না থাকলে, এই ধরনের অর্থ পরিশোধ করা হয় না। গড় পরিসংখ্যান আইন ‘অনিশ্চয়তা’ দূর করে বা হ্রাস করে-এমন যুক্তিগুলো ইসলামী পণ্ডিতদের দ্বারা বিবেচনা করা হয়েছে এবং প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে। উপরন্তু, একটি বীমা চুক্তি জুয়া খেলার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ, যা নিষিদ্ধ। প্রকৃতপক্ষে বীমাকৃত এবং বীমাকারী দৈবভাবে একটি ঘটনা ঘটার উপর বাজি ধরে। এছাড়াও, পরিশোধের প্রয়োজন হলে, বীমাকৃত ব্যক্তি পুরস্কার হিসেবে প্রদত্ত অর্থের চেয়ে বেশি অর্থ পান। এটিকে সুদের একটি রূপ হিসেবে বিবেচনা করা হয়, যা নিষিদ্ধ। সবশেষে, ‘অর্জিত’ মজুরির সমস্যা রয়েছে-বীমা কোম্পানী যেটির জন্য অর্থপ্রদান করছে তার দ্বারা কী (আসল) পরিষেবা প্রদান করা হয়েছে তা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে। বীমা কোম্পানির দ্বারা কোন ক্ষতি হয় যার জন্য ক্ষতির ক্ষেত্রে দায় বহন করতে হবে? ক্ষতির ক্ষেত্রে প্রিমিয়াম প্রদান বা ক্ষতিপূরণ উভয়ই ইসলামী শরীয়তে গ্রহণযোগ্য শর্তে সমর্থনযোগ্য বলে মনে হয় না। যদিও এই সকল প্রশ্নের পিছনে যথেষ্ট আলোচনা হয়েছে, তবুও উপরে উল্লেখিত সর্বসম্মত মতামত হলো, পশ্চিমে প্রচলিত বিদ্যমান বীমা চুক্তির বেশিরভাগই ইসলামী আইনের সাথে সাংঘর্ষিক। উদাহরণস্বরূপ, ১০ শা’বান ১৩৯৮ (১৬ই জুলাই ১৯৭৮) মক্কায় অনুষ্ঠিত ইসলামী আইন সমাবেশের সিদ্ধান্ত, যেখানে একজনের ভিন্নমত ছিলো; তুলে ধরেছেন আতিকুজ্জামান খান (২০০৫)।
প্রচলিত বীমা পদ্ধতি এবং ইসলামী আইনের মধ্যে বিদ্যমান বিরোধ সম্পর্কে প্রায় সর্বসম্মত রায়ের পরিপ্রেক্ষিতে প্রশ্ন হলো, কোন বিকল্পগুলো সম্ভব হতে পারে? গাজী এবং অন্যরা (১৯৯২) বিদ্যমান প্রতিষ্ঠানগুলোকে ইসলামী শরীয়তের রঙে ঢেলে সাজাবার পদ্ধতিকে প্রত্যাখ্যান করেন এবং পরামর্শ দেন যে, আমাদের ইসলামী বিকল্পগুলোর নতুন নাম দেওয়া উচিত যাতে ইসলামী ও পুঁজিবাদী বীমার মধ্যে আমূল পার্থক্য বিদ্যমান থাকে। এটি ব্যাপকভাবে গৃহীত হয়েছে, যাতে ইসলামী বীমাকে এখন তাকাফুল বলা হয়। গাজী প্রমুখ (১৯৯২) বিভিন্ন ধরণের বীমা চুক্তির উদ্দেশ্য বিবেচনা করে তাদের উদ্দেশ্য এবং ইসলামী শরীয়তের মধ্যে সামঞ্জস্যের মূল্যায়ন করেন এবং একই উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য বিভিন্ন পদ্ধতির পরামর্শ দেন যা ইসলামী শরীয়তের এখতিয়ারভুক্ত রয়েছে। সাধারণভাবে, বীমার উদ্দেশ্যগুলো (যার মধ্যে অর্থনৈতিক নিরাপত্তা, সম্ভাব্য ক্ষতির জন্য সুরক্ষা এবং উত্তরাধিকারীদের জন্য বিধান) শরীয়তের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ বলে মনে করা হয়। যাইহোক, একটি ইসলামী কাঠামোর মধ্যে এই উদ্দেশ্যগুলো অর্জনের জন্য বিভিন্ন উদ্দেশ্যে বিভিন্ন পদ্ধতির প্রয়োজন। ইসলামী পদ্ধতি সম্পর্কে সম্যক ধারণা অর্জনের জন্য আমরা বিস্তৃত রূপরেখায় কিছু ঘটনা আলোচনা করি। বিস্তারিত জানার জন্য, IIBI (ও৯৯২) দ্বারা সংকলিত Encyclopedia of Islamic Banking and Insurance দেখুন। এছাড়াও, আকরাম খানের (১৯৮৩, ১৯৯১, এবং ১৯৯৮) টীকাযুক্ত গ্রন্থপঞ্জিগুলো দ্রুত সম্প্রসারিত সাহিত্যের একটি প্রাথমিক ধারণা প্রদান করে।
জীবনবীমা এবং পেনশন পরিকল্পনার জন্য সরকার-স্পন্সরকৃত পরিকল্পনাগুলো সাধারণত গ্রহণযোগ্য, যেহেতু সরকার তার নাগরিকদের খেয়াল রাখার জন্য দায়বদ্ধ। অন্যান্য উদ্দেশ্যে বেসরকারী খাতের বীমা প্রকল্পগুলো বেশি উপযুক্ত। যাইহোক, সাধারণ নীতিগুলো যার উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত, তা প্রচলিত বীমা চুক্তি থেকে ভিন্ন। গাজী প্রমুখ (১৯৯২) নোট করেছেন যে, বীমার ভিত্তি হতে পারে শুধুমাত্র সহযোগিতা, পারস্পরিক সহানুভূতি, ভ্রাতৃত্ব এবং পারস্পরিক প্রতিশ্রুতির উপর। তাই এমন কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে না, যার আসল ও মৌলিক লক্ষ্য ব্যবসা, মুনাফা অর্জন এবং অর্থ মজুত করা। আতিকুজ্জাফার খান (২০০৫) অনুরূপ মতামত পোষণকারী অন্যান্য পণ্ডিতদের রেফারেন্স প্রদান করেছেন।
ইসলামী আইন শুধুমাত্র পারস্পরিক বীমার অনুমতি দেয়, যেখানে একটি দল সম্মিলিতভাবে তার সদস্যদের স্বার্থরক্ষা করবে এবং বিপদের সময়ে তাদের সমর্থন করার জন্য কাজ করবে। উদ্দেশ্য যদি একে অপরকে সাহায্য করা হয় এবং বীমা চুক্তিতে কোনো লাভের উদ্দেশ্য জড়িত না থাকে, তাহলে পূর্বে আলোচিত ঘারার, জুয়া, সুদ এবং অযৌক্তিক অর্থপ্রদানের উপাদানগুলো বর্জন করা হয়। পশ্চিমা বীমার সৃষ্ট কিছু সমস্যা, যা দু’পক্ষের মধ্যে স্বার্থের দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করে, প্রায়োগিক সাহিত্যে সেসব ‘নৈতিক বিপদ/ moral hazard’ এবং প্রতিকূল নির্বাচন/ adverse selection’ নামে পরিচিত। বেসরকারি চিকিৎসা বীমার ক্ষেত্রে রোগীদের খরচ কমানোর জন্য খুব সামান্য প্রণোদনা থাকে, ডাক্তাররা চিকিৎসার জন্য ব্যয়বহুল বিকল্প বেছে নিতে পারেন বা নিয়ে থাকেন এবং অতিরিক্ত মেডিকেল টেস্ট দেন; যেন বীমা কোম্পানিগুলোও খরচ সাশ্রয়ের জন্য প্রণোদনা কমিয়েছে, কারণ তারা গ্রাহকদের খরচ অতিক্রম করতে পারে। ফলস্বরূপ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বেসরকারি বীমাসহ রোগী প্রতি খরচ; ইউকে, ফ্রান্স, কানাডা, জার্মানি এবং জাপানের মতো দেশগুলোÑযেখানে সর্বজনীন স্বাস্থ্যসেবা প্রয়োগ করা হয়Ñতার তুলনায় দ্বিগুণ হয়। লেভিন গ্রুপের (২০০৫) রিপোর্ট বেসরকারি চিকিৎসা বীমার অদক্ষতা নথিভুক্ত করে। পরীক্ষামূলক অর্থনীতির ফলাফলগুলো দেখায় যে, সামাজিক এবং ব্যক্তিগত স্বার্থের মধ্যে দ্বন্দ্বের সমস্যাগুলো হ্রাস করা যেতে পারে যখন সহযোগিতাকে উৎসাহিত করা হয় এবং স্বার্থপর আচরণ যা গোষ্ঠীর স্বার্থকে উপেক্ষা করে তাকে নিরুৎসাহিত করা হয়। জামান (২০১৪, ২০১৩) দেখায় কীভাবে বীমার ক্ষেত্রে ইসলামী পদ্ধতির মধ্যে এই সমস্যাগুলো এড়ানোর সম্ভাবনা রয়েছে।
ইসলামী বীমার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলো সম্পদের ঘনত্ব রোধ করা। গাজী প্রমুখ (১৯৯২) বলেন যে, “ইসলাম ধন-সম্পদের পুঞ্জিভূতকরণ/সঞ্চয় করাকে নিষিদ্ধ করে। তাই, এমন কোনো আশ্বাসের ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে না, যার ফলে নির্দিষ্ট কিছু লোক ধনী হতে পারে…।” এই উদ্বেগের কারণ হলো যে, বীমার প্রচলিত ফর্মগুলোর জন্য বীমাকারীকে খুব ধনী হতে হবে। এটি অ্যাডাম স্মিথের (১৮৮৭) গবেষণাপত্রের শুরুর দিকেই উল্লেখ করা হয়েছিলো। বীমার ব্যাপক বিস্তৃতি মুনাফা অর্জন এবং সম্পদ বৃদ্ধির সুযোগ প্রদান করে যা শুধুমাত্র ধনীরাই ব্যবহার করতে পারে, ফলশ্রæতিতে সম্পদের ঘনত্ব বৃদ্ধির দিকে পরিচালিত করে। বীমার পারস্পরিক রূপগুলো এই সমস্যাটি এড়াতে পারে সম্মিলিতভাবে দায়িত্ব পালন করা এবং নিজেদের মধ্যে বীমার বোঝা ভাগ করার মাধ্যমে।
ইসলামী শরীয়তের কাঠামোর মধ্যে বীমা প্রদানের জন্য বেশ কয়েকটি ভিন্ন মডেল প্রণয়ন করা হয়েছে এবং সম্প্রতি প্রতিষ্ঠিত তাকাফুল কোম্পানিগুলোর মাধ্যমে তা বাস্তবায়ন করা হয়েছে। একটি মডেল ওয়াকফের ধারণার উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছে, যা এর সদস্যদের সহায়তা প্রদান করে। আরেকটি মডেল উপহার (তাবাররু) এর ধারণা ব্যবহার করে এবং এছাড়াও বেশ কয়েকটি মিশ্রিত ও বিকল্প ফর্ম প্রস্তাব করা হয়েছে। আর্থিক প্রকৌশলের এই অংশটির পেছনের ধারণাটি হলো বিদ্যমান বীমা প্রকল্পগুলোর সমরূপ একটি সমন্বয় তৈরি করার জন্য ঐতিহাসিকভাবে গ্রহণযোগ্য ইসলামী চিন্তাগুলো ব্যবহার করা। কিছু লেখক ঐতিহাসিক ইসলামী প্রতিষ্ঠানের উপর ভিত্তি করে আরো মৌলিক চিন্তা প্রস্তাব করেছেন; এর পেছনে মূল ধারণা হলো বিস্তৃত পরিমণ্ডলে দায়িত্ববোধ। উপরে যেমনটা উল্লেখ করা হয়েছে, বিপদের সময়ে পরিবারই আমাদের সহযোগিতার প্রথম উৎস। যদি এটি অপর্যাপ্ত প্রমাণিত হয়, তাহলে বর্ধিত পরিবার দায়ভার বহন করবে বলে আশা করা হয়। এমনকি আরও বড় সমস্যায় পড়লে তা সমাধান করা সমগ্র গোত্র/সম্প্রদায়ের সম্মিলিত দায়িত্ব হয়ে পড়ে।
এই প্রতিষ্ঠানগুলোর সৃজনশীল অভিযোজন বীমার বিকল্প প্রদান করতে পারে। পরিবার এবং গোত্রের পরিবর্তে, উদাহরণস্বরূপ, প্রথমে একটি শহর এবং তারপর একটি দেশের মধ্যে বাস মালিকদের একটি সমিতি গঠন করা সম্ভব। সাধারণভাবে বলতে গেলে, পশ্চিমা প্রতিষ্ঠানগুলোর ব্যক্তিত্ববাদী প্রবণতা তাদের ইসলামের সাথে বেমানান করে তোলে, যদিও বীমার ক্ষেত্রে, কিছু পশ্চিমা মডেল রয়েছে যেগুলোর ইসলামের মধ্যে অভিযোজনের সম্ভাবনা রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, জার্মান স্বাস্থ্য-বীমাব্যবস্থার সাথে উপরে আলোচনা করা প্রস্তাবগুলোর কিছু সাদৃশ্য রয়েছে, যেখানে ব্যক্তিদেরকে গোষ্ঠীতে প্রতিস্থাপন করা হয় এবং সকল গোষ্ঠী একই ধরণের বাধ্যতামূলক সুযোগ-সুবিধা পায়। এছাড়াও, স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা সংগঠনগুলো একটি মডেল অফার করে, যা দ্বারা পারস্পরিক বীমার ইসলামী মডেলগুলোর সাথে সমন্বয় করা সম্ভব। এখানে একদল লোক মাসিক অর্থ প্রদান করে, যা চিকিৎসক ও ভবন পরিষেবা নিয়োগের খরচ বহন করে এবং এই গোষ্ঠীর সকল প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্য চাহিদাগুলো তাদের দ্বারা পূরণ করা হয়। এই ধরনের পরিষেবা চুক্তি ইসলামী আইনের মধ্যে অনুমোদিত (নির্দিষ্ট সীমাবদ্ধতা সাপেক্ষে) এবং এটি বীমা চুক্তির একটি রূপ হিসেবে বিবেচিত হতে পারে।
ওয়াকফ (এন্ডোমেন্ট/ট্রাস্ট)
ওয়াকফ একটি অনন্য ইসলামী প্রতিষ্ঠান, যেটি অতীতে ইসলামী সুশীল সমাজে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভ‚মিকা পালন করেছে; যদিও এটি বর্তমানে প্রান্তিক পর্যায়ে রয়েছে, যার কারণ পরবর্তীতে আলোচনা করা হয়েছে। ইসলামী আইনের অধীনে যে কেউ সামাজিক কল্যাণের সুনির্দিষ্ট প্রকল্পের জন্য তার কোনো সম্পত্তি, তার ফল এবং তা থেকে প্রাপ্ত আয় স্থায়ীভাবে দান করতে পারে। আওকাফকে নবী (স.) ‘চিরস্থায়ী দাতব্য’ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এবং উৎসাহিত করেছিলেন; সংক্ষিপ্ত ভ‚মিকার জন্য কাহাফের গবেষণাপত্র দেখুন। ইতিমধ্যেই আলোচনা করা হয়েছে, সম্পদশালীদের দায়িত্ব রয়েছে অভাবীদের খুঁজে বের করার এবং এমনভাবে সাহায্য করার (ঋণ বা উপহার হিসেবে) যাতে তারা অসম্মানিত না হয়।
বিপরীতে, ওয়েবারের মতে, পুঁজিবাদের প্রাণসত্তা হলো নিজের স্বার্থে সম্পদের অযৌক্তিক সাধনা, যা অনেক অর্থনীতিবিদকে অর্থ উপার্জনে এমন প্রাধান্য দিতে পরিচালিত করেছে যে, এমনকি দরিদ্রদের সাহায্য করাকেও অর্থ উপার্জনের একটি উপায় হিসেবে দাঁড় করানো হয়েছে। ঐতিহ্যগতভাবে, ধনী মুসলমানরা আওকাফ স্থাপন করে, যা উদ্বৃত্ত অর্থ ব্যবহার করার সর্বোত্তম উপায়গুলোর মধ্যে একটি হিসেবে বিবেচিত হয়। যেহেতু সম্পত্তি (সাধারণত জমি) ব্যবহার করা হয় না, তাই তা থেকে প্রাপ্ত রাজস্ব তাত্তি¡কভাবে চিরস্থায়ী দাতব্য উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যেতে পারে; এটি ভালো কাজের প্রতিযোগিতায় শ্রেষ্ঠত্বের একটি উপায় হিসেবে বিবেচিত হয়, যা মুমিন জীবনের উদ্দেশ্য। আওকাফের অনেক বিষয়ে ইসলাহীর (২০০৩) ইংরেজি নিবন্ধের একটি গ্রন্থপঞ্জি রয়েছে এবং সেইসাথে সেখানে আরবী ভাষায় আরও বিস্তৃত গ্রন্থপঞ্জির উল্লেখ রয়েছে, যেহেতু আরবী ভাষায় এই বিষয়ে আরও কাজ রয়েছে। পশ্চিমা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে দাতব্য ফাউন্ডেশন এবং সম্ভবত এনজিওগুলোকে ওয়াকফের সাথে তুলনা করা যায়, পার্থক্য হলো ওয়াকফ ইসলামী শরীয়তের উপর ভিত্তি করে একটি বিস্তৃত নিয়মের অধীন।
কাহফ (২০০০), আঞ্জুম (১৯৯৫), এবং সাইত ও লিম (২০০৬, অধ্যায় ৭) এর মতো অনেক লেখক ইসলামের ইতিহাসে ওয়াকফের তাৎপর্য নিয়ে আলোচনা করেছেন এবং সকলেই এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, ওয়াকফ ইসলামী অর্থনীতির একটি উল্লেখযোগ্য এবং তাৎপর্যপূর্ণ অংশ গঠন করেছে এবং সুশীল সমাজের সকল স্তরে গুরুত্বপূর্ণ ভ‚মিকা পালন করেছে। অনুমান করা হয় যে, উসমানী খেলাফতের প্রায় এক তৃতীয়াংশ জমি এই ধরণের ট্রাস্টের জন্য উৎসর্গ করা হয়েছিল। মরিয়ম হোয়েক্সটার এবং অন্যদের মতে (২০০২)-
“শহুরে এলাকা গঠনে ওয়াকফের অবদানকে খুব কমই আঁচ করা যায়… (ইসলামী) শহরে জনপরিবেশের একটি বড় অংশ প্রকৃতপক্ষে অনুদানের ফলে সৃষ্টি হয়েছিলো।”
যদিও ইসলামী ভূমি জুড়ে লক্ষ লক্ষ আওকাফ বিভিন্নধর্মী দাতব্য উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়েছিলো, এর মধ্যে পাঁচটি প্রধান বিভাগ ছিলো : খাদ্য, বাসস্থান, স্বাস্থ্য, শিক্ষা এবং ধর্ম। কাহফ (এন.ডি., ২০০০) এই বিভিন্ন ক্ষেত্রের আপেক্ষিক আকার নিয়ে কিছু ঐতিহাসিক বিবরণ এবং রেফারেন্স তুলে ধরেছেন। সাইত ও লিম (২০০৬) এর মতে, উসমানীরা নিজেদেরকে সামাজিক কল্যাণমূলক কাজের জন্য দায়বদ্ধ মনে করতো না, যেহেতু আওকাফ জনগণের এ চাহিদাগুলোর পর্যাপ্ত যতœ নিচ্ছিলো। এইভাবে এই প্রতিষ্ঠানগুলো জনগণের চাহিদা পূরণের জন্য বর্তমান ইউরোপীয় কল্যাণ রাষ্ট্র মডেলের একটি ঐতিহাসিক ইসলামী বিকল্প গঠন করে।
ইসলামী মেথডোলজির দুটি স্বতন্ত্র সুবিধা রয়েছে :
- আওকাফ স্থানীয়ভাবে প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত হতো। রাষ্ট্র-চালিত সিস্টেমের তুলনায় তাদের কাছে যথেষ্ট পরিমাণে স্থানীয় তথ্য ছিলো এবং তাই তারা আরও দক্ষতার সাথে কাজ করতে পারতো।
- সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে দায়িত্ববোধ জাগ্রত করতে হবে, সামাজিক বন্ধনকে শক্তিশালী করতে হবে এবং সামাজিক সচেতনতা বাড়াতে হবে- ইসলামের এই দাবিও এই ব্যবস্থার মাধ্যমে পূরণ করা হয়েছিলো।
সাইত ও লিম (২০০৫, পেপার ৭) লেখেন যে “ইসলামী ভ‚মিতে সম্পদ পুনঃবণ্টনে আওকাফের পদ্ধতি শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে সফল হয়েছে”, যা ন্যায়সঙ্গত ফলাফলের দিকে পরিচালিত করে এবং কোরআনের নির্দেশ অনুযায়ী সম্পদের সঞ্চালন করে। এছাড়াও, অসংখ্য ক্ষুদ্র ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে স্বাধীন উপার্জনের সুযোগ করে দেয়ার মাধ্যমে আওকাফ সিভিল সোসাইটিকে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ক্ষমতায়িত করেছে। ঐতিহাসিকভাবে, রাষ্ট্র এই ক্ষমতাকে দাবিয়ে রাখার এবং বিভিন্ন উপায়ে আওকাফকে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করেছিলো, কিন্তু এ ধরণের প্রচেষ্টা সফলভাবে প্রতিহত করা হয়েছিলো।
মহিলারা একটি উল্লেখযোগ্য পরিমাণ আওকাফ প্রদান করেছেন বা পরিচালনা করেছেন এবং সিভিল সোসাইটিতে একইভাবে উল্লেখযোগ্য প্রভাব ফেলেছেন; ফাইজার (২০০৭) এর উপর প্রয়োজনীয় গ্রন্থপঞ্জি উল্লেখ করেছেন। আওকাফের মাধ্যমে শিক্ষার সমান প্রবেশাধিকার এবং ইসলামী সমাজে শিক্ষার প্রতি সাধারণ সম্মান প্রদানের কারণে সকল সামাজিক শ্রেণির প্রতিনিধিত্বের জায়গাগুলো ঐ সমাজের শ্রেষ্ঠ বুদ্ধিজীবীদের হাতে ছিলো; কাহফ (২০০০) আবদুল মালিক আল-সায়িদ এর বক্তব্য উল্লেখ করেছেন যে, “কখনও কখনও, সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম পÐিতরা সমাজের দরিদ্র ও দাস শ্রেণি থেকে এসেছেন এবং প্রায়শই তারা শাসকদের নীতির তীব্র বিরোধিতা করতেন।”
ওয়াকফের একটি শক্তিশালী আইনগত ভিত্তি রয়েছে। বিভিন্ন ধরনের ওয়াকফ এবং তাদের কার্যক্রম সংক্রান্ত নিয়মাবলী, ওয়াকফের জন্য বিভিন্ন ধরণের সম্পত্তি ব্যবহারের অনুমতি এবং আওকাফের প্রধান ও ছোটখাটো দিক নিয়ে ইসলামী আইনের বিভিন্ন মাযহাবের মধ্যে বিতর্কের বিষয়ে একটি বিশাল সাহিত্য রয়েছে। একবার চালু হয়ে গেলে ওয়াকফ সহজে বন্ধ করা যায় না। অধিকন্তু, ওয়াকফের প্রতিষ্ঠাতার মূল উদ্দেশ্য সহজে পরিবর্তন করা যায় না। এই ইসলামী নিয়মের কারণে কুরন (২০০৪) যুক্তি দিয়েছিলো যে, ইসলামী সভ্যতার পতনের একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ হলো অনেক আওকাফ এমন কাজে আটকে ছিলো, যা সময়ের সাথে সাথে অকার্যকর হয়ে পড়েছিলো।
প্রকৃতপক্ষে, ইসলামী আইনে যথেষ্ট গতিশীলতা এবং নমনীয়তা রয়েছে এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে পরিবর্তনশীল পরিস্থিতিতে এর সৃজনশীল অভিযোজন নথিভুক্ত করা যেতে পারে, যেমনটি আমরা এই বইতে বিভিন্ন প্রসঙ্গে আলোচনা করেছি। বরং এটা স্পষ্ট যে, সামগ্রিকভাবে ইসলামী সমাজ স্থবির হয়ে পড়েছিলো এবং বিভিন্ন মাত্রায় পরিবর্তনশীল পরিস্থিতির সাথে খাপ খাইয়ে নিতে পারেনি। হজসন (১৯৭৪) মুসলিমদের পতনের কারণ সম্পর্কে বিস্তৃত দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরেছেন, যা ওরিয়েন্টালিস্টদের বিশ্লেষণ দ্বারা পেশকৃত বেশিরভাগ প্রাথমিক ত্রুটিগুলোকে এড়িয়ে যায়। ইসলাহী (২০০৩) এর গ্রন্থপঞ্জীতে আওকাফকে কীভাবে হালনাগাদ এবং আধুনিকীকরণ করা যায় সে সম্পর্কিত প্রচুর নিবন্ধের তালিকা রয়েছে।
ইসলামী শরীয়তে আওকাফের দৃঢ় ভিত্তির কারণে অনেক মুসলিম শাসকদের দ্বারা তার প্রভাব রোধ করার প্রচেষ্টাকে সে প্রতিহত করতে সক্ষম হয়েছিলো। যাইহোক, ঔপনিবেশিক শক্তি ইসলামী আইন মানতে বাধ্য ছিলো না। শুধুমাত্র সম্পদের জন্যই নয়, বরং আওকাফের সাংগঠনিক শক্তি ও বস্তুগত সম্পদ প্রায়ই উপনিবেশের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে কাজ করার সুযোগ দিয়েছিলো বলে তারা প্রচুর পরিমাণে ওয়াকফের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করেছিলো।
উত্তর-ঔপনিবেশিক যুগে, বিভিন্ন জটিল কারণে, বেশ কয়েকটি মুসলিম দেশ আওকাফকে বিলুপ্ত, জাতীয়করণ বা এর উপর কঠোর প্রবিধান তৈরি করেছে। সাইত এবং লিম (২০০৫, পেপার ৭, পৃ. ১৫) লেখেন যে, ওয়াকফের বিলুপ্তি জনসেবার ক্ষেত্রে একটি শূন্যতা তৈরি করেছে, যা অনেক মুসলিম দেশে রাষ্ট্র সহজে পূরণ করতে পারেনি। যাইহোক, ওয়াকফের ‘ধারণা’ উভয়ই প্রভাবশালী রয়ে গেছে এবং এর পুনরুজ্জীবনের স্পষ্ট লক্ষণ রয়েছে। পাবলিক পলিসি এবং মুসলিম জীবনের সকল দিকের উপর প্রভাববিস্তারকারী একটি হাতিয়ার হিসেবে ওয়াকফ কাজ করেছে এবং করে যাচ্ছে।
ওয়াকফের প্রতিষ্ঠানকে পুনরুজ্জীবিত করার এবং অতীতে এটিকে কেন্দ্রীয় গুরুত্ব দেওয়ার প্রয়োজনীয়তার বিষয়ে আজ মুসলমানদের মধ্যে ব্যাপক ঐকমত্য রয়েছে। কীভাবে আওকাফের আইনকে নমনীয় করা যায়, প্রতিষ্ঠানটিকে পুনরুজ্জীবিত করা যায় এবং আধুনিক বাস্তবতার সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়া যায়, সে বিষয়ে আলোচনা ইসলামী অর্থনৈতিক সাহিত্যে প্রচুর আছে। এর সাথে সংশ্লিষ্ট সমস্যাগুলোর সকল দিক নিয়ে আলোচনা করে অসংখ্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। সাইত এবং লিম (২০০৫ পেপার ৭, ২০০৬) কিছু প্রয়োজনীয় সংস্কার নিয়ে আলোচনা করে উল্লেখ করেন যে, কুয়েত এই ক্ষেত্রে নেতৃত্ব দিয়েছে। এছাড়াও মনজার কাহফ (১৯৯৮ন, ২০০০, হ.ফ.) এবং আনাস যারকা (১৯৯৪) আলোচনা করেন, কীভাবে এই গুরুত্বপূর্ণ ইসলামী প্রতিষ্ঠানটিকে পুনরুজ্জীবিত করা যায় এবং অর্থায়নের উপযুক্ত পুরানো ও নতুন পদ্ধতিগুলো চিহ্নিত করা যায়।
হিসবাহ (অডিট বা জবাবদিহিতা)
মনজার কাহফ (১৯৯৬, অধ্যায় ৬) বিভিন্ন ধরণের বাজার ব্যর্থতার একটি প্রাথমিক ভূমিকা প্রদান করেন, যার জন্য রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ প্রয়োজন। তিনি ইসলামী অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানের চেতনা নিয়েও আলোচনা করেন, যা অবাধ বাণিজ্যের পথে বাধা হ্রাস করার সাথে সাথে এজাতীয় সমস্যার একটি সহযোগিতামূলক সমাধান খুঁজে বের করে। প্রকৃতপক্ষে, ইসলাম কর্মের সকল ক্ষেত্রে (বাজার সহ) ব্যক্তি স্বাধীনতার উপর অনেক বেশি জোর দেয় এবং কেবল সামাজিক স্বার্থের প্রয়োজন হলেই তা নিয়ন্ত্রণ করে। কাহফ (১৯৯৬, অধ্যায় ৬, পৃ. ৫৫) উল্লেখ করেছেন যে, আল-হিসবাহ-এর আধা-বিচারিক প্রতিষ্ঠান, যা ইসলামের প্রথম দিন থেকে চালু ছিলো এবং সিস্টেমের স্পিরিট চালু রাখার দায়িত্বে নিয়োজিত থাকেতো, এমন শর্তাবলী নির্ধারণ করে যা জনগণের স্বাস্থ্য ও স্বার্থ সংরক্ষণ করে, ভোক্তাদের অধিকার রক্ষা করে, ব্যবসা ও শ্রম বিরোধ সমাধান করে এবং ভালো মার্কেট-বিহেভিয়ারের প্রচার ও অনুসরণ নিশ্চিত করে।”
নাজ (১৯৯১) ইসলামী শরীয়তে হিসবাহর ভিত্তি, ইসলামী রাষ্ট্রের মধ্যে এর তাত্তি¡ক ও ঐতিহাসিক কার্যাবলী এবং একটি ইসলামী কাঠামোর মধ্যে অন্যান্য বিচার বিভাগীয় ও নির্বাহী প্রতিষ্ঠানের সাথে এর মিল ও পার্থক্য-সহ হিসবাহের একটি ব্যাপক সমীক্ষা দেন। বাজারের নিয়ন্ত্রণ হিসবাহের প্রধান কাজগুলোর মধ্যে একটি এবং আমাদের অর্থনীতির বিষয় হওয়ার করার কারণে আমি প্রধানত এই দিকটির উপর আলোচনা করবো। যাইহোক, নাজ উল্লেখ করেছেন যে, বেশ কিছু পশ্চিমা লেখক হিসবাহর অনুবাদ মার্কেট সুপারভাইজার ব্যবহার করেছেন, যা হিসবাহের তুলনায় খবই সংকীর্ণ অর্থ বহন করে, যার মধ্যে জনসাধারণের আখলাকী সকল দিক অন্তর্ভুক্ত। ব্যাখ্যাস্বরূপÑ
- অনাথ এবং বিধবাদের জন্য সঙ্গী খোঁজা (যখন তারা নিজেরা তা করতে অক্ষম),
- নিশ্চিত করা যে শিক্ষকরা ছাত্রদের খুব বেশি কঠোর শাস্তি দেননি,
- ইসলামী আচরণবিধি প্রয়োগ করা, যার মধ্যে সামাজিক রীতিসিদ্ধ আচরণগুলোও অন্তর্ভুক্ত থাকবে,
- কূপ, খাল বা শহরের দেয়ালের মতো সরকারি সম্পত্তি মেরামত।
সাধারণত, হিসবাহ এমন ক্ষেত্রে জনস্বার্থ রক্ষা করে যেখানে আদালতে মামলা নিয়ে যেতে পারে এমন কোনো তাৎক্ষণিক সংক্ষুব্ধ পক্ষ নেই। বাজারের মধ্যে হিসবাহর দায়িত্ব হলো, সরকারী মান অনুসারে প্রদত্ত মানের স্ট্যাম্প অনুযায়ী ওজন এবং পরিমাপ, বিক্রিত পণ্যের মান নিশ্চিত, মিথ্যা বিজ্ঞাপন প্রতিরোধ, মূল্যবৃদ্ধির জন্য পণ্য মজুদ প্রতিরোধ, গোপন চুক্তি এবং একচেটিয়া কর্ম ইত্যাদি বিষয়ের ব্যাপারে ব্যবস্থা গ্রহণ; এবং সাধারণভাবে জনস্বার্থ রক্ষা করা। নদী বা পরিবেশ দূষণের মতো বিষয়গুলোও হিসবাহের এখতিয়ারের মধ্যে পড়ে। নাজ (১৯৯১) এর অধ্যায় ৫-এ ইসলামী ইতিহাসের বিভিন্ন সময়ে এর বিভিন্ন ভ‚মিকা এবং তা বাস্তবায়নের একটি নিরীক্ষণ তুলে ধরা হয়েছে। একটি সূ² কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো যে, হিসবাহ শুধুমাত্র পাবলিক বিষয়গুলোর সাথে সম্পর্কিত দৃশ্যমান অনৈতিকতাগুলো নিয়ে কাজ করে। যদি লোকেরা ব্যক্তিগতভাবে মদ্যপান করে বা জুয়া খেলে, হিসবাহ এটি তদন্ত এবং উন্মোচন করার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত নয়। প্রকৃতপক্ষে, কোরআন (৪৯:১২) আদেশ দেয় যে ব্যক্তিগত কর্মের তদন্ত করা উচিত নয়।
হিসবাহকে পশ্চিমা প্রতিষ্ঠানের সাথে তুলনা করার ক্ষেত্রে আমি প্রথমে মুক্ত বাজার ব্যবস্থার একটি সুপরিচিত ঘাটতি লক্ষ্য করি যে, যেখানে একটি ছোটো গোষ্ঠী অনেক বেশি লাভবান হয় এবং যেখানে একটি বৃহৎ গোষ্ঠীর উপর অল্প পরিমাণ ক্ষতিকে বন্টন করা হয়, সেখানে মুক্ত বাজার ব্যবস্থাপনা সাধারণত সেই ছোটো গোষ্ঠির স্বার্থের পক্ষে এবং জনস্বার্থের জন্য ক্ষতিকর ফলাফলের দিকে নিয়ে যায়। এই সমস্যাটি কাটিয়ে উঠতে ক্লাস অ্যাকশন স্যুটের ধারণাটি তৈরি করা হয়েছে এবং সাম্প্রতিক বছরগুলোতে যথেষ্ট আইন ও সাহিত্য এই সমস্যাটির সমাধান করেছে। ভোক্তা অ্যাডভোকেট ও অ্যাক্টিভিস্ট রাল্ফ নাদেরের কর্মজীবনের একটি গবেষণায় জনস্বার্থে বড় বড় কর্পোরেশনের দায়িত্ব গ্রহণের কারণে সৃষ্টপ্রধান সমস্যাগুলো সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। রবার্ট পিটফস্কি (১৯৭৭) বিজ্ঞাপনের প্রেক্ষাপটে সমস্যাগুলো নিয়ে আলোচনা করেছেন, যখন নিউজিল্যান্ডের ভোক্তা বিষয়ক মন্ত্রণালয় (২০০৫) এ বিষয়ে একটি বিস্তৃত পর্যালোচনা করেছে এবং সাহিত্য সমীক্ষা প্রদান করেছে। তাই এটা খুবই আগ্রহের বিষয় যে, শুরু থেকেই ইসলামী রাষ্ট্রগুলোতে রাল্ফ নাদেরের চিত্রিত সরকারী প্রতিষ্ঠান ইসলামী সরকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিদ্যমান ছিলো।
সাধারণভাবে, অর্থনৈতিক তাত্ত্বিকদের laissez-faire ওরিয়েন্টেশন এবং বাজারের ফলাফলগুলোকে (market outcomes) সর্বোত্তম ধরে নেয়ার ফলে বাজারের ব্যর্থতার স্বীকৃতি যথেষ্ট বিলম্বিত হয়, যা ভোক্তাদের ক্ষতি করে এবং সমস্যা থেকে প্রতিকারের উপযুক্ত পদ্ধতি বিকাশে ব্যর্থ হয়। ফ্রিডম্যান (২০০৫) চরমপন্থা অবলম্বন করে যুক্তি দেন যে, “ব্যবসার একমাত্র ব্যবসা হলো মুনাফা অর্জন করা”, যা ইঙ্গিত করে যে লাভের তাড়নায় সামাজিকভাবে ক্ষতিকারক পরিণতি উপেক্ষা করা যেতে পারে। ইসলাম এই বিষয়ে একটি সুস্পষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করে, ফার্ম-সহ সকল কর্মীদের সামাজিক দায়বদ্ধতা অর্পণ করে এবং হিসবাহ প্রতিষ্ঠান ও সংশ্লিষ্ট প্রশাসনিক ব্যবস্থার আকারে জবাবদিহিতা নিরীক্ষণ ও প্রয়োগের ব্যবস্থা রাখে।
পরিবেশগত সুরক্ষা, বাস্তুবিদ্যা এবং প্রাকৃতিক সম্পদ
দায়িত্বজ্ঞানহীন এবং অনিয়ন্ত্রিত ব্যবসায়িক ক্রিয়াকলাপ এবং বিলাসবহুল জীবনযাত্রা অনুসরণের সামাজিক পরিণতির মধ্যে আমরা পরিবেশগত সমস্যাগুলোকে অন্তর্ভুক্ত করতে পারি, যা এ গ্রহের মানব ও অন্যান্য জীবনকে যথেষ্ট হুমকির সম্মুখীন করেছে। উদাহরণস্বরূপ, রিচার্ড রবিনস (২০০৭) লিখেছেন যে, একটি ধনী দেশে একজন ব্যক্তির জীবনমান বজায় রাখার জন্য গড়ে প্রায় ৫ হেক্টর উৎপাদনশীল জমি প্রয়োজন, যেখানে বিশ্বব্যাপী ব্যক্তি প্রতি মাত্র ১.৭ হেক্টর জমি বিদ্যমান রয়েছে। বিলাসবহুল জীবনধারার চাহিদা পূরণের প্রক্রিয়া গ্রহের সম্পদকে এমন ব্যাপকভাবে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যায়, যা আমাদের সমসাময়িক এবং ভবিষ্যত প্রজন্ম উভয়ের জন্যই স্পষ্টত অন্যায়। এর প্রতিক্রিয়া হিসেবে, ‘টেকসই উন্নয়ন (sustainable development)’ ধারণা, যা দীর্ঘমেয়াদে টেকসই হতে পারে এমন পদ্ধতিতে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের প্রস্তাব করে। এটি তার আকাঙ্খিত ফলাফলের পরিপ্রেক্ষিতে ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গির সাথে অনেক বেশি সাদৃশ্যপূর্ণ হলেও উদ্দেশ্যের ক্ষেত্রে নাটকীয়ভাবে ভিন্ন, যেমনটি ইউসরি (২০০৫) আলোচনা করেছেন। এইভাবে, টেকসই উন্নয়নের কিছু দৃষ্টিভঙ্গিতে-যদিও অবশ্যই সব নয়-অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিই মুখ্য উদ্দেশ্য এবং পরিবেশ সুরক্ষাকে একটি উপায় হিসেবে বিবেচনা করা হয় যাতে ভবিষ্যতে সম্পদের বৃদ্ধি অব্যাহত থাকে।
ইসলামী দৃষ্টিতে প্রাকৃতিক সম্পদ একটি পবিত্র আমানত এবং ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য এগুলো রক্ষা করা মানুষের একটি মৌলিক দায়িত্ব। অর্থনৈতিক উন্নয়ন কোনক্রমেই এখানে (সরাসরি) লক্ষ্য নয়, তবে এটি অর্থনৈতিক উন্নয়ন যেমন, দারিদ্র্য বিমোচন এর একটি উপায় হতে পারে। এম. ফাহিম খান (২০০৩) ভোক্তা আচরণের তত্তে¡র সাথে এই বিষয়গুলোর প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে আলোচনা করেছেন। যদিও পরিবেশ সুরক্ষার কিছু দিক হিসবাহের অধীনে পড়ে, তবুও পরিবেশগত সমস্যাগুলো সাধারণত সামগ্রিকভাবে সমাজের সম্মিলিত দায়িত্ব। পাশাপাশি, পরিবেশ সুরক্ষা, প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণ এবং জীববৈচিত্র্য রক্ষণাবেক্ষণ নিশ্চিত করার ব্যবস্থা রাষ্ট্র, নির্দিষ্ট প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তির দ্বারা নেওয়া যেতে পারে। কোরআন (২:২০৪-২০৫) এমন লোকদের সম্পর্কে তিরস্কার করে, যাদের কথাবার্তা মানুষকে মুগ্ধ করে, কিন্তু তারা পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করে এবং ফসল ও বংশধারা ধ্বংস করে। মহানবী (স.) মদীনার চারপাশে বারো মাইলের একটি সবুজ বেষ্টনী স্থাপন করেছিলেন এবং এই এলাকায় গাছ কাটা বা শিকার নিষিদ্ধ করেছিলেন। তিনি পানীয় জলের দূষণও নিষিদ্ধ করেছিলেন; ফকীহরা বলেছেন যে, আবর্জনা এবং বর্জ্য দ্রব্য নদীতে ফেলা জায়েজ নয়। এছাড়াও তিনি অনুর্বর জমির পুনরুজ্জীবনকে উৎসাহিত করেছেন, এ কাজ যারা করে তাদের জমির স্বত্বাধিকারী করার মাধ্যমে। এ ঐতিহ্যের ভিত্তিতে ইসলামের স্বর্ণযুগে ফকীহগণ পরিবেশ দূষিত করে এমন কর্মকাÐের বিরুদ্ধে আইন প্রণয়ন করেন। বিস্তারিত জানার জন্য মুনাওয়ার ইকবাল (২০০৫) দেখুন।
ইসলাম সকল প্রাকৃতিক সম্পদকে আমানত হিসেবে বিবেচনা করে এবং সেগুলোর ব্যক্তিগত মালিকানা নিষিদ্ধ করেছে। ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য প্রাকৃতিক সম্পদকে সংরক্ষন করার জন্য রাষ্ট দায়বদ্ধ থাকবে এবং তাকে অবশ্যই নিশ্চিত করতে হবে যেনো সকলেই সেগুলো থেকে উপকৃত হতে পারে। অনাগত মানব সন্তানদের প্রতি ইনসাফের জন্য প্রাকৃতিক সম্পদের সংরক্ষণ এবং তাদের ব্যবহার এমনভাবে প্রয়োজন যা সবার জন্য ন্যায্য। উদাহরণস্বরূপ, নবী (স.) আমাদের নির্দেশ দিয়েছেন যে, আমরা নদীর ধারে থাকলেও পানির কয়েক ফোঁটাও অপচয় না করতে। সেনাবাহিনীকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিলো যে, তারা গাছ পোড়াবে না বা কৃষি জমি ধ্বংস করবে না। পশু, উদ্ভিদ বা প্রাণীক‚লের আবাসস্থল ধ্বংস করাও অনুমোদিত নয়। বৃক্ষ ও ফুলগাছ লাগানোর উপর জোর দেওয়া হয়েছে এবং এগুলোকে সওয়াবের কাজ হিসেবে গণ্য করা হয়। একটি হাদীসে বলা হয়েছে যে, আপনি যদি বৃক্ষ রোপণরত থাকেন এবং এ অবস্থায় কিয়ামত এসে পড়ে, তাহলেও তা রোপণ করতে থাকুন। আদালত শুধু মানুষের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য নয়, বরং পশুদের প্রতিওÑএমনকি পশুদের উপর অত্যাচার করা বা শুধুমাত্র আনন্দের জন্য তাদের শিকার করা নিষিদ্ধ। সেবার জন্য ব্যবহৃত পশুদের সাথে অবশ্যই ন্যায্য আচরণ করা উচিত এবং তাদের আঘাত করা বা কঠোর শাস্তি দেওয়া উচিত নয়।
উপরন্তু, মুসলমানদেরকে বিলাসবহুল জীবনধারা অনুসরণ না করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। মজার বিষয় হলো, সাম্প্রতিক গবেষণায় দেখা গেছে অযথা খরচের মাধ্যমে অতিরিক্ত সুখ জীবনে সন্তুষ্টি বা সুস্থ অনুভ‚তির দিকে নিয়ে যায় না; সম্পদের অন্বেষণ মানুষকে মোহের দিকে নিয়ে যায়, যেমন কোরআন (৩:১৮৫) বলে।
মুসলিম সমাজের বর্তমান অবস্থার বিশদ পরিসংখ্যান এবং এর পরিবর্তে নীতিগত অগ্রাধিকারগুলো মনজার এবং কাহফ (২০০৩) তুলে ধরেছেন। মালয়েশিয়ার প্রেক্ষাপটে ইসলামী পদ্ধতির একটি বাস্তব চিত্র তুলে ধরেছেন এম. এ. চৌধুরী এবং এম. এস. সালেহ (১৯৯৩)। অনেক সহজ অর্থনীতির যুগে ইসলামী নীতিমালা প্রণয়নের ক্ষেত্রে ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গির দূরদৃষ্টি (বিচক্ষণতা ও বিজ্ঞতা) বিস্ময়কর।