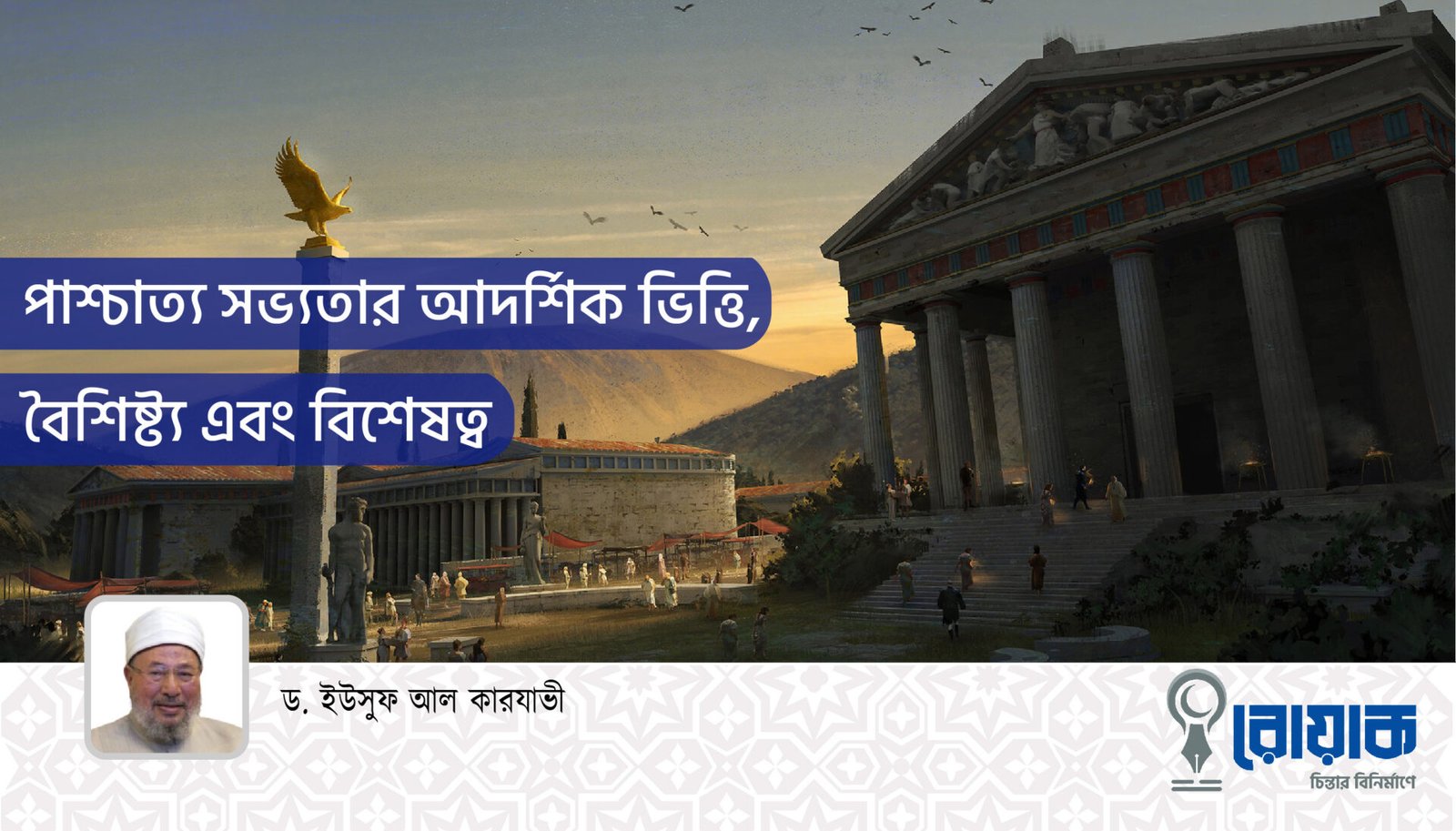পাশ্চাত্য সভ্যতার আদর্শিক ভিত্তি
পাশ্চাত্য সভ্যতার মূল ভিত্তি বা উৎস সম্পর্কে জানতে হলে গ্রিক ও রোমানদের সময়ে ফিরে যেতে হবে। কারণ পাশ্চাত্য সভ্যতার উৎস যা থেকে এ সভ্যতা তার নীতিমালাসমূহ আহরণ করে, তা জানতে না পারলে আমরা এ সভ্যতা সম্পর্কে সমালোচনামূলকভাবে জানতে সক্ষম হবো না। সেইসাথে পাশ্চাত্য মতাদর্শের উপাদান ও বিশেষত্বগুলোও আমাদেরকে ভালোভাবে উপলব্ধি করতে হবে।
পাশ্চাত্য মতাদর্শ মূলত ‘তাত্ত্বিক মতাদর্শ’, যা ইউরোপ এবং আমেরিকার সমসাময়িক পশ্চিমাদের মধ্যে বিরাজমান। এ মতাদর্শ বলতে আমরা পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষণভিত্তিক ‘বৈজ্ঞানিক মতাদর্শ’কে বুঝাই না; বরং আমরা সেই দার্শনিক মতাদর্শের কথা বলছি, যা ধর্ম ও জীবন, দুনিয়া ও মানুষ, জ্ঞান ও মূল্যবোধের প্রতি মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ন্ত্রণ করে। এ মতাদর্শের সাথে আরও সম্পৃক্ত রয়েছে মেটাফিজিক্যাল দর্শন (স্বীকার বা অস্বীকার যাই করুক না কেন), নানা ধরনের শিক্ষায়তনসমৃদ্ধ নৈতিক দর্শন এবং বিভিন্ন শাখা ও আদর্শসমৃদ্ধ সামাজিক দর্শন।
পাশ্চাত্য মতাদর্শ উদারনৈতিক বা সামাজিক, পুঁজিবাদী বা সাম্রাজ্যবাদী যাই হোক না কেন, এটি মূলত সকল মৌলিক বৈশিষ্ট্য ও বিশেষত্বের দিক থেকে পুরোপুরি পশ্চিমা, যদিও এর প্রয়োগ বা শাখা-প্রশাখায় ভিন্নতা রয়েছে।
আরোহ-প্রণালীর (Inductive) ভিত্তিতে গড়ে উঠা বৈজ্ঞানিক মতাদর্শ নিয়ে আমাদের কোনো আপত্তি নেই। প্রকৃতপক্ষে, এ মতাদর্শের মৌলিক বিষয়গুলো ইসলামী সভ্যতা থেকে উদ্ভূত, যা একই মেথডোলজির উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছিলো এবং ইসলামী সভ্যতা বিভিন্ন প্রেক্ষিতে এর ব্যবহারের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ সফলতার পরিচয় দিয়েছিলো। মুসলিম আলেমগণ এটিকে কোরআনী মেথডোলজি হিসেবে অভিহিত করেছেন, এবং কয়েকজন সৎ চিন্তার অধিকারী পশ্চিমা পণ্ডিত, বিজ্ঞান ও সভ্যতার ইতিহাস বিশেষজ্ঞগণ মুসলমানদের অবদান এবং অগ্রগণ্যতা সম্পর্কে এ সাক্ষ্য দিয়েছেন যে, পশ্চিমারা তাদের থেকেই এ মেথডোলজি অর্জন করেছে। রিভোলেট, জর্জ সার্টন, গুস্তাভ লে বন তাদের অন্যতম।
পাশ্চাত্য মতাদর্শের বৈশিষ্ট্য এবং বিশেষত্ব
পাশ্চাত্য মতাদর্শের নিজস্ব কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে যা এটিকে প্রাচ্যের মতাদর্শ থেকে সম্পূর্ণরূপে পৃথক করেছে এবং আরবীয় ও ইসলামী প্রাচ্যের মতাদর্শ থেকে কিছু ক্ষেত্রে পৃথক করেছে। পাশ্চাত্যের মূলভিত্তি প্রথমে এসেছিলো গ্রিকদের থেকে, তারপর এসেছিলো রোমানদের থেকে, যতদিন না এটি সমসাময়িক ইউরোপ ও আমেরিকায় উপনীত হয়েছিলো। মধ্যযুগের সংগ্রাম ও সংঘাতকালীন সময়ের অনেক ঐতিহাসিক ঘটনা এ মতাদর্শকে প্রভাবিত করেছিলো, যার ছাপ এখনো বিদ্যমান রয়েছে।
◆ পাশ্চাত্য মতাদর্শের বৈশিষ্ট্য এবং বিশেষত্বগুলো হলো,
১. উলুহিয়্যাত সম্পর্কে অস্পষ্ট ধারণা :
পাশ্চাত্য মতাদর্শের প্রথম বৈশিষ্ট্য হলো উলুহিয়্যাত বা আল্লাহর অস্তিত্ব সম্পর্কে অস্পষ্ট ধারণা। এটি শুধুমাত্র একটি অস্পষ্ট দৃষ্টিভঙ্গিই নয়, বরং এটি অজ্ঞতা ও বিভ্রান্তি দ্বারা পরিবেষ্টিত একটি সমস্যাপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি। প্রকৃত অর্থে, পাশ্চাত্য সভ্যতায় গড়ে ওঠা জ্ঞান দিয়ে কেউ কখনো এ মহাবিশ্বের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহকে সঠিকভাবে চিনতে পারেনি এবং কখনো তার প্রতি সঠিক বিশ্বাসের পথে পরিচালিত হতে পারেনি। পাশ্চাত্য কখনোই সর্বজ্ঞ, মহাজ্ঞানী, সর্বশক্তিমান এবং দয়াময় আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে সত্যিকারার্থে জানতে পারেনি। এর কারণ হলো পথনির্দেশক নবুয়ত ও ওহী সম্পর্কে সরাসরি না জানা। আর এ অজ্ঞতার কারণে এ সভ্যতা প্রথম সূচনাকারীকে (আল্লাহ) খোঁজার জন্য একাকী নিজস্ব পথে চলছিলো, কিন্তু এক পর্যায়ে হোঁচট খায় এবং পথ হারিয়ে ফেলে।
দর্শনের ইতিহাসে যে সকল পশ্চিমা দার্শনিককে ধর্মতত্ত্ববিদ হিসেবে আখ্যা দেওয়া হয়, অর্থাৎ যারা ইলাহে বিশ্বাসী ছিলেন, ইলাহকে অগ্রাহ্য করতে এবং নাস্তিকতাকে গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিলেন, তাদেরও ইলাহ সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা ছিলো না। যেমন,সক্রেটিস, প্লেটো ও এরিস্টটল।
এরিস্টটলের মতে, ইলাহ কে ছিলো? যে ইলাহকে আমরা জানি, তিনিই কি সেই ইলাহ? যিনি সকল কিছুর সৃষ্টিকারী; সকল জীবের রিযিক সরবরাহকারী; যিনি সকল কিছু পরিচালনা করেন; যিনি সর্বজ্ঞ, অতীতে যা ঘটেছে, বর্তমানে যা ঘটছে, ভবিষ্যতে যা ঘটবে তার সব যিনি জানেন! এরিস্টটলের ইলাহ কি যা চায় তাই করতে পারেন? তিনিই কি সর্বশক্তিমান? নাকি আমরা যে ইলাহকে জানি, তিনি এরিস্টটলের ইলাহ থেকে আলাদা?
উইল ডুরান্ট ইলাহ সম্পর্কে এরিস্টটলের ধারণা প্রসঙ্গে বলেছেন, “এরিস্টটলের ইলাহ কোনো কাজ করে না, তার কোনো ইচ্ছা বা উদ্দেশ্য নেই। সে পরিপূর্ণ, তাই তার কোনো ইচ্ছা থাকতে পারে না এবং সে কোনো কাজও করতে পারে না। তার কাজ শুধু ধ্যান করা। এরিস্টটলের ইলাহ দরিদ্র। সে শাসক, কিন্তু শাসন করে না।”
যদি এরিস্টটলের ইলাহ দরিদ্র হয়, কারণ তিনি মহাবিশ্বের সমস্যার সমাধান অথবা মহাবিশ্বের সাথে নিজেকে সংযোজন করতে পারেন না, তবে প্লেটোর ইলাহ-এর (যিনি নিউ প্লেটোজমের প্রবক্তা) অবস্থা আরও করুণ। সে কোনো কিছু নিয়েই চিন্তা করতে পারে না, এমনকি নিজেকে নিয়েও না!
২. বস্তুবাদী প্রবণতা :
বস্তুবাদী প্রবণতা বলতে আমরা এমন একটা বিশ্বাসকে বুঝি, যা মনে করে, শুধুমাত্র যুক্তিই এ মহাবিশ্ব, জ্ঞান এবং আচরণের একমাত্র ব্যাখ্যাকারী। এ প্রবণতা সকল অদৃশ্য বিষয় এবং ইন্দ্রিয়শক্তি দ্বারা ব্যাখ্যা করা যায় না এমন প্রতিটি বিষয়কে অস্বীকার করে। এটি বিশ্বাস করে না যে, মহাবিশ্বের কোনো স্রষ্টা থাকতে পারে এবং স্রষ্টা প্রদত্ত নবীরা শ্বাশত জীবন বিধান নিয়ে আগমন করতে পারে। এটি মানুষের অনন্ত জীবনে বিশ্বাসী নয়, এমনকি পরকালেও বিশ্বাসী নয়। দৃষ্টিসীমার বাইরে, পৃথিবীর সকল কিছুর অগোচরেও যে একটি গায়েবী দুনিয়া আছে তাও বস্তুবাদী দর্শনে অনুপস্থিত। এটি দুনিয়াবি ভোগবিলাসের ঊর্ধ্বে উঠে আদর্শিক কোনো মূল্যবোধ লালন করতে পারে না। আর এর কারণ হলো এসবের কোনো কিছুই ইন্দ্রিয়শক্তি দ্বারা বোঝা সম্ভব নয় এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে প্রমাণিত নয়।
এককথায় পাশ্চাত্য মতাদর্শ মূলত বস্তুবাদী, যা আধ্যাত্মিকতাকে অবজ্ঞার চোখে দেখে এবং নৈতিকতা ও আদর্শের যথাযথ মূল্যায়ন করে না। যদিও পশ্চিমাদের অনেকেই আধ্যাত্মিকতা ও নৈতিকতায় বিশ্বাসী, তবুও আমরা তাদেরকে তাদের মতাদর্শ এবং সংখ্যাগরিষ্ঠতার দিক থেকে বিচার করবো। আমরা আমাদের বিচারের মাপকাঠিতে সংখ্যালঘু কোনো গোষ্ঠীকে গ্রহণ করতে পারি না।
সাধারণভাবেই এটি বলা যায় যে, বর্তমানে পাশ্চাত্যের একমাত্র ধর্ম হলো বস্তুবাদ। কেউ কেউ বাহ্যিক কিছু বিষয়ের উপর লক্ষ্য রেখে হয়তো এটি প্রমাণ করার চেষ্টা করবে যে, পাশ্চাত্যের ধর্ম হলো খ্রিষ্ট ধর্ম। এমনকি তারা এটিও দাবি করে যে, ফ্রান্স ক্যাথলিক মতবাদে বিশ্বাসী এবং তারা নিজেদেরকে পৃথিবীর সকল ক্যাথলিকদের রক্ষাকারী বলে মনে করে। অন্যদিকে ইংল্যান্ড নিজেদেরকে প্রোটেস্ট্যান্ট মতবাদের রক্ষক হিসেবে দাবি করতো, কিন্তু বর্তমানে আমেরিকা উত্তরাধিকার সূত্রে তা পেয়ে গেছে। অন্যদিকে জার্মানি, ফ্রান্স, ইতালি এবং বেলজিয়ামের অনেক ক্যাথলিক দল রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল করেছে। তাহলে কীভাবে আমরা এটি ধরে নিতে পারি যে, পাশ্চাত্যের ধর্মীয় ভিত্তি হলো খ্রিষ্টবাদ!
বর্তমানে পাশ্চাত্যের খ্রিষ্টান ধর্ম শুধুমাত্র গলায় নির্দিষ্ট প্রতীক পরিধান করা, ক্রুশের চারপাশে জড়ো হয়ে প্রার্থনা করা, সপ্তাহান্তে গির্জায় পিকনিক করার মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছে। তাদের মাঝে সেই মূল্যবোধের উপস্থিতি নেই যা তারা বিশ্বাস করে।
এক্ষেত্রে আমরা সংখ্যাগরিষ্ঠদের কথা বলছি, এমন কারো কথা বলছি না যে পাশ্চাত্যের সামাজিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম বলে বিবেচিত হয়। যদি বাস্তবে আপনি পাশ্চাত্যের সমসাময়িক কোনো ব্যক্তিকে গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করেন, তাহলে আপনি তার ভেতরে এমন এক মানুষকে খুঁজে পাবেন, যে বস্তুবাদ ছাড়া অন্য কোনো আদর্শ বা ধর্ম এবং উপযোগবাদ ছাড়া অন্য কোনো মতবাদের অনুসারী নয়।
ইসলাম গ্রহণকারী অস্ট্রিয় নাগরিক মুহাম্মদ আসাদ (আগে যিনি লিওপোল্ড উইস নামে পরিচিত ছিলেন) তার Islam in the middle of the Road বইয়ে বলেছেন, “সমসাময়িক ইউরোপীয়রা জীবনের লক্ষ্যকে ব্যবহারিক গুরুত্বের কোনো বিষয় হিসেবে বিবেচনা করে না। তারা প্রকৃত জীবনবোধ এবং জীবনের উদ্দেশ্যকে পেছনে ফেলে এসেছে। ধর্মীয় মতাদর্শ একটি বৃহৎ নৈতিক মূল্যবোধের বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠে, যা আমরা মানুষরা অনুসরণ করতে বাধ্য। কিন্তু আধুনিক পাশ্চাত্য সভ্যতা এটিকে অস্বীকার করে। তাদের মতে অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং জাতীয় মূল্যবোধ ছাড়া অন্য কোনো মূল্যবোধের কাছে নতি স্বীকার করার প্রয়োজন নেই। এ সভ্যতায় প্রভুর কোনো আধ্যাত্মিক মূল্য নেই, কারণ বিলাসিতাই তাদের প্রভু!”
অতঃপর মুহাম্মদ আসাদ পাশ্চাত্য সভ্যতার বিরোধিতার কারণকে দুটি প্রধান ভাগে বিভক্ত করে বিশ্লেষণ করেছেন।
প্রথমটি হলো, এ সভ্যতা মানুষের জীবন এবং এর বিষয়গত মূল্যের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ বস্তুবাদী প্রবণতা সমৃদ্ধ রোমান সভ্যতার উত্তরাধিকারী।
দ্বিতীয়টি হলো, পার্থিব জীবনকে অবজ্ঞার চোখে দেখা এবং মানুষের স্বভাবসুলভ ইচ্ছাগুলোকে দমিয়ে রাখার কারণে খ্রিষ্টান ধর্মের বিরুদ্ধে মানব প্রকৃতির বিদ্রোহ।
তিনি রোমান সভ্যতাকে (যাকে বলা হয় পাশ্চাত্য সভ্যতার মা) আরও সমালোচনামূলকভাবে ব্যাখ্যা করার ক্ষেত্রে বলেন, “পাশ্চাত্য সভ্যতা প্রকাশ্যে এবং দৃঢ়ভাবে স্রষ্টার অস্তিত্বকে অস্বীকার করে না, কিন্তু এটি তার সমসাময়িক আদর্শিক পদ্ধতিতে স্রষ্টার মূল্য উপলব্ধি করতে পারে না। আধুনিক ইউরোপীয়রা কেবল সেই ব্যবহারিক চিন্তাধারাগুলোকেই বিবেচনা করে থাকে যা পরীক্ষামূলক বিজ্ঞান ক্ষেত্রের মধ্যে পড়ে, অথবা যা মানুষের সামাজিক সম্পর্ককে উল্লেখযোগ্যভাবে প্রভাবিত করবে বলে আশা করা হয়। যেহেতু স্রষ্টা এ ধারণার আওতায় পড়েন না, তাই ইউরোপীয় মনন স্রষ্টার ধারণাকে তাদের ব্যবহারিক বিবেচনার বাইরে রাখে।”
মুহাম্মদ আসাদ এ কথা অস্বীকার করেননি যে, পাশ্চাত্যের কিছু সংখ্যক ধর্মপ্রাণ মানুষ আছেন। কিন্তু তারা কেউই বস্তুবাদের এ ঢেউকে প্রতিহত করতে পারেননি। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, “আধুনিক ইউরোপীয়রা বিশ্বাস করে যে, জীবনকে সহজ থেকে সহজতর করা ছাড়া জীবনের আর কোনো উদ্দেশ্য নেই। এ ধর্মের উপাসনালয় হলো ফ্যাক্টরি, সিনেমা, বৈজ্ঞানিক গবেষণাগার, ডিস্কো, ইলেকট্রিক জেনারেটর। আর এ ধর্মের পুরোহিত হলো ইঞ্জিনিয়ার, অর্থনীতিবিদ, অভিনেতারা। আর এর অনিবার্য ফলাফল হলো ক্ষমতা ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য লাভের জন্য কঠোর প্রচেষ্টা চালানো। অথচ এটি শুধুমাত্র পরস্পর বিরোধী দল সৃষ্টি করার মাধ্যমেই সম্ভব, যে দলগুলো উন্নত সামরিক শক্তিসম্পন্ন হবে এবং নিজের স্বার্থের জন্য একে অপরকে ধ্বংস করতে উন্মুখ থাকবে। আর সাংস্কৃতিক দিক বিবেচনা করলে দেখা যায়, এ মতাদর্শ এমন সব মানুষ গড়ে তুলছে, যাদের নৈতিক দর্শন ব্যবহারিক মূল্য আছে এমন বিষয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ। এছাড়াও এ মানুষদের দৃষ্টিতে ভালো এবং মন্দের মধ্যে চূড়ান্ত পার্থক্য হলো ব্যবহারিক অগ্রগতি, এর বেশি কিছু নয়।”
আমেরিকার বিখ্যাত সাংবাদিক জন জান্টার তার Inside Europe বইয়ে ইউরোপীয়দের এ মানসিকতার সারাংশ হিসেবে বলেন, “ব্রিটিশরা সপ্তাহে ছয়দিন ইংল্যান্ড ব্যাংকে পূজা করে, আর সপ্তম দিনে তারা গির্জায় যায়!”
এ সমীক্ষাগুলো অনেক পুরাতন, বর্তমান অবস্থা আরও শোচনীয়। বর্তমান পরিসংখ্যান মতে, রবিবারেও পশ্চিমাদের মাত্র ৫% লোক গির্জায় যায়, যা কোনোভাবেই ধর্মীয় অনুরাগের প্রকৃত পরিচয় বহন করে না।
৩. ধর্মনিরপেক্ষ প্রবণতা :
ধর্মনিরপেক্ষ প্রবণতা পূর্ববর্তী দুটি বৈশিষ্ট্যের প্রাকৃতিক ফলাফল। এ প্রবণতার দ্বারা ধর্ম এবং রাষ্ট্র, অর্থাৎ ধর্ম এবং সামাজিক জীবনের মধ্যকার বিচ্ছিন্নতাকে বুঝানো হয়। একজন পশ্চিমা ব্যক্তির মতে ধর্ম হলো মানুষ এবং ঈশ্বরের মধ্যকার একটি সম্পর্ক, যা শুধুমাত্র তার মনে অবস্থিত। ধর্ম যদি প্রকাশিত হয়, তবে তার মন্দির ও গীর্জাগুলোর প্রাচীর অতিক্রম করা উচিত নয়; আইন মানা এবং দায়িত্ব-কর্তব্য পালনের মাধ্যমে জীবন গড়ার ক্ষেত্রে প্রভাব রাখা উচিত নয়, অথবা সমাজকে নিয়ন্ত্রণকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ, যেমন শিক্ষা, সংস্কৃতি, গণমাধ্যম, ব্যবস্থাপনা, অর্থনীতি, রাজনীতি, আইন ইত্যাদির উপর চেপে বসা উচিত নয়।
পশ্চিমাদের এমন বিশ্বাসের কারণ হলো নিজেদেরকে ঈশ্বরের ইচ্ছার প্রতীক হিসেবে দাবিকারী গির্জা এবং যাজকদের দ্বারা পরিচালিত ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর সাথে তাদের তীব্র লড়াই। যাজকরা এটিও দাবি করতো যে, তাদের ইচ্ছাই ধর্ম, তাদের প্রতি অনুগত হওয়া প্রার্থনার অন্তর্ভুক্ত এবং তাদের অবাধ্য হওয়া পাপের কাজ।
দুর্ভাগ্যবশত তাদের চিন্তা এবং মতাদর্শসমূহ, যেগুলোকে তারা খোদায়ী ধর্ম মনে করতো, সেগুলো মূলত বিজ্ঞানের বিপরীতে কুসংস্কার, স্বাধীনতার বিপরীতে কঠোরতা, আদালতের বিপরীতে অবিচার ও জুলুম এবং আলোর বিপরীতে অন্ধকারকে সমর্থন করে।
গির্জা বিজ্ঞানকে তাড়াতে, চিন্তাকে বাধা দিতে, উদ্ভাবনকে প্রতিহত করতে এবং সকল নবসৃষ্ট বিষয়ের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে Courts of Inquisition স্থাপন করেছিলো। গির্জার প্রতিনিধিরা বিজ্ঞানী, চিন্তাবিদ, উদ্ভাবকদেরকে এমনভাবে নির্যাতন করেছিলো, মানবতার ইতিহাসে যা ছিলো নজিরবিহীন। কেননা তারা তাদেরকে হত্যা করে মৃতদেহ পুড়িয়ে ফেলতো।
অতঃপর যখন পশ্চিমা খ্রিষ্টানরা প্রাচ্যের মুসলিম বিশ্বের সংস্পর্শে এসেছিলো, তখন তারা তাদের অধিকার রক্ষার জন্য সোচ্চার হয়েছিলো, তাদের পরিচালকদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিলো এবং তাদেরকে পার্থিব জীবন, বিজ্ঞান ও চিন্তা থেকে দূরে সরিয়ে রাখা ধর্মকে প্রত্যাখ্যান করেছিলো। তারা গির্জা ও যাজকদের সেই ধর্মকে প্রত্যাখ্যান করেছিলো, যা ক্ষতিকর সিদ্ধান্ত দেয় এবং প্রভুর ক্ষমা প্রাপ্তির বিষয়টিকে নিজেদের ইচ্ছাধীন করে রাখে।
এ নতুন পাশ্চাত্য চিন্তা ধর্মকে প্রত্যাখ্যান করেছিলো যা তাদেরকে বন্দী করে রেখেছিলো, ধর্মকে শুধুমাত্র মনে সীমাবদ্ধ রাখার অনুমতি দিয়েছিলো এবং ধর্মের বহিঃপ্রকাশের ক্ষেত্রকে কেবলমাত্র রবিবারে গীর্জায় প্রার্থনার মধ্যে সীমাবদ্ধ করে দিয়েছিলো।
আর ধর্মকে তার সিংহাসন ছুঁড়ে ফেলে, জীবন পরিচালনার অবস্থান থেকে বিচ্ছিন্ন করার পরেই পশ্চিমারা ঘুমন্ত অবস্থা থেকে জাগতে শুরু করেছিলো, পিছিয়ে পড়া অবস্থান থেকে অগ্রসর হয়েছিলো, দরিদ্র অবস্থান থেকে ধনী হয়েছিলো, দুর্বল অবস্থান থেকে শক্তিশালী হয়ে উঠেছিলো। এ উন্নতির ফলাফলস্বরূপ এ ব্যাপারে তাদের বিশ্বাস মজবুত হয়েছিলো যে, রাষ্ট্র ও সমাজের নেতৃত্বে ধর্মের কোনো অবকাশ নেই।
বাইবেল নিজেই এটিকে সমর্থন করে। যীশু খ্রিষ্ট বাইবেলে বলেছেন, “সিজারের যা কিছু আছে তা সিজারকে দাও, আর যা কিছু ঈশ্বরের তা ঈশ্বরকে দাও।”
এটির মর্মার্থ হলো, যীশু জীবনকে দুই ভাগে ভাগ করেছেন। অর্ধেক হলো রাষ্ট্রের, যার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে ‘সিজার’ (রোমান সম্রাটদের পদবী)-এর মাধ্যমে, আর অর্ধেক হলো ধর্মের, যা দ্বারা বোঝানো হয়েছে ‘ঈশ্বর’-এর মাধ্যমে।
সিজার ও ঈশ্বর বা ধর্ম ও রাষ্ট্রের মধ্যে এ পৃথকীকরণ পাশ্চাত্য মতাদর্শের অন্যতম মৌলিক বৈশিষ্ট্য।
৪. সংগ্রাম :
পাশ্চাত্য সভ্যতা মূলত সংগ্রাম বা লড়াইয়ের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। এ সভ্যতা শান্তি, নিরাপত্তা, ভালোবাসা চিনে না, জানে না। সংগ্রাম বা লড়াই পশ্চিমা জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রের সাথেই নানা রূপে এবং নানা ধরনের অস্ত্র ও উপায়-উপকরণের সমন্বয়ে ওতপ্রোতভাবে জড়িত।
বিভিন্নভাবে, বিভিন্ন কারণে পাশ্চাত্য সভ্যতার মানুষেরা অনবরত এসব সংগ্রামে লিপ্ত।
এ সংগ্রাম একজন মানুষ ও তার নিজস্ব সত্তার। পশ্চিমা মানুষদেরকে তাদের ফিতরাতের সাথে সংগ্রাম করতে হয়, যে ফিতরাত মানুষের জন্মগত ও আল্লাহ প্রদত্ত। কেউ যদি খ্রিষ্টান ধর্মের নির্দেশিত উপায়ে জীবন যাপন করতে চায়, তবে তাকে যৌন চাহিদাকে একটি নোংরা কাজ হিসেবে বিবেচনা করতে হবে, ধন-সম্পদ, অর্থকে প্রত্যাখ্যান করতে হবে। কারণ তাদের ধর্ম বলে, “ধনী ব্যক্তিরা ততক্ষণ পর্যন্ত স্বর্গে প্রবেশ করতে পারবে না, যতক্ষণ না একটি উট সূচের মাথা দিয়ে প্রবেশ করতে পারবে।” নিজেকে আল্লাহ প্রদত্ত নিয়ামতসমূহ থেকে বঞ্চিত করতে হবে, বঞ্চিত করতে হবে সেই সকল সুযোগ-সুবিধা থেকে, যা মহান আল্লাহ শুধুমাত্র তাদের সেবার জন্য সৃষ্টি করেছেন। তাকে অবশ্যই অন্যের দুর্ব্যবহার সহ্য করতে হবে, উপরন্তু কেউ তার ডান গালে চড় মারলে বাম গাল এগিয়ে দিতে হবে। যদি সে এমনটি না করতে পারে, তবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই যা ঘটে তা হলো, তার আদর্শ এবং বাস্তবিক জীবন-যাপনের মধ্যে একটি চিরন্তন সংগ্রামের জটিলতা সৃষ্টি হয়।
এ সংগ্রাম মানুষের সাথে প্রকৃতির। পাশ্চাত্য সভ্যতার মানুষেরা প্রকৃতির সাথে অনবরত সংগ্রামে লিপ্ত থাকে। কারণ তারা প্রকৃতিকে শত্রু ভাবে এবং মনে করে যে, প্রকৃতির উপর কর্তৃত্ব খাটাতে হবে। আর তারা এ বিষয়টিকে ‘প্রকৃতির বিজয়’ বলে অভিহিত করে, নামের মাধ্যমেই যে অভিব্যক্তির তীব্রতা প্রকাশ পায়।
অপরদিকে ইসলাম বলে, প্রকৃতিতে যা কিছু রয়েছে, সবই মানুষের উপকারের জন্য।
মহান আল্লাহ বলেন,
اَلَمۡ تَرَوۡا اَنَّ اللّٰهَ سَخَّرَ لَكُمۡ مَّا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الۡاَرۡضِ وَاَسۡبَغَ عَلَيۡكُمۡ نِعَمَهٗ ظَاهِرَةً وَّبَاطِنَةً
অর্থ : “তোমরা কি দেখো না, আকাশসমূহ এবং পৃথিবীতে যা কিছু আছে, সবই আল্লাহ তোমাদের অধীন করে দিয়েছেন। আর তোমাদের জন্য তার নিয়ামত পূর্ণ করেছেন প্রকাশ্যভাবে এবং অপ্রকাশ্যভাবে।”
(সূরা লোকমান : ২০)
এ বিষয়টি রাসূল (স.)-এর কথায়ও খুব সুন্দরভাবে প্রকাশিত হয়েছে, যখন তিনি উহুদ পর্বত সম্পর্কে মন্তব্য করেছিলেন।
তিনি বলেছিলেন,
“এটি এমন একটি পর্বত যা আমাদেরকে ভালোবাসে এবং আমরাও তাকে ভালোবাসি।” (সহীহ বুখারী)
এ সংগ্রাম এক মানুষের সাথে অপর মানুষের। পরস্পরের বিপরীতমুখী চাহিদা ও স্বার্থ, বিশেষত বিরাজমান ব্যক্তিত্ববাদ, উপযোগবাদ এবং হবসের একটি উক্তির ব্যাপক প্রভাবের ফলে এটি সৃষ্টি হয়েছে। হবস বলেছিলেন, “মানুষ অন্য মানুষদের ক্ষেত্রে নেকড়ের মতো।” ফলস্বরূপ প্রত্যেকেই বলতে শুরু করলো, “একমাত্র আমিই গুরুত্বপূর্ণ, দুনিয়া জাহান্নামে যাক!”
এ সংগ্রাম বিভিন্ন শ্রেণি ও গোষ্ঠীর। বিশেষত প্রত্যেক গোষ্ঠীর একচেটিয়াভাবে সুযোগ-সুবিধা ভোগ করার আকাক্সক্ষা, অন্যান্য গোষ্ঠীর উপর নিপীড়ন এবং অন্য সবকিছুকে তুচ্ছ করার ফলে এটি সৃষ্টি হয়েছে।
এ সংগ্রাম জাতি ও সম্প্রদায়সমূহের। বিশেষত উগ্র জাতীয়তাবাদ চর্চা এবং প্রত্যেক জাতির নিজেদেরকে শ্রেষ্ঠ ভাবার প্রবণতার কারণে এটি সৃষ্টি হয়েছে। এসবের ফলশ্রুতিতে সীমান্তবর্তী দেশসমূহের মধ্যে এবং বিশ্বব্যাপী যুদ্ধের সূত্রপাত ঘটেছে। শেতাঙ্গ এবং কৃষ্ণাঙ্গদের মধ্যে আমরা এখনো এর প্রভাব দেখতে পাই।
এ সংগ্রাম প্রতিষ্ঠানসমূহেরও। যেমন,গির্জা ও রাষ্ট্রের মধ্যকার সংগ্রাম, যা ধর্মনিরপেক্ষতা প্রবণতার অংশে আলোচনা করা হয়েছে।
এ সংগ্রাম মানুষ এবং সৃষ্টিকর্তার। এটিই সবচেয়ে নিকৃষ্ট সংগ্রাম, যা নিম্নোক্ত দুটি মূল উৎস থেকে সৃষ্টি হয়েছে,
১. গ্রীকদের পৌত্তলিকতা এবং তাদের দেব-দেবীরা, যারা হিংসা, ধ্বংস ও হত্যায় অভ্যস্ত ছিলো।
২. ওল্ড টেস্টামেন্ট, যা ঈশ্বরকে ঈর্ষান্বিত এবং ক্রুদ্ধ এক সত্তা হিসেবে মনে করে। কারণ ওল্ড টেস্টামেন্ট অনুযায়ী ঈশ্বর আদমকে সৃষ্টি করেন, তারপর তিনি তাকে নিয়েই ভীতি অনুভব করেন, এমনকি তিনি এ কথা ভেবে ভয় পান যে, আদম তার সাথে জ্ঞান ও অবিনশ্বরতা নিয়ে প্রতিযোগিতা করবে, আর এজন্যই তিনি আদমকে বৃক্ষ থেকে ফল খেতে নিষেধ করেছিলেন।
৫. অন্যের উপর শ্রেষ্ঠত্ববোধ :
অন্যের উপর শ্রেষ্ঠত্ববোধও পাশ্চাত্য মতাদর্শের বৈশিষ্ট্যগুলোর মধ্যে অন্যতম। পশ্চিমারা মনে করে যে, তারাই সর্বোত্তম জাতি, তাদের শরীরেই পবিত্র রক্ত বহমান এবং তাদেরকে নেতৃত্ব ও শাসন করার জন্যই সৃষ্টি করা হয়েছে। আর অন্যদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে তাদের অধীনস্থ ও শাসনাধীন থাকার জন্য।
আর এ কারণেই তাদের মতাদর্শে ‘জাতিগত শ্রেষ্ঠত্ববোধ’ তত্ত্ব প্রচলিত। ‘মানুষ সমান নয়’,এ ধারণাটি ইসলামী বিশ্বাসের বিপরীত। মানুষ সবাই সমান, কারণ সব মানুষই এক আদমের বংশধর এবং এক আল্লাহর বান্দা। অথচ পশ্চিমারা বিশ্বাস করে যে, মানুষ সৃষ্টির বৈশিষ্ট্য অনুসারে পরস্পর থেকে ভিন্ন এবং এক্ষেত্রে বুদ্ধিমত্তা ও ক্ষমতার দিক থেকে আর্য জাতিই শ্রেষ্ঠ।
তাদের এ তত্ত্ব বৈজ্ঞানিকভাবে ভুল প্রমাণিত হয়েছে, কারণ বিজ্ঞান সৃষ্টি ও ফিতরাতগত কারণে এক জাতির অন্য জাতির তুলনায় শ্রেষ্ঠ হওয়ার কোনো প্রমাণ খুঁজে পায়নি, বরং এটি হয় পরিবেশ এবং পারিপার্শ্বিকতার কারণে।
পূর্ববর্তী সময়ে সভ্যতার মশাল প্রাচ্যের জাতিসমূহ, যেমন ফেরাউনী, ভারতীয়, চীনা ইত্যাদি সভ্যতার হাতে ছিলো। তারপর তা গ্রীক এবং রোমান সভ্যতার সময়কালে পশ্চিমাদের হাতে চলে যায়, পরবর্তীতে ইসলামী আরবীয় সভ্যতার সময়কালে তা আবার প্রাচ্যে চলে আসে। কিন্তু বর্তমানে তা আবার পশ্চিমাদের হাতে, যা আন্দালুস ও সিসিলির মধ্য দিয়ে পশ্চিমাদের ইসলামী প্রাচ্যের সংস্পর্শে আসা এবং ক্রুসেড এর ফলাফল।
সভ্যতার মশাল পাশ্চাত্যের হাত থেকে আবার পাচ্যে নিয়ে আসার এখনি সময়, কারণ পাশ্চাত্য সভ্যতা বিশ্ব পরিচালনা এবং শান্তি আনয়নে ব্যর্থ হয়েছে।
জাতিগত শ্রেষ্ঠত্ববোধ তত্ত্বটি বৈজ্ঞানিকভাবে ব্যর্থ প্রমাণিত হলেও মনস্তাত্ত্বিকভাবে এখনো প্রচলিত, যা পশ্চিমাদের পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রকে প্রভাবিত করছে। বিজ্ঞানে নোবেল বিজয়ী আ্যলেক্স ক্যারেল এর মতো মহান পণ্ডিতও শেতাঙ্গদের শ্রেষ্ঠত্বে বিশ্বাসী, যা প্রকৃতপক্ষেই বিস্ময়কর!
এ কারণে বর্তমান সময়েও আমরা দেখি, ইউরোপীয়রা বিশ্বাস করে যে, ইউরোপ পৃথিবীর কেন্দ্র, ইউরোপ থেকেই ইতিহাসের শুরু এবং শেষও হবে ইউরোপেই। তাদের বিশ্বাস প্রাচীন যুগ, মধ্য যুগ এবং আধুনিক যুগের ইতিহাস শুধুই ইউরোপের ইতিহাস এবং তাদের সভ্যতাই একমাত্র সভ্যতা।
আর এ প্রবণতা ইউরোপীয়রা রোমানদের থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছিলো। রোমানরা বিশ্ববাসীদেরকে দুই ভাগে বিভক্ত করেছিলো। যথা,রোমান ও বার্বার। সাম্প্রতিক ইতিহাসেও আমরা এর যথেষ্ট উদাহরণ লক্ষ্য করি। হিটলার বলেছিলেন, “সবার উপরে জার্মানি,” অনুরূপ মুসোলিনি বলেছিলেন, “ইতালি সবার উপরে।” ব্রিটিশরা স্লোগান তুলেছিলো, “ব্রিটেনই বিশ্ব শাসন করবে।”
আর তারা প্রত্যেকেই বনী ইসরাইলের মতো, যারা জাতিগত বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করে বলেছিলো, তারাই আল্লাহর নিকটবর্তী মানুষ।
এসবই হলো পাশ্চ্যত্য মতাদর্শের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য, যা পশ্চিমাদের মুয়ামালাত ও আচার-আচরণকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করেছে। এ মতাদর্শের কিছু ভালো দিক পরিলক্ষিত হলেও অনেক ত্রুটিপূর্ণ এবং তিক্ত দিক রয়েছে। বর্তমানে পশ্চিমারা নিজেরাই বস্তুবাদী সভ্যতার এ খারাপ প্রভাবগুলো অনুধাবন করতে পারছে, যার ফলে তারা পাশ্চাত্যের গ্রহণকৃত মতাদর্শগুলো এড়িয়ে যেতে শুরু করেছে এবং ভবিষ্যতে ধর্মের প্রত্যাবর্তনের আশা প্রকাশ করছে।
অনুবাদঃ কাজী সালমা বিনতে সলিম।