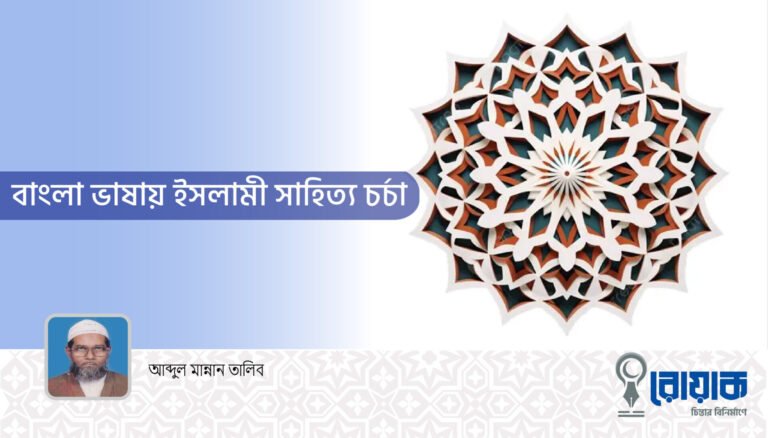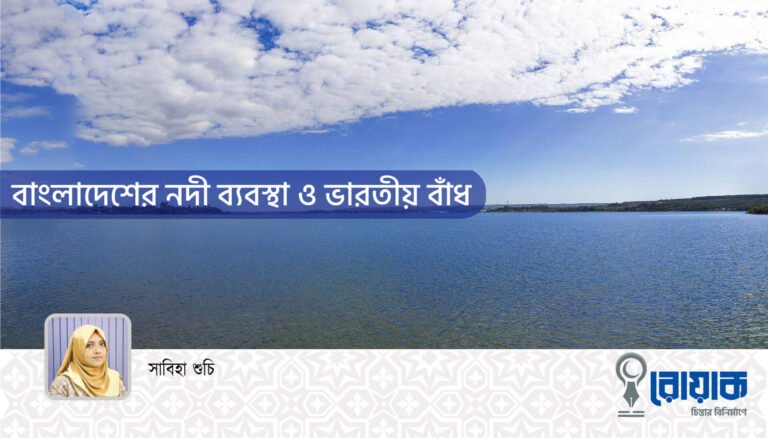আমার বন্ধুদের, অবশ্যই উচিত হবে না, আজ আমার কাছ থেকে একটা জ্ঞানগর্ভ ও সুসম্পন্ন বক্তৃতা আশা করা। কারণ, বক্তৃতার বিষয়বস্তুর উপর চিন্তা করার জন্য আমি ঘণ্টা দুয়েকের বেশি সময় পাইনি। কিন্তু ঠিক এ প্রসঙ্গে কিছুদিন আগে আমি বিশ্ববিদ্যালয়ে একটা বক্তৃতা দিয়েছিলাম। আশা করি সেখানে বলা কিছু কথা আজও মনে করতে পারবো এবং আপনাদের সামনে তা-ই উপস্থাপন করবো।
টিবর মেনডে হচ্ছেন ইদানীংকালের একজন শ্রেষ্ঠ চিন্তাবিদ। তার গবেষণার বিষয় ছিলো ‘তৃতীয় বিশ্ব’। হাঙ্গেরীয়-ফরাসি এ বিখ্যাত পণ্ডিত তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর ইতিহাস ও সভ্যতার উপর ব্যাপক গবেষণা করেন। তৃতীয় বিশ্ব সম্পর্কিত তার সুচিন্তিত মতামত ও রচিত গ্রন্থ অত্যন্ত আধুনিক ও প্রগতিশীল বলে বিবেচিত হয়। তিনি এশিয়া, আফ্রিকা ও দক্ষিণ আমেরিকার মতো তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলো পর্যবেক্ষণ করে “Glance at Tomorrows’ History” নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেন। আমি এখানে তার অনাগত ইতিহাস চেতনা বা তার গ্রন্থটি সম্পর্কে কোনো আলোচনা করবোনা; বরং আমি তার কাছ থেকে গুরুত্বপূর্ণ কিছু কথা আপনাদের সামনে উপস্থাপন করবো। তার কথাগুলো ছিলো আধুনিক ও বিস্ময়কর।
আন্দ্রে জিদ বলেছিলেন, কিছু কথা বা বাণী কোনো ব্যক্তিকে স্মরণীয় করে রাখার ক্ষমতা রাখে। আর স্মরণীয় করে রাখতে না পারলেও তা অন্তত একটা বোধ বা উপলব্ধির জন্ম দেয়। এমনও হয় যে, আমাদের মধ্যেই কোনো কোনো বোধ বা উপলব্ধি লুকিয়ে থাকে যার সম্পর্কে আমরা নিজেরাই ভালো বুঝি না। আবার লুকানো বোধ বা উপলব্ধিগুলো আমরা নিয়ে প্রকাশ করতে পারি না। কিন্তু আমরা যখন এমন একটা বক্তব্য শুনি যা আমাদের মাঝে লুকানো বোধ বা উপলব্ধির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ও পরিপূরক হয় তখন তা আমাদের প্রচ্ছন্ন বোধের সাথে মিলেমিশে একটা ধারণার জন্ম দেয় এবং এভাবেই আমাদের মনোজগতে কোনো বিষয় বা বস্তু সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা তৈরি হয়।
‘আগামী দিনের ইতিহাস’ ভাবনাটা মূলত একটা আধুনিক ও বিপ্লবী অভিব্যক্তি। ইতিহাস তার বিষয় ও মেজাজগত দিক থেকে সর্বদাই অতীতাশ্রয়ী। ইতিহাস হলো অতীতের প্রতিফলন। ইতিহাস বলতেই আমরা বুঝি অতীত। যা কিছু পুরোনো তা-ই অতীত। এক্ষেত্রে ‘আগামী দিনের ইতিহাস’ কথাটা একটা নতুন ভাবনার দ্যোতক। আজকের আধুনিক মানুষ কেবল অতীত ও বর্তমানকে জানতে পারলেই সুখী নয়। মানুষ তার অনাগত ভবিষ্যতকেও নিশ্চিত জানতে চায়। কারণ, আধুনিক মানুষ অনেক বেশি সতর্ক ও সচেতন। তাই আধুনিক মানুষকে আগামী দিন সম্পর্কে ভাবতে হয়। আর আগামী দিনের ইতিহাস বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে আমাদের অবশ্যই হতে হবে বিজ্ঞানমনস্ক। এ ক্ষেত্রে ইতিহাসকে বিজ্ঞান হিসেবে বিশ্লেষণ করা অপরিহার্য।
আমরা যদি সেই অনাগত দিনের ইতিহাস লিখতে পারি তা হলেই ইতিহাস পাবে তার সত্যিকার মর্যাদা। সে ইতিহাসকে হতে হবে নিশ্চিত ভবিষ্যৎ নির্দেশক। যদি সে ইতিহাস ভবিষ্যৎ নির্দেশে ব্যর্থ হয়, এমনকি ন্যূনতম পক্ষে বর্তমান মানব গোষ্ঠী ও অনাগত মানব গোষ্ঠী সম্পর্কে জানতে সহায়ক না হয় তবে তা হবে অর্থহীন। কারণ মানবজাতি, ভবিষ্যৎমুখী মানুষের বহমান জীবন এবং বর্তমান ও অনাগত মানবগোষ্ঠীর ভবিষ্যৎ ও আদর্শ নির্দেশে সামগ্রিক সহায়তা প্রদান করাই সমস্ত বিজ্ঞানের ন্যূনতম ভূমিকা হওয়া উচিত। এক্ষেত্রে প্রথমেই মানবজাতির অতীত ইতিহাস সম্পর্কে সমান ধারণা থাকা আবশ্যক- যা আমাদের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ ইতিহাস নির্মাণে সহায়ক হবে।
টিবর মেনডের মতো নয়; বরং আমি আমার বিশ্বাসের আলোকেই আগামী দিনের ইতিহাসকে বিশ্লেষণ করতে চাই। আমার কথা বলার ভঙ্গি বক্তার মতো না হয়ে শিক্ষকের মতো হওয়াটাই স্বাভাবিক। কারণ পেশায় আমি একজন শিক্ষক। এজন্য আমি ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। সৌভাগ্যবশত আমার সামনে বসা মুখগুলো বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদেরই যারা আমার বাচনভঙ্গি ও বক্তব্যের সাথে পরিচিত।
আমার বক্তব্যকে অনুধাবনের জন্য আমি আপনাদেরকে কল্পনায় একটা ‘কোণ’ ধরে নিতে বলবো। (কোনো একটা গাণিতিক কাঠামো যার ভূমি সংলগ্ন অংশটা সবচেয়ে বিস্তৃত ও বৃত্তাকার। কাঠামোটি ভূমি থেকে উপরের দিকে ক্রমশই বৃত্তাকারভাবে সরু হবে। কাঠামোর শীর্ষ বিন্দু সূক্ষ বা সুচালো -অনুবাদক।) আমার বক্তৃতা শেষ হওয়া পর্যন্ত আশা করি কোণটার কথা মনে রাখবেন। কারণ এর ভিত্তিতেই আমি আমার বক্তব্যকে বিশ্লেষণ করবো।
এ ‘কোণ’ হলো আমাদের চিন্তা, বিচার বিশ্লেষণ ও অনুধাবনের কাঠামো। একটা যুগের সমাজ, সভ্যতা ও ইতিহাস তার পরবর্তী যুগের সমাজ, সভ্যতা ও ইতিহাসকে অনুসরণ করে। ব্যপারটা এমন যে, অতীতের মানবসভ্যতার কোনো একটা যুগ ক্রমশ পরবর্তী একটা সভ্যতার ঐতিহাসিক যুগে উত্তীর্ণ হয়। কোনো একটা যুগ তার শেষ পর্যায়ে এসে থেমে যায় না; বরং পরবর্তী ঐতিহাসিক যুগের সূচনা করে। এর অর্থই হলো ইতিহাস বহমান। টিবর মেনডের ভাষায়, মানবসভ্যতার প্রথম সূর্যোদয় হতে আজ পর্যন্ত ৩, ৪, ৫, ১০ এমনিভাবে ২৭টি যুগ পার হয়ে গেছে।
একটা অস্তিত্বশীল জীবন্ত সত্তার মতো প্রতিটি যুগেরই আছে ভিন্ন মেজাজ, চিন্তাধারা ও বিশেষ ধরনের ভাবপ্রবণতা। আমরা আজ ভালোভাবেই জানি অবস্থা, স্বকীয়তা, চিন্তাধারা, ঝোঁক-প্রবণতা ও লক্ষ্যের দিক থেকে প্রতিটি যুগই তার আগের যুগ হতে স্বতন্ত্র।
সুতরাং প্রত্যেকটি যুগকে বুঝার জন্যে আমাদের ‘কল্পিত কোণ’ খুবই প্রয়োজনীয় এবং এরই আলোকে ইতিহাসের প্রতিটি যুগকেই সূক্ষভাবে বিভক্ত করা যাবে এবং এর উপর সতর্ক অধ্যয়নের মাধ্যমে আমরা এমনকি ভবিষ্যত সম্পর্কেও বলতে পারব।
উদাহরণ হিসেবে, ‘আমরা তিনশ’ বছর আগের মধ্যযুগের ইউরোপীয় ইতিহাসকে বিশ্লেষণ করতে পারি। এক্ষেত্রে আমাদের কল্পিত ‘কোণ’কেই আমরা মানদণ্ড হিসেবে ব্যবহার করবো। এর ভূমি সংলগ্ন অংশ যা সবচেয়ে বেশি বিস্তৃত, সমাজের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের দ্বারা পূর্ণ। এই জনগণ কারা? এরা হলো সমাজের সাধারণ মানুষ। প্রত্যেকটি সমাজেরই সাধারণ মানুষ তাদের সংখ্যা ও স্তর বিবেচনায় আমাদের ‘কল্পিত কোণের’ ভূমিতেই অবস্থান করে।
প্রতিটি যুগের বুদ্ধিজীবি, পণ্ডিত ও চিন্তাবিদদের অবস্থান আমাদের ‘কোণ’টির উপরের অংশে। এরা হলো বুদ্ধিজীবী। তার মানে হলো, এদের যাবতীয় কার্যাদি মূলত বহুমুখী চিন্তার ক্ষেত্রে আবর্তিত। শরীরের কোনো অঙ্গ বা কারখানার কোনো হাতিয়ারের মতো এরা কাজ করেন না। এমনিভাবে ধর্মীয় নেতা, পণ্ডিত, কবি, সাহিত্যিক, চিন্তাবিদ ও দার্শনিকগণের অবস্থান হলো ‘কোণে’র উপরের অংশে।
‘কোণ’টির সবচেয়ে নিচের অংশে অবস্থান করে প্রতিটি সমাজের সাধারণ মানুষ। বুদ্ধিজীবি শ্রেণির অবস্থান হলো এর উপরের অংশে। আদিম সমাজের জন্যও এ কথা প্রযোজ্য। আদিম সমাজের গোত্রবন্ধ গণমানুষ ‘কোণে’র ভূমিতেই অবস্থান করে। তখনকার ক্ষেত্রে বুদ্ধিবৃত্তিক লোকগুলো বলতে বোঝাত জাদুকর, শ্বেতশ্মশ্রুধারী অথবা যে কোনোভাবে জনগণের নেতৃত্ব দেয় এমন ব্যক্তিবর্গ ।
বহু যুগ পার হয়ে গেছে। কিন্তু আমাদের ‘কোণ’টি সব যুগ বিশ্লেষণে সমানভাবে প্রযোজ্য। আমার বিশ্বাস, দিন যত এগুচ্ছে ‘কোণে’র ভূমিসংলগ্ন সাধারণ মানুষের অবস্থানও ক্রমশ বুদ্ধিবৃত্তিক স্তরের নিকটবর্তী হচ্ছে। অর্থাৎ, সাধারণ মানুষের সংখ্যা কমে যাচ্ছে এবং একই হারে তা বুদ্ধিবৃত্তিক শ্রেণিতে যুক্ত হচ্ছে। অর্থাৎ, প্রতিটি যুগেই বিদ্বান ব্যক্তিদের সংখ্যা তার পূর্ববর্তী যুগের সংখ্যা হতে বৃহত্তর হচ্ছে। কারণ শিক্ষা ও সংস্কৃতি এখন ব্যাপক রূপ লাভ করেছে। চিন্তার বিকাশ ঘটেছে। শিল্প ও বিজ্ঞানচর্চা অতি সাধারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। ফলে সাধারণ মানুষ ক্রমান্বয়ে বুদ্ধিবৃত্তিক স্তরের দিকে উন্নীত হচ্ছে।
সাধারণ জনগণ ও বুদ্ধিবৃত্তিক শ্রেণির মধ্যে আজ আর তেমন পার্থক্যসূচক সীমারেখা নেই। আমরা আমাদের ‘কল্পিত কাঠামো’ বা ‘কোণ’ ধরে যতই উপরে উঠবো, দেখবো যে সাধারণ জনগণ ক্রমশই বুদ্ধিবৃত্তিক শ্রেণির নিকটবর্তী হচ্ছে এবং উচ্চতর স্তরে বুদ্ধিবৃত্তিক শ্রেণিরই অবস্থান। আবার নিচের দিকে নামলে দেখা যাবে যে, বুদ্ধিবৃত্তিক শ্রেণিটা সাধারণ জনগণের কাছাকাছি এসে পড়েছে। অপরদিকে ‘কোণ’টি বেয়ে উপরে যেতে যেতে এমন একটা অবস্থানে পৌঁছানো যায় (যা শীর্ষবিন্দু) যেখানে প্রতিটি যুগের বিশেষ কিছু পণ্ডিত ব্যক্তিত্ব অবস্থান করেন। এ সব ব্যক্তি সমাজের শিক্ষিত মানুষের কাছে রীতিমতো মূর্তিতে পরিণত হন। এমনিভাবে প্রতিটি যুগের শীর্ষস্থানীয় চিন্তাবিদগণ তাদের যুগের চিন্তা-চেতনার উৎস হয়ে দাঁড়ান।
উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, জ্যা পল সার্ত্রে, বার্ট্রান্ড রাসেল, সোয়ার্জ প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ। আমাদের কোণ-এর শীর্ষবিন্দুতে অবস্থানরত; তাদের অবস্থান হলো বুদ্ধিবৃত্তিক শ্রেণির শীর্ষে। এ শ্রেণির নিম্নতম ব্যক্তিবর্গ হচ্ছেন স্কুল পড়ুয়াগণ। অবস্থানের দিক দিয়ে তারা অবশ্য সাধারণ জনগণের কাছাকাছি। আমি যা বলতে চাই এটাই হলো তার ভূমিকা। এবার আমি আমার মূলবক্তব্য শুরু করবো।
কল্পিত ‘কোণ’টা আমরা মধ্যযুগের বেলায় প্রয়োগ করবো। মধ্যযুগের সাধারণ জনগণ কারা? তখনকার ফ্রান্স, ইতালি ও ইংল্যান্ডের জনসাধারণ গির্জায় যেত। তারা যাজকদের আদেশগুলো পালন করতো। বাইবেল, পেন্টাটুক, যীশু এবং ঈশ্বরের নামে দেয়া সরকারি পণ্ডিতদের নির্দেশগুলো বাস্তবায়িত করতো সে-সব নির্দেশ শ্রবণ, গ্রহণ ও অনুশীলন করাই ছিলো তাদের কাজ। এরা হলো মধ্যযুগের সাধারণ মানুষ।
এই একই অনুভূতি ও বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন সাধারণ জনগণের উপস্থিতি আজও সমাজে রয়েছে। বড়দিন উপলক্ষে সেন্ট পিটার্সের বাতায়ন পথে পোপ যখন আবির্ভূত হন তখন তার মহামূল্যবান শ্বেত শুভ্র পবিত্র পোশাক দেখে আজও লক্ষ লক্ষ ধর্মপ্রাণ খ্রিস্টান ধর্মীয় অনুভূতি ও আবেগে উদ্বেল হয়ে পড়ে। তারা উচ্চস্বরে ক্রন্দন জুড়ে দেয়। এ হলো তেমন অনুভূতি ও চিন্তা যেমনটা তিন-চার শতাব্দী আগে মধ্যযুগীয় ইতালি বা ফ্রান্সের জনগোষ্ঠী ধর্মীয় আবেগে লালন করতো।
আমরা প্রায়ই বলি, এখন একটা নতুন যুগ চলছে। এর অর্থ কী? অর্থ হলো বুদ্ধিবৃত্তিক শ্রেণির মধ্যে একটা পরিবর্তন ঘটেছে, সাধারণ মানুষের মধ্যে নয়। সুতরাং প্রতিটি যুগের এসব বুদ্ধিবৃত্তিক শ্রেণির মধ্যে কী ধরনের বৈশিষ্ট্য ও স্বকীয়তা ছিলো তা আজ আমাদের খুঁজে বের করতে হবে।
এরপরেও কথা থেকে যায়। প্রতিটি যুগে সাধারণ মানুষ ও উচ্চস্তরে অবস্থানরত শিক্ষিত বুদ্ধিবৃত্তিক শ্রেণির বাইরেও হাতে গোনা ব্যতিক্রমধর্মী কিছু ব্যক্তিত্ব থাকেন যাদের চিন্তা ও বিশ্বাস তাদের সমসাময়িক বুদ্ধিবৃত্তিক শ্রেণির চিন্তা ও বিশ্বাসের মধ্যে বৈপরীত্যসূচক চৈতন্যের সূচনা করে। তারা সে যুগের স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব হিসেবে আবির্ভূত হন। সাধারণের মধ্যেও তাদেরকে গণ্য করা যায় না। তাদেরকে কোনো বিশেষ কালের বুদ্ধিবৃত্তিক শ্রেণির মধ্যেও ফেলা যায় না। তাঁরা হচ্ছেন সমগ্র মানব গোষ্ঠীর সেই প্রখ্যাত প্রতিভাবান ব্যক্তিত্ব যাঁদের কোনো কালের মধ্যে সীমাবদ্ধ করা যায় না। কারণ তারা যে কথা বলছেন বা চিন্তা করছেন বুদ্ধিজীবি শ্রেণি বলে পরিচিত গোষ্ঠী সে কথা বলেন না, তা ভাবেন না বা তা বিশ্বাসও করেন না, করার প্রয়োজনও বোধ করেন না। তাদের কথাগুলো খুবই নতুন। বোমার মতোই তার বিস্ফোরণ।
এদের পরিচয় কী? এদেরকে তো কোনো বিশেষ শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত করা যায় না। এদের সংখ্যা খুবই নগণ্য, হাতে গোনা ক’জন মাত্র। তবে এটা ঠিক যে, এরা প্রতিভাবান। এঁরা আধুনিক চিন্তা ও চেতনার উদ্ভাবক। এদের মানস প্রবণতা সমসাময়িক সমাজের প্রতিষ্ঠিত মূল্যবোধ হতে ভিন্নতর, শিক্ষা ঐতিহ্যের পরিপন্থী, বিজ্ঞান পদ্ধতির বিপরীতে এবং যুগধর্মের সাথে সাংঘর্ষিক।
মধ্যযুগের শেষ পর্যায়ে একটা গুরুত্বপূর্ণ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিলো। তখনকার ইউরোপের সাধারণ মানুষ বর্তমান ইউরোপের সাধারণ মানুষের মতোই জীবনযাপন করত। যেমন, আজকের আধুনিক ইউরোপের সাধারণ মানুষ গির্জার আনুগত্য করে এবং সাবেক মধ্যযুগীয় ধর্মীয় পণ্ডিতদেরই তারা মেনে চলে।
ইউরোপের শিক্ষিত সমাজের আবির্ভাব তিন শতাব্দী আগে, সতের শতকে। এ শতকেই বুদ্ধিবৃত্তিক শ্রেণির উদ্ভব ও বিকাশ ক্রমশ বর্তমান অবস্থায় পরিণতি লাভ করে। আজ যারা বুদ্ধিজীবি ও শিক্ষিত জনগোষ্ঠী হিসেবে পরিচিত, যাঁরা নতুন সংস্কৃতির ধারক ও বাহক তারা মূলত সতের শতকের বুদ্ধিজীবীদের আধুনিক সংস্করণ মাত্র। আজও তাদের ভাবধারাকে লালন করা হয়, তাদের মতোই তাঁরা চিন্তা করেন, বৈজ্ঞানিক ধ্যান-ধারণা, বিশ্বাস ও তত্ত্বের বেলায় তাদেরকেই তারা অনুকরণ করেন। এভাবে তারা সতের শতকে ইউরোপে গড়ে উঠা, শিক্ষিত সমাজ যাঁরা অদ্যাবধি বিশ্ববিদ্যালয়, বিজ্ঞান ও আধুনিক জীবন ধারাকে চালিয়ে নিচ্ছে তাদের অনুগামীদের বাড়তি একটা সংযোজনে পরিণত হয়।
মধ্যযুগের এসব শিক্ষিত ও বুদ্ধিজীবিদের পরিচয় কী? তারা ছিলেন খ্রিস্টান ধর্মযাজক ও গির্জার অনুমোদিত প্রতিষ্ঠানগুলোতে শিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গ। তাদের লক্ষ্য ছিলো, ধর্মীয় সত্যকে আবিষ্কার করা। সাধারণ মানুষদের আলো অভিসারে নিয়ে আসা। জনগণের নেতৃত্ব নেয়া। মূলত তাদের লক্ষ্য ছিলো একই ধর্ম আবর্তে বিপুল জনগোষ্ঠীকে উদ্বুদ্ধ ও একই দলভুক্ত করে তোলা।
এভাবে দেখা যায় যে, ‘কোণ’টি যখন আমরা মধ্য যুগ বিশ্লেষণে ব্যবহার করি তখন বুদ্ধিজীবি শ্রেণি বলতে যা বুঝাত তা মূলত খ্রিস্টান যাজক ও ধর্মীয় নেতাদের দ্বারাই পরিপূর্ণ ছিলো। তখনকার দিনের ধর্মীয় নেতাদের আপনারা ভালোভাবেই চেনেন। কিন্তু পনেরো হতে সতেরো শতকের মাঝামাঝি এই দীর্ঘ সময়ে এসব ধর্মীয় নেতাদের পাশাপাশি আরোও কিছু প্রতিভাধর ব্যক্তিত্ব জন্ম নিয়েছিলেন। তাঁরা ছিলেন নতুন চিন্তার ধারক ও বাহক। কিন্তু তখনও পর্যন্ত কোনো শ্রেণিতে রূপান্তরিত হতে পারেননি।
এ সময়ের কতিপয় চিন্তাবিদ সাধারণ ধর্মপ্রাণ, ঈশ্বর ভক্ত খ্রিস্টান মূল্যবোধ পরিহার করে একটা নতুন চিন্তাধারার প্রবর্তন করেন। তারা ষোলো হতে আঠারো শতকের মধ্যবর্তী সময়ে ধীরে ধীরে ‘কোণ’-এর শীর্ষে আরোহণ করেন। মধ্যযুগীয় শিক্ষিত সমাজের ধর্মবোধে অনুগত না হয়ে তারা হয়ে উঠলেন বিজ্ঞানমনস্ক। ধর্মের কথা হলো, ধর্মীয় গ্রন্থগুলোর দ্বারা অনুমোদিত বিষয়গুলোকেই গ্রহণ করতে হবে আর যা উল্লেখ করা হয়নি তা সবই পরিত্যাজ্য। ঠিক তেমনিভাবে তারা ঘোষণা করলেন যে, কেবল বিজ্ঞান ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা দ্বারা প্রমাণিত বিষয়গুলোকেই তারা বিশ্বাস করবেন। ধর্মীয় বা পবিত্র গ্রন্থসমূহে উল্লিখিত থাকলেই কোনো কিছুর উপর তারা বিশ্বাস আনবেন না, যতক্ষণ না তা পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও গবেষণার দ্বারা প্রমাণিত সত্যে পরিণত হয়।
এভাবেই আধুনিক বৈজ্ঞানিক যুগের সূচনা হলো। কেপলার ও গ্যালিলিওর মতো বিখ্যাত পণ্ডিতবর্গ বিজ্ঞান ভাবনার প্রচার ও প্রসার ঘটালেন। এভাবেই মধ্যযুগীয় ধর্মীয় মূল্যবোধের বিরুদ্ধে বিজ্ঞানের জয়যাত্রা ও প্রচার তীব্র আকার ধারণ করলো। তখন এই বিজ্ঞান মনস্ক ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে কায়েমি স্বার্থবাদী শ্রেণি সোচ্চার হয়ে উঠলো। তাদেরকে নিন্দা করলো, ধর্মের শত্রু বলে আখ্যা দিলো, কারাগারে নিক্ষেপ করলো, বিচারের কাঠগড়ায় আসামি হিসেবে হাজির করলো; এমনকি আগুনে পোড়ালো। গ্যালিলিও যার জ্বলন্ত উদাহরণ। কেনো? কারণ, তারা সমাজের সনাতন শিক্ষিত ও বুদ্ধিজীবিদের বিরুদ্ধে নতুন ধ্যান-ধারণার প্রচার করেছিলেন।
মধ্যযুগের শেষ পর্যায়ে সাধারণ জনগণ ও শিক্ষিত শ্রেণির (ধর্ম বিষয়ে শিক্ষিত ও গির্জার সাথে সম্পর্কযুক্ত) চেয়ে উপরের স্তরের একটা স্বতন্ত্র প্রতিভাবান দলের উন্মেষ ঘটে। যারা ছিলেন সংখ্যায় অতি নগণ্য, ১০/২০ জনের মতো। এই ক্ষুদ্র দলভুক্ত প্রতিভাধর ব্যক্তিবর্গ ধর্মীয় মূল্যবোধের বিপরীতে নতুন চিন্তা-চেতনার প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। কিন্তু তখনও পর্যন্ত তারা সমাজে একটা শ্রেণি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হতে পারেনি। তারা ছিলেন বিচ্ছিন্ন কতিপয় ব্যক্তি মাত্র।
এবার আমরা আধুনিক যুগ বিশ্লেষণে আমাদের ‘কোণ’টা ব্যবহার করবো। আধুনিক যুগের কাল সতেরো থেকে বিংশ শতাব্দী পর্যন্ত বিস্তৃত। আমরা দেখবো যে, এ যুগের সাধারণ জনগণের মধ্যে মূলত কোনো পরিবর্তন ঘটেনি। শুধু আয়তনের দিক থেকে এ শ্রেণির হ্রাস ঘটেছে এবং এ শ্রেণি হতে কিছু ব্যক্তি শিক্ষিত হয়ে উপরের শ্রেণিতে যোগ দিয়েছে।
আধুনিক যুগের শিক্ষিত বুদ্ধিজীবিদের নিয়ে এবার ভাবা যাক, তাদের অবস্থান হবে আমাদের ‘কোণ’-এর শীর্ষে। আজ তাঁরা ঠিক একই কথা বলছেন যা ষোলো শতকের প্রতিভাধর বিচ্ছিন্ন কতিপয় ব্যক্তি বলতেন। যে কথাগুলো তথাকথিত বুদ্ধিজীবিদের কাছে গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হয়নি। এমনিভাবে দেখা যায় যে, ‘কোণ’-এর শীর্ষে সর্বদাই সমাজের এমন কিছুসংখ্যক শিক্ষিত ও বুদ্ধিদীপ্ত প্রতিভাবান ব্যক্তিত্বের অবস্থান যারা তথাকথিত বুদ্ধিজীবিদের প্রচলিত চিন্তাধারার বিপরীতে নতুন চিন্তাধারার প্রবর্তন করেন। এ পর্যায়ে এসে এ সব বিচ্ছিন্ন, স্বল্প পরিচিত, প্রতিভাবানদের মতবাদগুলো আগামী দিনের শিক্ষিত সমাজের জন্য একটা মননশীল চিন্তাধারার উদ্ভব ঘটায় এবং সেসব চিন্তাধারা পরবর্তী যুগের মানুষদের বিশ্বাস ও চিন্তাধারার মধ্যে প্রভাব বিস্তার করতে থাকে।
এভাবেই আমরা দেখছি যে, আমাদের কল্পিত যে, ‘কোণ’-এর শীর্ষদেশে এমন সব প্রতিভাধর ব্যক্তিবর্গ অবস্থান করেন যাঁরা তাদের সমকালীন বুদ্ধিজীবিদের বিরোধী হন এবং তাদের বক্তব্যকে অগ্রাহ্য করেন। এখানেই শুরু হয় মূল বিরোধ। প্রতিভাধর ব্যক্তিগণ সংখ্যার দিক দিয়ে যেমন নগণ্য তেমনি স্বল্প পরিচিত। ক্রমান্বয়ে প্রসারিত হতে থাকে তাদের চিন্তাধারা ও আদর্শ। ক্রমে কালের প্রয়োজনে তাঁরা নিজেরাই একটা শিক্ষিত বুদ্ধিজীবী শ্রেণিতে উত্তীর্ণ হন। এমনকি তাঁরা তাদের পূর্ববর্তী বুদ্ধিজীবিদের সামাজিক অবস্থানটা দখল করে ফেলেন।
আজকের ইউরোপে এখনও যে যাজকরা রয়েছেন সমাজে তাদের কর্তৃত্ব রয়েছে। কিন্তু এ যুগের মানস প্রবণতা শিক্ষিতদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, যাঁরা বিজ্ঞানের দাস; ঈশ্বরের নয়। তবে আমরা যদি ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে আধুনিক যুগকে বিশ্লেষণ করি তাহলে দেখব যে, এ যুগেও সাধারণ মানুষদের চিন্তা-চেতনা মূলত ধর্মবোধ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। এমনকি ধর্ম সংস্কৃতির সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণে দেখা যাবে যে, আজও ‘ধর্ম’ সাধারণ মানুষদের চিন্তা-চেতনার মূল ভিত্তি হয়ে টিকে আছে।
আজ আমরা দেখছি যে, এক শ্রেণির মানুষ আছে যারা বিজ্ঞানের পূজারি। আজকের বুদ্ধিজীবী ও শিক্ষিত শ্রেণি বিজ্ঞানের পূজা করেন ধর্মীয় অনুভূতি ও বিশ্বাসকে পাওয়ার জন্য নয়। সুতরাং এ নিয়ম অনুযায়ী আধুনিককালে শিক্ষিতদের কোনোভাবেই ধার্মিক হওয়া যাবে না। কেনো? কারণ, এ নতুন যুগে সাধারণ মানুষরাই কেবল ধর্মে বিশ্বাস করেন। কিন্তু এর বিপরীতে দেখা যাবে যে, মধ্যযুগের বুদ্ধিজীবিরা একই সঙ্গে বুদ্ধিজীবী ও ধার্মিক ছিলেন। এ যুগের নব্য শিক্ষিতদের সবাই বিজ্ঞানের পূজারি এবং বিজ্ঞানের পূজা করাই এদের আদর্শে পরিণত হয়েছে। বিজ্ঞানের পূজারি নব্য শিক্ষিতরা ধর্মীয় নির্দেশ ও বিশ্বাসের বিপরীত মতবাদ হিসেবে এ সব আদর্শ প্রচার করেন। তাদের মতবাদ বিজ্ঞানের পূজা করা। এর বিপরীতে ধর্মের আদর্শ হচ্ছে ধর্মীয় নির্দেশ, বিশ্বাস ও রীতিনীতি; যা প্রশ্নাতীতভাবেই মেনে নিতে হবে।
একটা বিষয় এখানে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, মধ্যযুগের মতো আজও ‘ধর্ম’ সাধারণ মানুষের মাঝেই বিরাজমান। অন্যদিকে, বিজ্ঞানমনস্ক নব্য শিক্ষিতদের উদ্ভব হয়েছিলো সতেরো শতকে। আজ যাদের আদর্শ হচ্ছে বিজ্ঞানের পূজা করা। সতেরো শতক হতে আজ পর্যন্ত এ দীর্ঘ সময়ে এ সব শিক্ষিত জনগণ বিজ্ঞান পূজার দিকে যতই ঘনিষ্ঠ হয়েছে ধর্মীয় ধ্যান-ধারণা হতে তারা ততই দূরত্বে চলে যাচ্ছে। আর ঠিক একই হারে সাধারণ জনগণ হতেও তারা বিচ্ছিন্ন হচ্ছে।
মধ্যযুগের শিক্ষিত শ্রেণি ও সাধারণ জনগণের মধ্যে চিন্তা ও বিশ্বাসের সাদৃশ্য ছিলো। তারা একই লক্ষ্যে একইভাবে কথা বলতো, কিন্তু আজকের শিক্ষিত ও সাধারণ মানুষের মধ্যে চিন্তা ও বিশ্বাসের বৈসাদৃশ্য ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। শিক্ষিতরা বিজ্ঞানের পূজারি আর সাধারণ মানুষ ধর্মপ্রাণ।
এটা একটা চরম বাস্তবতা যা আমাদের সমগ্র চিন্তা, বিশ্বাস ও হাজারো মন্তব্য দিয়ে বিশ্লেষণ করা সম্ভব নয় যে, কেনো বিজ্ঞানের জয়যাত্রা এতো ব্যাপক ছিলো। একটা দীর্ঘ সময়ব্যাপী ইউরোপ, আমেরিকা, আফ্রিকা, দক্ষিণ আমেরিকা, ইরান এবং বিস্তৃত এশিয়ার মানুষদের মধ্যে বিজ্ঞানমনস্ক দৃষ্টিভঙ্গি ক্রমশই প্রাধান্য বিস্তার করে চলেছে। এমনিভাবে, সতেরো, আঠারো ও উনিশ শতকব্যাপী বিজ্ঞানের জয়যাত্রা এতই ব্যাপক আকার ধারণ করে যে, মানুষের ধর্মবোধ ক্রমশই আমাদের কল্পিত কাঠামো’র শীর্ষস্থান থেকে ভূমিতে অবতরণ করেছে। ক্রমে এভাবেই বিজ্ঞান ধর্ম এবং ধর্মবোধকে ধ্বংস করে দিতে থাকে। সেই ধ্বংসের পাদপীঠে বিজ্ঞান-ভাবনা এবং বিজ্ঞানের মহিমা স্থান জুড়ে বসে।
আজকের সাধারণ মানুষ মধ্যযুগের সাধারণ মানুষদের মতোই ধর্মে বিশ্বাস করে। বিশ্বব্যাপী তাঁরা ধর্মেরই অনুসারী। সাবেক ধর্মবিশ্বাস এখনও তাদের মধ্যে বিরাজমান। আজকের নব্যশিক্ষিতরা বিজ্ঞান পূজার আদর্শে যতই বিশ্বস্ত হচ্ছে ততই তাঁরা তাদের ঐতিহ্যগত ও জাতীয় ধর্ম হতে বিচ্যুত হচ্ছে। ধর্ম বিশ্বাসই ছিলো তাদের পূর্ব ঐতিহ্য যা হতে তারা আজ দূরে সরে গেছে। আজকে যারা ইউরোপ-আমেরিকা প্রাচ্য বা পাশ্চাত্যের ধর্ম সংস্কৃতির সমাজতান্ত্রিক গবেষণায় নিয়েজিত আছেন তাঁরা সবাই এই একই সত্য উপলব্ধি করতে পারবেন।
এর পরেও একটা সমস্যা থেকে যায়। বর্ণিত দুটো শ্রেণির বাইরে অন্য একটা দলকে আমরা খুঁজে বের করতে পারি। আমরা দেখেছি, প্রত্যেক যুগেই কতিপয় বিরল প্রতিভাবান ব্যক্তিত্ব থাকেন যাদেরকে ‘কোণ’-এর শীর্ষবিন্দুতে স্থান দিতে আমরা বাধ্য। প্রত্যেক যুগের শেষ পর্যায়ে এসে এসব বিরল প্রতিভাবান ব্যক্তি সংখ্যার দিক থেকে বড় হতে থাকেন। ক্রমেই তারা ক্ষমতা ও শক্তিলাভে সমর্থ হন। তারা আগামী দিনের বুদ্ধিজীবিদের চিন্তা ও চেতনার মধ্যে প্রভাব বিস্তার করেন। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, কেপলার, আইজাক নিউটন, ফ্রান্সিস বেকন ও রজার প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ তাদের নিজেদের যুগের মানব সমাজের জন্য ভবিষ্যত চিন্তা-চেতনার সুদৃঢ় ভিত্তি রচনা করেছিলেন। আমার বর্ণিত বিশ্লেষণ অনুযায়ী বর্তমানে কল্পিত ‘কোণ’-এর শীর্ষে অবস্থানরত ব্যক্তিবর্গ আগামী দিনের বিদ্যাবিদদের চিন্তা-চেতনার নির্মাতা হয়ে থাকেন।
এভাবেই আমরা আগামী দিনের ইতিহাসের প্রতি দৃষ্টিপাত করতে পারি। তা কীভাবে? যদি আমরা বর্তমান ‘কোণ’-এর শীর্ষে অবস্থানরতদের চিনতে পারি, তাদের চিন্তার পদ্ধতি সম্পর্কে আপনাদের বলতে পারি এবং দেখাতে পারি বিগত তিন শতক ধরে চলে আসা বিজ্ঞান পূজাকে তারা কীভাবে বিরোধিতা করেছেন তাহলেই আমরা সমাধানে পৌঁছে যাবো। এমনকি, আমরা এ যুগের শেষ পর্যায়ের চিন্তাবিদদের ভাবপ্রবণতা কীভাবে আগামী দিনের চিন্তাবিদদের বিশ্বাস, অনুভূতি ও ভাবপ্রবণতাকে প্রভাবিত করবে তা-ও নিশ্চিতভাবে জানতে পারবো।
আধুনিককালেও মানব জাতির মধ্যে কতিপয় বিরল প্রতিভাবান ব্যক্তিত্বের অবস্থান আমরা লক্ষ করে থাকি। শিক্ষিতদের মধ্যে এদের শীর্ষে স্থান দিতে আমরা বাধ্য। কারণ একদিকে শিক্ষিত মহল তাদেরকে অভিশিক্ষিত বলে মনে করেন, অপরদিকে তারা শিক্ষিতদের চেয়ে ভিন্ন চিন্তা করেন ও ভিন্ন কথা বলেন। এঁদেরই একজন হলেন গুইনন । সম্প্রতি তার রচিত গ্রন্থ ‘ক্রাইসিস অব দি মডার্ন ওয়ার্ল্ড’ ও ‘ধর্মীয় গবেষণা-পত্র’ ইউরোপে প্রকাশিত হয়েছে। এ বিখ্যাত ফরাসি পণ্ডিত ব্যক্তিত্ব হঠাৎ করেই একদিন আধুনিক বিজ্ঞান ও বিজ্ঞান পূজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। তিনি প্রাচ্যে চলে যান। সেখান থেকে যান মিসরে। কোনো শাব্দিক অর্থে নয়; বরং সত্যিকার অর্থেই তিনি বর্তমান ইউরোপীয় সমাজ ও চিন্তাধারা হতে সরে দাঁড়ান, যাতে করে তিনি ইউরোপীয় জনগণের প্রয়োজনে ও জ্ঞানপিপাসা নিবারণে সাহায্য করতে পারেন।
তেমনি ইদানীংকালের অপর আর একজন প্রতিভাধর ব্যক্তিত্ব হচ্ছেন এলেক্সিস ক্যারেল। তার প্রখ্যাত গ্রন্থ “Man, The Unknown” সহ বেশ কিছু লেখা ফার্সি ভাষার অনূদিত হয়েছে। তার লেখা ‘Reflections on Life’-এর দুটো সংস্করণ বের হয়েছে। অনুবাদ সুন্দর না হলেও বিষয়বস্তুর দিক থেকে বইটি মূলপাঠ্য। এ ছাড়াও আইনস্টাইন, উইলিয়াম জেমস, বাসালার্ড প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ।
এমনকি সাম্প্রতিককালের জ্যা পল সার্ত্রে ও বার্ট্রান্ড রাসেলের মতো ব্যক্তিবর্গ যাদেরকে বিশ্ববাসী ভালোভাবেই জানেন তাঁদের চেয়েও অনেক শ্রেষ্ঠতর হচ্ছেন ফরাসি বিজ্ঞানী দার্শনিক ও চিন্তাবিদগণ। আরও আছেন ম্যাক্স প্ল্যাংক, জর্জ গারভিচ, প্যাট্রিক ডোনিজ ও ডা. জিভাগোর লেখক প্যাস্টারনাক। নব্যশিক্ষিতদের কাতারে এসব মহান ব্যক্তিকে টেনে আনা যাবে না। এদের অবস্থান হচ্ছে শীর্ষে। কারণ বিজ্ঞান পূজার তারা সাধারণত বিরোধিতা করেন। বিগত তিন শতাব্দী ধরে এসব শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি তথাকথিত শিক্ষিতদের পালিত বিজ্ঞান ধর্মের বিরুদ্ধে কথা বলে এসেছেন।
অবশ্য এ কথাও বলা যাবে না যে, গুইনন ঠিক ম্যাক্স প্লাংকের মতো এবং ম্যাক্স প্লাংক ও ক্যারেল দু’জনেই হুবহু একই কথা বলেছেন। প্রত্যেকেরই নিজস্ব ও ভিন্ন ভিন্ন মতামত আছে। তা সত্ত্বেও কিছু কিছু ব্যপারে তাদের মিলও রয়েছে। আর সে মিলটাই হবে আমাদের বিবেচ্য বিষয়।
আমরা যদি তাঁদের সে সব অভিন্ন চিন্তাগুলোকে চিহ্নিত করতে পারি তাহলে দেখবো যে, আজ তাঁদের মধ্যে যে সব সাধারণ প্রবণতা পরিলক্ষিত হচ্ছে তা মূলত আজকের বুদ্ধিজীবিদের মৌলিক ঝোঁক প্রবণতায় পরিণতি লাভ করেছে এবং সেই ঝোঁক প্রবণতার মূলে রয়েছে বিজ্ঞান পূজার সম্পূর্ণ বিরোধী হয়ে ওঠা। মূলত এ প্রবণতাটাই হচ্ছে আধুনিক বুদ্ধিজীবিদের ধর্ম।
আগামী দিনগুলোতে এ প্রবণতাই অনাগত পণ্ডিত ও বুদ্ধিজীবিদের ধর্মে পরিণত হবে এবং আধুনিককালের বুদ্ধিজীবিদের এই ঝোঁক প্রবণতা ক্রমে বিজ্ঞান পূজার স্থলাভিষিক্ত হবে। এসব ব্যক্তিত্বের মধ্যে একটা সাধারণ ধারণা ব্যতিক্রমহীনভাবে বিদ্যমান, তা হলো আধ্যাত্মিকতার মাঝে ধর্মীয় অনুভূতি ও বিশ্বাসকে লালন করা। (দুর্ভাগ্যবশত সময় স্বল্পতার জন্য তাদের প্রত্যেকের উদ্ধৃতি দেয়া গেল না)।
আমরা জানি, ধর্মের প্রতি আইনস্টাইনের একটা গভীর অনুরাগ ছিলো। কিন্তু, আমরা বলেছি, ধর্ম হচ্ছে সাধারণ জনগণের বিশ্বাসের বুনিয়াদ। তাহলে আমরা কি বলতে পারি যে, আইনস্টাইন সাধারণ মানুষের একজন ছিলেন! অথবা তিনি হাইস্কুল পড়ুয়া, কলেজের ডিগ্রিধারী বা আমার মতো একজন পি.এইচ.ডি ওয়ালা নব্য শিক্ষিতদের শ্রেণিভুক্ত ছিলেন। কখনো না। অথচ তিনি ছিলেন ধার্মিক।
এভাবে দেখা যাচ্ছে যে, বিজ্ঞান পূজা ছাড়াও দুনিয়াতে চিন্তার রাজ্যে একটা নতুন ও বিশাল চিন্তা তরঙ্গের প্রবাহ সৃষ্টি হয়েছে। আমরা কখনো বলবো না যে, আইনস্টাইন ও ক্যারেল সাধারণ মানুষের মতো একই ধরনের ধর্মবিশ্বাস পোষণ করেন। বরং আমরা বলতে পারি যে, ‘ধর্ম’ বুদ্ধিজীবিদের বিশ্বাস ও বিজ্ঞানের চেয়েও ঊর্ধ্বে।
মূলত ধর্মে দুই ধরনের অস্তিত্ব বিদ্যমান। একটা ধর্ম কল্পিত ‘কোণ’-এর ভূমিতে অবস্থানরত জ্ঞান-বিজ্ঞানহীন সাধারণ জনগণের দ্বারা আচরিত ধর্ম। আমরা ধর্মের উঁচুস্তরের দিকে এগুলে আমাদের যুগে বৈজ্ঞানিক আস্তিকস্তরে উপনীত হবো এবং এরপর আরো উপরে প্রতিভাধর ব্যক্তিদের অবস্থান। আজকের দুনিয়াতেও এমনটাই পরিলক্ষিত হচ্ছে।
শিক্ষিতদের দিকে তাকিয়ে দেখুন। একজন মানুষ একইসঙ্গে শিক্ষিত ও ধার্মিক। কিন্তু তার সে ধর্মবোধ অত্যন্ত নিচুস্তরের। কারণ, ধর্মকে সেই ব্যক্তি তার প্রয়োজনের অতীত একটা বাড়তি সংযোজন বলে মনে করেন। ডাক্তার বা ইঞ্জিনিয়ার যা-ই সে হোক না কেনো ধর্মকে সে ধরে রেখেছে, অত্যন্ত নাজুকভাবে। তাঁর এ ধর্মবোধ সাধারণ জনগণ হতে নেয়া যা সে গ্রহণ করেছে ও আঁকড়ে ধরেছে। এমনি ধর্মবোধ একেবারেই অস্বাভাবিক ও অবশ্যই পরিত্যাজ্য। আমার ধারণা, সে যদি ধর্মহীন হয়ে যায় তবে সে বিজ্ঞান বহির্ভূত হবে এবং নাস্তিক্য ধর্মের কাছাকাছি পৌঁছে যাবে।
অন্য একজন শিক্ষিত ব্যক্তিকে যদি দেখা যায় যে, তিনিও ধার্মিক, তাহলে আমরা দেখব বিজ্ঞানের ঊর্ধ্বে অবস্থিত একটা ধর্মকে তিনি কীভাবে অনুসরণ করেন। তার সেই ধর্মবোধ সহজেই তার লেখনিতে প্রতিফলিত হবে। এ ধরনের ধর্মবোধ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষিত ও চিন্তাশীল ব্যক্তিদের মধ্যে পরিলক্ষিত হয়।
যে ধর্ম বিজ্ঞানের চেয়ে কম গুরুত্বপূর্ণ তা শিক্ষিতদের চেয়েও নিম্নস্তরের। কিন্তু যে ধর্ম বিজ্ঞানের ঊর্ধ্বে, বিজ্ঞান যার উচ্চতায় এখনও পৌঁছতে পারেনি তা হচ্ছে এ যুগের চিন্তানায়কের ধর্ম। তারা শিক্ষিত সম্প্রদায়ের চিন্তা-চেতনার অনেক ঊর্ধ্বে অবস্থান করছেন। এরা হলেন বর্তমান যুগের প্রতিভা।
ম্যাক্স প্লাংক, আইনস্টাইন বা ক্যারেলের কোনো বই বা তাঁদের কোনো অনুবাদ গ্রন্থের মধ্যে সহসাই আমরা এমন সব কথা বা উদ্ধৃতি লক্ষ করি যেসব কথা কোরআনে উল্লিখিত বাণীর সাথে মিলে যায়। অর্থাৎ তাদের কোনো কোনো কথা কোরআনের উল্লিখিত বাণীর সাথে সামঞ্জস্যের ইঙ্গিত বহন করে। আমাদের বর্ণিত এ সব ব্যক্তিত্বের অনেকেই বহু যুগের বহু সংকট অতিক্রম করেছিলেন। একটা যুগ গেছে চরম নাস্তিকতার যুগ। তারপর যুগের প্রয়োজনেই এসেছে সংস্কারের যুগ এবং সবশেষে এসেছে ধর্মবোধের যুগ যে ধর্ম বিজ্ঞানের চেয়েও উঁচু ও শ্রেষ্ঠ।
সে সব সুবিদিত ও সুশিক্ষিত মানুষ যারা প্রতিটি যুগের সংকটকে অতিক্রম করে বিজ্ঞান পূজার বিরোধিতা করেছিলেন তাদের সবাই আজ আমাদের অতি পরিচিত হয়েছেন। তাদের সাধারণ প্রবণতা হচ্ছে আধ্যাত্মিকতা, ধর্মীয় অনুভূতি ও পরিবেশের দিকে ফিরে যাওয়া। ধর্ম যেহেতু সাধারণ জনগণের চিন্তা ও বিশ্বাসের বুনিয়াদ সেহেতু তা অপাঙক্তেয় এই যুক্তিতে গত তিন শতক ধরে এ সব চিন্তাবিদদের অবজ্ঞা ও নিন্দা করা হয়েছে। আজ তারা মোটেই অবজ্ঞার পাত্র নন, অপাঙক্তেয়ও নন।
আজ আমাদের নবতর উপলব্ধির সময় এসেছে। এতদিনে ষোলো শতকের সে সব বিজ্ঞানমনস্ক, প্রতিভাধর ব্যক্তিবর্গ ও আজকের শিক্ষিত শ্রেণির চিন্তা- চেতনার মধ্যে ব্যাপক ব্যবধান সৃষ্টি হয়ে গেছে। যদিও এখন পর্যন্ত তাদের বক্তব্যগুলো কোনো প্রাতিষ্ঠানিক স্বীকৃতি পায়নি। এখনও তাদের চিন্তাগুলো বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে গৃহীত ও পরিশ্রুত হয়নি। কিন্তু তাদের কথাগুলো বা চিন্তার পদ্ধতি বিশ্ববিদ্যালয়ের ধী-সীমার ঊর্ধ্বে স্থান পাবার যোগ্য। এসব ব্যক্তির বাণী বা বক্তব্যগুলো আগামী দিনের শিক্ষিত বুদ্ধিজীবি শ্রেণির বিশ্বাস ও চৈতন্যের বুনিয়াদ তৈরি করবে এবং এসব বুদ্ধিজীবীই আগামী দিনের ঐতিহাসিক যুগের সূচনা করবে।
সুতরাং, সন্দেহাতীতভাবে বলা যায় যে, আজকের ‘ধর্ম’ হবে সেই ধর্মের কাছে ফিরে যাওয়া, যে ধর্ম বিজ্ঞানকে অতিক্রম করছে অথবা বিজ্ঞানের চেয়েও শ্রেষ্ঠ বলে স্বীকৃত হয়েছে। এভাবে আমাদের আলোচনা অনুযায়ী আমরা বলতে পারি যে, আজকের বিজ্ঞান পূজা যা সতেরো শতক থেকে অদ্যাবধি ধর্মবিমুখ ভাবনার দ্বারা পরিচালিত হয়েছে সেই বিজ্ঞান পূজা তার অন্তিম পর্যায়ে এসে উপনীত হয়েছে। কেনো? কারণ, আজকের বিশ্বে নবতর চিন্তানায়কের অবির্ভাব ঘটেছে, যাদের চিন্তা-চেতনা আধুনিক বিজ্ঞান ভাবনার ঊর্ধ্বে। যাদের বৃহৎ চিন্তা-বিশ্বাস, মেধা ও মনন দৃঢ়ভাবে মানব জাতির নবতর উপলব্ধির ঘোষণা দিয়েছে। আর তা হলো সমগ্র বিশ্বমানবের কল্যাণে বিজ্ঞান পূজার বিপরীতে ধর্মীয় বিশ্বাসকে উজ্জীবিত করে তোলা।
মাক্স প্লাংক ও কেপলার দুজনেই ছিলেন পদার্থবিদ। কেপলার সম্বন্ধে প্লাংক বলেছেন, “পণ্ডিত কেপলার জ্ঞানের সামগ্রিকতায় বিশ্বাস করতেন। সৃষ্টির তাবৎ বিষয়ে জ্ঞান লাভের জন্য গভীর মনোযোগ, সতর্কতা ও সচেতনতার প্রয়োজন রয়েছে বলে তিনি মনে করেন।” অপর একজন পণ্ডিত ব্যক্তির উদাহরণ দিয়ে তিনি বলেছেন, “তাকে আমরা একজন ক্ষুদে শিক্ষানবিশ পণ্ডিত হিসেবে চিহ্নিত করতে পারি। কারণ, বিশ্বের বহুমুখী চিন্তার সামগ্রিকতায় তিনি বিশ্বাস করতেন না। তাঁকে ক্ষুদে পণ্ডিত বলা হচ্ছে সেই অর্থে যে, তিনি জ্ঞানের সাবর্জনীনতায় বিশ্বাস করতেন না। কেপলার জ্ঞানের সার্বজনীনতায় বিশ্বাস করতেন। আর এ জন্যই তিনি আধুনিক পদার্থবিদ্যারস্রষ্টা হতে পেরেছেন।”
এক্ষেত্রে আইনস্টাইন আরো স্পষ্ট বক্তব্য রেখেছেন। তিনি বলেছেন, “ধর্মীয় অনুভূতি ও সৃষ্টির গূঢ় রহস্যের উপর বিশ্বাসই হলো যে কোনো বৃহৎ বৈজ্ঞানিক গবেষণার চাবিকাঠি।” এই কথাগুলোর জন্য জনগণের গোত্রেও তাকে ফেলা যায় না। তবে, আলেক্স ক্যারেল অবশ্যই প্রথম মানব যিনি দুই বার নোবেল শান্তি পুরস্কার লাভে সমর্থ হয়েছেন। লারইউজ ডিকশনারিতে তাকে এজন্য বিখ্যাত ব্যক্তিত্ব হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। উক্ত গ্রন্থে তাকে বিংশ শতকের একজন শ্রেষ্ঠ চিন্তানায়ক হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। তিনি বলেছেন, “যদি সমাজ থেকে স্রষ্টার প্রতি ভক্তের আনুগত্য ও প্রার্থনার নিয়ম তুলে দেয়া হয়, তবে তা হবে আমাদের জন্যে মৃত্যুর সনদপত্রে স্বাক্ষর করার মতো ভয়ঙ্কর।”
সতেরো, আঠারো ও উনিশ শতকের শিক্ষিত বুদ্ধিজীবিরা কী কখনও এমন কথা বলতেন? সতেরো, আঠারো ও উনিশ শতকের শিক্ষিত শ্রেণির বক্তব্য ছিলো “যদি আমি আমার অস্ত্রোপচারের ছুরির নাগালের মধ্যে খোদাকে দেখতে না পাই, তবে আমি তাঁর উপর বিশ্বাস আনতে পারি না। বিজ্ঞান পূজারিদের ভাবনাই মূলত নাস্তিকতা। কিন্তু আজ নতুন চিন্তা ও চিন্তানায়কদের আবির্ভাব ঘটেছে। একজন মনোবিজ্ঞানী বলেছেন অন্যভাবে। তিনি বলেন, “জীবন ধারণের জন্য মানুষের যেমন অক্সিজেন ও খাদ্যের প্রয়োজন, তেমনি খোদার আনুগত্য ও তার নিকট প্রার্থনার প্রয়োজনও অপরিহার্য। কেননা, এটাই মানব জাতির নিয়তি। এগুলো মানুষের অকৃত্রিম প্রয়োজন। আমরা যদি এই আনুগত্যের প্রয়োজনকে অস্বীকার করি তাহলে আমরা ধ্বংস হয়ে যাবো।”
এবার ক্যারেলের কথায় আসা যাক। তিনি মোটেই ধার্মিক ছিলেন না। চড়ুই পাখির হৃৎপিণ্ড সংযোজন প্রক্রিয়ার উপর তিনি গবেষণা করেন। আর এ জন্যই তিনি দুইবার নোবেল শান্তি পুরস্কারে ভূষিত হন। তিনি বলেন, “শ্বাস-প্রশ্বাস ও খাদ্য গ্রহণের মতোই আমাদের প্রয়োজন রয়েছে খোদার আনুগত্য করার। এমনকি আমাদের দৈহিক, মানসিক, স্নায়ুবিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক, প্রয়োজনেও তার আনুগত্য করা আবশ্যক। তিনি আরো বলেছেন, “ধর্মের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস ও আস্থার অভাবেই রোম সভ্যতার পতন হয়েছিলো।”
কথাগুলো আলেক্সিস ক্যারেলের। যিনি ধার্মিক নন, যাজকও নন। এমনকি আমাদের ‘কল্পিত কাঠামো’র ভূমিসংলগ্ন সাধারণ ধার্মিক আস্তিকতায়ও বিশ্বাস করেন না। গারভিচের বক্তব্য হলো, সুদীর্ঘ উনিশ শতকব্যাপী সমাজবিজ্ঞান ১৯৮ ধরনের সূত্র আবিষ্কার করেছে এবং যেগুলোতে মানুষ বিশ্বাস এনেছে, কিন্তু বিংশ শতকের সমাজবিজ্ঞান সেসবের কোনোটাতেই আজ আর বিশ্বাস আনতে পারছে না।
প্রখ্যাত ফরাসি গণিতবিদ সোয়ার্জ বলেন, “উনিশ শতকের পদার্থবিজ্ঞানের ধারণা ছিলো, প্রতিটি জীবনসত্য আবিষ্কারে তারা সক্ষম হবেন। এমনকি কবিতারও। কিন্তু বিংশ শতকের পদার্থবিজ্ঞান বিশ্বাস করে যে, ‘বস্তু’ কি, তারা তা-ই জানে না।”
কেন বিংশ শতকের বিজ্ঞান ভাবনা হঠাৎ করেই এমন বিনয়ী মূর্তি ধারণ করেছে? কেনোই বা ষোলো, সতেরো, আঠারো ও উনিশ শতকব্যাপী বিরাজমান বিজ্ঞানের দাম্ভিক আস্ফালন বিচূর্ণ হয়ে গেল? কারণ, ইতোমধ্যেই বিশ্বব্যাপী একটা নতুন যুগের সূচনা হয়ে গেছে। আগামী দিনের শিক্ষিতদের চিন্তা-ভাবনা হবে বর্তমানকালের শিক্ষিতদের বিপরীত। তাদের চিন্তাধারা হবে ধর্মকেন্দ্রিক। তা হবে এমন একটা ধর্ম যা অবশ্যই বিজ্ঞানের চেয়ে নিচু নয়; বরং বিজ্ঞানের চেয়ে অনেক উঁচু ও শ্রেষ্ঠ।
অনুবাদ : মাহমুদ আব্দুল্লাহ