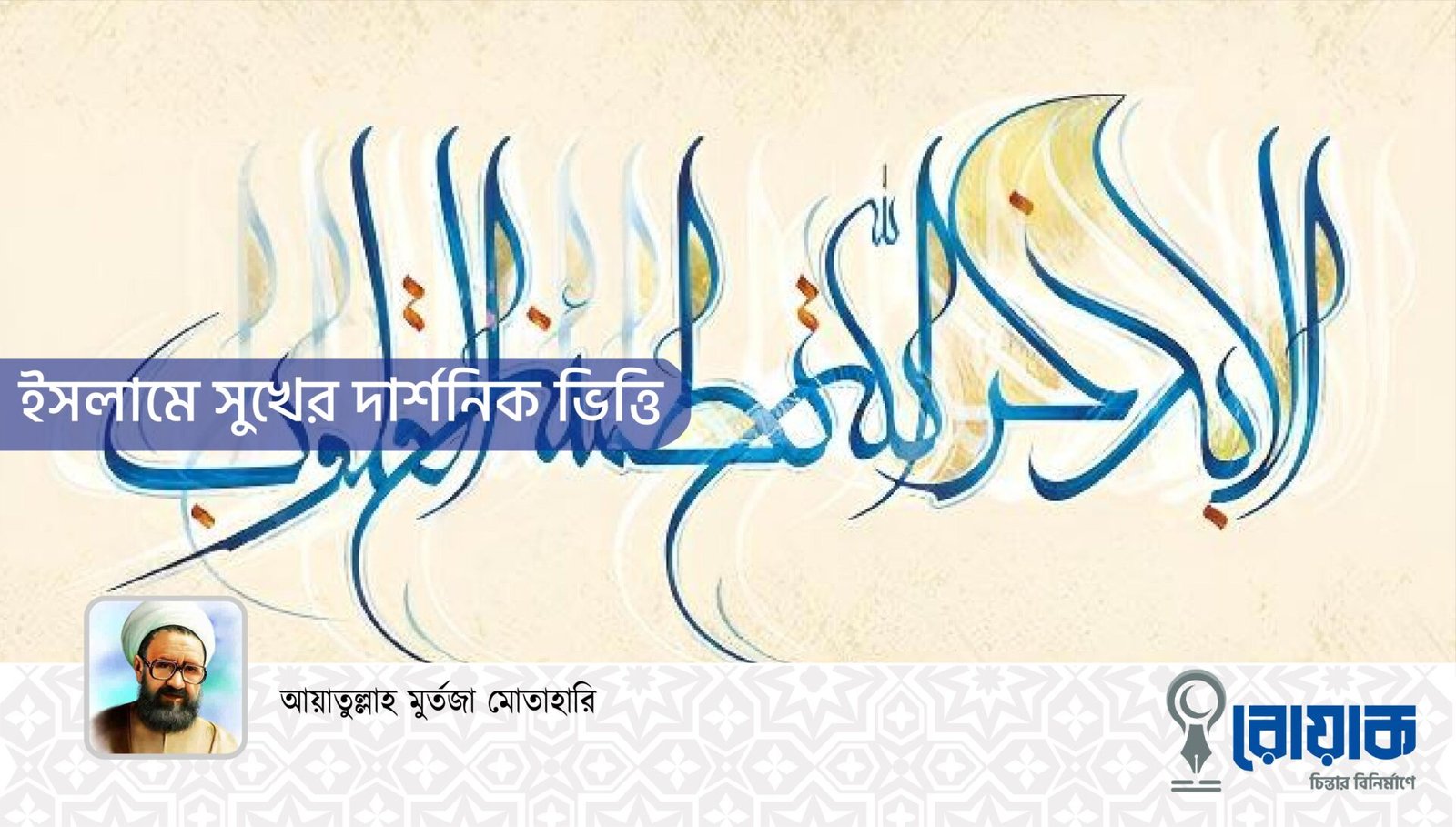দর্শনশাস্ত্র যে সব বিষয় আলোচনা করেছে তন্মধ্যে মানব জাতির ইতিহাসে সুখের প্রশ্নটি হচ্ছে একটি অত্যন্ত পুরনো বিষয়। বিষয়টি ব্যবহারিক বা প্রয়োগীয় দর্শনের অন্তর্ভুক্ত। নীতিশাস্ত্র ও সমাজতত্ত্ব বিশারদ বিজ্ঞ পণ্ডিতগণ এর প্রকৃতি শর্তাবলী, কারণ, বাধাপ্রতিবন্ধকতা ও অসঙ্গগতিসমূহ আলোচনায় ব্যস্ত থাকেন। যদি সুখ ও দুঃখ বা দুর্ভাগ্যের প্রশ্নটি জল্পনাধর্মী দর্শন ও ধর্মতত্ত্বের আলোচনায় উত্থাপিত হয়, তখন এটি সমস্যার একটি ছোটখাট বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত থাকে, অর্থাৎ সুখ (এবং দুঃখ) কি দৈহিক ও বস্তুগত? অথবা এটা কি নিম্নে বর্ণিত দুই প্রকার? যেমন:
- ১. শারিরীক ও বস্তুগত সুখ।
- ২. আধ্যাত্মিক ও মানসিক সুখ।
ধর্মতত্ত্ববিদগণ এ প্রশ্নটি আলোচনা করেছেন। তার কারণ এই যে, তাঁরা প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে- আধ্যাত্মিক এবং মানসিক সুখ-দুঃখ অনেক মহান, অনেক বড়। বু-আলী, (আবু আলী ইবনে সিনা), ইউরোপে যিনি এভি-সেনা নামে পরিচিত, তাঁর লিখিত ‘ইশারাত’ পুস্তকের ৮ম অধ্যায় এবং সদরুল মোতাআলেহীনের লিখিত ‘আসদার’ গ্রন্থের ৪র্থ বিষয়টি আলোচনাকালে, সুখ প্রশ্নটির শুধু এ দিকটি বিবেচনা করেছেন এবং এর অন্যান্য দিক বাদ দিয়েছেন। অপরদিকে আমরা আজ পর্যন্ত ইসলামী ও অনৈসলামী দর্শন পুস্তকে এ বিষয়টি সম্পর্কে কোন সর্বাত্মক ও পূর্ণাঙ্গ আলোচনা দেখতে পাইনি। যদিও এ রচনায় পাঠক যা কিছু পাবেন, তা আলোচ্য বিষয় সম্পর্কে একটি পূর্ণাঙ্গ আলোচনা বলে বিবেচিত হতে পারে না, তবুও এটাকে একটি সংক্ষিপ্ত জরিপ বা সাধারণ আলোচনা বলা যেতে পারে। এখানে যেসব প্রশ্ন ও আলোচনা উঠে আসে তা নিম্নরূপ:
- ১. সুখ কি?
- ২. সুখ ও আনন্দ।
- ৩. মানুষ কি প্রকৃতিগতভাবেই সুখের আকাঙ্খা করে?
- ৪. সুখ ও ব্যাকুল বাসনা।
- ৫. সুখ ও সন্তুষ্টি।
- ৬. একটি সামাজিক আলোচনা।
- ৭. সুখের প্রকারভেদ।
- ৮. সুখের স্তর বা পর্যায়।
- ৯. সুখের উপাদান ও কারণসমূহ।
- ১০. ধারাবাহিক আলোচনা সম্পর্কে একটি জরীপ।
- ১১. সুখলাভের জন্যে মানুষের কি হিদায়াতের প্রয়োজন?
প্রথমেই সুখ এবং দুঃখ শব্দ দু’টির অর্থ সুস্পষ্ট বলে মনে হয়। এক্ষেত্রে যদি কোন জটিলতা ও অসুবিধা থেকে থাকে, তা অন্যান্য সমস্যার সাথে সম্পর্কিত। কারণ আপনি যদি কোন ব্যক্তির কাছে জানতে চান যে, তিনি সুখ কামনা করেন কিনা, তখন বিনা দ্বিধায় তিনি ইতিবাচক জওয়াব দেবেন এবং আপনি যদি প্রশ্ন করেন “দুঃখ সম্পর্কে কি মত, তাও চান কি না?” তখন নিঃসন্দেহে একটি নেতিবাচক উত্তর আপনার কানে পৌঁছবে। কেউ এ প্রশ্ন সম্পর্কে একটুও এমন চিন্তা করে না এবং কেউই একথা বলে না যে- “প্রথমে সুখ ও দুঃখের অর্থ ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দাও, যাতে করে আমি কোনটি চাই সে সম্পর্কে ভেবে দেখতে পারি।” সুতরাং সব মানুষের কাছেই সুখ এবং দুঃখের সুস্পষ্ট অর্থ আছে, কাজেই এগুলো এমন সব বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত যাদের কোন সংজ্ঞার প্রয়োজন নেই। কিন্তু আমি বলতে চাই যে, সুখের কোন সংজ্ঞাদানের প্রয়োজন নেই একথা মনে করা যথেষ্ট নয়। অনেক ধারণাই প্রথমে এরকম মনে হয়, কিন্তু যখনই আমরা দ্বান্দ্বিক বা প্রশ্নোত্তর পদ্ধতি ব্যবহার করি এবং সে অর্থকে এর সাথে কাছাকাছি অন্যান্য অর্থের সাথে তুলনা করি ও বিশ্লেষণ করি, তখন আমরা দেখতে পাই যে সুস্পষ্ট ও পরিষ্কার ধারণা ক্রমেই এক ধরনের জটিলতা ও অস্পষ্টতার দ্বারা পরিবর্তিত হয়ে যাচ্ছে।
অনেকেই সুখ শব্দটিকে আনন্দ, প্রশান্তি, সাফল্য, আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি, পরমানন্দ এবং বিভিন্ন ঘটনা প্রবাহে সন্তুষ্টি লাভ ও অনুরূপ আরো কিছু বিষয়ের সমার্থবোধক বলে মনে করেন। কিন্তু যখনই আমরা সুখ শব্দটিকে এর প্রত্যেকটির সাথে তুলনা করি তখন আমরা দেখতে পাই যে ঐগুলো অর্থের দিক থেকে সঠিক ও যাথাযথ হলেই ধারণা হিসেবে সবগুলি এক নয়। সুতরাং প্রথমেই তাদের তুলনা করা প্রয়োজন, যাতে করে পরবর্তী সময়ে এসব তুলনার ভেতরেই আমরা সুখের সঠিক অর্থ খুঁজে পেতে পারি।
সুখ শব্দটি বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে সাহায্য অর্থে ব্যবহৃত হতে পারে কিনা, যাতে করে পৃথিবীতে বিভিন্ন উপলক্ষে যে ব্যক্তি সাহায্য লাভ করে তাকে আমরা সুখী বলতে পারি। এজন্যে সুখ ও আনন্দের শব্দগত মৌলিক অর্থ আলোচনার কোন প্রয়োজন নেই। অপরদিকে এর বিপরীত অর্থে আমরা দুঃখ শব্দটিকে বিবেচনা করতে পারি। অথবা দুঃখ মানে তাই- যা শুরু থেকে গভীর বেদনা, ব্যথা ও দুর্ভাগ্যের অর্থে ব্যবহৃত হয়। অপরদিকে সুখ শব্দটি ঠিক তার বিপরীত মানে বুঝায় অর্থাৎ বেদনা ও কষ্ট থেকে মুক্তি।
বাহ্যত অভিধানগত অর্থে আমরা এ দু’টি শব্দের বিপরীত অর্থ দেখতে পাই না, কিন্তু সাধারণ ও বিশেষ অর্থে ব্যবহারকালে সুখ ও দুঃখ শব্দ দু’টিকে বিপরীত অবস্থানে রাখতে হয়। আল-কোরআনেও এ ধরনের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায় যেমন, “সেদিন যখন উপস্থিত হবে, তখন কারো পক্ষে তাঁর (আল্লাহর) অনুমতি ছাড়া কোন কথা বলা সম্ভব হবে না, অনন্তর এদিন কিছু লোক হবে হতভাগ্য, আর কিছু সৌভাগ্যবান, যারা হতভাগ্য হবে তারা দোযখে যাবে- আর যারা সৌভাগ্যবান হবে তারা জান্নাতে যাবে।” (১১: ১০৫-১০৮)
সুখ ও আনন্দ
সুখ এবং আনন্দ শব্দ দু’টি অর্থের দিক থেকে খুবই কাছাকাছি (দুর্ভাগ্য ও বেদনার ন্যায়), কিন্তু তারা সমার্থবোধক নয়। আনন্দলাভ করা ও সুখ হাসিল করা একই কথা নয়। ঠিক একইভাবে ব্যথা-বেদনা সহ্য করাকে পুরোপুরি দুর্ভাগ্য বলা যেতে পারে না। কেননা আনন্দের পেছনে আসতে পারে অনেক ব্যথা-বেদনা, যেমনিভাবে আবার ব্যথা-বেদনা ও মহত্তর, বৃহত্তর গুরুত্বপূর্ণ আনন্দের ভূমিকা হিসেবে পরিগণিত হতে পারে। এটাও সম্ভব যে আমরা একটি আনন্দলাভ করি, আর তারই ফলশ্রুতিতে আরো বৃহত্তর, মহত্তর ও গুরুত্বপূর্ণ আনন্দ হারিয়ে ফেলি, অথবা একটি বেদনা, একটুখানি কষ্ট আরে। কঠিন ও তীর ব্যথা-বেদনাকে প্রতিরোধ করে।
এ সমস্ত ক্ষেত্রে আনন্দ ও বেদনার বাস্তবতা অক্ষুণ্ণ থাকে অর্থাৎ আমাদের মনে করা উচিত নয় যে, আনন্দ আরো একটি বৃহত্তর বা মহত্তর আনন্দের পথ বেঁধে দেয়, অথবা আরো বেশী ব্যথা-বেদনার কারণ হয়ে দাঁড়ায়, তাকে আর আনন্দ বলা যাবে না। কিন্তু এমনি ধরনের আনন্দ সুখ নয়। একইভাবে যখন একটি ব্যথা বা বেদনা আরো বড়ো আনন্দের ভূমিকা গ্রহণ করে অথবা কঠিন যন্ত্রণা বা বড়ো কষ্ট নিবারণ করে, তাকে অবশ্যই বিরূপ দৃষ্টিতে দেখা উচিত হবে না।
আমরা যখন কোন কিছু লাভ করি, কোন কিছু পাই, তখন যদি আমাদের মনে কোন দুঃখ বা অনুতাপ না আসে, আমরা যদি দুঃখিত না হই, তাহলে সেটাই সুখ এবং দুঃখ-দুর্দশা হচ্ছে যে জিনিস বা বিষয়ের কোন কারণ কোনক্রমেই আমরা ব্যাখ্যা করতে পারি না. খুজে পাই না, তা সয়ে যাওয়া, অর্থাৎ মানুষ তার চূড়ান্ত আকাঙ্খা বা কামনা-বাসনার জন্যে হয় বোধকে বেছে নিয়েছে এবং দুঃখকে গ্রহণ করেছে, ঠিক তার বিপরীত কারণে, অর্থাৎ যা তার সব সময় পরিহার করা উচিত। অন্যকথায়, সুখ হচ্ছে মানুষের নিঃশর্ত ইচ্ছা অভিলাষ, আর কষ্ট বা দুঃখ হচ্ছে তা নিঃশর্ত বিতৃষ্ণা বা ঘৃণা। সুতরাং যদি কোন ব্যক্তি বা একটি ধর্ম অথবা বিশেষ চিন্তাধারা দাবী করে যে, সে মানব জাতির জন্যে সুখ বয়ে আনছে, তাহলে তার মানে হবে- “আমি যে বিষয়ে পথ নির্দেশ দেয়ার দাবী করছি, তা যা ধারণা করা হয় তার চাইতে অধিকতর উৎকৃষ্ট নয়।” কিন্তু আনন্দ সে রকম কিছু নয়। কেউ যদি দাবী করে যে সে আনন্দ দিচ্ছে, তাতে যদি আরো গভীর বেদনা বিজড়িত থাকে অথবা আরো মহত্তর বা বৃহত্তর আনন্দ হারিয়ে যায়, তবুও ব্যাপারটি ভিন্ন।
আনন্দ মানুষ অথবা অন্যান্য প্রাণীর বিশেষ ক্ষমতা এবং সামর্থ্যের সাথে সম্পর্কিত থাকে, কিন্তু সুখ মানুষের সামগ্রিক ক্ষমতা, সামর্থ্য ও জীবন ধারণের পদ্ধতির ওপর নির্ভরশীল। আনন্দ প্রীতিকর ও অপ্রীতিকর বিষয়ের নিয়ন্ত্রক। অপরদিকে যা কাম্য এবং কাম্য নয়, সুখ তারই ওপর আধিপত্য করে। আনন্দ বর্তমান সময়ের সাথে সম্পর্কিত, অপরদিকে সুখ বর্তমান ও ভবিষ্যৎ উভয়ের সাথেই সমানভাবে অন্বিষ্ট। আনন্দ ও বেদনা মানুষের জীবনের প্রত্যেকটি দিকের সাথে পৃথক পৃথকভাবে জড়িত, অপর দিকে সুখ হচ্ছে একটি সামগ্রিক ব্যাপার।
এ কারণে আনন্দ ও বেদনার মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করা সহজ, কিন্তু সুখ ও তার বিপরীত অনুভূতিকে স্বতন্ত্রভাবে চিহ্নিত করা খুবই কষ্টকর এবং কোন কোন সময় দুঃসাধ্য। একজন মনস্তত্ববিদ, যিনি শুধু মানসিক প্রক্রিয়াকেই স্বীকৃতি দেন, তিনি আনন্দ ও বেদনা সম্পর্কে তাঁর মতামত দিতে পারেন, অপর- পক্ষে সুখ ও দুঃখ সম্পর্কে মতামত পেশ করা দার্শনিকের কাজ, কেননা তিনি পৃথিবীকে তার সমাজ ও মানুষকে জানার ও চেনার দাবী করেন। সুখ ও দুঃখ সম্পর্কে সে দার্শনিকের মতামত নির্ভর করে পৃথিবী ও মানুষ সম্পর্কে তাঁর জ্ঞানের ওপর। একারণে সুখ সম্পর্কে দার্শনিকেরা যে পরামর্শ, উপদেশ বা মতামত দেন, তা একই ধরনের নয়। প্রত্যেকেই এক্ষেত্রে ভিন্ন মত পোষণ করেন। তাঁদের একজন মনে করেন আনন্দলাভই হচ্ছে সুখ, কিন্তু আরেক জনের মতে আনন্দ বিসর্জন দেয়া এবং ইচ্ছা দমন করাই হচ্ছে সুখ। কেউ বা পার্থিব বিষয়ের প্রতি মনযোগ নিবদ্ধ করেন, আর অপর কেউ মনোযোগ দেন আধ্যাত্মিক বিষয়ের প্রতি। তাদের একজন মনে করেন বর্তমান মূহুর্তই গুরুত্বপূর্ণ, আরেক জনের মূলমন্ত্র ও উদ্দেশ্য হচ্ছে ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করা। কিন্তু যেহেতু আদশ ও বেদনা অহংয়েরই বিশেষ কর্ম-ফসল বা পরিণতি, সে কারণে সেগুলো গভীর অনুসন্ধান ও পরীক্ষার ওপর নির্ভরশীল এবং সেগুলো সম্পর্কে ঐক্যমতে উপনীত হওয়া সহজ।
মানুষ সুখ কামনা করে, এটা তার দাবী, কিন্তু তারপরও কেন সে বিভিন্ন লক্ষ্য অনুসরণ করে বা সুখ লাভের জন্ম বিভিন্ন উপায় বা পথ অবলম্বন করে। এর কারণ হচ্ছে এই যে, তাদের ব্যক্তিগত চিন্তা পদ্ধতির মধ্যে পার্থক্য রয়েছে অথবা তারা মানুষ ও বিশ্ব সম্পর্কে রচিত বিশেষ কোন চিন্তাধারা বা ধর্মের সাথে জড়িত। এর আরো একট কারণ আছে, যা আমরা ‘সুখ কি নিরপেক্ষ বা আপেক্ষিক’-এ প্রশ্নের সাথে আলোচনা করবো।
মানুষ কি প্রকৃতিগতভাবেই সুখের আকাঙ্ক্ষা করে?
সুখ ও আনন্দের মধ্যে আমরা যে পার্থক্যের কথা উল্লেখ করেছি, তাতে দেখা যায় যে আনন্দ একমুখী, কিন্তু সুখ বহুমুখী। আনন্দ হচ্ছে মানুষের অহংয়ের বিশেষ সৃষ্ট অবস্থার একটি দিক এবং বিবেকের অনুমোদন সাপেক্ষ। অপরদিকে সুখ হচ্ছে একটি সাধারণ ও পৃথক বিষয়, যা সকল আনন্দ বেদনার তুলনা ও হিসেব নিকেশ করে পাওয়া যায়। মানুষ সুখের ধারণা লাভ করেছে আনন্দ ও বেদনাকে তুলনা করার সামর্থের মধ্য দিয়ে, তার বিভিন্ন দিক অধ্যয়ন করে, মহত্তর ও ব্যাপক আনন্দ লাভ ও সার্বিকভাবে উপভোগের একটি পন্থা গ্রহণ করে এবং সকল দুঃখ যাতনাকে নিঃশেষ করে দিয়ে। কিন্তু আনন্দ হচ্ছে একটি মানসিক অবস্থার নাম, যা নির্ভর করে কোন কিছু বা একটি শক্তি বা সামর্থ্য বা মানব দেহের নমনীয়তার ওপর। কাজেই আনন্দ ও বেদনাকে প্রকৃতি ও সহজাত বৃত্তির দ্বারা পৃথকভাবে চিহ্নিত করা যায়।
কিন্তু সহজাত বৃত্তি ও প্রকৃতির দ্বারা সুখ ও দুঃখকে চেনা যায় না, বুদ্ধিবৃত্তিই এ কাজ করতে পারে। বুদ্ধিবৃত্তি সরাসরি পৃথকভাবে চিহ্নিত করার দাবী করে কিনা, নাকি মানুষকে সুখের দিশারী চিন্তাধারা বা ধর্মের দিকে পরিচালিত করে, সেটা ভিন্ন কথা। তবে একথা ঠিক যে, যেকোনভাবেই হোক, সহজাত বৃত্তি এ কাজ করতে পারে না। সুতরাং একথা সত্যি নয় যে- প্রত্যেক মানুষই প্রকৃতগতভাবে সুখ কামনা করে এবং সর্বদাই তাই চায়। মানুষ যা চায় তা হচ্ছে আনন্দ।
কোন মানুষ সঠিক পথ বাছাই করুক বা না করুক, যেকোন অবস্থায় সে সুখ চায়। একথা আমরা একমাত্র তখনই বলতে পারি, যখন সে সঠিক হিসেব-নিকেশ করে, লাভ-ক্ষতির তুলনা করে এবং এর মধ্য থেকে একট পথ নির্বাচন করে। কাজেই মানুষ প্রকৃতগতভাবেই সুখ চায় কিনা- এই প্রশ্নের জওয়াবে একথা অবশ্যই বলতে হবে যে- যদি এর মানে এই হয় যে, সব মানুষই হারানো সুখের পেছনে দৌঁড়ায়, কিন্তু শুধুমাত্র তারা পার্থক্য করার সময়ে প্রায়ই ভুল করে, তাহলে একথা ঠিক নয়। কেননা মানুষ প্রায়শই প্রকৃতিকে অনুসরণ করে, বুদ্ধিবৃত্তিকে নয় এবং তারা আনন্দ চায়, সুখ নয় এবং যদি এটা বুঝায় যে, মানবীয় বুদ্ধিবৃত্তি সুখকে আলাদাভাবে চিহ্নিত করে, স্বাভাবিকভাবে তা পেতে চায়, তাহলে এটি হবে একটি সঠিক কথা বা বক্তব্য।
সুখ ও ব্যাকুল বাসনা
প্রত্যেক মানুষেরই অবশ্যই বেশ কিছু ইচ্ছা আছে এবং সেগুলো পূরণ করার প্রবল আকাংখাও আছে। যদি তাকে জিজ্ঞাসা করা হয় যে, কোন কোন জিনিসে তার সুখ নিহিত আছে, যাতে করে সে তা হাসিল করতে পারে। সে তখন তার প্রয়োজন ও ব্যাকুল বাসনাগুলোকে সামনে নিয়ে আসবে।
কিছু লোক মনে করেন যে সুখ হচ্ছে ব্যাকুল বাসনার নিবৃত্তি ও আকাংখা পূরণে সাফল্য লাভ এবং যে কেহ এসবের নাগাল পেয়েছে, সে পরিপূর্ণ সুখ লাভ করেছে এবং যে কোনটাই পায়নি সে পুরোপুরি অসুখী অথবা যে তার কিছু বাসনা পূরণ করেছে, সে তার প্রাপ্তি বা সাফল্যের অনুপাতে কিছু সুখও লাভ করেছে। কাজেই তার সাথে যে অবিচার করা হয় নাই। শুধু তাই নয়, বরং একটি শ্রেণীর সদস্য হিসেবে কিছু কল্যাণও সে হাসিল করেছে।
কিন্তু আমরা বলতে পারি যে, সম্ভাব্য সর্বোচ্চ আনন্দ লাভ এবং সর্বাধিক দুঃখ-বেদনা দূরীকরণ বা হ্রাসকরণই হচ্ছে সুখ। অন্য কথায় একজন মানুষ যখন যে কোন পরিস্থিতিজাত প্রতিবন্ধকতা এবং অসামঞ্জস্য ও বৈপরিতোর কারণে ব্যথা-বেদনা ও দুখ-যন্ত্রণা অতিক্রম করার জন্যে স্বীয় বস্তুগত ও বুদ্ধিগত সম্পদের সুসামঞ্জস্য ব্যবহার করে, তখন সুখ সেখান থেকেই বেরিয়ে আসে। অবশ্য এ ক্ষেত্রে একথা সত্য বলে মেনে নেয়া হয় যে- মানুষ তার জন্মগত ক্ষমতা ও সামর্থ্য সম্বন্ধে সচেতন এবং সৃষ্ট জগতের স্বাভাবিক নিয়ম অনুসারে উক্ত ক্ষমতা ও সামর্থ্য ব্যবহারের সম্ভাবনা অনুধাবন করতে সক্ষম।
এ প্রসঙ্গে এটা উল্লেখযোগ্য যে, কোন কোন সময় সমাজের শোষিত ও দুর্বল শ্রেণীর লোকজন এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে যে- শোষকেরা প্রয়োজন মনে করে বস্তুগত যেসব সুযোগ-সুবিধা তাদের দিচ্ছে তারা তাতে সুখী। বাস্তবে তারা যখন ধড়িবাজ, সুবিধাবাদী ও স্বার্থপর লোকদের শোষণের কাছে আত্মসমর্পণ করছে, তখন তাদের সুখকে প্রকৃত সুখ বলা যেতে পারে না। এই ভাবে যে অন্যায়-অবিচার হচ্ছে, তা অসন্তোষের কারণে সৃষ্ট জুলুম না-ইনসাফীর চেয়ে অধিকতর বেদনাদায়ক ও করুণ। কারণ যারা অন্যায়-অবিচার অনুভব করে, তাদের জন্য সেটা যন্ত্রণাদায়ক অসুখের মতোই যা রোগীকে বাধ্য করে প্রতিকার খুঁজে বের করার জন্যে। কিন্তু যারা জুলুম, না-ইনসাফী অনুভব করে না, তাদের জন্যে সেটা ব্যথাহীন অসুখের মতোই। আর সাধারণতঃ ব্যথাহীন অসুখের রোগীরা রোগের প্রতিকার বা ঔষধ তালশ করা থেকে বিরত থাকে।
সমাজের স্বচ্ছল শ্রেণীর লোকেরা দুর্বল শ্রেণীর সবচাইতে বড়ো খিদমত যা করে তা হচ্ছে, তাদের (দুর্বল শ্রেণীর লোকজন) মধ্যে সন্তুষ্টর মনোভাব সৃষ্টি করে দুঃখ-কষ্ট দূর করে দেয়। কিন্তু সুখ মানে শুধুমাত্র কষ্ট থেকে মুক্তিলাভ নয়। এর মানে ব্যথাবেদনা না থাকা নয়, সুখ মানে হচ্ছে সামগ্রিকভাবে সম্পূর্ণ পরমানন্দ কল্যাণ লাভ করা। আগেই বলা হয়েছে যে, এধরনের কষ্ট ও যন্ত্রণাকে চোখ ও দাঁতের ব্যথার সাথে তুলনা করা যেতে পারে না এবং যে কোন ক্ষেত্রে এগুলোর দূরীকরণকে খিদমত হিসেবে হয়তো চিন্তা করা হবে না। সামাজিক সতর্কতা আসে এধরনের কষ্ট-যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে এবং এক্ষেত্রে এসব কমিয়ে দেয়া হচ্ছে আরেকটি পাপ ও অপরাধ।
সুখের প্রকারভেদ
সুখকে যদি আমরা মানুষের ওপর আরোপ করি যে, মানুষ হচ্ছে দেহ ও আত্মার সমন্বয়, তাহলে এটা হবে শুধু এক প্রকার। কিন্তু আমরা দেহ ও আত্মাকে যদি পৃথক পৃথক অস্তিত্ব মনে করি, তাহলে বলতে হবে সুখ দুই প্রকার- শারীরিক ও আধ্যাত্মিক। আনন্দের স্থিতিশীলতা, তীব্রতা, শক্তি অথবা দূর্বলতা অনুযায়ী এবং দৈহিক ব্যথা-বেদনার সর্বাধিক মাত্রায় উপশম বা দুরীকরণের মাধ্যমে আমরা সামগ্রিকভাবে সম্পূর্ণরূপে যে শারীরিক আনন্দ লাভ করি তাই হচ্ছে শারীরিক সুখ। আধ্যাত্মিক সুখ হচ্ছে সামগ্রিক ও পরিপূর্ণভাবে আধ্যাত্মিক আনন্দলাভ এবং আধ্যাত্মিক জীবনে দুঃখ বেদনার হাত থেকে সর্বাধিক মাত্রায় মুক্তি। আমরা দেহের প্রতিটি অংগের সুখকে পৃথক করতে পারি এবং দেহের শক্তি ও অংগের ভিত্তিতে ভাগ করতে পারি। উদাহরণস্বরূপ দৃষ্টির সুখ, শ্রবণের সুখ, যুক্তির সুখ ইত্যাদি। সে যাহোক, যে কোন ক্ষেত্রেই হোক না কেন, সুখ আনন্দ থেকে পৃথক। দৃষ্টির সুখ দৃষ্টির আনন্দ থেকে পৃথক। কোন কিছু চোখের জন্যে আনন্দদায়ক হতে পারে, কিন্তু যেহেতু তা দৃষ্টিশক্তির জন্য ক্ষতিকরও হতে পারে, সে কারণে সেটা সুখ বলে বিবেচিত হতে পারে না। আনন্দের কথা বাদ দিলে যখন কোন কিছুর সুখের কথা বলি, তা সে হোক মানুষের, দেহের অথবা আত্মার বা দেহের কোন অঙ্গের সুখ, তখন তার সামগ্রিক গুরুত্বকে আমরা অবহেলা করতে পারি না বা বাদ দিতে পারি না।
সুখের স্তর যা পর্যায়
আনন্দ ও বেদনা, সুখ ও দুঃখের প্রধান ভিত্তি, তাদের প্রত্যেকের স্তর বা পর্যায় আছে। ব্যক্তিভেদে তাদের প্রভাব ভিন্ন ভিন্ন ধরনের হয়। আনন্দে অনুভূতি বা উপলব্ধির ক্ষেত্রে বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে যে পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়, তা শুধু দৈহিক তৃপ্তি বা উপভোগের মধ্যেই স্পষ্ট হয়ে উঠে না, বরং বৃদ্ধিগত নান্দনিক এবং ধর্মীয় উপলদ্ধিতেও সুস্পষ্টভাবে ধরা পড়ে। প্রকৃতিগতভাবেই বিভিন্ন যোগ্যতা ও মেধা দিয়ে মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে। সে অনুযায়ী সুখের পর্যায় ও স্তর বিভিন্ন এবং সকল মানুষই সমপর্যায়ে সুখ ভোগ করতে পারে না। অধিকন্তু বাইরের উপাদানগুলো যা মেধাকে সক্রিয় রাখে অথবা বেদনা ও দুঃখ যন্ত্রণাকে নিয়ন্ত্রণ করে, তা সব মানুষের জন্যে সমান নয়। সুতরাং এসব উপাদানের ওপর নির্ভরশীল হওয়ার কারণে সুখও বিভিন্ন ধরনের হয়। সুখ হচ্ছে একট সামগ্রিক প্রাপ্তি বা লাভ।
এ সামগ্রিক প্রাপ্তির ব্যাপারটি পূর্ণাঙ্গভাবে সর্বোচ্চ সীমারেখার মধ্যে অথবা অন্যভাবে হতে পারে। একারণে সুখের বিভিন্ন পর্যায় ও স্তর লক্ষ্য করা যায়।
এ পর্যন্ত আমরা যা কিছু ব্যাখ্যা করেছি তাতে দেখা যায় যে সুখ পুরোপুরি নির্ভর করে গতি, বিবর্তনমূলক কার্যধারা ও মানুষের অন্তর্নিহিত সম্ভাবনার আলোকে পূর্ণত্ব অর্জনের ওপর। সুতরাং, সুখ পূর্ণতার সাথে সম্পর্কিত। কিন্তু গতি ও আন্দোলনের মধ্যে এমনিতে কোন পূর্ণতা নেই, কিন্তু এগুলো হচ্ছে পূর্ণতালাভ তথা সুখলাভের মাধ্যম বা উপায়। সুখ ও পূর্ণতা একই নিয়মের অধীন।
এখন আমরা সুখের উচ্চতর অর্থের দিকে যেতে পারি এবং সুখ ও অস্তিত্বকে পাশাপাশি ২ জন অশ্বারেহী ব্যক্তির মতো মনে করতে পারি। প্রতিটি সৃষ্ট প্রাণীই তার ক্রমঃবিকাশ ও বর্ধনের ক্ষমতার অনুপাতে সুখভোগ করে। অস্তিত্বের চিরস্থায়ী উৎস ও উৎপত্তি থেকে সৃষ্ট বক্ররেখার সাথে যতটুকু নৈকট্য বা সম্বন্ধ থাকে, ক্রমবিকাশের ক্ষমতাও সে অনুপাতে হয়। এবং মানুষ এ উৎপত্তি বা মূলের যত কাছাকাছি থাকে, সুখ থেকে উপকৃত হওয়া বা কল্যাণ লাভ ঠিক সে অনুপাতেই তার হয়ে থাকে এবং উৎপত্তি বা মূল থেকে যত দূরে থাকে সে অনুপাতে কষ্টও ভোগ করে। মানুষের সব ধরনের সুখলাভের শক্তি বা যোগ্যতা সৃষ্টি হয় আল্লাহর নৈকট্যলাভের কতটুকু শক্তি বা যোগ্যতা তার আছে তা দিয়ে।
সুখের উপাদান বা কারণ
যেসব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বিশেষতঃ বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি থেকে আলোচনা করা হয়, সুখের উপাদান হচ্ছে তন্মধ্যে অন্যতম।
এক্ষেত্রে অনেক প্রশ্ন আছে, উদাহরণস্বরূপ নীচে কয়েকট দেয়া গেল-
- ১. যেসব কারণ মানুষকে যথর্থাই সুখী করে, আসলে তার কোন অস্তিত্ব আছে কি? অথবা সুখ কি শুধুই স্বপ্ন বা কল্পনা? দুঃখ, বেদনা, কষ্ট এবং সে ভয়ের কারণগুলোই কি শুধু পৃথিবীতে সৃষ্টি করা হয়েছে? প্রাচীন ও আধুনিক দার্শনিকগণ, যারা শিল্প-সৌন্দর্য, সংস্কৃতি ইত্যাদির প্রতি ঘৃণা পোষণ করে তাঁরা এই মত পোষণ করেন। স্পষ্টতঃ এমনি ধরনের চিন্তাধারার সাথে খোদায়ী দর্শনের কোন মিল নেই, ধর্মতাত্ত্বিক দার্শনিকদের মধ্যে এমন কোন লোক খুঁজে পাওয়া যায় না, অথচ বস্তুবাদী দর্শন এ ধরনের বহু লোকের জন্ম দিয়েছে। কিন্তু বিষয়টি আলোচনা করার ক্ষেত্র এটা নয়।
- ২. সুখের উপাদান বা এর পেছনে যে কারণ নিহিত রয়েছে তাই কি শুধু খুঁজে বের করতে হবে, অথবা এটা কি বিভিন্ন উপাদান বা কারণের ওপর নির্ভরশীল?
- ৩. সে উপাদান বা কারণ (বা উপাদানগুলোও বা কারণসমূহ) কি স্বাভাবিকভাবেই মানুষের অস্তিত্বে বিদ্যমান অথবা এটা কি বাইরের জগতে আছে এবং সেখান থেকেই তা হাসিল করতে হবে? অথবা কারণ বা উপাদান- সমূহের একাংশ কি ভেতরের এবং অপরাংশ বাইরের?
- ৪. যদি এসব উপাদান বা কারণসমূহ মানব প্রকৃতিতে স্বাভাবিকভাবে বিস্তমান থেকে থাকে, সেগুলো কি তার দেহে এবং শারীরিক শক্তি, অথবা তার আত্মায় এবং আধ্যাত্মিক শক্তিতে? অথবা কোন অংশ তার দেহে এবং কিছু তার আত্মায়?
এগুলো অসংখ্য প্রশ্নের অন্তর্ভুক্ত, যেগুলো আলোচনার সূত্রপাত ঘটায় এবং যে সম্পর্কে যথেষ্ট আলোচনা করা হয়েছে, সংক্ষেপে এসবই প্রশ্ন করে, “সুখের উৎস কোথায়”?
যেমন আমরা জানি, কিছু লোক দাবী করছে যে নিজের ভেতরেই সুখ অন্বেষণ করতে হবে। এসব চিন্তাবিদদের অধিকাংশই সুখকে ব্যথা-বেদনার হাত থেকে মুক্তি হিসেবে বিবেচনা করেন এবং বিশ্বাস করেন যে বহির্জগতের সংস্পর্শে এসে কলুষিত হলে ব্যথা-বেদনা ও দুঃখ-যন্ত্রণার সৃষ্টি হয় এবং ব্যক্তি নিজেকে যত বেশী বাইরের জগৎ থেকে আলাদা রাখে এবং এর সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে, সে ততবেশী সুখের কল্যাণ প্রাপ্ত হয়, যা (সুখ) আসলে ব্যথা-বেদনার হাতে মুক্তিলাভ ছাড়া আর কিছুই নয়।
ভারতীয় দর্শনে, সুফীবাদ এবং বুদ্ধের চিন্তাধারায়, গ্রীসের সর্বশ্রেষ্ঠ দার্শনিক ডাইওজিনিসের ন্যায় গ্রীক বৈরাগ্যবাদী দার্শনিকদের দর্শনে এবং মেইনস ও তাঁর অনুসারীদের শিক্ষায় আমরা এমনি ধরনের ভাবধারার সন্ধান পাই।
দুর্ভাগ্যবশত এ চিন্তা-পদ্ধতি যা দার্শনিক বৈরাগ্য ধর্মীয় মতবাদের ফসল এবং ইসলামী একত্ববাদের সম্পূর্ণ বিরোধী ও বিপরীত, তা এ চিন্তাধারায় বিশ্বাসী ও অভ্যস্ত লোকজনের সাথে মেলামেশা ও এ সম্পর্কিত চিন্তাধারার প্রচারণার ফলে মুসলমানদের মধ্যে বহুল পরিমাণে প্রচলিত হয়েছে। কঠোর সংযম, খোদাভক্তি, সংসারত্যাগ অথবা এমন কি সুফীবাদের নামে মুসলমানদের মধ্যে এ চিন্তাধারায় প্রচলন হয়েছে এবং সেটা তাদের মধ্যে এমনভাবে বহুমূল হয়েছে যে, কিছু কিছু অজ্ঞ মূর্খ লোকদের ধারণা অনুযায়ী ইসলামী দৃষ্টিভংগীতে এ চিন্তাধারার প্রয়োজন আছে।
আরেক দল মনে করেন বাইরের দুনিয়াই হচ্ছে সুখের উৎস। তাঁরা বলেন যে মানুষ এ পৃথিবীর একটি অংশ, প্রাকৃতিক শক্তি দ্বারা সে প্রভাবিত হয় এবং এ কারণেই সে বেঁচে থাকে এবং পৃথিবীর আনন্দ উপভোগ করে। মানুষের নিজস্ব বলতে যা আছে তা হচ্ছে দারিদ্র ও অভাব। কিছু পার্থিব উপাদান বা কারণের প্রতিকূলে এক ধরণের স্নায়বিক সংবেদনশীলতা ও প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হলে তখন আনন্দের সৃষ্টি হয়। উদাহরণস্বরূপ- মানুষ কোন কিছুর প্রতি দৃষ্টিপাত করলে তখন তার দৃষ্টির সাথে সম্পর্কিত স্নায়ুতে যে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়, অথবা মুখগহ্বর জিহ্বা ও পরিপাক যন্ত্রে খাদ্যের সংস্পর্শে যে প্রতিত্রিয়ার সৃষ্টি হয় বা একজন পুরুষ ও নারী যখন একে অপরকে স্পর্শ করে, তখন তাদের মধ্যে স্পর্শের যে অনুভুতি বা বোধ জন্মে, তারই ফলে এক ধরনের স্নায়বিক সংবেদনশীলতা ও পারস্পরিক ক্রিয়ার আমরা আনন্দলাভ করি। একমাত্র যে জিনিষটি মানুষের অভ্যন্তরে সৃষ্টি হতে পারে বলা যায় তা হচ্ছে খাদ্যের অপ্রাচুর্য অথবা অন্যান্য দোষত্রুটি বা অভাবের কারণে মানবদেহে ব্যথা-বেদনা ও দুঃখকষ্ট দেখা দিতে পারে।
এ মতাবলম্বীদের মতে সুখ পুরোপুরিভাবে বাহ্যিক কারণ বা জ্ঞানদানের ওপর নির্ভরশীল। কিন্তু কষ্ট বা দুঃখ মানুষের অভ্যন্তরে সৃষ্ট কোন কারণে হতে পারে এবং সে কারণে পার্থিব প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির স্বল্পতা হতে পারে, অথবা এর একটি বাহ্যিক কারণও থাকতে পারে যেমন কোন ব্যক্তি ব্যথা-বেদনা অনুভব করে বা কষ্ট পায় যদি সে কারো হাতে মার খায়, অথবা কারাবন্দী হয় বা তার অধিকার যদি কেউ কেড়ে নেয়। সুখের উপাদান বা কারণ সম্পর্কে এটাই হলো জড়বাদী চিন্তাধারা।
এসম্পর্কে একটি তৃতীয় মত আছে, তা হচ্ছে সুখ শুধু আভ্যন্তরীণ বা বাহ্যিক কারণ বা উপাদানের নির্ভর করে, এমনি ধরনের বিশ্বাস প্রকৃত বিষয়ের অতিরঞ্জন বা বাড়াবাড়ি। মানুষকে এমনভাবে তৈরী করা হয়েছে যে, সে বাহ্যিক উপাদান বা কারণ বাদ দিয়ে চলতে পারে না এবং এগুলোর সাহায্য ছাড়া পূর্ণতা ও সুখ হাসিল করতে পারে না (অথবা দার্শনিক পরিভাষায় মানুষ তার অস্তিত্ব ও আভ্যন্তরীণ অবস্থা থেকে স্বাধীন নয়)। অথবা সে এমন কোন অপ্রধান ও পরগাছা জাতীয় জীব নয় যে, তার সব আনন্দই বাইরে থেকে আসবে। মানুষের দেহের আধ্যাত্মিক রাজ্যে কিছু আনন্দের কেন্দ্র আছে, সেগুলো সে যদি কাজে লাগাতে পারে, ব্যবহার করতে পারে, তাহলে তা বস্তুজাগতিক কেন্দ্র থেকে বৃহত্তর, মহত্তর ও সমৃদ্ধ হবে। জড় স্নায়বিক প্রতিক্রিয়ার দ্বারাই শুধুমাত্র আনন্দের সৃষ্টি হয়, এরূপ ধারণা করা ভুল। এমন কিছু আনন্দ থাকতে পারে, যার কোন বাহ্যিক বা স্নায়বিক উৎপত্তি কেন্দ্র নেই এবং বাইরের জড় উপাদানের সাথে তার কোন যোগাযোগ নেই।
এখানে আমরা এ দাবী খণ্ডন বা গ্রহণ কোনটাই করতে পারি না অথবা কারণ দর্শাতে পারি না। কিন্তু আধ্যাত্ম বিদ্যায় পারদর্শী পণ্ডিতগণ এ মত পোষণ করেন। মহান গূঢ় রহস্যবাদী পণ্ডিতগণ এ ধরনের আনন্দের প্রচলন করতে চেয়েছিলেন এবং এমনি ধরনের আনন্দের তুলনায় বস্তুগত আনন্দ যে একেবারেই তুচ্ছ তা বিবেচনা করতে চেষ্টা চালিয়েছিলেন। তাঁদের মতে মানুষ এমন এক মৌলিক সৃষ্টি যে, সে নিজেই নিজেকে আনন্দের কেন্দ্রবিন্দু ও সুখের বিশাল সমুদ্রে পরিণত করতে পারে।
মাওলানা জালালউদ্দীন রুমী এ কেন্দ্রের সাথে আমাদের পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন এবং ইঙ্গিতে বলেছেন, দেহের অভ্যন্তরে এ মহান উৎসমূল ও সমুদ্রের মোকাবেলায় বাইরের আনন্দের উৎসগুলো অতি তুচ্ছ এবং কিছুই না। মদ্যপানের ভেতরেই যে আনন্দের সন্ধান করে, তাকে উদ্দেশ্য করে রুমী বলেছেন-
কি করতে চাও তুমি নিজেকে সে সমুদ্র দিয়ে ওসব অস্তিত্ব থেকে তুমি কোন
অনস্তিত্ব খুঁজে পেতে চাও?
তুমি সুখী, তুমি ভালো, তুমি প্রতিটি আনন্দের খনি, উৎস?
তাহলে তুমি শরাবের কাছে কাছে কেন
অনুগ্রহ ভিক্ষা কর?
সুরা কি, অথবা মৈথুন বা সংগীত কি,
এর কোনটি থেকে তুমি চাও আনন্দ ও কল্যাণ?
তুমি কি বাজে বই থেকে জ্ঞান তালাশ করছো?
ভূসির মিঠাইয়ের মাঝে স্বাধ খুঁজে বেড়াচ্ছো?
মানুষ হচ্ছে অস্তিত্ব, নির্যাস সার,
আর পৃথিবী হচ্ছে বাহ্যিকে অবয়ব, প্রতিমূতি,
সবকিছুই ছায়া ও অপ্রধান
কিন্তু তুমি হচ্ছো উদ্দেশ্য।
সূর্য কখন অনুর কাছে ঋণ ভিক্ষা করেছিল?
প্রেমদেবী ভেনাস কখন একটি পেয়ালার পরিবর্তে মদের বৃহৎপাত্র চেয়েছিল?
তুমি হচ্ছো এমন এক আত্মা, যাতে কোন আনন্দ নেই,
মাতলামি ও নেশার হাতে বন্দী তুমি,
আহা সূর্য জটিলতার হাতে বন্দী, কি দুঃখ!
পৃথিবীর অধিকাংশ পণ্ডিত ব্যক্তিই সুখকে আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক কারণ বা উপাদানের সাথে সম্পর্কিত বলে বিবেচনা করেন, যদিও কারণ বা উপাদান গুলোর মূল্য ও প্রভাবের পরিমাণ নিয়ে বিরাট মতপার্থক্য আছে।
এরিস্টটল এসব ফ্যাক্টরকে তিনভাগে বিভক্ত করেছেনঃ বাহিক, শারীরিক ও আধ্যাত্মিক। এর প্রত্যেকট আবার তিনটি অপ্রধান ভাগে বিভক্ত-
- ১. বাহ্যিক কারণ বা উপাদানসমূহ- ধন সম্পদ, পদমর্যাদা, পরিবার ও গোত্র।
- ২. শারিরীক কারণ বা উপাদানসমূহ- স্বাস্থ্য, শক্তি সৌন্দর্য।
- ৩. আধ্যাত্মিক কারণ বা উপাদানসমূহ- জ্ঞান, সুবিচার ও সাহস।
স্পষ্টতঃ সুখের কারণ বা উপাদানগুলোকে উপরোক্ত তিনটি কারণ বা উপাদানের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে পারে না এবং এদের প্রত্যেকটির মধ্যে অন্যান্য কারণগুলোও উল্লেখ করা যেতে পারে। যেমন প্রগতির সহায়ক সামাজিক পরিবেশ, স্বাধীনতা, নিরাপত্তা, অনুকূল, প্রাকৃতিক ও ভৌগোলিক অবস্থা, উত্তম জাতি বা বংশ, ছোট ছেলেমেয়ে, যোগ্য স্বামী কিংবা স্ত্রীল, বিশ্বস্ত ও অকপট বন্ধু। এসবই বাহ্যিক কারণ বা উপাদান, এরপরে আছে উত্তম কণ্ঠস্বর, কাজ, সৎকাজ, এগুলো হচ্ছে শারীরিক কারণ বা উপাদান এবং সর্বশেষে আছে ঈমান, মহান অনুভূতি বা মনোভাব, মানসিক স্বাস্থ্য, দৃঢ় ইচ্ছা, শৈল্পিক ও কারিগরি প্রতিভা- এসবই হচ্ছে আধ্যাত্মিক ফ্যাক্টর।
দেহ ও আত্মার মধ্যে কতগুলো সাধারণ ফ্যাক্টর আছে। যেমন- ইবাদত, আর কতগুলো যেমন বই-পুস্তক এসবই তিনটি প্রধান কারণ বা উপাদানের মধ্যে শামিল রয়েছে।
ধারাবাহিক আলোচনা সম্পর্কে একটি জরিপ
আরো কতগুলো বিষয় আছে, যেমন- প্রভাববিস্তারকারী কারণ বা উপাদানগুলোর মূল এবং পরিমাণ, উদাহরণস্বরূপ কোনটি প্রথম শ্রেণীর পদমর্যাদার এবং কোনটি দ্বিতীয় শ্রেণীর পদমর্যাদার অন্তর্ভুক্ত। অন্যকথা প্রত্যেকটির মর্যাদার শতকরা একভাগ দশভাগ, না আরো বেশী? সুদীর্ঘ আলোচনা বা ব্যখ্যা পরিহার করার উদ্দেশ্য এসব বিষয় এখানে আলোচিত হবে না।
আরেকটু চিন্তা করার বিষয় হচ্ছে, সুখের জন্য কোন ফ্যাক্টরটি মৌলিক, যা ছাড়া চলে না এবং কোনটি মৌলিক নয় অর্থাৎ যা সুখের পূর্ণতা বৃদ্ধি করতে পারে, তবুও তার অনুপস্থিতি সুখকে দুঃখে রূপান্তরিত করে না?
তবু আরো একট বিষয় থেকে যায়, তা হচ্ছে এসব কারণ বা উপাদানগুলোর মধ্যে কোনটি প্রত্যক্ষ এবং কোনটি পরোক্ষ?
অধিকন্তু, এসব উপাদান বা কারণগুলো কি পরিবর্তনযোগ্য বা নিত্য বা অপরিবর্তনীয়? যে জিনিস একবার মানুষের জন্য সুখের কারণ বা উপাদান ছিল, তা কি সবসময় তাই আছে এবং ভবিষ্যতেও সেরকম থাকবে? অথবা এটা কি সম্ভব যে কোন বিষয় কোন এক যুগে বা সময়ে সুখের কারণ বা উপাদান হবে এবং ভিন্ন সময়ে বা যুগে দুঃখের কারণ হয়ে দাঁড়াবে?
সুখের জন্যে কি একটা সর্বাত্মক পরিকল্পনা তৈরী করা সম্ভব যদিও ওহী এবং নবুয়তের মাধ্যমে সুখলাভ করা সবযুগের জন্য যথেষ্ট? অথবা এটা কি মূলত অসম্ভব ও অসাধ্য ব্যাপার? যারা ধর্মের বিরুদ্ধে, তারা এ যুক্তি দেখিয়েছে এবং দাবী করেছে যে, অতীতে ধর্ম মানবজাতির সুখ ও প্রগতির কারণ ছিল, কিন্তু বর্তমান যুগে দুর্ভাগ্য, প্রতিবন্ধকতা ও অবক্ষয়ের কারণ হচ্ছে এই ধর্ম। ইসলামের দৃষ্টিকোণ বিষয়টি মনোযোগের দাবীদার এবং অনুসন্ধানযোগ্য। বিশেষতঃ শেষ ধর্ম হিসেবে যখন এর নির্দেশাবলী সবযুগের জন্যে প্রদান করা হয়েছে।
এতে কোন সন্দেহ নেই যে সুখের কিছু কারণ বা উপাদান পরিবর্তনশীল, একইভাবে অপর কতগুলো নিত্য বা অপরিবর্তনীয়। কিন্তু কোনটি পরিবর্তনশীল এবং কোনটি স্থির বা অপরিবর্তনীয়, তা স্থির করার জন্যে আমাদের একটি নির্ণয়ক খুঁজে বের করতে হবে। একথা কি বলা যেতে পারে যে, প্রত্যক্ষ কারণসমূহ বা উপাদানগুলো অপরিবর্তনীয় এবং পরোক্ষগুলো পরিবর্তনশীল এবং সুখ ভোগের বিধিসমূহ প্রত্যক্ষ কারণ বা উপাদানসমূহের সাথে সম্পর্কের দিক থেকে অপরিবর্তনীয় এবং যখন সেগুলো সিদ্ধান্তকারী কারণ বা উপাদানের সাথে সম্পর্কিত হয় তখন পরিবর্তনশীল হয়? যদি আমরা ইসলামী আইনকানুন সম্বন্ধে এ আলোচনা চালিয়ে যেতে চাইতাম, তাহলে আমাদের সামনে এক বিরাট অধ্যায় এসে হাজির হতো।
ভিন্ন একটি প্রশ্ন হচ্ছে, সুখ কি নিরপেক্ষ না আপেক্ষিক? যে বিষয় বা জিনিস সুখ সৃষ্টি করে, তা কি সব ব্যক্তি, জাতি, প্রত্যেক অঞ্চল ও প্রত্যেক বংশের জন্যে নির্ভুলভাবে সমান বা একই? অথবা সে একই জিনিস বা বিষয়গুলো কি বিভিন্ন ব্যক্তি, অথবা ন্যূনপক্ষে বিভিন্ন জাতি, অঞ্চল এবং বংশের চিন্তাপদ্ধতি, অভ্যাস, দৈহিক ও মানসিক কাঠামো ও ধরনের পার্থক্যের কারণে অবশ্যই ভিন্ন ভিন্ন হবে? সমগ্র পৃথিবী, সব ব্যক্তি, সকল জাতি এবং অঞ্চলের জন্যে এমন কোন একটি আইন পাওয়া যেতে পারে কি যা সমানভাবে সুখ সৃষ্টি করতে পারে? অথবা পারে না? এ বিষয়টিও ইসলামী আইনে প্রয়োগের ক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে অবধানযোগ্য।
এগুলো হচ্ছে আলোচনার বিষয়, যার জন্যে আমরা শুধুমাত্র একত্র সমাবিষ্ট বহুদৃশ্যপূর্ণ সুদীর্ঘ চিত্র তুলে ধরতে বাধ্য হয়েছি। অন্যথা একটি বই লিখেও বিষয়গুলোর প্রতি প্রয়োজনানুরূপ সুবিচার করা সম্ভবপর হতো কি না সন্দেহ।
মানুষের কি সুখ লাভের জন্য হেদায়েতের প্রয়োজন? সুখ যদি শুধুমাত্র আনন্দ ও ব্যাথা-বেদনাজনিত কষ্টের সমন্বয়ে সৃষ্টি হতো এবং আনন্দ ও বেদনা দুটি যদি প্রত্যেকটি প্রাণীর সীমিত শারীরিক যন্ত্রণা ও আনন্দের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতো, স্বাভাবিক দৈহিক পৃষ্টসাধন ও বৃদ্ধির পাশাপাশি সহজাত বৃত্তিগত কারণেই সে সম্পর্কে জ্ঞাত থাকতো, তাহলে হিদায়াতের কোন প্রয়োজন হতো না। আবার, মানুষ নিজের বুদ্ধি ও জ্ঞানের সাহাযো যা কিছু বুঝতে পারে, তাতেই যদি মানুষের প্রয়োজন সীমাবদ্ধ থাকতো এবং এভাবেই নিজের সুখের একটি সুদীর্ঘ চিত্র সে দেখতে পেতো, তাহলে এটা তার পক্ষে জ্ঞান, কলাকৌশল, সভ্যতার অগ্রগতি ও সহযোগিতার মাধ্যমে ক্রমেই নিজস্ব পথে অগ্রসর হওয়ার জন্যে যথেষ্ট হতো।
কিন্তু সুখ শুধুমাত্র স্বভাবজাত আনন্দ ও বেদনার একটি প্রশ্ন নয়। অথবা এটি কতগুলো লক্ষণীয় প্রয়োজনও নয়, যেমন অসুস্থতা অথবা নিরাপত্তাহীনতা, যার ফলে আমরা হয়তো বলতে পারি যে মানুষ পরিণামে তার প্রচেষ্টার মাধ্যমে নিরাপত্তার পথ খুঁজে পেতে পারে এবং সুখের উপায় বের করতে পারে। মানুষের প্রয়োজন একটি বা দুটিতে সীমিত নয়।
মানুষের জন্যে যে বিষয়টি সবচেয়ে অজ্ঞাত ও অস্পষ্ট, তা হচ্ছে মানুষ নিজেই এবং তার সহজাত প্রতিভা ও প্রচ্ছন্ন কর্মক্ষমতা। শিল্প ও বিজ্ঞানে মানুষ বিরাট অগ্রগতি সাধন করেছে এবং ঘনবস্তু, উদ্ভিদ ও জীবন্ত প্রাণীদের বিশ্বে বহু আবিষ্কার হয়েছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও মানুষ এখনও একটি অজানা রাশি।
মানবজাতি এখন পরমাণুর প্রাকৃতিক গঠন এবং মহাশুন্যের প্রকৃতি সম্বন্ধে একমত হতে সক্ষম হয়েছে। পরমাণু এবং মহাশুন্য সম্পর্কিত বিভিন্ন সমস্যার ওপর যে সব মতামত দেখা যায়, তা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত রাশিয়া সহ সর্বত্র একই ধরনের। সে যাহোক, সুখের উপাদান কি এবং পরিপূর্ণ সুখ হাসিলের জন্যে মানুষ কোন পথ অবলম্বন করবে সে সম্পর্কে পর্যন্ত ঐকামত প্রতিষ্ঠিত হয়নি। পঁচিশ শতাব্দী পূর্বে এমনি ধরণের প্রশ্নে পণ্ডিত ও দার্শনিকের মধ্যে যে মতপার্থক্য ছিল, তা এখনো তাছে। কিন্তু কেন? কারণ পরমাণুর অভ্যন্তরে কি আছে, তা আমরা জানতে পেরেছি। কিন্তু মানুষ আজো আমাদের অজানা রয়ে গেছে। মানুষের সুখের জন্যে পরিকল্পনা তৈরী করা নির্ভর করে মানুষের সকল প্রাতিভা, ধারণক্ষমতা, যোগ্যতা ও অর্জিত গুণরাজি এবং তার বিবর্তনবাদী প্রতিক্রিয়ার ওপর। এ সবকিছুই অনন্ত অসীমের দিকে পরিচালিত করে। সুখ কি সকল প্রতিভার বিকাশ সাধন, সকল ধারণক্ষমতার পূর্ণতা, সকল শক্তির সক্রিয়তা। এক মানুষকে অস্তিত্বের শীর্ষ পরিচালনাকারী সোজাপথ অনুসরণ ছাড়া অন্য কিছু?
অপরদিকে, এ বিষয়ে কি ঐক্যমতে পৌঁছা যেতে পারে যে, যদি তেমন কোন মহান প্রয়োজন থেকে থাকে, যা পূরণ না হওয়ার কারণে জটিলতা সৃষ্টি হতে পারে অথবা এমন কি মানব জাতির ধ্বংস ডেকে আনতে পারে, তাহলে সৃষ্টির মহান, সুসামঞ্জস্য ও সুশৃঙ্খল পদ্ধতি, যা সব সময় প্রয়োজন পূরণকালে স্বীয় শ্রেষ্ঠত্ব প্রদর্শন করে থাকে, তা এধরনের একটা শূন্যতাকে মেনে নেবে, এ প্রয়োজনকে অবহেলা করবে এবং মানবীয় দৃষ্টির বাইরের জ্ঞান, অভিজ্ঞতা ও চিন্তাধারার সীমারেখা অর্থাৎ ওহীর সীমারেখা থেকে পূত-পবিত্র, সুযোগ্য ব্যক্তিদের মাধ্যমে আধ্যাত্মিক জ্ঞান দানের উদ্দেশ্যে মানবজাতিকে হিদায়েত করতে অস্বীকার করবে?
ইবনে সিনা তাঁর লিখিত আন-নাজাত পুস্তকের শেষাংশে বলেছেন, “মানবজাতির প্রয়োজন এমন একজন ব্যক্তির, যে তাকে অলৌকিক মদদ দিয়ে পথপ্রদর্শন করে পরিচালনা করবে। মানুষের উদবর্তন বা পৃথিবীতে টিকে থাকার জন্যে এ প্রয়োজন অনেক বেশী, অনেক বড়ো, মহত্তর। চোখের পাতার জন্যে সৃষ্ট চোখের লোমের প্রয়োজন আছে, চোখের জন্যে ভ্রুর অথবা পায়ের পাতার জন্যে প্রয়োজন আছে পায়ের নীচে খালিস্থান বা ফাঁপা জায়গা। কিন্তু মানবজাতিকে অলৌকিক সাহায্য দিয়ে পথপ্রদর্শন করার যোগ্য একজগুন লোকের প্রয়োজন এসবের চাইতে অনেক বেশী।” যদিও উপরোক্ত জিনিসগুলো স্বত্বই প্রয়োজনীয়, কিন্তু তাদের সৃষ্টির জন্যে সেগুলো কোন বিশেষ বা জরুরী প্রয়োজনের প্রতিনিধিত্ব করে না।
অনুবাদঃ আহমদ ইয়াহিয়া খালেদ।