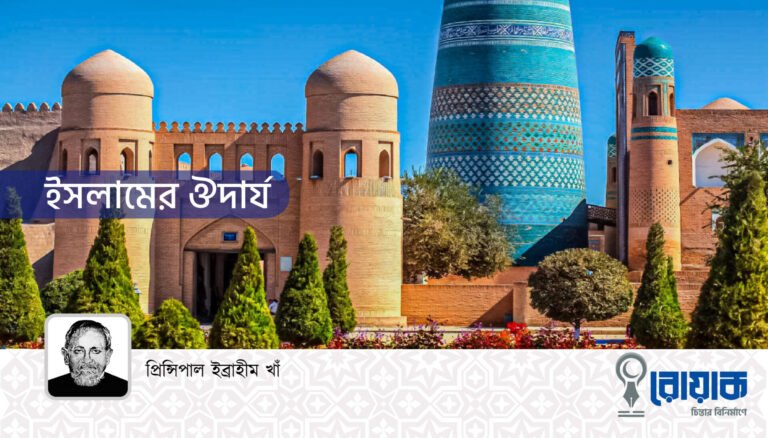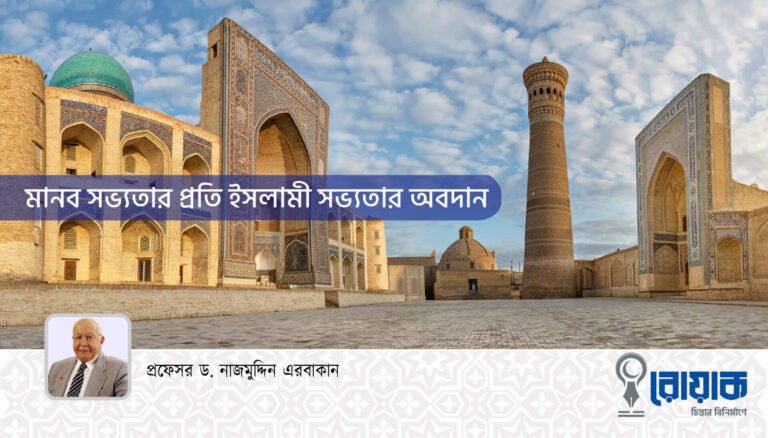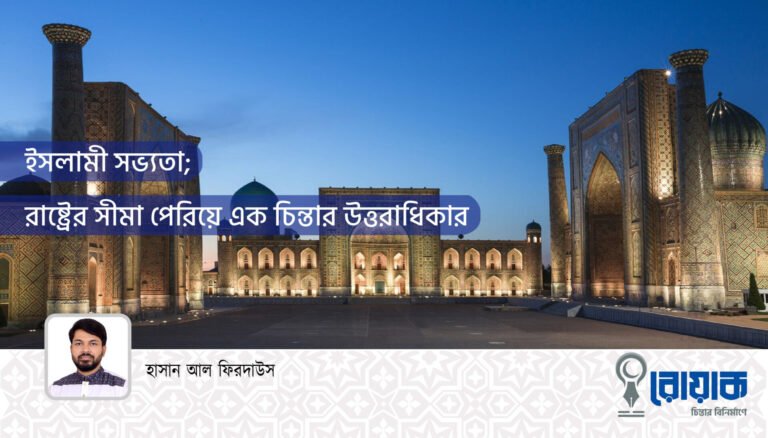Even if in the blooming spring we didn’t reach the garden, We still have the autumn to behold.
এক
আধুনিক ভারতীয় ইসলামের এক শক্তিশালী ও বর্ণাঢ্য চরিত্র হলেন মোহাম্মদ শিবলী নুমানী এবং ভারতীয় ইসলামের পুনর্জাগরণবাদী ধারার উজ্জ্বল রত্ন সৈয়দ আহমদ খান, সৈয়দ আমীর আলী, আলতাফ হোসেন হালী, মোহাম্মদ ইকবালের পাশেই তার স্থান নির্দিষ্ট হয়ে আছে । শিবলী ছিলেন একই সাথে কবি, প্রেমিক, চিন্তক, সাহিত্য সমালোচক, ঐতিহাসিক, সংস্কারক, শিক্ষাবিদ, প্যান ইসলামবাদী ও মুতাকাল্লিম । সৈয়দ আহমদ খানের হাত ধরে আলীগড় মোহামেডান এ্যাংলো ওরিয়েন্টাল কলেজে তিনি দীর্ঘদিন কাজ করেছেন, কিন্তু তিনি কখনও তাঁর অনুবর্তী হননি । উল্টো শিবলী তাঁর বিপরীতে প্যান ইসলামবাদী ভাবনায় উজ্জীবিত হয়েছেন । ১৮৯৩ সালে তিনি ইস্তাম্বুল যান, সুলতান আবদুল হামিদ-এর কাছ থেকে তিনি মেডেল নেন, দামেস্কে তিনি নকশবন্দী সুফীদের সাহচর্যে আসেন এবং কায়রোতে তিনি কিংবদন্তীতুল্য জামালুদ্দীন আফগানীর ভাবশিষ্য মুফতী আবদুহর সাথে মোলাকাত করেন। অন্যদিকে বৈচিত্র্যময় চরিত্রের অধিকারী নুমানী সৈয়দ আহমদ খানের উৎসাহে উর্দু ভাষায় ইসলামী ইতিহাস চর্চার সূত্রপাত করেন এবং এর একটি পুনর্জাগরণবাদী রং দেন। ভারতীয় মুসলমানদের রাজনৈতিক ক্ষমতার অবক্ষয়ের দিনে তিনি তাদের ঐতিহাসিক গৌরব গাঁথাকে তুলে ধরে মনস্তাত্ত্বিকভাবে শক্তিশালী করার প্রয়াস পান ।
ঔপনিবেশিকতার সূত্র ধরে শিবলীর আরেকটি উদ্বেগের জায়গা ছিল ইউরোপের বিজ্ঞান ও দার্শনিকতা ইসলামী চিন্তার মৌলিক কাঠামোকে আঘাত হানার চেষ্টা করছে এবং সেই প্রেক্ষিতে মুসলিম চিন্তার পুনর্গঠনের ভাবনাও তাকে আলোড়িত করেছে। তিনি নতুন পরিস্থিতিতে কালাম শাস্ত্রের পুনর্মূল্যায়নের পক্ষপাতী ছিলেন। কিন্তু তার এই পক্ষপাত দুর্বল চিত্তের কোনো বেদনাবিধুর আকাঙ্ক্ষা ছিল না। উল্টো তার প্রতিক্রিয়াকে বিখ্যাত ইসলামবিদ চার্লস জে. এডামস এভাবে বর্ণনা করেছেন,
Unlike many other Muslim leaders in recent times, he both recognised and acknowledged a threat to his religious faith from science and the modern intellectual milieu, and also unlike others his response did not come as defensive apologetics but as a creative reconsideration of the Islamic heritage in the light of the problems posed by science.১
কবিতাকে তিনি বেছে নিয়েছিলেন নিজের আবেগ প্রকাশের জায়গা হিসেবে এবং তার কবিতার মধ্যে অনেকখানি মূর্ত হয়েছে সমকালীন মুসলিম সমাজের চিত্র।
পশ্চিমা প্রাচ্যতত্ত্ববিদদের ইসলামোফোবিক চরিত্রের তিনি কঠোর সমালোচক ছিলেন কিন্তু পশ্চিমা বুদ্ধিজীবীদের তিনি ভূয়সী প্রশংসা করেছেন এই কারণে যে প্রাচ্যবিদরা অনেক ক্ষেত্রে ইসলামের বহু হারিয়ে যাওয়া জ্ঞানের ভাণ্ডারকে যথাযথভাবে সংগ্রহ ও সম্পাদনা করে রক্ষা করেছেন । যেমন এক সময় মুসলিম আলেমগণ গ্রীক জ্ঞানবিজ্ঞানকে আরবিতে তরজমা করে নিশ্চিত ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করেছিল ।
শিবলী ইসলামের একটি বিশ্বকোষ লেখার পরিকল্পনাও করেছিলেন। কিন্তু প্রাচ্যবিদদের অবদানের সামনে বুদ্ধিবৃত্তির জমিনে ভারতীয় উলামাদের নিঃস্ব চেহারা তাকে দারুণভাবে ব্যথিত করেছিল । শিবলী ছিলেন বরাবর স্বাপ্নিক ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের শক্তিশালী অভিঘাতের সামনে ধ্বংসোন্মুখ ভারতীয় মুসলমানদের সাংস্কৃতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক জাগরণের ভিতর দিয়ে ঘুরে দাঁড়ানোর ভাবনাই তাকে সে সময় আচ্ছন্ন করে রেখেছিল।
দুই
মোহাম্মদ শিবলী নু’মানী ১৮৫৭ সালের ৩ জুন ভারতের উত্তর প্রদেশের আজমগড়ের বিন্দওয়াল গ্রামে এক রাজপুত জমিদার পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তার আব্বা শেখ হাবিবুল্লাহ জমিদারী পেশা ছাড়াও ওকালতি ও চিনির ব্যবসা করতেন। শিবলী যেদিন জন্মগ্রহণ করেন সেদিন বিপ্লবী সিপাহীরা আজমগড়ের জেল ভেঙে বন্দীদের মুক্ত করে দেয় এবং জেলার কোষাগার খাজাঞ্চিখানা দখলে নেয় । সিপাহী অভ্যুত্থান ও পরবর্তীতে মুসলমানদের বেদনাদায়ক অভিজ্ঞতাগুলোর ভিতর দিয়ে এমনি করে শিবলী বড় হয়ে উঠেছিলেন, যা তাঁর পরবর্তীকালের সাংস্কৃতিক-বুদ্ধিবৃত্তিক চিন্তার কাঠামো নির্মাণে ভূমিকা রেখেছিল।
শিবলীর আনুষ্ঠানিক শিক্ষা শুরু হয় গ্রামের মক্তবে। এখানে তিনি কুরআন পড়া শেখেন এবং ইসলামের মৌলিক বিষয়াদির উপর পাঠ নেন । গ্রামের মক্তব থেকে তিনি জৌনপুর মাদরাসায় ভর্তি হন এবং মৌলভী হেদায়েতুল্লাহ খান রাম পুরীর তত্ত্বাবধানে কিছুদিন লেখাপড়া করার পর গাজীপুরের মওলানা ফারুক চারিয়াকোটির তত্ত্বাবধানে কিছুদিন থাকেন ও লেখাপড়া করেন । ৩
এরপর শিবলী লাখনৌর মওলানা আবদুল হাই ফারাঙ্গীমহলী এবং রামপুরের এরশাদ হোসাইন মুজাদ্দেদীর তত্ত্বাবধানে লেখাপড়া করেন । সেখান থেকে তিনি লাহোর যান এবং মওলানা ফয়জুল হাসান সাহারানপুরীর তত্ত্বাবধানে আরবি সাহিত্য পড়েন।৪
শিবলীর বারবার স্থান পরিবর্তনের স্বভাব এবং বিভিন্ন শিক্ষকের অধীনে লেখাপড়া করার অভ্যাসের কারণে তার কোনো আনুষ্ঠানিক শিক্ষা হয়নি। তিনি কোনো মাদরাসায়ই লেখাপড়া শেষ করতে পারেননি। কিন্তু তার এই ভ্রাম্যমাণ অবস্থার মধ্যেই তিনি ফিকাহ (ইসলামী আইন), উসুল (ইসলামী নীতিশাস্ত্র), হাদিস (রসুল (স.) এর কথা ও কাজ), মুনাজরা (ধর্মীয় বিতর্ক), মানকুলা’ত (যুক্তিবিজ্ঞান), মানকুলাত (হাদিস বিজ্ঞান), জ্যোতির্বিদ্যা প্রভৃতিতে পারদর্শী হয়ে ওঠেন। তার অন্তত দুজন শিক্ষক ফারুক চারিয়াকোটি ও এরশাদ হোসাইন রামপুরী ছিলেন। নিষ্ঠাবান হানাফী এবং তাদের প্রভাবে শিবলীও হানাফী মতালম্বী হয়ে ওঠেন এবং তার এই বিশ্বাস আজীবন অটুট ছিল। শিবলীর নিসবাহ নুমানী ইমাম আবু হানিফার নামের অংশ নুমান থেকে নেয়া।
শিবলী কোনো আনুষ্ঠানিক ইংরেজি শিক্ষা পাননি কিন্তু আলীগড়ে অবস্থানকালে তিনি এ ভাষার উপর দক্ষতা অর্জন করেছিলেন। শিবলীর ভ্রাম্যমাণ লেখাপড়ার ইতি ঘটে আব্বার সাথে হজ্বে যাওয়ার পর (১৮৭৬)। হজ্ব থেকে প্রত্যাবর্তনের পর তিনি আর কোনো লেখাপড়া করেননি। বরং বিচিত্র রকমের বইপত্র পড়ে তিনি রীতিমত স্বশিক্ষিত হয়ে ওঠেন।
আব্বার পরামর্শে তরুণ শিবলী ১৮৭৯ সালে আইন পরীক্ষা দিয়ে অকৃতকার্য হলেও দ্বিতীয়বার ১৮৮১ সালে কৃতকার্য হন এবং আইনজীবী হিসেবে লাখনৌতে কাজ শুরু করেন কিন্তু অচিরেই তিনি এই কাজ ছেড়ে দেন এবং তিনি উপলব্ধি করেন এটা তাঁর উপযুক্ত পেশা হতে পারে না ।
জীবনের শুরুতেই অকৃতকার্যতা অবশ্য শিবলীকে নিরুৎসাহিত করতে পারেনি। বরং তিনি মনে করতেন এই অকৃতকার্যতার কারণ হচ্ছে তার অমনোযোগিতা ও অনাগ্রহ। এর মানে এই নয় তিনি সফল হওয়ার যোগ্যতা রাখেন না। তিনি তার বিশ্বাসকে প্রমাণ করে দেখান যখন তিনি আলীগড় কলেজে শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ পান । এইভাবে তিনি তার স্বপ্ন জয়ের দিকে অগ্রসর হন।
আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসে শিবলী নুমানী একজন খুবই গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি এবং আলীগড়ে বসেই তার লেখক জীবনের সূত্রপাত। তিনি ১৮৮৩ সালে ফারসির প্রভাষক ও আরবির সহকারী প্রভাষক হিসেবে আলীগড় কলেজে যোগ দেন।
স্যার সৈয়দ আহমদ খানের সাথে মোলাকাতের পর শিবলীর অনুসন্ধানী মন তৃপ্ত হয় এবং স্যার সৈয়দ শিবলীকে তার ব্যক্তিগত গ্রন্থাগার ব্যবহারের অনুমতি দেন । এই গ্রন্থাগারে বসে জ্ঞান রাজ্যের এক বিশাল জগত তার সামনে উন্মুক্ত হয় এবং ইউরোপ থেকে প্রকাশিত ইসলাম বিষয়ক ও আরবি সাহিত্যের অসংখ্য বই। তিনি দেখার ও পড়ার সুযোগ পান । এই সময় বিখ্যাত প্রাচ্যবিদ টি ডব্লিউ, আরনল্ড আলীগড়ে দর্শনের অধ্যাপক হিসেবে কর্মরত ছিলেন এবং শিবলীর সাথে তার অন্তরঙ্গ সম্পর্ক তৈরি হয়। শিবলী দেখেন আরনল্ডের সাথে তার এক ধরনের সাদৃশ্য আছে। এইভাবে তারা লেখাপড়া ও ভাব বিনিময়ের জগতে একে অপরের অংশীদার হন এবং পরস্পরের আনার্জনের সুবিধার জন্য লেখাপড়ার বিষয়বস্তুর আদান প্রদান শুরু হয়। আরনল্ড ইউরোপ থেকে শিবলীর জন্য বই পুস্তক, তথ্যাদি সংগ্রহ করে এনে দিতেন এবং শিবলীকে ফরাসী ভাষা শেখান। অন্যদিকে শিবলী আরনল্ডকে আরবির বিষয়াদি সংগ্রহ করে দেন। এইভাবে দুই মেধাবী পণ্ডিত পরস্পরের ক্ষুধার্ত মনকে তৃপ্ত করেন। এটা ছিল ব্রিটিশ-মুসলিম বন্ধুত্বের একটা বড় নজীর। সম্ভবতঃ স্যার সৈয়দ এরকম স্বপ্নই দেখেছিলেন । ৭
আলীগড়ে থাকতে শিবলী দুটো জাতীয় জাগরণমূলক কবিতা লিখেছিলেন, কাসিদা-ই-ইনিভিয়া (১৮৮৩) এবং মসনবীয়ে সুবে উম্মীদ (১৮৮৪)। এ দুটো কবিতায় ভারতীয় মুসলমানদের জেগে উঠে আলীগড় আন্দোলনের সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার আহ্বান ছিল । এ সময় তিনি নিজ শহরে একটি আধুনিক স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন এবং নাম দেন জাতীয় স্কুল। আলীগড়ে থাকতেই তিনি তার প্রথম গবেষণামূলক নিবন্ধ ‘মুসলমানোন কি গুজাশতা তালিম‘ লেখেন এবং আলীগড় কলেজ ম্যাগাজিনের জন্য লেখেন ‘জিজিয়া’, ‘হুকুক আল জিম্মিইন’, ‘ইসলামী কুতুবখানা’, ‘কুতুবখানা-ই-ইস্কেন্দারিয়ার মতো চিন্তামূলক প্রবন্ধ। উল্লেখ আলীগড়ে বসেই তিনি ‘আল মামুন’, ‘সিরাত আল নুমান’, ‘আল ফারুকের‘ মতো বিখ্যাত বইগুলো লিখেছিলেন।
১৮৯২ সালে শিবলী ও আরনল্ড দুই বন্ধু একত্রে ইস্তাম্বুল সফর করেন। পরে অবশ্য আরনল্ড শিবলীর সফরসঙ্গী হননি । শিবলী তার ভ্রমণ অব্যাহত রাখেন এবং মিশর ও সিরিয়া ঘুরে দেখেন । সেখানকার বিখ্যাত কয়েকজন ব্যক্তিত্বের সাথে তার মোলাকাত হয়। এই সফরকালে তিনি এসব দেশের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, গ্রন্থাগার, যাদুঘর ঘুরে দেখেন এবং সেখানকার শিক্ষাব্রতীদের সাথে আলোচনা করেন । এখানকার আধুনিক ও ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর সিলেবাস ও কারিকুলাম খুটিয়ে খুটিয়ে পর্যবেক্ষণ করেন যার অভিজ্ঞতা, পরবর্তীকালে দেশে ফিরে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সিলেবাস প্রণয়নের সময় তার প্রচুর কাজে লাগে। তবে এসব প্রতিষ্ঠানের পুরনো ধাঁচের সিলেবাস তাকে প্রাণিত করেনি, উল্টো এর মধ্যে নতুনত্ব ও উদ্ভাবনীমূলক কিছু না থাকায় তিনি কিছুটা আশাহত হয়েছিলেন।
তুরস্কে অবস্থানকালে তাকে সে দেশের সরকার ‘তমঘায়ে মজিদী’ খেতাব দেয়। দেশে ফেরার পর তিনি বিদেশ ভ্রমণের অভিজ্ঞতা নিয়ে লেখেন ‘সফরনামা ই-রুম ও মিশর-ও-শাম’ (১৮৯৩)। একই বছর ব্রিটিশ সরকার তাকে ‘শামসুল উলামা’ উপাধি দেয়। তিনি একই সাথে এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মানিত সদস্য হন এবং আলীগড়ের পাশাপাশি কলা বিভাগের লেকচারার হিসেবেও যোগ দেন। আলীগড় কলেজের সমৃদ্ধ কুতুবখানাটি ছিল শিবলীর প্রিয় স্থান এবং তিনি মনে করতেন শিক্ষক হিসেবে তার সামান্য বেতনের চেয়ে এর গুরুত্ব অনেক বেশি তাৎপর্যপূর্ণ। মুসলিম সভ্যতা নিয়ে দীর্ঘ পড়াশুনার পর তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন মুসলমানরা এক সময় গৌরবের শিখরে উঠেছিল। মুসলমান দেশগুলোতে চলমান শিক্ষা ব্যবস্থার সংস্কার করতে পারলে তারা আবার তাদের হৃত গৌরব ফিরে পাবে । তিনি খেয়াল করেন মুসলিম দেশগুলোর শিক্ষা ব্যবস্থা তাদের পতন ও পশ্চাদপসরণের জন্য দায়ী। এই প্রেক্ষিতে তিনি আধুনিক ও ঐতিহ্যবাহী শিক্ষার সমন্বয়ে একটি শিক্ষা ব্যবস্থার পক্ষপাতী ছিলেন, যা কিনা তাদের পশ্চাদপদতা দূর করতে পারবে।
আলীগড়ে থাকতে সেকালের তারকা ব্যক্তিত্ব মুহসিন-উল-মূলক, আলতাফ হোসেন হালী, নাজির আহমদ, আবদুল রাজ্জাক কানপুরী, বিলগ্রামী ভ্রাতৃদ্বয়, সৈয়দ আলী, সৈয়দ হুসাইন প্রমুখের সাথে তার সখ্যতা হয় মওলানা মোহাম্মদ আলী ও জাফর আলী খানের মতো কীর্তিমান ব্যক্তিরা ছিলেন তার ছাত্র, যাদের উপর তার ব্যক্তিত্বের বড় প্রভাব পড়েছিল। সৈয়দ আহমদ খানের ইন্তিকালের পর তিনি আলীগড় কলেজ ছেড়ে দেন এবং লাখনৌর নাদওয়াত-উল-উলামা নিয়ে তার আগ্রহ তৈরি হয়। শিবলীর আলীগড় কলেজ ছেড়ে দেয়ার ঘটনায় সেইকালে মুসলিম সমাজে বেশ আলোড়ন তৈরি হয়েছিল যাই হোক এ সময় তিনি নিজের শহর আজমগড়ে তৈরি স্কুলটির তত্ত্বাবধান করেন এবং তার সুবিশাল ব্যক্তিগত কুতুবখানাটি এখানে স্থানান্তর করেন। এর মধ্যে এলাহাবাদ, লাখনৌ, কাশ্মীরের বিভিন্ন স্থান ভ্রমণ করেন। ১৮৯৯ সালে রোমে অনুষ্ঠিত প্রাচ্যতত্ত্ববিদদের সম্মেলনে যোগ দিতে চেয়েছিলেন, কিন্তু পারেননি। ইরানে যাওয়ার ইচ্ছা ছিল কিন্তু সেটাও পূরণ হয়নি। পারিবারিক সংকট, দ্বিতীয় বিবাহ, পিতার মৃত্যু প্রভৃতি তার ব্যক্তিজীবনকে দারুণভাবে ধাক্কা দেয়। পুরনো বন্ধু আরনল্ড লাহোরে দাওয়াত দেয়া সত্ত্বেও যেতে পারেননি। উল্টো ১৯০১ সালে হায়দারাবাদে চলে যান, যেখানে তিনি সার রিশতা-ই-উলুম ও ফুনুন-এর নাজিম নিযুক্ত হন এবং দাগ, শারার, বিলগ্রামী প্রভৃতি মশহুর সাহিত্যিকদের সাহচর্যে আসেন । হায়দারাবাদে বসে তিনি আল গাজ্জালী, ইলম আল-কালাম (১৯০২), মাওয়াজিনা-ই-আনিস-ও-দাবীর (১৯০৩) ও সাওয়ানীহ মওলভী রুমের (১৯০৪) মতো বিখ্যাত বই লেখেন । হায়দারাবাদেও তিনি স্থায়ী হতে পারেননি। সেখানকার স্থানীয় রাজনীতির শিকার হয়ে তিনি চাকরি ছেড়ে দেন। মুহসিন-উল-মুলক তাকে পুনরায় আলীগড়ে ফিরে আসার আহ্বান জানালে তিনি তা একপ্রকার প্রত্যাখ্যান করেন ।
১৯০৫ সালে তিনি লাখনৌর নাদওয়াত-উল-উলামা মাদরাসার অধ্যক্ষের দায়িত্ব নেন এবং এটিকে নানাভাবে সমৃদ্ধ করেন অন্যদিকে নিজের জন্য শিক্ষা, রাজনীতি ও রোমাঞ্চ মিলিয়ে এক বৈচিত্র্যময় জীবনের শুরু হয়। শিবলী নাদওয়ার সদস্য ও পৃষ্ঠপোষকের সংখ্যা বাড়ান । ফান্ড বৃদ্ধি করেন এবং এর অবকাঠামোগত বিপুল উন্নয়ন কাজ করেন । তার তত্ত্বাবধানে নাদওয়ার সিলেবাস, শিক্ষাপদ্ধতি ও শিক্ষকদের ভিতরে আমূল পরিবর্তন সাধিত হয়। বিশেষ করে তিনি তার ছাত্র সৈয়দ সুলায়মান নদভী, আবদুল আলম, আবুল কালামকে নিজের মতো করে গড়ে তোলেন । নাদওয়ায় তিনি শিক্ষামেলার আয়োজন করেন যেখানে প্রধান অতিথি হিসেবে আগা খান ও রশিদ রিদার মতো বিখ্যাত ব্যক্তিরা উপস্থিত হন । নাদওয়ার মুখপত্র আল-নাদওয়া তার সম্পাদনায় নিয়মিত প্রকাশিত হতে থাকে, যেখানে তার নিজের লেখা গবেষণা নিবন্ধও স্থান পেতো, যেগুলো নিয়ে পরবর্তীকালে আট খণ্ডে মাকালাত প্রকাশিত হয়। মোহাম্মদ আলীর অনুরোধে তিনি আওরঙ্গজেবের উপর (১৯০৬-১৯০৮) । ধারাবাহিকভাবে প্রবন্ধ লেখেন এবং পাঁচ খণ্ডে লেখেন কবিতার ইতিহাস শির-আল আজম (১৯০৮-১৯১২), যেটি পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বছরের সেরা বই হিসেবে নির্বাচিত ও পুরস্কৃত হয়। মোহাম্মদ আলীর অনুরোধে মারগোলিয়ণকৃত রসূলের জীবনীর প্রত্যুত্তরে ১৯১২ সালে তিনি সিরা-আল নুমান লেখা শুরু করেন এ সময় বোম্বে সফরকালে বিখ্যাত ফাবদী ভগ্নিদের সাথে তার দেখা হয় বিশেষ করে আতিয়া বেগমের সাথে তার স্থায়ী ঘনিষ্ঠতা তৈরি হয়। আতিয়া বেগমকে নিয়ে তার লেখা কবিতা দাস্তাই-গুল (১৯০৬-১৯০৭) ও বুয়ে গুল (১৯০৮) নামে প্রকাশিত হয় আতিয়ার কাছে লেখা তার আকর্ষণীয় চিঠিগুলো ‘ঘুতুত-ই-শিবলীতে’ (১৯০৬-১৯০৯) সংকলিত হয়েছে। এ সময় তিনি অনেক ইসলামী ও রাজনৈতিক কবিতা (১৯১১-১৯১৩) লেখেন যা তার কুল্লিয়াতে সংকলিত হয়েছে । তার বিখ্যাত রাজনৈতিক প্রবন্ধ ‘মুসলমানোন কি পলিটিকাল কারওয়াত’ ১৯১২ সালে প্রকাশিত হয়।
আলেমদের সাথে কাজ করার আন্তরিক ইচ্ছা থাকলেও তার পক্ষে সেটা শেষ পর্যন্ত সম্ভব হয়নি। নাদওয়ার সিলেবাস নিয়ে তার লেখা প্রবন্ধ ‘মাসালা-ই ইরতিকা আওর ডারউইন’ এবং তার বই আল কালামের কোনো কোনো মন্তব্য নিয়ে আলেমরা তীব্র সমালোচনা করে । এ প্রেক্ষিতে তিনি নাদওয়া থেকে পদত্যাগ করেন এবং আজমগড়ে ফিরে যান । এখানে তিনি প্রতিষ্ঠা করেন দারুল মুসান্নিফীন- লেখক বাড়ি । শিবলী তার নিজের বাড়ি, কুতুবখানা এই প্রতিষ্ঠানের জন্য দান করে দেন । এখানে বসে তিনি সিরাত আল নবী লেখার কাজ করেন এবং ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ের উপর শিক্ষার্থীদের প্রশিক্ষণ দেন। শিবলী আজমগড়ে ১৯১৪ সালের ১৮ নভেম্বর ইন্তিকাল করেন এবং এখানেই চিরনিদ্রায় শায়িত হন ।
তিন.
৩৫ বছর বয়সী শিবলী নুমানী যখন তার পশ্চিম এশিয়া সফরের কাহিনী লেখার সিদ্ধান্ত নেন তখন তিনি এই বলে কৈফিয়ত দেন যে তার এই সফরনামা লেখার কোনো ইচ্ছাই ছিল না। তার বন্ধু ও পরিবারের সদস্যদের কারণে তাকে এই কাজ করতে হচ্ছে যাতে তারা ভারতের বাইরের মুসলমানদের সম্বন্ধে জানতে পারে। ১৯ শতকের শেষের দিনগুলো ছিলো বহু মুসলিম চিন্তানায়কদের মতে ভারতীয় মুসলমানদের জন্য বড় দুর্দিন। শিবলী তাই ভারতের বাইরের মুসলমানদের কথা বিবৃত করে আশা প্রকাশ করেছিলেন হয়তো এটা ভারতীয় মুসলমানদের উপকারে আসতে পারে। জাহাজে করে যখন তিনি বোম্বে হয়ে এডেন, সাইপ্রাস, বৈরুত, পোর্ট সাঈদ ও ইজমির অতিক্রম করেন তখন তিনি আশা প্রকাশ করেন এই সব শহরের সামাজিক জীবনের বর্ণনা যা তার সফরনামায় বিবৃত হয়েছে তা ভারতীয় মুসলমানদের আধ্যাত্মিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক জাগরণে ভূমিকা রাখবে । এর মধ্যে শিবলী তুরস্ককে বিশেষ চোখে দেখেছিলেন, কারণ Numani looked at Turkey in particular, because the Ottoman Empire appeared to him to be the last bastion against the colonial onslaught.৯
শিবলী যখন তার ভ্রমণ কথা লেখেন তখন উর্দু ভাষায় ভ্রমণ সাহিত্য একটা জনপ্রিয় ধারা হয়ে উঠেছে । তিনি তার সফর নামার ভূমিকায় লেখেন তার এ বইয়ে প্রচলিত ভ্রমণ সাহিত্যের স্বাদ পাওয়া যাবে না। তিনি আরো লেখেন, Readers who are seeking to read this as a typical travelogue will not be able to enjoy it. ১০
শিবলী তার পাঠকদের ভ্রমণস্থলের দৃশ্যাবলী কিংবা অভিজ্ঞতার কথা ঠিক বলতে চাননি । তিনি মূলতঃ তার সফরনামার ভিতর দিয়ে এক আন্তর্জাতিক মুসলিম সম্প্রদায়ের কথা সাম্রাজ্যবাদের দেয়াল দিয়ে ঘেরা ভারতীয় মুসলমানদের কাছে তুলে ধরতে চেয়েছেন, যাদের নৈতিক, সাংস্কৃতিক, বুদ্ধিবৃত্তিক ও রাজনৈতিক অবস্থান বাকি মুসলিম বিশ্বের কাছে প্রকৃতপক্ষে অধরা হয়ে আছে শিবলীর কাছে তুরন্ত ছিল একটা তাৎপর্যপূর্ণ ভূগোল- Significant geography(১১) সাহিত্যে এই শব্দটা ধার করা হয়েছে দক্ষিণ এশিয়ার সাহিত্য বিষয়ক পণ্ডিত ফ্রানসিসকা ওরসিনির কাছ থেকে, যা কিনা প্রচলিত বিশেষ বিশেষ সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক কেন্দ্রকে প্রধান ও অন্যান্যরা প্রান্তিক এই ধারণাকে চ্যালেঞ্জ করে । পশ্চিমা ‘উৎপাদন’ ও পূর্বীয় ‘অনুকরণ’ সাম্রাজ্যবাদী এই তত্ত্ব থেকে এখানে সরে আসা হয়েছে এবং ‘তাৎপর্যপূর্ণ ভূগোলের ধারণাকে সাহিত্যের বহুভাষিক কেন্দ্রগুলোর ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় রাজা রামমোহন রায় ভারতের প্রথম সংবাদপত্র ‘মীরাত-উল-আকবর’ প্রতিষ্ঠা করেন। গালিব ও ইকবালের মতো বিখ্যাত উর্দু কবিরা ফার্সীতে কবিতা লিখেছেন অথবা দেওবন্দে একটা গুরুত্বপূর্ণ সংখ্যক হাদিসের আলোচনা আরবিতে হয়েছে ।
এই প্রথম কিন্তু ‘মুসলিম দুনিয়া’ নিয়ে ভাবা হয়নি বা সেখানে কেউ যায়নি এবং শিবলীর বর্ণনার ভিতর দিয়েও দেখা যায় ভারতীয়রা দূরে দূরে ছড়িয়ে পড়েছে। তিনি ইস্তাম্বুলে ভারতীয়দের আসা ও অবস্থান দেখে এবং তুর্কীদের উপরের শ্রেণিতে তাদের মেলামেশা দেখে বিস্মিত হয়েছেন। তিনি আরো উল্লেখ করেছেন, মুসলমানরা এখানে অন্যান্য ধর্ম সম্প্রদায়ের তুলনায় নিম্নস্থানে অবস্থান করছে। উদাহরণস্বরূপ এখানে বড় বড় ব্যবসায়ী হিসেবে খ্রিস্টান ও ইহুদীদের প্রভাবশালী অবস্থান তার তীক্ষ্ণ নজর এড়ায়নি এবং তাদের বাড়িঘরও অনেক সুন্দর ও পরিপাটি করে সাজানো। তিনি তুরস্কে নারীদের মর্যাদাপূর্ণ অবস্থান দেখে প্রীত হয়েছেন এবং ফাতিমা খানম নামে একজন মহিলা বুদ্ধিজীবীর কথা বলেছেন । অবশ্য ইস্তাম্বুলে শিবলীর মুসলমানদের দুর্দশার বর্ণনাকে অনেক বিশ্লেষক স্বীকার করেননি। যেমন ডানিয়েল মাজক্রোউইকজ শিবলীর সফরনামাকে বলেছেন Travel of reform. তার ভাষায় “the depiction of the entire ummah as impoverished is a rhetorical device meant to inspire Indian Muslims into action. ১২
মাজক্রোউইকজ আরো লিখেছেন : both India and Turkey had once belonged to the larger Persianate world through the medium of Persian language and courtly and poetic culture one could expect to integrate easily into high society
ক্লাসিকাল ইসলামী শিক্ষায় পারদর্শী, আরবি-ফারসিতে প্রবুদ্ধ উত্তর ভারতের (১৩) অভিজাত শিবলীর পক্ষে তাই ইস্তাম্বুলের পরিবেশের সাথে সহজে মিশে যাওয়া মোটেও কষ্টকল্পিত হয়নি। ক্রিমিয়ার যুদ্ধের পর ব্রিটিশ ও উসমানী সাম্রাজ্যের দ্বন্দ্বের প্রেক্ষিতে শিবলী অবগত ছিলেন তিনি এমন এক সাম্রাজ্যে পা রাখতে যাচ্ছেন যা কিনা অতীতে গৌরবের শিখরে উঠেছিল। তারপরেও শিবলীর কাছে মনে হয়েছে অবক্ষয়ের পরে এই মুসলিম জগত আজও ভারতীয় মুসলমানদের অনুপ্রেরণাস্থল হতে পারে। শিবলীর সফরনামার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য অংশ হচ্ছে মুসলিম দুনিয়া নিয়ে ইউরোপীয় লেখকদের লেখার নিপুণ পর্যালোচনা। সফরন মোর ভূমিকায় তিনি ইউরোপীয় লেখকদের মুসলিম দুনিয়াকে বুঝার ক্ষেত্রে এক ধরনের অসহিষ্ণুতার সমালোচনা করেছেন এবং সামান্য অভিজ্ঞতাকে তারা একটা বিরাট জনগোষ্ঠীর ক্ষেত্রে সাধারণীকরণ করে ফেলেছে বলে তিনি মনে করেন। তিনি কৌতুকের সাথে লিখেছেন : ….as if civilisational knowledge has magically and suddenly been bestowed upon them 18
তিনি তুর্কী সমাজের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটকে আলোচনায় আনেননি, কারণ এর জন্য তিনি নিজেকে যথোপযুক্ত মনে করেননি। কিন্তু ইউরোপীয় বুদ্ধিজীবীদের প্রবণতা সম্পর্কে তিনি বলেছেন, এটি খণ্ডাংশকে রাতারাতি পূর্ণাঙ্গে পরিণত করে।
তিনি ইউরোপীয় লেখকদের দ্বারা তুর্কী জাতিকে সচরাচর ‘দস্যু’ ও ‘পশ্চাৎ পন্থী’ হিসেবে চিহ্নিত করার প্রবণতার তীব্র সমালোচনা করেন। তিনি আরো বলেন, এ আধিপত্যবাদী প্রবণতার প্রভাবে পাঠকের মনে এক ধরনের নির্জীবতা নেমে আসে যার ফলে তারা এই ভুল ধারণাগুলোকে যথাযথভাবে প্রশ্ন ও পর্যালোচনা করতে পারে না ।
শিবলী এ বইয়ে অকল্পনীয় এক তিক্ত সুরে মন্তব্য করেছেন অধিকাংশ ইউরোপীয় লেখক তুর্কী জনজাতি ও ভূগোল সম্বন্ধে একই রকম কথা বলেছেন, যেমন তুর্কীদের বৈদেশিক ঋণ কিংবা যৌন অমিতাচার, কিন্তু তাদের চোখে এদের কোনো ইতিবাচক দিক চোখে পড়ে না। শিবলী লিখেছেন, পশ্চিমের লেখকেরা তাদের খ্রিস্টান পথ প্রদর্শকদের ইশারায় মুসলিম জগত সম্বন্ধে ভাসাভাসা, অপর্যাপ্ত উপসংহার টেনে ফেলেন। তিনি এ প্রসঙ্গে নমুনা হিসেবে বলেন, তার এক ইউরোপীয় সহকর্মীকে গাইড বুঝিয়েছিল কায়রোর আল আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ে অমুসলমানরা প্রবেশ করতে পারে না। শিবলী অবাক হন ‘মুসলিম অসহিষ্ণুতার’ গল্প নিয়ে পূর্বানুমানের ভিত্তিতে তার এই বন্ধু সহজেই এই মিথ্যাচারকে বিশ্বাস করে নেয় ।
শিবলী দেখেছেন ভারতের ক্ষেত্রেও ইউরোপীয় লেখক ও ভ্রমণকারীরা একই রকম সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলে। এডওয়ার্ড সাঈদের ‘ওরিয়েন্টালিজম’ লেখার প্রায় একশ বছর আগে শিবলী বুঝতে পারেন এই ‘বাস্তবতা’ মোকাবেলা করা কত কঠিন। এ যেন তার ভাষায় bird singing her melody in a European drum house.
শিবলী যুক্তি দেন, ধর্মীয় বিদ্বেষ এখানে রীতিমত শিল্প, সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক প্রপাগান্ডায় পরিণত হয়েছে। যখন কোনো নির্ভরযোগ্য সূত্রের হদিস পাওয়া যায় না অথচ ধর্মীয় বিদ্বেষ থাকে পুরোপুরি। শিবলী লিখেছেন, ইউরোপীয়রা তখন ঘটনাকে উপন্যাসে পরিণত করে। শিবলীর ভাষায়, They took up a cleverer approach, the problems of Islamic rules, societies and communities were written about as “historical” facts, and by producing biased writings such as novels, short-stories and poetry they made these views settle so deeply that they can not be changed.
শিবলী যখন এই মুসলিম দেশগুলো সফর করেন তখন তিনি ছিলেন আলীগড় কলেজের শিক্ষক । কিন্তু তিনি কলেজের প্রতিষ্ঠাতা ও বিখ্যাত সংস্কারক সৈয়দ আহমদ খানের সাথে সব বিষয়ে সহমত পোষণ করেননি। সৈয়দ আহমদ খান চেয়েছিলেন ইসলামী চিন্তাকে গোড়ামী মুক্ত করতে এবং সেইভাবে তিনি আলীগড় আন্দোলনের পত্তন করেন যার লক্ষ ছিল মুসলমানদেরকে আধুনিক ও ব্রিটিশ শিক্ষা দিয়ে ঔপনিবেশিক আমলাতন্ত্রে চাকরির সুযোগ করে দেয়া।
শিবলী ছিলেন রাজনৈতিকভাবে প্যান ইসলামবাদী এবং তিনি আলীগড় মোহামেডান এ্যাংলো ওরিয়েন্টাল কলেজের আধুনিকায়ণের উদ্যোগ ও দারুল উলুম দেওবন্দের ঐতিহ্যবাহী ধারার মাঝামাঝি একটি পথ খোঁজার চেষ্টা করেছিলেন । আলীগড় আন্দোলনের সাথে তার আদর্শিক দূরত্বের কারণ ছিল, তিনি মনে করেছিলেন এখানে ইসলামী বুদ্ধিজীবিতাকে যথেষ্ট গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে না। তাই তিনি লাখনৌর নাদওয়াতুল উলামা মাদরাসাকে কেন্দ্র করে পরবর্তীতে এই দুই ধারাকে সমন্বয় করার চেষ্টা করেছিলেন। শিবলীর কিন্তু কায়রোর আল আজহারের শিক্ষা ব্যবস্থাও ভালো লাগেনি এবং এখানকার মুখস্থ বিদ্যার রেওয়াজকে তিনি কৌতুকভরে বলেছিলেন, এটা কি করে ইসলামী শিক্ষার ভরকেন্দ্র হতে পারে।
তারপরেও বলতে হবে শিবলীর এই বই যেকোনো বুদ্ধিবৃত্তিমূলক উদ্যোগের চেয়েও অতিরিক্ত কিছু । এখানে যেমন তিনি এসব মুসলিম দেশগুলোর শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে পর্যালোচনা করেছেন তেমনি আকর্ষণীয় ঘটনা- দর্শনীয় স্থানগুলো সম্পর্কে তথ্য এবং তার শাসক ও এলিটশ্রেণীর সাথে সাক্ষাতের কথাও বলেছেন । এছাড়াও রয়েছে এখানকার জীবনধারা এবং মেয়েদের প্রতি এখানকার আচরণের কথাও এ বইতে আছে । শিবলী ভারতীয় মুসলমানদের কাছে অন্যান্য দেশের মুসলমানদের কথা তুলে ধরতে চেয়েছেন । অন্যথায় তারা ইউরোপীয় লেখকদের লেখা পড়ে বিভ্রান্ত হবে। তিনি এ বইয়ের মাধ্যমে ভারতের বাইরের মুসলমানদের একটা ভিন্ন চিত্র উপস্থাপন করেছেন। একই সাথে বিশেষ করে তুরস্কের শিক্ষা প্রণালীকে মডেল হিসেবে উপস্থাপন করেছেন, যেটার পরীক্ষা-নিরীক্ষা তিনি নাদওয়াতুল উলামায় বসে করেছিলেন। শিবলী আলীগড় ও দেওবন্দের বাইরে যেয়ে একটা মধ্যবর্তী জমিন খোঁজার চেষ্টা করেছিলেন এবং দেখার বিষয় হচ্ছে সেই জমিনে তিনি তুরস্ককে জায়গা দিয়েছিলেন। তিনি অবশ্য যা দেখেছেন তা কিন্তু এক কথায় সমালোচনার দৃষ্টিতেই গ্রহণ করেছেন এবং নিজের প্রস্তাবিত প্রগতির ধারণাকেও সমালোচনা করার চেষ্টা করেছেন বিশেষ করে লিঙ্গ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সামরিক দক্ষতা প্রভৃতি মানদণ্ড ব্যবহার করে । কিন্তু তুরস্ককেই শেষ পর্যন্ত Significant geography ধরে তিনি তার বইকে একদিকে তুরস্ক ও অন্যদিকে ভারতের মুসলমানদের কাছে সমান তাৎপর্যপূর্ণ হিসেবে তুলে ধরেছেন ।
চার
শিবলী নুমানী প্রধানত ইতিহাস ও জীবনীকার হিসেবে জীবদ্দশায় প্রচুর খ্যাতির অধিকারী হয়েছিলেন এবং আধুনিক উর্দু সাহিত্যে তিনি একজন প্রধান ঐতিহাসিক হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছেন। আলীগড়ে অবস্থানকালে এখানকার বুদ্ধিবৃত্তিক পরিবেশ তার সৃষ্টিশীলতার বিকাশে বড় রকম ভূমিকা রেখেছিল। বিশেষ করে স্যার সৈয়দ আহমদ খান, যিনি নিজেও রসূলের জীবনী ও ইতিহাস বিষয়ে প্রচুর লিখেছেন, তাঁর প্রেরণা শিবলীর লেখক সত্তা নির্মাণে যুৎসই উপাদান হিসেবে কাজ করেছে । আলীগড়ে অবস্থান কালেই তিনি ইউরোপের কার্লাইল, হেগেল প্রভৃতির মতো বিখ্যাত লেখকদের লেখালেখি দ্বারা হয়েছিলেন এবং এদের মাধ্যমেই তিনি ইংরেজি, জার্মান ও ফরাসী ভাষায় ইসলামের উপর লেখালেখির সাথে পরিচিত হন । এ সমস্ত রচনা তাকে ইতিহাস লেখার কাজে আধুনিক গবেষণা ও পর্যবেক্ষণের নীতিগুলো সম্বন্ধে পরিচিত করে এবং ইতিহাস সম্বন্ধে চিন্তাভাবনা করতে শেখায়। আলীগড়ে যখন সৈয়দ আহমদ খান রাজনীতি ও সামাজিক কাজকর্মে বেশি জড়িয়ে । শিবলী তখন তার ঐতিহাসিক মিশনকে এগিয়ে নেন এবং এটিকে এতদূর পড়েন সমৃদ্ধ করেন যে তার সমকালে আর কেউ করতে পারেনি । শিবলীর ইতিহাস সম্বন্ধে আগ্রহের আর একটা কারণ হচ্ছে সমকালের ইউরোপের লেখকরা পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদের সহযোগী হিসেবে ইসলাম ও মুসলমান শাসন নিয়ে যে দুরভিসন্ধিমূলক প্রচারণা শুরু করেছিল তিনি তার যুক্তিপূর্ণ ও বুদ্ধিবৃত্তিক জওয়াব দিতে চেয়েছিলেন এবং মুসলমানদেরকে তাদের ইতিহাসের গৌরবময় অধ্যায় সম্বন্ধে সচেতন করে বর্তমানের জড়তা ও অন্ধতা থেকে বের করে আনতে চেয়েছিলেন। মোটকথা ইতিহাসের জাগরণের ভিতর দিয়ে তিনি ভারতীয় মুসলিম
সমাজে এক ধরনের আলোড়ন সৃষ্টির পক্ষপাতী ছিলেন। ইতিহাস তার কাছে শুধুমাত্র ঘটনার বিবরণ ছিল না। তিনি তার বিখ্যাত আল ফারুক কিতাবে লিখেছেন – to find out the past events (waqiah) and organize them in such a manner that would explain the outcome of a present event from the previous event. ১৬
ইতিহাস তার কাছে প্রতিভাত হয়েছিল এমন একটা বিষয় হিসেবে যা কিনা মানব সমাজকে ভবিষ্যতের কৌশল নির্মাণে যথাযথ পাঠদান করতে পারে। শিবলীকৃত ইতিহাসের প্রত্যেকটি ঘটনার বর্ণনার অর্থ হচ্ছে পূর্ববর্তী মুসলমানদের কাজকর্ম ও তার ফলাফল দেখে সমসাময়িকদের শিক্ষা নেয়া। উদাহরণ স্বরূপ তিনি দেখিয়েছেন শাসকরা জ্ঞান ও শিক্ষা বিস্তারে কি পরিমাণ অর্থ ও সময় ব্যয় করেছেন। সেকালের কারিকুলামগুলোর নমনীয়তা ও পরিবর্তনযোগ্যতা এবং শিক্ষার প্রতি শাসক ও জনগণের দুর্নিবার আবেগ ও ভালবাসা । এটা ইসলামের বিস্তৃতিতে সহায়ক হয়েছে। শিবলী দেখিয়েছেন অতীতের প্রত্যেকটি ঘটনা তুলে ধরার অর্থ হচ্ছে যদি একালেও একই ধরনের নীতি প্রয়োগ করা যায় তবে সেই সমানুপাতে ফলাফল আসবে । এই কারণে কুরআন শরীফেও অতীতের ঘটনা তুলে ধরা হয়েছে তার থেকে যথাযথ শিক্ষা নেবার জন্য ।
শিবলী মনে করতেন ইতিহাস কোনো প্রকৃতি বিজ্ঞান বা সাহিত্য নয় বরং এটি হচ্ছে যৌক্তিকভাবে তুলে ধরা বর্ণনামূলক এক বিজ্ঞান। ইতিহাসকে তিনি দার্শনিকতা দিয়েছেন এবং কারণ ও ফলাফলের (cause and effect illat wa-ma lul) ভিতর দিয়ে ব্যাখ্যা করে এর থেকে শিক্ষা নেবার উপর জোর দিয়েছেন। মুসলমানের ভিতরে তিনি এক নতুন শক্তি জাগাতে চেয়েছেন এ কথা মনে করিয়ে যে, কি করে অশিক্ষিত আরব জনগোষ্ঠী একটি গৌরবময় সভ্যতা তৈরি করেছিল। ঐতিহাসিকের কাজ হচ্ছে ইল্লাত-ওয়া মা’লুলের ভিত্তিতে ধারাবাহিকতা রক্ষা করে সেই সব উপাদানকে চিহ্নিতকরণ যা নির্দিষ্ট ফলাফল দিয়ে থাকে । আল মামুন কিতাবে তিনি লিখেছেন, Every event of universal history is bound by a chain of different events. To investigate these fibres and study them philosophically to extract their historical results is the soul and spirit of history.
শিবলী মনে করতেন ইতিহাসের এই সব ঘটনাগুলো হচ্ছে একটি দীর্ঘ ধারাবাহিকতা ও পরম্পরার পরিণাম যাকে তিনি বলেছেন সিলসিলা-ই-আসবাব তিনি যুক্তি দেন একই রকম আন্তরিকতা ও সাহস যদি ইতিহাসের জমিনে কারণ ও ফলাফলের ভিত্তিতে দেখানো যায় তবে পূর্বসুরীদের মতোই ফলাফল আসবে । এই কারণেই তিনি পূর্বসুরীদের পদাঙ্ক অনুসরণ করার পক্ষপাতী। শিবলী মুসলিম ইতিহাসের কয়েকজন রত্ন, যারা ইতিহাসকে ধরে রীতিমত নাড়া দিয়েছিলেন তাদের ঐতিহাসিক জীবনী লিখেছিলেন, কার্লাইলের ভাষায় তিনি যাদেরকে বলেছিলেন Heroes of Islam.
আব্বাসীয় রাজবংশের সপ্তম খলিফা আবদুল্লাহ আল মামুন বিন হারুনকে নিয়ে তিনি লেখেন ‘আল মামুন’ যা শিবলীকে লেখক হিসেবে প্রথম পাদপ্রদীপের আলোয় নিয়ে আসে। আল মামুনের মধ্যে ঐতিহাসিকতার স্বাদ পুরোটাই ছিল যা আধুনিক ইতিহাসের যেকোনো ছাত্রকেই আকর্ষণ করে। শিবলী তার এই বইয়ের জন্য বিপুল প্রশংসিত হন এবং ভারতের আকাশের উদীয়মান নক্ষত্র হিসেবে তাকে বিবেচনা করা হতে থাকে। বইটি দুই পর্বে বিভক্ত প্রথম পর্বে আছে আল মামুনের প্রথম জীবন, শিক্ষা, অভিষেক, অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব-সংঘাত, সামরিক বিজয় ও মৃত্যুর কথা। দ্বিতীয় পর্বে আছে সেই সময়কার আর্থ-সামাজিক-সাংস্কৃতিক অবস্থার কথা, মামুনের চরিত্র বিচার প্রভৃতি। বর্ণনার ভঙ্গি সরল ও পাঠকচিত্ত আকর্ষণকারী। ঘটনার বর্ণনাগুলো নৈর্ব্যক্তিক এবং পক্ষপাতিত্ত্ববিহীন।
শিবলীর দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হচ্ছে সিরাত-আল নুমান । এটি হানাফী মাজহাবের প্রতিষ্ঠাতা মশহুর ধর্মতত্ত্ব ও আইনবিদ ইমাম আবু হানিফার জীবন ও কর্মকে ভিত্তি করে লেখা ইমাম আবু হানিফার উপর ছিল শিবলীর অপরিসীম শ্রদ্ধা এবং হানাফী মাজহাবের আইন-কানুনকে তিনি মনে করতেন সবচেয়ে আধুনিক ও কালোপযোগী । তার ভাষায় : eminently symbolised consideration for this worldly human needs and was best suited for culturally more advanced societies, in other words, because it stood for change and progress.১৮
উর্দুতে ইমাম আবু হানিফার উপর শিবলীকৃত বইটি হচ্ছে প্রথম জীবনী এবং এখানে তিনি ইসলামী আইনশাস্ত্রের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেছেন যা এই জীবনীটিকে আগ্রহী পাঠকদের জন্য আরো আকর্ষণীয় করে তুলেছে। এখানে বিশেষ করে তিনি শেলডন এ্যামসের ইসলামী আইন রোমান আইন থেকে ধার নেয়া এই জাতীয় বক্তব্যের তীব্র সমালোচনা করেছেন শিবলী নুমানীর ম্যাগনাম ওপাস হচ্ছে একদিকে আল ফারূক, অন্যদিকে সিরাত আল নবী। আল ফারূক হচ্ছে ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা হযরত উমরের জীবনী এবং একই সাথে ইসলামের ইতিহাসের একটি গৌরবজনক সামাজিক রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক পর্বের অসামান্য কীর্তিগাথা । এ বইটি লিখতে যেয়ে তিনি ভারত, বৈরুত, দামেস্ক ও কায়রোর বিভিন্ন কুতুবখানায় তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ করেন এবং মশহুর মুসলিম পণ্ডিতদের প্রচুর লেখাজোখা নাড়াচাড়া করেন। বইটির অসাধারণ পাঠকপ্রিয়তার কারণে এটি ইংরেজি, ফারসি, আরবি, পশতু, তুর্কী, বাংলা ও মালয়ালাম ভাষায় তরজমা হয়েছে এই বইটিতে শিবলী হযরত উমরকে ইনসাফ ও সমতার আদর্শিক প্রতীক হিসেবে হাজির করেছেন এবং তিনি দেখানোর চেষ্টা করেছেন ফারূকী খেলাফতের ভিতর দিয়ে ইসলামের রাজনীতি, অর্থনীতি ও পারস্পরিক সহাবস্থানের প্রকৃত রূপ ফুটে উঠেছে ।
জীবনী গ্রন্থের দিক দিয়ে বিচার করলে শিবলীর সেরা বই হচ্ছে রসূল (সঃ) এর জীবনী সিরাত আল নবী। রসূল (সঃ)-এর জীবন ও শিক্ষাকে উর্দু ভাষাভাষীদের কাছে তুলে ধরাই ছিল তার প্রাথমিক উদ্দেশ্য ।
রসুল (সঃ)-এর বাণী ও তার ঐতিহাসিক ভূমিকা নিয়ে শিবলীর গভীর উপলব্ধির প্রকাশও এ বই বইটির বিষয়বস্তু, উপস্থাপনা, গবেষণামূলক পর্যবেক্ষণ ও ঐতিহাসিক সূত্রের নির্ভরযোগ্যতার বিচারে এটিকে একটি একক স্থানের অধিকারী করেছে যার তুলনা আরবি ভাষায়ও রীতিমতো দুর্লভ। শিবলী যখন আলীগড় কলেজের শিক্ষক তখন স্যার সৈয়দ আহমদ খানের নির্দেশে তিনি কলেজের গ্রাজুয়েট ছাত্রদের জন্য বদি আল-ইসলাম বলে একটি বই লেখেন, যে বইটি মূলত পরবর্তীকালে সিরাত আল নবী লেখার অনুপ্রেরণাস্থল হয়ে ওঠে । বদি আল ইসলাম পরে সবাই তাকে রসূল (সঃ)-এর একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনী লেখার অনুরোধ করে।
সমসাময়িককালে ইউরোপের প্রাচ্যতত্ত্ববিদরা যেমন পালমার, ম্যুর, স্প্রেংগার, মারগোলিয়থ প্রমুখ রসূল (সঃ)-এর জীবনী লিখে তাঁর সম্পর্কে বিভ্রান্তিকর কথাবার্তা প্রচার করেছে- এতে মুসলমানরা সংগত কারণেই ক্ষুব্ধ হয়েছে । তখন থেকেই এটা মনে করা হচ্ছিল ইউরোপীয় লেখকদের রসূল (সঃ)-এর জীবনী নিয়ে প্রমাণবিহীন-যুক্তিবিহীন অভিযোগের জওয়াব জরুরি। শিবলী যার নিজের ইসলামী বুদ্ধিবৃত্তির জগতে ছিল উজ্জ্বল বিচরণ, তার মত ছিল ইসলাম কেবল আল্লাহ ও তার সৃষ্টির বিষয়কে বুঝার জিনিস নয়। এটা বুঝতে হলে নবুয়ত, খোদার সৃষ্টিতে রসূলের বিশেষ স্থান এবং খোদার সাথে রসূলের বিশেষ সম্পর্কগুলোকেও বুঝতে হবে। শিবলী মনে করতেন পুরো মানবজাতিকে এই ব্যাপারটির বৈশ্বিক গুরুত্ব ও মর্মকে স্বীকৃতি দিতে হবে। ১৯১২ সালে শিবলী রসূলের জীবনী লেখায় সহায়তার জন্য একটি কমিটি গঠন করেন এবং এর সদস্য হন সৈয়দ সুলায়মান নদভী, হামিদুদ্দীন ফারাহী, আবদুস সালাম নদভী ও আবদুল মজিদ দরিয়াবাদীর মতো চিত্তকেরা। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় দুই খণ্ড লেখার পর শিবলী ইন্তিকাল করেন। শিবলীর আরাধ্য কাজ সমাপ্ত করেন তার যোগ্য ছাত্র সৈয়দ সুলায়মান নদভী । শিবলী অত্যন্ত কৃতিত্বের সাথে এই দুই খণ্ডে ইসলামে জীবনী সাহিত্যের ধারা, সিরাত, মাঘাজী ও হাদিস সাহিত্যের মধ্যে পার্থক্য, রসূলের পূর্ববর্তী জীবনীগুলোর সীমাবদ্ধতা নিয়ে আলোচনা করেছিলেন । চারটি মৌলিক নীতিকে নির্ভর করে তিনি তার সীরাত গ্রন্থের প্রামাণিকতা স্পষ্ট করেছিলেন। কুরআনে বর্ণিত রসূলের জীবনের ঘটনাগুলোকে মূলসূত্র ধরে লেখালেখি করা, নির্ভরযোগ্য বিশেষ করে বোখারী শরীফের হাদিসের উপর জোর দেয়া, প্রথম যুগের ইবনে ইসহাক, ইবনে সাদ ও তাবারীর মত সীরাত গ্রন্থের উপর নির্ভরতা এবং প্রচলিত সীরাতের বিভ্রান্তি ও পূর্বানুমানকে পরিহার করা ।
জীবনী সাহিত্য নিয়ে শিবলীর এই বিশেষ অনুরাগ আলীগড়ে থাকাকালে স্যার সৈয়দ আহমদ খানের প্রেরণা ও দিকনির্দেশনার বদৌলতে অনেকখানি সজীব হয়ে উঠেছিল তা এক প্রকার বলা যায়।
পাঁচ.
উনিশ শতকে পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদের অভিঘাতের মুখে মুসলিম চিন্তক, বুদ্ধিজীবী ও দার্শনিকেরা তাদের চিন্তাভাবনাকে সংস্কার, পুনর্মূল্যায়ন ও পুনর্নবায়ণের যেমন চেষ্টা করেছিলেন তেমন নতুন পরিস্থিতিতে খাপ খাওয়ানোর একটা চেষ্টাও লক্ষণীয়। এই ক্ষেত্রে শিক্ষা ব্যবস্থার সংস্কার ছিল একটা অন্যতম প্রধান ক্ষেত্র। ঐতিহ্যগতভাবে মুসলমানরা শিক্ষা ব্যাপারে কুরআন ও হাদিস থেকেই অনুপ্রেরণা পেয়ে আসছে। জ্ঞানার্জন তাদের কাছে শুধু ইবাদতের সমতুল্য নয়, খোদা ও তার সৃষ্টিকে যথাযথ বুঝার এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। তারপরেও ইউরোপের বস্তুগত সমৃদ্ধি এবং পরিবর্তিত সময়ের সাথে দ্রুত তাল মেলানোর আকাঙ্ক্ষায় কোনো কোনো মুসলিম বুদ্ধিজীবী ও সমাজনেতারা ইউরোপীয় মডেলকে গ্রহণের সুপারিশ করেন। কিন্তু ঐতিহ্যবাদী শিক্ষার সাথে ইউরোপীয় ব্যবস্থার একটা সুস্পষ্ট সম্পর্ক নিরূপণ না হওয়া পর্যন্ত সেটা সম্ভব ছিল না। এই প্রেক্ষিতেই শিবলী নুমানী আধুনিক ইসলামী চিন্তার ক্ষেত্রে একজন খুবই গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি। তিনি নাদওয়াতুল উলুম মাদরাসায় ইসলামী ও আধুনিক শিক্ষার একটা সমন্বয় করে নতুন সিলেবাস ও কারিকুলাম তৈরি করেছিলেন। উনিশ শতকের প্রেক্ষাপটে একে এক ধরনের জ্ঞানের ইসলামীকরণ বলা যায়। এক্ষেত্রে শিবলীর সাথে সৈয়দ আহমদ খানের একটা তফাৎ দেখিয়েছেন বিখ্যাত ইসলামবিদ উইলফ্রেড কান্টওয়েল স্মিথ, যা আমাদেরকে শিবলীর মনোগঠনকে বুঝতে সাহায্য করবে : Sayyid Ahmad approached Islam from the values of the modern West, Shibli approached Western values from the view point of Islam.
শিবলীর এই বিশেষ চিন্তা কাঠামোর জন্য তিনি সেকালের মুসলিম সমাজে সৈয়দ আহমদ খানের চেয়ে অনেক ক্ষেত্রে বেশি গৃহীত হয়েছিলেন। সৈয়দ আহমদ খান রাজনীতির দিক দিয়ে ছিলেন মুসলিম স্বার্থপন্থী ও সংরক্ষণবাদী। কিন্তু ইসলামী চিন্তার দিক দিয়ে তিনি ছিলেন উদারনৈতিক ও পশ্চিমা চিন্তাভাবনা দ্বারা প্রভাবিত।
শিবলী তুরস্ক ও মিশর থেকে ঘুরে আসার পর শিক্ষা সংস্কার কাজে আত্মনিয়োগ করেন । এ কাজ করতে যেয়ে তিনি বুঝতে পারেন মুসলিম জগতের বিশেষতঃ ভারতের চলমান মাদরাসা শিক্ষার দুর্বলতা । তিনি অবাক হয়েছেন যুগের পরিবর্তন হয়েছে, মানুষের চিন্তালোকে ভাবান্তর এসেছে, কিন্তু মাদরাসা কারিকুলাম কোনো পরিবর্তন ছাড়া আগের মতো রয়ে গেছে। মাদরাসা কারিকুলামের উদাহরণ টেনে শিবলী বিশেষ করে লিখেছেন কেন আল আজহারের মতো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমাজকে নেতৃত্ব দেয়ার মতো বুদ্ধিজীবী তৈরি করতে পারছে না। এই পরিস্থিতির জন্য তিনি দুটো কারণ উল্লেখ করেছেন। একটি হচ্ছে মাদরাসা কারিকুলামে আধুনিক জ্ঞানের অনুপস্থিতি ও পুরনো গ্রীক দর্শনের উপস্থিতি এবং অন্যটি ইংরেজি শিক্ষার অভাব। কেবলমাত্র এরকম পরিস্থিতি সৃষ্টি হলেই আলেমরা আধুনিক শিক্ষিত মুসলমানদের উপর প্রভাব ফেলতে সক্ষম হবে, ইউরোপে প্রচারণা চালাতে পারবে এবং ইসলামের সমালোচনার যথাযথ জওয়াব দিতে পারবে। শিবলীর ছাত্র ও জীবনীকার সৈয়দ সুলায়মান নদভীর প্রশ্নের উত্তরে শিবলী বলেছিলেন, Greek sciences are not our religious sciences, and understanding of our religion is not based on them. Al-Ghazali included them in the curriculam of ‘ulama’ to respond to the effect of atheism (ilhad) in his time…..Now its place has been taken by the new sciences and philosophy, therefore there is a need to acquire them.20
আলেমদের ইংরেজি শিক্ষা প্রসঙ্গে তিনি বলেছিলেন, New education is spreading very fast and Arabic education is declining within the Muslim nobility Now the modern educated learn about Islam from the books of the English and English translations of Islamic books. Isn’t this the job of our Ulama.
শিবলী উল্লেখ করেছেন, আগের জামানার মুসলমানরা তাদের সময়কার সব জ্ঞান-বিজ্ঞানে সম্বন্ধে অবহিত ছিলেন এবং কুরআন-হাদিসের প্রেরণায় জ্ঞানার্জনের জন্য দূরবর্তী স্থানে চলে যেতেন। আজকের দিনের মুসলমানদের কেউ কেউ বিশ্বাসের ক্ষেত্রে ইংরেজি শিক্ষার পরিণতি নিয়ে সন্দিহান। কিন্তু শিবলী উল্টো যুক্তি দেন বিশ্বাসীদের জন্য এটা তেমন ক্ষতিকর হতে পারবে না ।
শিবলী মনে করতেন আলেমরা তাদের নিজ নিজ ক্ষেত্রে যথেষ্ট পারদর্শী হলেও সাম্প্রতিক বিষয়াদিতে তাদের তেমন কোনো দক্ষতা নেই। অথচ এটিও তাদের ধর্মীয় কর্তব্যের অংশ ছিল। মুসলমানের মনোভাব পরিবর্তনে তাদের রয়েছে একটা বড় ভূমিকা যদিও আধুনিককালে তারা এ কাজটা যথাযথভাবে আঞ্জাম দিতে পারছে না। আল-গাজালীর উদাহরণ দিয়ে শিবলী লিখেছেন, Masses became destitute of good qualities because kings (salatin) were spoiled and kings were spoiled because ulama were spoiled and the reason for their corruption was their love of dignity and rank 22
অতীতে আলেমরা মুসলমানদের ধর্মীয় ও জাগতিক সব ধরনের দায়িত্ব পালনে নেতৃত্ব দিতেন । কিন্তু তারা এখন বিশ্বাস করেন সরকার তাদের থেকে সেই দায়িত্ব নিয়ে নিয়েছে, যা শিবলী মনে করেন সর্বোতভাবে ঠিক নয়। তিনি বলেছেন: The Ulama still have great authority over the nation, (although) they may not need this (authority) but the nation needs them badly. This is because, if they do not take the control of the thinking, morality, culture and civilization of the nation, it would not progress. 20
শিবলী মনে করতেন ধর্মীয় ও আধুনিক শিক্ষা উভয়কে যুগপৎভাবে গ্রহণ না করলে এবং ইসলামী প্রেক্ষিতে আধুনিক শিক্ষাকে গ্রহণ না করলে মুসলমান সমাজ আগে বাড়তে পারবে না। সমস্যা হচ্ছে আধুনিক শিক্ষার ভিতরে ধর্ম নেই অন্যদিকে ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা জাগতিক প্রয়োজনে তেমন কাজে আসে না। এই কারণে পৃথকভাবে এই ভিন্ন ভিন্ন ধারার উদ্যোগগুলো মুসলিম সমাজের সার্বিক কল্যাণে ভূমিকা রাখতে পারছে না। শিবলী তাই ভারতীয় মুসলমানদের তাদের অতীত ইতিহাস থেকে সবক নেয়ার কথা বলেন। যখন ভারতে একই সাথে দুই ধারার শিক্ষা ব্যবস্থা চালু ছিল। একটি জাগতিক (দুনিয়াবী) অন্যটি ধর্মীয় (বীনি) । জাগতিক শিক্ষায় ফারসি বই ও কুরআন শিক্ষা দেয়া হতো এবং এইসব শিক্ষার্থীরা সরকারি দফতর ও ব্যবসার সাথে সংশ্লিষ্ট ছিল। উপর্যুপরি এরা বিশ্বাসের দিক দিয়ে ছিল দৃঢ় । নৈতিকভাবে শক্তিমান । জাগতিক শিক্ষা পাওয়ার পরও ইসলামী পরিবেশে শিক্ষিত হওয়ার ফলে বিচ্যুতির সম্ভাবনা কম ছিল।
অন্যদিকে ইসলামী ইতিহাসে ধর্মীয় বা আধ্যাত্মিক শিক্ষাই ধর্মের প্রহরী হিসেবে কাজ করেছে এবং এই শিক্ষা যে আলেম শ্রেণি তৈরি করেছে, তারা জনগণের উপর ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করেছে। এরা ইমামতি করেছে, খুতবা দিয়েছে এবং ইসলামী আইন বিষয়ে ফয়সালা করেছে। এদেরকে শিবলী মনে করতেন : If this group becomes extinct, the effects of Islam will be annihilated and will not be compensated by thousands and millions of schools and colleges. But the way the curriculam and method of education has been changing from the beginning of Islam, it is necessary that (the present religious curriculam) be changed now to make the madaris more influential 28
শিবলী এমন একটা শিক্ষা ব্যবস্থা চেয়েছিলেন যেখানে মুসলমানরা ধর্মের ভিত্তিতে গড়ে উঠবে । একই সাথে তাদের থাকবে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের উপর অধিকার। শিবলী মনে করতেন আলেমদেরও ফিকাহ ও হাদিসের পাশাপাশি আধুনিক বিজ্ঞান পড়তে হবে। আজকাল জ্ঞানের ইসলামীকরণ কথাটা বহুল প্রচলিত । শিবলী সেইকালে এই কথাটি ব্যবহার করেননি। কিন্তু কার্যতঃ তিনি সেটাই চেয়েছিলেন । একজন গবেষকের মন্তব্য : Shibli was perhaps the first person in modern times to talk about ‘reforming’ the modern sciences in the light of the Qur’an’, but did not use the term ‘Islamization’ which is popular today 20
ছয়.
পশ্চিমা চিন্তার অভিঘাতে ভারতীয় মুসলমানদের বুদ্ধিবৃত্তির জগতে যে আলোড়ন আমরা দেখি তাতে এক ধরনের সৃষ্টিশীল প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছিলেন সৈয়দ আহমদ খান, সৈয়দ আমীর আলী, শিবলী নুমানী প্রমুখ। পরবর্তীকালে ইকবালে এসে এই ধারা পূর্ণ পরিণতি পায়। এরা প্রত্যেকে নিজের মতো করে আধুনিকতার মোকাবেলায় ইসলামের চিন্তার জগতকে পুনর্গঠন করতে চেয়েছিলেন। মুসলিম সমাজে আধুনিকতা প্রতি আধুনিকতার এই দ্বন্দ্ব ও চিন্তার বিবর্তন নিয়ে লেখালেখি করেছেন অধ্যাপক আজিজ আহমদ। একাডেমিয়ার জগতে মুসলিম চিন্তার বিবর্তন বুঝতে তার লেখা Islamic Modernism in India and Pakistan 1857-1964 খুবই গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হয়। এখানে তিনি শিবলীর চিন্তার কাঠামো বুঝাতে এ কথাগুলো লিখেছেন, Unlike Sayyid Ahmad Khan, he is not a neo-Mutazilite modernist. The cast of his mind is essentially medieval, though he is prepared to make compromises with the radical responses necessitated by challenges of Europe’s scientific outlook. He is also preoccupied with the concept of reason’, and to some extent with that of ‘nature’ But for him rationalism is almost synonymous with medieval Muslim kalam He takes the historically static view that all in kalam that was effective in the tenth to thirteenth centuries of Islam should be so even now, for the correctness or actuality of a process of thought does not alter with the passage of time 26
ইসলামের কালাম শাস্ত্র গড়ে উঠেছিল প্রধানতঃ মধ্যযুগে গ্রীক দর্শনের প্রভাবে ও প্রতিক্রিয়ায়। কালাম হচ্ছে ইসলামের দিক দিয়ে এক ধরনের দার্শনিক যুক্তিবাদিতা যা গ্রীক দার্শনিকতাকে মোকাবেলা করতে চেয়েছিল। ঊনিশ শতকেও মুসলিম জগতের ভিতরে ইউরোপীয় আধুনিকতার প্রতিক্রিয়ায় নতুন ধরনের একটি যুক্তিবাদী ধারা গড়ে ওঠে। মধ্যপ্রাচ্যে যার নেতৃত্ব দেন মুফতী আবদুহ, রশিদ রিদা এবং ভারতে সৈয়দ আহমদ খান, শিবলী নুমানী প্রমুখ। সৈয়দ আহমদ খান ইউরোপীয় আধুনিকতা ও বৈজ্ঞানিক চিন্তাকে মানসও ধরে ইসলামী শাস্ত্রকে ব্যাখ্যা করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু ইউরোপের আলোয় একালের মুসলিম কালাম তৈরির পথ সহজ ছিল না। এটি ইসলামের সনাতন ও নিষ্ঠাবান ব্যাখ্যায় বিশ্বাসীদের থেকে তাকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়। এর ফলে তার জনপ্রিয়তায় ধ্বস নামে এবং তার তৈরি নতুন কালাম ইসলামী চিন্তার প্রতিনিধিত্বমূলক বয়ান হতে পারেনি ।
সৈয়দ আহমদের মতো শিবলীও আধুনিককালের উপযোগী নতুন কালাম চেয়েছিলেন । কিন্তু সৈয়দ আহমদ থেকে পৃথক হয়ে তিনি বিকল্প প্রস্তাবনা দেন। শিবলী তার নতুন কালামের চিন্তাভাবনাকে তার লেখা ‘ইলম-আল-কালাম’, ‘আল গাজ্জালী’, ‘আল কালাম’ ও ‘সওয়ানী মাওলানা রুম’ প্রভৃতি বইয়ে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন।
শিবলী কখনো কখনো সৈয়দ আহমদ খানের সাথে শুধু অমত করেননি, তিনি তার চিন্তাভাবনাকে সমালোচনাও করেছেন। নতুন কালাম তৈরির ক্ষেত্রে সৈয়দ আহমদ খানকে সমালোচনা করে তিনি লিখেছেন : It is being claimed today that the old philosophy could not destroy religion since it is based on conjectures and hypothetical assumptions (qiyasat awr zanniyat); but since modern philosophy is based wholly on experiment and observation (tajribah awr mushahadah), religion can not survive in to it. This is a common cry which having once arisen from Europe has resounded all over the world. But we must discern carefully the element of fallacy (mughalatah) which has entered into this factuality (waqi’iyyat),
শিবলী ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা করেছেন বিজ্ঞানের সাথে ইসলামের কোনো বিরোধ নেই । কিন্তু ইউরোপীয় দর্শনের সাথে চিন্তার ভিন্নতা আছে। এরকম ব্যাখ্যা হাজির করে শিবলী মূলতঃ বিজ্ঞান ও ধর্মের বিরোধকে পাশ কাটাতে চেয়েছেন এবং ইসলামকে বিতর্কের ঊর্ধ্বে রাখার চেষ্টা করেছেন। শিবলীর উদ্দেশ্য ছিল অলৌকিকতা ও মজেজাকে ইসলামের গরীর মধ্যে বিজ্ঞানের পাশাপাশি জায়গা দেয়া এবং ইসলামকে যথেষ্ট পরিমাণ বৈজ্ঞানিক প্রমাণ করা। এভাবে শিবলী নিজেকে সৈয়দ আহমদ থেকে পৃথক করলেন, যিনি অলৌকিকতাকে বিজ্ঞানের সামনে জবাই দিয়েছিলেন। শিবলী ইসলামকে অলৌকিকতা মুক্ত দেখতে চাননি, তিনি অবিনশ্বর সত্যের স্পর্শ নিয়ে চলতে চেয়েছেন । কিন্তু মুশকিল হচ্ছে শিবলী যেভাবে অতি সহজে বিজ্ঞান ও দর্শনের তফাৎ করেছেন, সেই কাজটা আসলে তত সহজ নয়। বিজ্ঞানতো শুধুমাত্র দৃশ্যমান ও পরিক্ষিত ঘটনা নয় এবং দর্শনও শুধু চিন্তার সমষ্টি নয় বিজ্ঞানকেও ধর্মের প্রশ্নে কখনো কখনো দার্শনিকতার আশ্রয় নিতে হয়, আবার দর্শনকেও কখনো কখনো নিরীক্ষামূলক বিজ্ঞানের উপর ভর করতে হয় দর্শন ও বিজ্ঞান সাদা ও কালোয় পৃথক করার জিনিস নয়। বাস্তবে সেটা অনেক ক্ষেত্রেই হয় না, একটি আরেকটির উপর জড়িয়ে যায় । শিবলী সৈয়দ আহমদের মতো মুতাজিলা ভাবাপন্ন ছিলেন না, আবার তিনি পুরোপুরি আশারীয় চিন্তাকেও নিতে পারেননি। তিনি দুই ধারার মাঝামাঝি ইটিতে চেয়েছিলেন যদিও কার্যতঃ তিনি সব সময় ভারসাম্য রাখতে পারেননি। তার এক হাত টেনেছে মুতাজিলারা, আরেক হাত টেনেছে আশারীয়রা। এই কারণে তিনি কখনো ইউরোপীয় চিন্তাকে অমিত সাহসের সাথে ইসলামকে নিয়ে মোকাবেলা করেছেন । আবার কখনো ইউরোপীয় চিন্তার সাথে ইসলামী চিন্তাকে আপোষের মাধ্যমে দফা রফা করতে চেয়েছেন। শিবলীর ভাবজগতের এই টানাটানির ব্যাপারটা আধুনিকতার মুখোমুখি দাঁড়ানো তার কালেরই হয়তো একটা বৈশিষ্ট্য শিবলী কখনো কখনো আশারীয়দের চিন্তাকে সমালোচনা করেছেন। কিন্তু মজার ব্যাপার হলো আল গাজ্জালী, আল রাজী, রুমী ও শাহ ওয়ালিউল্লাহ তার চিন্তা নির্মাণে বড় ভূমিকা রেখেছে। এদের অনেকেই ছিলেন আশারীয় চিন্তার পথিকৃত এবং এদের প্রত্যেকেই ছিলেন ক্লাসিকাল ইসলামী চিন্তার অগ্রপথিক। শিবলী শাহ ওয়ালিউল্লাহর চিন্তা ভাবনা দ্বারা প্রাণিত হয়েছিলেন বিশেষ করে ইউরোপীয় চিন্তার ধাক্কা যখন ইসলামী চিন্তার কাঠামোতে এসে লাগে তখন তৌহীন, নবুয়ত, রিসালাত, আখেরাত প্রভৃতি বিষয়ক শাহ ওয়ালিউল্লাহর ভাবনা তাকে ইউরোপকে মোকাবেলা করতে সাহায্য করে। শিবলী আশারীয়দের সমালোচক হলেও হানাফী মাজহাবের ছিলেন ঘোরতর সমর্থক।
শিবলীর চিন্তার মধ্যে এরকম বহু বৈচিত্র্য দেখা যায় যেগুলো আপাতদৃষ্টিতে বিপরীতধর্মী মনে হতে পারে। বিশেষ করে শিবলী যে যুগের প্রতিনিধিত্ব করেছেন। সেইকালে ইউরোপের কাছে ভারতীয় মুসলমানরা রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিকভাবে পরাজিত হয়েছে। একটি পরাজিত সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি হিসেবে তাকে কখনো কখনো ইসলামকে সমসাময়িকতার তুলাদণ্ডে মাপতে হয়েছে, যখন ইউরোপ কিনা বিশ্বের নেতৃত্বের আসনে আসীন। এই কারণে শিবলী মধ্যযুগের মুসলিম দার্শনিকদের তৈরি কালামকে আজকের যুগের চাহিদা অনুযায়ী নতুন করে পুনর্গঠন করতে চেয়েছিলেন । সেইকালে মুসলিম দার্শনিকরা যেমন করে গ্রীক দর্শনকে মোকাবেলা করেছিলেন, শিবলীও তেমনি পুনর্গঠিত কালাম দিয়ে ইউরোপীয় আধুনিকতাকে এক ধরনের জওয়াব দিতে চেয়েছিলেন। ফজলুর রহমান যথার্থ লিখেছেন, Under the aggressive attacks of the Western critics of Islam, he was virtually forced to take up arms and to show the excellence of the age-old social institutions of Islam by contemporary Western standards and value criteria. Put on the defensive he even went to the extent of deliberately making the socio-legal institutions of Islam an essential part of his new kalam. Left alone, he, and perhaps many others, would have responded differently, more creatively to the intellectual-cultural stimuli of the West ২৮
সাত
শিবলী নুমানীর উপর সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য জীবনী লিখেছেন তার ভাবশিষ্য সৈয়দ সুলায়মান নদভী। এই জীবনী গ্রন্থের নাম হায়াত-ই- শিবলী এখানে শিষ্য তার ভাবগুরুর রাজনৈতিক চিন্তা নিয়ে কিছুটা আলোকপাত করেছেন । নদভী লিখেছেন: In view of the attachment he had with Islam. Islamic civilisation, history, sciences and arts, it was only natural that he should hold dear the rule of Islam and should wish to see the picture he had been looking at the books realised in actuality.
এটা সত্য শিবলী জামালুদ্দীন আফগানীর মতো সক্রিয় প্যান ইসলামবাদী ছিলেন না। কিন্তু মুসলিম উম্মাহর চিন্তা তার রাজনৈতিক ভাবনায় যথেষ্ট ক্রিয়াশীল ছিল। মিল্লাতের আন্তর্জাতিকতা নিয়ে তিনি একবার লিখেছিলেন, extends over Iraq, Faris, Najd, Hijaz and Qayrawan. o
উম্মাহ কেন্দ্রিক চিন্তাভাবনা তার সক্রিয় থাকলেও ব্রিটিশ ভারতে তিনি একজন ব্রিটিশ অনুগত নাগরিক হিসেবে উসমানী খেলাফতের ব্যাপারে আগ্রহ দেখিয়েছেন। সক্রিয় রাজনীতিবিদ বলতে যা বুঝায় শিবলী তা কখনোই ছিলেন না। তবে একজন চিন্তাশীল মানুষ হিসেবে তিনি রাজনৈতিক ঘটনা প্রবাহ দ্বারা আলোড়িত হয়েছেন এবং নিজের মতামত বিবৃত করেছেন। শিবলী রাজনীতি বিষয় নিয়ে বড় রকমের কিছু লেখালেখি করেননি। যা লিখেছেন তা তিনি প্রধানত কবিতার ভাষায় প্রকাশ করেছেন। এই কারণেই মুসলিম উম্মাহর রাজনীতি চিন্তার ক্ষেত্রে তিনি স্যার সৈয়দের মতো রুঢ় বাস্তববাদী না হয়ে অনেক বেশি মাত্রায় রোমান্টিক হয়ে উঠেছেন।
উসমানী খেলাফতের সাথে তার প্রাণের সম্পর্ক ছিল। ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদের কূটচালে যখন তুর্কী খেলাফত ভেঙে পড়ছিল তখনও তিনি এই মেনে নিতে পারেননি। তার কাছে মনে হয়েছিল ইসলামের শেষ প্রতিরক্ষা ব্যুহ ভেঙে পড়লে জাতি কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে ।
১৯১১ সালে ইতালির ত্রিপোলি আক্রমণ এবং ১৯১২ সালে বলকান যুদ্ধে খেলাফতের বিপর্যয় তাকে বিমূঢ় করে দেয়। তার সেই বিমূঢ়তা কবিতায় রূপ নেয় । তিনি লেখেন শাহর আশোব-ই-ইসলাম- ইসলামের পোড়োজমি। এখানে তার তুর্কী খেলাফতের অবক্ষয়কে ইসলামের বস্তুগত ও আদর্শিক অবক্ষয় হিসেবে মনে হয় তার কাছে মনে হয় এটা যেন শেষের শুরু । এক কবিতায় তিনি লেখেন উসমানীদের ঐশ্বর্য ক্ষয়ে যাওয়া মানে মিল্লাত ক্ষয়ে যাওয়া। তার চোখে মনে হয়। ইউরোপীয়রা তুর্কীদের নিয়ে যে খেলা খেলছে তা এক নতুন ক্রুসেড যার পরিণতি গিয়ে দাঁড়াবে খ্রিস্টানদের দ্বারা মক্কা দখল । আর একটি কবিতায় তিনি লেখেন, How much will you take the revenge for the Ayyubid Victory from us, How long will you show us the scene of the crusade.
শিবলীর এই প্যান ইসলামবাদী আবেগ কখনো কখনো দেশের রাজনীতির ক্ষেত্রেও দেখা যায় ৷ ১৯১৩ সালে কানপুর মসজিদকে কেন্দ্র করে ব্রিটিশের ইন্ধনে কয়েকজন মুসলমান মারা গেলে তিনি এই হত্যাকাণ্ডকে রীতিমত বলকানের হত্যাকাণ্ডের সাথে তুলনা করে লেখেন : Are you asking about the nation of the Arabian prophet, Why is it decreasing today in number and manifestation? Listen! those precious treasures are buried.31 Some in the dust of the Balkan, some in Kanpur. ৩২
শিবলীর বুঝতে বাকি ছিল না এই সব রকম অনাচারের পিছনে ব্রিটিশের হাত কাজ করছে । তিনি তাই লিখেছেন এটাই সময় কিছু করার বা প্রশ্ন তোলার, O teachers of human civilisation! how long these atrocities? how long these horrors?৩৩
আশ্চর্যের বিষয় হলো শিবলী আন্তর্জাতিক স্তরে প্যান ইসলামবাদী হলেও ভারতীয় জাতীয় স্তরে সৈয়দ আহমদ খানের মতো স্বাতন্ত্র্যবাদী ছিলেন না। সৈয়দ আহমদ মুসলমানদেরকে কংগ্রেসের রাজনীতি থেকে দূরে থাকতে বলেছিলেন । এক্ষেত্রে সৈয়দ আহমদের প্রখর বাস্তববাদিতা ও ইতিহাসবোধ এই ধরনের সিদ্ধান্ত নিতে ভূমিকা রেখেছিল এই ভাবনাই পরবর্তীকালে ইকবাল, জিন্নাহকেও প্রভাবিত করেছিল। কিন্তু শিবলীর রোমান্টিকতা তাকে সৈয়দ আহমদ থেকে পৃথক করে দেয় এবং কংগ্রেসের প্রথম যুগের জাতীয়তাবাদী মুসলিম নেতা বদরুদ্দীন তায়েবজী, রহমতুল্লাহ সায়ানী প্রভৃতির দ্বারা তিনি কিছুটা হলেও প্রভাবিত হন। তিনি ভারতের স্বার্থে হিন্দু-মুসলিম ঐক্যবদ্ধ জাতীয় রাজনীতির পক্ষপাতী হয়ে ওঠেন। ঠিক একই কারণে তিনি মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠার পর এই দলটির কাজের ধারা নিয়েও বিস্তর সমালোচনা করেছিলেন। হিন্দু-মুসলিম ঐক্য ভাবনা ভারতীয় রাজনীতিতে খুবই মুখরোচক ও রোমান্টিক ধারণা হলেও কার্যত ইতিহাস এটি গ্রহণ করেনি। জিন্নাহর মতো উদারনৈতিক রাজনীতিককেও কংগ্রেস ছেড়ে দিতে হয়েছিল তার ছদ্মবেশী সাম্প্রদায়িকতার কারণে। শিবলী যদি আরো কিছুদিন বেঁচে থাকতেন তবে ইতিহাসের রূঢ় বাস্তবতা তার চিন্তার ভিতরে কোনো আলোড়ন তুলতো
আট
শিবলী নুমানী ছিলেন বহুপ্রজ ও বহুমাত্রিক ব্যক্তিত্ব। তত্ত্ব ও প্রয়োগ উভয় ক্ষেত্রেই তিনি ছিলেন সমান পারদর্শী। তার আরবি ও ফারসিতে লেখালেখিগুলো সমকালে মধ্যপ্রাচ্যের মুসলিম দেশগুলোতে প্রচুর জনপ্রিয় হয়েছিল। তার কবিতার ইতিহাস শির-উল-আজম ফারসি পাঠকদের কাছে খুবই জনপ্রিয়। ইতিহাস ও সিরাত রচনায় তিনি দেখিয়েছিলেন নতুন মাত্রা। তিনি ছিলেন তার সমকালের সবচেয়ে ব্যাপক বুদ্ধিসম্পন্ন, বর্ণাঢ্য ও গতিশীল ব্যক্তিত্ব।
বৈচিত্র্যময় ব্যক্তিত্ব হওয়ার কারণে বিচিত্র চিত্তার ছাত্রদের তিনি এক সাথে ধারণ করেছেন। তার ছাত্রদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন ইতিহাসবিদ ও একাডেমিসিয়ান সৈয়দ সুলায়মান নদভী (১৮৮৪-১৯৫৪), ভারতীয় জাতীয়তাবাদের পথিকৃত আবুল কালাম আজাদ (১৮৮৮-১৯৫৮), খেলাফত আন্দোলনের অগ্রদূত মওলানা মোহাম্মদ আলী (১৮৭৮-১৯৩১) ও কুরআনের তাফসিরকার হামিদুদ্দীন ফারাহী (১৮৬৩-১৯৩০)।
নাদওয়াতুল উলামা ছিল শিবলীর চিন্তা ও ভাব কেন্দ্র। এটাকে কেন্দ্র করে তিনি বিভিন্ন ধারার উলামা ও আধুনিক শিক্ষিতদের এক প্লাটফরমে আনার কথা ভেবেছিলেন । তার একটা স্বপ্ন ছিল এই কেন্দ্রকে বুনিয়াদ করে আলেমরা জাগতিক ও ধর্মীয় দুই জায়গায় নেতৃত্ব দিয়ে মুসলমানদের বহুস্বরকে এক স্বরে পরিণত করবে তাও পূরণ হয়নি। শেষ জীবনে গড়া দারুল মুসান্নিফিন ভারতের মুসলমানদের সাহিত্য ও গবেষণার কেন্দ্র হয়ে উঠেছিল এবং এর মুখপত্র মাআরিফ ছিল একটি উচ্চাঙ্গের বৃদ্ধিবাদী পত্রিকা ।
এটা সত্য তার জীবন ও ভাবনাচিন্তা নিয়ে প্রচুর সমালোচনা হয়েছে। যা অনেক ক্ষেত্রেই তার আরাধ্য কাজকে সব সময় সমাপ্ত করতে দেয়নি । যাই তার সম্পর্কে বলা হোক না কেন শেষ পর্যন্ত ইসলামই ছিল তার চিন্তার ভরকেন্দ্র । কুরআনকে তিনি নজীর হিসেবে ব্যবহার না করে পথ প্রদর্শক হিসেবে ব্যবহার করতে চেয়েছিলেন ।
হদিস
১/ Charles J. Adams, ‘Preface’ in Intellectual Modernism of Shibli Numani, Mehr Afroz Murad. New Delhi Kitab Bhavan, 1996.
২/ Arshad Islam, Allama Shibli Numani (1857-1914 ) A Monumental Islamic Scholar Pakistan Journal of History and Culture, 26 (1) 1-15, 2005.
৩। Azimabadi Badr, ed. Great Personalities in Islam, 1st ed, Delhi Adam Publishers and Distributors, 1998
৪. Mehr Afroz Murad, Intellectual Modernism of Shibli Numani. New Delhi Kitab Bhavan, 1996.
৫. Ibid.
৬. Lelyveld David, Aligarh’s First Generation. Oxford Oxford University Press, 1978,
৭. Ibid.
৮Mehr Afroz Murad, Intellectual Modernism of Shibli Numani. ৯ Sumaira Nawaz, Shibli Numani’s imagined community, immersive himalmay.com
১০. Ibid.
১১. Francesca Orsini. Significant Geographies: In lieu of World Literature. The Journal of World Literature, 3(3), 290-310, 2018
১২. Daniel Majchrowicz, The Means to Victory Urdu Travel Writing and Aspiration in Islamicate South Asia. Unpublished Phd Thesis at Harverd University
১৩. Ibid.
১৪. Cited in Sumaira Nawaz, Shibli Numani’s imagined community
১৫ Ibid
১৬. Shibli Numani, Al-Farooq (Tr. Maulana Zafar Ali Khan). Lahore Muhammad Ashraf
১৭. Shibli Numani, Al-Mamun. ১৮.Shibli Numani, Al-Numan.
১৮ W.C Smith, Modern Islam in India. Delhi Usha Publications, 1979
২০. S.S. Nadvi, Hayat-1-Shibli. Repr. Azamgarh Dar al Musannifin Shibli Academy, 1993.
২১.Ibid.
২২/ Al-Ghazali, Ihya ulum al-din.
২৩. Shibli Numani, Rasail Shibli, Delhi Rahmani Press, 1971
২৪. Shibli Numani, Khutbat-i-Shibli. Azamgarh Dar al-Musannifin Shibli Academy, 1990.
২৫. Nusba Parveen, Relevance of Shibli’s Educational Philosophy Intellectual Discourse, 19(2), 219-243, 2011 26. ২৬. Aziz Ahmad, Islamic Modernism in India and Pakistan 1857-1964. Oxford, Oxford University.
২৭. Shibli Numani, Al-Kalam. Cited in Intellectual Modernism.
২৮. Fazlur Rahman, Islam. London, 1966.
২৯. S.S. Nadvi, Hayat-1-Shibli. co, ৩০.Shibli Numani, Kulliyat. Cited in Intellectual Modernism.
৩১Ibid.
৩২ Ibid.
৩৩. Ibid.