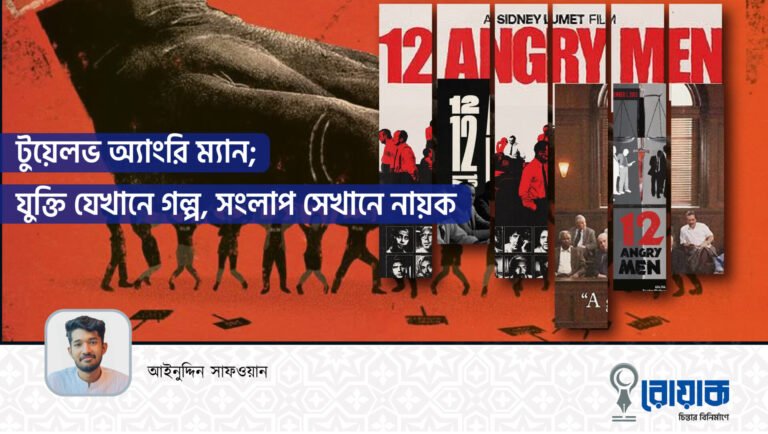এক,
মেকলে চেয়েছিলেন দেশী সাহেব তৈরি করতে। সাহেব তৈরি করতে হলে তো আগে মন মগজের পরিবর্তন চাই। তাই তিনি প্রথমেই হাত দিয়েছিলেন এদেশের শিক্ষা ব্যবস্থার গোড়ায়। কারণ তিনি জানতেন যত বেশি করে ইংরেজের শিক্ষা ও দর্শনটা এইসব নেটিভদের গলাধঃকরণ করিয়ে দেয়া যাবে ততই তাদের বিপ্লবী ভাব নিস্তেজ হয়ে পড়বে, ইংরেজের সামনে অবনত হয়ে পড়াই হবে তাদের নিয়তি। আজ মেকলে নেই, আর সেই ইংরেজ উপনিবেশের রমরমাও নেই একালে। কিন্তু মেকলের ভূত আমাদের পিছু ছাড়েনি। মেকলের সাহেব তৈরির কারখানা ইংরেজের রাজনৈতিক ও শিক্ষা ব্যবস্থা আমরা শুধু টিকিয়ে রাখিনি, একে ফলবান ও বীর্যবস্ত করে রাখতে আমাদের শ্রম ও মেধার সমানে অপচয় করে চলেছি। মেকলে বেঁচে থাকলে তার কারখানার এই উৎপাদন সাফল্যে আজ তিনিও রীতিমতো হতচকিত হয়ে উঠতেন। আজও এখানে আমাদের সবার দুপয়সা হলে কিংবা মধ্যবিত্তের সন্তানরা কিছু লেখাপড়া শিখে রুজী করলে আমাদের সাহেব সুবো সাজতে ইচ্ছে হয়, ইংরেজিতে কথা বলতে ইচ্ছে করে, ইউরোপ-আমেরিকা ঘুরে আসতে না পারলে আত্মার শান্তি হয় না। বেশ কিছু দিন হলো আমাদের আচ্ছন্ন করেছে আর এক খোড়া রোগ।
এতকাল দেখে এসেছি যাদের গাটের জোর একটু বেশি তাদের ছেলে মেয়েদের অক্সফোর্ড, কেমব্রিজ, হার্ভাড ঘুরিয়ে নিয়ে আসে। কারণ ওখানকার সার্টিফিকেট পকেটে থাকলে জাতে উঠতে সুবিধা বেশি। এখন পয়সাওয়ালারা তাদের ছেলের বৌরা সন্তানসম্ভবা হলে বিলেত-আমেরিকার হাসপাতালগুলোতে পাঠিয়ে দেয়। ওখানেই বাচ্চা হয়, যাতে ওখানকার গ্রীণকার্ড ধরতে সুবিধা হয়। আগে সার্টিফিকেট পেলেই চলতো, এখন ওখানে পাড়ি জমাতে না পারলেই যেন জীবনটা বৃথা।
আমাদের চোখের সামনের একটা উদাহরণ দেই। আজকাল তো ঢাকার পাড়ায় পাড়ায় নাম না জানা সব ইংরেজি স্কুল। ভাবটা এমন এসব স্কুলে সন্তানদের না পড়াতে পারলে ভবিষ্যৎ একেবারেই অন্ধকার। এই স্কুলগুলো কি গড়ে উঠেছে বিশ্বায়নের তাগিদে, সংকীর্ণ দেশ ছাড়িয়ে দৃষ্টিকে প্রসারিত করতে না নেহাৎই নব এক উপনিবেশবাদের চাপে, সে বিতর্কের সমাধান হওয়া আজ জরুরি। যে দেশের মানুষ কিনা ভাষার আর আর ইজ্জত রক্ষার জন্য দুর্দান্ত এক লড়াই করল তারাই কিনা আজ ইংরেজির প্রকরণ কলা আর বিষয় ভাবনা আত্মস্থ করবার জন্য উঠে পড়ে লেগেছে।
মেকলের সময় কথা উঠেছিল পাশ্চাত্য না প্রাচ্য শিক্ষা। অনেকের ধারণা পাশ্চাত্য বিরুদ্ধে ফতোয়া দিয়ে আমাদের আলেম সমাজ ভুল করেছিলেন। ভুল কি শুদ্ধ সে বিতর্কে না যেয়ে এটুকু আমরা বলতে পারি ইংরেজরা যখন আমাদের দেশে আধিপত্য কায়েম করতে আসে তখন কিন্তু এখানকার অর্থনীতি, সমাজ ব্যবস্থার নীতি ইউরোপের চেয়ে বহুগুণ শ্রেয় ছিল। সাহেব ঐতিহাসিকরা এই সময়টাকে সবরকমের অবনতি আর অন্ধযুগ হিসেবে বর্ণনা করে তাদের অভিসন্ধিমূলক ইচ্ছাকে গোপন করে রাখতে পারেননি। ভাবটা এমন ইংরেজরা না এলে আমাদের উদ্ধারের আর কেউ ছিল না। আমাদের অনেক বুদ্ধিজীবাই আজ মনে করেন নিজের শক্তিতে বিবর্তিত হলে আমাদের সমাজ যে উন্নত ও যুগোপযোগী হতে পারতো না এমন অবিশ্বাসের কারণ নেই। কিন্তু ইতিহাসের চাকা যেহেতু ঘোরানো যায় তাই কি হতো আর কি না হতো তা ভেবে আর কতদূর লাভ। আজকের এববিংশ শতাব্দী প্রাযুক্তিক উৎকর্ষতা এতদূর এগিয়ে যাওয়ার পর মেকলের কাজকারবারকে দান না অভিশাপ সেটা বিচার করার প্রয়োজন রয়েছে বলে মনে করি।
একালে ইংরেজির দরকার আছে নাকি ইংরেজির সংস্কৃতিও কি আমাদের গ্রহণ করতে হবে? ভাষার সাথেই সংস্কৃতির যোগ। ভাষা টান দিলে সংস্কৃতিও আসে। আধুনিক জীবনের সাথে তাল মিলানোর জন্য না হয় ভার্নাকুলার হিসেবে ইংরেজি গ্রহণ করলাম, কিন্তু সেই গ্রহণের মধ্যে সংস্কৃতির যে ফাঁকটা আছে- তা ধরতে না পারলে আমরা অস্তিত্বসম্মান নিয়ে টিকতে পারবে না। আমাদের ইতিহাস, সংস্কৃতি ও আদর্শের অনুজ্ঞা দিয়েই আমাদের আত্মোদ্ধারের পথ খুঁজতে হবে। মেকলেকে ছাড়া আমাদের চলে কিনা তা আমাদের রাজনীতি নীতি নির্ধারকদের ভেবে দেখতে হবে।
মেকলেও জানতেন উপনিবেশ চিরস্থায়ী হবে না। কিন্তু উপনিবেশের সামাজিক, রাজনৈতিক, বৌদ্ধিক ব্যবস্থা উপনিবেশিত হয়ে গেলে তার ফল হবে সুদূরপ্রসারী এটা তিনি ভালো করে বুঝতে পেরেছিলেন। মেকলে যে দেশী সাহেব তৈরির কারখানা বানিয়ে গেলেন তাই হবে ইংরেজের অগ্রবাহিনী। এখন থেকে আর সাম্রাজ্যবাদকে সৈন্য সামন্ত নিয়ে দেশ দখলের লড়াইয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ার দরকার নেই। এই অগ্রবাহিনীই সাম্রাজ্যবাদের হয়ে কাজটা এগিয়ে দেবে। লক্ষ্য করুন তুরস্কের কামাল আতাতুর্ক, ইরানের রেজা শাহ পাহলভী কিংবা আজকালকার হামিদ কারজাইদের। কেউতো বলতে পারবেন না এরা তুর্কী, ইরানী কিংবা আফগানী নন। কিন্তু কাজটা তারা দেশের জন্য করেননি, করেছেন সাম্রাজ্যবাদের হয়ে মেকলে এরকমটাই চেয়েছিলেন। উপনিবেশের স্থায়িত্ব তিনি চেয়েছিলেন অবশ্যই। কিন্তু উপনিবেশের ভিতরেই যে আর একটি উপনিবেশের কথা তিনি ভেবে রেখেছিলেন তার স্বরূপ আমরা কি আজও পুরোপুরি শনাক্ত করতে পেরেছি?
মেকলের কৌশল সবচেয়ে বেশি কার্যকর হয়েছে আমাদের সাংস্কৃতিক চৈতন্যের ক্ষেত্রে। দীর্ঘদিনের উপনিবেশিক শাসন আমাদের সাংস্কৃতিক চরিত্র দূষিত, বিকৃত, উল্টাপাল্টা করে দিয়েছে। আমাদের আত্মপরিচয়কে করে তুলেছে সংশয়াপন্ন। মেকলের বরাতে পশ্চিমের চিন্তা Orient এর কাভার পেজে সালমান রুশদী ১৯৮৬ তে তার প্রশংসামূলক পরিচয় লিখে দেন। ১৯৮৯-৯০তে যখন রুশদীর সাটানিক ভার্সেস নিয়ে তীব্র বাদানুবাদ চলছে তখন কাব্বানীর হুঁশ হয়। ইসলামের নেতিবাচক চরিত্রায়নে রুশদীর অভিসন্ধিমূলক কাজের তিনি প্রতিবাদ করেন। আর যায় কোথায়। পশ্চিমা মিডিয়া তাকে ছেকে ধরে। যেন মৌচাকে ঢিল পড়ার মতো অবস্থা। কাব্বানীর কেমব্রিজের শিক্ষা, মধ্যপ্রাচ্যের অভিজাত পারিবারিক সম্পর্ক কোনো কিছুই কাজে লাগে না। তাকে মৌলবাদী প্রতিক্রিয়াশীল বলে গাল দেয়া হয়। তার পুরাতন বন্ধুরা তার এই নতুন ভূমিকায় ত্যক্ত বিরক্ত হয়ে পরিত্যাগ করে। কাব্বানী পুরোপুরি একদার হয়ে পড়েন। তাকে ক্লাব ছাড়তে হয়। বার ত্যাগ করতে হয়। এটা পরিষ্কার হয়ে যায় : You were either with us or damned for ever এর সাথে আজকের প্রেসিডেন্ট বুশের দয়োক্তির কথা স্মরণ করুন। এই হচ্ছে আধুনিকতাবাদী পাশ্চাত্যের বিচার বিবেচনার নমুনা।
দুই,
মেকলে যে নাটকের শুরু করে গিয়েছিলেন এখন মনে হচ্ছে এইসব আধুনিকতাবাদী সাহিত্যসেবী ও বুদ্ধিজীবীরা সেই নাটকের শেষ দৃশ্যের পাত্রপাত্রী হিসেবে অবতীর্ণ হয়েছেন। এদের মধ্যে আবার কেউ কেউ আছেন পুরনো মার্কসবাদী ও সাম্যবাদী চিন্তাভাবনার উজ্জীবিত। যদিও এদের ব্যক্তিগত জীবনাচার, পারিবারিক সুযোগ সুবিধা ও পাশ্চাত্যের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাপ্ত শিক্ষা সমাজতন্ত্রী চিন্তাভাবনার সাথে ঠিক কতটুকু সামঞ্জস্যপূর্ণ তা বিবেচনাসাপেক্ষ। বিলাতে অবস্থানকারী পাকিস্তানী লেখক শাব্বির আখতার এদের বলেছেন Champagne Socialists সালমান রুশদীর মতো বামপন্থী হানিফ কোরেশী, তারিক আলী প্রমুখ পশ্চিমে বসে কিছু পরিচিতি পেয়েছেন, তাদের ইসলাম বিদ্বেষের সুবাদে। যদিও মুসলিম জনসাধারণের মধ্যে তাদের প্রভাব প্রায় নেই বললেই চলে।
কিছুদিন আগে পাকিস্তানী বংশোদ্ভূত তারিক আলী বিলাতে বসে Iranian Nights নামে একটা নাটক লেখেন। এ নাটকে ইসলামের চরিত্রায়ন করা হয়েছে অত্যন্ত কদর্যতার সাথে। ইসলামকে যত ভয়ানক ও নেতিবাচকভাবে সম্ভব এ নাটকে তুলে ধরা হয়েছে। উন্মাদ মোল্লাহ, মাদক চোরাচালানী ও ব্যবসা, নানা রকম যৌন অনাচার প্রভৃতির সাথে ইসলামকে এখানে সুনির্দিষ্ট অভিসন্ধি নিয়ে একাত্ম করে দেখানো হয়েছে। উল্লেখ্য সালমান রুশদী ও তার বন্ধু-বান্ধব এ নাটকটির প্রচারণার জন্য বেশ কিছু প্রোগ্রাম করেন, যদিও তা ফ্লপ করে। এবার বিলাতের মুসলমানরাও সতর্ক হন। তারা এবার রুশদীর সাটানিক ভার্সেস-এর মতো এ নাটকটির কপি রাস্তায় এনে পুড়িয়ে প্রতিবাদ জানাননি। তারিক আলীর বরাত খারাপ, ফলে মিডিয়ার নজর যথাযথভাবে তিনি কাড়তে পারেননি। তার রুশদী হওয়ার স্বপ্নও পুরোপুরি সফল হয়নি। বোধহয় মুসলমানরা অতীত থেকে কিছু কিছু শিক্ষা নিচ্ছেন। বিলাতের তারিক আলী এবং আমাদের এই ঢাকার হুমায়ুন আজাদদের লেখালেখি, চিন্তাভাবনা, বিশ্বাসের চেতনাগত কোনো তফাৎ নেই। তারিক আলীর Iranian Nights এবং আজাদের পাক সার জমীন সাদ বাদের মূল সুর একই। এদের সকলের সাধারণ প্রতিপক্ষ হচ্ছে ইসলাম এবং এটির বিরুদ্ধে লড়াই জারি রেখে সাম্রাজ্যবাদের প্রীতিভাজন হয়ে ওঠাই হচ্ছে এদের একমাত্র কাজ। সাহিত্য ও শিল্পগত বিচারে এদের লেখালেখির মূল্য সামান্যও নেই। কিন্তু পাশ্চাত্যের মিডিয়ার কাছে এদের কদর বড় বেশি। মিডিয়ার জোরেই এরা সেলিব্রেটি। মুসলিম দেশগুলোতে মার্কসবাদ ব্যর্থ হয়েছে। এর কারণ ইসলামের নিজের ভিতরেই সমাজ বিপ্লব ঘটানোর মতো যোগ্যতা, সামর্থ্য ও উপকরণ রয়েছে। নাসেরের আরব সমাজতন্ত্র, গাদ্দাফীর গ্রীন রেভ্যুলেশন- গ্রীন বুক ধরনের সমাজতন্ত্র, ইরাক ও দরিয়ার বাঘ পাটি ধাচের সমাজতন্ত্র, আমাদের দেশের বাকশাল মার্কা সমাজতন্ত্র, এর প্রত্যেকটির পরীক্ষা-নিরীক্ষার পরিণতি আমাদের চোখের সামনে আছে। এরপরেও মুসলিম সমাজে পশ্চিমা ভাবাপন্ন কিছু মার্কসবাদী আছেন যাদের কাছে স্বাধীনতার অর্থ হলো যৌনতার স্বাধীনতা। শরাব পানের স্বাধীনতা এবং সুবিধাবাদিতার নগ্ন প্রতিযোগিতা। প্রকৃত বিচারে মার্কসবাদী আদর্শের প্রতি এক ধরনের বুড়ো আঙ্গুল তারা দেখিয়ে চলেছেন। যৌবনের সমাজতন্ত্রী আবেগ ধীরে ধীরে নিঃশেষ হয়ে এলে এরাই দ্রুত পারিবারিক বৃত্তে প্রবেশ করেন এবং নিজেদের ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্প, জমিদারী দেখাশোনা নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। তাদের অধীনে কর্মরত শ্রমিক ও মেহনতী মানুষ ভুলেও তাদের মার্কসবাদী অতীত নিয়ে সন্দেহ করতে পারে না।
আসলে মার্কস নিজে দরিদ্রের প্রতি যে আবেগ দেখিয়েছেন তাও কিন্তু বর্ণবাদী ভেদরেখা অতিক্রম করতে পারেনি। তার এই আবেগ কিন্তু শ্বেতাঙ্গ দরিদ্রদের প্রতি সীমাবদ্ধ ছিল। এশিয়ানদের সম্পর্কে তার মতামত রীতিমতো বর্ণবাদী দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা পরিচালিত এবং সমাজতাত্ত্বিকভাবেও সেই বিবেচনা নির্ভুল নয়। তার বন্ধু এঙ্গেলসের মতোই অবচেতনভাবে তিনিও ছিলেন বর্ণবাদী। এশিয়ার মার্কসবাদীরা এই সত্যকে ধামাচাপা দিতে চান, এটি হচ্ছে বুদ্ধিবৃত্তিক অসততার বড় নমুনা।
কমিউনিজমের পতনের পর মার্কসবাদী রাজনীতিবিদ, বুদ্ধিজীবী, সাহিত্যসেবীরা কিছুটা হতচকিত হয়ে পড়লেও এদের দুর্বীনিত বিশ্বাস আচরণে কোনো প্রকার পরিবর্তন ঘটেনি। অনেকেই তাদের কেবলা পরিবর্তন করেছেন এবং পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদের দেয়া সুযোগ সুবিধা হাতিয়ে নিতে দ্রুত তাদের দলে ভিড়ে গেছেন। কিন্তু এদের পুরনো মজ্জাগত ইসলাম বিদ্বেষে এতটুকুও ভাটা পড়েনি।
তিন,
মেকলের নীতি যেমন আমাদের সাংস্কৃতিক চৈতন্যকে দূষিত করেছে তেমনি আমাদের জাতিক চেতনাকেও দেউলিয়া ও সংশয়ী করে দিয়েছে। আমাদের এখানে বহুদিন হলো আমরা কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছুতে পারিনি আমরা মুসলমান না বাঙালী। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর পুরো আরব আরব। একই রকম ঘটনা আমরা তুরস্কে কামাল আতাতুর্কের উত্থানের পর লক্ষ্য করেছি। দুনিয়া জুড়ে এক অবিমৃষ্যকারী ও আত্মবিনাশী চেতনা প্রবল হয়ে ওঠে তারা মুসলমান না মুসলমান ও ইউরোপিয়ান হওয়ার টানাপোড়েনের মধ্যে। রেজা শাহ পাহলভী তো সোজাসুজি বলতেন তিনি হচ্ছেন আর্য। জাতিকতা ও বিশ্বাসের দিক দিয়ে মুসলিম সমাজে এই দ্বিধা, সংশয় ও সন্দেহের জন্য কলোনির কালে কলোনির প্রভুদের শিক্ষা ও দর্শন আমাদের চিন্তা ও এমনভাবে খণ্ডিত করে ফেলেছে যে আমাদের আধুনিকতাবাদীরা আর ইসলামের পরিচয়ে নিজেদের উন্মোচন করতে চান না। এদের অনেকেরই ধারণা এই যে আমরা ইসলাম ধর্মটা গ্রহণ করেছি এটা একটা বাইরের প্রয়োজনে। এই প্রয়োজন থেকে বেরিয়ে আসতে পারলে আমাদের মুক্তির লক্ষ্য অর্জিত হবে। কেউ কেউ আর একটু বাড়িয়ে বলতে চান আমরা যে ইসলাম ধর্ম পেয়েছি তা অনেকটাই লৌকিক ধর্ম, আচার অনুষ্ঠান সর্বস্ব। এর বাইরে গভীরতর কোনো ধর্ম জিজ্ঞাসায় আমাদের পৌঁছুনো দরকার। আধুনিকতাবাদীদের এইসব তাত্ত্বিক মারপ্যাচ ও জটিলতা সৃষ্টির পিছনে উদ্দেশ্য একটাই- ইসলাম ভিন্ন অন্য কোনো উৎসের কাছে আমাদের আদর্শিক প্রেরণার জন্য হাত বাড়িয়ে দেয়া।
আমাদের এখানে কোনো কোনো সংস্কৃতিসেবী আছেন যারা তারস্বরে বলে বেড়ান আমাদের বিপদে, শংকায়, অস্বস্তিতে রবীন্দ্রনাথ হচ্ছেন পরম আশ্রয়। কেউ কেউ তো এমন কথাও বলেন, রবীন্দ্র-সংগীত শ্রবণ হচ্ছে ইবাদতের মতো। একটা অদ্ভুত বিস্ময় কাজ করে যখন দেখি আমাদের হীনমন্যতা কোথায় টেনে নিয়ে যাচ্ছে। একজন মুসলমানের বিপদের আশ্রয় কি রবীন্দ্রনাথ হতে পারেন? এ তার মৌলিক বিশ্বাসের পরিপন্থী। এই অপচার, অপবিশ্বাস, অপসংস্কৃতি লালন করে কেউ মুসলমান থাকতে পারেন না। অথচ সে কাজটিই এখন আমাদের করতে বলা হচ্ছে বাঙালী সংস্কৃতির নামে।
এদেশে যারা বাঙালী সংস্কৃতি ও জাতীয়তার দাবি নিয়ে সোচ্চার তারা এদেশের ইসলামের ইতিহাস, ঐতিহ্য, উত্তরাধিকার নিয়ে মাথা ঘামান না। ইসলামের বাইরের অন্য কোনো অতীত, অন্য কোনো উত্তরাধিকার নিয়ে তারা অতিশয় ব্যস্ত। এদের ঝোঁক এমন এক বাংলাদেশের দিকে যেখানে ইসলামী মন মানস, সংস্কৃতি, জীবনভাবনা ও উত্তরাধিকার অনুপস্থিত। ইসলামের কথা শুনলেই এরা উত্তেজিত হন। এই সব হারিকিরি করতে উদ্যত বুদ্ধিজীবীরা আমাদের জাতিকতার ধারণাকে ইতোমধ্যে কুয়াশাচ্ছন্ন করে ফেলেছেন এবং আমাদের জনগণকে বিভক্ত বিচ্ছিন্ন করতে সমর্থ হয়েছেন। মেকলের বুদ্ধির তারিফ না করে উপায় নেই।
আমাদের এখানকার বাঙালি জাতীয়তাবাদীদের মতো এক সময় পুরো মধ্যপ্রাচ্যে সাম্রাজ্যবাদীদের মদদে পল্লবিত হয় আরব জাতীয়তাবাদের ধারণা। এই জাতীয়তাবাদের ভিত্তি হচ্ছে একদিকে আরবি ভাষা, অন্যদিকে আরবি মননশীলতা ও সৃষ্টিশীলতার এক অন্ধ বিশ্বাস। এই সব ধর্মনিরপেক্ষ আরবি জাতীয়তার অনুসারীরা ইমরুল কায়েসের কথা বলেন, ইসলাম পূর্ব পৌত্তলিক আরবের ঐতিহ্য ও উত্তরাধিকার নিয়ে গৌরববোধ করেন। ইমরুল কায়েস প্রতিভাবান কবি ছিলেন। কিন্তু তার কবিতা পৌত্তলিকতা ও অশ্লীলতার দায়মুক্ত নয়। এই কারণে তা ইসলাম অনুমোদন করতে পারে না।
‘আরবি জাতীয়তাবাদীরা মনে করেন ইসলাম হচ্ছে আরবি মননশীলতার আবিষ্কার। অদ্ভুত যুক্তি বটে। একথা মানতে হলে তো এই যে আমরা যুগ যুগ ধরে ইসলামকে আল্লাহ প্রদত্ত জীবন ব্যবস্থা হিসেবে মান্য করে আসছি তার ব্যতিক্রম ঘটাতে হবে। মনে রাখা দরকার এক সময় ইসলামের কারণেই আরবরা ঐক্যবদ্ধ হতে পেরেছিল, পরিণতিতে তারা একটি শক্তিশালী সভ্যতারও জন্ম দিয়েছিল। কিন্তু আরবরা যখন ইসলাম হয়েছে তখন থেকে দুর্গতি-দুর্দশা তাদের উপর ভর করেছে। আরব জাতীয়তাবাদ ঐক্যের কথা বললেও কার্যত এটি আরবদের ঐক্যবদ্ধ করতে পারেনি। এটি পরিণত হয়েছে সিরিয়, হিজাজী, লিবিয় প্রভৃতি নানারকম জাতীয়তাবাদে। নীতি, আদর্শ, চিন্তাভাবনার দিক দিয়েও তা ঐক্যবদ্ধ নয়। পরস্পরের দিকে মুখিয়ে থাকাই যেন এখন তাদের কাজ।
মুসলিম সমাজের ঐক্যের ভিত্তি হচ্ছে ইসলাম। এই আদর্শগত ঐক্যের পরিবর্তে নানারকম জাতীয়তাবাদ, স্থানিক সংস্কৃতি ও রজনৈতিক চেতনা, পশ্চিমী মূল্যবোধ আজকাল এর স্থান দখল করেছে। ফলে যে সংহতি চেতনা একদিন মুসলিম সমাজকে তাড়িয়ে নিয়ে ফিরতো তা কিন্তু দুর্বল হয়ে পড়ছে। আর এই দুর্বলতর পটভূমিতে মুসলিম সমাজ ও রাষ্ট্রগুলোর ওপর সাম্রাজ্যবাদের নিয়ন্ত্রণও বাড়ছে। এর ফলে তাবৎ পৃথিবী জুড়ে মুসলিম সমাজগুলোর মধ্যে বিরাজ করছে এক বিশৃঙ্খল অবস্থা, এর সাংস্কৃতিক অঙ্গনে চলছে চরম বিকৃতি আর অর্থনৈতিক জীবনে সীমাহীন দুর্নীতি ও অব্যবস্থা। চিন্তাক্ষেত্রে বুদ্ধিজীবী ও রাজনৈতিক নেতাদের দেউলিয়াপনা উৎকটভাবে প্রকাশ পাচ্ছে। এই সংকট থেকে উত্তরণের একমাত্র পথ হলো ইসলামকে ভিত্তি করে মুসলিম সমাজের গণতান্ত্রিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক সর্বোপরি মনোজাতিক বুনিয়াদকে শক্তভাবে প্রতিষ্ঠিত করা। ঐতিহাসিক বিবর্তনের নানা বাঁকে একটি সমাজের মধ্যে আদর্শিক বিচ্যুতির কারণে এবং যুগোপযোগী দৃষ্টিভঙ্গির অভাবে নানারকম ক্ষয় ও পতন আসতে পারে। সেই পতনের বিরুদ্ধে অন্যের কাছ থেকে ধার করা আদর্শে নয়, নিজের আদর্শের মৌলিকত্বের দাবি নিয়েই নতুন করে সংগ্রামের প্রয়োজন দেখা দেয়। এই নতুন সংগ্রামে অগ্রণী ভূমিকা পালন করার ঐতিহাসিক দায়িত্ব এসে পড়েছে মুসলমানদের উপরে। তারা কি এই মহান দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হবেন?