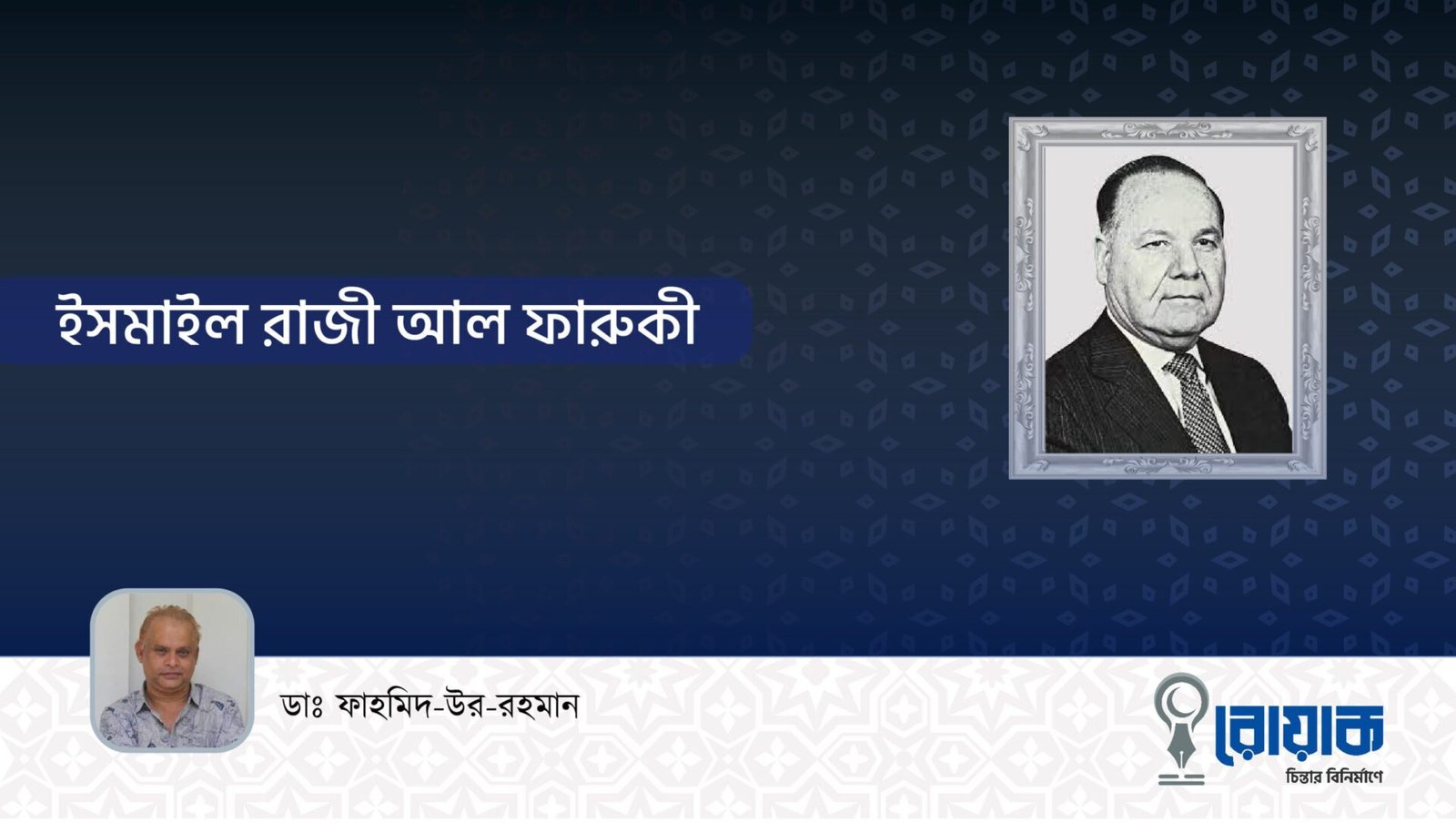১৯৮৬ সালের ২৪ মে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মাটিতে কৃতী অধ্যাপক ইসমাইল রাজী আল ফারুকী ও তার স্ত্রী লুইস লামিয়া ফারুকী আততায়ীর গুলিতে শহীদ হন। এ শাহাদাতের মধ্য দিয়ে এ কালে মুসলিম চিন্তার জগতের এক উজ্জ্বল ধ্রুবতারা খসে পড়ে এবং একজন সৃষ্টিশীল বুদ্ধিজীবীর কর্মঘন জীবন নীরব হয়ে যায়। ফারুকী যুক্তরাষ্ট্রে ইসলামী চিন্তার বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। তিনি বিশ্বব্যাপী আন্তঃধর্মীয় সংলাপের একজন নিষ্ঠাবান উদ্যোগী, বিশেষ করে ইসলামী সমাজের কালোপযোগী রূপান্তর প্রচেষ্টায় তিনি ছিলেন একজন মহান কর্মী।
অধ্যাপক ফারুকী তার জীবনব্যাপী সাধনায় ইসলামকে শক্তিমান ও পয়মন্ত করার লক্ষ্যে এক বুদ্ধিবৃত্তিক সংগ্রামে (Intellectual Struggle) নেতৃত্ব দিয়ে গেছেন। সেদিক দিয়ে তার জীবনকে আল্লাহর পথে সংগ্রামরত এক যথার্থ মুজাহিদের জীবনের সাথে তুলনা করা যেতে পারে। তার জন্য কথাটি আরো বেশি সত্য এ কারণে যে, জীবনের প্রথম দিকে তাকে একজন ফিলিস্তিনী মুহাজির হিসেবে এবং পরবর্তীকালে ইসলামের বুদ্ধিবৃত্তিক সৈনিক হিসেবে তাকে লড়াই করতে হয়েছিলো। ফিলিস্তিনী শিকড়, আরব ঐতিহ্য ও ইসলামের বিশ্বাস– এ সবের সমন্বয়ে তার চিন্তা-ভাবনা, মানসিকতার যে ভূগোল তৈরি হয়, তাই পরবর্তীকালে তার লেখালেখি ও বুদ্ধিবৃত্তিক আলোচনার উপাদান হয়েছিলো। সন্দেহ নেই যে, একালে আত্মপরিচয় (Identity), বিশুদ্ধতা (Authenticity) সাংস্কৃতিক চাপ ও অনুপ্রবেশ (Acculturation) এবং পশ্চিমী রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সাম্রাজ্যবাদ একটি বড় ঘটনা। স্বাভাবিকভাবেই ফারুকীর এ সমস্ত বিষয়গুলো খুব গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে, যদিও তিনি তা বিভিন্ন সময় বিভিন্নভাবে উপস্থাপন করার চেষ্টা করেছেন। যেমন তিনি জীবনের প্রথম দিকে আরববাদ (Arabism) ও ইসলামকে পুরোপুরি অভিন্ন হিসেবে দেখেছেন, পরবর্তীকালে চিন্তার এই স্তর অতিক্রম করে ভিন্ন একটি মাত্রায় অবস্থান নেন যেখানে তিনি তৌহিদকে সবকিছুর ভরকেন্দ্র হিসেবে বিবেচনা করেন এবং তৌহিদকে ভিত্তি করেই বিশ্বাস, ও আদর্শ সমাজের রূপরেখা নির্মানে অগ্রসর হন।
অধ্যাপক ফারুকীর জন্ম ১৯২১ সালের ১ জানুয়ারি, ফিলিস্তিনের অন্তর্গত জাফার এক বর্ধিষ্ণু পরিবারে। তার পিতা আবদ আল-হুদা আল-ফারুকী ছিলেন একজন বিচারক এবং ফিলিস্তিনের সুপরিচিত ব্যক্তিত্ব। শৈশবে মক্তবে তার ইসলামী শিক্ষায় হাতে খড়ি হয়। পরে তিনি ফিলিস্তিনের ফরাসী ক্যাথলিক স্কুলে অধ্যয়ন করেন। ১৯৪১ সালে বৈরুতের আমেরিকান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি স্নাতক ডিগ্রি লাভ করেন। ফারুকী এ সময়ে আরবী, ইংরেজি ও ফরাসী– এ তিনটি ভাষায় গভীর ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন এবং পরবর্তীকালে বুদ্ধি ও মননগত সকল প্রেরণা ও কর্মসূচীর জন্য এসব উৎসের দিকে তিনি অকৃপণভাবে হাত বাড়ান। স্নাতক ডিগ্রি অর্জনের পর তিনি প্রাথমিকভাবে সরকারি চাকরিতে প্রবেশ করেন এবং ১৯৪৫ সালে মাত্র ২৪ বছর বয়সে ফিলিস্তিন সরকারের অধীনস্থ গ্যালিলির জেলা গভর্নর নিযুক্ত হন। এভাবে তার ভবিষ্যতের পথ রচনা হতে শুরু করে। কিন্তু হঠাৎই একদিন তার প্রশাসক জীবনের অবসান ঘটে, যখন ১৯৪৮ সালে ফিলিস্তিনে ইসরাইলী দখলদার বাহিনী প্রবেশ করে এবং পশ্চাত্যের সাম্রাজ্যবাদের চক্রান্তে ফিলিস্তিনীরা নিজ ভূমে পরবাসী হয়ে যায়। হাজার হাজার ফিলিস্তিনী মুসলিম পরিবারের মত ফারুকীর পরিবারও ফিলিস্তিন থেকে বহিষ্কৃত হয়ে লেবাননে আশ্রয় নেয়। এ ছিলো ফারুকীর জীবনের সন্ধিক্ষণ মুহূর্ত। একদিকে দেশান্তর, ফিলিস্তিনীদের উপর আপতিত দুর্ভোগ, অন্যদিকে নিজের জীবনের ভবিষ্যৎ অনিশ্চয়তা– এসব মিলিয়ে ফারুকীর মনন ও চিন্তার জগতে যে এক ধরনের ঝড় বইতে শুরু করেছিলো তাতে কোনো সন্দেহ নেই। আর এসব ঘটনা তার মানসিকতা ও ব্যক্তিত্ব নির্মাণে প্রভাব ফেলেছে।
প্রশাসক জীবনের ইতি ঘটলেও লেখাপড়ার উৎসাহে তার কখনো ভাটা পড়েনি। পারিবারিক অনিশ্চয়তা ও অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের মধ্যেও তিনি লেখাপড়া চালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। প্রাথমিকভাবে যুক্তরাষ্ট্রের ইন্ডিয়ানা ও হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি নেওয়ার পরে তিনি ১৯৫২ সালে ইন্ডিয়ানা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দর্শনে পিএইচডি করেন। কিন্তু এ সময়গুলো তার জন্য ছিলো রীতিমত উদ্বেগ ও কষ্টের। অর্থনৈতিক কারণে তাকে এক সময় লেখাপড়া ছেড়ে দিতে হয় এবং অতঃপর তিনি পারিবারিক নির্মাণ ব্যবসায় জড়িত হন। অবশ্য ফারুকীর অদম্য ইচ্ছা শক্তির সামনে এসব বাধা-বিপত্তি পরাজিত হয়। পরবর্তীকালে তিনি তার এ দিনগুলোর কথা স্মৃতিচারণ করেছেন এভাবে যে, সার্ডিনের স্যান্ডউইচের সাথে লেবুর রস মিশিয়ে খেয়ে তিনি ও তার এক চাচাতো ভাই দিনের পর দিন পার করে দিতেন!
ফারুকী যদিও পাশ্চাত্য দর্শনে পিএইচডি করেছিলেন, কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রে তখন চাকরির বাজার ছিলো মন্দা, তাছাড়া প্রথমদিকে সেখানে তার চাকরি ভাগ্যও ভালো হয়নি। তাই তাকে ফিরে আসতে হয়। অতঃপর তিনি কায়রোর বিখ্যাত আল আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে যুক্ত হন এবং ১৯৫৪ থেকে ১৯৫৮ এ চার বছর ইসলামের উপর অধ্যয়ন ও গবেষণা করে কাটান। ১৯৫৯ সালে তিনি পুনরায় পাশ্চাত্যের আমন্ত্রণ পান এবং ম্যাকগিল বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক স্টাডিজের অধ্যাপক হিসেবে যোগ দেন। ১৯৫৯ থেকে ১৯৬১ সাল পর্যন্ত তিনি এ পদে ছিলেন এবং এ সময়ে তিনি খ্রিস্টান ও ইহুদী ধর্মের উপর গবেষণা করেন। ১৯৬১ সালে তিনি করাচী সেন্ট্রাল ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক রিসার্চের অধ্যাপক হিসেবে যোগ দেন এবং ১৯৬৩ সাল পর্যন্ত এ পদে কর্মরত ছিলেন। পরবর্তী বছর শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের History of Religions এর ভিসিটিং প্রফেসর হিসেবে যোগ দেন। একই বছর তিনি পুনরায় সিরাকুজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হিসেবে যোগ দেন এবং ১৯৬৮ সালে টেম্পল বিশ্ববিদ্যালয়ের Islamics and History of Religions এর অধ্যাপক হন। ১৯৮৬ সালে মৃত্যু বরণের আহ পর্যন্ত তিনি এ পদে কর্মরত ছিলেন।
ফারুকী তার বৈচিত্র্যময় পেশাগত জীবনে অন্ততপক্ষে ২৫ টি বই রচনা, সম্পাদনা অথবা তরজমা করেন, একশর উপর গবেষণামূলক নিবন্ধ তৈরি করেন, আফ্রিকা, ইউরোপ, মধ্যপ্রাচ্য, দক্ষিণ ও দক্ষিণপূর্ব এশিয়ায় প্রায় ২০ টি বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিপিটি প্রফেসর হিসেবে কাজ করেন এবং ৭টি মূল্যবান গবেষণা পত্রিকার সম্পাদকমন্ডলীর সাথে যুক্ত ছিলেন। এ তার অদম্য ইচ্ছাশক্তি, আত্মবিশ্বাস ও উদ্দেশ্যের প্রতি সমর্পিত চিত্তের প্রকৃষ্ট নজির।
অধ্যাপক ফারুকীর আরব ঐতিহ্য ও ফিলিস্তিনী শিকড় তার প্রথম জীবনের চিন্তাভাবনায় একটি বড় প্রভাব ফেলেছে বলে মনে করা হয়। এ সময় তিনি আরবীদের শক্তি ও ঐশ্বর্যের (যেটিকে তিনি ‘আরববাদ’ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন) সাথে ইসলামকে অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত করে দেখেছেন। তখন তার চিন্তাভাবনার প্রধান বিষয়ই ছিলো আরববাদ। আর তার এ সকল চিন্তাভাবনার প্রকাশ ঘটেছে On Arabism Urubah and Religion গ্রন্থে। এ গ্রন্থে তিনি আরববাদকে ইসলামী আদর্শ, ইতিহাস ও সংস্কৃতির প্রাণ হিসেবে যেমন উল্লেখ করেন, একই সাথে আরবীয় জীবনের আত্মা হিসেবেও দেখানোর চেষ্টা করেন। তার ভাষায় আরববাদ হলো ‘…as old as the Arab stream of being itself since it is the spirit which animates the stream and gives the momentum’।
ফারুকীর ভাষায় আরববাদের সীমান্ত বহু বিস্তৃত, যার মধ্যে পুরো মুসলিম উম্মাহ ও আরবী ভাষাভাষী অমুসলমানরাও অন্তর্ভুক্ত। আরববাদ শুধু একটি নিছক ধারণার নাম নয়, বরং এটি একটি বাস্তবতা, এটি আত্মপরিচয় ও মূল্যবোধের নাম যা সকল মুসলমান ও আরবী ভাষাভাষী অমুসলমানদের সাথে অবিচ্ছিন্নভাবে যুক্ত। তিনি আরববাদকে উম্মাহর শক্তি হিসেবেও উল্লেখ করেন, কেননা তিনি মনে করেন, আরবী ভাষা এবং আরব সচেতনতা ও মূল্যবোধ হলো ইসলামের সাধারণ বিশ্বাসের চাবিকাঠি। এ সময় ফারুকীর আরবপ্রেম (Arabophobia) এতই প্রবল ও দৃশ্যমান ছিলো যে, পবিত্র কোরআন শরীফও তিনি আরবীয় চোখ দিয়ে পড়তে থাকেন। যেহেতু কোরআনের ভাষা আরবী, তাই ফারুকীর অবশ্যম্ভাবী যুক্তি হলো ‘ওহীর মূল বক্তব্য বা বাণীও আরবদের উদ্দেশ্যে প্রেরিত’। মুসলিম উম্মাহকে লক্ষ্য করে প্রথম কোরআনের বাণীকে তিনি আরবদের উদ্দেশ্যে প্রেরিত বলে উল্লেখ করেন, “তোমরাই মানবমন্ডলীর মধ্যে সর্বোত্তম হিসেবে স্বীকৃত।” ফারুকীর চিন্তার জগত জুড়ে এ সময়ে আরবাদই যে প্রধান স্থান দখল করে ছিলো তা বোঝা যায় তার আরববাদের উপর চারটি সিরিজ বইয়ের শিরোনামের দিকে চোখ বুলালে। শিরোনামগুলো গলো Urubah and Religion, Urubah and Art, Urubah and Society, Urubah and Man। তিনি মনে করেন, আরববাদ বা আরব সচেতনতা হলো ঐশী বাণীর বাহক এবং বিশ্বাস, সমাজ ও সংস্কৃতির অবশ্যম্ভাবী অংশ। এ প্রক্রিয়ায় আরববাদ হলো হযরত ইব্রাহীম (আ.) থেকে আগত তিনটি ঐশী ধর্মের ইতিহাসের প্রধান নিয়ামক শক্তি। ফারুকীর ভাষায়, “Arabism is coextensive with the values of Islam as well as with the meaning of the Hebrew prophets and Jesus.”
তিনি আরববাদকে আরবী ভাষাভাষী অমুসলমানদের প্রকৃত আত্মপরিচয় হিসেবেও চিহ্নিত করার চেষ্টা করেছেন, যদিও তার কথা হলো ইউরোপীয় ঔপনিবেশিকতার প্রভাবে এসব অমুসলমান আরবী ভাষাভাষীরা তাদের সেই পরিচয় ভুলতে বসেছে। একই কারণে তিনি মনে করেন, আরবী ভাষাভাষী খ্রিস্টানরা এখনও কিছুটা ‘গেমিডিয় পবিত্রতা’ রক্ষা করে চলেছে, কিন্তু পাশ্চাত্যের খ্রিস্টানরা যীশুর বাণী থেকে বিচ্যুত হয়েছে। ফারুকী পরবর্তীকালে যখন ইসলামের দিকে ঝুঁকেছেন, তখনও তিনি আরববাদের প্রতি মায়া পুরোপুরি ছাড়তে পারেননি। ইসলামের ভিতরে যে আরববাদের এক স্থান আছে সে কথা তিনি অবলীলায় বলতে ভোলেননি। তার ভাষ্যে, “The Quran is inseparable from its Arabic form, and hence… Islam is ipso facto inseparable from urubah.”
ফারুকীর এসব চিন্তাভাবনা, বিশেষ করে আরববাদকে ইসলামের সাথে মিশিয়ে ফেলার ধারণা এক ধরনের অতিশয়োক্তি বলে মনে হয়। এটি সত্য যে, গত শতকে যখন ফিলিস্তিনে সম্পূর্ণ সন্ত্রাসী কায়দায় ইহুদীরা পরাশক্তির সহযোগিতায় তাদের অবৈধ রাষ্ট্রের জন্ম দেয়, তখন অসংখ্য আরব গৃহহীন ও দেশান্তরী হয়। এর ফলে তাদের অবচেতন মনে এক ধরনের আরবীয় সচেতনতা দানা বেঁধে ওঠে। তারা ভাবতে থাকে, আরব হওয়ার কারণে, সেই সাথে মুসলমান হওয়ার কারণে তাদের উপর এ জুলুম নেমে এসেছে। এ অনুভূতি তাদের মনে যে Counter reaction এর জন্ম দেয়, তার থেকেই আরববাদের মতো এক ধরনের অতিশয়োক্তিমূলক ধারণার উদ্ভব ঘটা অস্বাভাবিক কিছু নয়। হয়তো ফারুকীর পক্ষেও এ অস্বাভাবিক মানসিক অবস্থা থেকে অন্তত কিছুদিনের জন্য হলেও বের হয়ে আসা সম্ভব হয়নি। যদিও ফারুকী তার আরববাদকে কিছু আরবীয় খৃস্টান, যেমন কনস্টানটাইন ডুবাইক ও মাইকেল আফলাক কর্তৃক প্রচারিত আরব জাতীয়তাবাদের ধারণা থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখেছেন এবং বলেছেন আরব জাতীয়তাবাদ হলো ইউরোপীয় প্রভাবের ফল, অন্যদিকে তার আরববাদ হলো কোরআনের বিশ্বজনীন ধারণা প্রসূত এবং সে হিসেবে তা সকল মুসলমানের উত্তরাধিকার। পাশ্চাত্য প্রভাবিত আরব জাতীয়তাবাদকে তিনি নতুন ধরনের শুউবিয়া-গোত্রবাদের সাথে তুলনা করেছেন এবং উম্মাহর সংহতির পক্ষে যে এটি ক্ষতিকর সে কথাও বলেছেন। তবে ফারুকীর আরববাদ কোরআনের ধারণা প্রসূত– এ কথা যে পুরোপুরি বিচারোর্ধ নয়, তা বলাই বাহুল্য। ফারকী যখন তার আরববাদের চিন্তা-ভাবনা নিয়ে মেতে ছিলেন, তখন তাকে বলা হতো মুসলিম আধুনিকতাবাদী। তিনি মূলত পশ্চিমের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে পড়িয়েছেন এবং সেখানে অনেক সময় কাটিয়েছেন। পশ্চিমের শ্রোতাদের কাছে ইসলামকে তুলে ধরতে সে সময় তিনি পাশ্চাত্যের পরিভাষার সাহায্য নিয়েছেন এবং ইসলামকে তিনি যুক্তি, বিজ্ঞান ও প্রগতির ধর্ম হিসেবে প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন। এজন্য অনেকে বলেছেন, তিনি আলোক প্রাপ্তি (Enlightenment) ও প্রোটেট্যাস্ট বিশ্ববিক্ষায় (Protestant work chic) উজ্জীবিত হয়ে ইসলামকে উপস্থাপন করেছেন।
গত শতকের ৫০ ও ৬০ এর দশকে অধ্যাপক ফারুকী তার ইসলাম ও বিশ্বভাবনাকে যেমন দেখেছেন আরববাদের আয়নায়, তেমনি ৭০ ও ৮০ এর দশকে এসে তার মধ্যে আমরা রূপান্তর লক্ষ্য করছি। তিনি একটু একটু করে তার পুরনো অবস্থান থেকে সরে এসেছেন এবং তার আত্মপরিচয়কে ইসলামের মধ্যে সমাহিত করার চেষ্টা করেছেন। একইভাবে ইসলামই হয়ে উঠেছে তার সকল চিন্তা ভাবনার নির্ণায়ক। তিনি তার এ রূপান্তরের স্মৃতিচারণা করেছেন এভাবে,
“There was a time in my life… When all I cared about was proving to myself that I could win my physical and intellectual existence from the West. But, when I won it, it became meaningless, I asked : who am I? A palestinian, a philosopher, a liberal humanist? My answer was: I am a Muslim!”
ফারুকী তার চিন্তার কেন্দ্রস্থলকে যখন আরববাদের পরিবর্তে ইসলামের মধ্যে এনে নির্দিষ্ট করলেন, তখন তার এ যাবৎকালের সব পরিকল্পনার ছকই ওলটপালট হয়ে যায়। তার আরববাদের উপর লেখা বইপত্র ও প্রবন্ধরাজির জায়গায় স্থান নেয় ইসলামকেন্দ্রিক চিন্তাভাবনার ফসল। ইসলাম শুধু তার লেখালেখিতেই গুরুত্বপূর্ণ স্থান নেয়নি, বরং ইসলামই হয়ে উঠে সকল কিছুর নিয়ামক। তিনি ইসলামকে এবার উপস্থাপন করলেন বিশ্বজনীন আদর্শ, জগৎব্যাপী বিশ্বাসীদের সাধারণ আত্মপরিচয় এবং সমাজ ও সংস্কৃতির জন্য উত্তম পরিচালক ও নীতি হিসেবে। ইসলামের বিশ্বচিন্তা তখন থেকে ফারুকীর জীবন ও কর্মকাণ্ডকে নিয়ন্ত্রণ করতে থাকে এবং একই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে তিনি তার লেখালেখি, বক্তৃতা, বিবৃতি, ইসলামী আন্দোলন ও জাতীয় সরকারগুলোর সাথে যোগাযোগ, সর্বোপরি যুক্তরাষ্ট্রের মুসলমানদেরকে এক মঞ্চে ঐক্যবদ্ধ করার লক্ষ্যে তিনি অগ্রসর হন। বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে ফারুকীর এসব চিন্তা-ভাবনা ও কর্মকাণ্ডের ফলাফল হলো তার অসাধারণ দুটি গ্রন্থ। Tawhid Its Implications for Thought and Life এবং The Cultural Atlas of Islam।
এসব বইয়ে তার বিশ্বভাবনা প্রতিফলিত হয়েছে ইসলামী আয়নায় এবং যাবতীয় সমস্যা, যেমন– আত্মপরিচয়, ইতিহাস, বিশ্বাস, সংস্কৃতি, সামাজিক নিয়মকানুন এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ইত্যাদি সবকিছুকেই তিনি ইসলামী নীতির ভিত্তিতে নির্ধারণ করতে চেয়েছেন। ইসলামী দুনিয়ার জাতীয় ও সাংস্কৃতিক পার্থক্য সত্ত্বেও মুসলমানদের শক্তি ও দুর্বলতার ক্ষেত্রগুলোকে তিনি ইসলামের ভিত্তিতেই চিহ্নিত করার চেষ্টা করেছেন, মুসলিম সমাজের দুঃখ-দুর্দশার কারণ ও তার প্রতিকারও তিনি খুঁজেছেন ইসলামী আদর্শের আলোয়। মুসলিম সমাজের আধ্যাত্মিক বন্ধ্যাত্ব, মুসলিম শিক্ষা ও সমাজের পাশ্চাত্যকরণ, দরিদ্রতা, অর্থনৈতিক নির্ভরতা, রাজনৈতিক ভেদাভেদ, অকার্যকর সামরিক সুবিধা, ফিলিস্তিনের স্বাধীনতা এসব কিছুর সমাধান খুঁজতে পুরনো আরববাদের স্থলে তিনি তখন ইসলামের পথে হাঁটতে শুরু করেন। ফারুকীর মতে ক্রুসেড, ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদ, জায়নবাদ এবং পরাশক্তিগুলোর নব্য উপনিবেশবাদ এখনো পাশ্চাত্যের মনোভাব ও নীতি প্রণয়নে যেমন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে, তেমনি মুসলিম দুনিয়ার সাম্প্রতিক রাজনৈতিক বাস্তবতার বিশ্লেষণ করলেও উপরোক্ত উপাদানগুলোর উপস্থিতি দৃশ্যমান হয়ে ওঠে। ঔপনিবেশিক আমলে শুরু হওয়া মুসলিম সমাজের পাশ্চাত্যকরণ প্রক্রিয়া আজও মুসলিম সমাজ ও রাষ্ট্রগুলোকে বিপযস্ত করে চলেছে। জাতীয় সরকারগুলো আজও সেই ধ্বংসাত্মক পশ্চিমা জীবাণু ছড়িয়ে দিতে ব্যস্ত যা কিনা পুরনো গোত্রবাদের (tribalism) নব্য সংস্করণ এবং এটি মুসলিম উম্মাহকে দুর্বল ও টুকরো টুকরো করে ফেলছে। পাশ্চাত্যকরণ মূলত মানুষের জাগতিক সমৃদ্ধি ও প্রয়োজনের উপর গুরুত্বারোপ করেছে, কিন্তু আধ্যাত্মিক মূল্যবোধকে করেছে ধূল্যবলুণ্ঠিত। একই কারণে জাতীয় সরকারগুলো ও তার বশংবদ আধুনিক এলিট শ্রেণি ধর্মকে গুরুত্বহীন করে ফেলেছে। আধুনিকায়ন পরিকল্পনার নামে কোনো বিচার-বিশ্লেষণ ব্যতীত চোখ বুজে পাশ্চাত্যের মূল্যবোধকে মুসলিম সমাজে অনুপ্রবেশ করানো হয়েছে। যার ফলে মুসলমানরা ঐতিহ্যের সাথে সম্পর্কচ্যুত হয়ে গেছে এবং পরিশেষে তারা যা হতে পেরেছে, তা হলো আধুনিক মানবের এক ব্যঙ্গচিত্র (Caricature of Modern Man)।
ফারুকী আঠারো ও উনিশ শতকে মুসলিম সমাজে আবির্ভূত পুনরুজ্জীবনবাদী আন্দোলনগুলো সম্বন্ধে উৎসাহ প্রকাশ করলেও তার কাছে মনে হয়েছে পাশ্চাত্যের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় এদের যথাযথ প্রস্তুতি ছিলো না, এমনকি হাসান আল বান্নার মুসলিম ব্রাদারহুডও ইসলামী সমাজের পূর্ণ রূপরেখা জনগণের সামনে যথার্থ অর্থে তুলে ধরতে পারেনি বলে তার মনে হয়েছে। এসব আন্দোলনের অর্জন যাই হোক না কেন, মুসলিম উম্মাহ কিন্তু দিনে দিনে আরো দুর্বল ও বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে পাশ্চাত্যের উপর তার অবিরাম রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামরিক ও সাংস্কৃতিক নির্ভরশীলতার কারণে। চারিদিকে ফারুকী তাই মুসলিম উম্মাহর দুঃখজনক ছবি দেখে উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠেন। তার ভাষায় মুসলিম উম্মাহ এখন বিভক্ত, হতাশাগ্রস্ত এবং নির্ভরশীল, বহিরাগত ও অভ্যন্তরীণ শত্রুর সহজ শিকার। তিনি তাই মনে করতেন, মুসলিম সমাজের মধ্যে আজ যেমন প্রয়োজন তাজদীদ (পুনরুজ্জীবন), তেমন প্রয়োজন ইসলাহ (সংস্কার)।
ফারুকীর একজন খ্রিস্টান বন্ধু একবার বলেছিলেন, ফারুকী মনে করতেন, ইসলামের ভিতরে এখন একটি সংস্কার প্রয়োজন এবং বন্ধুটি বিশ্বাস করতেন সেই সংস্কারের অবশ্যম্ভাবী লুথার হবেন ফারুকী। ফারুকী হয়তো বাস্তবতার কারণে লুথার হতেন না, কিন্তু লুথারের কাজ তিনি করতেন। সম্ভবত লুথারের পরিবর্তে তিনি একজন মুজাহিদ হওয়াকেই অগ্রাধিকার দিতেন, কারণ মুজাহিদের কাজ হলো ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে আল্লাহর ইচ্ছা প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম করা। হয়তো সে কারণেই অতীতের ত্রুটিগুলো সংশোধন করে মুসলমানদের ভাগ্য পরিবর্তনের লক্ষ্যে শেষ জীবনে তিনি তার সব রকমের লেখালেখি ও প্রচেষ্টা নিবন্ধ করেছিলেন। ইসলাম ও পাশ্চাত্য দর্শনে সমানভাবে প্রবুদ্ধ ফারুকীর বর্তমান মুসলিম উম্মাহর যে কোনো বুদ্ধিবৃত্তিক প্রয়োজনকে সামাল দেওয়ার প্রকৃতি ছিলো। তার মধ্যে ইসলামের আধুনিক ব্যাখ্যা দাতা মোহাম্মদ আবদুহু ও ইকবালের প্রভাব যেমন লক্ষ্যণীয়, তেমনি মোহাম্মদ ইবনে আবদ আল ওহাবের পুনরুজ্জীবনবাদী চিন্তা-ভাবনাও লক্ষ্যণীয়। তিনি আবদ আল ওহাবের মতোই ইসলামের উপর সুফীবাদের ধ্বংসাত্মক প্রতিক্রিয়া, পাশাপাশি ইসলাম বহির্ভূত সাংস্কৃতিক প্রভাবের তীব্র সমালোচনা করেছেন এবং মানব জীবনের সবকিছুকে তৌহিদের শিকড়ের সাথে যুক্ত করেছেন। এর মানে ইসলামকে হতে হবে জীবনের সবকিছুর মাপকাঠি। অন্যদিকে তার মধ্যে মোহাম্মদ আবদুহুর মতো ইসলামকে যুক্তিবাদের নিরিখে যাচাই-বাছাই করার একটি প্রবণতাও লক্ষণীয়। যেমন– তিনি বলেছেন, “Knowledge of the divine will is possible by reason, certain by revelation.”
তার লেখালেখিতেও আবদ আল ওহাব ও মোহাম্মদ আবদুহুর যথেষ্ট প্রভাব লক্ষণীয়, বিশেষ করে Tawhid Its Implications for Thought and Life-এ এ দুই মনীষীর প্রভাব স্পষ্ট। ফারুকী এখানে একদিকে তৌহিদকে যেমন ইসলামের ভিত্তি হিসেবে তুলে ধরেছেন, তেমনি ইজতিহাদের প্রতি গুরুত্বারোপ করেছেন, পাশাপাশি আধুনিককালে ইসলামের গ্রহণযোগ্যতা ও আরোপযোগ্যতার কথাও ভেবেছেন। তৌহিদকে তিনি উপস্থাপন করেছেন ধর্মীয় অনুভূতি ও অভিজ্ঞতার সারাৎসার, ইসলামের মৌলিক বিন্দু এবং ইতিহাস, জ্ঞান, সৌন্দর্যবোধ, উম্মাহ, পরিবার ও রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক সর্বোপরি বৈশ্বিক শৃঙ্খলার নীতি সূত্র হিসেবে। তৌহিদই হলো ইসলামের বিশ্বচিন্তার হৃদয় ও ভিত্তি । ফারুকীর ভাষায়,
“All the diversity, wealth and history, culture and learning, wisdom and civilization of Islam is compressed in this shortest of sentences La ilaha illAllah (There is no God but Allah).”
ইসলামকে এভাবে উপস্থাপনের ক্ষেত্রে ফারুকীর বড় সাফল্য হলো তিনি একই সাথে তার স্বধর্মী ও পশ্চিমা শ্রোতাদের মুখোমুখি হতে পেরেছেন। পাশ্চাত্য সভ্যতার জ্ঞানতাত্ত্বিক কাঠামোর উপর তার শক্ত অধিকার থাকায় এবং পশ্চিমা আধুনিকতা মুসলিম সমাজে যে দ্বন্দ্ব ও প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে সে সম্পর্কে তার সজাগ দৃষ্টি থাকায় তিনি ইসলামকে নতুন যুগের আলোকে ব্যাখ্যা দিতে পেরেছেন, বিশেষ করে পশ্চিমা চিন্তাভাবনায় প্রভাবিত মুসলমানদের কাছে ইসলামকে সেভাবে তুলে ধরতে পেরেছেন। ফারুকীর মত হলো মুসলিম সমাজের ক্ষতকে পশ্চিমা আধুনিকতা দিয়ে সারানো যাবে না, মুসলমানদের ভিতর থেকেই এ ক্ষতের উপশম বের করতে হবে। ইসলামকে তাই তিনি মানুষের জন্য এক স্বাভাবিক প্রাকৃতিক ধর্ম হিসেবে তুলে ধরেন এবং এটিকে তিনি সত্যিকারের প্রেমশীলতা, মানবিকতা, নৈতিকতা ও সমাজব্যবস্থার উদাহরণ হিসেবে হাজির করেন। তৌহিদকে তাই তিনি মনে করেন, এটি সৃষ্টি করে ঐক্যবোধ, ব্যক্তিত্ব এবং সত্যের উপলব্ধি যা মানুষকে আল্লাহর প্রতি অবনত করে এবং পরিণতিতে ধর্ম ও বিজ্ঞানের দ্বন্দ্ব নিরসন করে, ইসলামের নৈতিক ভিত্তিকে সমুন্নত করে এবং জ্ঞানের সকল শাখায় ইসলামীকরণের পথ নিশ্চিত করে। তিনি স্পষ্ট করে বলেন, ইসলাম মানুষকে খন্ড খন্ড করে না, এক অখন্ড, অবিভাজ্য সত্তা হিসেবে বিবেচনা করে। তার ভাষায়,
“The Islamic mind knows no pair of contraries such as ‘religious secular’, ‘sacred-profane’, ‘church state’, and in Arabic, the religious language of Islam, has no words for them in its vocabulary.”
জ্ঞানের ইসলামীকরণের ধারণা ফারুকীর জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। তার বাস্তব পরিকল্পনাগুলোর মধ্যে ছিলো নতুন প্রজন্মের মুসলমানদেরকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আধুনিক পদ্ধতিতে কিন্তু ইসলামী আদর্শের ছায়ায় সুশিক্ষিত করে তোলা। তিনি মনে করতেন, মুসলিম দুনিয়ার রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং ধর্মীয়-সাংস্কৃতিক বন্ধাত্বের কারণ হলো এখানকার দ্বিমুখী শিক্ষাব্যবস্থার পরিণতিস্বরূপ সৃষ্ট জীবনদৃষ্টির অভাব। তিনি সমস্যার গভীরতা বিশ্লেষণ করে বলেছেন,
“দ্বিমুখী শিক্ষাব্যবস্থার কারণে সমাজে দুটি প্রতিদ্বন্দ্বী শ্রেণির সৃষ্টি হয়, ফলে মুসলিম উম্মাহর সাম্যাবস্থা বিঘ্নিত হয়। এর একদিকে আছে সেক্যুলার এলিটরা, অন্যদিকে ঐতিহ্যবাহী ধর্মীয় নেতৃত্ব।”
তিনি এ দুর্যোগের প্রতিকার হিসেবে দুটি উপায় দেখিয়েছেন। প্রথমত, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ইসলামী সংস্কৃতি ও নীতিগুলোকে বাধ্যতামূলক করা এবং দ্বিতীয়ত, আধুনিক জ্ঞানের ইসলামীকরণ করা।
ফারুকীর এ প্রস্তাবনার মধ্যে তার প্রিয় বিষয় ইসলামী আধুনিকতাবাদী ও পুনরুজ্জীবনবাদী উভয়বিধ ভাবনার সমন্বয় আমরা দেখতে পাই। তিনি মুসলিম উম্মাহর দুর্বলতা ও ব্যর্থতার কারণ চিহ্নিত করে বলেছেন,
“ইসলামের সৃষ্টিশীলতার উৎস ইজতিহাদ পরিত্যাগ, ওহী (Revelation) ও আকলের (Reason) মধ্যে বিরোধিতা, চিন্তা ও কর্মের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা এবং সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় দ্বৈততা।”
এ কারণেই তিনি চিন্তা ও কর্ম, আদর্শ ও বাস্তবায়নের মধ্যে ঐক্যের কথা ভেবেছেন। এ লক্ষ্যে তিনি মুসলিম দুনিয়ার বিভিন্ন দেশ সফর করেছেন, বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে বক্তৃতা দিয়েছেন এবং সর্বোপরি নিজের টেম্পল বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে মুসলিম ছাত্রদেরকে নিয়ে তিনি তার ‘জ্ঞানের ইসলামীকরণ’ এর নিরীক্ষা চালিয়েছেন। ইসলামের ইতিহাসের একজন নিবিড় পাঠক হিসেবে ফারুকী এটি বুঝেছিলেন, আধুনিকতা ও ঔপনিবেশিকতা নামের পশ্চিমা দানব মুসলিম সমাজকে ভেঙ্গেচুরে পুরদস্তুর ওলটপালট করে দিয়েছে। ঔপনিবেশিক শাসকরা মুসলিম রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে গুঁড়িয়ে দিয়েছে, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে মুসলিম দুনিয়াকে পাশ্চাত্যের উপর পুরোপুরি নির্ভরশীল বানিয়ে ছেড়েছে এবং সর্বোপরি শিক্ষা ও সংস্কৃতির পাশ্চাত্যকরণ করে মুসলমানদের ঐতিহাসিক চেতনাবোধকে দুর্বল করে দিয়ে একটি হীনম্মন্য জাতিতে পরিণত করেছে। এটি বোঝা দরকার, পাশ্চাত্যের সেক্যুলার শিক্ষাব্যবস্থা তাদের নিজস্ব জীবন ও জগত সম্পর্কিত ধ্যান-ধারণার প্রতিফলন মাত্র এবং এ শিক্ষা আমাদের জীবন ও দর্শনের সাথে আদৌ সংগতিপূর্ণ নয়। প্রত্যেক শিক্ষার পিছনেই একটি দর্শন থাকে এবং সেই দর্শনই জাতির লক্ষ্যকে সমুন্নত করে। ঔপনিবেশিক শাসকরা যখন সেক্যুলার শিক্ষা আমাদের উপর চাপিয়ে দেয়, তখন তারা ভালো করেই জানতো, এর মাধ্যমে মুসলমানদেরকে বিজাতীয় গবেষণা ও নেতৃত্বের উপর নির্ভরশীল করে রাখা যাবে এবং এ কাজে তারা শতভাগ সফল হয়েছে। তাই ঔপনিবেশিক শাসকরা বিদায় নিলেও তাদের শিক্ষাব্যবস্থা আজও মুসলিম মনকে উপনিবেশিত করে রেখেছে। বিগত কয়েকশ বছর ধরে সেকুলার জাতীয়তাবাদ পাশ্চাত্যের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে অনুপ্রেরণা দিয়ে আসছে। পশ্চিমারা যে অর্থে জাতীয়তাবাদী কিংবা সেক্যুলার জীবন দর্শনে বিশ্বাসী, সে অর্থে মুসলমানদের বিশ্বাসী হওয়া সম্ভব নয় । আত্মদর্শন ছাড়া কোনো কিছু সৃষ্টি করা যায় না। ইসলামই হলো মুসলিম সমাজের জীবন দর্শন। ইসলাম বর্ণিত সেক্যুলার শিক্ষাব্যবস্থার অধীন মুসলমানরা তাই গত দুশ বছরে তেমন কিছুই সৃষ্টি করতে পারেনি। তারা পশ্চিমা দৃষ্টিভঙ্গির শুধু শুধু অনুলিপি করেছে মাত্র। এজন্যই মুসলিম চিন্তার জগতে আজকাল যারা নেতৃত্ব দিচ্ছেন বলে দাবি করছেন, তারা আসলে মূলত সুশিক্ষাবিহীন। তাদের না আছে সংস্কৃতি চেতনা, না আছে লক্ষ্য সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা। কারণ তারা মুসলিম সমাজে জন্মগ্রহণ করে মুসলিম চৈতন্যকে ধারন করেননি। পশ্চিমা চিন্তাকে মুসলিম সমাজে প্রতিস্থাপিত করে আধুনিকতার নকলনবিস সৃষ্টি করেছেন মাত্র। যার ফলে মুসলিম সমাজের ঐক্য, সংহতি ও মূল্যবোধ ভেঙ্গে পড়েছে এবং এ পরিপ্রেক্ষিতে মুসলিম দেশগুলোর উপর পাশ্চাত্যের খবরদারীও বাড়ছে। ইকবাল, মোহাম্মদ আসাদ, সাইয়েদ কুতুবের মতো পণ্ডিতরা পশ্চিমের এ জ্ঞানতাত্ত্বিক কাঠামোর নিয়ন্ত্রণ থেকে মুসলিম সমাজকে বের করে আনতে চেয়েছিলেন। ফারুকী মুসলিম জগতের এ জ্ঞানতাত্ত্বিক de-colonization বা অ-উপনিবেশীকরণের সিলসিলাকে আরো এগিয়ে নিয়েছেন এবং বিশেষ করে শিক্ষাব্যবস্থাকে অ-উপনিবেশিকরণের লক্ষ্যে বাস্তব কর্মসূচী প্রণয়ন করেছেন। তিনি জ্ঞানের বিষয় বা শাখা হিসেবে মানবিক, সমাজবিজ্ঞান ও প্রাকৃতিক বিজ্ঞানকে ইসলামী দর্শনের আলোকে পুনর্গঠিত করার উপর জোর দিয়েছেন, বিশেষ করে তৌহিদের মূলনীতিকে শিক্ষাব্যবস্থার সাথে সামঞ্জস্যশীল করার কথা বলেছেন।
জীবনের শেষ দিনগুলোতে তিনি ইসলামী সংস্কারের লক্ষ্যে কৌশলগত পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নের উপায়গুলো বারবার ওলটপালট করে দেখেছেন এবং তার ব্যাখ্যায় ইসলামের অর্থের সাথে মুসলিম জীবনে তার তাৎপর্যপূর্ণ স্থানকে চিহ্নিত করবার চেষ্টা করেছেন। একই সাথে মুসলমানদের শিক্ষিত ও ঐক্যবদ্ধ করার প্রয়াসও চালিয়েছেন। তিনি অনুভব করেছেন, মুসলিম সমাজে তার অপাশ্চাত্যমুখী (Non-Western Model) উন্নয়নের মডেল বাস্তবায়নের জন্য নতুন প্রজন্মের মুসলমানদের যথাযথভাবে শিক্ষিত করে তোলা দরকার। তিনি তার মিশনকে এগিয়ে নেয়ার জন্য তাই বেশ কয়েকটি প্রকল্প হাতে নেন। ফারুকী শিকাগোতে American Islamic College প্রতিষ্ঠা করেন এবং দীর্ঘদিন এর সভাপতি হিসেবে কাজ করেন। ১৯৮১ সালে ভার্জিনিয়াতে তিনি International Institute of Islamic Thought প্রতিষ্ঠায় নেতৃত্ব দেন। তার স্বপ্ন ছিলো আমেরিকায় একটি ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা, কিন্তু তার এ মহৎ পরিকল্পনা জীবদ্দশায় বাস্তব রূপ পায়নি। ফারুকীর কথা হলো মুসলিম সমাজ, বিশেষ করে এর বুদ্ধিজীবীরা যেভাবে পশ্চিমীকৃত হয়ে উঠছে, তার মোকাবেলায় জ্ঞানের ইসলামীকরণের বিকল্প নেই। এক্ষেত্রে তার প্রতিষ্ঠিত International Institute of Islamic Thought জ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়কে ইসলামীকৃত করে এক স্বতন্ত্র দৃষ্টিভঙ্গি ও স্রোত সৃষ্টিতে ভূমিকা রাখবে। এভাবে মুসলিম সমাজ পশ্চিমীকৃত না হয়েও আধুনিক ও যুগোপযোগী চিন্তার উন্মেষ ঘটাতে পারবে এবং তারা ইসলামী নীতি ও মূল্যবোধকে আঁকড়ে থেকেও বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সুফলগুলো ভোগ করতে সক্ষম হবে।
ফারুকীর আর একটি আগ্রহের কথা না বললে এ আলোচনা অসম্পূর্ণ রয়ে যাবে। এটি হলো আন্তঃধর্মীয় আলোচনায় (Interfaith Dialogue) তার অপরিসীম আগ্রহ। ইসলাম সম্পর্কে তার বিশিষ্ট চিন্তাভাবনা পশ্চিমের সামনে তুলে ধরার পরেও তিনি মনে করতেন বিশ্বের স্থিতিশীলতা ও শান্তির স্বার্থে ইব্রাহীমের সন্তানদের (ইহুদী, খ্রিস্টান ও মুসলমান) ধর্মীয়, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক একটি সাধারণ প্লাটফর্মে বোঝাপড়া প্রয়োজন। ফারুকীর এ আগ্রহের ফসল হলো তার বিখ্যাত বই Trialogue of the Abrahamic Faiths Historical Atlas of the Religions of the World। এছাড়া ১৯৬৭ সালে তার প্রকাশিত বই Christian Ethics খ্রিস্টান ধর্মের উপর কালের এক বিদগ্ধ মুসলমানের চিন্তাভাবনার বহিঃপ্রকাশ। একজন ইসলামী বুদ্ধিজীবী, দাওয়াতী কর্মী হিসেবে তিনি আমৃত্যু ইসলামের সাথে অন্যান্য ধর্ম, বিশেষ করে খ্রিস্টান ও ইহুদী ধর্মের আলোচনার উপর গুরুত্ব দিয়েছেন এবং পারস্পরিক সহিষ্ণুতা ও একটি সাধারণ নৈতিক মূল্যবোধকে পারস্পরিক যোগাযোগ-সহযোগিতার ভিত্তি করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে গেছেন।
এ সাধারণ নৈতিক ভিত্তিকে তিনি বলেছেন হানিফ, যা তার ভাষায়, incorporates every noble thought in the old Testament। ‘হানিফ’ কথাটি ফারুকীর লেখাজোখায়, বিশেষ করে ধর্মগুলোর পারস্পরিক আলোচনায় বারবার ফিরে এসেছে। হানিফ বলতে তিনি ইব্রাহীমের ঐতিহ্যকেও বুঝিয়েছেন, যা সব রকম শিরক ও পৌত্তলিক রীতির বিরোধী এবং নৈতিকভাবে স্বতন্ত্র এক গোষ্ঠী। ১৯৭০ এর দশক থেকেই অন্য ধর্মের সাথে আলোচনায় তিনি একজন প্রধান ব্যক্তিত্বে পরিণত হন এবং তার লেখা, বক্তৃতা, আন্তঃধর্মীয় সংলাপগুলোতে অংশগ্রহণ ব্যাপকভাবে সমাদৃত হয়। বিশেষ করে তার লেখা ও উপস্থাপনা এ ধরনের আন্তঃধর্মীয় সংলাপে মুসলিম অংশগ্রহণের নীতি তৈরিতে সহায়ক হয়।
ফারুকী তার বিখ্যাত বই Christian Ethics লিখেছিলেন ম্যাকগিল বিশ্ববিদ্যালয়ে কাজ করার সময়। এ সময় খ্রিস্টীয় চিন্তা ও ধর্মতত্ত্ব নিয়ে তিনি বিপুল অধ্যয়ন করেছিলেন এবং এ সূত্রেই তিনি তার বিখ্যাত সহকর্মী উইলফ্রেড কান্টওয়েল স্মিথ, চার্লস এ্যাডামস, স্ট্যানলি ব্রাইস ফ্রন্ট প্রমুখের সাথে এ বিষয়ে আলোচনা ও বিতর্কে প্রবৃত্ত হওয়ার সুযোগ পান।
Christian Ethics-এ ফারুকীর বুদ্ধিজীবিতা, চিন্তার বৈদগ্ধা ও ভাষাতাত্ত্বিক জ্ঞানের বিস্তৃতি যেন ঝলমলিয়ে উঠেছে। এ বইয়েই তিনি আন্তঃধর্মীয় আলোচনার একটি নীতি উপস্থাপনা করেছেন, যেটিকে তিনি বলেছেন meta religious approach এবং এ নীতি কোনো একটি বিশেষ ধর্মীয় ঐতিহ্যকে অনুসরণ করবে না। তিনি এ ধরনের আলোচনায় হীনম্মন্যতামূলক (apologetic) ও বিতর্কিত (polemic) বিষয়কে পরিহার করার কথা বলেছেন এবং সুনির্দিষ্ট, বিষয়ভিত্তিক, পাণ্ডিত্যমূলক আলোচনার উপর জোর দিয়েছেন। তিনি উল্লেখ করেছেন, অতীতের এ সমস্ত আলোচনা নানা রকম দ্বন্দ্ব ও প্রতিক্রিয়ার স্মৃতিজাত এবং মিশনারী ও প্রাচ্যতত্ত্ববিদদের বিকৃতির ফলে সে সমস্ত আলোচনার ফলাফল শুভ হয়নি। তাই তিনি এমন একটি পদ্ধতির প্রস্তাব করেছেন, যা প্রচলিত সংকীর্ণ ধর্মতত্ত্বকে অতিক্রম করে এক ধর্মতত্ত্বমূলক উচ্চতর ধর্মের (theology free meta religion) পাটাতনে বসে সব ধর্মের ভিতরকার বুঝাবুঝির ক্ষেত্রগুলোকে চিহ্নিত করবে। ফারুকীর এ প্রস্তাবনা এমন এক পদ্ধতির কথা বলেছে, যা পারস্পরিক আলোচনার ভিতকে এগিয়ে নিতে পারে। তার ভাষায়,
“…higher principles which are to serve as the basis for the comparison of various systems of meanings, of cultural patterns, of moralities, and of religions; the principles by reference to which the meanings of such systems and patterns may be understood, conceptualized, and systematized.”
গত ২০০ বছর ধরে আধুনিকতা ও ঔপনিবেশিকতা মুসলিম সমাজকে যেভাবে ভেঙ্গেচুরে বিপর্যস্ত করে দিয়েছে, তা এক কথায় নজিরবিহীন। এ সময়ের মধ্যে মুসলিম সমাজে যত দ্রুততার সাথে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক পরিবর্তনগুলো এসেছে, তার তুলনাও একেবারে নেই বললে চলে। মুসলিম দুনিয়ায় জাতীয়তাবাদী আন্দোলন, জাতি রাষ্ট্রের উদ্ভব, আধুনিকায়ন ও পাশ্চাত্যায়ন, আরব-ইসরাইল যুদ্ধ, সমাজতন্ত্রী চিন্তাভাবনার প্রসার, নানা রকমের গৃহদাহ ও আঞ্চলিক যুদ্ধ এ সময়েরই ঘটনা এবং এসব ঘটনা যুগপৎভাবে ইসলামের যে বৈশ্বিক পরিচয় তা অনেকটা বিবর্ণ করে দিয়েছে। আশার কথা হলো ইতিহাসের এ নজিরবিহীন ধাক্কাতেও মুসলিম সমাজ বারবার ঘুরে দাঁড়ানোর চেষ্টা করেছে, বিশেষ করে তার ভিতরের শক্তিকে একত্রিত করে যাবতীয় বৈরী পরিস্থিতি মোকাবেলা করার চেষ্টা করেছে। সাম্প্রতিককালে মুসলিম দুনিয়ায় এমন কয়েকজন বুদ্ধিজীবীর উপস্থিতি দৃশ্যমান, যারা একই সাথে ইসলামী ও পাশ্চাত্যের জ্ঞানে প্রবুদ্ধ এবং এরা আজকের যুগের সমস্যাকে সামনে রেখে ইসলামকে উপস্থাপন করার চেষ্টা করেছেন। ইসমাইল রাজী আল ফারুকী এ ধারার উজ্জ্বলতম প্রতিনিধি, যিনি শুধু আত্মিকভাবে ইসলামের ধারণা ও মূল্যবোধকে তুলে ধরেননি; নিজের কাজকর্ম, গবেষণা, শিক্ষকতা, আন্তঃধর্মীয় সংলাপ প্রভৃতির মাধ্যমে তিনি তার যুক্তিকে উপস্থাপন করেছেন। তিনি লিখেছেন, বলেছেন এবং এমন স্পষ্টতা ও বিশ্বাসের সাথে কাজ করেছেন, যা তার একমাত্র লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হয়ে ওঠে। ফারুকী মনে করতেন, ইসলাম হলো বিশ্বাস ও কর্মের ধর্ম। বিশ্বাস ছাড়া যেমন কর্মের মূল্য নেই, তেমনি চর্চা ছাড়া বিশ্বাসও অকেজো হয়ে যায়। ফারুকী তার জীবনব্যাপী সাধনায় দেখিয়ে দিয়ে গেছেন একজন মুসলমানের জীবনে কিভাবে বিশ্বাস আর কর্ম জীবন্ত হয়ে উঠতে পারে। এ কালের ঝিমিয়ে পড়া মুসলমানদের জন্য এটি বড় একটি দৃষ্টান্ত বটে।