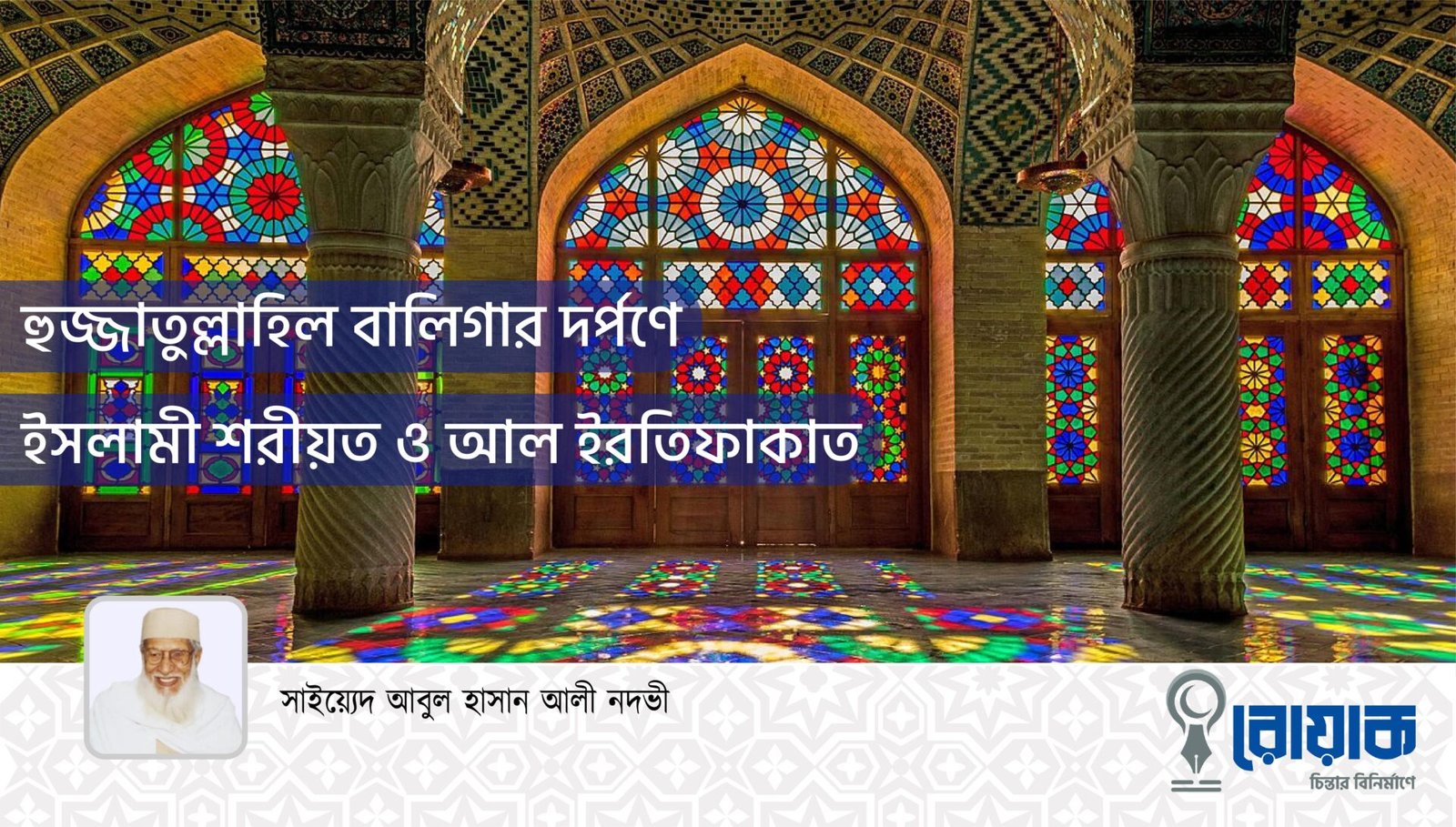হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগার বৈশিষ্ট্য
শাহ সাহেবের সবচেয়ে আলোড়ন সৃষ্টিকারী গ্রন্থ ও জ্ঞানগত কৃতিত্ব ‘হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা’। যার মধ্যে ইসলামী শরীয়তের এমন এক মজবুত, সামগ্রিক ও প্রামাণ্য চিত্র পেশ করা হয়েছে, যেখানে আকীদা-বিশ্বাস, ইবাদত-বন্দেগী, লেনদেন, আচার-অনুষ্ঠান, আখলাক-চরিত্র, সামাজিকতা, সভ্যতা-সংস্কৃতি, রাজনীতি ও ইহসান (অনুগ্রহ-দান) কে এমন এক যোগসূত্র ও সঠিক সামঞ্জস্যের সঙ্গে পেশ করা হয়েছে, মনে হয় যেন তা একই মালার মুক্তা ও একই শিকলের অসংখ্য কড়া। তাতে আসল ও শাখা-প্রশাখা, লক্ষ্য- উদ্দেশ্য ও উপায়-উপকরণ এবং সার্বক্ষণিক ও সাময়িকের পার্থক্য দৃষ্টির আড়াল হতে পারে না। এ তো সেসব রচনাবলি ও গবেষণাকর্মের পুরোনো দুর্বলতা, যা কোনও বাড়াবাড়ি ও অন্যায়, বে-ইনসাফী প্রত্যাখ্যান কিংবা কোনও আবেগ-আগ্রহ নিয়ে রচিত হয়েছে। এই যোগসূত্রতা ও সামঞ্জস্যের কারণ (শাহ সাহেবের জন্মগত মানসিক ও চিন্তাগত সুস্থতা ও মিতাচার ব্যতিত) তার হাদীস শাস্ত্রের গভীর ও ব্যাপক অধ্যয়ন এবং সেই বিশেষ মানসিকতা ও আকর্ষণ, যা হাদীস ও সীরাতের নিমগ্নতা কিংবা নববী মেজায ও আদর্শের সঙ্গে সামঞ্জস্যশীল কোনও ‘আলেমে রব্বানী’ (বুযুর্গ আলেম)- এর সংস্পর্শ ও তরবিয়ত-তত্ত্বাবধানে সৃষ্টি হয়। ইসলামের এই মজবুত ও পূর্ণাঙ্গ ব্যাখ্যা, যা হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগার পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় পরিলক্ষিত হয়, তা খুব কম ধর্মীয় বই-পুস্তক ও রচনাবলিতেই দৃষ্টিগোচর হবে। এভাবে হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা সেই যুক্তিবিদ্যা ও দর্শন শাস্ত্রের যুগে এক নতুন ইলমে কালাম হয়ে গেছে, যার মধ্যে রয়েছে হকপন্থী ও সুস্থ মনের মানুষের জন্য (যার শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অন্তদৃষ্টিও কিছুটা আছে) প্রশান্তি ও স্বস্তির পর্যাপ্ত খোরাক। আমার জানামতে কোনও মাযহাবের সমর্থনে এবং তার প্রজ্ঞাপূর্ণ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে (আমাদের পরিজ্ঞাত ভাষায়) এই মানের গ্রন্থ রচনা করা হয়নি। আর রচিত হয়ে থাকলেও বর্তমান সময়ে তা শিক্ষাজগতের সামনে নেই। বারো হিজরী শতকের সামান্য পরেই ভারতবর্ষ এবং গোটা মুসলিম বিশ্বে বিভিন্ন শিক্ষা-সাংস্কৃতিক ও জ্ঞান-গবেষণামূলক নানা কারণে এক বিশেষ ধরনের ‘দর্শন ও যুক্তিবিদ্যা’ -এর যে যুগ শুরু হতে যাচ্ছিল এবং শরীয়তের আহকামের তত্ত্বাবলি ও উপকারিতা অনুসন্ধানের যে গণজোয়ার সৃষ্টি হচ্ছিল, সে কারণে অনেক মেধা-মনন বিভ্রান্ত হওয়া এবং বহু কলম বিপথে চালিত হওয়ার জন্য প্রস্তুত ছিল। বিশেষতঃ হাদীস ও সুন্নাহ (বিশেষ কারণে) নানা আপত্তি-অভিযোগ ও সংশয়-সন্দেহের সবচেয়ে বেশি লক্ষ্যস্থলে পরিণত হচ্ছিল। এসব নতুন চাহিদার কারণে সঠিকভাবে সে ব্যক্তিই কর্তব্য পালন করতে পারত, যিনি কুরআন-সুন্নাহ, দর্শন ও হিকমত শাস্ত্র, কালাম শাস্ত্র, চারিত্রিক জ্ঞান, জীববিদ্যা, (সমকালীন গণ্ডিতে) ব্যবস্থাপনা, অর্থনীতি ও রাষ্ট্রনীতি সম্পর্কে জ্ঞাত। সেই সাথে ইহসান ও আত্মশুদ্ধির রত্ন ও বাস্তবতা সম্পর্কে শুধু জ্ঞাতই নয় বরং এক্ষেত্রে ইজতিহাদের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হবেন। চাহিদা ছিল, সে যুগ শুরু হওয়ার পূর্বে হিজরী বারো শতকের ইমামের কলমে এমন গ্রন্থ রচিত হয়ে যাবে, যা এই প্রয়োজনীয়তা এমন পর্যাপ্তভাবে পূর্ণ করবে, যা এরূপ কোনও মানুষের কলম দ্বারাই সম্ভব, যিনি একজন মানুষ মাত্র। না তিনি নিষ্পাপ; না তার জ্ঞান প্রত্যেক যুগ, স্থান ও শাস্ত্রসমূহের উপর পরিব্যাপ্ত। তার উপর সমকালের (ন্যূনতম পর্যায়ে) স্পর্শ এবং সেই শিক্ষাব্যবস্থা ও তরবিয়তের প্রভাবও আছে, যেখানে তিনি বেড়ে উঠেছেন। অধিকন্তু তাকে মূলতঃ কুরআনিক শিক্ষাকেন্দ্র, হাদীস ও সুন্নাহর বিদ্যাপীঠের বরকত ও সংশ্রবপ্রাপ্ত এবং মুখপাত্র বলেই পরিলক্ষিত হয়।
শাহ সাহেব উক্ত গ্রন্থ রচনার উৎসাহ-প্রেরণার কারণ সম্পর্কে লিখেন, ‘উলূমে হাদীসের মধ্যে সবচেয়ে জটিল, সূক্ষ্ম ও গভীর, উঁচু ও নতুন শাস্ত্র হল, দীনের তত্ত্ব–রহস্যের সেই জ্ঞান, যাতে আহকাম ও বিধি–নিষেধের হিকমত, তার শ্রেষ্ঠত্ব ও বিশেষ বিশেষ আমলগুলোর সূক্ষ্মতা ও তত্ত্ব বর্ণনা করা হবে। যার মাধ্যমে মানুষ শরীয়তের আনীত বিষয়গুলোর ব্যাপারে অন্ত দৃষ্টি সম্পন্ন হয়ে যায় এবং ভুল–ভ্রান্তি থেকে নিরাপদ থাকে’।
বিষয়বস্তুর কমনীয়তা
ধর্মীয় গভীরতা ও শরয়ী আহকামের রহস্য, উপকারিতাসমূহ, কারণ ও ইল্লতগুলো বর্ণনা করার বিষয়টি অত্যন্ত সূক্ষ্ম। সামান্য অসতর্কতা-পক্ষপাতিত্ব, বিশেষ কোনও দৃষ্টিভঙ্গির প্রাধান্য কিংবা যুগের প্রভাবে পাঠকবর্গের মেধা-মনন আসমানী শরীয়ত ও নববী শিক্ষার সেই ফলক- যেখানে মূল লক্ষ্য বলা হয়েছে আল্লাহর সন্তুষ্টি, নৈকট্য ও পারলৌকিক মুক্তি, সেখান থেকে নেমে এসে বস্তুবাদী জীবনোপকরণগুলোর সুব্যবস্থা ও সাংস্কৃতিক কল্যাণ কিংবা রাজনৈতিক স্বার্থ হাসিলের ফাঁদে পড়ে যায়। আর চেষ্টা-সংগ্রামের পূর্ণ ক্রমধারা থেকে ঈমান ও হিসাব প্রস্তুতির প্রাণ হয়ত সম্পূর্ণরূপে বেরিয়ে যায় অথবা অত্যন্ত দুর্বল ও আহত হয়ে যায়। উদাহরণস্বরূপ নামাযের রহস্য ও উপকারিতা প্রসঙ্গে বলা যায়, তা এক ধরনের সামরিক প্যারেড। এর দ্বারা শৃঙ্খলা, আমীরের আনুগত্য ও ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠায় সাহায্য পাওয়া যায়। রোযা সুস্থতার জন্য ফলপ্রসূ পদ্ধতি। যাকাত ধনাঢ্যদের উপর গরীব-অসহায়দের প্রাপ্য ট্যাক্স। হজ্জ একটি আন্তর্জাতিক ইসলামী কনফারেন্স। যেখানে জাতীয় স্বার্থে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে চিন্তা-ভাবনা ও পরামর্শ করা হয়।
সেসব সমস্যা-সংকটে অবস্থার প্রেক্ষিতে (যেগুলো সম্ভাবনা ও আশঙ্কা থেকে অগ্রসর হয়ে ঘটনাবলি ও বাস্তব দৃষ্টান্তের স্থান দখল করে নিয়েছে) এ বিষয়ে সঠিকভাবে সে আলেমই দায়িত্ব পালন করতে পারেন, যার হাতে থাকবে দীন ও শরীয়তের আসল সংবিধান, যিনি আল্লাহর শরীয়ত অবতরণ এবং নবী-রাসূল (স) প্রেরণের উদ্দেশ্য সম্পর্কে হবেন সম্যক অবগত। যার শিরা-উপশিরায় বিস্তৃত থাকবে ঈমান ও হিসাব প্রস্তুতির প্রাণ। যার চিন্তাধারা ও জ্ঞানগত উন্নতি হবে কুরআন-সুন্নাহ, ঈমান ও হিসাব প্রস্তুতির পরিবেশে এবং তার ছায়াতলে। আর শাহ সাহেব (র) ছিলেন (যেমনটি তার জীবনকর্ম থেকে জানা যায়) এই স্পর্শকাতর জটিল বিষয়ে কলম ধরার জন্য উচ্চ মাপের ব্যক্তিত্ব।
পৃথক সংকলনের প্রয়োজনীয়তা এবং প্রবীণ আলেমদের প্রাথমিক চেষ্টা
শাহ সাহেব (র) এ বিষয়ে প্রবীণদের সংক্ষিপ্ত চেষ্টা-সাধনার বর্ণনা দিয়ে লিখেন- ‘পূর্বসূরীগণ সেসব উপকারিতার পর্দা উন্মোচন করেছেন, শরয়ী অধ্যায়গুলোতে যার প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়েছে। পরবর্তী গবেষকগণ কতিপয় অতি মূল্যবান তত্ত্বও বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তার পরিমাণ এতটুকু যে, আজ এ বিষয়ের সমালোচনা ঐক্য বিনষ্টকারী হয়নি। কেউ এ বিষয়ে স্বতন্ত্র গ্রন্থ রচনা করেনি। এর মূলনীতি ও শাখামূলক বিষয়গুলো কেউ পুরোপুরি বিন্যাস করেননি।’ এ প্রসঙ্গে শাহ সাহেব (র) ইমাম গাযালী (র), আল্লামা খাত্তাবী ও শায়খুল ইসলাম ইযযুদ্দীন ইবনে আবদুস সালাম (র)-এর উদ্ধৃতি দিয়েছেন। যাদের গ্রন্থাবলি ও রচনাবলিতে অল্প অল্প এমন সব বিষয়বস্তু ও ইংগিত পাওয়া যায়, শাহ সাহেব (র) “শরয়ী আহকাম উপকারিতা নির্ভর নয় এবং আসল ও প্রতিদানের মধ্যে সামঞ্জস্য থাকা তেমন একটা জরুরী নয়।” এই দাবী প্রত্যাখ্যান প্রসঙ্গে সেসব আয়াতে কারীমা ও হাদীসসমূহ দ্বারা প্রমাণ পেশ করেছেন, যেগুলোর মধ্যে বিভিন্ন আমল এবং তার পরিণতির মাঝে সম্পৃক্ততার বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। কোনও কোনও বিধি-বিধানের ইল্লত এবং উপকারিতাও বর্ণনা করা হয়েছে। আবার সেসব হাদীসও উল্লেখ করেছেন, যেগুলো কোনও ইবাদত-বন্দেগী অথবা কোনও আমল শরীয়ত-নির্দেশিত হওয়ার কারণ এবং নিরূপণের রহস্য বর্ণনা করা হয়েছে। আবার কোনও কোনও নিষেধাজ্ঞার সেসব কারণ ও রহস্যের বিভিন্ন উদাহরণও দিয়েছেন, যা হযরত উমর (রা) এবং অন্যান্য সাহাবায়ে কিরাম থেকে বর্ণিত আছে।
আর প্রত্যাখ্যান করেছেন সেসব চিন্তাধারা ও দৃষ্টিভঙ্গি এবং সেসবের জবাবও দিয়েছেন, যারা এই জটিল বিষয়ের সংকলনকে অসম্ভব কিংবা নিরর্থক বা অভিনব কাজ বলতেন। তাছাড়া এ বিষয়ে সে সময় পূর্ণ মনোযোগিতা না থাকার কী কারণ ছিল, তারও ব্যাখ্যা দিয়েছেন।
এ শাস্ত্র সংকলনের প্রয়োজনীয়তা ও রহস্য বর্ণনা করতঃ শাহ সাহেব লিখেন, “এমন কিছু হাদীস বাহ্যতঃ যেগুলোকে পুরোপুরি কিয়াসবিরোধী মনে হত, কোনও কোনও ফকীহ সেগুলোকে অযৌক্তিক বলে প্রত্যাখ্যান করাকে বৈধ জ্ঞান করতেন। এ কারণেও হাদীসসমূহের যৌক্তিকতা প্রমাণ করা জরুরী হয়ে দাঁড়ায়।“ উম্মতের বিভিন্ন শ্রেণীর বিরোধপূর্ণ কর্মপদ্ধতি, কারও কারও যুক্তি ও বিবেক থেকে একেবারে চোখ বন্ধ করে নেওয়া, কারও কারও অলীক ব্যাখ্যা দান এবং এহেন অবস্থায় ‘صرف عن الظاهر’ (বাহ্যিকতা বিমুখ হওয়া)-এর উপর নির্দ্বিধায় আমল করা, যেখানে হাদীসসমূহ যৌক্তিক নীতিমালার পরিপন্থী দেখা যায় এবং এ ব্যাপারে অসংখ্য দলের সীমালঙ্ঘন শাহ সাহেবের নিকট এ শাস্ত্রের নতুন সংকলনকে না কেবল বৈধ ও উপকারী সাব্যস্ত করে বরং একে দীনের বিরাট বড় খেদমত এবং সময়ের অতি গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজন বলেই প্রমাণ করে।
প্রয়োজনীয়তার এই অনুভূতি, বাস্তব অভিজ্ঞতা ও সময়ের চাহিদাগুলো ছাড়া শাহ সাহেব এই মহান কাজের পূর্ণতা দানের জন্য কিছু গাইবী (অদৃশ্য) সুসংবাদ এবং নবুওয়াতের দরবার থেকে এমন একটি ইংগিতও পেয়েছেন- যাতে অনুমিত হয়, দীনের নতুন একটি বৈশিষ্ট্যের ব্যাখ্যা উদ্দেশ্য। শাহ সাহেব (র) বলেন, ‘আমি অন্তরে এমন একটি আলোকবর্তিকা পেলাম, যা বরাবরই বৃদ্ধি পেতে থাকে। মক্কা শরীফে অবস্থানকালে আমি একবার ইমাম হাসান ও ইমাম হুসাইন (রা) কে স্বপ্নে দেখলাম। তারা আমাকে কলম দান করলেন আর বললেন, এটা আমাদের নানা রাসূলুল্লাহ (স)-এর কলম।’ শাহ সাহেবের শিষ্য ও সঙ্গীদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি স্নেহের ছাত্র তার মামাতো ভাই, শ্যালক, ঘর-বাইরের বন্ধু শায়খ মুহাম্মদ আশেক ফুলতী (র)- এর সবচেয়ে বেশি আকাঙ্ক্ষা ও পীড়াপীড়ি ছিল এ কাজের পূর্ণতা দানের পেছনে। যিনি শাহ সাহেবের মন-মানস সম্পর্কে সবচেয়ে অভিজ্ঞ, তার জ্ঞান-প্রজ্ঞা ও যোগ্যতা সম্পর্কে সর্বাধিক ওয়াকিফহাল ছিলেন। মোটকথা, আল্লাহ তা’আলা শাহ সাহেবকে এই গুরুত্বপূর্ণ কাজ সুসম্পন্ন করার তাওফীক দান করেন আর তার কলম দ্বারা এই অমূল্য গ্রন্থ রচিত হয়ে জ্ঞানী মহলের হাতে পৌঁছে যায়।
ভূমিকা, মৌলিক বিষয়সমূহ, আদেশ দান, পুরস্কার ও শাস্তি
কিতাবের প্রথমভাগে শাহ সাহেব ভূমিকাস্বরূপ সেসব আলোচনা সন্নিবেশিত করেছেন, যার দ্বারা সৃষ্টিকর্তার হেদায়াত, আসমানী শিক্ষা, নবী- রাসূল প্রেরণ ও তাদের শিক্ষা-দীক্ষার প্রয়োজনীয়তা প্রতীয়মান হয়। তাতে অত্যন্ত মৌলিক ও ভিত্তিমূলক আলোচনাটি তিনি باب سر التكليف শিরোনামের অধীনে বর্ণনা করেছেন। যেখানে তিনি প্রমাণ করেছেন, ‘তাকলীফ বা আদেশ দান‘ মানবজাতির জন্মগত চাহিদাগুলোর একটি। মানুষ তার যোগ্যতার ভাষায় আবেদন করে- আল্লাহ তা’আলা যেন তার উপর এমন জিনিস ওয়াজিব করেন, যা ফিরিশতাসুলভ শক্তিতুল্য। এরপর তার বিনিময়ে যেন সওয়াব দেন। আর তার উপর (তার মধ্যে সুপ্ত) পশুবৃত্তি বা পাশবিকতায় নিমজ্জিত হওয়াকে হারাম করেন এবং তাকে শাস্তি দেন। এ ব্যাপারে শাহ সাহেবের প্রাণী জগৎ, উদ্ভিদ এবং মানব জাতির উপর ব্যাপক ও গভীর জ্ঞান-গবেষণার বহিঃপ্রকাশ ঘটে। সাথে সাথে মনস্তত্ত্ব, চিকিৎসা ও বনাজী সম্পর্কে অবগতিও প্রকাশ পায়। শাহ সাহেব যৌক্তিকভাবে প্রমাণ করেছেন, মানুষের প্রাণীজগৎ ও উদ্ভিৎজগতের সাথে যে বিশেষ পার্থক্য রয়েছে এবং তার ভেতর যেসব যোগ্যতা ও জন্মগত প্রত্যাশা-চাহিদা সুপ্ত রাখা হয়েছে, তা বস্তুতঃ শরয়ী তাকলীফ (আল্লাহর পক্ষ থেকে বান্দাকে সম্বোধন করে কোনও বিধি-নিষেধ পালনের আদেশ দান) এবং মহান স্রষ্টা আল্লাহ তা’আলার হেদায়াত প্রত্যাশা করে। শাহ সাহেব একে ‘التكفف الحالى” প্রকৃতির ভাষায় ভিক্ষে চাওয়া ও হাত পাতা) -এর মত উচ্চাঙ্গের শব্দে ব্যক্ত করেছেন। সেসঙ্গে ‘ التكففا لعلمى’ (জ্ঞানের ভিক্ষাবৃত্তি) শব্দ বৃদ্ধি করেন।
তাঁর মতে মানুষের মধ্যে (বিবেক-বুদ্ধি ও বাকশক্তি ছাড়াও) আরও দুটি বিষয় রয়েছে। براعة القوة العملية وزيادة القوة العقلية এতে মানুষের মধ্যে কেবল বিবেকবুদ্ধি ও কর্মশক্তির অস্তিত্বই নয় বরং সেসবের উন্নতি, সাহসিকতা, পূর্ণতা কামনা, অতৃপ্তিও তার জন্মগত স্বভাব। শাহ সাহেবের মতে ফিরিশতাগণের সৃষ্টি, বড় বড় ঘটনাবলি ও নবী-রাসূল প্রেরণ এরই ফলাফল। প্রকারান্তরে ঐ অনুগ্রহ ও ব্যবস্থাপনার বিস্ময়-কমনীয়তা, যা গোটা মানবজাতির মাঝে ব্যাপৃত। এসব খোদায়িত্ব ও আল্লাহর রহমতের ঝলক। তার মতে ইবাদত–বন্দেগী ও শরীয়ত পরিপালন মানব জাতির এমন এক জাতিগত চাহিদা, যেমন– হিংস্র প্রাণীর গোশত ভক্ষণ, চতুষ্পদ জন্তুর ঘাসে বিচরণ, মৌমাছির স্বীয় নেতা (রাণী) –এর প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন। তবে প্রাণীজগতের জ্ঞান প্রাকৃতিক প্রত্যাদেশের সাথে সম্পৃক্ত, আর মানবীয় জ্ঞান, কাজকর্ম ও জীবিকার্জন দেখা বা অহী কিংবা অনুসরণ–অনুকরণের সাথে সম্পৃক্ত।
এরপর শাহ সাহেব মাজাযাত (প্রতিদান ও শান্তি) কে শরয়ী তাকলীফের কুদরতী চাহিদা বলেন। তার নিকট এর কারণ চারটিঃ
১. শ্রেণীগত চাহিদা।
২. উর্ধ্বজগতের প্রভাব।
৩. শরীয়তের চাহিদা।
৪. নবী প্রেরণের ফল ও চাহিদা।
আল্লাহ তা’আলার কাছে তার গ্রহণযোগ্যতা ও সাহায্যের ফায়সালার আবশ্যকীয়তা। তারপর মানুষের মধ্যে নিজের স্বভাব-প্রকৃতিতে পার্থক্যের কারণে চরিত্র, কাজকর্ম ও যোগ্যতার স্তরেও পার্থক্য হয়ে থাকে। এ প্রসঙ্গে শাহ সাহেব মালাকিয়্যাত ও রাহীমিয়্যাত (ফিরিশতাসুলভ ও পশুসুলভ অবস্থা-গুণ)-এর সহাবস্থান, এগুলোর প্রবলতা ও দুর্বলতার সাদৃশ্য আর এগুলোর পারস্পরিক সম্পর্কের প্রকারভেদের (যেগুলোকে তিনি ‘আকর্ষণ’ ও ‘পরিভাষা’ শব্দে ব্যক্ত করেন) আটটি রূপ এবং সেগুলোর বৈশিষ্ট্যাবলি বর্ণনা করেছেন। তন্মধ্যে যেগুলো প্রাধান্যপ্রাপ্ত, সেগুলো উল্লেখ করেছেন। এই আলোচনা ও বিশ্লেষণ শাহ সাহেবের ধীশক্তি ও বুদ্ধিমত্তার নিদর্শন এবং কিতাবেরই একটি বৈশিষ্ট্য। এতে মানুষের অবস্থা ও স্বভাব-প্রকৃতি সম্পর্কে তার গভীর জ্ঞান-গবেষণা জানা যায়।
আমলের গুরুত্ব ও তার প্রভাব
শাহ সাহেব আমলের গুরুত্ব, মানবীয় বৈশিষ্ট্য-গুণের উপর তার প্রভাব এবং দুনিয়া-আখেরাতে তার প্রতিক্রিয়ার রূপরেখা বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, একটি সময় এমন আসে, যখন আমলসমূহে (উর্ধ্বজগতের পছন্দ- অপছন্দের কারণে) এমন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়, যা হয়ে থাকে সেসব তাবীয ও নকশায়, যেগুলো সবিশেষ গঠন-বৈশিষ্ট্যসহ প্রবীণদের থেকে বর্ণিত।
এভাবে বইটির এ প্রারম্ভিক আলোচনা অধ্যয়নকারীদের মেধা–মননকে সামনের সেসব আলোচনার জন্য প্রস্তুত করে দেয়, যার ভিত্তিই হল, মানুষের শ্রেণীগত চাহিদাসমূহ উপলব্ধি করা, শরয়ী তাকলীফের কারণগুলো ও তার উপর আরোপিত সাজা ও পুরস্কার, খোদায়িত্ব ও রহমতের দাবীসমূহ, আমলসমূহের রূপরেখা এবং সেগুলোর মানুষের সামাজিক পদ্ধতি, মানবজীবনের সঙ্গে সম্পৃক্ততা এবং সেসব অদৃশ্য আলামত ও জিনিসগুলোর অস্তিত্ব স্বীকার করে নেওয়ার উপর সীমাবদ্ধ।
ইরতিফাকাত বা আশ্রয় গ্রহণ
হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা পাঠ করলে মনে হয়, শাহ সাহেবের দূরদৃষ্টি ও পরিবর্তনশীল অবস্থা-পরিস্থিতিগুলোর গভীর ও বাস্তবদর্শী পর্যবেক্ষণ (আল্লাহর সমর্থনের সাহায্যে) বুঝে নিয়েছিল যে, শীঘ্রই এমন যুগ আসবে, যাতে একদিকে মানুষ শরীয়তের আহকামে বিশেষতঃ হাদীস ও সুন্নাহর শিক্ষা আর নবীজীর পবিত্র বাণীসমূহের রহস্যভেদগুলো বুঝার জন্য সচেষ্ট হবে। এসবের সভ্যতা-সাংস্কৃতিক, সম্মিলিত, সামাজিক ও বাস্তবিক উপকারিতাগুলো জানতে চাইবে। অপরদিকে সে দীন-ধর্ম ও জীবনের মধ্যকার সম্পর্ক উপলব্ধি করবে। ধর্মীয় শিক্ষাদীক্ষা ও আসমানী হেদায়াতকে জীবনের বিস্তৃত পরিমণ্ডল এবং মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক, উপকরণ ও ফলাফলের মধ্যকার সম্পর্কের নিরিখে বুঝা এবং এসবের উপকারিতা উপলব্ধির চেষ্টা করবে।
এজন্য শাহ সাহেব যে ‘হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা’ কে মূলতঃ শরীয়তের রহস্যভেদ এবং হাদীস ও সুন্নাহর যৌক্তিক ব্যাখ্যাস্বরূপ লেখা হয়েছে, সে গ্রন্থখানা ‘শরীয়া ব্যবস্থা’ থেকে শুরু করার কারণে- যার শুরুভাগে সেসব আদেশ-নিষেধ বর্ণিত হয়েছে, যার মৌলিক সম্পর্ক প্রতিদান ও শাস্তি, পরলৌকিক মুক্তি আর শাহ সাহেবের পরিভাষা محبث البر والاثم ( পাপ-পুণ্য অধ্যায়) এর সাথে, প্রথমে সেসব আলোচনা দ্বারা শুরু করেছেন, যার সম্পর্ক বিশ্ব চরাচরের সৃষ্টিগত ব্যবস্থা ও মানব জীবনের সাথে। যার অনুসরণে একটি সুস্থ সামাজিক রূপরেখা ও একটি সুস্থ সভ্যতা অস্তিত্ব লাভ করে। শাহ সাহেব এক্ষেত্রে ‘ইরতিফাকাত’ পরিভাষা ব্যবহার করেছেন। যা আমাদের জানামতে ইতোপূর্বে মুসলমান দার্শনিক-মুতাকাল্লিম, প্রজ্ঞাবান চিন্তাবিদ ও আলেম শ্রেণী (অন্তত এতটুকু সুস্পষ্ট ও ধারাবাহিকভাবে) ব্যবহার করেননি।
ইরতিফাকাতের গুরুত্ব
ইরতিফাকাত বলে শাহ সাহেবের উদ্দেশ্য, মানুষের পারস্পরিক বৈধ হিতাকাঙ্ক্ষা, সাহায্য–সহযোগিতা, সামাজিক সম্মিলিত কর্মকাণ্ড, ন্যায়ানুগ ও ভারসাম্যপূর্ণ নাগরিক জীবন প্রতিষ্ঠার জন্য ‘হিতকর ব্যবস্থাপনা‘। এভাবে শাহ সাহেব মানবীয় উৎকর্ষতার ব্যক্তিগত ও সামাজিক উভয় দিক এবং ইহ ও পারলৌকিক উভয় জীবন সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। শাহ সাহেবের মতে এই ‘নেযামে তাকবীনী’ তথা সৃজনশীল ব্যবস্থাপনা কেবল নবীগণের আনীত শরয়ী ব্যবস্থাপনার অনুকূল হওয়াই যথেষ্ট নয় বরং তার জন্য সাহায্য-সহযোগিতাকারী ও তার লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের খাদেম হয়ে থাকা উচিৎ। তিনি সভ্যতার আলেম ও অভিজ্ঞ অর্থনীতিবিদদের মাঝে প্রথমবার চারিত্রিক জ্ঞানের সাথে অর্থনীতি ও জীবিকা নির্বাহ জ্ঞানের গভীর সম্পর্ক স্থাপন করেছেন। শাহ সাহেবের মতে যখন এই সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায়, তখন অর্থনীতি ও চরিত্র–নৈতিকতা দুটিই চরম মুমূর্ষু অবস্থায় পতিত হয়। যার প্রভাব ধর্ম, চরিত্র, স্থিতিশীল শান্তিপূর্ণ জীবন, মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক এবং সভ্যতা–সংস্কৃতির উপর পতিত হয়। তার মতে মানুষের সামাজিক অবকাঠামো তখনই একেবারে ধ্বংস হয়ে যায়, যখন কোনও কঠোরতা আরোপের মাধ্যমে তাদেরকে অর্থনৈতিক সংকটে বাধ্য করা হয়। সে সময় এই মানুষ (যাদের ভেতর আল্লাহ তা‘আলা উচ্চস্তরের আত্মিক যোগ্যতা, আধ্যাত্মিক শক্তি ও উন্নতির অপার সম্ভাবনা সুপ্ত রেখেছেন, তারা) এক টুকরো রুটির জন্য গাধা ও বলদের মত বাধ্যগত হয়ে থাকে এবং সব ধরনের উন্নতি–সমৃদ্ধি ও সৌভাগ্য থেকে হয়ে যায় বঞ্চিত।
নাগরিক ও সামাজিক জীবনের গুরুত্ব ও তার রূপরেখা
শাহ সাহেব নাগরিক ও সামাজিক জীবনের পরিচয় (যার কেন্দ্রস্থলকে المدينة -রাজধানী শব্দে ব্যক্ত করে) এমন জ্ঞানগর্ভ ভাষায় পেশ করেন, যার চেয়ে উৎকৃষ্ট ও স্বয়ংসম্পূর্ণ সংজ্ঞা আজ পর্যন্ত (লেখক-দার্শনিকদের মাঝে) করা হয়নি। তিনি (باب سياسية المدنية )শহরের রাজনীতি অনুচ্ছেদ শিরোনামে লিখেছেন- ‘শহর বলে আমার উদ্দেশ্য মানুষের সে দল, যাতে কোনও শ্রেণীর ঘনিষ্ঠতা থাকবে এবং তাদের মধ্যে লেনদেন ও আচার- অনুষ্ঠানে থাকবে অংশীদারিত্ব। অবশ্য তারা বসবাস করবে বিভিন্ন স্থানে।
তিনি নগর ব্যবস্থা-এর সংজ্ঞায় বলেন, ‘নগর ব্যবস্থা‘ দ্বারা আমার উদ্ধেশ্য হল এমন কৌশল, যা এই নাগরিক জীবনের মানুষের মধ্যকার পারস্পরিক সম্পর্ক সংরক্ষণের পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করে।
অনন্তর তিনি এই সভ্যজীবন বা শহরের সংজ্ঞায় আরেকটু অগ্রসর হয়ে বলেন, ‘শহরকে তার অধিবাসী বা নাগরিকদের মাঝে বিদ্যমান পারস্পরিক সম্পর্কের কারণে একক ব্যক্তি মনে করা উচিৎ, যা বিভিন্ন অঞ্চল ও সামাজিক রূপরেখায় গঠিত হয়েছে।’ তার মতে “ইরতিফাক” (মৌলিক অধিকার) দুই প্রকার। ১. প্রাথমিক ও প্রয়োজনীয়। যা গ্রাম্যলোকদেরও আছে।
২. সামাজিক বা উন্নত, যা শহরবাসীর (শহুরে ও সভ্য লোকজনের) রয়েছে।
এছাড়া তৃতীয় আরেকটি প্রকারও আছে। সেটি হচ্ছে, রাজনীতি ও ব্যবস্থাপনা। অধিকন্তু এর ফলে চতুর্থ আরেক প্রকার বেরিয়েছে– গণপ্রতিনিধিত্ব। শাহ সাহেব চতুর্থ ইরতিফাকে দেশবাসী (বিভিন্ন রাষ্ট্র ও দূরাঞ্চলগুলো) –এর পারস্পরিক সম্পর্ক রক্ষার উপর জোর দেন। এই সম্পর্ক (বিভিন্ন অঞ্চলের মাঝে) এতই জরুরী, যেমন ছিল একই শহরের নাগরিকদের মাঝে প্রাথমিক ও নির্দিষ্ট অবস্থায়।‘
কর্মক্ষেত্র ও জীবিকা নির্বাহের প্রশংসিত ও ঘৃণিত রূপরেখা
ইরতিফাকাত প্রসঙ্গে জীবিকা নির্বাহের উপায় বর্ণনা করতে গিয়ে শাহ সাহেব অস্বাভাবিক ও অনৈতিক জীবনোপকরণ বা জীবিকা নির্বাহের পথগুলো উল্লেখ করতে ভুলেননি। তিনি বলেন, ‘অনেকের মন-মানসিকতা এমন হয়ে থাকে, যাদের বৈধ পন্থায় জীবিকা নির্বাহ কঠিন মনে হয়। তখন তারা জীবিকা নির্বাহের এমন সব পথে অগ্রসর হয়, যা নাগরিক ও সামাজিক জীবনের জন্য ক্ষতিকর হয়ে দাঁড়ায়। যেমন- চুরি, জুয়া, লুটতরাজ, ভিক্ষাবৃত্তি এবং বেআইনী ও অনৈতিক কাজ-কারবার।’
এই ‘ইরতিফাকাত’ সম্পর্কিত আলোচনায় শাহ সাহেবের কলম থেকে এমন কিছু তত্ত্বকণিকা বেরিয়ে এসেছে, যার দ্বারা সভ্যতা, সমাজ ও মানবতার উত্থান-পতনের ইতিহাস সম্পর্কে তার গভীর-জ্ঞান-প্রজ্ঞাই প্রমাণ করে। তিনি বলেন, ‘যখন মন-মানসে অস্বাভাবিক স্পর্শকাতরতা, ভারসাম্যহীনতা, সীমাতিরিক্ত স্বাদ-আহলাদ, বাড়াবাড়ি পর্যায়ের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও শঙ্কামুক্ত নিরাপত্তা এসে যায়, তখন জীবিকা নির্বাহের স্পর্শকাতর-মসৃণ ও জঘন্য নীচু পথ সৃষ্টি হয় আর প্রত্যেক ব্যক্তি একটি বিশেষ জীবনোপকরণ বা উৎপাদন প্রক্রিয়ার ঠিকাদার হয়ে যায়।’
শাহ সাহেব নাগরিক জীবনের জন্য ক্ষতিকর বিষয়গুলোর মধ্যে আরও উল্লেখ করেছেন, সকল নাগরিকের একই আয়ের পথ বেছে নেয়া। যেমন, সকলেই ব্যবসা শুরু করল, কৃষিকাজ ছেড়ে দিল অথবা যুদ্ধের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহের পথ অবলম্বন করল। তাঁর মতে কৃষি খাদ্যের পর্যায়ে আর কারিগরি, শিল্প, ব্যবসা ও আইন–শৃঙ্খলা লবণের পর্যায়ে। এ প্রসঙ্গেই শাহ সাহেব বিরাট এক তাত্ত্বিক কথা লিখেছেন। বলেছেন, ‘এ যুগে দেশ ধ্বংসের বড় দুটি কারণ রয়েছে।
১. বিনা পরিশ্রমে সরকারী তহবিলের উপর বোঝা হওয়া।
২. কৃষক, ব্যবসায়ী, পেশাজীবী ও বিভিন্ন কর্মজীবীদের উপর ভারী ভারী ট্যাক্স চাপিয়ে দেওয়া। শেষাংশে বলেন- আমাদের যুগের লোকদের এই তাত্ত্বিক বাস্তবতা বুঝে নেওয়া এবং সচেতন হয়ে যাওয়া উচিত।’
সভ্যতা ও সামাজিক বিপর্যয় ও অবক্ষয় সৃষ্টিকারী কারণগুলোর মধ্যে শাহ সাহেব অতিরিক্ত আনন্দ-বিনোদনকেও গণ্য করেন। এতে জীবনোপকরণ ও পরকাল উভয়ই ক্ষতিগ্রস্থ হয়। তন্মধ্যে দাবা খেলায় বিভোর-মত্ততা, শিকারের ব্যাপকতা ও কবুতর পালনকে অন্তর্ভুক্ত করেন। এভাবে চারিত্রিক অপরাধসমূহ ও এমন সব কাজকর্মকে মেনে নেওয়া, সাধারণতঃ যেগুলোকে কোনও সুস্থ-বিবেকবান মানুষ নিজের সত্ত্বার জন্য মেনে নিতে পারে না। সেগুলোকে সভ্যতার জন্য ক্ষতিকর মনে করে। তার মতে এসব কারণে রাজত্বের পতন দেখা দেয়।
সৌভাগ্য ও তার চার উৎস
কিতাবের চতুর্থ অনুচ্ছেদ مبحث السعادة (বা সৌভাগ্যের সোপান) প্রসঙ্গে। তাতে বলা হয়েছে, সৌভাগ্য অর্জন করা মানুষের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আর তা আত্মশুদ্ধি এবং পশুবৃত্তিকে ফিরিশতাসুলভ শক্তির অনুগত বানানোর দ্বারা অর্জিত হয়।
শাহ সাহেবের মতে সৌভাগ্য লাভের মূল উৎস চারটি। যার জন্য নবী- রাসূল প্রেরিত হয়েছেন। আর এর ব্যাখ্যা আসমানী শরীয়ত। এটা বস্তুতঃ ধর্ম ও শরীয়তসমূহের মৌলিক শাখাগুলোর সামগ্রিক শিরোনাম এবং নবী-রাসূল (স) প্রেরণের উদ্দেশ্যসমূহ পূর্ণতা দানের কার্যকরী মাধ্যম।
১. পবিত্রতা (তথা শারীরিক পবিত্রতা, যা মানুষকে আল্লাহর প্রতি মনোনিবেশ ও আল্লাহর সাথে সম্পর্ক স্থাপনের জন্য প্রস্তুত করে)।
২. আল্লাহর প্রতি মুখাপেক্ষিতা (তথা তাওবা ও অক্ষমতা প্রকাশ, অনুতাপ-অনুশোচনা, আল্লাহর প্রতি মনযোগিতা এবং বিনয়-নম্রতা)।
৩. সততা, উন্নত চরিত্র ও উঁচু স্তরের কাজকর্ম।
৪. দীনদারী ও ন্যায়নিষ্ঠা (তথা এমন আত্মিক যোগ্যতা, যার প্রতিক্রিয়ায় দেশ ও জাতির শৃঙ্খলা সহজেই প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়)।
এভাবে শাহ সাহেব মানুষের ব্যক্তিত্ব গঠন, আল্লাহর সাথে সম্পর্ক স্থাপন এবং একটি সুস্থ ও পরস্পর সহমর্মী সমাজ বিনির্মাণের মূলনীতিগুলো তুলে ধরেছেন, যা আসমানী শরীয়ত ও নবী-রাসূল প্রেরণের অন্যতম উদ্দেশ্য।
এরপর উক্ত চারটি গুণ অর্জনের পদ্ধতি বর্ণনা করেছেন। অনন্তর সেসব প্রতিবন্ধকতা উল্লেখ করেছেন, যেগুলো স্বভাবজাত আদর্শ বিকাশের ক্ষেত্রে অন্তরায়। তন্মধ্যে তিন প্রকার গ্রহণ করেছেনঃ
১. হিজাবুত তবা (তথা মানবিক ও মানসিক চাহিদাগুলোর প্রাধান্য)।
২. হিজাবুর রুসম (বাইরের অবস্থা ও পরিবেশের ক্ষতিকর প্রভাব)।
৩. হিজাবু সূইল মা’রিফা (তথা ভ্রান্ত শিক্ষা-দীক্ষা ও প্রচলিত ভ্রান্ত আকীদাসমূহের প্রভাব)।
এরপর তিনি এসবের প্রতিকার বর্ণনা করেছেন।
আকীদা ও ইবাদত
কিতাবের মূখ্য বিষয় শুরু হয়েছে পঞ্চম অধ্যায় مبحث البر والاثم থা পাপ-পুণ্য অনুচ্ছেদ থেকে। বস্তুতঃ কিতাবের আলোচ্য বিষয় ও উদ্দেশ্য এটিই। ‘بر’ বা পুণ্যের মূলনীতি হিসেবে শাহ সাহেব সর্বপ্রথম তাওহীদ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। কারণ, এর উপরই মুখাপেক্ষিতা, অক্ষমতা, অনুতাপ-অনুযোগ প্রকাশ সীমাবদ্ধ, যা সৌভাগ্য লাভের সবচেয়ে বড় উপায়। এক্ষেত্রে শাহ সাহেব তাওহীদের চারটি স্তর বর্ণনা করেছেন। সাথে সাথে আরবের মুশরিকদের শিরকের বাস্তবতা উন্মোচন করেছেন। তাওহীদের পর আল্লাহ পাকের গুণাবলির উপর ঈমান আনয়ন, ভাগ্যলিপির উপর ঈমান আনয়ন এবং আল্লাহর নিদর্শনাবলির প্রতি সম্মান প্রদর্শন (যেমন- শাহ সাহেবের মতে কুরআন, কা’বা, নবী এবং নামায সবচেয়ে সুস্পষ্ট ও গুরুত্বপূর্ণ নিদর্শন)। এর আলোচনা করতঃ শাহ সাহেব ইবাদত-আনুগত্য ও ফরযসমূহের প্রসঙ্গ শুরু করেছেন এবং সংক্ষেপে অযু-গোসলের রহস্য, নামাযের রহস্য, যাকাতের রহস্য, রোযার রহস্য ও হজ্জের রহস্য সম্পর্কে বিবরণ দিয়েছেন। এসব আলোচনা যদিও মৌলিক ও সংক্ষিপ্ত, তথাপি তাতে এমন এমন তত্ত্ব ও তথ্য রয়েছে, যা অন্য কোথাও পাওয়া কঠিন।
যেমন ‘নামাযের রহস্য’ অনুচ্ছেদে শাহ সাহেব লিখেন, ইবাদতের এই পদ্ধতি তিনটি শারীরিক অবস্থা তথা কিয়াম (দণ্ডায়মান হওয়া), রুকু (মাথা অর্ধনমিত করে ঝুঁকে থাকার অবস্থা) ও সিজদা (কপাল মাটিতে মিলানো অবস্থা) এর সমন্বয়। এখানে বড় থেকে ছোট দিকে অবনমিত হওয়ার স্থলে নিচ থেকে বড় দিকে (কিয়াম থেকে রুকু; রুকু থেকে সিজদার দিকে) উন্নীত হওয়ার নিয়ম রাখা হয়েছে। আর এটাই যুক্তি ও স্বভাবসম্মত। এরপর শাহ সাহেব ইবাদত প্রসঙ্গে আল্লাহ পাকের শ্রেষ্ঠত্ব-মাহাত্ম্য চিন্তাভাবনা, ধ্যান-মগ্নতা ও অব্যাহত যিকির-এর উপর আলোচনা সংক্ষিপ্ত না করার (যা ছিল প্রাচ্যবিদ, দার্শনিক ও হিন্দু সন্ন্যাসীদের রীতি আবার কোনও কোনও লাগামহীন সূফী দরবেশও এ পদ্ধতি অবলম্বন করেছিল) কারণ বর্ণনা করেছেন। বলেছেন, এই চিন্তা-গবেষণা ও ধ্যান-তন্ময়তা সেসব লোকদের জন্য সম্ভব ও উপকারী ছিল, যাদের মন-মানস সেসবের সাথে সামঞ্জস্য রাখত। তারা এর মাধ্যমে উন্নতি করতে পারত। নামায হচ্ছে চিন্তা–গবেষণা ও কাজ, মানসিক আকর্ষণ ও শারীরিক কর্মব্যস্ততার অবলেহ সমন্বয়। নামায সর্বশ্রেণীর জন্য উপকারী ও বিরাট প্রতিক্রিয়াশীল প্রতিষেধক। কুসংস্কারের বিষবাষ্প (পরিবেশের বিরূপ প্রভাব) থেকে পরিত্রাণ লাভ এবং মন–মানস বিবেকের অনুগত হওয়ার প্রশিক্ষণের জন্য নামায অপেক্ষা বড় কোনও ফলপ্রসূ ও কার্যকরী পদ্ধতি নেই।
রোযা ও হজ্জের সম্পর্ক যতদূর, সে সম্পর্কেও এ আলোচনায় কিছুটা ইংগিত প্রদান করা হয়েছে। কিন্তু কিতাবের দ্বিতীয় খণ্ডে এসবের উদ্দেশ্য, রহস্য ও তত্ত্বাবলি সম্পর্কে যে বর্ণনা দেওয়া হয়েছে, তার উপমা ইতোপূর্বে কোনও গ্রন্থে দৃষ্টিগোচর হয়নি। তার বিবরণ সামনে যথাস্থানে দেওয়া হবে।
জাতীয় রাজনীতি ও নবী-রাসূলের প্রয়োজনীয়তা
ষষ্ঠ অধ্যায়ের শিরোনাম مبحث السياسات الملية বা জাতীয় রাজনীতি প্রসঙ্গ। এটি কিতাবের অতি গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গ। এর প্রথম অনুচ্ছেদে শাহ সাহেব অত্যন্ত বিচক্ষণতা, দূরদর্শীতা ও বাস্তবধর্মীতার সাথে বলেছেন, মানবজাতির জন্য সত্যের পথপ্রদর্শক ও জাতির সংস্কারক-সংগঠক (তথা নবী- রাসূল)-এর প্রয়োজন কেন হয়েছে? এর জন্য তাদের সুস্থ স্বভাবজাত জ্ঞান ও সাধারণ বিবেক-বুদ্ধি কেন যথেষ্ট ছিল না? এরপর তিনি এ দলের গুণাবলি ও প্রয়োজনীয় শর্তাবলী সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। আরও লিখেছেন, তিনি কখন, কিভাবে আপন উদ্দেশ্য পূর্ণ করতে পারেন এবং তাতে সাফল্য লাভ করতে পারেন। এ অনুচ্ছেদটি কালাম শাস্ত্রের কিতাবাদিতে বর্ণিত, ‘নবুওয়াত প্রমাণের সাধারণ আলোচনা’ থেকে সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম মনে হয়। এতে সুস্থ জ্ঞান-বিবেককে আশ্বস্ত করার মত এমন উপাদান রয়েছে, যা কালাম শাস্ত্র ও আকাঈদের কিতাবাদিতে সাধারণতঃ পাওয়া যায় না। এ আলোচনায় নবুওয়াতের পদমর্যাদা ও এর বৈশিষ্ট্যাবলী সম্পর্কে যে অনুচ্ছেদ রয়েছে, তা শাহ সাহেবের শরীয়তের প্রাণ ও নবুওয়াতের মেজাযের বাস্তবতা সম্পর্কে বিজ্ঞতা, মানবাত্মা সম্পর্কে গভীর অধ্যয়ন এবং চরিত্রের আভ্যন্তরীণ উৎস সম্পর্কে সচেতনতার প্রতি ইংগিত করে। এ অধ্যায়ে নবী-রাসূল প্রেরণের কারণসমূহের ব্যাপারে স্ববিস্তার আলোচনা করা হয়েছে।
সমসাময়িক দূতপ্রেরণ
শাহ সাহেব লিখেন, সবচেয়ে পূর্ণাঙ্গ নবুওয়াত বা রিসালাত সেই নবী- রাসূলেরই হয়ে থাকে, যার প্রেরণ ‘মাকরূন’ (বা যৌথ) হয় অর্থাৎ তার নবুওয়াতের সাথে গোটা এক জাতি তাবলীগ ও দাওয়াতের জন্য আদিষ্ট এবং তার সংস্পর্শের বরকতে তৈরী হয়ে অন্যান্য মানুষের শিক্ষা-দীক্ষার মাধ্যম হয়। নবীর আবির্ভাব হয় মৌলিকভাবে (আর একে নবুওয়াত বলা হয়); উম্মতের স্থলাভিষিক্ততা ও খেদমতের দায়িত্ব অর্পণ হয় মধ্যস্থতা ও প্রতিনিধিত্ব হিসেবে। রাসূলে কারীম (স) -এর আবির্ভাব এমনই পূর্ণাঙ্গ ছিল, যার সাথে পুরো এক উম্মতকে তাঁর নবুওয়াতের পদমর্যাদার খেদমত ও প্রসারের জন্য হাতিয়ার ও অস্ত্র বানানো হয়েছে। আর এর জন্য দূতপ্রেরণ ও সমার্থক শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। কুরআনে কারীমে ইরশাদ হয়েছে-
کنتم خير امة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون
عن المنكر.
‘যত উম্মত সৃষ্টি হয়েছে, তন্মধ্যে তোমরা শ্রেষ্ঠ উম্মত। তোমাদেরকে মানুষের জন্য বের করা হয়েছে, যাতে তোমরা লোকদেরকে সৎকাজের আদেশ কর আর নিষেধ কর অসৎকাজ থেকে। (সূরা আলে ইমরান : ১১০)
হাদীস শরীফে (বা’ছাত) ‘দূত প্রেরণ’ শব্দই ব্যবহার করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (স) সাহাবায়ে কিরামকে লক্ষ্য করে বলেন,
فانما بعثتم ميسرين ولم تعثوا معسرين
‘তোমাদেরকে সহজতার জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে; কঠিনতার জন্য সৃষ্টি করা হয়নি।’
এ অনুচ্ছেদের বিশেষ প্রতিপাদ্য হচ্ছে সেটি, যাতে নবী-রাসূলগণের সীরাত (জীবন চরিত), তাদের আগ্রহ-চেতনা, মন-মানসিকতা, তাদের দাওয়াত-তাবলীগের পদ্ধতি, তাদের সম্বোধন ভঙ্গি ও শিক্ষাধারা বর্ণনা করা হয়েছে। এতে শাহ সাহেবের দূরদর্শীতা, বিচক্ষণতা, নবুওয়াত ও আম্বিয়ায়ে কিরামের বৈশিষ্ট্যাবলির গভীর অধ্যয়ন এবং কুরআনে কারীমের অগাধ ব্যুৎপত্তি অনুমান করা যায়।
ইরান ও রোম সভ্যতায় চারিত্রিক ও ঈমানী মূল্যবোধের বিভৎসতা এবং মানবতার দুরাবস্থা
বর্বরতার যুগ যদিও আরবের সাথে সুনির্দিষ্ট ছিল না। তা ছিল বিশ্বময় বিস্তৃত আকীদাগত, চারিত্রিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক এক বিপর্যয়, যা গোটা পৃথিবীকে গ্রাস করে নিয়েছিল। কিন্তু ইরানী ও রোমীরা ছিল এর নেতা ও আসল কর্ণধার। তাদের সভ্যতা-সংস্কৃতিকেই সে সময় পৃথিবীতে মানদণ্ড মনে করা হত। তারই (অন্ধ) অনুকরণ করা হত সর্বত্র। তাদের দেশগুলো, কেন্দ্রীয় শহর ও সমাজ সবচেয়ে বেশি এর আক্রমণে ছিল। এই অবস্থা-পরিস্থিতির যে চিত্র শাহ সাহেব অংকণ করেছেন এবং এর যেসব কারণ তিনি উল্লেখ করেছেন, এর উত্তম চিত্র প্রাচীন জীবনচরিত ও ইতিহাসের কোনও কিতাবে এবং ইতিহাসে-দর্শন ও সামাজিক জ্ঞানের কোনও পণ্ডিতের কলমে রচিত হতে দেখা যায়নি। এখানে এসে শাহ সাহেবের কলম তার পূর্ণ কৃতিত্ব দেখিয়েছে। তার লিখনী শক্তি ও রচনাশৈলী আপন উৎকর্ষতায় দেখা যায়। এর দ্বারা সাহেবের ইতিহাসের গভীর জ্ঞান, বাস্তবতা পর্যন্ত পৌঁছার যোগ্যতা ও প্রকৃত অবস্থাচিত্র পর্যবেক্ষণের আল্লাহর প্রদত্ত যোগ্যতা উপলব্ধি করা যায়। শাহ সাহেব লিখেন,
‘শত শত বছর ধরে স্বাধীন রাজত্ব করতে করতে আর দুনিয়ার নানা স্বাদ আস্বাদনে নিমজ্জিত থেকে, পরকালকে একেবারে ভুলে যাওয়া ও শয়তানের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণাধীন হয়ে যাওয়ার কারণে ইরানী ও রোমীরা জীবনের সহজতা–অনাড়ম্বরতা ও সুখ–শান্তির উপকরণে বিরাট জটিলতা ও স্পর্শকাতর চিন্তাধারা সৃষ্টি করে নিয়েছিল। এতে সর্বপ্রকার উন্নতি ও উৎকৃষ্টতায় একে অন্যের থেকে অগ্রগামী হওয়া এবং গর্ব করার চেষ্টা চালাত। পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চল থেকে এসব কেন্দ্রস্থলে বড় বড় শিল্পী–কারিগর, পেশাজীবী ও দক্ষ লোকজন এসে জড়ো হয়েছিল। যারা আরাম–আয়েশ ও সুখ–শান্তির উপকরণে জটিলতা সৃষ্টি করত। নতুন নতুন সাজগোজ–প্রসাধন বের করত। তার উপর তাৎক্ষণিক আমল শুরু হয়ে যেত। তাতে যথারীতি পরিবর্ধন ও চমক থাকত। এসব নিয়ে গর্বও করা হত। জীবনযাত্রা এত উঁচু হয়ে গিয়েছিল যে, আমীরদের কারও জন্য এক লাখ দিরহামের কমমূল্যের পাগড়ী বাঁধা ও মুকুট পরা ছিল চরম দোষণীয়। কারও নিকট যদি বিলাসবহুল প্রাসাদ, ফোয়ারা, গোসলখানা, বাগ–বাগিচা, আয়েশী খাবার, প্রশিক্ষিত জীবজন্তু, সুদর্শন যুবক ও গোলাম না থাকত, খাবারে বিলাসিতা ও আড়ম্বরতা আর পোশাক–পরিচ্ছদে বৈচিত্র্য না হত, তাহলে সম–সাময়িকদের মাঝে তার কোনও সম্মান থাকত না। এ বিবরণ অনেক দীর্ঘ। স্বদেশের রাজা–বাদশাদের যে অবস্থা দেখছেন, তা এর সঙ্গে অনুমান করতে পারেন।
এসব বিলাসিতা তাদের জীবন ও সমাজের (অবিচ্ছেদ্য) অংশ হয়ে গিয়েছিল। তাদের মনের ভেতর এমনভাবে বদ্ধমূল হয়ে গিয়েছিল যে, কোনভাবেই বের করা যেত না। এ কারণে এমন এক দূরারোগ্য ব্যাধি সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল, যা তাদের সভ্যতায় ছড়িয়ে পড়েছিল। এ ছিল এক মহাবিপদ। যার থেকে সাধারণ–অসাধারণ, ধনী–দরিদ্র কেউই নিরাপদ ছিল না। প্রত্যেক নাগরিকের উপর এই বিলাসিতা ও আমীরানা জীবনধারা এমনভাবে চেপে বসেছিল, যা তাদেরকে (সহজ) জীবন থেকে অক্ষম করে দিয়েছিল। তাদের মাথার উপর প্রতিনিয়ত উদ্বেগ–উৎকণ্ঠার এক পাহাড় পড়ে থাকত।
কথা হল, এই বিলাসিতা বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় করা ছাড়া লাভ করা যেত না আর এই অর্থ ও অঢেল ধন–সম্পদ কৃষক, ব্যবসায়ী ও অন্যান্য পেশাজীবীদের উপর কর ও ট্যাক্স বাড়ানো এবং তাদের উপর শোষণ চালানো ছাড়া হস্তগত হত না। তারা যদি এসব দাবী পূরণ করতে অস্বীকৃতি জানাত, তবে তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করা হত। তাদেরকে নানা ধরনের শাস্তি দেওয়া হত। আর তারা যদি মেনে নিত, তবে তাদেরকে খাটানো হত গাধা ও বলদের মত। যাদের দ্বারা পানি উত্তোলন ও কৃষিকাজে সাহায্য নেওয়া হত। কেবল সেবার জন্যই তাদের লালন–পালন করা হত। তারা কখনও কষ্ট–পরিশ্রম থেকে নিষ্কৃতি পেত না।
এই কষ্টপূর্ণ ও পশুসুলভ (মানবেতর) জীবনের পরিণামে কখনও তাদের মাথা উঠানো এবং পরকালীন সৌভাগ্য লাভের কল্পনা করারও সময়–সুযোগ হত না। অনেক সময় গোটা দেশেও এমন কোনও মানব সন্তান পাওয়া যেত না, যার মধ্যে নিজ ধর্মের চিন্তা–ভাবনা ও গুরুত্ব রয়েছে।‘
আরও কিছু উপকারী কথা
এর পরের বিষয়বস্তু ‘ধর্মের আসল/উৎস একটি।’ আর শরীয়তের রাস্তায় বিশেষ কোনও যুগ ও জাতির পক্ষাবলম্বনের কারণে মতবিরোধ হয়। তারপর এর ব্যাখ্যা দিয়ে বলেন, দীন-ধর্মের একটি উৎস হওয়া সত্ত্বেও সেসব পথে কেন জবাবদিহি করা হয়?
সহজিকরণ, উৎসাহ প্রদান ও ভীতি প্রদর্শনের তত্ত্ব ইত্যাদির অধীন বিষয়গুলো আলোচনার পর শাহ সাহেব এমন ধর্মের প্রয়োজনীয়তা প্রমাণ করেছেন, যা সকল ধর্ম বিলুপ্তকারী হবে। তাছাড়া ধর্মকে কিভাবে বিকৃতির ছোবল থেকে রক্ষা করা যায়, বিকৃতি-পরিবর্তন কোন কোন পথে ও ছিদ্র দিয়ে ধর্মে অনুপ্রবেশ করে, কী কী রূপে তা বিকশিত হয়? আর কী কী রঙ-রূপ ধারণ করে? শরীয়ত সেসবের প্রতিকার হিসেবে কী পন্থা অবলম্বন করেছে এবং কী কী ব্যবস্থা নিয়েছে? এরপর বিশদভাবে বর্ণনা করেছেন, নবুওয়াতের যুগে জাহেলী যুগের কী অবস্থা ছিল, রাসূলে কারীম (স) যার সংস্কার করেছেন।
হাদীস ও সুন্নাহর মর্যাদা এবং এ ব্যাপারে উম্মতের কর্মপদ্ধতি
সপ্তম অধ্যায়ের শিরোনামمبحث الشرائع من حديث النبى صلى الله ، عليه وسلم তথা হাদীসে নববী সম্পর্কে শরয়ী দৃষ্টিভঙ্গি। এতে সেসব আলোচনা স্থান পেয়েছে, যেগুলো সরাসরি হাদীস ও সুন্নাহর জ্ঞান, তা থেকে মাসায়েল উৎসারণ, উলুমে নববী (স)-এর শ্রেণীবিভাগ, নবী (স) থেকে শরীয়ত আহরণের অবস্থা-পদ্ধতি, হাদীস গ্রন্থাবলির শ্রেণীবিন্যাস, কুরআন- সুন্নাহর আলোকে শরয়ী উদ্দেশ্যসমূহ উদঘাটনের পদ্ধতি ও বিভিন্ন হাদীসের মাঝে সমন্বয় সাধন কিংবা প্রাধান্য দানের বিষয়। এ প্রসঙ্গে অত্যন্ত বিচক্ষণতা ও সূক্ষ্মদর্শিতার সাথে শাহ সাহেব শাখামূলক আলোচনায় সাহাবায়ে কিরাম ও তাবেঈদের মতানৈক্যের কারণগুলো বর্ণনা করেন। সেসবের উদাহরণ উদ্ধৃত করার পর ফকীহগণের মতাদর্শে মতবিরোধ এবং হাদীস বিশারদ ও চিন্তাবিদগণের মতানৈক্যের পার্থক্য বর্ণনা করেন। চতুর্থ হিজরী শতকের পূর্বাপর মানুষের মাসআলা জিজ্ঞাসা ও এর উপর আমল করা এবং এক্ষেত্রে বিশেষ-অবিশেষ মহলের দৃষ্টিভঙ্গি কী ছিল? এসবের সবিস্তর ব্যাখ্যা দেন, যা অত্যন্ত সূক্ষ্ম ও গভীর আলোচনা সমৃদ্ধ এবং যা কালাম কিংবা উসূলে ফিকহ শাস্ত্রের কোনও কিতাবে পাওয়া দুষ্কর।
ফরযসমূহ ও রুকনগুলোর তত্ত্ব-রহস্য
শাহ সাহেব আকাঈদ থেকে নিয়ে ইবাদত-আনুগত্য, লেনদেন, আচার-অনুষ্ঠান, ইহসান-অনুগ্রহ; আত্মশুদ্ধি, আইন-শৃঙ্খলা, অবস্থা-পরিস্থিতি, জীবনোপকরণ বা জীবিকা নির্বাহের পদ্ধতি, দান ও সাহায্য-সহযোগিতা, পরিবার ব্যবস্থা, খেলাফত ও শাসন ব্যবস্থা, বিচারব্যবস্থা, যুদ্ধ-জিহাদ, পানাহারের শিষ্ঠাচার, বন্ধুত্ব নীতি, সামাজিকতা আর সবশেষে ফিতান, পরকালীন ঘটনাপ্রবাহ ও কিয়ামতের আলামত পর্যন্ত হাদীসের আলোকে আলোচনা করেছেন। এ প্রসঙ্গে সীরাতে নববী (স)-এর সারমর্মও পেশ করেছেন। সেসব অনুচ্ছেদের উদ্দেশ্য-রহস্য বর্ণনা করতে গিয়ে লিখেছেন, এসব বিষয়ের সম্পর্ক জীবন, সভ্যতা, চরিত্র-নৈতিকতা থেকে কখনও বিচ্ছিন্ন হতে পারে না। বস্তুতঃ এটিই কিতাবের কেন্দ্রীয় বা মূল প্রতিপাদ্য। শাহ সাহেবের ইচ্ছা ছিল, হাদীস শিক্ষাদান যেন সেসব তত্ত্ব-রহস্যের আলোকে আমল ও চরিত্র-নৈতিকতা, সভ্যতা-সামাজিকতা, মানবীয় সাফল্য ও পারস্পরিক সম্পর্কের সঙ্গে হয়। যেন সেসবের পূর্ণ প্রভাব পড়ে জীবন, আমল-আখলাক, সভ্যতা ও সামাজিকতার ওপর। সামঞ্জস্য বিধান হয় ঐতিহ্যগত ও যৌক্তিক দলীল-প্রমাণের মাঝে, বিরুদ্ধবাদীদের পক্ষে এসবের উপর আপত্তি উত্থাপন, হাদীস ও সুন্নাতের মূল্য, উপকারিতা এবং তার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা হ্রাস করা (যাকে শাহ সাহেবের দূরদর্শী ও সূক্ষ্মদৃষ্টি দেখে নিয়েছিল) ও মানসিক বিক্ষিপ্ততা সৃষ্টির সুযোগ না হয়। আমলী আরকান ও চার ফরয সম্পর্কে যা কিছু লিখেছেন, তা এরই অংশ এবং ‘হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা’ -এর একটি বৈশিষ্ট্য। এখানে উদাহরণস্বরূপ কেবল রোযা ও হজ্জের উদ্দেশ্যভেদ এবং এগুলোর ইসলামী ও শরয়ী রূপরেখার সূক্ষ্মতার উপর শাহ সাহেব যা কিছু লিখেছেন, তা উল্লেখ করা হচ্ছে। রোযা সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে তার পরিমাণ ও রোযার সংখ্যা নির্ধারণের রহস্য (যা ইসলামী শরীয়তের সাথে নির্দিষ্ট) এবং এর শরয়ী বিধানের উপর আলোকপাত করতে গিয়ে তিনি লিখেন, ‘রোযার মধ্যে (সময়, সংখ্যা ও পরিমাণের) স্বেচ্ছাধিকার দিয়ে দেওয়া হলে অপব্যাখ্যা ও পলায়নের পথ উন্মুক্ত হয়ে যাবে। রুদ্ধ হয়ে যাবে সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধ–এর পথ। বিরাট উদাসীনতার শিকার হয়ে যাবে ইসলামের এই সবচেয়ে বড় আনুগত্য–ইবাদত।
এরপর রোযার পরিমাণ ও সংখ্যা প্রসঙ্গে লিখেন, এর (সময়) নির্ধারণেরও প্রয়োজন ছিল। যেন তাতে বাড়াবাড়ি ও উদাসীনতার অবকাশ না থাকে। নতুবা কেউ কেউ এর উপর এতটুকু আমল করত, যার দ্বারা তার কোনও কল্যাণ হত না আর না কোন প্রভাব পড়ত। আবার কেউ কেউ এত বাড়াবাড়ি ও অতিরঞ্জন করত যে, তারা অক্ষমতা ও দুর্বলতার সীমায় পৌঁছে যেত। আর সে হয়ে যেত মৃতপ্রায়/অর্ধমৃত। মূলতঃ রোযা একটি প্রতিষেধক। প্রবৃত্তির বিষ নামানোর জন্য যার ব্যবস্থা করা হয়েছে। কাজেই এতে প্রয়োজনীয়তার প্রতি লক্ষ্য রাখা বাঞ্ছনীয়।
তারপর রোযার উভয় শ্রেণীর (তথা প্রথমতঃ সেই রোযা, যাতে পানাহারসহ রোযার পরিপন্থী সকল প্রকার কাজকর্ম থেকে পুরোপুরি বেঁচে থাকতে হয়। দ্বিতীয়তঃ সেই রোযা যাতে কতিপয় বিষয় থেকে বাঁচতে হয়। আর কতিপয় বিষয় থেকে বাঁচতে হয় না -এর মাঝে তুলনা করে প্রথমোক্ত রোযাকে প্রাধান্য দেন।) সাথে অভিজ্ঞতা, জ্ঞানের গভীরতা ও আধ্যাত্মিকতার আলোকে এর শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করতঃ লিখেন, ‘আহার কমানোর দুটি পদ্ধতি। এক. খাবারের পরিমাণ হ্রাস করে দেওয়া। দুই. আহারের মধ্যে এত দীর্ঘ বিলম্ব রাখা, যাতে উদ্দেশ্য পূর্ণ হয়ে যায়। শরীয়তে এই দ্বিতীয় পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়েছে। কেননা এতে ক্ষুৎ-পিপাসার সঠিক ধারণা জন্মে। পাশবিক কামনায় আঘাত লাগে। বাস্তবেই এতে হ্রাস পেতে দেখা যায়। পক্ষান্তরে প্রথম পদ্ধতিতে মানুষের উপর বিশেষ কোনও প্রভাব পড়ার পূর্বে তা সৃষ্টি হয় না। কেননা যথারীতি পানাহার চালিয়ে যাওয়া হয়। দ্বিতীয়তঃ প্রথম পদ্ধতির জন্য কোনও সাধারণ নীতিমালা প্রণয়ন করা কঠিন। কারণ, মানুষের অবস্থা বিভিন্ন ধরনের। কেউ এক পোয়া খায় আবার কেউ খায় আধা সের। সুতরাং এ পদ্ধতি নির্ধারণের ফলে যদি একজনের কল্যাণ হয়, তবে অন্যজনের ক্ষতি হবে।’
তিনি আরও বলেন, এই সুনির্দিষ্টতা ও সময়ের বাধ্যবাধকতায় ভারসাম্য থাকা প্রয়োজন। তিনি লিখেন, ‘এটাও জরুরী ছিল যে, এ সময় যেন অসাধ্য সাধন বা সাধ্যাতীত হুকুম পালনে আক্রান্তকারী না হয়। যেমন, তিনদিন তিনরাত। কেননা এটা শরীয়তের আলোচ্য বিষয়ের বাইরে এবং তার উদ্দেশ্য পরিপন্থী। সাধারণতঃ এর উপর আমল করাও অসম্ভব।’
হজ্জ প্রসঙ্গে তার আলোচনা সম্পূর্ণ ব্যতিক্রমধর্মী ও স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। তিনি সেখানে লিখেন-
‘(হজ্জের উদ্দেশ্যসমূহের মধ্যে) সেই উত্তরাধিকার সত্ত্ব সংরক্ষণও আছে, যা আমাদের জাতির পিতা ইবরাহীম (আ) ও আমাদের নেতা ইসমাইল (আ) আমাদের জন্য রেখে গেছেন। কারণ, এ দুজনই মিল্লাতে হানীফার (পবিত্র উম্মাহর) ইমাম এবং আরবে তার প্রতিষ্ঠাতা ও স্থপতি বলা যেতে পারে। রাসূলে কারীম (স)-এর শুভাগমনও এজন্য হয়েছিল, যেন মিল্লাতে হানীফা তার মাধ্যমে পৃথিবীতে জয়লাভ করে এবং তার ঝাণ্ডা সমুন্নত হয়।’
আল্লাহ তা’আলা বলেন,
ملة أبيكم ابراهيم
তোমাদের পিতা ইবরাহীম (আ) এর ধর্ম।
কাজেই এই ধর্মের ইমামের (দিশারীর) পক্ষ থেকে যেসব বিষয় আমরা উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছি, যেমন- স্বভাবজাত গুণাবলি, হজ্জব্রত পালন ইত্যাদি আমাদের সংরক্ষণ করা জরুরী। রাসূলুল্লাহ (স) ইরশাদ করেন-
قفوا على مشاعركم فانكم على أرث من إرث أبيكم.
‘আপন নিদর্শন/স্থানসমূহে অবস্থান করো। কেননা তোমরা আপন পিতার একই উত্তরাধিকার সত্ত্বের উত্তরাধিকারী।’
এছাড়া তিনি আরেকটি তত্ত্ব-দর্শন বর্ণনা করে লিখেন- ‘যেভাবে সরকারের কিছুদিন পরপর একটি গণজরিপ ও পরিদর্শনের প্রয়োজন হয়, যেন সে জানাতে পারে– কে কৃতজ্ঞ? কে বিদ্রোহী? কে কর্তব্য পরায়ণ, দায়িত্বশীল আর কে কামচোরা প্রতারক? সাথে সাথে এর মাধ্যমে তার সততা, বিশ্বস্ততার সুখ্যাতি ও সুনাম হয়। তার শ্রমিক, কর্মচারী–কর্মকর্তা ও নাগরিকগণ একে অন্যের সাথে পরিচিত হয়। অনুরূপভাবে জাতির জন্য হজ্জ প্রয়োজন। যাতে মুনাফিক–অমুনাফিক (কপট–অকপট)-এর মাঝে পার্থক্য নির্ণয় হয়। আল্লাহ পাকের নির্দিষ্ট দিনে আল্লাহ পাকের দরবারে আবেগ–উচ্ছাস নিয়ে দলে দলে লোকজন হাজির হয়। মানুষ পরস্পর পরিচয় লাভ করে। প্রত্যেক ব্যক্তি যা তার কাছে নেই, সে বিষয়ে অন্যের থেকে উপকার লাভ করে। কেননা উত্তমতর ও সুন্দর আনন্দদায়ক বিষয়গুলো সাধারণতঃ সংস্পর্শ ও বন্ধুত্বের মাধ্যমে এবং একে অপরকে দেখে–শুনেই অর্জিত হয়।‘
তিনি আরও লিখেন, ‘হজ্জ যেহেতু এমন একটি মুহূর্ত, যেখানে সকলেই সমবেত হয়, তাই এটি বিভ্রান্তিকর রুসম-রেওয়াজ থেকে নিরাপত্তা লাভের জন্য খুবই ফলপ্রসূ। জাতির মধ্যে তাঁদের ইমাম ও দিশারীদের স্মৃতিচারণ এবং মনের মণিকোঠায় তাদের আনুগত্য ও অনুকরণের আগ্রহ সৃষ্টি করার জন্য কোনও কিছু এ পর্যায়ের নেই, যা তার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারে।’
অন্যত্র লিখেন, ‘হজ্জের উদ্দেশ্যসমূহের মধ্যে আরেকটি বিষয় হল, যার জন্য সরকার-প্রশাসন কোনও প্রদর্শনী কিংবা সরকারী উৎসবের আয়োজন করে। আর তা দেখার জন্য কাছে-দূরের সকল স্থান থেকে মানুষ এসে সমবেত হয়। মিলিত হয় একে অন্যের সাথে। নিজের শাসন ব্যবস্থা ও জাতির শিক্ষা-দীক্ষা সম্পর্কে অবগতি লাভ করে। তার পবিত্র ও পুণ্যময় স্থানগুলোর সম্মান রক্ষা করে। অনুরূপভাবে হজ্জ মুসলমানদের একটি জাতীয় প্রদর্শনী কিংবা রাজকীয় অনুষ্ঠান। যেখানে তাদের প্রভাব-প্রতিপত্তি প্রকাশ পায়। তাদের শক্তিসমূহ ঐক্যবদ্ধ হয়। তাদের জাতির নাম উজ্জল হয়।’ আল্লাহ তা’আলা ইরশাদ করেন-‘
. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا
‘আর (স্মরণ করো সে সময়ের কথা) আমি কাবাকে করেছি মানুষের জন্য প্রত্যাবর্তনস্থল ও নিরাপদ শান্তির স্থান।’
কিতাবের স্বয়ংসম্পূর্ণতা
এ গ্রন্থের আরেকটি বৈশিষ্ট্য হল, ফিকহ, হাদীস, আকাঈদ, ইবাদত, লেনদেন ও আচার-অনুষ্ঠানের সাথে সম্পৃক্ত অধ্যায় ও অনুচ্ছেদগুলো ব্যতীত এতে পরিবারব্যবস্থা, পারিবারিক শৃঙ্খলা বিধান, খেলাফত (গণপ্রতিনিধিত্ব) ও বিচারব্যবস্থা, অর্থনৈতিক অধ্যায় এবং সাহচর্যের শিষ্টাচারসমূহের আলোচনাও রয়েছে। যা চরিত্র, নৈতিকতা, সামাজিকতা, সভ্যতা ও জীবনোপায়ের সাথে সম্পৃক্ত। সাধারণতঃ কোনও ফিকহী কিংবা দর্শন শাস্ত্রের বই-পুস্তকে এসবের আশা করা যায় না।
অনুগ্রহ ও আত্মশুদ্ধি
অধিকন্তু এ গ্রন্থে শাহ সাহেব হাদীস ও জীবন-চরিতের আলোকে বিন্যস্ত অনুগ্রহ ও আত্মশুদ্ধির এমন নীতিমালা উপস্থাপন করেছেন, যার উপর চলে মানুষ আল্লাহর নৈকট্যের উঁচু থেকে উঁচু সিঁড়িগুলো, বেলায়েতের স্তরসমূহ, মর্যাদার আসন ও অবস্থাসমূহ পর্যন্ত পৌঁছতে পারে। ইহসান সম্পর্কিত এই অনুচ্ছেদটি কিতাবের ৬৬-১০১ পৃষ্ঠা পর্যন্ত বিস্তৃত। এ অনুচ্ছেদে শাহ সাহেব সেসব উপাদানসমূহ নিয়ে আলোকপাত করেছেন, যেগুলো বিভিন্ন সহীহ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। তন্মধ্যে শুধুমাত্র হাজির করা, ইচ্ছা-সংকল্প এবং শারীরিক ও বাতেনী অবস্থাসমূহের সঙ্গে আত্মার প্রতি মনোনিবেশ করার উপর জোর দিয়েছেন। সেসঙ্গে ক্রমাগত দুঃখ-ব্যথা ও রোগ-ব্যাধির চিকিৎসা, ঐ শরীয়তসম্মত পন্থা, ফরয, ইবাদত ও যিকির-আযকারের মাধ্যমে নির্বাচন করেছেন। সাথে সাথে বদঅভ্যাস ও নীচুতার প্রতিষেধক চিকিৎসা এবং উত্তম-উন্নত স্বভাব-চরিত্র অর্জনের পন্থাও শরীয়ত ও সুন্নাতের সুস্পষ্ট নির্দেশনায় বর্ণনা করেছেন।
এ অধ্যায়ে তিনি বর্ণিত যিকিরসমূহ, শরীয়তসম্মত দু’আসমূহ এবং ইস্তিগফার-তাওবার গুরুত্বপূর্ণ শব্দাবলীও সন্নিবেশিত করেছেন। কার্যকরী মাকবুল দু’আর পদ্ধতি এবং তার শর্তাবলীও বর্ণনা করেছেন। এ প্রসঙ্গে মানবিক চাহিদা, জীবনের প্রয়োজনাদি ও ধর্মীয় আমলগুলো নিয়তের পরিচ্ছন্নতার সাথে আদায় করার প্রতি তাগিদ করেছেন। এসবের প্রভাব- ক্রিয়া ও অবস্থাবলি ব্যতিক্রম হওয়ার ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তিনি লিখেছেন, ‘ভালোভাবে হৃদয়াঙ্গম করে নিন, নিয়ত হচ্ছে (সবকিছুর) প্রাণ–আত্মা। আর ইবাদত হল দেহ। আত্মা ছাড়া শরীর/দেহ বেঁচে থাকা সম্ভব নয়। আত্মা দেহ থেকে পৃথক হয়ে যাওয়ার পরও জীবিত থাকে। কিন্তু জীবন/বেঁচে থাকার প্রতিক্রিয়া দেহ ছাড়া পুরোপুরিভাবে প্রকাশ পায় না। কাজেই আল্লাহ তা’আলা বলেন,
لن ينال الله لحمها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم
‘আল্লাহ পাকের এসব কুরবানীর (পশুর) গোশত ও রক্ত পৌঁছে না। সেখানে পৌঁছে তোমাদের তাকওয়া বা আল্লাহভীরুতা। (সূরা হজ্জ ৩৭)
আর রাসূলে কারীম (স) ইরশাদ করেছেন,
إنما الاعمال بالنيات
‘সকল আমলের গ্রহণযোগ্যতা নিয়তের উপর নির্ভরশীল।’
অনন্তর শাহ সাহেব নিম্নোক্ত ভাষায় ‘নিয়ত’-এর সংজ্ঞা পেশ করেন। ‘নিয়ত বলে আমাদের উদ্দেশ্য তাসদীক তথা সত্যায়ন ও বিশ্বাসের সেই মানসিক অবস্থা, যা তাকে সে কাজের প্রতি উদ্বুদ্ধ করে। অর্থাৎ আল্লাহ তা’আলা স্বীয় নবী-রাসূলগণের মাধ্যমে আনুগত্যকারীদের প্রতিদান আর অবাধ্যদেরকে শাস্তি দেওয়ার যে অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছেন, তা এই হুকুম পালন এবং এই পাপাচার থেকে বেঁচে থাকার কারণ -এ বিশ্বাস করা।’
আলোচ্য অনুচ্ছেদের শেষে শাহ সাহেব উন্নত চরিত্র গঠন, সৃষ্টিজীবের অধিকার সংরক্ষণ ও উত্তম আচার-ব্যবহার সম্পর্কে কয়েকটি হাদীস বাছাই করে লিখে দিয়েছেন। যার উপর আমল করলে মানুষ কল্যাণ ও পবিত্রতার উচ্চস্তরে পৌঁছে যেতে পারে। এরপর সেসব মর্যাদা ও অবস্থার বর্ণনা দিয়েছেন, যেগুলো উপকার ও পবিত্রতার সুফলে অর্জিত হয়; যা বাতেনী নূর, অন্তরের সচেতনতা, আত্মার পরিচ্ছন্নতা, মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি ও ঊর্ধ্বজগতের সাহায্য-সমর্থনের সুফল।
জিহাদ
উক্ত গ্রন্থে জিহাদ সম্পর্কেও একটি অনুচ্ছেদ রয়েছে। আর তা শাহ সাহেব এক তথ্যবহুল ও বিস্ময়কর শব্দমালা দিয়ে শুরু করেছেন। যা সকল ধর্ম ও জাতির পুরো ইতিহাস, মানব সৃষ্টির উদ্দেশ্যসমূহ ও সমগ্র বিশ্বজগতের স্রষ্টার উদ্দিষ্ট ব্যবস্থার উপর অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন কোনও জ্ঞানী পণ্ডিতই লিখতে পারেন। শাহ সাহেব লিখেন, ‘স্মরণ রাখুন! সার্বিকভাবে পূর্ণাঙ্গ শরীয়ত এবং তার স্বয়ংসম্পূর্ণ সংবিধান হচ্ছে সেই শরীয়ত, যাতে জিহাদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।‘
মোটকথা, এই গ্রন্থখানা তার স্বয়ংসম্পূর্ণতা, তাত্ত্বিকতা, দীন ও শরীয়তের ব্যাপক-প্রশস্ত, মজবুত নিবিড় ব্যাখ্যা এবং কিতাবের পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় ছড়ানো ছিটানো শত-সহস্র অমূল্য তথ্য-কণিকা ও সূক্ষ্ম গবেষণার ভিত্তিতে ইসলামী গ্রন্থশালায় বহুদিক থেকে সম্পূর্ণ স্বকীয় বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। এক কথায় ،كم ترك الأول للآخر’ ‘কত কী রেখে গেলেন প্রবীণগণ পরবর্তীদের জন্য’-এর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। মাওলানা শিবলী (র) তার বিখ্যাত ‘ইলমুল কালাম’ গ্রন্থে লিখেছেন- ‘আল্লামা ইবনে তাইমিয়া (র) ও ইবনে রুশদ -এর পরে বরং স্বয়ং তাদের যুগেই মুসলমানদের মধ্যে চিন্তাধারার যে অধঃপতন শুরু হয়, সেই দৃষ্টিকোণ থেকে এ আশা ছিল না যে, ফের কোনও (মুসলিম) চিন্তাবিদ, সূক্ষ্মদর্শী ও গবেষক জন্ম নিবেন। কিন্তু মহান কুদরতের আপন যাদুর শক্তি দেখানোর ইচ্ছা ছিল। শেষ যুগে যখন ইসলামের প্রাণ ওষ্ঠাগত, ঠিক তখন শাহ ওয়ালীউল্লাহ (র)-এর মত ব্যক্তিত্বের শুভজন্ম হয়, যার বিচক্ষণতার সামনে ইমাম গাযালী (র), রাযী (র) ইবনে রূশদ (প্রমুখ ব্যক্তিত্ব) -এর কৃতিত্বও ম্লান হয়ে যায়।’
আরেকটু সামনে লিখেন- ‘শাহ সাহেব ইলমে কালাম বা দর্শন শাস্ত্রের শিরোনামে কোনও রচনা লিখেননি। সে দৃষ্টিকোণ থেকে তাকে দার্শনিকদের কাতারে শামিল করা বাহ্যতঃ উচিত নয়। কিন্তু তার রচিত ‘হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা’, যাতে তিনি শরীয়তের তত্ত্বভেদ বর্ণনা করেছেন, বস্তুতঃ কালাম শাস্ত্রের উজ্জ্বল প্রাণ।’
সমকালীন চিন্তাবিদ মাওলানা আবদুল হক হক্কানী (তাফসীরে হাক্কানী ও আকাঈদুল ইসলাম রচয়িতা) হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা -এর অনুবাদ গ্রন্থ ‘নি’মাতুল্লাহিস সাবিগাহ’ -এর ভূমিকায় লিখেন- ‘যে শাস্ত্রে এই গ্রন্থনা, তাঁর (শাহ সাহেব) পূর্বে একত্রে কেউ তা সন্নিবেশিত করেনি। এ শাস্ত্রের বিষয়বস্তু শরীয়তে মুহাম্মদী (স)-এর ব্যবস্থাপনা من حيث المصلحة و المفيدة (উপকারী সংস্কারের দৃষ্টিকোণে)। আর তার লক্ষ্য-উদ্দেশ্য হচ্ছে, মানুষ যেন স্পষ্ট জেনে নেয়- আল্লাহ ও তার রাসূল (স)-এর হুকুম-আহকামের মধ্যে কোন সংকীর্ণতা নেই; আর না তা সুস্থ স্বভাবরীতির পরিপন্থী। যেন সেগুলোর উপর মানুষের পরিপূর্ণ আস্থা জন্মে। সেগুলোকে প্রকৃতির উপর নির্ভরশীল জ্ঞান করে মন সেদিকে আকৃষ্ট হয়। কোনও সন্দিগ্ধতার অজুহাতে মনের মধ্যে সংশয় না জাগে। এর সংজ্ঞা হচ্ছে- এটি সেই ইলম, যাতে ধর্মীয় আইন-কানুন ও শরয়ী আহকামের সূক্ষ্মতা-প্রজ্ঞা জানা যায় আর এর উৎস তার সকল ইলম।’
অনুবাদঃ আবু সাঈদ মুহাম্মদ উমর।