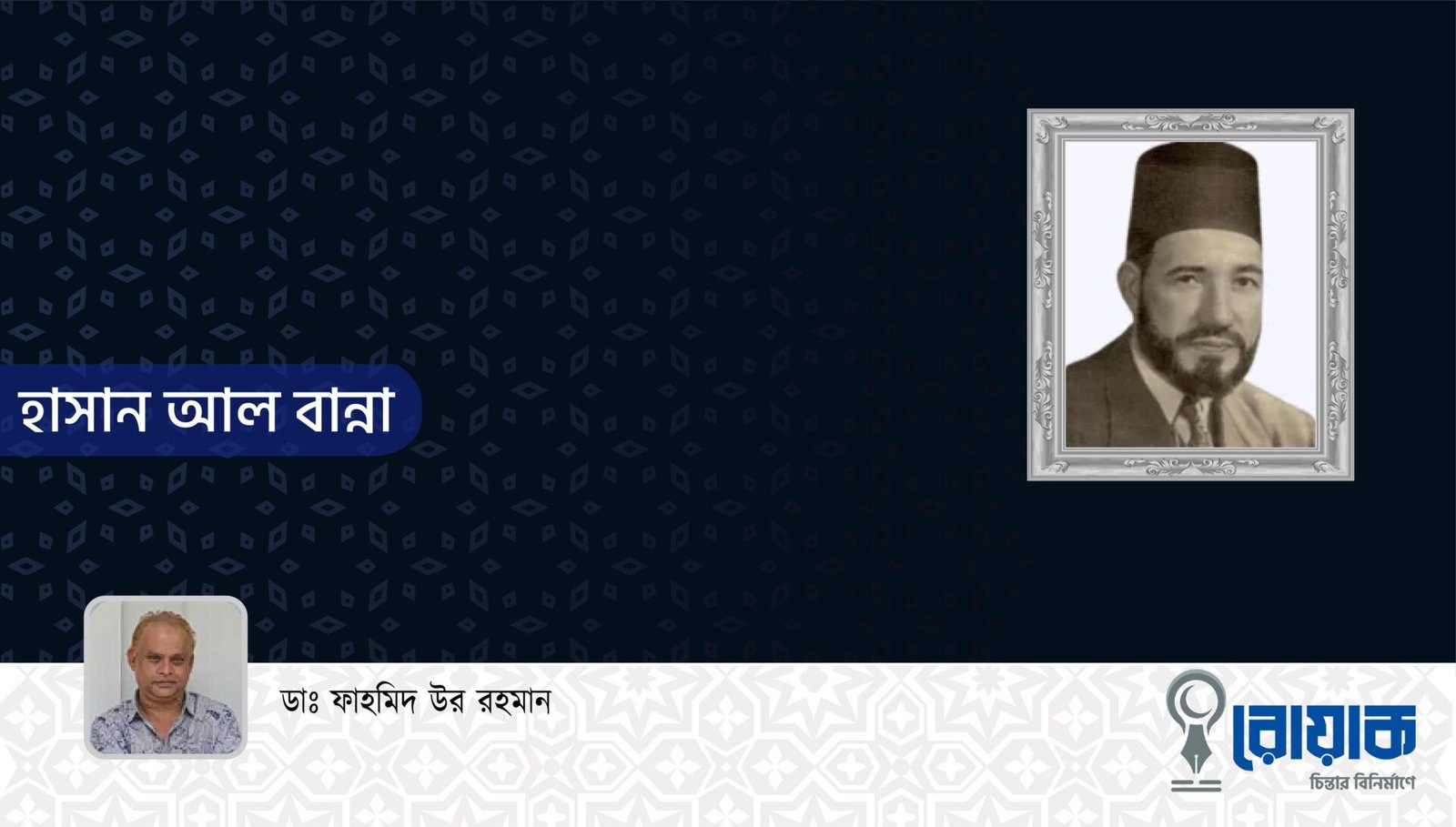এক
১৯২৮ সালে মাত্র ২২ বছর বয়সে তরুণ স্কুল শিক্ষক হাসান আল বান্না একালের সবচেয়ে প্রভাবশালী মুসলিম পুনর্জীবনবাদী সংগঠন ইখওয়ানুল মুসলেমুন (মুসলিম ভ্রাতৃসংঘ, ইংরেজিতে Muslim Brotherhood) প্রতিষ্ঠা করেন। তখন পর্যন্ত ইসলামী ব্যবস্থার সংস্কার এবং সমাজের চালিকাশক্তি হিসেবে ইসলামের প্রধান ভূমিকা পালনের চিন্তাভাবনা কিছু শিক্ষিত মানুষের মনে আবেদন সৃষ্টি করলেও এটি কখনোই গণআন্দোলনে পরিণত হয়নি। এর আগে আফগানী, আবদুহু, রশিদ রিদার মত মানুষেরা একই লক্ষ্যে লড়াই করেছিলেন, মুসলিম ভাবজগতে তারা অসাধারণ প্রভাব ফেলেছিলেন এ সব কথা সত্য, কিন্তু তাদের সেসব লড়াই ছিল অনেকটা ব্যক্তিগত পর্যায়ের। এটি কখনো রাজনৈতিক আন্দোলনের রূপ নেয়নি। হাসান আল বান্নাই এই এলিটিস্ট, বুদ্ধিবৃত্তিক প্রবণতাকে জনপ্রিয় আন্দোলনে পরিণত করেন, যা কিনা মিসর ছাড়িয়ে মুসলিম দুনিয়ার সর্বত্র রাজনীতিতে ইসলামের ভূমিকাকে গুরুত্বপূর্ণ করে তোলে।
বিশ শতকের শেষে এবং একুশ শতকের প্রথম পাদে এসে তাই আমরা দেখি বান্নার চিন্তাভাবনায় উজ্জীবিত রাজনৈতিক নেতা ও প্রতিষ্ঠানগুলো আলজেরিয়া, তিউনেসিয়া, মিসর, জর্ডান, সুদান, ফিলিস্তিন ও মুসলিম দুনিয়ার অন্যত্র রাজনৈতিক ক্ষমতা অর্জনের পথে এগুচ্ছে এবং সমাজে ও রাষ্ট্রে ইসলামের ভূমিকাকে এখন আর কেউ অস্বীকার করতে পারছে না। এইসব বিশিষ্ট চিন্তাভাবনাকে জনপ্রিয় করা, একটি সাংগঠনিক কাঠামোর মধ্যে তা ধারণ করা এবং আকর্ষণীয় নেতৃত্বের চমকে পুরো মিসরীয় জাতিকে জাগিয়ে দেয়া ও তার পরিকল্পনার পক্ষে একদল নিবেদিত ও আন্তরিক মানুষের নিশিদিন কাজ করে যাওয়ার প্রেরণা সৃষ্টিতে তিনি তুলনাহীন নজির সৃষ্টি করেছেন। মার্কস এক জায়গায় লিখেছিলেন: Philosophers have tried to understand the world. Our problem is to change it. মার্কসের লেখালেখির সাথে বান্নার যোগাযোগ হয়েছিল কিনা তা জানা না গেলেও মার্কস কথিত এ মন্তব্যের সার্থক ও কার্যকরী নমুনা হচ্ছেন হাসান আল বান্না। তিনি যথার্থ অর্থে বুঝতে পেরেছিলেন মিসর তথা পুরো মুসলিম দুনিয়া ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদের নিগড়ে আটকা পড়েছে এবং এর হাত থেকে পরিত্রাণ পেতে হলে মুসলিম সমাজকে ঘুরে দাঁড়াতে হবে।
বলাবাহুল্য বান্না আমাদের সেই ঘুরে দাঁড়ানোর পথটিই দেখিয়েছেন। তিনি যখন তার আরাধ্য কর্মসূচী নিয়ে অগ্রসর হন তখন মিসর ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের করতলধৃত। এর রাজনীতি ও অর্থনীতির নিয়ন্ত্রকও তারা। এই নিয়ন্ত্রণের পাশাপাশি মিসর তখন ইউরোপীয় সাংস্কৃতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক আগ্রাসনেরও চারণক্ষেত্র। অন্যদিকে সেখানকার ধনী ও অভিজাত শ্রেণী ইউরোপীয় প্রথা-পদ্ধতি নির্বিচারে আত্মস্থ করতে উন্মুখ। এইরকম রাজনৈতিক অর্থনৈতিক সাংস্কৃতিক আগ্রাসন স্বাভাবিকভাবেই মিসরীয় জনমানসকে আঘাত করে। ফলে সেখানে এক ধরনের সাম্রাজ্যবাদবিরোধী জাতীয়তাবাদী আন্দোলন গড়ে ওঠে। মিসরে বিশ শতকের প্রথম দিককার এসব জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের একজন জনপ্রিয় নেতা ছিলেন সাদ জগলুল এবং তার নেতৃত্বে মিসরের আজাদীর লড়াই শুরু হয়।
বান্নার স্মৃতিকথা থেকে জানা যায় খুব অল্প বয়স থেকে তিনি এই সব ব্রিটিশবিরোধী মিছিল সমাবেশে সোৎসাহে অংশ নিতেন১। বান্নার শৈশবের মিসরীয় রাজনৈতিক পরিবেশ, সাম্রাজ্যবাদ আধিপত্যবাদবিরোধী আজাদীর লড়াই, সবমিলিয়ে তার ভবিষ্যৎ মানসিক গঠন ও দৃষ্টিভঙ্গি নির্মাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।
বিশেষ করে বিংশ শতাব্দীর বিশ ও ত্রিশের দশকে মিসরের রাজনৈতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক জগতে ব্যাপক ধর্মনিরপেক্ষকরণ (Secularization) শুরু হয় এবং রেস্টুরেন্ট, নাইটক্লাব, সিনেমা প্রভৃতির মাধ্যমে মিসরীয় সমাজে ইউরোপীয় জীবনধারা অনুপ্রবেশের চেষ্টা চলে। মিসরের সেক্যুলার লেখকরা সেখানকার প্রাক ইসলামী ফেরাউনের যুগের মধ্যে এক জাতীয় আত্মপরিচয় আবিষ্কার করার চেষ্টা করে এবং এই সেকুলার মিসরীয় জাতীয়তাবাদ সেখানকার সমাজ থেকে ইসলামের শক্তিশালী ভূমিকাকে প্রান্তিক অবস্থানে ঠেলে নেওয়ারও চেষ্টা চালায়। নতুন এই সংস্কৃতি মুষ্টিমেয় অথচ ক্ষমতাশালী পাশ্চাত্য প্রভাবিত শহুরে শিক্ষিত শ্রেণীর মনের ক্ষুধা পূরণ করলেও মিসরীয় সাধারণ জনমানসের মধ্যে এর কোন প্রাসংগিকতা ছিল না।
এই সব সেক্যুলার আধুনিকতাবাদীরা ইউরোপীয় সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠত্বে বিশ্বাস করতো এবং এটিকে মিশরীয় জনসমাজে জনপ্রিয় করে তোলার চেষ্টা করতো। স্বাভাবিকভাবে তারা তুরস্কের মোস্তফা কামালের খেলাফত বিলোপের ঘটনায় আহাদিত হয় এবং এটিকে ধর্মনিরপেক্ষকরণের পক্ষে বিরাট বিজয় হিসেবে চিহ্নিত করে। রাজনীতির জগতের পাশাপাশি তারা যুক্তি দেখাতো মুসলমানদের উচিত এ যুগের বৈজ্ঞানিক সংস্কৃতিকে আত্মস্থ করা। তারা ঐতিহ্যবাহী মুসলিম সমাজে মেয়েদের অবস্থানকেও বদলে ফেলতে আগ্রহী হয় ও তাদের পর্দাকে বাতিল করার জন্য ওকালতি করে। ইসলামী সংস্কৃতি প্রভাবিত মিসরীয় সমাজে সেক্যুলার ও আধুনিকতাবাদীদের এই সব কর্মসূচী যেমন সাধারণ জনমানসকে আহত করতে থাকে তেমনি খ্রিস্টান মিশনারীদের ইসলামবিরোধী তৎপরতা ও সমালোচনাও বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে।
এই সব ঘটনা হাসান আল বান্নাকে প্রভাবিত করে বিশেষ করে পশ্চিমা সেক্যুলার সংস্কৃতি যেভাবে মিসরীয় ইসলামী সংস্কৃতিকে হুমকির মুখে ফেলে দিয়েছিল তা তার শংকা বাড়িয়ে দেয়। এমনি এক আবহাওয়ায় বান্না তার কাজ শুরু করেন, কর্মকৌশল ঠিক করেন, বিকল্প উত্তরণের পথ প্রস্তুত করেন এবং তার নেতৃত্বের গুণপনায় অচিরেই চলমান মিসরীয় স্রোতের ধারা ঘুরতে শুরু করে। মিসরীয় সমাজে ইসলাম প্রান্তিক অবস্থান থেকে পুনরায় মধ্যমঞ্চে এসে হাজির হয়। অবশ্য এর আগেই জাতীয়তাবাদী সেকুলার আন্দোলনগুলো ও তার নেতৃত্ব দুর্নীতি, ক্ষমতার দ্বন্দ্ব ও কখনো কখনো সাম্রাজ্যবাদের আচল ধরা চরিত্রের কারণে ব্যাপক মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্যতাও হারিয়ে ফেলেছিল। ফলে এই শূন্যতা পূরণে ইসলাম এগিয়ে আসে এবং হাসান আল বান্না এটিকে একটি মতাদর্শিক কাঠামোর মধ্যে নিয়ে এসে পশ্চিমের সেক্যুলার সংস্কৃতির জন্য এক চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দেন।
দুই
হাসান আল বান্না ১৯০৬ সালে মিসরের রাজধানী কায়রোর ৯০ মাইল উত্তর-পশ্চিমে মাহমুদিয়া নামক ক্ষুদ্র শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা ছিলেন পেশাগতভাবে একজন ঘড়ি মেরামতকারী, একই সাথে স্থানীয় মসজিদের ইমাম। তিনি আল আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ের মুফতী আবদুহুর তত্ত্বাবধানে কিছুদিন লেখাপড়া করেন এবং পরে ইসলামী ন্যায় ও আইন শাস্ত্রের উপর কিছু বইও লেখেন। বান্না তাই শৈশব থেকেই এক সংস্কারমুখী ধর্মীয় পরিবেশে বেড়ে ওঠেন। পিতার মত তিনিও ঘড়ি মেরামতের কাজ শেখেন, পাশাপাশি ধর্মীয় শিক্ষায় তার হাতে খড়ি হয়। বার বছর বয়সে তিনি একটি সরকারি প্রাথমিক স্কুলে ভর্তি হন। এ সময় তিনি কয়েকটি ধর্মীয় ও সামাজিক সংগঠনের সাথেও জড়িয়ে পড়েন, যাদের উদ্দেশ্য ছিল ইসলামী নীতিকে কার্যকরি করে এক সামাজিক বিশুদ্ধতা আনয়ন। তবে তের বছর বয়সে বান্নার হাসাফিয়া সুফী ধারার সাথে সংযোগ ঘটে এবং এই যোগাযোগ বান্নার জীবনে বড় রকমের প্রভাব ফেলে। পরবর্তীকালে সংস্কার ও রাজনীতির পাশাপাশি তিনি সবসময় ব্যক্তিজীবনে এক মিস্টিক অন্তর্লীনতাকে লালন করে গেছেন। মনের দিক দিয়ে তিনি সবসময় ছিলেন একজন সুফী: Banna was a sufi and throughout his life the spiritual exercises and ites of sufism remained important to him২।
হাসাফিয়া সুফী ধারাটি ছিল শরীয়াহর অনুগত এবং বান্নার কাছে এটি পছন্দনীয় ছিল এই কারণে যে এই ধারা কখনো ইসলাম নির্ধারিত সীমানাকে অতিক্রম করেনি। বান্না এই সুফী ধারাটির একটি দাতব্য প্রতিষ্ঠানের সম্পাদক হিসেবেও কিছুদিন কাজ করেন যার উদ্দেশ্য ছিল সামাজিক নৈতিকতার স্থানকে রক্ষা করা এবং এতিমদের সাহায্য করে খ্রিস্টান মিশনারীদের প্রভাবকে খর্ব করা। সুফীবাদী প্রবণতার কারণেই পরবর্তীকালে বান্না তার হাতে গড়া প্রতিষ্ঠান ইখওয়ানুল মুসলেমুনের নেতা ও কর্মীর পারস্পরিক সুসম্পর্কের উপর জোর দিয়েছিলেন। তিনি তার স্মৃতিকথায় জানিয়েছেন কিভাবে তার এক শিক্ষক মুরশিদ ও সাগরেদের মধ্যকার আধ্যাত্মিক ও মানবিক সম্পর্ককে ঘনিষ্ঠ করার বিষয়াদি নিয়ে আলোচনা করেছিলেন। সুফীবাদের সাথে সংযোগের ফলে তার নিজেরও সুফীদের প্রতি প্রবল দুর্বলতা ছিল। সুফীদের তিনি কখনও সমালোচনা করেননি। তিনি বরং সুফীবাদ থেকে ভ্রান্ত সুফীদের বিদআতমূলক কার্যকলাপের সংশোধনের উপর জোর দিয়েছেন৩।
বান্না যেমন সুফীদের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন তেমনি তরুণ বয়সে ইমাম গাজ্জালীর লেখা পড়েও বিমোহিত হন। গাজ্জালীর লেখা পড়ে তিনি একটা জিনিস বুঝতে পারেন শিক্ষার মানে নিজের স্বার্থবুদ্ধি দ্বারা পরিচালিত হওয়া নয় বরং জীবনকে কল্যাণকর পথে পরিচালনার চেষ্টা করা। ১৯২৩ সালে ১৭ বছর বয়সে বান্না মাহমুদিয়া ত্যাগ করেন এবং কায়রোর শিক্ষক প্রশিক্ষণ বিদ্যালয় দার-উল-উলুমে আরবী শিক্ষক হিসেবে প্রশিক্ষণের জন্য আসেন।
রাজধানী কায়রোতে এসে স্থানীয় হাসাফিয়া সুফীদের সাথে তার যোগাযোগ ও সখ্যতা হয়। ফলে নতুন পরিবেশে তাকে মানিয়ে নিতে কষ্ট হয় না। কায়রো থাকাকালে বান্না রশিদ রিদার সালাফিয়া আন্দোলনের কর্মীদের প্রতিষ্ঠিত লাইব্রেরীতে ঘন ঘন যেতেন এবং তার সম্পাদিত আল মানারের তিনি ছিলেন একনিষ্ঠ পাঠক। এ সময় তার রশিদ রিদা ও মুফতী আবদুহুর অন্যান্য ছাত্রদের খুব কাছে থেকে দেখারও সুযোগ হয়।
কায়রোয় পাঁচ বছর অবস্থানকালে রাজধানীর কোলাহলের পাশে মিসরের প্রতিদ্বন্দ্বী রাজনৈতিক দলগুলোর কাড়াকাড়ি ও প্রতিযোগিতার ছবিও তার নজরে আসে। বিশেষ করে মিসরীয় সমাজের পশ্চিমীকরণ যাকে তিনি অনৈতিকতা ও নাস্তিকতার সাথে তুলনা করেছেন কায়রোয় বসে খুব কাছে থেকে তা বোঝার চেষ্টা করেন। অনেক মুসলমানের মত এ সময় কামাল আতাতুর্কের খেলাফত উচ্ছেদ ও তুরস্ককে ধর্মনিরপেক্ষ করার চেষ্টাকে তিনি উদ্বেগের সাথে পর্যবেক্ষণ করেন। ১৯২৫ সালে মিসরে একটি সেক্যুলার জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার আন্দোলনকে তিনি তুরস্কের মত ইসলাম পরিত্যাগের পূর্বলক্ষণ হিসেবে চিহ্নিত করেন। তিনি পত্র পত্রিকা সাময়িকীগুলোতে নিরন্তরভাবে পশ্চিমী সেক্যুলার মূল্যবোধ সম্পন্ন লেখালেখির বিষয়টিও শংকার সাথে দেখতে থাকেন। এই পরিস্থিতি বান্না ও তার সহগামীদের বেদনাসিক্ত করে দেয়: Banna and his friends were moved almost to tears by the political and social confusion in city8.
কিন্তু বেদনা বান্নার উদ্যমকে কেড়ে নিতে পারেনি। তিনি এরি মধ্যে কাজ চালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। তিনি কায়রোয় দার-উল-উলুম, আল আজহার, আইন বিদ্যালয় ও সালাফিয়া লাইব্রেরীতে অনেক সমমনাদের সন্ধান পান যারা তারই মত কিছু একটা করার চিন্তাভাবনা করছিলেন। নতুন পরিচিতদের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ছিলেন আল আজহারের পন্ডিত শায়খ ইউসুফ আল দিজভী, যিনি ইসলামের পুনর্জীবনের জন্য একটি সংগঠন খাড়া করেছিলেন। বান্না তার স্মৃতিকথায় লিখেছেন দিজভী তার কাছে স্বীকার করেন তার সংগঠন ব্যর্থ হয়েছে এবং আল আজহারের উলামারাও পশ্চিমী সংস্কৃতির স্রোতকে আটকাতে পারেননি। তিনি বান্নাকে ইসলামের সাথে সংশ্লিষ্ট থেকে এ অবস্থায় ব্যক্তিগত মুক্তির চেষ্টার পরামর্শ দেন। তরুণ বান্না দিজভীর এই হাল ছেড়ে দেয়া মানসিকতার সমালোচনা করেন এবং দিজভীকে মুসলিম জনগণের শক্তির উপর নির্ভর করার আহ্বান জানান৫। বান্নার কর্মোদ্যোগের প্রথম নমুনা হচ্ছে কায়রোতে বসে ইয়ং ম্যানস মুসলিম এসোসিয়েশেন (YMMA) প্রতিষ্ঠা। এই সংগঠনটি প্রতিষ্ঠায় তাকে সহযোগিতা করেন সিরীয় বুদ্ধিজীবী মুহিব আল দীন আল খতিব।
খতিব কায়রোয় সালাফিয়া লাইব্রেরীর পরিচালক ছিলেন এবং নিয়মিতভাবে তিনি সংস্কারধর্মী ‘আল ফাতহ’ পত্রিকা প্রকাশ করতেন। ১৯২৭ এর নভেম্বরে প্রতিষ্ঠিত এই সংগঠনটির উদ্দেশ্য ছিল ইসলামের নীতির কাছে ফিরে গেয়ে মুসলিম সমাজের ভিতরে জাগরণ সৃষ্টি করা। এই কারণে এটি ইসলামী নৈতিকতা, মুসলিম সংহতি ও আধুনিক প্রযুক্তি আয়ত্ত করার উপর বিশেষ জোর দেয়। অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনের জন্য YMMA স্কুল প্রতিষ্ঠা করে, সেমিনার-সিম্পোজিয়াম সংগঠন করে, পত্র-পত্রিকা প্রকাশ করে, সমাজে ইসলামবিরোধী নীতি-নৈতিকতার বিরুদ্ধে আওয়াজ তোলে এবং বহু দাতব্য সংস্থা, ব্যাংক ও সমবায়ী প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলে। অচিরেই এর শাখা মিসরের বিভিন্ন স্থানে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং মধ্যপ্রাচ্যের অন্যান্য জায়গায় যেমন ফিলিস্তিন, সিরিয়া ও ইরাকেও স্থাপিত হয়। স্পষ্টতঃই এই সংগঠনটি নতুন ধরনের সংস্কার কার্যক্রম নিয়ে অগ্রসর হয় যার উপর ভিত্তি করে কয়েক মাস পর হাসান আল বান্না ইখওয়ানুল মুসলেমুন–মুসলিম ভ্রাতৃসংঘ প্রতিষ্ঠা করেন৬।
কায়রোয় অবস্থানের শেষ দিকে এসে বান্না একটি প্রবন্ধ লেখেন যেখানে তিনি স্কুল শিক্ষক ও সুফী শায়খদের সামাজিক ভূমিকার তুলনামূলক বিশ্লেষণ করেন। তিনি সুফীদের আন্তরিকতা, শৃঙ্খলা ও আত্মত্যাগের প্রশংসা করলেও জীবনবিমুখতার জন্য তাদের সামাজিক ভূমিকা যে সীমিত হয়ে আসছে তাও তিনি উল্লেখ করেন। অন্যদিকে শিক্ষকরা তাদের শিক্ষকতা পেশার মাধ্যমে মানুষের কাছাকাছি পৌঁছতে পারেন এবং এইভাবে শিক্ষকরা সুফীদের চেয়ে এগিয়ে আছেন, বিশেষ করে বান্নার মত হচ্ছে তারা ইচ্ছা করলে মিসরীয় যুব সমাজকে পশ্চিমী সংস্কৃতির কবল থেকে উদ্ধার করে ইসলামের দিকে ফিরিয়ে আনতে পারেন। বান্না ঘোষণা দেন তার লক্ষ্য হচ্ছে দিনের বেলায় ছাত্রদের পড়িয়ে এবং রাতে ক্লাস, বক্তৃতা ও প্রচার কাজ চালিয়ে মিসরীয়দের ইসলামের দিকে ফিরিয়ে আনা৭।
এই প্রবন্ধ থেকে পরিষ্কার হয় তিনি সুফীবাদী ধারা থেকে একটু একটু করে সরে এসে শিক্ষকতার পেশাকে বেছে নিয়েছিলেন। যদিও তিনি শেষ পর্যন্ত কোন নির্দিষ্ট সুফী ধারার সাথে যুক্ত ছিলেন না, কিন্তু তিনি পরবর্তীকালে ইখওয়ানুল মুসলেমুনের মধ্যে কিছু সুফীবাদী প্রবণতাকে প্রবেশ করিয়েছিলেন, যেমনঃ শায়খের প্রতি আনুগত্য, খোদার স্মরণ, ধর্মীয় কর্তব্যের যথাযথ অনুসরণ। বান্না কখনোই সুফীদের খোদার সাথে ব্যক্তিগত সম্পর্কের ব্যাপারটাকে অস্বীকার করেননি। তিনি বরং এই সম্পর্ককে একটি সাংগঠনিক কাঠামোর মধ্যে নিয়ে আসেন।
দার-উল-উলুম থেকে গ্রাজুয়েশন করার পর ১৯২৭ সালে শিক্ষা মন্ত্রণালয় বান্নাকে আরবী শিক্ষক হিসেবে ইসমাইলিয়ার একটি প্রাথমিক স্কুলে নিয়োগ দেন। এই ইসমাইলিয়াতেই সুয়েজ খাল কোম্পানীর তৎকালীন সদর দফতর অবস্থিত ছিল এবং যেখানে ব্রিটিশরা মজবুতভাবে খুঁটি গেড়ে বসেছিল। ব্রিটিশ ও অন্যান্য বিদেশীদের স্থানীয় জনগণের ব্যাপারে কোন আগ্রহ ছিল না কিন্তু স্থানীয় অর্থনীতি ও জনগণের প্রয়োজনীয় বিষয়গুলোর তারা নিয়ন্ত্রক বনে গিয়েছিল। বান্না বিশেষ করে বিদেশী ও মিসরীয়দের জীবন যাপনের নিদারুণ বৈষম্যে আহত হন এবং মিসরীয়দের দূরবস্থা তাকে আকুল করে দেয়: He was shamed by the contrast between the luxurious homes of the British and the miserable hovels of the Egyptian workers.৮ বান্না তার জনগণের ভাগ্য পরিবর্তনের জন্য যা কিছু করা দরকার তা জানতেন। তিনি ভাল করে বুঝেছিলেন জাতীয়তাবাদ কিংবা ইউরোপের সাথে মিসরের সম্পর্ক বিষয়ক উচ্চমার্গের আলোচনা এই মুহূর্তে একেবারে অর্থহীন, কেননা জনগণের বিরাট অংশ সিদ্ধান্তহীনতা ও নীতিহীনতায় ভুগছে। তার দৃষ্টিতে এর থেকে পরিত্রাণের একমাত্র পথ হলো জনগণকে কুরআন ও সুন্নাহর নীতির দিকে ফিরে আসা। তিনি তার আশেপাশের নিকটজন ও বন্ধুবান্ধবদের বুঝান।
তাদেরকে নিয়ে স্কুলে, মসজিদে, কফি হাউসে ছোট ছোট বৈঠক করে তার বিশিষ্ট চিন্তাভাবনা প্রচারের চেষ্টা করেন। তিনি তার শ্রোতাদের বলেন পশ্চিমের প্রভাব এবং সাম্প্রতিক রাজনৈতিক পরিবর্তন তাদেরকে একেবারে লন্ডভন্ড করে দিয়েছে এবং তাদের ধর্ম থেকে তারা সরে এসেছে। ইসলাম ঠিক পশ্চিমের কোন আদর্শ বা ভাবধারার মত নয়। এটি একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা এবং এটিকে যদি আবার মুসলমানরা পুরোপুরি আঁকড়ে ধরে তবে বিদেশীদের দ্বারা উপনিবেশিত হওয়ার আগের গতি ও শক্তি তারা ফিরে পাবে। উম্মাহকে শক্তিশালী করতে হলে তাদেরকে অবশ্যই তাদের মুসলিম আত্মার পুনরাবিষ্কার করতে হবে। যদিও তিনি ছিলেন বয়সে তরুণ, তবুও তিনি সবার ভিতর একটা স্বপ্ন ও অনুরণন সৃষ্টি করেন। তিনি ছিলেন বলিষ্ঠ মনের, ব্যক্তিত্ববান ও মানুষকে উজ্জীবিত করার শক্তিসম্পন্ন। অধ্যাপক রিচার্ড পি. মিচেল একটা ঘটনার কথা স্মরণ করেছেন ১৯২৮ সালের মার্চ মাসের এক সন্ধ্যায় ইসমাইলিয়াতে কর্মরত ৬ জন স্থানীয় ব্যক্তি তার কাছে এসে একটা কিছু করা দরকার বলে জানালেন:
We know not the practical way to reach the glory of Islam and to serve the welfare of the Muslims. We are weary of this life of humiliation and restriction. So we see that the Arabs and the Muslims have no status and no dignity. They are not more than mere hirelings belonging to foreigners. We possess nothing but this blood and these souls… and these few coins. We are unable to percieve the road to action as you percieve it, or to know the path to the service of the fatherland, the religion and the Ummah as you know it.৯
এই আবেদনে বান্না অভিভূত হয়ে যান। তিনি ও তার আগন্তুকরা একসাথে শপথ নেন যে তারা ইসলামের বাণী প্রচারের সৈনিক (জুনদ) হবেন। সেই রাতে ইখওয়ানুল মুসলেমুনের জন্ম হয়। এইভাবে ক্ষুদ্র অবস্থা থেকে ইখওয়ানের প্রসার ঘটতে থাকে। ১৯৪৯ সালে আল বান্নার মৃত্যুর সময় পর্যন্ত ইখওয়ান গোটা মিশর জুড়ে ২০০০ শাখা গড়ে তুলেছিল। প্রতিটি শাখায় ৩,০০,০০০ থেকে ৬,০০,০০০ পর্যন্ত সদস্য ছিল। এটি মিসরীয় সমাজের সর্বস্তরের প্রতিনিধিত্বশীল সংগঠন হয়ে উঠেছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ইখওয়ান মিসরীয় রাজনৈতিক মঞ্চে সবেচেয়ে শক্তিশালী সংগঠন হিসেবে আবির্ভূত হয়। বান্না সাফল্যের সঙ্গে ইসলামকে একটি বৈপ্লবিক শক্তিতে রূপান্তরিত করেছিলেন। সাইয়েদ কুতুব ১৯৫৩ সালে এই দলে যোগদান করেন এবং নেতা হন।
ইখওয়ান সম্বন্ধে নেতিবাচক যাই বলা হোক না কেন বান্না সবসময় বলেছেন ক্ষমতা দখল কিংবা অভ্যুত্থানের কোন ইচ্ছা তার নেই। ইখওয়ানের প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে ইসলামের প্রকৃত শিক্ষার প্রচার। তার কথা ছিল জনগণ যখন ইসলামের বাণী আত্মস্থ করবে এবং সেই আলোকে নিজের ও সমাজের সংস্কার করে নেবে জাতি তখন কোন রকম সশস্ত্র পদ্ধতি ছাড়াই ইসলামী রঙে রঙ্গিন হয়ে উঠবে। শুরুতে বান্না তার কর্মসূচী বাস্তবায়নের জন্য ৬ দফা পরিকল্পনা করেন। যার মধ্যে আফগানী, আবদুহু ও রিদার সালাফিয়া আন্দোলনের কর্মসূচীগত ঐক্য দেখা যায়। বান্না মূলতঃ ছিলেন এদের ভাবশিষ্য এবং এদের চিন্তাধারাকেই তিনি কার্যকর করার চেষ্টা করেছিলেন মাত্র। তার পরিকল্পনাগুলো ছিল এ রকম:
- ১. যুগোপযোগিতার ভিত্তিতে কুরআনের নীতিকে ব্যাখ্যা করা,
- ২. মুসলিম জাতি ও দেশসমূহের ঐক্য,
- ৩. মুসলমানদের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন এবং ইনসাফভিত্তিক সামাজিক ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলা,
- ৪. অশিক্ষা ও দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে লড়াই,
- ৫. উপনিবেশিক শক্তির হাত থেকে মুসলিম দেশগুলোর আজাদী,
- ৬. শান্তি ও ইসলামী ভ্রাতৃত্বের বন্ধন দৃঢ় করা।১০
বান্না কখনোই চাননি ইখওয়ান একটি র্যাডিকাল প্রতিষ্ঠানে পরিণত হোক। তার প্রধান লক্ষ্য ছিল মুসলিম সমাজের মৌলিক সংস্কার যা কিনা দীর্ঘ ঔপনিবেশিক শাসনের ফলে বিধ্বস্ত ও শিকড় বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছে ১১।
মিসরীয়রা বান্নার ভাষায় ঔপনিবেশিক শাসনের কারণে হীনম্মন্যতায় ভুগছে এবং ইউরোপীয়দের চেয়ে অধঃস্তন মনে করতে শুরু করেছে। কিন্তু বান্নার কথা হলো এরকম মনে করার কোন কারণ নেই। কারণ মিসরীয়দেরও চমকপ্রদ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য বর্তমান যা কিনা আমদানিকৃত যে কোন মতাদর্শের চেয়ে উজ্জ্বল ১২।
তাদের ফরাসী কিংবা রুশ বিপ্লবের থেকে কিছু ধার করার দরকার নেই কেননা রসুল (স.) ১৩০০ বছর আগে সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতা, ইনসাফ, সামাজিক সুবিচার প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দিয়েছেন১৩।
শরীয়াহ আইন যেভাবে মধ্যপ্রাচ্যের সামাজিক আবহাওয়ায় কাজ করবে, বিদেশী আইন সেভাবে কাজ করবে না। জনগণ যতক্ষণ অন্যদের অনুকরণ করতে থাকবে ততক্ষণ তারা সাংস্কৃতিকভাবে এক শংকর প্রজাতি হয়ে থাকবে১৪।
তিন
হাসান আল বান্না ভাল করে বুঝতে পেরেছিলেন মুসলমানের আজাদী ও মর্যাদা পুনরুদ্ধারের কোন সহজ রাস্তা নেই। এর একটাই পথ ইসলামকে ভিত্তি করে তাদের আত্মপরিচয়কে পুনরাবিষ্কার এবং তাদের ব্যক্তি ও সামাজিক জীবনের পুনঃনির্মাণ করতে হবে। এই কারণে বান্না বছরের পর বছর ধরে পর্যবেক্ষণ, পর্যালোচনা ও আত্মসমালোচনার মাধ্যমে ইখওয়ানকে একটি মজবুত, গতিশীল ও আধুনিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলার চেষ্টা করেন এবং এর কর্মীদের চূড়ান্ত আত্মত্যাগ করবার জন্য প্রস্তুত করেন। আধুনিক ইসলামী আন্দোলনের ক্ষেত্রে বান্নার সবচেয়ে বড় অবদান হচ্ছে কার্যোপযোগী সংগঠন গড়ে তোলা এবং কাজের মাধ্যমে একটা মডেলকে তুলে ধরা। কায়রোর দার-উল-উলুমে ছাত্রাবস্থার অভিজ্ঞতা থেকে তিনি বুঝেছিলেন পূর্বতন সংস্কারকদের যথেষ্ট আন্তরিকতা থাকা সত্ত্বেও তারা কোন কার্যকরী পন্থা বা সংগঠন গড়ে তুলতে পারেননি। ইসলামী সংস্কারের লক্ষ্যে পূর্বতন পথিকৃৎদের আরদ্ধ কাজকে তিনি গণসংগঠন গড়ে তোলার মাধ্যমে সমাধা করার চেষ্টা করেছেন।
মার্কিন পন্ডিত ও ঐতিহাসিক অধ্যাপক রিচার্ড মিশেল ইখওয়ানুল মুসলেমুনের উপর প্রথম শ্রেণীবদ্ধভাবে কাজ করেছেন এবং ইখওয়ানকে নিয়ে তার গুরুত্বপূর্ণ বইয়ের নাম হচ্ছে: The Society of Muslim Brothers। এখানে তিনি ইখওয়ান সম্পর্কে বলেছেনঃ
the first mass supported and organized, essentially urban-oriented effort to cope with the plight of Islam in the Modern world. ১৫
অধ্যাপক মিশেল ১৯৫৩-৫৪ সালে যখন ইখওয়ানের উপর নাসের সরকারের জুলুম নেমে আসে এবং তাদের মামলাগুলোর বিচার চলে তখন তিনি প্রায় দেড় বছর ধরে ইখওয়ানের সমাবেশ-প্রোগ্রামে অংশগ্রহণ করেন এবং দেখে অবাক হন সমাজের বিভিন্ন শ্রেণী ও পেশার মানুষ কিভাবে এই দলটির সাথে নিজেদেরকে একাত্ম করে ফেলেছে। পশ্চিমের কেতাদুরস্ত সুট-প্যান্ট পরিহিত এবং পশ্চিমী শিক্ষায় শিক্ষিত লোক থেকে শুরু করে ছাত্র, রাজকর্মচারী, শিক্ষক, কেরানী, অফিসের নিম্নপদস্থ কর্মচারী, স্থপতি, প্রকৌশলী, হিসাবরক্ষক, ব্যাংকার, সাংবাদিক সবাই ইখওয়ানের সাথে জড়িত ছিল। অধ্যাপক মিশেল দেখতে পান প্রথমদিকে ত্রিশের দশকে ইখওয়ানের সাথে গ্রামের খেটে খাওয়া এবং চল্লিশের দশকে শহুরে নিম্নবিত্ত মানুষেরা সম্পৃক্ত হয়। কিন্তু সেই সব কর্মীরা যারা ইখওয়ানের রাজনৈতিক ভাগ্যকে নির্ধারণ করতেন তারা ছিলেন মূলত শহরে মধ্যবিত্ত শিক্ষিত শ্রেণী। অধ্যাপক মিশেলের কাছে মনে হয়েছে ইখওয়ানের এই আন্দোলন হচ্ছে:
An effort to reinstitutionalize religious life for those whose commitment to the tradition and religion is still great, but who at the same time are already effectively touched by the forces of Westernization; a movement which not only sought to imbue the present with some sense of the past terms meaningful for the present.১৬
ইখওয়ানের নেতৃত্বের মধ্যবিত্তীয় প্রেক্ষাপট দলটির নীতি ও আদর্শ নির্মাণেও বড় ভূমিকা রেখেছে। যেমন: বিদেশী ও তার দেশীয় এজেন্ট (ইহুদী ও খ্রিস্টান) কর্তৃক মিসরীয় অর্থনীতি নিয়ন্ত্রণের বিরোধিতা, সাম্রাজ্যবাদের সহযোগী শাসক গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে লড়াই, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে শ্রেণী সংগ্রামের বিরোধিতা, কর্তৃপক্ষ ও শ্রমিক, জমির মালিক ও কৃষকদের মধ্যে সহযোগিতার পরিবেশ সৃষ্টি করা ইত্যাদি। তারপরেও ১৯৩০ ও ৪০ এর দশকে মিসরের শিল্প-কলকারখানার মালিক ছিল মূলতঃ বিদেশীরা। সেইসব জায়গায় ইখওয়ান শ্রমিকদের শোষণের বিরুদ্ধে পক্ষ নেয় এবং মিশরীয় শ্রম আন্দোলনে একটি বিরাট ভূমিকা রাখে। কোন কোন জায়গায় তারা ইউনিয়নকেও নিয়ন্ত্রণ করে।
এটা সত্য প্রথম দিকে ইখওয়ান নৈতিক ও সামাজিক সংস্কারের কথা বললেও পরবর্তীতে ব্রিটিশ আধিপত্যের মোকাবিলা ও তাদের জায়নবাদীদের পক্ষে ন্যাক্কারজনক ভূমিকার বিরোধিতা করতে গিয়ে এটি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়। ইখওয়ান ফিলিস্তিনকে মনে করতো The heart of the Arab World, the knot of the Muslim peoples এবং জেরুজালেমকে দেখতো ইসলামের Third of the Holy places হিসেবে। ১৯৩৬-৩৭ সালে ফিলিস্তিনে আরবদের বিদ্রোহ ও ধর্মঘটের সময় ইখওয়ান তাই সর্বাত্মকভাবে সহযোগিতা করে এবং ১৯৪৮ সালে ইসরাইলের সাথে যুদ্ধের সময় মিসর সরকারের যুদ্ধ ঘোষণার আগেই ইখওয়ান স্বেচ্ছাসেবক পাঠিয়ে সহযোগিতা করে। ১৯৪৩ সালে হাসান আল বান্না তার অনুসারীদের উদ্দেশ্যে এক বক্তৃতায় উল্লেখ করেছেন: My Brothers, you are not a benevolent society, nor a political party, nor a local organization having limited purposes. Rather, you are a new soul in the heart of this nation to give it life by means of the Koran…১৭
এটা সত্য ইখওয়ান কোন প্রচলিত রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান ছিল না বরং প্রচলিত রাজনীতির দলাদলিকে তারা মনে করতো এটা খামখা জাতিকে বিবদমান গ্রুপে বিভক্ত করছে। এর ঐক্যবদ্ধ শক্তি বরং ইসলামের স্বার্থে ব্যবহার করা যেতো। সাংবাদিক এডওয়ার্ড মর্টিমার এই ব্যাপারটি খেয়াল করে লিখেছেন:
But Brotherhood was not the old style of political party consisting of a handful of notables- land lords or intellectuals who got together to plan a conspiracy or put up a slate for elections. It was a mass organization, bearing some charecteristic marks of the decade in which it developed-the 1930s. It sought to organize not only the political opinions of its followers but their entire way of life.১৮
১৯৩২ সালে ইসমাইলিয়া থেকে কায়রো বদলী হয়ে আসার পর বান্না পুরো মিসর জুড়ে শক্ত সাংগঠনিক কাঠামো গড়ে তোলেন। ১৯৩৮ সালে তিনি কাজের সুবিধার জন্য ইখওয়ানকে তিনটি ব্যাটেলিয়নে বিভক্ত করেন। একটি শ্রমিকদের, একটি ছাত্রদের অন্যটি ব্যবসায়ী ও সরকারি কর্মকর্তাদের জন্য। ১৯৪৩-এ এসে তিনি ব্যাটেলিয়নকে ফ্যামিলিতে (আল উসরা) বিভক্ত করেন। প্রত্যেকটি উসরার ১০ জন সদস্য নিয়ে আবার একটি ইউনিট তৈরি হতো। উসরা ছিল ইখওয়ানের ক্ষুদ্রতম প্রশাসনিক ও আধ্যাত্মিক ভাগ। প্রত্যেকটি উসরা ব্যাটেলিয়নের তত্ত্বাবধানে সদর দফতরের নির্দেশের অধীন পরিচালিত হতো। উসরার সদস্যরা প্রতি সপ্তাহে মিলিত হতো। নামাজ, জিকর, আত্মশুদ্ধি, আত্মসমালোচনা ও আধ্যাত্মিকতার চর্চা করতো এবং ইসলামী নীতিবিরুদ্ধ সুদ, জুয়া, মদ, ব্যভিচার প্রভৃতি থেকে দূরে থাকার তাগিদ দেয়া হতো।
ইখওয়ানের এই ‘পরিবারের’ ধারণা এমন সময় মুসলমানের পারস্পরিক সম্পর্ক, সহানুভূতি, সহমর্মিতা, সাহায্য ও সংহতির উপর জোর দিয়েছিল যখন নাকি আধুনিকায়নের ধাক্কায় মিসরের ঐতিহ্যবাহী সমাজগুলো ভেঙ্গে যাচ্ছিল। বান্না মনে করতেন এই ইসলামী নৈতিকতার উজ্জীবনের মাধ্যমে কেবল মুসলিম জনসাধারণের কাছে আধুনিক প্রতিষ্ঠান ও সংস্কার অর্থবহ হতে পারে।
একটি পর্যায়ে বান্না ইখওয়ানের মাধ্যমে মিসর জুড়ে মসজিদ, মাদ্রাসা, স্কুল, হাসপাতাল, ক্লিনিক, রোভার স্কাউট, ক্ষুদ্র শিল্প প্রভৃতি সমাজ সেবামূলক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন এবং মানব কল্যাণের ক্ষেত্রে ইখওয়ানের কর্মীরা অপূর্ব দৃষ্টান্ত স্থাপন করে। রোভাররা দরিদ্রদের স্বাস্থ্য শিক্ষার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। ইখওয়ান আধুনিক ট্রেড ইউনিয়ন গড়ে শ্রমিকদের স্বার্থের পক্ষে, তাদের উপর মালিকদের শোষণের বিরুদ্ধে কথা বলে। ইখওয়ানের শত্রুরা বান্নাকে অভিযোগ করতো তিনি রাষ্ট্রের ভিতর আরেকটি রাষ্ট্র গড়ে তুলছেন। আসলে বান্না কাজের মাধ্যমে তথাকথিত জাতীয়তাবাদী সরকারগুলোর ব্যর্থতাকে খুলে ধরেন এবং জনগণের মণিকোঠায় জায়গা নিয়ে নেন।
সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে পন্ডিতেরা যাই দাবি করুন না কেন ইখওয়ান সাফল্যজনকভাবে দেখিয়ে দিয়েছিল মিসরীয়রা ধার্মিক থাকতে চায় এবং ধর্মীয় জাতীয়তাবাদকেই পছন্দ করে। ইখওয়ান এটিও প্রমাণ করেছিল ইসলাম একটি প্রগতিশীল আদর্শ। তারা ইসলামের কথা বলেছিল কিন্তু সপ্তম শতাব্দীতে প্রত্যাবর্তন করতে চায়নি। এই কারণে তারা সৌদি আরবের ওহাবীদের কুরআন শরীফের আক্ষরিক ব্যাখ্যার পরিবর্তে কুরআনের নীতির ভিত্তিতে একালের সমস্যার সাথে বুঝতে চেয়েছিল। যদিও তখন পর্যন্ত ইখওয়ান একটি সুস্পষ্ট ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থার মডেল গড়ে তুলতে পারেনি তবু তারা এটা মনে করতো কুরআন ও সুন্নাহভিত্তিক রাষ্ট্র ব্যবস্থায় সম্পদের সুষম বন্টন ও ইনসাফ ভিত্তিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হবে। তাদের ধারণা ইসলামের প্রথম যুগের মত শাসকরা নির্বাচিত হবেন, পূণ্যবান খলিফাদের মত শাসকরা জনগণের কাছে জবাবদিহি করবেন, স্বৈরাচারী কায়দায় দেশ চালাবেন না। কিন্তু বান্না অনুভব করতেন ইসলামী রাষ্ট্র নিয়ে আলোচনা এই মুহূর্তে অনর্থক। কেননা অনেক মৌলিক কাজকর্ম ও প্রস্তুতি শেষ হয়নি। তবে বান্না এ কথাটা প্রায়ই বলতেন মিসরকে ইসলামী হতে দেয়াটাই স্বাভাবিক কাজ হবে। যেমন রুশীয়রা কমিউনিজমকে এবং পাশ্চাত্য গণতন্ত্রকে গ্রহণ করেছে। যে দেশের অধিকাংশ মানুষ মুসলমান সেখানে জনগণ চাইলে ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা হওয়াটাই স্বাভাবিক১৯।
১৯৪০-এর দশক ছিল মিসরের জন্য ক্রান্তিকাল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, উদারনৈতিক, সেকুলার, গণতন্ত্রী রাজনীতিবিদদের ব্যর্থতা সর্বোপরি ইসরাইলের কাছে ১৯৪৮ সালে আরবদের অপমানজনক পরাজয় সর্বত্র হতাশার গ্লানি সৃষ্টি করেছিল। ব্রিটিশ বা জাতীয়তাবাদী রাজনীতিবিদরাও মিশরে আধুনিক রাষ্ট্র ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে ব্যর্থ হয়েছিল, কারণ দেশটি চরিত্রগতভাবে এই ধরণের ব্যবস্থাকে ধারণ করতে প্রস্তুত ছিলনা। ওয়াফদ পার্টির মতো জনপ্রিয় রাজনৈতিক দলও বারবার নির্বাচিত হয়ে ব্রিটিশ কিংবা রাজার ষড়যন্ত্রে ক্ষমতা থাকতে পারত না। পরে ১৯৪২ সালে ওয়াফদ ব্রিটিশদের সাথে আঁতাত করে ক্ষমতায় যাওয়ায় তার জনপ্রিয়তাও পড়তে থাকে। এরকম অবস্থায় মিসরের রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনকারী ইখওয়ান মিসরের সমস্যা হিসেবে বৃটেনকে চিহ্নিত করে ব্রিটিশ বিরোধী লড়াই শুরু করে। কারেন আর্মস্ট্রং লিখেছেন এরকম হতাশাজনক পরিস্থিতিতে যেহেতু ইখওয়ানের আবেদন ছিল সাধারণ জনগণের কাছে তাই এটি কারো কারো কাছে হয়ে উঠেছিল anti-intellectual, defensive, self righteous.২০ এই পরিস্থিতিতে সবার অজান্তে ইখওয়ানের ভিতর থেকে একটি ক্ষুদ্র সশস্ত্র দল বেরিয়ে আসে যারা সম্ভবতঃ দ্রুত কিছু করে দেখাতে চাচ্ছিল। এই দলটির কথা ইখওয়ানের সাধারণ কর্মীরা আদৌ জানত না, যাদের সামনে মিসরের রাজনৈতিক ও আধ্যাত্মিক সংস্কারই ছিল মুখ্য। বান্না এ ধরনের উদ্যোগের কথা কখনো জানতে পারেননি এবং তিনি এ ধরনের কাজকেও কখনো সমর্থন জানাননি। এই সশস্ত্র দলটির কার্যকলাপ ইখওয়ানকে কলঙ্কিত করে, পরিণতিতে তার বিপর্যয়ের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এই দলটির একজন প্রধানমন্ত্রী মোহাম্মদ আল নূরকাশীকে হত্যা করে, যে ঘটনাকে বান্না তীব্র ভাষায় নিন্দা করেন। নতুন প্রধানমন্ত্রী ইব্রাহীম আবুল হাদী জনপ্রিয় ইখওয়ানকে ধ্বংসের এই সুবর্ণ সুযোগ হাতছাড়া করতে চাননি যা কিনা মিসরীয় রাজনীতিতে অত্যন্ত শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল। অচিরেই ইখওয়ানের সদস্যদের উপর সরকারের জুলুম, নিবর্তন, হুলিয়া নেমে আসে এবং পরিশেষে রাজা ফারুকের গুপ্ত বাহিনীর পরিকল্পনায় ১৯৪৯ সালের ১২ ফেব্রুয়ারি রাস্তার উপর বান্নাকে গুলি করে শহীদ করা হয়। সত্য কথা বলতে কি বান্নার ইন্তেকালের ফলে ইখওয়ানের নেতৃত্বের যে শূন্যতা সৃষ্টি হয় এটি তা আর কখনো কাটিয়ে উঠতে পারেনি।
চার
হাসান আল বান্না তার পূর্বসূরী জামাল আল দীন আল আফগানী ও মুফতী আবদুহুর মত বিশ্বাস করতেন ইসলাম থেকে দূরে মরে যাওয়ার কারণে ইউরোপীয় আধিপত্যের সামনে মুসলমানরা নতজানু হয়ে পড়েছে। মুসলমানদের এই দুরবস্থা দূর করতে হলে তাই আজ দরকার কুরআন ও সুন্নাহর নীতির কাছে প্রত্যাবর্তন করা যার উদাহরণ প্রথম যুগের মুসলমানরা (যাদেরকে সালাফ বলা হয়েছে) পেশ করেছিলেন। রসুলুল্লাহ (সা.) ও তার পূণ্য খলিফাদের (রাশিদুন) পর যে সব শাসকরা এসেছেন তাদের সময় নানা কারণে ইসলাম দুর্বল হয়ে যায়, যেমন: ক্ষমতার দ্বন্দ্ব, তুচ্ছ বিষয় নিয়ে ধর্মীয় বিবাদ, জনগণের প্রতি শাসকদের দায়িত্বে অবহেলা, ভোগবিলাসে মত্ত হয়ে পড়া, প্রাযুক্তিক বিদ্যায় অনাগ্রহ এবং পূর্বতন কর্তৃত্বের অন্ধ অনুকরণ (তাকলীদ)। ত্রয়োদশ শতকের মধ্যে এই সব কার্যকারণের ফলে মুসলিম দুনিয়া মঙ্গোল ও ক্রুসেডের আগ্রাসনের শিকার হয়। যদিও পরবর্তীকালে এ অবস্থা মামলুক ও অট্যোম্যানরা কিছুটা ঘুরানোর চেষ্টা করে কিন্তু তারা ইউরোপের বৈজ্ঞানিক ও রাজনৈতিক অগ্রগতিকে উপেক্ষা করে। এই উপেক্ষোর ফলে আঠার-উনিশ শতকের মধ্যে মুসলিম দুনিয়া ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদীদের কাছে পুরোপুরি পদানত হয়। এই রাজনৈতিক পরাজয়ের পথ ধরেই মুসলিম দুনিয়ায় ইউরোপীয় সাংস্কৃতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক আগ্রাসন শুরু হয়। বান্না ইউরোপের জড়বাদী সংস্কৃতিকে নাস্তিকতা ও নীতিহীনতার সাথে তুলনা করেছেন। তিনি বলেছেন সাম্রাজ্যবাদীরাই সুদ, মদ ও উলঙ্গপনার সংস্কৃতি নিয়ে এসেছে এবং এর ফলে মুসলমানের ভিতরে সৃষ্টি হচ্ছে হীনম্মন্যতা। মিসরের বর্তমান রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক বিপর্যয়ের জন্য তারাই দায়ী। এই বিপর্যয়কে রুখতে হলে ইসলামকে সামনে নিয়ে আসতে হবে। ইসলামের আবির্ভাব হয়েছে ১৩০০ বছর আগে এটা সত্য কিন্তু বান্না মনে করেন এটা এমন একটা ব্যবস্থা যার নীতিকে স্থান কাল নির্বিশেষে কার্যক্ষমভাবে ব্যবহার করা যাবে।
বান্না তার স্বল্পায়ু জীবনে ইখওয়ানের সাংগঠনিক শক্তি বৃদ্ধিতে সময় দিয়েছিলেন বেশি। এ কারণে তার চিন্তাভাবনাগুলোকে লিপিবদ্ধ করার তেমন একটা সময় তিনি পাননি। বিভিন্ন সময় দেয়া তার বক্তৃতা, বিবৃতি ও কিছু লেখালেখি থেকে আমরা তার বিশিষ্ট চিন্তা সম্বন্ধে ধারণা পাই।
বান্না কুরআন ও সুন্নাহর উপর মুসলমানদের দৃঢ় থাকার ব্যাপারে জোর দিয়েছিলেন এই কারণে যে, তারা ইসলামের সাথে সামঞ্জস্যশীল এক জীবন গড়ে তুলবে, কোন ধর্মীয় কর্তৃত্বের আনুগত্যের জন্য নয়।
বান্না মনে করতেন ইসলামের মধ্যে অনেক অনাচার, কুসংস্কার ঢুকে পড়েছে, এর পরিশুদ্ধি প্রয়োজন। কুরআন ও সুন্নাহর নীতি বিরুদ্ধ কোন কিছু ইসলামে গ্রহণযোগ্য হবে না। পীরপূজা সম্বন্ধে তিনি বলেছেন কোন সৎকর্মশীল ব্যক্তির সৎকাজের জন্য আমরা দোয়া করতে পারি, শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করতে পারি কিন্তু ব্যক্তির কোন অলৌকিক ক্ষমতা আছে এ ধরনের বিশ্বাস ভুল। আবার এ রকম বিশ্বাস নিয়ে কবর জিয়ারত করাও ইসলাম অনুমোদন করে না।
ইসলামী রাষ্ট্র সম্বন্ধে বলতে গিয়ে তিনি তিনটি নীতির কথা বলেছেন: (১) শাসককে খোদার নীতির আওতায় জনগণের কাছে জবাবদিহি করতে হবে। (২) মুসলিম দেশসমূহকে একত্রে কাজ করতে হবে কেননা ইসলামী ভ্রাতৃত্ব ইসলামী বিশ্বাসের অংশ। (৩) মুসলমান জনগণ শাসকের কাজকর্ম তত্ত্বাবধান করবে, প্রয়োজনে পরামর্শ দেবে এবং সেটি কার্যকরী হচ্ছে কিনা তাও নজর রাখবে।
এই নীতির আওতায় ইসলামী রাষ্ট্র সংসদীয় কিংবা রাষ্ট্রপতি ব্যবস্থা যে কোনটাই অনুসরণ করতে পারে। সুদূরপ্রসারী লক্ষ্য হিসেবে তিনি খেলাফতের পুনর্জীবনের কথা বলেছেন। তিনি মন্তব্য করেছেন এই ভাবে মুসলিম দেশগুলোর মধ্যে সহযোগিতা, সম্প্রীতি, চুক্তি, জোট, এমনকি ইসলামী জাতিসংঘও গড়ে ওঠা অবিচিত্র কিছু নয়২১। তিনি এ কথাও বলেছেন সাংবিধানিক সরকারই হচ্ছে ইসলামী সরকারের নীতির সবচেয়ে কাছাকাছি। তিনি সাংবিধানিক সরকারের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা, সংসদীয় পরামর্শ, জনগণের প্রতি শাসকের দায়বদ্ধতার ব্যাপারগুলোর প্রশংসা করেছেন।
সংসদীয় ব্যবস্থাকে তিনি প্রশংসা করলেও ইসলামী রাষ্ট্রের জন্য তিনি বহুদলীয় ব্যবস্থাকে অনুমোদন করেননি। মিসরীয় অভিজ্ঞতা থেকে তিনি বুঝেছিলেন বহুদলীয় ব্যবস্থা জাতীয় ঐক্যকে বিভক্ত করে ফেলে যা ইসলাম সমর্থন করতে পারে না। তিনি বরং ইসলামী নীতির আওতায় বিভিন্ন ব্যক্তির মতান্তরকে সমর্থন করেন, বহুদলীয় ব্যবস্থা বাতিল করার সুপারিশ করেন এবং একটি মাত্র দল তৈরি করে জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠার উপর জোর দেন। নির্বাচন জনগণের মতকে প্রতিফলিত করলেও মিসরীয় অভিজ্ঞতা মোটেই সুখকর ছিল না। যোগ্য লোকেরা চলমান ব্যবস্থায় নির্বাচিত হয়ে আসতে পারতো না। এই কারণে তিনি নির্বাচনী আইন সংশোধনের সুপারিশ করে বলেন প্রার্থীদের যোগ্যতা পূর্বেই নির্ধারিত করে দিতে হবে। বিশেষ করে ইসলামী আইন ও সামাজিক সমস্যাগুলো যুগপৎভাবে যিনি ভাল করে বোঝেন তাকেই নির্বাচনে প্রার্থী হওয়া উচিত। নির্বাচনের সময় ব্যক্তিগত আক্রমণকেও তিনি নিষিদ্ধ করার সুপারিশ করেন।
ইসলামী রাষ্ট্রের দায়িত্ব সম্বন্ধে বলতে গিয়ে তিনি বলেছেন এটি নিরাপত্তা, জনগণের সম্পত্তি রক্ষা, আইনের শাসন, শিক্ষা বিস্তার, জনকল্যাণ, নৈতিক উন্নয়ন, মুসলিম দেশসমূহের আত্মরক্ষা ও ইসলামের প্রচার-প্রসারে (দাওয়াহ) কাজ করবে। ধনী দরিদ্রের ব্যবধান কমিয়ে আনা, বেকারত্ব দূর করা, শ্রমিকের অধিকার নিশ্চিত করাও এ সরকারের কাজ। বিশেষ করে ইসলামী রাষ্ট্রকে জাতীয় অর্থনীতি গড়ে তুলতে হবে। বান্না বলেছেন মিসরকে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বৃটেনের আধিপত্যকে ভাঙ্গতে হবে। প্রয়োজনে বিদেশী মালিকানাধীন ব্যবসা-বাণিজ্যের কথা তিনি জাতীয়করণের কথা বলেছিলেন। যে সরকার এই দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হবে তার ক্ষমতায় থাকার অধিকার নেই। প্রয়োজনে এই রকম সরকারকে অপসারণ করতে হবে।
বান্না তার সেক্যুলার সমালোচকদের উত্তরে একবার বলেছিলেন জাতীয়তাবাদ যদি দেশপ্রেম হয় তাহলে ইসলামী নীতির দিক দিয়ে কোন আপত্তি নেই। কিন্তু জাতীয়তাবাদের উদ্দেশ্য যদি হয় প্রাক ইসলামী মূল্যবোধের পুনর্জীবন তাহলে সেটা গ্রহণযোগ্য নয়।
বান্না তার পূর্বসূরীদের থেকে এগিয়ে এসে তার ইসলামী সংস্কার পরিকল্পনার মধ্যে অর্থনৈতিক ও সামাজিক সুবিচারের ব্যাপারটিও গুরুত্বের সাথে তুলে ধরেছিলেন। তিনি মিসরীয়দের দারিদ্র্য, বেকারত্ব, স্বল্প আয়, অপুষ্টি, অস্বাস্থ্য, বিদেশী কোম্পানীগুলোর একচেটিয়া দখলদারিত্ব ও শোষণের বিষয়গুলো নিয়ে গভীরভবে চিন্তা করেছিলেন। বিশেষ করে সামাজিক বিষয়গুলো নিয়ে পশ্চিমী আদর্শের তরফ থেকে ইসলামের দিকে যে চ্যালেঞ্জ ছুটে আসছিল তার মোকাবিলার কথাও তিনি ভাবছিলেন। তার কাছে মনে হয়েছিল মুসলিম দুনিয়া এখন প্রতিদ্বন্দ্বী অর্থনৈতিক মতাদর্শগুলোর সংঘাতের ভিতরে ওঠানামা করছে এবং প্রত্যেকটির প্রবক্তরা মুসলমানদের নানা প্রলোভনে তাদের সাথে কাজ করার আহবান জানাচ্ছে। তিনি নাজীদের শৃঙ্খলা ও আনুগত্যের প্রশংসা করলেও তাদের বর্ণবাদের তীব্র সমালোচনা করেন। তিনি কমিউনিস্টদের আন্তর্জাতিক চেতনা ও শ্রেণীহীন সমাজের ধারণার প্রতি ইতিবাচক মনোভাব দেখান কিন্তু তাদের ধর্মহীনতা তার পছন্দ হয়নি। পুঁজিবাদ সম্পর্কে তিনি বলেন এটি গণতন্ত্র ও ব্যক্তি স্বাধীনতার কথা বললেও অর্থনৈতিক শোষণ ও অনৈতিকতাকে দূর করতে পারেনি। সুতরাং বান্নার কথা হলো মুসলমানদের বিদেশী কোন আদর্শের কাছে হাত পাতার দরকার নেই। কেননা ইসলামের মধ্যেই পূর্ণাঙ্গ একটি ব্যবস্থা বহাল রয়েছে।
সবশেষে বান্নার মত হলো ইসলামী রাষ্ট্রকে একটি ইসলামী সংস্কৃতিও গড়ে তুলতে হবে। সেই সংস্কৃতি পশ্চিমের নীতিহীনতাকে মুছে ফেলবে এবং কুরআনী আইনকে সমাজ জীবনে প্রতিষ্ঠা করবে। তার ভাষায়:
….by converting Muslims to true Islam (Sharia-minded sufism) and reshaping their personalities, eventually a purely Muslim society would develop and then transform the state. ২২
পাঁচ
আমাদের বোঝা দরকার একজন গভীর তাত্ত্বিক হিসেবে নয় বরং জনপ্রিয় বাস্তববাদী রাজনৈতিক নেতা হিসেবে হাসান আল বান্না কাজ শুরু করেছিলেন। তাই ঘটনা ও অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে তিনি তার চিন্তাভাবনার উন্মেষ ঘটিয়েছেন। মোহাম্মদ আবদুহু ও রশিদ রিদা যেভাবে তাদের বুদ্ধিবৃত্তিক চিন্তাভাবনাগুলোকে বিশ্লেষণ করেছেন, বান্নার সহজ সরল আলোচনার মধ্যে তা পাওয়া যাবে না। কিন্তু একদিক দিয়ে এটি বলা যায় আবদুহু ও রিদার চিন্তাভাবনাগুলোকে ব্যবহার করে তিনি গণআন্দোলনের জন্ম দিয়েছিলেন। ইখওয়ানুল মুসলেমুন প্রতিষ্ঠা করে তিনি একালে মুসলিম দুনিয়ার জন্য একটি মডেল তৈরি করে গেছেন।
আবদুহু ও রিদার সাথে তার আর একটা পার্থক্য লক্ষ্যণীয়। এরা দুজন মূলতঃ ঐতিহ্যবাহী ধর্মীয় শিক্ষায় শিক্ষিত ছিলেন। বান্না ধর্মীয় শিক্ষার পাশাপাশি আধুনিক বিষয়াদির সাথেও পরিচিত হয়েছিলেন। ফলে মুসলিম সমাজের সমস্যা বিশ্লেষণে তিনি আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি ও ভাষার ব্যবহার করেছেন। পাশ্চাত্যের আধিপত্যের প্রেক্ষিতে পশ্চিমের পন্ডিতরা তাদের অবস্থান থেকে মুসলিম সমাজকে বরাবর অনগ্রসর হিসেবে বিবেচনা করেছেন এবং এই অনগ্রসরতার ধারণা রাজনীতি, অর্থনীতি, সংস্কৃতি প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে বিস্তারিত হয়েছিল। বান্না মুসলিম সমাজের এই অনগ্রসরতার সামাজিক দিক নিয়ে পরীক্ষা করার চেষ্টা করেছেন এবং মুসলিম সমাজতত্ত্ব খাড়া করেছেন, অন্যদিকে ব্যক্তিগত পর্যায়ে মুসলিম মনস্তত্ত্ব তৈরী করেছেন। আধুনিকতার সংসর্গে মুসলিম সমাজে যে দ্বন্দ্ব ও প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছিল তার প্রেক্ষিতে বান্নার আলোচনা অত্যন্ত আধুনিক এমনকি তার সময় থেকে অগ্রগামী। এই অগ্রগামীমনস্তত্ত্ব তৈরি করে তিনি মুসলিম সমাজকে ইউরোপীয় আধিপত্যের বিরুদ্ধে লড়াই করার সাহস যুগিয়েছেন। সম্ভবত বান্নার সাফল্য এখানেই।
গ্রন্থঋণঃ
১. Hasan al-Banna, Memoirs of Hasan al-Banna Shaheed. Karachi International Islamic Publishers, 1981.
২. Richard P. Mitchell, The Society of the Muslim Brothers, New Work Oxford University Press, 1969.
৩. Banna, Memoirs.
৪.Mitchell, Society of Muslim Brothers.
৫. Banna, Memoirs.
৬. David Commins, ‘Hasan al-Banna in Ali Rahnema, ed., Pioneers of Islamic Revival. London: Zed Books Ltd., 1994.
৭. Banna, Memoirs.
৮. Mitchell, Society of Muslim Brothers.
৯. প্রাগুক্ত।
১০. Karen Armstrong, The Battle for God. New York: The Random House Publishing Group, 2000.
১১. Mitchell, Society of Muslim Brothers.
১২. প্রাগুক্ত।
১৩. প্রাগুক্ত।
১৪. প্রাগুক্ত।
১৫. প্রাগুক্ত।
১৬. প্রাগুক্ত।
১৭. প্রাগুক্ত।
১৮. Edward Mortimer, Faith and Power: The Politics of Islam. London: Faber and Faber, 1982.
১৯. Mitchell, Society of Muslim Brothers.
২০. Karen Armstrong, The Battle for God.
২১. Commins, ‘Hasan al-Banna’
২২. প্রাগুক্ত।