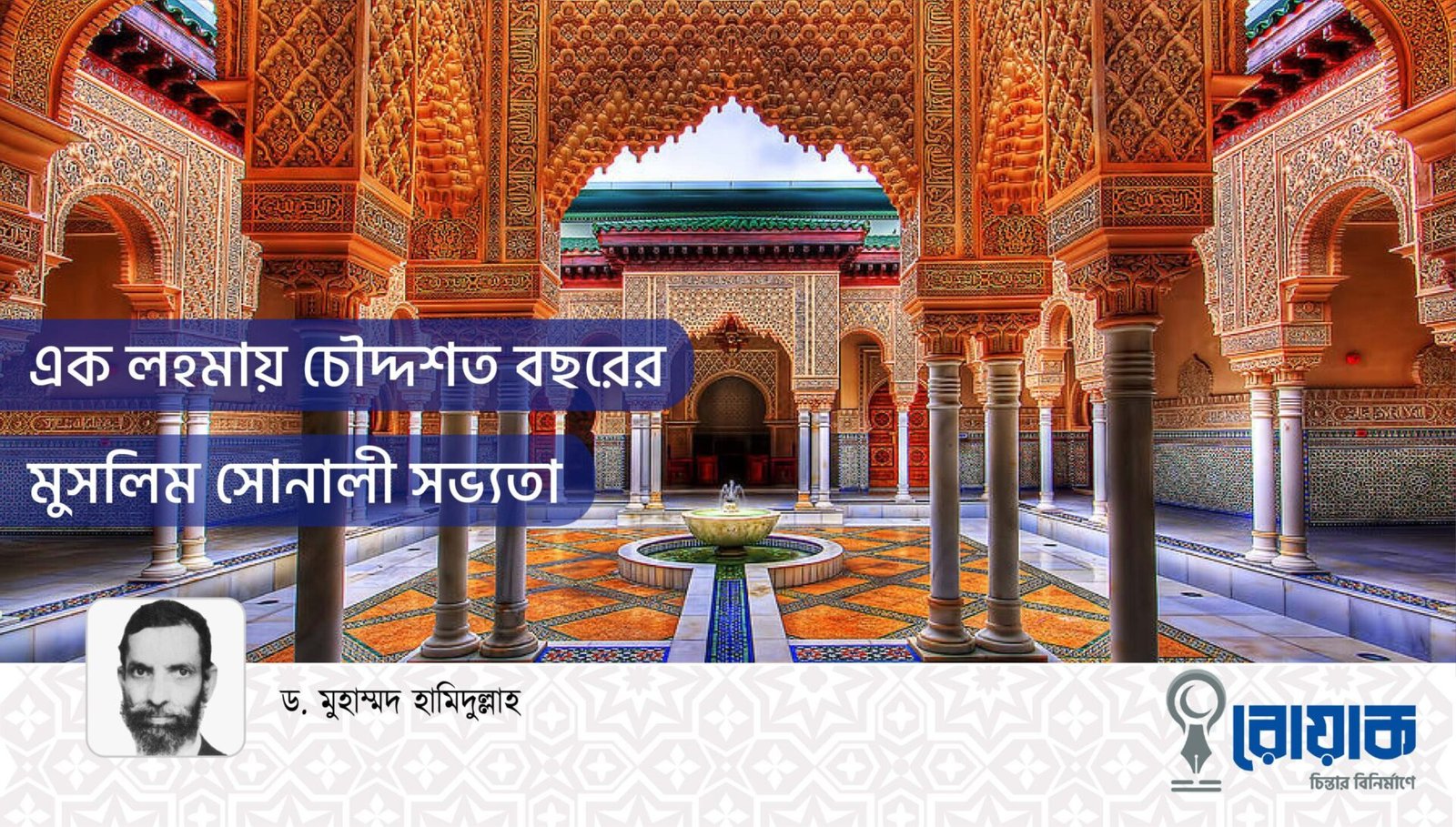ইসলামের ইতিহাস বলতে সাধারণত বিগত চৌদ্দোশত বছরের ইতিহাস বোঝানো হয়। সুবিশাল এই ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাগুলোর সারাংশ আঁকা হয়েছে আলোচ্য প্রবন্ধটিতে।
💠আল খিলাফাতুর রাশিদাহ
হযরত মুহাম্মাদ (সা.) ৬৩৪ খ্রিস্টাব্দে (১১হিজরি) মৃত্যুবরণ করেন। ইসলাম নামক একটি ধর্মকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য এবং প্রায় শূন্য থেকেই একটি রাষ্ট্রের ভিত্তি গড়ে তোলার জন্য জীবনের শেষ ২৩ বছরে তিনি অক্লান্ত পরিশ্রম করে গিয়েছিলেন, এতে তিনি সফলও হয়েছিলেন। মাত্র ১০ বছরের সংক্ষিপ্ত একটি সময়ে মদীনার অভ্যন্তরীণ ছোট্ট একটা শহর থেকে এই রাষ্ট্রটির যাত্রা শুরু হয়েছিলো। ইরাক-ফিলিস্তিনের দক্ষিণাঞ্চল থেকে শুরু করে সম্পূর্ণ আরব উপদ্বীপে এটিই ছিলো একমাত্র রাষ্ট্রীয় প্রশাসন ব্যবস্থা। এছাড়াও, তাঁর মহান এই কর্মকাণ্ডকে এগিয়ে নেবার জন্য কয়েক লক্ষ সাহাবী রেখে গিয়েছিলেন তিনি, যারা ছিলেন দক্ষ, সুযোগ্য এবং এই কাজের জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।
নবুয়তের এমন অসাধারণ প্রভাব, প্রতিপত্তি ও প্রতিফলন বিশ্ব-দরবারে উন্মোচিত হবার ফলে আশপাশের কয়েকটি স্থানে কয়েকজন ভণ্ডনবীর উদ্ভব হয়। ঘটনাগুলো সংঘটিত হতে শুরু করেছিলো মুহাম্মাদ (সা.) এর ওফাতের পূর্বমুহূর্তে। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁরই সুযোগ্য উত্তরসূরী প্রথম খলিফা হযরত আবু বকর (রা.) এ’সব ভণ্ডনবীদের দমন করার জন্য বেশ কয়েকটি সেনাবাহিনী গঠন করেন। কারণ, নবী (সা.) এর মৃত্যুর সংবাদ এবং আবু বকর (রা.) এর সেনাবাহিনী প্রস্তুতের সংবাদ পেয়ে সব ভণ্ডনবীই একত্রিত হতে শুরু করেছিলো। তবুও, তাদের শেষ রক্ষা হয়নি।
রাসূল (সা.) এর মৃত্যুর সময় তৎকালীন বিশ্বের সর্ববৃহৎ দু’টি পরাশক্তি রোম-পারস্যের সাথে যুদ্ধাবস্থা বিরাজ করছিলো।
বার্তাবহনের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক মূলনীতি হলো, দূতকে হত্যা করা আইনত দণ্ডনীয় অপরাধ। তথাপি, বাইজেন্টাইন এলাকায় একজন মুসলিম দূতকে হত্যা করা হলে রোম সম্রাট কায়সার যথাযথ ব্যবস্থা তো নেয়নি, উপরন্তু মুহাম্মাদ (সা.) এর দেয়া বিকল্প প্রস্তাবগুলোর প্রতিও ভ্রুক্ষেপ করেনি। ফলশ্রুতিতে যুদ্ধাবস্থা তরান্বিত হয় এবং রাসূল (সা.) হত্যাকারীদের বিরুদ্ধে সেনাবাহিনী প্রেরণ করেন। বিপরীতে, সম্রাট কায়সারও মুসলিমদের বিরুদ্ধে তার সেনাবাহিনী প্রেরণ করে।
আর অন্যদিকে, বিগত কয়েক বছর যাবত পারস্যের মূল বাহিনী ও তার আশ্রিত রাজ্যগুলোর মাঝে বেশ ঘনঘনই খণ্ডযুদ্ধ চলছিলো। পারস্যের “আগ্রাসন-নিপীড়ন”মূলক কর্মকাণ্ড আন্তর্জাতিক অঙ্গনে মারাত্মক জটিলতা সৃষ্টি করেছিলো।
এটা আসলেই বিস্ময়কয় ব্যাপার যে, সুদীর্ঘকাল যাবত প্রতিষ্ঠিত তৎকালীন বিশ্বের সর্ববৃহৎ দু’টি পরাশক্তি রোম-পারস্যর বিপরীতে ধরতে গেলে আরবরা তখন ছিলো সুবিশাল মরুভূমিতে একমুঠো বালির মতো। অথচ, মুসলিমদের হাতেগোনা কয়েকটা যাযাবর গোষ্ঠী ব্যতীত তাঁদের কোনো উন্নত মানের সরঞ্জামাদি বা সামরিক আয়ের উৎস না থাকার পরেও মুসলিমরা টক্কর দিয়েছিলো পরাশক্তি-দু’টোর সাথে।
ইসলামের সুমহান ও সুদৃঢ় এক আধ্যাত্মিক শক্তির বলয়ে হযরত আবু বকর (রা.) একইসঙ্গে এই পরাশক্তি-দু’টোর সাথে যুদ্ধ চালিয়ে গিয়েছিলেন। বিস্ময়কর ব্যাপার হলো, প্রথম আক্রমণেই মুষ্টিমেয় উজ্জীবিত এই মুসলিমরা বেশ কয়েকটি সীমান্ত দখল করে নেয়। এরপর, খলিফা আবু বকর (রা.) রোমের রাজধানী কনস্টান্টিনোপলে (বর্তমান ইস্তাম্বুল) একজন দূত প্রেরণ করেন শান্তিপূর্ণ একটা সমাধানের জন্য। কিন্তু, অভিযানটি ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। রোম সম্রাট কায়সার যুদ্ধে হেরে যাবার পর পুরো রাজ্যে জরুরী অবস্থা জারি করে নতুন উদ্যমে নতুন সৈন্য সংগ্রহ করে বাহিনী গঠন করতে থাকে। আবু বকর (রা.) বিষয়টির গুরুত্ব অনুধাবন করে তিনিও পারস্য থেকে রোমে, বিশেষ করে সিরিয়ায় সেনাবাহিনী স্থানান্তর করেন। ৬৩৪ খ্রিস্টাব্দে জেরুজালেমের কাছেই অবস্থিত আজনাদাইনের প্রান্তরে রোমের বিরুদ্ধে বিশাল এক জয় অর্জন করে মুসলিমরা। অল্প সময়ের ব্যবধানে তারা ফিহলও (বর্তমান পেলা) জয় করে নেয়। ফলশ্রুতিতে, ফিলিস্তিন অঞ্চল তাদের হাতছাড়া হয়ে মুসলিমদের অধীনে চলে আসে।
ঠিক এমন সময়ই হযরত আবু বকর (রা.) ইন্তেকাল করেন এবং দ্বিতীয় খলিফা হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন হযরত উমর (রা.)। দায়িত্ব পাবার পরেই উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া কাজগুলোর প্রতি তিনি দৃষ্টি নিবদ্ধ করেন। এরপর, খুব দ্রুতই দামেস্ক মুসলমানদের অধীনে চলে আসে। উত্তর সিরিয়ায় হিমসের অধিবাসীরা স্বেচ্ছায় মুসলমানদের নিকট তাদের রাজ্য হস্তান্তর করে। বিষয়টি থেকে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, সেসব অঞ্চলের অধীবাসীরা মুসলিমেদরকে শত্রু বা বিজেতা হিসেবে নয়, বরং তাদের মুক্তিদাতা হিসেবে গ্রহণ করেছিলো।
হিমস হাতছাড়া হবার পর, সম্রাট হিরাক্লিয়াসের সমস্ত মনোযোগ একীভূত হয় মুসলমানদের কর্তৃত্বাধীন রোমের অঞ্চলগুলো পুনরুদ্ধার করা এবং বাকী অঞ্চলগুলো দখল করার আগেই মুসলিমদের বিতাড়িত করার প্রতি। এই লক্ষ্যকে সামনে রেখে আগের চেয়েও শক্তিশালী এক সেনাবাহিনী গঠন করতে শুরু করে সে। যখন সম্রাট হিরাক্লিয়াসের এমন সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হয়, তখন মুসলিম সেনাপতি ঘোষণা করে, জনগণের নিকট থেকে গ্রহণ করা এতোদিনের করগুলো ফেরত দেয়া হবে। কারণ, করের যথাযথ ব্যবহার তখনই সম্ভব হবে, যখন ঐ সুনির্দিষ্ট অঞ্চলের জনগণকে তাদের পর্যাপ্ত নিরাপত্তার নিশ্চয়তা প্রদান করা যাবে। উক্ত ঘোষণা শোনার পর উল্লিখিত অঞ্চলের অধীবাসীদের আবারো সেই পূর্বের অত্যাচারী শাসকের অধীনে পুনরায় ফিরে যাবার সমূহ সম্ভাবনা তৈরী হওয়ায়, তাদের মাতমকে বিস্ময়কর কিছু বলা যায় না।
De Goeje তাঁর বিখ্যাত Memoir sir la conquete de la Syrie বইয়ে লিখেছেন, “আসলে, তৎকালীন প্রেক্ষাপটে সিরিয়ান ও আরবরা একে অপরের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলো। আরবদের এমন উত্থানের খবর জানার পর সিরিয়ানরা বেশ মুখিয়ে ছিলো। কারণ, সিরিয়ানরা বাইজেন্টাইন শাসকদের দ্বারা ভয়াবহ অত্যাচারের স্বীকার হয়ে আসছিলো বহুকাল ধরেই, আর তাদের ধৈর্যের বাঁধও ভেঙ্গে গিয়েছিলো। তাই আরবদেরও (মুসলিম) অধিকার ছিলো সিরিয়া জয় করার।”
সে সময় মুসলিমরা সুকৌশলে পিছিয়ে গিয়ে কিছুদিনের মধ্যেই আবার ফিরে এসেছিলো পূর্ণ শক্তি ও লোকবল সহকারে।
অন্যদিকে, পারস্যকেও এমন ভাগ্য বরণ করতে হয়েছিলো। হিরাহ অঞ্চলসহ বেশ গুরুত্বপূর্ণ সুরক্ষিত এলাকাগুলো হারানোর মাধ্যমে তাদের পরাজয় শুরু হয়েছিলো। তবে, কিছু কিছু অঞ্চলে হঠাৎই দুর্ভিক্ষ শুরু হওয়ায় বিজয়াভিযান সাময়িকভাবে বন্ধ ছিলো। কিন্তু এর কয়েক মাস পর পারস্যের রাজধানী মাদায়েন খুব সহজেই মুসলমানদের অধীনে চলে আসে। সম্রাট ইয়াযদিগার্দ চীনা সম্রাট এবং তুরস্কের রাজা-সহ প্রতিবেশি রাজ্যগুলোর রাজপুত্রদের কাছে সাহায্য চেয়ে পাঠায়। কিন্তু এই সাহায্যও তার কোনো উপকারে আসেনি। এমনকি, তার মিত্র রাজ্যগুলোকেও বেশ খেসারত পোহাতে হয়েছিলো এজন্য।
হযরত উমর (রা.) এর সময়ে অর্থাৎ ৬৩৪-৬৪৪ খ্রিস্টাব্দে, লিবিয়া থেকে আফগানিস্তান, আর্মেনিয়া থেকে পাকিস্তান হয়ে ভারত এবং এগুলোর মাঝে অবস্থিত রাষ্ট্রগুলোতে–যেমন, সিরিয়া, ইরাক ও ইরান–মুসলিমরা শাসন করেছিলো বেশ গর্বের সাথেই। উমর (রা.) এর পর হযরত উসমান (রা.) এর সময়ে নুবিয়া মুসলিমদের অধীনে চলে আসে এবং ডোঙ্গোলা (সুদান)-সহ তার আশপাশের এলাকাও মুসলমানরা তাঁদের করতলে নিয়ে নেয়। আন্দালুসিয়াতেও ইসলামের পতাকা উড্ডীন করে তাঁরা। আর পূর্বদিকে, জাইহুন নদী অতিক্রম করে চায়নার কিছু অংশেও মুসলমানরা ইসলামের বাণী ছড়িয়ে দেয়। এছাড়াও, সাইপ্রাস, রোডস এবং ক্রিটি (রোডস এবং ক্রিটি হলো গ্রীসের বড়ো দুটি শহর) জয় করার মধ্য দিয়ে ইসলামের সীমানা বৃদ্ধি করা হয়।
এছাড়াও রোম সাম্রাজ্যের সীমানা ধীরে ধীরে সংকুচিত হতে থাকে। সংকুচিত হতে হতে একটা সময় রাজধানী কনস্টান্টিনোপলকেও মুসলিমদের আক্রমণের মুখে পড়তে হয়। আবার, সাম্রাজ্যের যতটুকু এলাকাও বা তাদের আয়ত্তে ছিলো, সেটাও পরিচালনার জন্য সিরিয়ার দূরদৃষ্টি গভর্নরকে নিরপেক্ষ থাকার শর্ত দিতে হতো।
রাসূল (সা.) এর মৃত্যুর মাত্র ১৫ বছরের মাথায় পূর্বের আটলান্টিক থেকে শুরু করে পশ্চিমের ইন্দো প্যাসিফিকের বিভিন্ন অঞ্চল পর্যন্ত ইসলাম তার সুশীতল ছায়া বিস্তার করেছিলো, যা ছিলো আয়তনে সমগ্র ইউরোপ মহাদেশের সমান। সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় হলো, ইসলামের এমন উত্থানকালেও বিজিত এলাকাগুলোর কোথাও অসন্তোষ দেখা যায়নি। বিষয়টির আরও সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় ৬৫৬ খ্রিস্টাব্দের ঘটনা থেকে। এই সালে ইজতিহাদগত ভুলের কারণে যখন গৃহযুদ্ধ শুরু হয়ে মুসলিমরা কয়েকটি ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়, তখনও বিজিত অঞ্চলের কোথাও কোনোরূপ বিদ্রোহ দেখা যায়নি।
ইসলামের এমন দ্রুততম গৌরবময় উত্থানের পেছনে শুধু মুসলিমদের কর্মকাণ্ডকে একমাত্র কারণ হিসেবে দর্শানো ঠিক হবে না। রোম-পারস্যের পারস্পরিক দ্বন্দ্ব এবং সাম্রাজ্য দু’টোর অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বের মাধ্যমে তাদের ভেতরে যে দুর্বলতা সৃষ্টি হয়েছিলো, সে দুর্বলতা আরব-মুসলিম সেনাপতিদের সমরাস্ত্র, বিভিন্ন সংস্থা ও বস্তুগত উপাদানের অভাব পূরণ করে দিয়েছিলো। অতএব, মুসলিমদের উত্থানের পেছনে তাদের দুর্বলতাও একটা কারণ হিসেবে কাজ করেছে। তবে, পূর্বের স্পেন থেকে পশ্চিমের চীন পর্যন্ত ব্যাপকভাবে মুসলিমদের পক্ষে ছড়িয়ে পড়া সম্ভব ছিলো না। কারণ, সুবিশাল এই অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ার মতো যথেষ্ট আরব-মুসলিম জনসংখ্যা ছিলো না।
ইসলামের প্রথম দিকের যুদ্ধগুলো হয়েছিলো সম্পূর্ণ রাজনৈতিক কারণে। রোমান খ্রিস্টান পোপদের মতো জোর করে ইসলামকে চাপিয়ে দেওয়ার কোনো ইচ্ছাই ছিলো না মুসলমানদের মধ্যে। এমনকি ইসলামেও সরাসরি নিষেধ করা হয়েছে এ ব্যাপারে। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, সেই সময়ে মুসলিমরা বিজয়ী হবার পর বিজিত অঞ্চলের অধীবাসীদের উপর ধর্মান্তরের জন্য কোনোরূপ জোর-জবরদস্তি করেনি। বরং মুসলিমদের উদারতা, সরলতা, মহানুভবতা, আখলাক এবং ইসলামের ধর্মতাত্ত্বিক মতবাদ ও দৃষ্টিভঙ্গি বাস্তব জীবনে প্রয়োগের মাধ্যমে মুসলিমরা যে উদাহরণ পেশ করেছিলো, সে বিষয়টাই অন্যদেরকে ধর্মান্তরিত হতে বা ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে এসে সমবেত হতে উৎসাহিত করতো। আর যুদ্ধলব্ধ সম্পদ-সহ বিভিন্ন ক্ষেত্র থেকে আগত অর্থের মাধ্যমে মুসলিমদের ধনী হওয়াটা ছিলো ইসলাম বিস্তৃত হবার সবচেয়ে ক্ষুদ্রতম কারণ।
আবার প্রশাসনিক ক্ষেত্রে সুযোগ্য নেতৃত্ব প্রদানের মাধ্যমে বিজিত অঞ্চলের অধীবাসীদের বেশ প্রশংসাও কুড়িয়েছিলো মুসলিমরা। সম্প্রতি মিশরে প্যাপিরাসে লিপিবদ্ধ করা তৎকালীন ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থার কিছু প্রশাসনিক নথিপত্র পাওয়া গিয়েছে। নথিপত্রগুলো থেকে সুস্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, মিশরে মুসলিম শাসকরা নামেমাত্র কর আদায় করে কীভাবে ন্যায়পরায়ণতার সাথে রাষ্ট্র পরিচালনা করেছিলো। অতএব, এটা এখন সুনিশ্চিতভাবেই বলা যায়, মুসলিমদের তৎকালীন রাষ্ট্রব্যবস্থায় বাকী সকল অঞ্চলেও একই অবস্থা বিরাজ করছিলো।
মুসলিম প্রশাসকদের স্বাভাবিক ও সৎ জীবনযাত্রার পাশাপাশি ন্যায়পরায়ণতার সাথে রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য প্রশাসনিক ব্যয় পূর্বের তুলনায় অস্বাভাবিক হারে কমে গিয়েছিলো। আবার, যুদ্ধলব্ধ সম্পদ বা গনীমতের ক্ষেত্রেও সেনাপতিরা যাচ্ছেতাই ব্যবহার করতে পারতো না। ইসলামের আইন অনুযায়ী, গনিমত সরাসরি সরকারের কাছে হস্তান্তর করতে হবে এবং আইন ও বিধান অনুযায়ী সেনাবাহিনী-সহ সকল প্রাপকদের মাঝে বন্টন করে দেওয়া হবে।
এমনকি খলিফা হযরত উমর (রা.) পর্যন্ত আশ্চর্যান্বিত হতেন তাঁর যোদ্ধা ও রাষ্ট্রের উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের সততা ও আমানতদারিতায়। কারণ, তিনি তাঁদের নিকট এমনসব দামী-মূল্যবান পাথর এবং গুরুত্বপূর্ণ নথিপত্র দিতেন, যা সহজেই লুকিয়ে ফেলা বা বিক্রি করে প্রচুর অর্থ উপার্জন করা যেতো।
অথচ, আমানতগুলো তাঁরা তার প্রাপকের নিকট যথাযথভাবেই নিরাপদে পৌঁছে দিতেন।
সমসাময়িক একটা খ্রিষ্টিয় নথির কথা উল্লেখ করে এই অংশের আলোচনা শেষ করা যেতে পারে। নথি মূলত একটা চিঠি, যেটা নেস্টোরিয়ান বিশপ তার বন্ধুর নিকট পাঠিয়েছিলো। নথি বা চিঠিটা cf.Assemani, Bibl. Orient, III, 2, p, XCVI এ সংরক্ষিত আছে। চিঠিটার বর্ণনা অনেকটা এমন,
❝এই আরবরা, আমাদের দুর্দিনে প্রভু যাদের সুদিন দেবার মাধ্যমে আমাদের উপর বিজয়ী করেছে, তারা এখনও খ্রিস্টান ধর্মের উপর একটা আঁচরও কাটেনি। বরং, তারাই আমাদের ধর্মবিশ্বাকে রক্ষা করছে, যাজকদেরকে সম্মান করছে। এমনকি, গির্জা ও মঠের জন্য অর্থও বরাদ্দ করছে।❞
💠উমাইয়া খেলাফত
৬৫৬ খ্রিস্টাব্দে তৃতীয় খলিফা উসমান (রা.) এর মৃত্যুতে মুসলিম উম্মাহ উত্তরাধিকার বিষয় সম্পৃক্ত একটা যুদ্ধের মুখোমুখি হয়, যার প্রভাবে পরবর্তী বিশ বছরে আরও বেশ কয়েকবার এই সমস্যা মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। ফলশ্রুতিতে, কমপক্ষে আরো নতুন ৬টি রাজ্যের উদ্ভব হয়। যদিও পরবর্তীতে মাত্র কয়েক বছরের ব্যবধানে রাজ্যগুলো অবশ্য বিলুপ্ত হয়ে যায়। কারণ, খলিফা আব্দুল মালিক (৬৮৫-৭০৫) তার রাজ্যের সিংহাসনে আরোহণের পর সবকিছুকে শক্ত হাতে সামাল দিয়ে নতুন উদ্যমে নতুনভাবে সবকিছু শুরু করেন। ফলে, রাজ্যকেন্দ্রিক সমস্যাগুলোর সমাধান হয় এবং মুসলিম উম্মাহর বিজয়াভিযানে নতুন মাত্রা যোগ হয়। একদিকে মরক্কো ও স্পেন, অন্যদিকে ইন্দো-পাকিস্তানি এবং ট্রান্সঅক্সিয়ানা (মা-ওয়ারাউন-নাহার) মুসলিমদের করতলে চলে আসে। এছাড়াও, ফ্রান্সের বোর্দো, নারবোন এবং টুলুজ শহরও মুসলিমরা শাসন করতে শুরু করে।
এক পর্যায়ে মদীনা থেকে দামেস্কে রাজধানী স্থানান্তর করা হয়। রাসূল (সা.) এর স্মৃতিবিজড়িত পবিত্র শহর থেকে বাইজেন্টাইন এলাকার নিকটবর্তী শহরে রাজধানী স্থানান্তর হবার ফলে এবং বাইজেন্টাইন সেকুলার ব্যবস্থাপনার প্রভাবে অনেকক্ষেত্রে মুসলিমদের ধর্মীয় অনুভূতি ও ভক্তিশ্রদ্ধা কমে যেতে থাকে। কারণ, সেখানে বিলাসিতা, সম্পদের অপব্যয়, পক্ষপাতিত্ব এবং এগুলোর ফলে সৃষ্ট বিদ্রোহ বা উত্থান-পতনের অভাব ছিল না।
তবে, মুসলিমরা বুদ্ধিবৃত্তিক অঙ্গন এবং সামাজিক দর্শনের ক্ষেত্রে এগিয়ে যেতে থাকে। শিল্পক্ষেত্রে নতুন বিপ্লব সূচিত হয়। এছাড়াও, সরকারি প্রণোদনায় গ্রিকসহ বিভিন্ন ভাষা থেকে চিকিৎসা বিষয়ক বইগুলোর আরবী অনুবাদ হওয়ায় চিকিৎসাক্ষেত্র এবং ঔষধশিল্পে নতুন এক মাত্রা যোগ হয়। পাশাপাশি, ইসলামের জন্য নিজেকে উৎসর্গকারী মুসলিম উম্মাহর অসংখ্য বিজ্ঞজন বিজ্ঞানকে উন্নতির চূড়ান্ত শিখরে পৌঁছে দেবার জন্য নিজস্ব উৎসাহ ও উদ্দীপনায় দুর্দান্ত গতিতে কাজ চালিয়ে নিয়ে যেতে থাকে।
এই সময়ের স্থাপত্য নিদর্শনগুলির মধ্যে অন্যতম হলো জেরুজালেমের ডোম অফ দ্য রক (কুব্বাত-আল-সাখরা, আল কুদস), যা ৬৮১ খ্রিস্টাব্দে নির্মিত হয়েছিলো। এছাড়াও, দামেস্ক-সহ বিভিন্ন স্থানের স্মৃতিস্তম্ভগুলোর ধ্বংসাবশেষ আজও অন্যসব অঙ্গনের সাথে স্থাপত্যশিল্পেও মুসলমানদের সমান অগ্রগতির সাক্ষ্য বহন করে আসছে।
সঙ্গীতশাস্ত্রেও মুসলিমরা দুর্দান্ত বিকাশ সাধন করেছিলো এবং এখানেও তাদের অসামান্য অবদান রয়েছে। কিন্তু, এই সম্পর্কিত নথিপত্র এখনও সবার সম্মুখে না আসায় এই শিল্পে মুসলিমদের অগ্রগতি সম্পর্কে একটি নির্দিষ্ট ধারণা পেয়ে তাদের যথাযথ মূল্যায়ন করতে সত্যিকারার্থেই আমরা অক্ষম ও অপারগ।
উমর বিন আব্দুল আযিযের (৮১৭-৮২০) সংক্ষিপ্ত সময়ে মুসলিম উম্মাহ যেনো সমৃদ্ধশালী নতুন একটা যুগের সাক্ষী হয়ে যায়। তিনি খোলাফায়ে রাশেদার আবু বকর ও উমর (রা.) এর প্রতিচ্ছবি আঁকতে পেরেছিলেন তাঁর সময়ে। ইতোপূর্বে কোনো এক কারণে শাসকদের বাজেয়াপ্ত করা জনসাধারণের সম্পদ পুনরায় তাদের নিকট হস্তান্তর করেন তিনি। অযৌক্তিক ও অপ্রয়োজনীয় অসংখ্য কর মওকুফ করে দেন। একজন মুসলিম দোষী এবং একজন অমুসলিম নির্দোষ হলেও বিচারের ক্ষেত্রে তিনি থাকতেন ন্যায়ের উপর অটল এবং দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ। এমনকি, সমরকন্দের একটা শহর অন্যায়ভাবে দখল করায় তিনি সৈন্যদের বাধ্য করেছিলেন শহরের মালিকানা হস্তান্তর করতে। রাজধানীর কেন্দ্রীয় মসজিদের কিছু অংশ অন্যের জমির উপর চলে যাওয়ায় পরবর্তীতে তা ভেঙে ফেলার নির্দেশ দিতে দ্বিধাবোধ করেননি তিনি। এ ঘটনাগুলোর ফলাফলও ছিলো বিস্ময়কর। এই রাজবংশের শুরুতে ইরাকের বার্ষিক রাজস্ব ছিলো ১৮ মিলিয়ন দিরহাম, কিন্তু, তাঁর সময়ে বিস্ময়করভাবে রাজস্ব বেড়ে দাঁড়ায় ১২০ মিলিয়ন দিরহামে। এছাড়াও, দুর্নীতির কঠোর দমন মুসলিম প্রশাসনকে সর্বত্র জনপ্রিয় করে তুলেছিলো।
তাঁর এমন ধর্মপরায়ণতা এবং ন্যায়ানুবর্তিতার কারণে বিশ্বব্যাপি ইসলামের নতুন এক রূপ ছড়িয়ে পড়ে। যার প্রভাবে তুর্কিস্থান, সিন্ধু এবং বারবেরি ল্যান্ডের রাজারা পর্যন্ত ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে এসে নিজেদেরকে ধন্য মনে করেছিলো। এমনকি, বিশ্বব্যাপি ইসলামকে নিয়ে নতুনভাবে অধ্যয়ন শুরু হয়েছিলো।
মুসলমানদের মধ্যে দুটি বড় সম্প্রদায় সুন্নী এবং শিয়ার উদ্ভবটাও প্রায় এই সময়কাল থেকেই। এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যকার পার্থক্য মূলত একটি রাজনৈতিক পারিবারিক প্রশ্নের উপর ভিত্তি করে তৈরি হয়েছিলো। প্রশ্নটা এমন ছিলো, “রাজ্য পরিচালনার জন্য নির্বাচনের মাধ্যমে উত্তরাধিকার নির্ণয় করা উচিত নাকি নবীর নিকটাত্মীয়দের মধ্য থেকে উত্তরাধিকার নির্ণয় করা উচিত।”
বিষয়টা শিয়াদের কাছে নিজস্ব মতবাদ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো। এর ফলে শিয়া উপদলের সৃষ্টি হয় এবং বিষয়টা একপর্যায়ে গৃহযুদ্ধে গড়ায়। এটি এমনই একটি বিদ্রোহ বা গৃহযুদ্ধ ছিলো যা উমাইয়া রাজবংশ বা খেলাফতের পতনকে তরান্বিত করে এবং ৭৫০ সালে আব্বাসীয়দের খেলাফতে অধিষ্ঠিত হবার পথ সুগম করে। কিন্তু শিয়ারা এই পরিবর্তন থেকেও কোনো প্রকার উপকৃত হতে পারেনি।
বর্তমান সময়ে মুসলিম বিশ্বের মোট জনসংখ্যার সম্ভবত দশ শতাংশ হচ্ছে শিয়া, বাকিরা সকলেই সুন্নি। এছাড়াও, খারিজি নামক খুবই ছোটো একটা দলও ঐ একই সময়ে অস্তিত্ব লাভ করেছিলো।
💠আব্বাসীয় খেলাফত
৭৫০ সালে আব্বাসীয়দের উত্থানের মাধ্যমে মুসলিম ভূখণ্ড দু’টি ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। এবং দামেস্ক থেকে বাগদাদে ইসলামী সভ্যতার রাজধানী স্থানান্তরিত হয়। এরপর ক্রমান্বয়ে আরও কয়েকটি স্বাধীন রাষ্ট্রের উত্থান হয়। যেমন, কর্ডোভা (স্পেন) সালতানাত। এই সালতানাত তাদের পতন অর্থাৎ ১৪৯২ সাল পর্যন্ত স্বাধীন ও স্বয়ংসম্পন্ন ছিলো।
৯২১ সালে বুলগার (রাশিয়ার ভলগা নদীর তীরে কাজান অঞ্চল) রাজা বাগদাদে অনুরোধ জানিয়েছিলেন একজন মুসলিম ধর্মপ্রচারককে পাঠানোর জন্য। ইবনে ফাদলানকে পাঠানো হয় সেখানে। তাঁর ভ্রমণবৃত্তান্ত থেকে বিস্ময়কর একটা বিষয় উঠে আসে। বুলগার রাজা স্বয়ং ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন এবং অমুসলিম অঞ্চলগুলির মধ্যেই একটি মুসলিম জনপদ গড়ে তুলেছিলেন। এভাবেই, ককেশাস এবং তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে ধীরে ধীরে ইসলাম ছড়িয়ে পড়তে থাকে।
আব্বাসীয় খেলাফতের সময় কেন্দ্রীয়ভাবে বড়ো ধরনের কোনো সামরিক অভিযানের দেখা পাওয়া যায় না। তবে, অনেকক্ষেত্রে কেন্দ্রের অধীনস্থ আঞ্চলিক শাসকরা তাদের সামরিক অভিযান চালু রেখেছিলো। এই আঞ্চলিক শাসকগণ বাগদাদকে তাদের কেন্দ্র হিসাবে স্বীকৃতি দিলেও পররাষ্ট্রনীতি, অভ্যন্তরীণ প্রশাসন বা রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে অনেক সময় খলিফার উপর নির্ভর করতেন না। প্রসঙ্গতঃ এখানে ভারতীয় উপমহাদেশের উল্লেখ বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। কিন্তু, এই স্থান সম্পর্কে আলাদা একটা পয়েন্টে আলোচনা করা হবে।
এই সময়টায় বাইজেন্টাইনদের সাথে মুসলিমদের সম্পর্ক ক্রমশ অবনতির দিকে যেতে থাকে, খণ্ডযুদ্ধেও গড়াতে থাকে। এছাড়াও, গ্রীক সাম্রাজ্যকে এশিয়া মাইনর ত্যাগ করতে হয় এবং কিছু সময়ের জন্য শুধুমাত্র ইউরোপীয় সম্পত্তি নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হয় তাদের।
আব্বাসীয়রা পূর্বের জনপ্রিয় স্বেচ্ছাসেবক সেনাবাহিনীর পরিবর্তে তুর্কি বংশোদ্ভূত অসংখ্য দক্ষ ও অভিজ্ঞ যোদ্ধা নিয়োগ দিতে শুরু করে, যা পরবর্তীতে সামন্তবাদের জন্ম দেয়। এবং এর ফলাফল হিসেবে বিভিন্ন রাজবংশের উত্থান হয়। রাজবংশগুলোর উত্থানের শত বছরের মাথায় আব্বাসীয় খেলাফতের কেন্দ্রীয় শক্তি ক্রমান্বয়ে কমতে থাকে এবং বাইরের শাসকদের বিশেষ ক্ষমতা প্রদান করতেও বাধ্য হতে থাকে খলিফাগণ। একটা পর্যায়ে, শুধু নিজ এলাকার মধ্যেই তাঁদের ক্ষমতা সীমিত হয়ে পড়ে। এমনকি, স্থান ও ক্ষেত্র-বিশেষে মহানগরীতেও বিভক্ত হয়ে আমিররা শাসন চালাতে থাকে।
এই পর্যায়ে এসে মুসলিম শাসকদের সাথে পোপদের সাথে একটা বৈপরিত্য লক্ষ্য করা যায়। কয়েক শতাব্দী পূর্বেও পোপদের কোনো রাজনৈতিক ক্ষমতা ছিলো না। কিন্তু রোমান সাম্রাজ্যের উত্থানের পর থেকে পর্যায়ক্রমে পোপরা রাজনৈতিক ক্ষমতা অর্জন করে, এবং রাজনীতিতে হস্তক্ষেপ করতে থাকে। এমনকি, পোপরা একসময় শাসকদের থেকেও শক্তিশালী হয়ে ওঠে। পক্ষান্তরে, খলিফারা সর্বোচ্চ শক্তিশালী হয়ে তাঁদের কার্যক্রম শুরু করলেও, পরবর্তীতে বিভিন্ন কারণে তৈরি হওয়া কেন্দ্রবিমুখ শাসকদের সাথে ক্ষমতা ভাগাভাগি করে নিতে হয়। এবং শেষে, শুধু নামেমাত্র শাসক হয়ে সিংহাসনে বসে রাজ্য পরিচালনা করতে হয়।
ইতালির সিসিলিতে চলতে থাকা একটা গৃহযুদ্ধের সমস্যা সমাধানকল্পে আব্বাসীয়দের অধীনস্থ আঘলাবিদ রাজবংশের তিউনিশিয়ার গভর্নরকে বিষয়টিতে হস্তক্ষেপের জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয় সেখানে। তিনি সেখানে গিয়ে দ্বীপটিকে মুসলিমদের অধীনে নিয়ে আসেন এবং ইতালির মূল ভূখণ্ড-সহ রোমের সীমানা পর্যন্ত পৌঁছতে সক্ষম হন। এমনকি, ফ্রান্স ও সুইজারল্যান্ডের সীমানাতেও নিজেদের পতাকা প্রতিস্থাপন করেছিলেন তিনি। তবে, পরবর্তীতে ফাতেমীয়রা আঘলাবিদ রাজবংশ দখল করে নেয় এবং মিশরের কায়রো অঞ্চল, আব্বাসীয়দের প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে দাঁড় করানো শিয়াদের এই খেলাফাতের রাজধানী হিসেবে গড়ে তোলা হয়। ফাতেমীয়দের শাসকগণ দূরদর্শী হলেও তাদের কোনো একজন অজ্ঞতাবশতঃ জেরুজালেমে অবস্থিত খ্রিস্টানদের মন্দিরগুলোকে অবজ্ঞা করে বসে। এতে করে ইউরোপে মুসলিম বিদ্বেষ মারাত্নক আকার ধারণ করে। এমনকি, পোপরা পর্যন্ত ইসলামের বিরুদ্ধে পবিত্র যুদ্ধের প্রতি ঘোষণা দেয়, অর্থাৎ ক্রুসেডের সূচনা হয়। এরপর শুরু হয় দুইশত বছরের দীর্ঘ এক পবিত্র যুদ্ধ, যা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে অসংখ্য মানুষের মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়ায়।
প্রথম ক্রুসেডের সময় ফাতেমীয়রা ফিলিস্তিন ত্যাগ করে চলে যায়। যার ফলে স্থানীয় নিরীহ জনসাধারণ খ্রিস্টানদের পৈশাচিক হিংস্রতার মুখোমুখি হয়। এর চেয়েও দুঃখজনক হলো, এই ফাতেমীয়দের অনেকেই আবার মাঝে মাঝে খ্রিস্টানদের সাথে একত্রিত হয়ে মুসলিমদের বিরুদ্ধে তাদের পবিত্র যুদ্ধ বা ক্রুসেডে সহযোগিতা করতে থাকে। এছাড়াও, ক্রুসেড চালিয়ে নেওয়া খ্রিস্টানদের পক্ষে সহজ হয়ে যাবার অন্যতম একটি কারণ হলো, সেই সময় ইসলামী বিশ্বে মুসলিমদের কোনো কেন্দ্রীয় শাসন বা শাসক ছিলো না, ছিলো অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য। যারা আবার নিজেরাই নিজেদের ভেতর গৃহযুদ্ধে লিপ্ত ছিলো। তবে, এইসব শাসকদের মধ্যে আবার কুর্দি ও তুর্কি শাসকরা অসংখ্য আরবদের নিয়ে পাশ্চাত্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে থাকে।
দ্বিতীয় ক্রুসেডের সময় মুসলিম বীর সুলতান সালাহউদ্দিন আইয়ূবী সিরিয়া-ফিলিস্তিন থেকে শুধু ইউরোপীয়দেরই বিতাড়িত করেননি, সাথে সাথে মিশরের ফাতেমীদেরকেও তাদের প্রাপ্য বুঝিয়ে দিয়ে জেরুজালেমকে সকলকিছু থেকে রক্ষা করেছিলেন। সুলতান সালাহউদ্দিন এবং তার উত্তরসূরিরা বাগদাদের খিলাফতকে স্বীকৃতি ও তাঁর সম্মান ফিরিয়ে দিয়েছিলেন বটে, তবুও তাঁরা পরবর্তীকালে তাঁদের রাজনৈতিক ক্ষমতা পুনরুদ্ধার করতে সফল হননি বা খণ্ড-বিখণ্ড রাষ্ট্রগুলোকে একত্রিতও করতে পারেননি। তবে, কেন্দ্রবিমুখ এই রাজ্যগুলোর মধ্যে অনেক শাসক আবার ইসলামের সীমানা প্রসারিত করতে সফল হয়েছিলো।
১৩ শতকে, তাতাররা তখনও ইসলাম গ্রহণ করেনি, হালাকু খানের নেতৃত্বে ১২৫৮ সালে খিলাফতের কেন্দ্র বাগদাদকে ধ্বংস করে দেয় তারা। এবং আসার পথেও কয়েক হাজার মানুষকে হত্যা করে। তবে, ফিলিস্তিনের আইনে জালুত প্রান্তরে মিশরের মামলুক সালতানাতের সেনাপতি রুকনুদ্দীন বাইবার্সের হাতে তার সেনাবাহিনীর পথ রুদ্ধ হয়। তাতাররা প্রথমবার পরাজয়ের স্বাদ আস্বাদন করে। পরবর্তীতে, হালাকু খান আবারও আক্রমণের প্রস্তুতি নেয় এবং ক্রুসেডারদেরও আমন্ত্রণ জানায়। কিন্তু, এ যাত্রায় সে আর সফল হয়নি।
তবে, পরবর্তীতে, মুসলিমদের সংস্পর্শেই বর্বর তাতাররা প্রভাবিত হয়ে ইসলামের ছায়াতলে এসে সমবেত হয়েছিলো। এরপর, তারা শুধু ইসলাম গ্রহণ করেই ক্ষান্ত হয়নি, বরং ইউরোপের বিভিন্ন দেশে অভিবাসন করে তাদের বাসস্থান গড়ে তুলেছিলো। ফলশ্রুতিতে, ফিনল্যান্ড, লিথুয়ানিয়া, পোল্যান্ড-সহ আরও কয়েকটি দেশে ইসলামের প্রভাব রয়েছে এবং স্থানীয় সম্প্রদায়গুলোতে আজও মুসলিম সংস্কৃতির ছোঁয়া রয়েছে। এভাবেই বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ইউরোপীয়দের পথচলা শুরু হয় এবং মুসলিমদের শিক্ষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির ফলেই তাদের অন্ধকার জগতের পরিসমাপ্তি ঘটে। কিন্তু, আজ একবিংশ শতাব্দীতে, মুসলমানরা এখন বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে আমেরিকান এবং ইউরোপীয়দের সমকক্ষ থেকে অনেক দূরে।
💠সেলজুক ও ওসমানীয় খেলাফত
এবার একটু পেছনে ফিরে আসা যাক, আব্বাসীয়দের সময়ে।
খণ্ড খণ্ড স্বাধীন কেন্দ্রবিমুখ রাজ্যগুলিতে তখন অরাজকতা বিরাজ করছিলো। কোথাও কোথাও এই রাজ্যগুলোর মাঝেও আবার বিদ্রোহ দেখা দিতো—রাজ্য ছোট হয়ে দুই বা ততোধিক ভাগে বিভক্ত হয়ে যেতো। আবার মাঝেমধ্যে কোথাও একজন শাসকের অধীনেই কয়েকটি রাজ্যের একত্রিত হবার কথাও শোনা যেতো। এমন অরাজকতার মাঝেও আব্বাসীয় খেলাফতের শাসকরা নিজেদের শক্তি হারাবার ফলে বাগদাদে বসে নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করতো। অথচ, এমন ঘটনা তখনই সংঘটিত হয়, যখন মুসলিম ব্যতিত অন্য কোনো ধর্ম বা মতাদর্শের শাসক রাজ্য শাসন বা পরিচালনা করে থাকে।
সেলজুকদের গঠিত সালতানাতের বিষয়টির উল্লেখও এখানে বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। তাদের উত্থান হয় ১১ শতকে। কোনিয়াকে রাজধানী বানিয়ে মধ্য এশিয়া থেকে শুরু করে সুদূর এশিয়া মাইনর পর্যন্ত তারা তাদের সালতানাতের সীমানা বিস্তৃত করেছিলো। কয়েক প্রজন্ম ধরে শাসনকার্য পরিচালনা করার পর যোগ্য উত্তরসূরী হিসেবে দুনিয়াবাসীর নিকট উসমানীয় সালতানাতকে উপহার দিয়ে যায় সেলজুকরা। যারা ইসলামী সভ্যতাকে বসফরাস অতিক্রম করে ভিয়েনার প্রাচীর পর্যন্ত বিস্তৃত করেছিলো। তাদের রাজধানী ছিল প্রথমে বুর্সা, তারপর কনস্টান্টিনোপল (ইস্তাম্বুল) এবং সর্বশেষ আঙ্কারা, তুরস্ক। ১৬ শতকে উসমানীয় খেলাফতের তুর্কিরা ইউরোপে অস্ট্রিয়া পর্যন্ত, উত্তর আফ্রিকায় আলজেরিয়া ও শাঁদ পর্যন্ত এবং এশিয়ায় জর্জিয়া থেকে মেসোপটেমিয়া, আরব ও এশিয়া মাইনর হয়ে ইয়েমেন পর্যন্ত শাসন করেছিলো। এরপর, তাদের পতন শুরুটা হয় ১৮ শতক থেকে, যখন তারা প্রতিনিয়ত একেরপর এক ইউরোপীয় ভূমি থেকে বিতাড়িত বা অপসারিত হচ্ছিলো। আর পতনের চূড়ান্ত পর্যায়ে এসে উপনীত হয় ১৯১৯ সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়, যখন তারা সব হারিয়ে একেবারে নিঃস্ব হয়ে যায়। চূড়ান্তরূপেই পতন হয় তখন উসমানীয় খেলাফতের।
উসমানীয় খেলাফতের মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলগুলো এখন স্বাধীন মুসলিম সার্বভৌমত্বের অধিকারী। তবে, এদের অনেককেই সোভিয়েত ইউনিয়নের যাঁতাকলে পিষ্ট হতে হয়েছে। আর অন্যান্য অঞ্চলগুলো তাদের ধর্ম বা মতাদর্শের সংখ্যাগরিষ্ঠতা অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন রাষ্ট্রে বিভক্ত হয়ে গেছে।
তুর্কি বংশোদ্ভূত একজন আন্তর্জাতিক ব্যক্তিত্বের কিছু উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম তুরস্ককে আবারও পূর্বের সেই প্রজাতন্ত্রে ফিরিয়ে নিয়ে যাবার সম্ভাবনা তৈরি করেছিলো। যদিও প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর থেকেই উগ্র জাতীয়তাবাদ এবং ধর্মনিরপেক্ষতার মায়াজালে আবদ্ধ ছিলো দেশটি। কিন্তু, জনসাধারণের রক্তে দীর্ঘ কয়েক শতকের গণতন্ত্রের আবহ থাকায় জাতীয়তাবাদ এবং ধর্মনিরপেক্ষতার মায়াজালে আবদ্ধ ব্যবস্থাপনাকেই হার মানতে হয়েছিলো।
💠আন্দালুসিয়ান খিলাফত
পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, আব্বাসীয়দের থেকে কর্ডোভা (স্পেন) আলাদা হয়ে স্বাধীন ইসলামী খেলাফত প্রতিষ্ঠা করেছিলো। প্রায় হাজার বছরের ন্যায়ের সাথে দাপুটে শাসনের পর ১৪৯২ সালে ক্যাস্টিলিয়ান খ্রিস্টানদের নিকট মুসলিমদের পতন হয়। স্পেনের মুসলিম যুগ ছিলো তৎকালীন স্বর্ণযুগ। সময়টা ছিলো, বৈষয়িক উন্নতি ও সমৃদ্ধির সময়। স্থানীয় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়গুলো ইউরোপীয়দের রীতিমতো আকৃষ্ট করতো। প্রতিনিয়তই ইউরোপের সব জায়গা থেকে অমুসলিম ছাত্ররা আসতো পড়াশোনার জন্য, নিজেদেরকে মুসলিমদের মতো উচ্চশিক্ষিত করে গড়ে তোলার জন্য। পূর্বেই বলা হয়েছে, ইউরোপীয়রাই উন্নত, শিক্ষিত ও জ্ঞানী হয়েছে মুসলিমদের সংস্পর্শে এসে।
মুসলিম স্থাপত্যের ধ্বংসাবশেষ এখনও আইবেরিয়ান উপদ্বীপে দেখা যায়। যেগুলো আর্কিটেকচারে মুসলিমদের অর্জিত বিস্ময়কর অগ্রগতির সাক্ষ্য বহন করে।
মুসলিমদের রাজনৈতিক পতনের পর, ক্যাস্টিলিয়ান খ্রিস্টানদের হাতে জোরপূর্বক খ্রিস্টান ধর্মে দীক্ষিত ও রূপান্তরিত হবার জন্য বর্ণনাতীত নির্যাতন ও নিপীড়নের শিকার হতে থাকে মুসলিমরা। এছাড়াও, মুসলিমদের লাইব্রেরিগুলোতে রীতিমতো তাণ্ডব ও ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ চালানো হয়। ছাপাখানা আবিস্কার হবার পূর্বের সেই সময়েও, কয়েক হাজার পাণ্ডুলিপি পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছিলো, যা আর কখনও লিপিবদ্ধ করা সম্ভব নয়। ক্ষতি এমন হয়েছিলো, যেটা আর কখনও পূরণ হবার নয়।
💠ভারতীয় উপমহাদেশ
মুহাম্মাদ বিন কাসিমের পর আফগানিস্তানের গজনভী রাজবংশ ভারতে পুনরায় বিজয়াভিযান শুরু করে। অন্যান্য রাজবংশও এসেছিলো, তবে তাদেরকে উত্তর ভারত পর্যন্তই সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছিলো। এরপরে অবশ্য খাইজিদরা এসে দক্ষিণ ভারত পর্যন্ত পৌঁছুতে সক্ষম হয়েছিলো। মালিক কাফুর নামক আলাউদ্দিন খিলজির একজন কমান্ডার আকস্মিক এক অভিযানে দক্ষিণ ভারতের শেষপ্রান্ত কানায়কুমার পর্যন্ত অগ্রসর হয়েছিলেন। এর কিছুদিন পরেই সেই অঞ্চলে ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো। ভারতীয় উপমহাদেশের ইসলামী ইতিহাসে মুঘল সালতানাত বিশেষ এক স্থান দখল করে আছে। ১৫২৬ – ১৮৫৮ সাল পর্যন্ত, বিশাল এই সময়ের শাসনকালে মুঘলরা পুরো ভারতীয় উপমহাদেশে ন্যায়-নিষ্ঠার সাথে শাসনকার্য পরিচালনা করেছে। তাই, মুঘল সালতানাত মুসলিম বিশ্বের আর সব সুবিশাল সালতানাত বা খেলাফতের মতোই একই পর্যায় বা স্থান দখল করে আছে। আঠারো শতকের মাঝামাঝি সময় থেকে প্রাদেশিক গভর্নরদের কিছু পদক্ষেপের ফলে কেন্দ্রীয় শাসন দুর্বল হতে শুরু করে। এর শত বছর পরে উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে, ১৮৫৭ সালে ব্রিটিশরা তাদের তথাকথিত সুসভ্য রাজ্য পরিচালনার নামে মুঘলদেরকে বিতাড়িত করে পুরো উপমহাদেশের তিন-পঞ্চমাংশ দখল করে নেয়। উপমহাদেশের বাকি অংশ বিভিন্ন রাজ্যে বিভক্ত হয়ে যায়, যার কয়েকটা ছিলো মুসলিম অধ্যুষিত এবং মুসলিমরা বর্তমান সময় পর্যন্ত সেই অঞ্চলগুলোতে এখনও ভারতীয়-মুসলিম সংস্কৃতি আঁকড়ে ধরে রেখেছে।
মুসলিম অধ্যুষিত এমনই একটি অঞ্চল হলো হায়দারাবাদ, যা ভারতের কেন্দ্রে অবস্থিত এবং আয়তনে তা পুরো ইতালির সমান। হায়দারাবাদে সেই সময়ে ২০ মিলিয়নেরও বেশি মানুষ ছিলো এবং তারা ইসলামী শিক্ষার সংস্কার ও অগ্রসরতার জন্যও সুপরিচিত ছিলো।
ইংরেজ অর্থায়নে প্রতিষ্ঠিত হলেও তৎকালীন একটা বিশ্ববিদ্যালয়ে আর সব অনুষদের সাথে “ইসলামী ধর্মতত্ত্ব” নামেও একটি অনুষদ ছিলো। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিটি স্তরে ও অনুষদে উর্দু ও স্থানীয় ভাষা-সহ আরবী অক্ষরে লিপিবদ্ধ আরও অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদির শিক্ষা প্রদান করা হতো। আর, এইসব বিষয়ের উপর গুরুত্বারোপ করা হতো স্কুল পর্যায় থেকেই।
স্কুলে পড়া অবস্থাতেই ছাত্রদেরকে ইংরেজি ও গণিত-সহ আরও কয়েকটি আধুনিক বিষয়ের পাশাপাশি আরবী ভাষা, ফিকহ (মুসলিম আইন) ও হাদিস (রাসূলের জীবনি ও বাণী) মূল বিষয় হিসেবে অধ্যয়ন করানো হতো।
এরপর, উচ্চশিক্ষা বা বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে এসে, ধর্মতত্ত্ব অনুষদের শিক্ষার্থীরা শুধুমাত্র উচ্চ মানের ইংরেজিই শিখতো না, বরং ইসলামকে বিশুদ্ধভাবে অধ্যয়নের জন্য আরবি-সহ এর সাথে সম্পর্কিত বাকি বিষয়গুলোও গুরুত্ব সহকারে পড়তো।
পরবর্তীতে, “তুলনামূলক অধ্যয়ন” করাটাই প্রচলিত হয়ে ওঠে। উদাহরণস্বরূপ, ফিকহের সাথে আধুনিক আইনশাস্ত্র, কালামের সাথে পশ্চিমা দর্শনের ইতিহাস এবং আরবির সাথে হিব্রু বা আধুনিক ইউরোপীয় ভাষা–যেমন (বিশেষ করে) ফরাসি বা জার্মান পড়ানো হতো বিশ্ববিদ্যালয়ে, অথবা ছাত্ররা নিজ উদ্যোগেই পড়ে নিতো। ছাত্ররা তাদের থিসিস তৈরির সময় ইসলামী ধর্মতত্ত্ব অনুষদের পাশাপাশি আর্ট, লিটারেচার বা ল’ অনুষদের প্রফেসরদেরও সাহায্য নিতো। ফলশ্রুতিতে, ইসলামী শিক্ষার পাশাপাশি আধুনিক পশ্চিমা বিষয়াদিও আয়ত্ত করতে পারতো তারা একইসাথে, সমান গতিতে। কিন্তু, তিন দশকের অসাধারণ এই দূরদর্শিতার সফলতা আজ যেনো শুধুই সুখকর স্মৃতি, এর কোনোকিছুই আর অবশিষ্ট নেই।
কারণ, ব্রিটিশরা ১৯৪৭ সালে মুসলিম ও হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠতার উপর ভিত্তি করে উপমহাদেশকে বিভক্ত করে পাকিস্তান ও ভারত-নামক দু’টি দেশের সীমানা নির্ধারণ করে উপমহাদেশ ত্যাগ করে। ফলে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যগুলো একত্রিত হলেও সকল ক্ষেত্রেই একটা বিভক্তি, বিচ্ছিন্নতা ও বিভাজনের সৃষ্টি হয়। সৃষ্টি হয় ভাষার উপর ভিত্তি করে নব্য জাতীয়তাবাদ, যা প্রশাসনিক কাজকর্মে আরও বিঘ্ন সৃষ্টি করে।
💠পূর্ব এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া
চীনের বিরাট একটা অংশ এখনও পর্যন্ত মুসলিমদের রাজনৈতিক করতলে আসেনি। মধ্য এশিয়া থেকে শুরু করে মুসলিমরা পূর্ব তুর্কিস্তান (বর্তমানে সিন-কিয়াং প্রদেশ) পর্যন্ত ইসলাম পৌঁছাতে সক্ষম হয়েছিলো। এবং সম্ভবত, সমুদ্রপথে ভ্রমণ করে তারা দক্ষিণের ইউনান প্রদেশের স্থানীয় জনগণের বিশ্বাস অর্জন করতেও সক্ষম হয়েছিল। খুব সামান্য সময়ের জন্যই সেখানকার কর্তৃত্ব অর্জন করতে পেরেছিলো মুসলিমরা। তবে, মুসলিম ধর্মপ্রচারকদের উচ্চ আখলাকী মূল্যবোধে চীন-তিব্বতের লক্ষ লক্ষ মানুষ সর্বোপরি ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলো। যদিও চীনা জনসাধারণের বিশাল একটা অংশ এখনও পর্যন্ত ইসলামের একেশ্বরবাদী ধর্মের বাইরে রয়েছে।
দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার গল্পটা অবশ্য বেশ ভিন্ন। কয়েক শতাব্দী পূর্বে, দক্ষিণ আরবের পাশাপাশি দক্ষিণ ভারতের মুসলিম বণিকরাও মহাদেশের এই অংশে ভ্রমণ করেছিলেন এবং ধর্ম প্রচারের জন্য নিঃস্বার্থভাবে প্রচেষ্টা চালিয়ে গিয়েছিলেন। শুধু মালয় উপদ্বীপই নয়, এই অঞ্চলের হাজার হাজার দ্বীপও এখন প্রায় সম্পূর্ণরূপে ইসলামের ছায়াতলে এসেছে। ইন্দোনেশিয়া এবং ফিলিপাইনের দক্ষিণ দ্বীপপুঞ্জও এখন ইসলাম-প্রধান হয়ে উঠেছে। পরবর্তীতে, বেশ কয়েক খণ্ডে বিভক্ত হয়ে যাওয়ায় এই অঞ্চলটি ধীরে ধীরে ইউরোপীয়দের, বিশেষ করে ইংরেজ ও ওলন্দাজদের অধীনে চলে যায়। কয়েক শতাব্দীর বিদেশী আধিপত্যের পর, ইন্দোনেশিয়া তার 70 মিলিয়ন মুসলিম নিয়ে এখন তার স্বাধীনতা পুনরুদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছে। অন্যদিকে, মালয় উপদ্বীপ ব্রিটিশ কমনওয়েলথের সহযোগিতা নিয়ে শান্তিপূর্ণভাবেই তার সার্বভৌমত্ব অর্জন করতে পেরেছে।
💠আফ্রিকা
উত্তর আফ্রিকার মিশর থেকে মরক্কো পর্যন্ত সুবিশাল এই এলাকা প্রায় শুরুর দিক থেকেই ইসলামী খেলাফতের অধীনে ছিলো। এছাড়াও, মহাদেশটির অন্যান্য অঞ্চলের ভিন্ন ভিন্ন পদ্ধতির নিজস্ব উন্নয়নের ধারা ও ইতিহাস রয়েছে। আরবের নিকটবর্তী হবার কারণে পূর্ব আফ্রিকা স্বাভাবিকভাবে প্রথমেই ইসলাম দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলো। বিস্তীর্ণ ঐ অঞ্চল শুধু ইসলামের অধীনেই আসেনি, বরং সেখানে এখন উল্লেখযোগ্য গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি মুসলিম রাষ্ট্রও গড়ে উঠেছে।
অন্যদিকে, পশ্চিম আফ্রিকায় অনেক পরে ইসলাম পৌঁছলেও, স্থানীয় কয়েকজন মুসলিম শাসক স্থানীয় আদিবাসী সংস্কৃতির সাথে সামঞ্জস্য রেখেই ইসলাম প্রচারের প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে থাকেন। ফলে, অনেক আদিবাসী ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে। আর তাই, আফ্রিকার ইতিহাসের পাতা খুললে যে কেউ শত শত বছরের ইসলামী সভ্যতার দেখা পাবে।
আরব ইতিহাসবিদদের মতে, এই অঞ্চলের দুঃসাহসিক সামুদ্রিক অভিযাত্রীগণই সর্বপ্রথম আমেরিকা, বিশেষ করে ব্রাজিলে যাওয়ার পথ আবিষ্কার করেছিলো। কারণ, ক্রিস্টোফার কলম্বাস ও তার সাথীরা সেখানে গিয়ে এই নিগ্রো বাসিন্দাদেরই খুঁজে পেয়েছিলো।
মুসলিমদের অসংখ্য ঐতিহাসিক দলিল ধ্বংস হওয়া সত্ত্বেও সর্বপ্রথম মুসলিমদের আমেরিকার পথ আবিষ্কারের বিষয়টিকে বিশ্বাস করার কারণও রয়েছে।
মুসলিম আফ্রিকান এবং বারবার উপজাতির লোকেরা সর্বপ্রথম আমেরিকায় কলোনি স্থাপন করেছিলো। ব্রাজিল নামকরণের ঘটনা থেকেও বিষয়টির সত্যতা উঠে আসে। বারবার উপজাতিদের মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত, প্রসিদ্ধ ও জনবহুল ছিলো বিরজালাহ নামক উপজাতিটি। আর তাদেরকে একত্রে ব্রাজিল বলা হতো। এছাড়াও, বর্তমানে আটলান্টিকের পালমা দ্বীপটির পূর্বের নাম “বেনে হাওরে” করা হয়েছিলো বারবার উপজাতির আরেকটা অংশ বেনি হুওয়ারার নামানুসারে। এই ঘটনাগুলো মুসলিমদের প্রথম আমেরিকা আবিস্কারের মতামতকে শক্তিশালী করে তোলে।
মুসলিম স্পেনের পতন এবং ইউরোপীয়দের আমেরিকা যাত্রা শুরুর পূর্ব পর্যন্ত আমেরিকান এবং পশ্চিম আফ্রিকানদের মাঝে সুসম্পর্ক বজায় ছিলো। কিন্তু, পরবর্তীতে, আমেরিকার মতো আফ্রিকাকেও উন্নয়নের নামে ফ্রান্স, ব্রিটেন, জার্মানি, ইতালি, স্পেন, পর্তুগাল এবং বেলজিয়ামের মতো ইউরোপীয়দের হাতে অমানুষিক নির্যাতনের শিকার হতে হয়েছিলো।
এখনও আফ্রিকা মহাদেশের বিস্তীর্ণ একটা অঞ্চল ইসলামের আদালতপূর্ণ শাসনকার্যের সাথে পরিচিত না। তবে, উক্ত দেশগুলোর শোষকদের এবং পাশ্চাত্যের প্রভুদের রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে ইসলাম এখন ঐ স্থানগুলোতে ছড়িয়ে পড়ছে।
বর্তমানে, উন্নয়নের নামে লুটেপুটে খাওয়া এই নির্যাতনকারী শোষকদের উপনিবেশ থেকে ইসলামী সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশগুলো ক্রমান্বয়ে স্বাধীন হয়েছে, এবং হচ্ছে। যদিও, কিছু কিছু দেশকে এরপরও অমুসলিম স্বৈরশাসন ও নিপীড়নের শিকার হতে হয়েছে।
💠সমসাময়িক বিশ্ব
ইন্দোনেশিয়া থেকে মরক্কো পর্যন্ত প্রায় চল্লিশটিরও বেশি মুসলিম রাষ্ট্র রয়েছে, যারা ইতিমধ্যেই জাতিসংঘের সদস্য হয়েছে। যদি ইউরোপে আলবেনিয়া থেকে থাকে, তবে রাশিয়ার অভ্যন্তরে মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চল অবশ্যই রয়েছে। যারা তাদের স্বাধীন ও স্বায়ত্তশাসনের পাশাপাশি ইসলামের বিষয়টিকেও অগ্রাধিকার দিচ্ছে।
বৃটিশদের দ্বারা পরিচালিত কমনওয়েলথ সবার সামনে তুলে ধরে যে, কোনো এক মুসলিম রাষ্ট্রের গদিতে বসা নেতৃত্বস্থানীয় ব্যক্তিটি যদি বুদ্ধিমান হয় এবং তার ব্যক্তিস্বার্থের চেয়ে জাতির স্বার্থ প্রধান হয়ে দাঁড়ায়, তাহলে এক্ষেত্রে অমুসলিম রাষ্ট্রগুলোর সাথে বা দলে যোগদান করলেও নিজেদের স্বাধীনতায় কোনো প্রকার বাঁধা আসবে না। পাশাপাশি, উক্ত মুসলিম দেশটির সাথে অন্যান্য মুসলিম দেশ বা রাষ্ট্রের সম্পর্কের মাঝেও বিঘ্ন সৃষ্টি হবে না। যদি স্পেন, ফ্রান্স, রাশিয়া, ভারত, চীন এবং অন্যান্য মোড়ল দেশ তাদের উপর নির্ভরশীল মুসলিম দেশগুলোকে তথাকথিত পশ্চিমীয় প্রকৃত স্বায়ত্তশাসন সম্পর্কে বুঝাতে পারে, তাহলে আর কোনো স্বাধীনতা বা মুক্তির সংগ্রাম থাকবে না পৃথিবীতে এবং তখন, বিশ্বজনীন মঙ্গলের জন্য সকলেই ঐক্য, সংহতি ও সহযোগিতার ভেতরেই বসবাস করতে পারবে।
কয়েক শতাব্দীর দীর্ঘ সময় ধরে একমাত্র আমেরিকার রেড ইন্ডিয়ান ব্যতিত আর সকল জাতির নিকটই ইসলাম তার বাণী পৌঁছে দিতে সক্ষম হয়েছে।
কুরআন ও হাদীস-সহ ইসলামকে সঠিকভাবে বুঝতে হলে যে ভাষার প্রয়োজন, সেটা হলো আরবি। আর তাই, আরবরা এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ একটা অংশ দখল করে আছে। আবার, ইন্দো-পাকিস্তানি এবং মালয়-ইন্দোনেশিয়ানরা মুসলিম বিশ্বের সর্বাধিক জনসংখ্যার অধিকারী দুটি জাতি। এছাড়াও, সেই আদিকাল থেকেই আফ্রিকানরা নিজেদেরকে ইসলামের সাথেই সম্পৃক্ত রেখেছে। এমনকি, ভবিষ্যতে আফ্রিকানদের উত্থানের কথা স্বীকার করে নিয়েছে স্বয়ং পশ্চিমা দার্শনিক আর্নল্ড জে. টয়েনবি। তার ধারণামতে, ভবিষ্যতে যদি কখনও আফ্রিকান কালোরা নেতৃত্বের স্থানে বসে, সেটা অবাক হবার কোনো বিষয় নয়।
আসলে, আফ্রিকানরা সহ আর সব জাতির অভাবনীয় উত্থানের পেছনে রয়েছে ইসলামের অসামান্য অবদান। আর তাই, প্রতিনিয়তই মুসলিমদের সংখ্যা নিয়মিত বেড়েই চলছে এবং নওমুসলিমরা ইসলাম প্রচারে অসামান্য অবদান রাখছে।
বর্তমান বিশ্বে মুসলিমদের সঠিক জনসংখ্যা নিরূপণ করা সত্যিকারার্থেই কঠিন। কারণ, প্রতিনিয়তই জন্ম-মৃত্যুর ঘটনা ঘটেই চলছে। এছাড়াও, ধর্মান্তরের বিষয়টাও এখানে ধর্তব্য। এখানে একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে, ধর্মান্তরিত হবার পর অসংখ্য মানুষ তাদের ধর্মান্তরের বিষয়টি প্রকাশ না করে গোপণ রাখে।
তবে, বর্তমানে অর্জিত প্রমাণাদি থেকে একটা বিষয় উঠে আসে যে, হযরত আদম ও হাওয়া (আ.) এর বংশধরদের মধ্য থেকে এক-চতুর্থাংশ বা এক-পঞ্চমাংশ বনী আদম বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে দৈনিক পাঁচবার কিবলামুখী হয়ে “আল্লাহু আকবার” ঘোষণার মাধ্যমে নিজেদের আত্মপরিচয় তুলে ধরে।
অনুবাদ: আল আহসান মিফতাহ