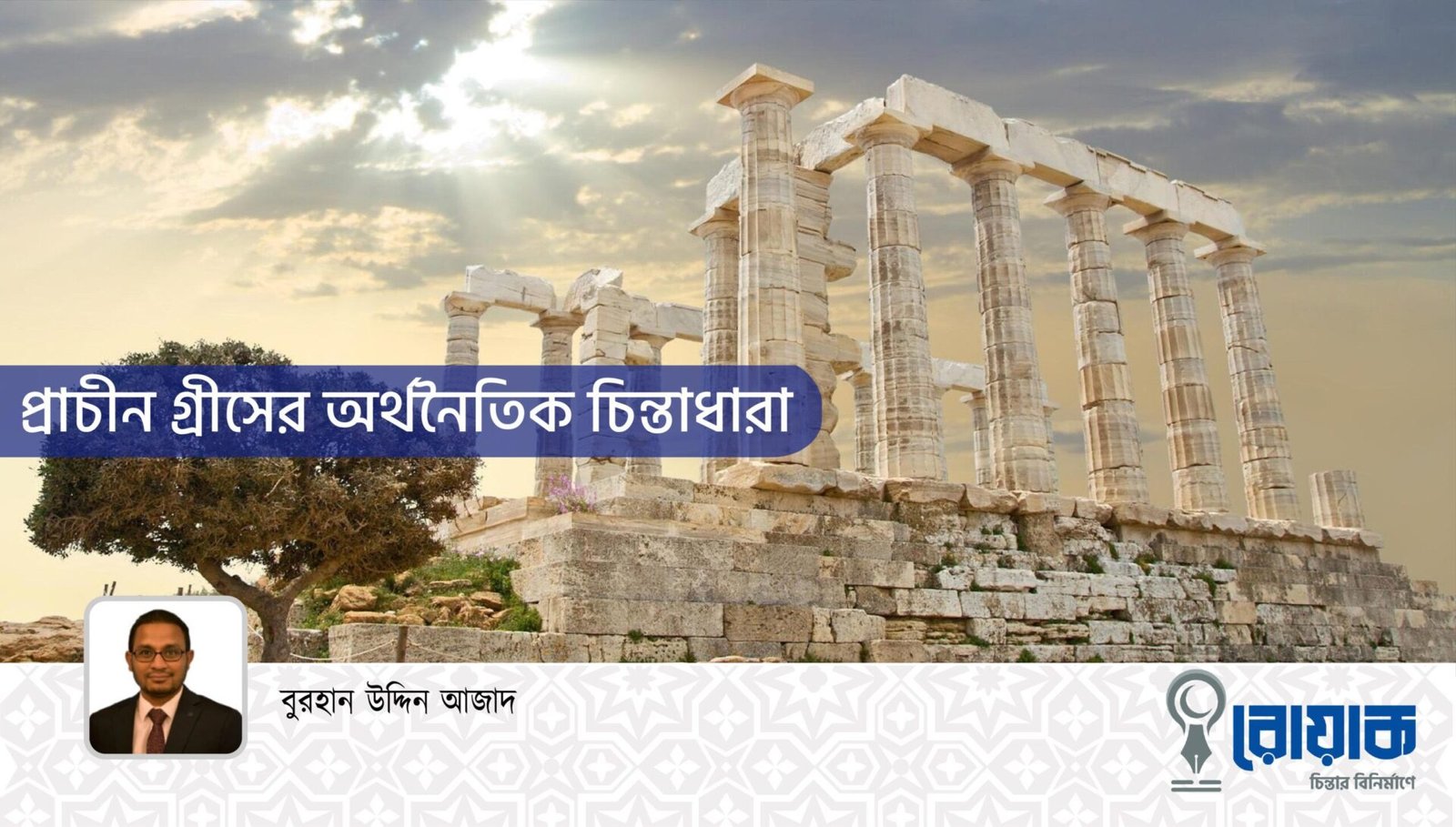প্রাচীন গ্রীসের অর্থনৈতিক চিন্তাধারা এর রাষ্ট্রব্যবস্থা; যাকে city state বলা হতো, তাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিলো। বিখ্যাত ঐতিহাসিক ও দার্শনিক জোসেফ শুম্পিটার এর মতে, প্রাচীন গ্রীসের চিন্তাধারা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে মানুষের জীবনের বাস্তবিক বিষয়াবলীকে গুরুত্ব দিতো। এই চিন্তাধারা গড়ে উঠেছিলো polis এর উপর ভিত্তি করে। গ্রীক সভ্যতার মতাদর্শ অনুযায়ী, সভ্যতার প্রাণকেন্দ্র এবং প্রতিফলিত রূপ হচ্ছে পলিস। সভ্যতা কেবল পলিসে’ই গড়ে তোলা সম্ভব। polis একটি পরিভাষা। এর মাধ্যমে গ্রীসে city state, শহর এবং এই শহর ও city state এর প্রশাসনিক ব্যবস্থাকে বোঝাতো। প্রাচীন গ্রীক সভ্যতায় অর্থনৈতিক বা অন্যান্য বিষয়ের উপর সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেয়া হতো রাজনৈতিক ব্যবস্থা বা রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে। এর কারণ হলো polis কে কেন্দ্রে রাখা। অর্থনীতিকে তারা কম গুরুত্ব দেয়ার কারণ হলো অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডসমূহ বেশিরভাগ পরিচালনা করতো slave (দাস) এবং patricians; যাদের তারা নাগরিক হিসেবে গণ্য করতোনা। ফলে গ্রীক দার্শনিকদের চিন্তাধারায় অর্থনীতির সেরকম কোন থিওরি পাওয়া যায়না। যেগুলো পাওয়া যায় তা তাদের রাষ্ট্রবিজ্ঞানের থিওরির মধ্যে থেকে।
প্লেটোর মতে রাষ্ট্রের মৌলিক কাজ হলো দুটি:
১. শাসক নির্বাচন করা
২. নির্বাচিতদের নিয়ন্ত্রণ ও পর্যবেক্ষণ করা।
তবে তাদের আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ আলোচ্য বিষয় ছিলো city state বা ঘর পরিচালনা। এ বিষয়টি নিয়ে Xenophon সর্বপ্রথম তার রচিত গ্রন্থ Oikonomikos এ আলোচনা করেন। oikos বলতে বুঝায় ‘গৃহ বা ঘর’, nomos বলতে বুঝায় ‘আইন বা রীতি’। অর্থাৎ Oikonomikos বলতে বুঝায় গৃহ পরিচালনার রীতি।
প্রাচীন গ্রীসে অর্থনৈতিক কার্যক্রমকে তারা marketing approach নয়, বরং administrative approach এ চিন্তা করতো। মার্কেটিং অ্যাপ্রোচ হলো উৎপাদন ও কেনা-বেচার সাথে সংশ্লিষ্ট। তারা তাদের অর্থনৈতিক চিন্তাকে এই কেন্দ্রিক না করে গৃহস্থালির বা রাষ্ট্রের কর্মকান্ড কীভাবে পরিচালিত হচ্ছে তার ভিত্তিতে দাঁড় করিয়েছে।
প্রাচীন গ্রীসে ব্যবসা ও প্রযুক্তির উন্নয়ন না হওয়ার কারণ সম্পর্কে বিখ্যাত ঐতিহাসিক M. Finley বলেন, তারা ব্যবসায়িক পন্থায় সম্পদ উপার্জনকে খুব বেশি পছন্দ করতোনা। পাশাপাশি যেহেতু তাদের অর্থনৈতিক কর্মকান্ড দাস এবং প্যাট্রিসিয়ানদের হাতে ছিলো, যারা গ্রামে বাস করতো এবং নাগরিক হিসেবে বিবেচিত হতোনা, তাই এরিস্টোক্র্যাটদের এটা নিয়ে মাথাব্যাথা ছিলোনা। এর ফলে প্রাচীন গ্রীস এবং রোমান সভ্যতায় ব্যবসা ও প্রযুক্তির সেরকম কোন উন্নতি সাধিত হয়নি৷
এরিস্টোক্র্যাটরা আইন ও রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ত থাকতো। এর মাধ্যমে যেহেতু তারা অর্থনৈতিক কার্যক্রমকে নিয়ন্ত্রণ করতো, এর দ্বারাই তারা সম্পদ উপার্জন করতো।
Xenophon (খ্রীস্টপূর্ব ৪৩০- ৩৫৪ খ্রী) তিনি মূলত এথেন্সের একজন ঐতিহাসিক। তিনি ভাড়াটে সৈন্য ছিলেন। টাকার বিনিময়ে যুদ্ধ করতেন। সক্রেটিসের যুগের ছিলেন বলে তিনি সক্রেটিসের ও ছাত্র ছিলেন। সক্রেটিসের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দর্শনকেই মূলত লিখিতভাবে Oikonomikos/ ওইকনমিয়া গ্রন্থে তুলে ধরেছেন। এই গ্রন্থের মূল আলোচ্য বিষয় গৃহাস্থলির কার্যক্রম কীভাবে পরিচালিত হয়। এই গ্রন্থটি যতটা না অর্থনীতির, তার চেয়ে বেশি রাজনৈতিক দর্শনের গ্রন্থ। এখানে তিনি সম্পদ উৎপাদন ও বন্টন নীতি নিয়ে আলোচনা করেছে। তিনি বলেন, যেহেতু সম্পদ সীমিত বা স্থিতিশীল; এর উৎপাদন ও বন্টনের ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখবে নেতারা। এখানে মূল ভিত্তি হলো man-power বা শ্রমশক্তি। বাড়ি, খামার বা ফার্ম যাই হোকনা কেন পরিচালকের পন্থার উপর বন্টননীতি নির্ভর করে। এক্ষেত্রে কর্মবন্টনের চেয়ে পেশাগত দক্ষতাকে তিনি বেশি গুরুত্ব দেন। যার পেশাগত দক্ষতা যত বেশি সে উৎপাদনের ক্ষেত্রে তত বেশি ভূমিকা রাখে এবং ঐ উৎপাদনের বন্টন ব্যবস্থাও সুন্দর হয়। অর্থাৎ এখানে Xenophon কর্মবন্টনের চেয়ে administration/ প্রশাসনিকভাবে পরিচালনা ও পেশাগত দক্ষতাকে বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন।
Xenophon এর আরেকটি বিখ্যাত গ্রন্থ হচ্ছে Cyropedia. তিনি যখন ভাড়াটে সৈন্য হিসেবে পারস্য সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে যান, তখন পারস্য সম্রাটের নেতৃত্ব ও যোগ্যতা নিয়ে এই বইটি লিখেন। এই বইয়ের কারণেই মূলত তাকে ঐতিহাসিক বলা হয়।
Oikonomikos এর আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ আলোচ্য বিষয় Subjective value theory. এবিষয়টি পরবর্তীতে এরিস্টটল বিশদভাবে আলোচনা করেছেন।
তার চিন্তার আরেকটি দিক হলো, উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য দাস এবং প্যাট্রিসিয়ানদের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করতে হবে। এজন্য আমাদের সিটি স্টেইটকে উন্নত এবং আকর্ষণীয় স্থানে পরিণত করতে হবে। ফলত সারা দুনিয়া থেকে দাস এবং প্যাট্রিসিয়ানরা আমাদের এখানে কাজ করতে আসবে। আজকের পাশ্চাত্যকেও এ নীতি অনুসরণ করতে দেখা যায়।
প্লেটোর চিন্তাধারা:
প্লেটোর (খ্রিষ্টপূর্ব ৪২৭- খ্রিষ্টপূর্ব ৩৪৭) আরবী নাম আফলাতুন। তিনি মূলত সক্রেটিসের ছাত্র ছিলেন। আখলাক, দর্শন, মানতিক, রাজনৈতিক দর্শন, গণিত সব কিছু নিয়েই তিনি কাজ করেছেন৷ তবে সবচেয়ে বিখ্যাত হয়েছেন তার রিপাবলিক এর জন্য। রিপাবলিক এর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচ্য বিষয় আইডিয়াল স্টেইট (আদর্শ রাষ্ট্র) এবং কর্মবণ্টন। এখানে তিনি সবচেয়ে বেশি আলাপ করেছেন আদালত নিয়ে৷ তিনি বলেছেন মানুষের জীবনের সবচেয়ে বড় উদ্দেশ্য হলো ফযিলতপূর্ণ জীবন৷ তার মতে ফযিলতপূর্ণ সমাজ কেবল আদালতের মাধ্যমেই প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব৷
রিপাবলিক এর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ পরিভাষা হলো ইউটোপিয়া। এখানে তিনি ইউটোপিয়া বলতে অলীক কল্পনাকে বুঝাননি। এখানে ইউটোপিয়া বলতে সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য মানুষের যে চিন্তাভাবনা, তাকে বুঝিয়েছেন। প্লেটোর ইউটোপিয়া হচ্ছে, একটি আইডিয়াল স্টেইট প্রতিষ্ঠা করতে হবে, এবং এর জন্য যে আখলাকী আদর্শগুলো প্রয়োজন সেগুলোকে রাজনৈতিকভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে।
প্লেটোর মতে রাষ্ট্রের মৌলিক দায়িত্ব ৩ টি:
- ১. মানুষের মৌলিক চাহিদা পূরণ
- ২. রাষ্ট্রকে রক্ষা করা (defense system)
- ৩. প্রশাসন (administration)
আদর্শ রাষ্ট্রের জনগণকে তিনি ৩ ভাগে ভাগ করেন:
- ১. যারা রাষ্ট্রকে রক্ষা করে
- ২. সৈন্যবাহিনী
- ৩. সাধারণ জনগণ
প্লেটোর এই বন্টন বর্ণপ্রথার ভিত্তিতে ছিলোনা, বরং পেশার ভিত্তিতে ছিলো। তার মতে, যদি কেউ জন্মগতভাবে দাস না হয়ে থাকে, তাহলে নিজ যোগ্যতায় সে রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ পদেও অধিষ্ঠিত হতে পারে৷ অর্থাৎ তিনিও দাসপ্রথাকে সমর্থন করেছেন।
প্লেটোর মতে রাষ্ট্র যারা পরিচালনা করবে, তারা প্রাইভেট সম্পদ বা সম্পদের ব্যক্তিমালিকানার অধিকারী হতে পারবেনা; তারা কোন ধরণের অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ করবেনা। তারা একটি ন্যূনতম স্ট্যান্ডার্ড এর জীবন যাপনের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ রাষ্ট্র থেকে বেতন নিবে৷ খুব বেশি ধনী বা খুব বেশি দরিদ্র হওয়া মানুষের ফিতরাতের পরিপন্থী।
এরিস্টটলের চিন্তা:
এরিস্টটল পৃথিবীর ইতিহাসের অন্যতম সেরা একজন চিন্তাবিদ। রসায়ন, জীববিজ্ঞান, পদার্থবিজ্ঞান, আখলাক, ইতিহাস, মানতিক, মেটাফিজিক্স, রেটোরিক, পদার্থবিজ্ঞান, ফিলোসোফি অব সায়েন্স, ফিলোসোফি অব মাইন্ড, সাইকোলজি, ভূতত্ব; এককথায় জ্ঞানের প্রায় সব ক্ষেত্রেই তার নিজস্ব চিন্তা রয়েছে। মেটাফিজিক্স এর মতো বিষয়েও তার গ্রন্থ রয়েছে। নিকোমাখেন এথিক্স এ তিনি soul, virtues, partnership এবিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করেছেন। পলিটিক্স এর ক্ষত্রে সংবিধান, বেইজ স্টেইট, বিপ্লব এসকল বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন৷ রেটোরিক এ আলোচনা করেছেন রাজনৈতিক বিতর্ক নিয়ে। পোয়েট্রিক্স এ তিনি আলোচনা করেছেন ট্র্যাজেডি এবং এপি-পোয়েট্রি নিয়ে৷ জীবজন্তুর ইতিহাস, প্রজন্ম, গতিবিধি নিয়ে কাজ করেছেন। তার ছাত্র আলেকজান্ডার দ্যা গ্রেট তাকে এ সংক্রান্ত গবেষণার জন্য একটি আলাদা বন প্রতিষ্ঠা করে দিয়েছিলেন। লজিক বা যুক্তিবিদ্যার ক্ষেত্রে তিনি categories, interpretation, prior of analysis, posterior of analysis এসকল বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন। এরিস্টটলের জ্ঞান চর্চার মেথড হচ্ছে এম্পিরিকাল বা গবেষণামূলক। তিনিই প্রথম বিজ্ঞানী যিনি প্রকৃতিকে এভাবে পরখ করে দেখেছেন।
পাশ্চাত্যের অধিকাংশ চিন্তাবিদই এরিস্টটলকে অর্থনৈতিক চিন্তার জনক মনে করে থাকেন। মূলত তার দুটি বইয়ে অর্থনৈতিক চিন্তা পাওয়া যায়। একটি হলো Politics (Politica), আরেকটি Nicomachean ethics.
পলিটিক্সের প্রথম এবং পঞ্চম অধ্যায়ে তিনি অর্থনীতি নিয়ে আলোচনা করেছেন।
Nicomachean ethics এ মূলত আখলাকের আলোচনার মধ্যে অর্থনৈতিক বিষয়ের আলোচনা এসেছে৷
এরিস্টটল এবং প্লেটোর চিন্তার মৌলিক পার্থক্য হচ্ছে এনালিটিক্যাল থিংকিং। এনালিটিক্যাল থিংকিং এ মূলত ডিডাকটিভ মেথড ব্যবহৃত হয়। এরিস্টটল তার প্রত্যেকটি গ্রন্থে মানতিককে ভালোভাবে ব্যবহার করেছেন এবং তার প্রত্যেকটি তত্ত্বকে তিনি কারণ এবং ফলাফল (cause and effect) এর মাধ্যমে ব্যাখ্যা করেছেন। জোসেফ শুম্পিটারের মতে, এনালিটিক্যাল হিস্ট্রি অব ইকোনমিকস এর দৃষ্টিকোণ থেকে এরিস্টটল গুরুত্বহীন একজন চিন্তাবিদ। এবং তার মতে, এরিস্টটল প্রাচীন গ্রীক রাষ্ট্রের সিটি স্টেইট এবং এর ব্যবস্থাপনার আখলাকী বিষয় নিয়ে বেশি আলোচনা করেছেন। অর্থনৈতিক বিষয়গুলো এই প্রশাসনিক এবং আখলাকী চিন্তার একটা অংশ৷ অর্থাৎ, এরিস্টটলের চিন্তাধারা মৌলিকভাবে অর্থনৈতিক চিন্তাধারা নয়। বর্তমান ফিলোসফি অব সায়েন্সের অন্যতম দাবী হলো বিজ্ঞানকে অবশ্যই value free হতে হবে। এখানে কোন নরম্যাটিভ বিষয় আসবেনা। অর্থনীতি যেহেতু নিজেকে বিজ্ঞান বলে দাবী করে, তাই এখানেও আখলাক আলোচ্য বিষয় নয়। এজন্য ন্যায়-অন্যায় বা এধরণের কোন প্রশ্ন আসতে পারবেনা। অথচ সায়ন্স ও একটা আদর্শ অনুসরণ করে। সায়েন্সের আদর্শ হচ্ছে পজিটিভিজম।
এরিস্টটলের মতে রাষ্ট্র হচ্ছে মানুষের সবচেয়ে বড় অর্জন। তার মতে, “রাষ্ট্র হলো একটি আখলাকী উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে মানুষ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত একটি ঐক্যবদ্ধ ব্যাবস্থাপনা।” সময়গত দিক বিবেচনায় পরিবার ও সমাজ রাষ্ট্রের আগে আসলেও রাষ্ট্র হচ্ছে সর্বোচ্চ পর্যায়। এরিস্টটলের মতে রাষ্ট্র হচ্ছে একটি প্রাকৃতিক বিষয়। তিনি মনে করেন স্বভাবগতভাবেই মানুষ রাজনৈতিক সত্ত্বা। মানুষ তার মৌলিক চাহিদা পূরণের জন্যই রাষ্ট্র গঠন করে থাকে। রাষ্ট্র বা সিটি স্টেইটকে এরিস্টটল পলিস বলে থাকেন। তার মতে ভালো এবং খারাপের সাথে সংশ্লিষ্ট আবেগ-অনুভূতিও এখানে গুরুত্বপূর্ণ। এরিস্টটলের মতে ভালো মানুষ তিনিই যিনি রাষ্ট্রের আইন এবং বিধানকে ভালোভাবে পালন করে থাকেন। আর ফযিলতপূর্ণ মানুষ তিনি, যিনি আদালত সম্পর্কে ভালোভাবে ধারণা রাখেন। আদালত হচ্ছে রাষ্ট্রের মেরুদন্ড।
এরিস্টটল মনে করেন সম্পদ দুইভাবে উপার্জন করা যায়:
- মানুষের জরুরি প্রয়োজন পূরণের জন্য (যেগুলো পশুপালন এবং কৃষিকাজের সাথে সম্পৃক্ত)
- অর্থ-সম্পদকে পুঞ্জিভুত করে রাখার জন্য সম্পদ উপার্জন (ব্যবসা ও প্রয়োজনহীন ক্রয়-বিক্রয়ের মাধ্যমে)
প্রথমটিকে তিনি Oikonomikos এবং দ্বিতীয়টিকে Chrematistics বলে অভিহিত করেন। দ্বিতীয়টিকে তিনি খারাপ কাজ হিসেবে দেখেন। বর্তমানে আমরা যে অর্থনীতি দেখি তাকে Chrematistics এর একটি প্রতিশব্দ বলা যায়। সতেরশো শতাব্দীর দিকে এটি political economy নামে পরিচিত ছিলো। ঊনবিংশ শতাব্দীতে এসে এই নামে পরিচিত হয়। অর্থাৎ আমরা বর্তমানে যাকে অর্থনীতি বলে থাকি, সেটি প্রাচীন গ্রীসের Chrematistics এর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ যা এরিস্টটলের মতে এক অর্থে অবৈধ বলা যায়।
ক্যাসেনোফন, প্লেটো সবার মতেই রাষ্ট্রের দায়িত্ব হল নাগরিকদের একটি সুখী-সমৃদ্ধশালী, ভালো জীবন দিতে হবে৷ আর এটা করা যায় একমাত্র শহরের মাধ্যমে। শহরে বসবাসকারী মানুষরাই একমাত্র ভালোভাবে জীবনযাপন করতে পারে। যেহেতু ব্যবসার দ্বারা কোন উৎপাদন করা যায়না, এজন্য এরিস্টটল এর পক্ষে নন। এছাড়াও তার মতে, যেহেতু ব্যবসার মাধ্যমে সীমাহীন সম্পদ উপার্জন করা যায়, তাই এটি অবৈধ।
Value Theory:
এরিস্টটলের মতে, যেসব সম্পদকে ব্যক্তি কর্তৃক উপার্জন করা সম্ভব, এর প্রত্যেকটির সাথে দুটি মূল্য সংশ্লিষ্ট আছে:
- ১. ব্যবহারিক মূল্য
- ২. বিক্রয় মূল্য
ব্যবহারিক মূল্য হলো, জিনিসটি ব্যবহার করে মানুষের কতটুকু প্রয়োজন পূরণ হচ্ছে তার পরিমাপ। আর বিক্রয়মূল্য হচ্ছে ক্রেতা কর্তৃক নির্ধারিত মূল্য। এটি ব্যবহারের উপযোগিতার উপর নির্ভর করেনা। যেমন, পানির অপর নাম জীবন হওয়া সত্বেও পানি অত্যন্ত সস্তা। কিন্তু ডায়মন্ডের সেরকম কোন প্রয়োজনীয়তা না থাকা সত্ত্বেও এটা এত মূল্যবান। এই মূল্য ক্রেতা কর্তৃক নির্ধারিত মূল্য।
এরিস্টটল তার Nicomachean ethics এ এবিষয়ে আলোচনা করেছেন। তার মতে, কোন দ্রব্যের ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে ভারসাম্য থাকতে হবে। কোন সম্পদ দুষ্প্রাপ্য হলেই বা ক্রেতা কর্তৃক মূল্য বেশি দিতে চাইলেই তার মূল্য বাড়ানো যাবেনা। একটা ভারসাম্য রাখতে হবে। এরিস্টটল এখানে ভ্যালু থিওরি নিয়ে আলোচনা করেননি।
তার আলোচনার আরেকটি বিষয় ছিলো সম্পদের মালিকানা বা মুলকিয়াত। এক্ষেত্রে তিনি ব্যক্তি মালিকানাকে স্বীকার করেছেন। অর্থাৎ মানুষকে সম্পদ অর্জনের ক্ষেত্রে মালিকানার অধিকার দিতে হবে। এটা সমষ্টিগত নয়, ব্যক্তিগত হতে হবে। যদি কোন সম্পদের সমষ্টিগত মালিকানা থাকে, তা একইসাথে সমাজের ভারসাম্য নষ্ট করে এবং উৎপাদনকে ব্যহত করে। এর একটা কারণ হলো নাগরিকদের ভালো বা সুন্দর জীবনযাপন ব্যক্তি মালিকানাধীন সম্পদের উপর নির্ভর করে। কারণ ব্যক্তিমালিকানার অধীনে সম্পদ না থাকলে সে তার মৌলিক অধিকার পূরণে প্রয়োজনমতো তা ব্যবহার করতে পারবেনা।
ফলশ্রুতিতে সমাজের মানুষ সুখী হতে পারবেনা। ক্যাসেনোফন, প্লেটো সবার মতেই, মানুষের জন্য সুখী-সমৃদ্ধ জীবন নিশ্চিত করা জরুরি। এখানে আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, দাস-দাসীরাও কি এই ব্যক্তি মালিকানার অন্তর্ভুক্ত হবে কিনা? এরিস্টটলের মতামত হলো, মানুষ দুই ধরণের; স্বাধীন মানুষ এবং গোলাম। যারা স্বাধীন হয়ে জন্ম গ্রহণ করে তারা মূলত নেতৃত্ব দেয়ার জন্য বা সমাজ পরিচালনার জন্য জন্ম গ্রহণ করে। আর দাস-দাসীদের জন্ম হয় স্বাধীন মানুষদের সেবা করার জন্য। ফলে এরিস্টটলের মতানুযায়ী, এই দাস-দাসীরাও মানুষের ব্যক্তিমালিকানাধীন সম্পদে রূপান্তরিত হয়। এরিস্টটল মূলত তিনি যে সমাজে বসবাস করতেন, সে সমাজের ব্যবস্থাপনাকে বৈধতা দেয়ার জন্য আদর্শিক একটা দৃষ্টিকোণ থেকে এভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। এর কোন প্রায়োগিক বা মানতিকী ব্যাখ্যা নেই। তার কোন এনালিটিক্যাল থিওরিই এটিকে সিদ্ধ করেনা। এটি পুরোপুরিই তৎকালীন রাষ্ট্রব্যবস্থা এবং পরিবেশের সাথে সংশ্লিষ্ট।
এরিস্টটলের মতে, টাকার কোন নমিনাল ভ্যাল্যু নেই। এর মূল্য রাষ্ট্র কর্তৃক নির্ধারিত। টাকা হচ্ছে শুধুমাত্র মুবাদালা করার মাধ্যম। সে নিজে কোন ভ্যালু বহন করেনা। সুদ হচ্ছে টাকা থেকে টাকা উপার্জন করা। যেহেতু এখানে কোন উৎপাদন হচ্ছেনা, তাই তার মতে অর্থ উপার্জনের সবচেয়ে ঘৃণিত মাধ্যম হচ্ছে সুদ। এমনকি এটি প্রকৃতিবিরুদ্ধ একটি কাজ। এটি সমাজের ভারসাম্যকে নষ্ট করে। অর্থাৎ আদালতের দৃষ্টিকোণ থেকে তিনি এটাকে অবৈধ মনে করেছেন।
প্রাচীন গ্রীসের অর্থনীতিকে আমরা মোটের উপর এই তিনজন ব্যক্তির চিন্তা দিয়ে ব্যাখ্যা করতে পারি।
সংকলকঃ নাজিয়া তাসনিম।