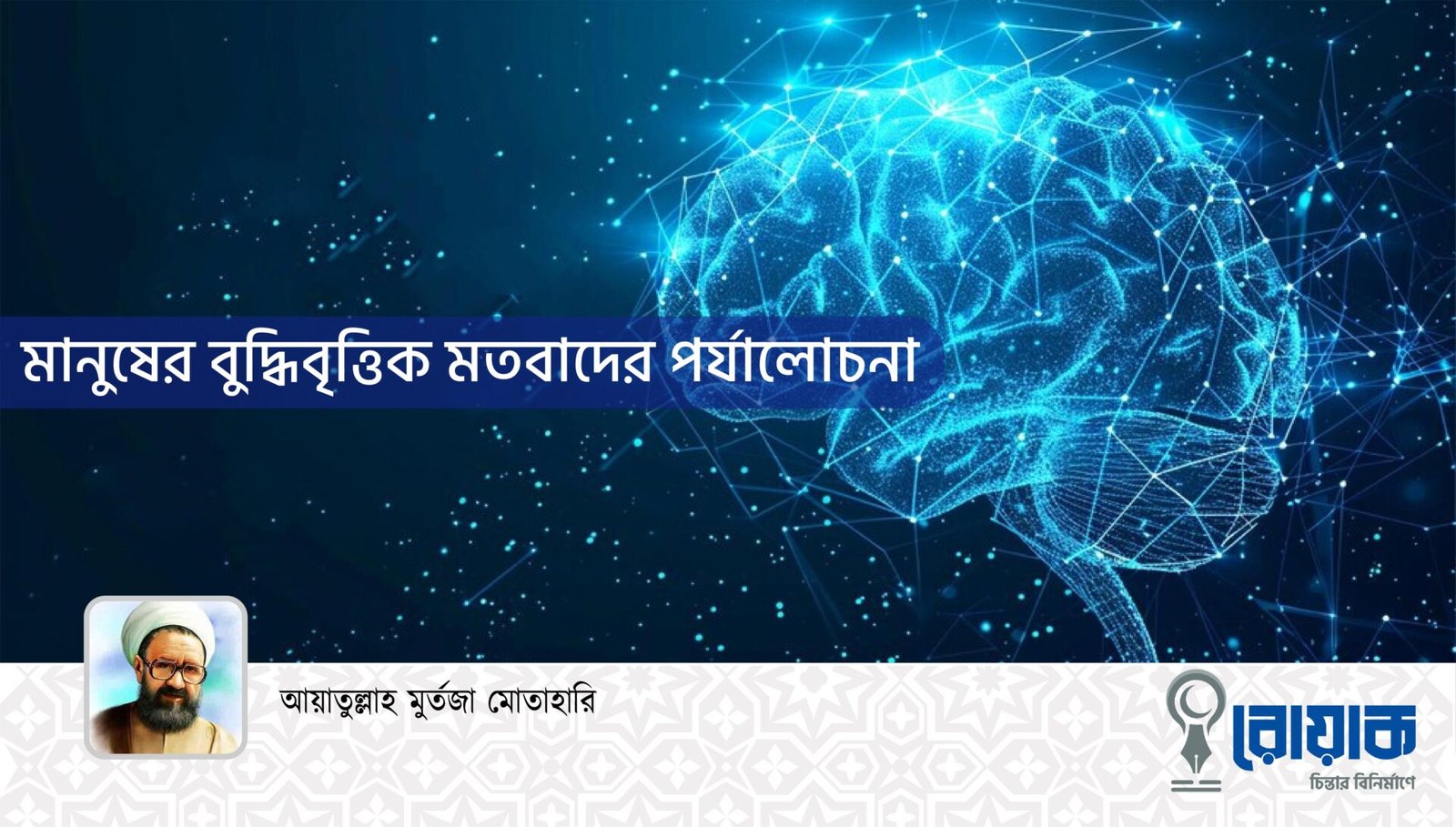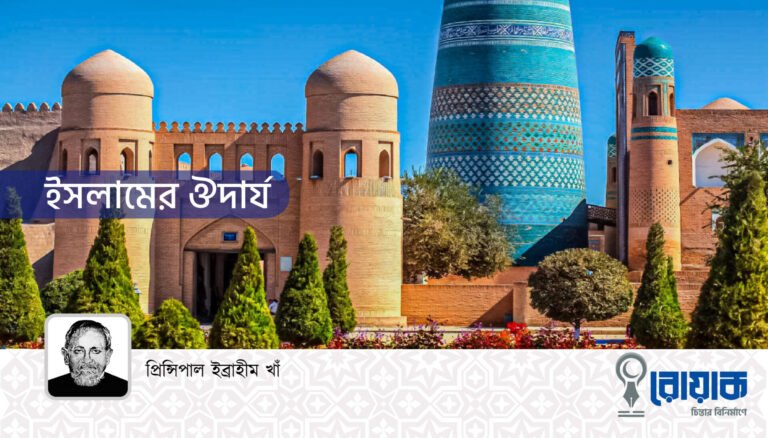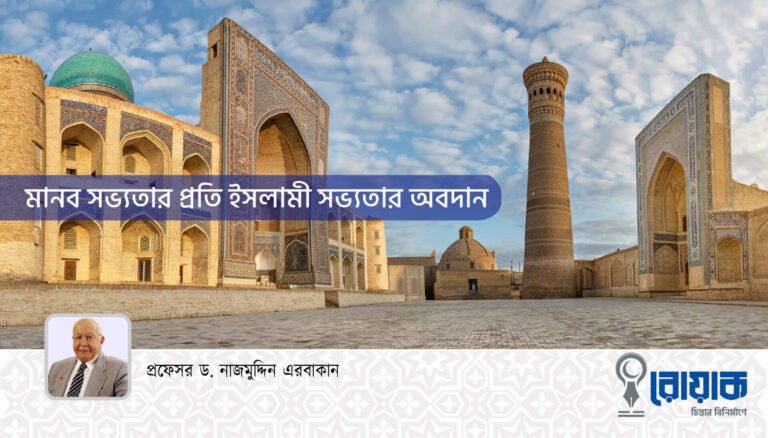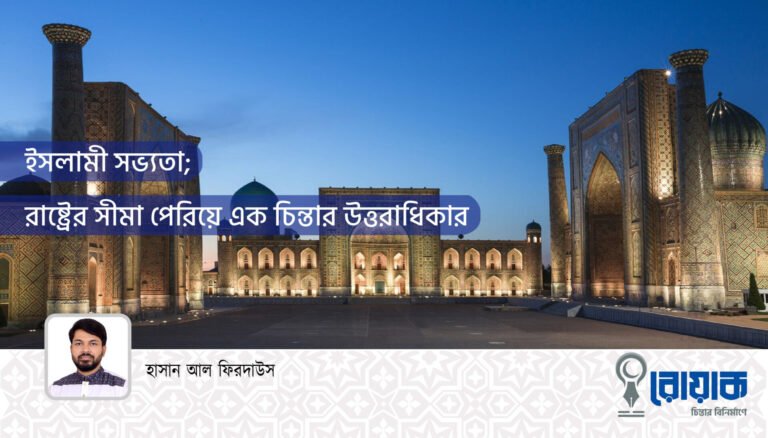পূর্ণ মানব (আদর্শ মানব) কে, তা জানা একটি অপরিহার্য বিষয়। ব্যক্তির প্রশিক্ষণ ও চরিত্র গঠনের জন্য প্রতিটি মতাদর্শেই আদর্শ মানবের দিকে দৃষ্টি দেয়া হয়। যেহেতু আমরা ইসলামের পূর্ণ ও আদর্শ মানবের প্রতিকৃতি ও স্বরূপ জানতে চাই, সেহেতু প্রচলিত অন্য সব মতবাদের আদর্শ মানবের প্রকৃতির পর্যালোচনার পর এ বিষয়ে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরব। গত দিনের আলোচনায় বিভিন্ন মতবাদ সংক্ষিপ্তভাবে আলোচনা করেছি। আজকে আমাদের আলোচনা বুদ্ধিবৃত্তিক মতবাদ দিয়ে শুরু করব।
বুদ্ধিবৃত্তিক মতবাদের সার–সংক্ষেপ
প্রাচীন দার্শনিক ভাবনায় মানুষের অস্তিত্বের মূল বিষয় ছিল তার বুদ্ধিবৃত্তি। তাদের মতে, মানুষের আমিত্ব হলো তার বুদ্ধিবৃত্তি বা আকল। যেমনভাবে মানবদেহ তার ব্যক্তিত্বের অংশ নয় তেমনিভাবে তার আত্মিক ও মানসিক শক্তি ও ক্ষমতা তার ব্যক্তিত্বের প্রকৃত সত্তা নয়। মানুষের ব্যক্তিত্বের মূল হলো তার চিন্তা করার শক্তি ও ক্ষমতা, মানুষের প্রকৃত সত্তা হলো যা দ্বারা সে চিন্তা করে।
মানুষ যা দ্বারা চোখে দেখে তা চিন্তার একটি উপকরণ মাত্র, তেমনি যা দ্বারা কল্পনা করে, যা দ্বারা চায়, যা দ্বারা ভালোবাসে বা মানুষ যে সত্তার কারণে জৈবিক চাহিদার অধিকারী, এ সবই চিন্তা সত্তার একেকটি উপকরণ। মানব সত্তার মৌল উপাদান তার চিন্তাশক্তি। তাই পূর্ণ মানব তিনিই, যিনি চিন্তার ক্ষেত্রে পূর্ণতায় পৌছেছেন। চিন্তার ক্ষেত্রে পূর্ণতায় পৌছার অর্থ বিশ্ব ও অস্তিত্বজগতকে ঠিক যে রূপে আছে সে রূপেই উদঘাটন করা ও জানা।
এ মতবাদ বুদ্ধিবৃত্তি বা আকলকে মানব সত্তার মৌল উপাদান বলে জানে। এ ছাড়াও বিশ্বাস করে যে, বুদ্ধিবৃত্তি বা চিন্তা-শক্তির দ্বারা বিশ্বকে তার প্রকৃত রূপে উদঘাটন করা সম্ভব। আকল বা বুদ্ধিবৃত্তি অস্তিত্বজগতকে তার আসল রূপে নিজের মধ্যে প্রতিফলিত করার ক্ষেত্রে সক্ষম। ঠিক আয়নার মত বিশ্বজগৎ তার প্রকৃত রূপ নিয়ে এতে প্রতিফলিত হয়।
ইসলামের দার্শনিক সমাজে যারা এ ধারণাকে গ্রহণ করেছেন তাঁরা বিশ্বাস করেন যে, ইসলামের দৃষ্টিতে ও কোরআনের আলোকে ঈমান বলতে বিশ্বকে ঠিক যেমনভাবে আছে তেমনভাবে জানার কথাই বোঝানো হয়েছে। ঈমান অর্থ বিশ্বজগতের স্রষ্টা, বিশ্বে বিরাজমান শৃঙ্খলা, প্রচলিত বিধান, বিশ্বের গতি ও লক্ষ্য এগুলোকে জানা। তাঁরা বলেন, কোরআনে যে আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস, ফেরেশতাগণের প্রতি বিশ্বাস, বিশ্বজগৎ আল্লাহর সৃষ্টি এ বিষয়ে বিশ্বাস, আল্লাহ্ বিশ্বজগতকে লক্ষ্যহীন ছেড়ে দেননি, বরং একে হেদায়েত ও পরিচালনা করছেন, যেমন নবী-রাসূলগণের মাধ্যমে মানুষকে হেদায়েত করছেন তা জানা, সবকিছু আল্লাহ্ থেকে এসেছে এবং তাঁর প্রতিই প্রত্যাবর্তনকারী প্রভৃতি- এ বিষয়গুলোতে বিশ্বাস স্থাপনের অর্থ হলো বিশ্বজগতকে তার প্রকৃতরূপে জানা। তাঁরা ঈমানকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন, ঈমান জ্ঞান ও প্রজ্ঞা ব্যতীত কিছু নয়। অবশ্য তাঁদের এ প্রজ্ঞা বা জ্ঞানের অর্থ বৈজ্ঞানিক জ্ঞান বা আংশিক জ্ঞান নয়, বরং এ জ্ঞান দার্শনিক ও প্রজ্ঞাগত। দার্শনিক জ্ঞানের অর্থ বিশ্বের উৎপত্তি ও পরিসমাপ্তি, অস্তিত্বের ধারা ও পর্যায়কে সামগ্রিকভাবে জানা ও উদঘাটন করা।
এ মতাদর্শের বিপরীত মতবাদ
এ মতাদর্শ যা বুদ্ধিবৃত্তিক মতবাদ বলে আমরা উল্লেখ করেছি এর বিপরীতে বেশ কিছু মতবাদ রয়েছে যেগুলো এ মতবাদের বিরোধী ও সমালোচক। মুসলিম বিশ্বে প্রথম যে মতবাদটি এ মতবাদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে, সেটা হলো ইশরাকী-সূফী-খোদাপ্রেমী মতবাদ। এরপর রয়েছে আহলে হাদীসের অনুসারীরা। শিয়াদের মধ্যে আখবারী এবং সুন্নীদের মধ্যে হাম্বলী ও আহলে হাদীসগণ আকলের ক্ষেত্রে দার্শনিকদের অস্বীকার করেছে। তাঁরা বলছেন, দার্শনিকরা আকল বা বুদ্ধিবৃত্তির ব্যাপারে যত বেশি গুরুত্ব দেয় আকলের গুরুত্ব এত অধিক নয়।
এদের থেকেও ইন্দ্রিয়বাদীরা বর্তমান সময়ে বুদ্ধিবৃত্তির চরম সমালোচক। বিগত তিন-চার শতক ধরে ইন্দ্রিয়বাদীদের জয়-জয়কার। তাদের মতে, বুদ্ধিবৃত্তিকে যতটা মূল্য দেয়া হচ্ছে, তা এতটা মূল্যের অধিকারী নয়। আকলের তেমন কোনো গুরুত্ব নেই, বরং আকল ইন্দ্রিয়ের অনুগত। মানবের মূল তার ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়জাত অনুভূতিসমূহ। আকল খুব বেশি হলে যা করতে পারে তা হলো ইন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞানের উপর কাজ করা। যেমন কোনো কারখানার কথা যদি আমরা চিন্তা করি, সেখানে কাঁচামাল প্রবেশ করে, তারপর কারখানার মেশিনের মধ্যে তা মিশ্রিত হয়ে বিভিন্ন রুপ ধারণ করে। উদাহরণস্বরূপ কাপড় বুনন কারখানায় প্রথমে তুলা থেকে সুতা বের করে সুন্দরভাবে সাজিয়ে বুননের মাধ্যমে নির্দিষ্ট কাপড়ের আকৃতি দেয়া হয়। তেমনি আকল মেশিনের মতো শুধু ইন্দ্রিয়লব্ধ কাঁচামালকে ব্যবহার করে নির্দিষ্ট আকৃতি দেয়। তবে বুদ্ধিবৃত্তিক মতবাদ তার নিজের স্থানে এখনও অটল। এখানে আমরা অবশ্য সে বিষয়ে আলোচনা করব না, বরং এ ব্যাপারে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি বর্ণনা করার চেষ্টা করব।
ইসলামে বুদ্ধিবৃত্তির মৌলিকত্ব
বুদ্ধিবৃত্তিক মতবাদে কয়েকটি বিষয় আছে যার প্রতিটিকে যাচাই করে দেখব যে, সেগুলো ইসলামের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ কিনা। প্রথম বিষয় বুদ্ধিবৃত্তিক পরিচিতি ও জ্ঞানের মৌলিকত্ব। বুদ্ধিবৃত্তিক পরিচিতি ও জ্ঞানের অর্থ হলো আকল বা বুদ্ধিবৃত্তি বিশ্বের বাস্তবতাকে আবিষ্কার করার ক্ষমতা রাখে এবং এ জ্ঞান মৌলিক, নির্ভরযোগ্য ও যুক্তিপূর্ণ।
অনেক মতবাদই বুদ্ধিবৃত্তির এরূপ ক্ষমতা ও যোগ্যতায় বিশ্বাসী নয়। এখন আমরা দেখব ইসলামী উৎসগুলো থেকে আমাদের নিকট এ ধরনের দলিল-প্রমাণ রয়েছে কিনা যে, বুদ্ধিবৃত্তির এরূপ ক্ষমতায় আমরা বিশ্বাসী হতে পারি। ঘটনাক্রমে আমাদের হাতে এ বিষয়ে পর্যাপ্ত দলিল রয়েছে যাতে আমরা বলতে পারি, ইসলামের মতো কোনো মতাদর্শেই আকলকে এত অধিক পৃষ্ঠপোষকতা করা হয়নি বা গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে আকলকে অন্য কোন ধর্মেই ইসলামের মতো গুরুত্ব দেয়া হয়নি।
আপনি খ্রিষ্টধর্মকে ইসলামের সঙ্গে তুলনা করে দেখুন, খ্রিষ্টধর্ম ঈমানের দৃষ্টিতে আকলে প্রবেশের বিরোধী। তাদের মতে, মানুষ যখন কোনো কিছুর উপর ঈমান আনবে তখন এর উপর চিন্তা করার অধিকার তার নেই। চিন্তা যেহেতু বুদ্ধিবৃত্তির কাজ তাই বিশ্বাসগত বিষয়ে চিন্তার অবকাশ নেই। যে বিষয়ে ঈমান রাখতে হবে সে বিষয়ে চিন্তা করা যাবে না। এ ক্ষেত্রে আকলকে ‘কি’ ও ‘কেন’ এ ধরনের প্রশ্ন করার সুযোগ দেয়া যাবে না। একজন বিশ্বাসী ব্যক্তি, বিশেষত চার্চের অধিপতির দায়িত্ব হলো ঈমানের গণ্ডিতে যুক্তি, চিন্তা ও বুদ্ধিবৃত্তির প্রবেশকে প্রতিহত করা। মূলত খ্রিষ্টবাদের শিক্ষা এর উপর ভিত্তি করেই গড়ে উঠেছে।
ইসলামের ক্ষেত্রে আমরা ঠিক এর বিপরীত অবস্থা দেখি। ইসলাম ধর্মের মৌলিক বিষয়ে (উসূল) বুদ্ধিবৃত্তি ব্যতীত অন্য কিছুর প্রবেশ নিষিদ্ধ। যেমন যদি আপনাকে প্রশ্ন করা হয় আপনার ধর্মের একটি মৌলিক বিষয় বলুন। আপনি হয়তো বললেন, তাওহীদ (একত্ববাদ)। এখন যদি আপনাকে প্রশ্ন করা হয়, কেন আপনি এক আল্লাহতে ঈমান এনেছেন? আপনাকে অবশ্যই এজন্য যুক্তি পেশ করতে হবে যেহেতু ইসলাম আকল ব্যতীত আপনার নিকট থেকে তা গ্রহণ করবে না। যদি বলেন, “আমি এক আল্লাহয় বিশ্বাস করি, কিন্তু এর পেছনে কোন যুক্তি পেশ করতে পারব না। আমার দাদীমার থেকে শুনে আমি বিশ্বাস করেছি। অবশেষে এক সত্যে পৌঁছেছি যেভাবেই হোক দাদীমার কাছে শুনে অথবা স্বপ্ন দেখে।” ইসলাম বলে, “না, যদিও এক আল্লাহতে বিশ্বাসী হও, কিন্তু এ বিশ্বাসের ভিত্তি স্বপ্ন বা পিতা- মাতার অন্ধ অনুকরণ অথবা পরিবেশের প্রভাবে হয়ে থাকে, তবে তা গ্রহণযোগ্য নয়।” কেবল চিন্তা ও বিচার-বিশ্লেষণের পর যুক্তির ভিত্তিতে যদি আপনি ঈমান আনয়ন করেন তবেই তা গ্রহণ করা হবে নতুবা নয়।
খ্রিষ্টবাদে ঈমানের গণ্ডিতে আকলের প্রবেশ নিষিদ্ধ। এটাই খ্রিষ্টবাদের ভিত্তি। একজন খ্রিষ্টধর্মে বিশ্বাসী ব্যক্তির দায়িত্ব হলো এই গণ্ডিতে আকল ও চিন্তার প্রবেশকে রোধ করা। ইসলামে ঈমানের গণ্ডিতে আকলের স্থান সংরক্ষিত। আকল ব্যতীত অন্য কোনো কিছুর এ গণ্ডিতে প্রবেশাধিকার নেই।
ইসলামের উৎসসমূহে অর্থাৎ কোরআন ও সুন্নাহতে আকলকে উচ্চ মর্যাদায় সমাসীন দেখা যায়। প্রথমত কোরআন সব সময়ই বুদ্ধিবৃত্তির প্রশংসা করেছে। তদুপরি আমাদের হাদীস গ্রন্থসমূহেও বুদ্ধিবৃত্তির গুরুত্ব ও মৌলিকত্ব এতটা প্রকট যে, এ গ্রন্থসমূহ খুললেই দেখা যায়, তাতে প্রথম অধ্যায় হিসেবে কিতাবুল আকল এসেছে এবং এ অধ্যায়ের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত বুদ্ধিবৃত্তির পৃষ্ঠপোষকতা করা হয়েছে।
ইমাম মুসা ইবনে জাফর (আ.) আকল সম্পর্কিত একটা আশ্চর্য বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, “আল্লাহপাকের দু’টি হুজ্জাত (দলিল) রয়েছে। এ দু’টি হুজ্জাত হচ্ছে দু’টি নবী। একটি অভ্যন্তরীণ নবী বা আকল, দ্বিতীয়টি বাহ্যিক নবী অর্থাৎ আল্লাহ্র প্রেরিত পুরুষগণ যাঁরা নিজেরা মানুষ এবং অন্য মানুষদের দীনের দিকে দাওয়াত করেন। আল্লাহপাকের এ দু’টি হুজ্জাত একে অপরের পরিপূরক অর্থাৎ যদি মানুষের বুদ্ধিবৃত্তি থাকে, কিন্তু পৃথিবীতে কোনো নবী প্রেরিত না হয়, তবে মানুষের পক্ষে সফলতার পথ অতিক্রম করা সম্ভব হবে না। তেমনি যদি নবী থাকেন, কিন্তু মানুষ বুদ্ধিবৃত্তির অধিকারী না হয় তাহলেও সে সাফল্য লাভ করতে পারবে না। আকল ও নবী একসঙ্গে একই দায়িত্ব পালন করে।” এর চেয়ে উত্তমরূপে আকলকে সম্মানিত করা ও পৃষ্ঠপোষকতা দান আর কোনভাবে সম্ভব কি?
এ ধরনের বর্ণনা ও রেওয়ায়েত সম্ভবত আরো শুনে থাকবেন। যেমনঃ
‘জ্ঞানীর নিদ্রা অজ্ঞের ইবাদত হতে উত্তম‘,
‘জ্ঞানীর খাদ্যগ্রহণ মূর্খের রোযা অপেক্ষা উত্তম‘,
‘জ্ঞানীর নিরবতা অজ্ঞের কথা হতে শ্রেয়‘,
‘আল্লাহ্ কোনো নবীকেই তাঁর আকল পূর্ণতায় পৌছা ও সমগ্র উম্মত থেকে তাঁর বুদ্ধিবৃত্তি উচ্চতর হওয়ার পূর্বে প্রেরণ করেননি।’
আমরা রাসূল (সা.)-কে বুদ্ধিবৃত্তির সমগ্র রূপ বলে জানি। আমাদের এ ধারণা খ্রিষ্টবাদের সঙ্গে সম্পূর্ণ অসামঞ্জস্যশীল। যেহেতু তারা বুদ্ধিবৃত্তি থেকে দীনকে পৃথক বলে জানে। কিন্তু আমরা আমাদের নবীকে আকলের পরিপূর্ণ রূপ মনে করি।
সুতরাং জ্ঞান ও প্রামাণ্যের ক্ষেত্রে আমরা আকলকে দলিল বলে জানি এ অর্থে যে, বুদ্ধিবৃত্তির মাধ্যমে বাস্তব জ্ঞান ও পরিচয় লাভ সম্ভব। দার্শনিকদের এ দৃষ্টিভঙ্গিকে ইসলাম সমর্থন করে।
বুদ্ধিবৃত্তিক মতবাদের দু‘টি ত্রুটি
দার্শনিক মতে মানুষের প্রকৃত সত্তা হলো তার বুদ্ধিবৃত্তি। এ ছাড়া বাকী যা আছে সেগুলো অপ্রধান এবং এগুলো মাধ্যম বৈ কিছু নয়। শরীর আকলের জন্য যেমনি একটি মাধ্যম, তেমনি চোখ, কান, ধারণক্ষমতা, কল্পনাশক্তি ও অন্য যে সকল যোগ্যতা আমাদের মধ্যে বর্তমান সেগুলোও আমাদের মূল সত্তা ‘আকল’র একেকটি মাধ্যম।
এখন প্রশ্ন হলো এ বক্তব্যের পক্ষে কোনো দলিল ইসলামে রয়েছে কি? না, এ ধরনের বক্তব্য যে, আমাদের মূল সত্তা শুধু আকল- এর সপক্ষে কোনো দলিল বা প্রমাণ ইসলামে নেই। ইসলাম এ ব্যাপারে স্বতন্ত্র দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করে যে, আকল মানুষের সমগ্র অস্তিত্বের একটি অংশ, তার সমগ্র অস্তিত্ব নয়।
দ্বিতীয় বিষয় হলো আমাদের অধিকাংশ দর্শনের গ্রন্থে ঈমানকে শুধু জ্ঞান বলে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। তাঁরা বলছেন, ইসলামে ঈমানের অর্থ বাস্তব পরিচিতি বা জ্ঞান। আল্লাহর প্রতি ঈমানের অর্থ আল্লাহকে জানা, তদ্রূপ রাসূল (সা.)-কে জানা। ফেরেশতাদের প্রতি ঈমানের অর্থ ফেরেশতাদের পরিচয় লাভ, আখেরাতের প্রতি ঈমানের অর্থ আখেরাতের পরিচয় জানা। কোরআনে যেখানেই ঈমান এসেছে এর অর্থ বাস্তব জ্ঞান ও পরিচিতি ছাড়া আর কিছু নয়। এ বিষয়টি কোনক্রমেই ইসলামের সাথে সংগতিপূর্ণ নয়। ইসলামে ঈমানের অর্থ শুধু পরিচিতি নয়, বরং এর চেয়ে বেশি কিছু। পরিচিতি অর্থ হলো জানা। যিনি পানিবিজ্ঞানী তিনি পানিকে চেনেন। যিনি জ্যোতির্বিজ্ঞানী তিনি জ্যোতিষ্ক সম্পর্কে জ্ঞান রাখেন, তদ্রূপ যিনি সমাজবিজ্ঞানী তিনি জানেন সমাজকে, যিনি মনোবিজ্ঞানী তিনি মনকে বোঝেন, যিনি প্রাণীবিজ্ঞানী তিনি প্রাণীদের সম্পর্কে জানেন অর্থাৎ এঁরা সবাই নিজেদের সম্পৃক্ত বিষয়ে পর্যাপ্ত জ্ঞান রাখেন। ঈমানও কি কোরআনে এরূপ জানা অর্থেই এসেছে? আল্লাহর প্রতি ঈমানের অর্থ কি শুধুই তাঁকে বোঝা ও অনুভব করা? না, এমন নয়। এটা ঠিক যে, পরিচয় লাভ ঈমানের শর্ত ও অংশ। পরিচিতি ব্যতীত ঈমান অর্থহীন, এটা সত্য, কিন্তু শুধু জানাও ঈমান নয়।
ঈমান এক প্রবণতা যার মধ্যে আনুগত্যের প্রবণতা রয়েছে, প্রেম ও ভালবাসার প্রবণতা রয়েছে, স্রষ্টার প্রতি আত্মনিবেদনের প্রবণতা রযেছে, কিন্তু জ্ঞানের মধ্যে এ ধরনের প্রবণতা অনুপস্থিত। একজন জ্যোতির্বিজ্ঞানী জ্যোতিষ্কমণ্ডলী সম্পর্কে জ্ঞান রাখেন- এর অর্থ এটা নয় যে, তিনি জ্যোতিষ্কসমূহের প্রতি অনুরক্ত। তদ্রূপ একজন খনিজবিজ্ঞানী বা পানিবিজ্ঞানী- এর অর্থ এটা নয় যে, তিনি খনিজ বা পানির প্রতি আসক্ত। বরং এ ধরনের সম্ভাবনা রয়েছে যে, মানুষ কোনো বস্তু সম্পর্কে জ্ঞান রাখে, কিন্তু তা থেকে বিতৃষ্ণ। বিশেষত রাজনীতিতে শত্রুকে মানুষ নিজের থেকেও ভালোভাবে চেনে। উদাহরণস্বরূপ কোন ইসরাইলী হয়তো আরব ও মুসলিম বিশ্ব সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ; হয়তো ইসলাম সম্পর্কেও তার জ্ঞান অত্যন্ত গভীর। ইসরাইলে মিশর, সিরিয়া, আলজেরিয়া বা ইরান বিষয়ক বিশেষজ্ঞ মুসলমানদের মধ্যকার এরূপ বিশেষজ্ঞ অপেক্ষা অনেক বেশি এটা অস্বীকার করার উপায় নেই। এখন প্রশ্ন হলো এরূপ মিশর বিষয়ক ইসরাইলী বিশেষজ্ঞ কি মিশরের প্রতি আনুগত্যশীল? কখনই নয়। তদ্রূপ মিশরে কোন ইসরাইল বিষয়ক বিশেষজ্ঞ থাকতে পারেন। কিন্তু তাই বলে তো তিনি ইসরাইলের প্রতি অনুরক্ত নন, বরং তিনি হয়তো ইসরাইলের প্রতি বীতশ্রদ্ধ। (যেহেতু ইসরাইল আরবদের প্রতি শত্রুপরায়ণ সেহেতু আরবরাও তাদের প্রতি সন্দেহ পরায়ণ।)
আলেম সমাজ যে বলেন, “ঈমান অর্থ শুধু জ্ঞান অর্জন নয় (যা দর্শন দাবি করে)” এর সপক্ষে সর্বোত্তম প্রমাণ খোদ কোরআন। যেহেতু কোরআন ঐ সকল ব্যক্তিকে আমাদের নিকট পরিচিত করিয়েছে যারা আল্লাহ পাককে সবচেয়ে উত্তমরূপে চেনে, সে সকল নবী ও আউলিয়াকেও উত্তমরূপে চেনে, কিয়ামতকেও ভালোভাবে জানে, কিন্তু ঈমানদার নয় বরং কাফের। যেমন শয়তান। শয়তান কি আল্লাহকে চেনে না? শয়তান তো বস্তুবাদীদের মতো নয় যে, আল্লাহকে চেনে না, বরং সে আল্লাহকে চেনে, কিন্তু আল্লাহপাকের বিরোধী। শয়তান আমার বা আপনার থেকে অনেক ভালোভাবে আল্লাহকে চেনে। কয়েক হাজার বছর সে আল্লাহর ইবাদত করেছে। কোরআন আমাদের বলছে, ফেরেশতাদের প্রতি ঈমান আনো এবং আমরাও ঈমান এনেছি।
কিন্তু শয়তান কি ফেরেশতাদের চেনে না? না বরং সে ফেরেশতাদের চেনে, তাদের সঙ্গে সহস্র বছর এক সঙ্গে ছিল, আমাদের তুলনায় হযরত জিবরাঈল (আ.)-কে সে উত্তমরূপে জানে। নবীদেরও তদ্রূপ খুব ভালোভাবে চেনে ও জানে। কিয়ামত সম্পর্কে আরো উত্তমরূপে জানে (এ কারণেই আল্লাহর নিকট কিয়ামত পর্যন্ত সময় চেয়েছে)। কিন্তু এত কিছু জানার পরেও কেন কোরআন তাকে কাফের বলে সম্বোধন করছে? কেন বলছে, “সে কাফেরদের অন্তর্ভুক্ত”? (সূরা সোয়াদ: ৭৪)
যদি ঈমানের অর্থ শুধু ‘জানা’ হতো (যেরূপ দর্শন বলছে), তাহলে শয়তান প্রথম মুমিন বলে পরিচিত হতো। কিন্তু জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও সে মুমিন নয়। কারণ সে অস্বীকারকারী জ্ঞানী অর্থাৎ যদিও সে সত্যকে জানে তদুপরি তার বিরোধীতা করে এবং সেটার প্রতি আনুগত্যশীল নয়। সে এ সত্যের প্রতি রুজু করে না বা তার প্রতি ভালোবাসাও অনুভব করে না। ফলশ্রুতিতে সে দিকে সে ধাবিতও হয় না।
সুতরাং ঈমান কেবল ‘পরিচয়’ নয়। এ জন্যই অনেক প্রজ্ঞাবান দার্শনিক সূরা ত্বীন-এর
لَقَدۡ خَلَقۡنَا ٱلۡإِنسَٰنَ فِيٓ أَحۡسَنِ تَقۡوِيمٖ
ثُمَّ رَدَدۡنَٰهُ أَسۡفَلَ سَٰفِلِينَ
إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّـٰلِحَٰتِ
এ আয়াতের তাফসীর এভাবে করেছেন যে, إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ অর্থাৎ তাত্ত্বিক প্রজ্ঞা ও وَعَمِلُواْ ٱلصَّـٰلِحَٰتِ অর্থাৎ ব্যবহারিক প্রজ্ঞা। এটা ঠিক নয়। إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ -এর মধ্যে তাত্ত্বিক প্রজ্ঞা অপেক্ষা উচ্চতর অর্থ নিহিত রয়েছে। তবে তাত্ত্বিক প্রজ্ঞা তার অংশ ও ভিত্তি হলেও প্রজ্ঞা, অনুধাবন, জ্ঞান, পরিচয় ও জানাই পূর্ণ ঈমান নয়, বরং ঈমান জ্ঞান ও জানা-বুঝা থেকে বড় অন্য কিছু।
এখানে আমরা বুদ্ধিবৃত্তিক মতবাদের দৃষ্টিকোণ থেকে তিনটি বিষয় তুলে ধরেছি। প্রথমত, আকল প্রামাণ্য দলিল, আকল দ্বারা গৃহীত বিষয় বিশ্বাসযোগ্য এবং আকল বা বুদ্ধিবৃত্তির মাধ্যমে সঠিক পরিচয় লাভ সম্ভব- এ বিষয়গুলো সত্য এবং ইসলাম তা গ্রহণ করে। দ্বিতীয়ত আকল মানুষের একক মূলসত্তা- ইসলাম এটাকে গ্রহণ করে না। তৃতীয়ত ঈমানের অর্থ বুদ্ধিবৃত্তিক অনুধাবন, জানা ও পরিচয় লাভ ব্যতীত অন্যকিছু নয়- ইসলামের দৃষ্টিতে এটা গ্রহণযোগ্য নয়।
ঈমানের মৌলিকত্ব
ঈমান ও পরিচয়কে একই জানি অথবা পরিচয়কে ঈমানের একাংশ জানি, এখন যে বিষয়টি আমাদের নিকট লক্ষণীয় তা হলো ঈমান ও পরিচিতির মৌলিকত্ব রয়েছে কি? নাকি মৌলিকত্ব নেই বরং এ দু’টি আমলের (কার্যের) পূর্বশর্ত মাত্র। এ ক্ষেত্রেও দু’টি বড় মতাদর্শের দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়।
ঈমানের মৌলিকত্বের অর্থ কি? এর অর্থ ইসলাম যেভাবে ঈমানকে আমাদের জন্য বর্ণনা করেছে তা এ দৃষ্টিকোণ থেকে যে, ঈমান মানুষের আমলের বিশ্বাসগত ভিত্তি। অর্থাৎ মানুষ পৃথিবীতে অবশ্যই চেষ্টা-প্রচেষ্টা চালাবে এবং কাজ করবে এবং এ চেষ্টা ও কার্যক্রম এক বিশেষ পরিকল্পনা, উদ্দেশ্য ও পদ্ধতি অনুযায়ী হতে হবে যার ভিত্তি বিশেষ চিন্তা ও বিশ্বাস থেকে উৎসারিত। অন্যভাবে বর্ণনা করলে যেহেতু মানুষ চায় বা না চায় তার সকল কর্মকাণ্ড চিন্তাগত এবং যদি সে তার ব্যবহারিক জীবনে নিজের উদ্দেশ্যে পৌঁছতে সঠিক একটি পরিকল্পনা তৈরি করতে চায় তবে তা চিন্তা ও বিশ্বাসের বিশেষ ভিত্তি ব্যতীত সম্ভব নয়। এ কারণেই তাকে চিন্তা ও বিশ্বাসের একটি ভিত্তি দিতে হবে যাতে তার উপর ভিত্তি করে সে তার চিন্তার কাঠামো নির্মাণ করতে পারে। যেমন কোন ব্যক্তি যদি একটি দালান নির্মাণ করতে চায় তাহলে তার লক্ষ্য চার দেয়াল, ছাদ, দরজা-জানালা বিশিষ্ট ঘর নির্মাণ করা, কিন্তু সে এগুলো নির্মাণের পূর্বে ভিত্তি বা স্তম্ভ তৈরি করে যার বেশ কিছু অংশ মাটির নীচে গ্রোথিত করে যদিও এটি তার লক্ষ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল না। কিন্তু সে এটা করে যাতে করে দালানের ভিত্তি মজবুত হয় এবং তা ভেঙ্গে না পড়ে। এজন্যই ভিত্তি নির্মাণ করতে হবে।
উদাহরণস্বরূপ কমিউনিজম কতগুলো চিন্তা ও বিশ্বাসের সমষ্টি যার ভিত্তি বস্তুবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত। এর সমাজ, রাজনীতি, অর্থনীতি এবং নৈতিকতা সম্পর্কিত মৌলিক কাঠামোটি বস্তুবাদের মৌলিক চিন্তা ও বিশ্বাসের ভিত্তির উপর নির্মিত হয়েছে। কিন্তু একজন কমিউনিস্টের এটা লক্ষ্য নয় অর্থাৎ বস্তুবাদ তার লক্ষ্যও নয় এবং তার নিকট এর মৌলিকত্বেরও মূল্য নেই। (প্রকৃতপক্ষে যাঁরা বস্তুবাদের ফাঁদে পা দিয়েছেন তা গীর্জাসমূহের রাজনৈতিক ও সামাজিক চিন্তাসমূহ, বিশেষত স্বাধীন চিন্তার বিরুদ্ধে যুক্তিহীন দ্বন্দ্বের কারণে। যার ফলে ইউরোপে এ চিন্তার উদ্ভব ঘটেছিল যে, হয় মানুষ স্বাধীন হয়ে সমাজে অধিকার প্রতিষ্ঠা করে ঈশ্বরকে দূরে ছুঁড়ে ফেলুক নতুবা নিজেকে অধিকারহীন ও বন্দি বলে জানুক। এর জন্য সর্বোত্তম পথ হিসেবে ধর্মের মূলোৎপাটনকে গ্রহণ করেছিল।)
কিন্তু সে চিন্তা করে (ভুল চিন্তা করে) বস্তুবাদ ব্যতীত সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মৌল চিন্তাকে ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়। আর তা ব্যাখ্যা করার জন্যই বস্তুবাদের মৌলিক চিন্তাকে গ্রহণ করে। সম্প্রতি পৃথিবীতে কয়েকজন কমিউনিস্ট ব্যক্তির সন্ধান পাওয়া গেছে যাঁরা বস্তুবাদকে কমিউনিজম থেকে পৃথক মনে করেন। তাঁরা বলেন, “আমাদের জন্য বস্তুবাদ কোন মৌলিকত্ব তো রাখেই না, বরং বস্তুবাদকে এক অখণ্ডনীয় মৌলনীতি হিসেবে গ্রহণ করার কোন প্রয়োজনই নেই। আমরা কমিউনিজম চাই যদিও তাতে বস্তুবাদের অস্তিত্ব না থাকে।” বর্তমানে পৃথিবীর আনাচে কানাচে অনেক কমিউনিস্ট নেতাই ধর্মের সঙ্গে দ্বন্দ্বের বিষয়টি পরিহার করার কথা বলছেন।
এটা এ কারণে যে, তাঁদের জন্য এ মৌল চিন্তার প্রতি বিশ্বাসের কোন মৌলিকত্ব নেই। এটা শুধু চিন্তা ও বিশ্বাসের ভিত্তি ব্যতীত কিছু নয়। যেহেতু জীবনাদর্শ বিশ্বদৃষ্টি ব্যতীত সম্ভব নয় সেহেতু এ বিশ্বদৃষ্টিকে (বস্তুবাদ) দালানের নীচে স্থাপন করা হয় যাতে করে জীবনাদর্শ স্থাপিত ও অগ্রসর হতে পারে। কিন্তু মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হলো জীবনাদর্শ।
কিন্তু ইসলামে কিরূপ? ইসলাম কি ইসলামী বিশ্বাস, যেমন আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস, ফেরেশতাদের প্রতি বিশ্বাস, নবী ও ওলীদের প্রতি বিশ্বাস, কিয়ামতের প্রতি বিশ্বাস এগুলোকে শুধু এজন্য বর্ণনা করেছে যে, চিন্তা ও বিশ্বাসের ভিত্তি হিসেবে পরিগণিত হবে? ইসলাম কি এজন্য এ মৌল চিন্তাসমূহকে উপস্থাপন করেছে যাতে করে জীবনাদর্শকে এ মৌল চিন্তার উপর ভিত্তি করে স্থাপন করতে পারে এবং এটাই (জীবনাদর্শই) তার উদ্দেশ্য? যদি তা-ই হয় তবে এ মৌল চিন্তার (ঈমান) কোন মৌলিকত্ব নেই। না, এমনটি নয়। এ মৌল চিন্তা ইসলামী জীবনাদর্শিক চিন্তা ও বিশ্বাসের ভিত্তি বটে, তবে তার মূল্য শুধু ভিত্তি হিসেবে নয়। ঈমান চিন্তা ও বিশ্বাসের ভিত্তি এবং ইসলামী জীবনাদর্শ এর উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। কিন্তু ঈমান ভিত্তি হিসেবে মূল্য ছাড়াও মৌলিকত্বের অধিকারী ও লক্ষ্য হিসেবেও পরিগণিত।
সুতরাং এ ক্ষেত্রে দর্শনের দৃষ্টিভঙ্গি ঠিক যে, ঈমান শুধু আমলের পূর্বশর্ত হিসেবে নয় বরং এর মৌলিকত্বের কারণে মূল্যের অধিকারী। এ রকম নয় যে, শুধু কর্ম ও প্রচেষ্টাই সব কিছু। বরং যদি আমল থেকে ঈমানকে বিচ্ছিন্ন করা হয়, একটি ভিত্তিকে নষ্ট করা হলো। তেমনিভাবে যদি আমলকে ঈমান থেকে বিচ্ছিন্ন করা হয় অন্য স্তম্ভটি ধ্বংস করা হলো। এজন্যই কোরআন সব সময় বলেছে, ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّـٰلِحَٰتِ “যারা ঈমান এনেছে ও সৎকর্ম করেছে।” যদি আমলহীন ঈমান হয়, তবে সেখানে সাফল্যের একটি স্তম্ভ আছে, অন্যটি অনুপস্থিত। অপর দিকে ঈমানহীন আমলও তদ্রূপ।
সাফল্যের তাঁবু একটি স্তম্ভের উপর দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না। ইসলামের দৃষ্টিতে ঈমানের সত্তাগত মূল্য ও মৌলিকত্ব রয়েছে। প্রকৃতপক্ষে মানুষের পূর্ণতা এ পৃথিবীতে এবং বিশেষত আখেরাতে এটাই যে, সে ঈমানের অধিকারী। কারণ ইসলামে আত্মা স্বাধীন এবং পূর্ণতার অধিকারী, তার মৃত্যু নেই। যদি আত্মা (ঈমানের মাধ্যমে) পূর্ণতায় না পৌঁছায়, অসম্পূর্ণ ও ত্রুটিযুক্ত হয় তাহলে কখনই সফলতায় পৌছতে পারে না।
কোরআন ও নাহজুল বালাগাহ্ থেকে এর সপক্ষে দলিল
কোরআন এ বিষয়ে বলছে,
وَمَن كَانَ فِي هَٰذِهِۦٓ أَعۡمَىٰ فَهُوَ فِي ٱلۡأٓخِرَةِ أَعۡمَىٰ وَأَضَلُّ سَبِيلٗا
“যে ব্যক্তি এ পৃথিবীতে অন্ধ, আখেরাতেও সে অন্ধ এবং অধিকতর পথভ্রষ্ট।” (সূরা ইসরা: ৭২)
ইমামগণ এবং অন্যান্য মুফাসসিরগণ এর তাফসীরে বলেছেন, এর অর্থ এমন নয় যে, কারো বাহ্যিক এ চক্ষু পৃথিবীতে অন্ধ হলে আখেরাতেও সে অন্ধ থাকবে। যদি এরূপ হতো, তবে আবু বাসির যিনি ইমাম সাদিক (আ.)-এর একজন অন্ধ সাহাবী ছিলেন তিনি পরকালীন দুনিয়াতেও শোচনীয় অবস্থায় পড়বেন। না, বরং এর অর্থ হলো যে, কারো অন্তর্চক্ষু যদি সত্যকে, তার স্রষ্টাকে, মহান আল্লাহর নিদর্শনাবলী এবং অন্যান্য যে সব বিষয়ে ঈমান বা বিশ্বাস থাকা উচিত তা থেকে অন্ধ হয়, তবে সে আখেরাতে অন্ধ হিসেবে পুনরুত্থিত হবে, এর অন্যথা সম্ভব নয়। যদি ধরে নিই, এ পৃথিবীতে একজন মানুষ যত প্রকার ভালো কাজ করা সম্ভব তা করে, সৎকর্মের আদেশ ও অসৎকর্মের নিষেধের দায়িত্ব পালন করে এবং সর্বশ্রেষ্ঠ দুনিয়াবিরাগী ব্যক্তির ন্যায় জীবন যাপন করে, সে সাথে নিজের জীবনকে আল্লাহর সৃষ্টির জন্য নিবেদিত করে, কিন্তু আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখে না, পরকাল ও ইহকালকে চেনে না- এরূপ ব্যক্তি অন্ধ, তাই পরকালীন দুনিয়াতেও সে অন্ধ।
সুতরাং এটা ঠিক নয় যে, ঈমান শুধু চেষ্টা-প্রচেষ্টার পূর্ব প্রস্তুতি এবং ব্যক্তির আমল ঠিক হলেই চলবে, ঈমানের প্রয়োজন নেই। এ ধরনের কথা অর্থহীন। ফখরে রাজী বলেন,
“আশংকা আমার,
চলে যাব বিশ্বের প্রাণ না দেখে,
চলে যাব বিশ্ব ছেড়ে বিশ্বকে না দেখে,
দেহের বিশ্ব ছেড়ে যাব মনের বিশ্বে ও প্রাণে,
দেহের বিশ্বে মনের বিশ্ব না দেখেই তাঁর পানে।”
অর্থাৎ আমার আশংকা এটি যে, এ পৃথিবী ছেড়ে চলে যাব, অথচ তা এ বিশ্বকে না দেখেই। তাঁর এ কথার উদ্দেশ্য এটা নয় যে, বিশ্ব বলতে পৃথিবীর মাটি, পাহাড়, সমুদ্র, তারকারাজি আর ঘরবাড়ি বোঝাচ্ছেন এবং এ সব না দেখেই চলে যাওয়ার জন্য চিন্তিত, বরং তাঁর আশংকা হলো এখানে যে, তাঁর অন্তর্চক্ষু উন্মোচিত যদি না হয় তবে বিশ্বের প্রাণ, এর উৎস ও সৃষ্টিকর্তাকে অনুধাবন- যাকে ইসলাম ঈমান বলেছে তা না করেই এ বিশ্ব ছেড়ে চলে যাবেন। তিনি বলছেন, যদি এ দেহের বিশ্বে মনের বিশ্বকে অনুভব না করি, তবে যখন দেহের বিশ্ব ছেড়ে প্রাণ ও মনের বিশ্বে গমন করব তা কিরূপে অনুভব করব? যেখানে সম্ভব ছিল সেখানেই পারিনি, তাই আফসোস। এ দু’টি পঙতিতে কোরআনের উপরোক্ত এ আয়াতেরই অর্থ করেছেন।
কোরআন অন্য একটি আয়াতে বলছে,
قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرۡتَنِيٓ أَعۡمَىٰ وَقَدۡ كُنتُ بَصِيرٗا
قَالَ كَذَٰلِكَ أَتَتۡكَ ءَايَٰتُنَا فَنَسِيتَهَاۖ وَكَذَٰلِكَ ٱلۡيَوۡمَ تُنسَىٰ
(সূরা ত্বাহা: ১২৫-১২৬)
কিয়ামতের দিন যে বান্দাকে অন্ধ হিসেবে পুনরুত্থিত করা হবে সে প্রতিবাদ করে বলবে, “প্রভু! কেন আমাকে অন্ধ করে পুনরুত্থিত করেছেন? আমি ঐ পৃথিবীতে চক্ষুষ্মান ছিলাম, কিন্তু কেন আমি এখানে অন্ধ? তার প্রতি বলা হবে, ঐ পৃথিবীতে তুমি যে চক্ষুর অধিকারী ছিলে তা এখানের জন্য প্রযোজ্য নয়। এখানে অন্য রকম চক্ষুর প্রয়োজন। তোমার যে চক্ষু ছিল তা নিজেই অন্ধ করেছ তাই তুমি এখানে অন্ধ।“ أنك آيائنا আমাদের নিদর্শনসমূহ এ পৃথিবীতে ছিল, তুমি এ নিদর্শনসমূহের মাধ্যমে আমাদের দেখা, অনুধাবন এবং সত্যকে উদ্ঘাটনের পরিবর্তে সেখানে নিজেকে অন্ধ করে রেখেছিলে। সেজন্যই প্রকৃত বিশ্বে এসে অন্ধ হিসেবে পুনরুত্থিত হয়েছ।
সূরা মুতাফফিফীন বলছে,
كَلَّآ إِنَّهُمۡ عَن رَّبِّهِمۡ يَوۡمَئِذٖ لَّمَحۡجُوبُونَ
“কখনই নয়, নিশ্চয়ই তারা তাদের প্রতিপালক হতে সেদিন পর্দাবৃত থাকবে।” (সূরা মুতাফফিফীন : ১৫)
অর্থাৎ এদের পরিত্যাগ কর। এদের উচিত ছিল পৃথিবীতে তাদের চক্ষুর সম্মুখ হতে গাফিলতির পর্দা উন্মোচন করা ও দেখা। ঈমানের অর্থ এটাই- হে মানুষ! তুমি এ পৃথিবীতে আগমন করেছ যাতে এ পৃথিবীতেই চক্ষুর মাধ্যমে ঐ পৃথিবীকে দেখতে ও কর্ণের মাধ্যমে ঐ পৃথিবীকে শ্রবণ কর।
আমি সব সময়ই এজন্য আনন্দিত যে, আমাদের যুবকরা বিশেষ করে নাহজুল বালাগার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দান করছে। নাহজুল বালাগার বিভিন্ন বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখবে। দেখবে নাহজুল বালাগাহ্ এরূপ চক্ষু ও কর্ণ সম্পর্কে কি বলে।
নাহজুল বালাগাহ্ ঈমানের ক্ষেত্রে মৌলিকত্বে বিশ্বাসী। ঈমানের মূল্য শুধু চিন্তা ও বিশ্বাসের ভিত্তি হিসেবে নয়, বরং চিন্তা ও ভিত্তি ছাড়াও মৌলিক হিসেবে নাহজুল বালাগাহ্ ঈমানকে উল্লেখ করেছে।
আলী (আ.) নাহজুল বালাগায় আল্লাহর বিশেষ বান্দাদের (আহলুল্লাহ্) সম্পর্কে বলেন,
يَتَنَسَّمُونَ بِدُعَائِه روح التجاوز
“এরা এমন বান্দা যে, যখন তারা দোয়া করে ও তওবায় নিমজ্জিত হয় আল্লাহর পক্ষ থেকে ক্ষমা প্রাপ্তির সমীরণ নিজেদের মধ্যে অনুভব করে।”
আলী (আ.) আরো বলেন,
إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى جَعَلَ الذِّكْرَ حِلاءً لِلْقُلُوْبِ تَسْمَعُ بِهِ بَعدَ الوقرة وَ تُبْصِرُ بِهِ بَعْدَ الْعَشْوَةِ وَ تَنقَادُ بِهِ بَعْدَ الْمَعَائِدَةِ وَ مَا بَرِحَ اللَّه عَزَّتْ الأَؤُهُ فِي الْبُرْهَةِ بَعْدَ الْبُرْهَةِ وَ فِي أَزْمَانَ الفَتَرَتِ عِبَادٌ نَاجَاهُمْ فِي فِكْرِهِمْ وَ كَلَّمَهُمْ فِي ذَاتِ عُقُولِهِمْ
“নিশ্চয় মহান আল্লাহ্ তাঁর স্মরণকে মানুষের আত্মার উজ্জ্বলতার কারণস্বরূপ করেছেন, যে কারণে (আত্মার স্বচ্ছতার কারণে) সে বধিরতার পর শ্রবণশক্তি, অন্ধত্বের পর দৃষ্টিশক্তি লাভ করে এবং নাফরমানীর পর আনুগত্যের পথ গ্রহণ করে, সকল অবস্থায় অফুরন্ত নেয়ামত দানকারী আল্লাহর জন্য নিজেকে নিবেদিত করে। সকল কালেই একদল ব্যক্তি রয়েছে যাদের চিন্তার মাধ্যমে আল্লাহ্ গোপন রহস্যের ভেদ উন্মোচন করেন। আর আকলের মাধ্যমে তাদের সঙ্গে কথা বলেন।” (নাহজুল বালাগাহ্, খুতবা নং ২২২)
সুতরাং আমি এখানে যে বিষয়টি বলতে চাই তা হলো আল্লাহর পরিচয় জানা, তাঁর ফেরেশতাদের পরিচয় জানা (যাঁরা অস্তিত্বজগতের জন্য মাধ্যম), তাঁর প্রেরিত নবী ও আউলিয়াগণের পরিচয় জানা (যাঁরা অন্য একভাবে আল্লাহর নেয়ামত সৃষ্টির নিকট পৌছানোর মাধ্যম), আমাদের এ পৃথিবীতে আসার উদ্দেশ্যকে জানা, আখেরাত ও আল্লাহর প্রতি প্রত্যাবর্তনকে জানা এ সবই মৌলিক। সত্যের প্রতি ঈমান যেমন মৌলিক তেমনি তা চিন্তা, বিশ্বাস ও ইসলামী জীবনাদর্শের ভিত্তিও বটে। কেবল একশ’ ভাগ মৌলিক এরূপ কোন ঈমানই পারে একটি জীবনাদর্শের জন্য সর্বোত্তম চিন্তা ও বিশ্বাসগত ভিত্তি হতে। সুতরাং কখনই আমলের জন্য যেমন ঈমানকে বিসর্জন দেয়া যুক্তিযুক্ত নয় তেমনি ঈমানের জন্য আমলকে বিসর্জন দেয়াও অযৌক্তিক। এদের কোনটিকেই অন্যটির জন্য বিসর্জন দেয়া যাবে না।
সুতরাং দর্শনের পূর্ণ মানব, পূর্ণ মানব নয় বরং অপূর্ণ মানব। অপূর্ণ মানবের অর্থ কি? অপূর্ণ মানব সে, যে পূর্ণতার অংশবিশেষ ধারণ করে। দর্শন বুদ্ধিবৃত্তিক পূর্ণতার ক্ষেত্রে মৌলিকত্বে বিশ্বাসী তা অবশ্যই ঠিক। কিন্তু দর্শনের পূর্ণ মানব মানবের পূর্ণতার অন্যান্য দিকগুলোকে উপেক্ষা করে শুধু আকলের পূর্ণতার মধ্যে তার পূর্ণতাকে খোঁজে। তাই এ মানব অপূর্ণ অথবা অর্ধপূর্ণ যা জ্ঞানের এক প্রতিমূর্তি বৈ কিছু নয়, জ্ঞান ব্যতীত সকল কিছু তার নিকট অনুপস্থিত। এরূপ মানব এমন এক অস্তিত্ব যে শুধু জানে, কিন্তু আবেগ, উত্তাপ ও গতিহীন এবং সৌন্দর্য বিমুখ। যে অস্তিত্বের সমগ্র শিল্প শুধু জ্ঞানের মধ্যে নিহিত সে অস্তিত্ব এক বিচ্ছিন্ন বিশ্বের মত পরিত্যক্ত। এটি ইসলামের পূর্ণ মানব নয় বরং ইসলামের অর্ধ মানব।
আকল ও বুদ্ধিবৃত্তির মূল্যের ক্ষেত্রে ইমাম মূসা ইবনে জাফর (আ.)-এর হাদীসটি আপনাদের জন্য ব্যাখ্যা করার সময় হলো না। এ প্রসঙ্গে প্রচুর কথা রয়েছে। যদি এ বিষয়ে আলোচনা করতে চাই তাহলে আরো দু’টি বৈঠক প্রয়োজন। সে সময় হাতে নেই বলে বুদ্ধিবৃত্তিক মতবাদ সম্পর্কিত আলোচনা এখানেই শেষ করছি।
অনুবাদঃ এ.কে.এম. আনোয়ারুল কবীর।