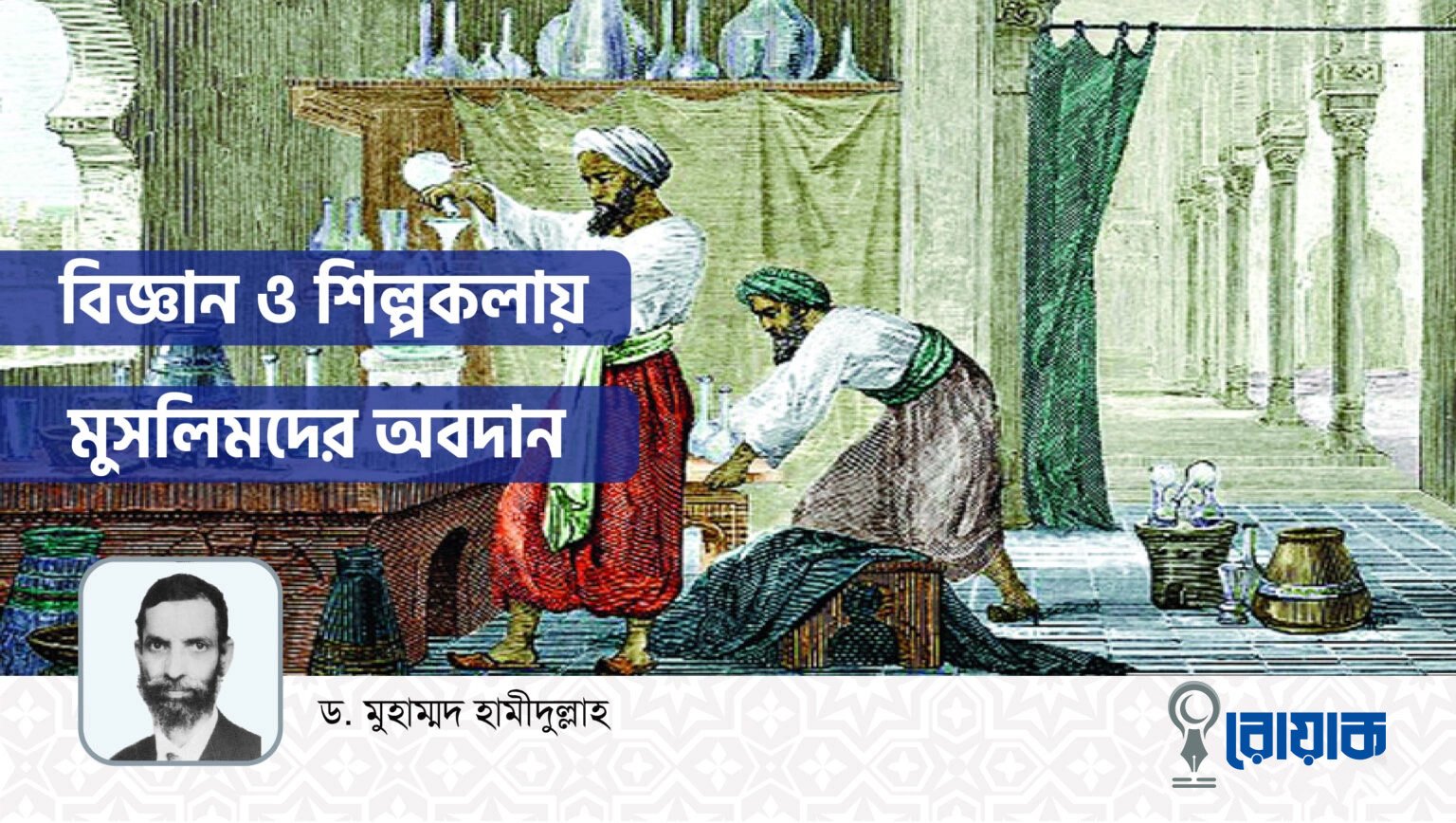প্রথমেই বলে রাখা আবশ্যক যে, ইসলাম কেবলমাত্র একটি ধর্ম নয়। স্রষ্টার সঙ্গে মানুষের সম্পর্কের মধ্যে ইসলামের আলোচনা সীমাবদ্ধ থাকে না। বরং ইসলাম হচ্ছে একটি পরিপূর্ণ জীবনব্যবস্থা। সে কারণেই বিজ্ঞান ও শিল্পকলা চর্চায় ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে আলোকপাত করা আবশ্যক।
দুনিয়ার জীবনকে ইসলাম নিরুৎসাহিত করেনি, বরং সুস্থ সুন্দর জীবনের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করে কোরআন মজীদে ইরশাদ হয়েছে।
বল, আল্লাহ তার বান্দাদের জন্য যেসব শোভার বস্তু ও বিশুদ্ধ জীবিকা সৃষ্টি করেছেন তা কে নিষিদ্ধ করেছে?
কোরআন মজীদে তাদের প্রশংসা করা হয়েছে যারা বলে,
“হে আমার রব! আমাদের ইহকালে কল্যাণ দাও এবং পরকালেও কল্যাণ দাও এবং আমাদের দোযখের আযাব হতে রক্ষা কর (২ঃ ২০১) “
কোরআন মজীদ শিক্ষা দেয় যে, “আল্লাহ যা তোমাকে দিয়েছেন তা দিয়ে আখিরাতে আবাস অনুসন্ধান কর। দুনিয়া হতে তোমার অংশ ভুলো না। পরোপকার কর যেমন- আল্লাহ তোমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন এবং পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করতে যেও না। আল্লাহ বিপর্যয় সৃষ্টিকারীকে ভালবাসেন না (২৮ঃ৭৭)।”
বস্তুতপক্ষে এমনি একটি সুন্দর জীবন লাভের প্রত্যাশায় মানুষ জগৎ সম্পর্কে জানতে চায়। বিশ্বচরাচরে বিরাজমান সমস্ত বিষয় সম্পর্কে যথার্থ জ্ঞান লাভের আশায় সে সাধ্যমত প্রচেষ্টা চালায়। তার নিরলস প্রচেষ্টায় মূল উদ্দেশ্য দুটি।
- প্রথমত বিশ্বজগতের বিভিন্ন জিনিস থেকে উপকৃত হওয়া।
- দ্বিতীয়ত মহান স্রষ্টা আল্লাহ তায়ালার প্রতি কৃতজ্ঞ থাকা।
কোরআন মজীদে বলা হয়েছে যে, “আমি তো তোমাদেরকে দুনিয়ায় প্রতিষ্ঠিত করেছি এবং তাতে তোমাদের জীবিকার ব্যবস্থা করেছি (৭ঃ১০)।” আরো ইরশাদ হয়েছে, “তিনি পৃথিবীর সব কিছু তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন (২৪ঃ২৯)।” অন্যত্র বলা হয়েছে, “তোমরা কি দেখো না আল্লাহ আকাশ মন্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সব কিছু তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত করেছেন । আর তোমাদের প্রতি তার প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করেছেন (৩১ঃ২০)।” কোরআন মজীদ একদিকে ইবাদত করার তাগিদ করে ইরশাদ হয়েছে তা হল, “ইবাদত করুক ওই গৃহের (অর্থাৎ কা’বা শরীফের) রক্ষকের, যিনি তাদের ক্ষুধায় আহার দিয়েছেন এবং ভীতি হতে তাদেরকে নিরাপদ করেছেন (১০৬: ৩-৪)”, অপরদিকে কাজ করার তাগিদ দিয়ে নির্দেশ করা হয়েছে যে, “আর এই যে মানুষ, তাই পায় যা সে করে (৫৩ঃ৩৯)।”
কোরআন মজীদে শুধুমাত্র আবিষ্কারের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়নি, বরং নিত্য নতুন বিষয় উদ্ভাবনের উপরও যথাযথ জোর দেওয়া হয়েছে। যেমন—বলা হয়েছে যে, “বল, তোমরা পৃথিবীতে পরিভ্রমণ কর এবং দেখ তোমাদের পূর্ববর্তীগণের পরিণাম কি হয়েছে। তাদের অধিকাংশই ছিল মুশরিক (৩০ঃ৪২)।” আবার এ কথাও উল্লেখ আছে যে, “যারা দাঁড়িয়ে, বসে এবং শুয়ে আল্লাহকে স্মরণ করে এবং আকাশ মন্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টি সম্বন্ধে চিন্তা করে এবং বলে, হে আমাদের রব, তুমি এসব নিরর্থক সৃষ্টি করনি….(৩ঃ ১৯১)।”
জ্ঞান অর্জনের পন্থা-পদ্ধতি সম্পর্কেও কোরআন মজীদে স্পষ্ট পথ-নির্দেশ রয়েছে। একটি অশিক্ষিত সমাজে নবী করীম (সা) জন্ম গ্রহণ করেন। কিন্তু তাঁর উপর প্রথম যে ওহী নাযিল হয় তাতেই পড়া ও লেখার জন্য নির্দেশ প্রদান করা হয়। সেখানে কলমের উচ্ছসিত প্রশংসা করে বলা হয়েছে যে, কলম হল মানুষের জ্ঞান ভাণ্ডারের নির্ভরযোগ্য হিফাজতকারী। বলা হয়েছে যে, “পাঠ কর তোমার রবের নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন, সৃষ্টি করেছেন মানুষকে আলাক হতে এবং তোমার রব মহা মহিমান্বিত, যিনি কলম দ্বারা শিক্ষা দিয়েছেন, শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে – যা সে জানতো না (৯৬ঃ৫)।” কোরআন মজীদ স্মরণ করিয়ে দেয় যে, “তোমরা যদি না জানো তবে জ্ঞানীগণকে জিজ্ঞাসা কর (১৬ঃ৩)।” সেখানে আরো উল্লেখ আছে যে, “তোমাদেরকে সামান্যই জ্ঞান দেওয়া হয়েছে (১৭ঃ৮৫);” “আমি যাকে ইচ্ছে মর্যাদায় উন্নীত করি। প্রত্যেক জ্ঞানবান ব্যক্তির উপর আছে সর্বজ্ঞানী (১২ঃ৭৬)।” প্রসঙ্গক্রমে এখানে একটি মুনাজাতের উল্লেখ করা যেতে পারে। মানবজাতিকে এই মুনাজাত সম্পর্কে শিক্ষা দিয়ে কুরআন মজীদ ঘোষণা দিয়েছে যে—”বল, হে আমার রব, আমার জ্ঞানের বৃদ্ধি সাধন কর (২০ঃ১১৪)।”
নবী করীম (সা) বলেছেন যে,
“ইসলামের ভিত্তি হল পাঁচটি ও এক আল্লাহর উপর পূর্ণ ঈমান আনা, সালাত কায়েম করা, রমযান মাসে রোজা রাখা, হজ্জ করা এবং যাকাত আদায় করা।”
বিশ্বাস বা ঈমানের সঙ্গে যদি তাত্ত্বিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের সংযোগ থাকে, তাহলে রোজা, সালাত, হজ্জ, যাকাতের সংযোগ রয়েছে পার্থিব জ্ঞান-বিজ্ঞানের সঙ্গে। যেমন সালাত কায়েম করার জন্য একজন মুসলমানকে কিবলামুখী হতে হয় এবং সালাত কায়েম করতে হয় সুনির্দিষ্ট কতকগুলো প্রাকৃতিক ঘটনা কখন ঘটে তার প্রেক্ষিতে। এ জন্য ভূগোল এবং জ্যোতির্বিদ্যা সম্পর্কে জ্ঞান থাকতে হয়। আবার সঠিকভাবে সিয়াম সাধনার জন্যও প্রাকৃতিক ঘটনাবলী সম্পর্কে জ্ঞান থাকা আবশ্যক।
যেমন সূর্য উদয় বা অস্ত সম্পর্কে জ্ঞান না থাকলে সিয়াম পালন করা দুষ্কর। অনুরূপভাবে, হজ যাত্রীদেরকে মক্কায় যাওয়ার জন্য রাস্তাঘাট এবং যানবাহন প্রভৃতি বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান থাকাটা জরুরী। আবার যাকাত আদায় বা উত্তরাধিকারীদের মধ্যে সম্পদ বিলি-বণ্টন করার জন্য অর্থ সম্পদ সম্পর্কে জ্ঞান থাকতে হয়।
কোরআনুল করীমে অনেক বৈজ্ঞানিক সূত্র এবং ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর প্রতি আলোকপাত করা হয়েছে। কোরআনকে জানা এবং বোঝার জন্য এ সমস্ত বিষয়বস্তু সম্পর্কে জ্ঞান থাকাটা অপরিহার্য। বস্তুতপক্ষে কোরআন অধ্যয়ন করতে হলে, যে ভাষায় কুরআন নাযিল হয়েছে প্রথমে সে ভাষা জানতে হবে। এখানেই এসে যাচ্ছে ভাষাবিজ্ঞান সম্পর্কে চর্চার প্রয়োজনীয়তা। এভাবেই ইসলাম আমাদেরকে ইতিহাস, ভূগোল এবং অন্যান্য জ্ঞান-বিজ্ঞান সম্পর্কে চর্চার জন্য অনুপ্রাণিত করে। প্রসঙ্গক্রমে নবী করীম (সা) মদীনায় এসে স্বাধীনভাবে বসতি স্থাপনের প্রারম্ভে একটি মসজিদ নির্মাণ করেন। মসজিদের একটি অংশকে নির্ধারণ করে রাখেন বিদ্যালয়ের জন্য। দিনের বেলায় এ স্থানটি ব্যবহৃত হয় লেকচার হল হিসেবে। আবার রাতের বেলা এটি ব্যবহৃত হত শিক্ষার্থীদের আবাসস্থল রূপে। স্থানটিকে বলা হত সুফফা।
কোরআনুল করীমে ইরশাদ হয়েছে, “হে মুমিনগণ, যদি তোমরা আল্লাহকে সাহায্য কর আল্লাহ তোমাদের সাহায্য করবেন” (৪৭ঃ৭, ২২ঃ৪০)। মুসলমানরা কোরআনের এ উপদেশবাণীকে অক্ষরে অক্ষরে অনুসরণ করেছিল। ফলে তাদের ভাগ্যও খুলে গিয়েছিল। সুতরাং এতে বিস্মিত হওয়ার কিছু নেই যে, জ্ঞান চর্চা ও বিস্তারের জন্য মুসলমানরা সস্তা এবং পর্যাপ্ত পরিমাণে কাগজের ব্যবস্থা করেছিল। বস্তুতপক্ষে হিজরী দ্বিতীয় শতাব্দী থেকেই বিশাল বিস্তীর্ণ মুসলিম শাসনাধীন বিভিন্ন স্থানে কাগজের কল প্রতিষ্ঠিত হয়। উৎপাদিত হয় প্রচুর কাগজ।
এখানে বিজ্ঞানের উন্নয়নে, বিশেষ করে মানবতার কল্যাণে মুসলমানগণ যে অসাধারণ অবদান রেখেছেন তার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হলঃ
ধর্ম ও দর্শন সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞান
ধর্ম বিষয়ক জ্ঞানের সূত্রপাত ঘটেছে কোরআনের মাধ্যমে। কোরআন মজীদ আল্লাহর কালাম। ওহীর মাধ্যমে এই কালাম মানুষের কাছে পৌছেছে। কোরআনকে জানতে ও বুঝতে হলে এর ভাষা, ব্যাকরণ এবং কোরআনের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট সম্পর্কে জানতে হয়। কালক্রমে সমাজে এ বিষয়গুলোর প্রয়োজনীয়তা বৃদ্ধি পায় এবং এর মতো বিষয় এক একটি স্বতন্ত্র বিজ্ঞান হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। যেমন— কোরআন পাঠ ও তিলাওয়াতের মধ্য দিয়েই উচ্চারণ রীতিরও বিকাশ ঘটে। পরবর্তীতে এই বিষয়টি স্বতন্ত্র বিজ্ঞানের রূপ নেয়।
আবার কোরআনের বাণী সংরক্ষণের চেষ্টা চলে সেই শুরু থেকে। এর ফলে আরবি হস্তলিপি শিল্প উৎকর্ষ লাভ করে। দিনে দিনে হস্তলিপি খুবই নিখুঁত, পরিচ্ছন্ন এবং সুন্দর হয়। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে উন্নততর বাক্য গঠন প্রণালী ও বিরতি চিহ্ন। এসবের সমন্বয়ে আরবি ভাষা খুবই সমৃদ্ধ হয়। দুনিয়ার অন্য কোন ভাষার সঙ্গে এর তুলনা হয় না। এভাবেই ভাষা বিজ্ঞানের উদ্ভব ঘটে।
ইসলামের একটি চিরন্তন বৈশিষ্ট্য এই যে, ইসলামকে বুঝতে হলে কোরআন বুঝতে হয়। আরব-অনারব সকলের জন্য একথা সত্য। সে কারণেই অন্যান্য ভাষায় কোরআনের তরজমা প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। নবী করীম (সা)-এর আমলে হযরত সালমান ফারসী (রা) ফারসী ভাষায় কোরআন শরীফের অংশবিশেষ তরজমা করেন। তরজমা করার এ ধারা এখনো অব্যাহত রয়েছে। এখানে বলে রাখা ভালো যে, যারা আরবি পড়তে পারে না, কোরআন বুঝে না, কেবলমাত্র তাদের বুঝার সুবিধার্থে কোরআনের তরজমা করা হয়। কিন্তু সালাত বা ইবাদত-বন্দেগীর সময় কোনভাবেই তরজমা ব্যবহার করা যায় না। তখন কেবলমাত্র কোরআনের মূল ভাষা বাবহার করতে হয়। এটা বাধ্যতামূলক।
কোরআনের আয়াতসমূহ যথাযথভাবে সংরক্ষণ করার জন্য নবী করীম (স) চমৎকার একটি পথ বাতলে দেন। আল্লাহ তা’আলার তরফ থেকে ওহী নাযিল হওয়ার সাথে সাথে সাহাবীগণ অতি যত্নের সঙ্গে তা লিখে রাখতেন। আবার কিছুসংখাক সাহাবী সঙ্গে সঙ্গে তা মুখস্থ করে ফেলতেন। ওহী ঠিকমত লেখা বা মুখস্থ করা হলে কিনা সাহাবীগণ তা পরীক্ষা করে নিতেন। ফলে আল্লাহর কালামের কোন বিকৃতি, বিচ্যুতি বা কোথাও কোন প্রকার ভুলক্রটি হওয়ার সম্ভাবনা ছিল না। কোরআনের বিশুদ্ধতা নিশ্চিত করার জন্য আরো একটি পরীক্ষণ ব্যবস্থা ছিল। তৎকালে বেশ কিছুসংখ্যক সাহাবায়ে কিরামকে কোরআন বিশারদ হিসাবে গণ্য করা হত। তারা হাতে লেখা কোরআন শরীফের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত তিলাওয়াত করে এর বিশুদ্ধতা পরীক্ষা করতেন এবং এর যথার্থতা সম্পর্কে সনদ প্রদান করতেন। এখনকার দিনেও মুসলিম সমাজে এ নিয়মটি চালু রয়েছে। যারা কোরআন শরীফ হিফজ বা মুখস্থ করেন, তাদের বিশুদ্ধতা এভাবে যাচাই করা হয়।
মুসলমানদের নিকট কুরআন যেমন গুরুত্বপূর্ণ তেমনি গুরুত্বপূর্ণ নবী করীম (সা) এর হাদীসসমূহ। অতি যত্নের সঙ্গে তারা নবী করীম (সা)-এর কথা ও কর্মের বিবরণসমূহ সংরক্ষণ করেন। ব্যক্তিগত বা সমাজ জীবনের কোন কিছুই বাদ যায়নি। নবী করীম (সা)-এর কিছুসংখ্যক ঘনিষ্ঠ সহচর তার জীবদ্দশাতেই এই সংরক্ষণ প্রক্রিয়া শুরু করেন। তার ইন্তেকালের পরও এই সংরক্ষণ প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকে। সাহাবায়ে কিরাম ব্যক্তিগত উদ্যোগে এ কাজটি শুরু করেন। তাঁরা হাদীসগুলো যেভাবে শুনেছেন, ঠিক সেভাবেই লিপিবদ্ধ করেছেন। অর্থাৎ প্রাইমারী সোর্সই ছিল হাদীস সংরক্ষণের মূল উৎস। সাহাবীগণ কারো নিকট কোরআনের আয়াত বর্ণনার সময় এর যথার্থতা অক্ষুন্ন রাখার ব্যাপারে যেমন সতর্ক থাকতেন তেমনি সতর্ক থাকতেন হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে।
হযরত নূহ (আ), হযরত মুসা (আ), হযরত ঈসা (আ) সহ অন্যান্য আম্বিয়া কিরামের সম্পর্কে কিংবা বুদ্ধ সম্পর্কে আমরা খুব সামান্যই জানি। বিস্তারিতভাবে কেউ লিখতে চাইলেও পৃষ্ঠা কয়েকের মধ্যেই তা শেষ হয়ে যায়। কিন্তু নবী করীম (সা)-এর জীবনী এত বিস্তারিতভাবে জানা আছে যে, শত শত পৃষ্ঠা লিখেও তা শেষ করা যায় না। ভবিষ্যৎ বংশধরদের জন্য তাঁর জীবনী যে কত যত্নের সঙ্গে সংরক্ষণ করা হয়েছে এ ঘটনা থেকেই তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে।
নবী করীম (সা)-এর জীবনকালেই মুসলমানগণের মধ্যে ইসলাম সম্পর্কে চিন্তার উন্মেষ ঘটে। পরবর্তীকালে এর উপর ভিত্তি করেই বিকশিত হয় বিভিন্ন বিজ্ঞানের। এর মধ্যে রয়েছে কালাম শাস্ত্র ও তাসাউফ বিজ্ঞান। মুসলমানগণের মধ্যে বেশ কিছু সংখ্যক প্রতিভাবান দার্শনিক জন্ম নেন। এদের মধ্যে ছিলেন আল-কিন্দি, আল ফারাবী, ইবন সিনা, ইবন রুশদ এবং আরো অনেকে। তাদের মৌলিক দর্শন ও পাণ্ডিত্যে ইলম, কালাম ও তাসাউফ বিজ্ঞান আরো সমৃদ্ধ হয়।
এছাড়া গ্রীক ও সংস্কৃত ভাষায় রচিত দর্শন সম্পর্কিত শত শত পুস্তক আরবি ভাষায় অনূদিত হয়। লক্ষণীয় বিষয় এই যে, মূল গ্রীক ও সংস্কৃত ভাষায় রচিত এ সমস্ত দর্শন গ্রন্থের বেশির ভাগই বিনষ্ট হয়ে গেছে। কিন্তু অনূদিত গ্রন্থসমূহ ভবিষ্যৎ বংশধরদের জন্য যত্নের সঙ্গে সংরক্ষিত আছে।
সমাজ বিজ্ঞানের উন্নয়ন
কোরআনুল করীম আল্লাহর কালাম। এর ভাষা আরবি। ইতিপূর্বে আরবি ভাষায় কোন পুস্তক ছিল না। পরবর্তীতে মাত্র দু’শ’ বছরের মধ্যে অশিক্ষিত বেদুঈনদের এই ভাষাই বিশ্বের অন্যতম সমৃদ্ধ ভাষায় পরিণত হয়। কালক্রমে বিজ্ঞান চর্চার ক্ষেত্রে আরবি আন্তর্জাতিক ভাষার মর্যাদা লাভ করে। এত অল্প সময়ের মধ্যে একটি ভাষা কিভাবে সমৃদ্ধির শীর্ষে পৌছল তা বিশ্লেষণ করে দেখা আবশ্যক। প্রথম যুগের মুসলমানদের বেশির ভাগই ছিলেন আরবীয়। অথচ ইসলামের প্রভাবে তারা তাদের স্বাতন্ত্রের কথা সম্পূর্ণরূপে ভুলে যান। অন্য ভাষা, বর্ণ ও গোত্রের মুসলমানগণকে পূর্ণ সমতায় গ্রহণ করার জন্য এটা দরকার ছিল। একমাত্র ব্যতিক্রম ছিল ভাষার ক্ষেত্রে। তারা আরবি ভাষাকে ভুলেননি। আর এটা এমন এক ভাষা, যে ভাষায় কোরআন ও হাদীস সংরক্ষিত হয়েছে।
বস্তুতপক্ষে সকল গোত্র ও বর্ণের মুসলমানগণকে একই সমতায় গ্রহণ করার ফলে তারা জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিকাশে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেন। আরবি, ইরাকী, গ্রীক-তুর্কী, যারাই ইসলাম গ্রহণ করেছেন, তাদের কেউ উদ্যোগ গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকেননি। মুসলমানদের ধর্মীয় সহিষ্ণুতা ছিল লক্ষ্য করার মতো। শিক্ষার ক্ষেত্রে তাদের পৃষ্ঠপোষকতা অত্যন্ত উৎকৃষ্ট মানের। ফলে খৃষ্টান, ইয়াহুদী, বৌদ্ধ এবং অন্যান্য জাতি তাদের সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেয়। নিজেদের ধর্মজ্ঞানে ও সাহিত্য দ্বারা মুসলমানদের জ্ঞান-বিজ্ঞানকে সমৃদ্ধ করে। এমনকি তাদের সহযোগিতা ও কর্মতৎপরতায় জ্ঞান-বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখারও ব্যাপক প্রসার ঘটে। আরবি ছিল মুসলমানদের অফিসিয়াল ভাষা। আর এ সময় মুসলমানদের ব্যাপ্তি ছিল স্পেন থেকে সুদূর চীন পর্যন্ত সমগ্র অঞ্চল জুড়ে। ফলে এ সময়ে অন্য যে কোন ভাষার চেয়ে আরবি ভাষার ব্যাপক বিস্তার ঘটে।
আইন
মুলমানগণই সর্বপ্রথম বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে আইন সম্পর্কে ব্যাপক চর্চা শুরু করেন। প্রাচীন কালেও আইনের প্রচলন ছিল। ক্ষেত্রবিশেষে এগুলো বিন্যাস্ত থাকলেও সে সব আইনের কোন বৈজ্ঞানিক ভিত্তি ছিল না। সে সময়ে আইনের দর্শন ও আইনের উৎস সম্পর্কে কোন আলোচনা হতো না। আইনের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ, প্রয়োগ-পদ্ধতি প্রভৃতি বিষয় সম্পর্কে আলোচনা ছিল অনুপস্থিত। এমনকি ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে এ বিষয়গুলো আইন বিশারদদের বিন্দুমাত্র নাড়া দিত না। মুসলমানগণ আইনের উৎস কোরআন ও হাদীসের আলোকে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে আইন সম্পর্কে ব্যাপক চর্চা শুরু করেন। তাঁরাই সর্বপ্রথম আইনকে বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠা করেন। এর পূর্বে আর কেউ আইনের মতো এত বস্তুনিষ্ঠ, এত বিমূর্ত বিষয় নিয়ে ব্যাপকভাবে আলোচনা করেননি। হিজরী দ্বিতীয় শতাব্দী থেকেই এর চর্চা শুরু হয়। তখন আইনকে বলা হত উসূলে ফিকহ।
প্রাচীনকালে আন্তর্জাতিক আইন বলতে যা বুঝানো হতো তাতে কোন আন্তর্জাতিকতা ছিল না। বস্তুতপক্ষে তাকে আইনও বলা যায় না। আসলে সেটা ছিল রাজনীতিরই একটা অংশ। এটা রাষ্ট্রনায়কদের ইচ্ছা এবং দয়ার উপর নির্ভর করত। তাছাড়া আন্তর্জাতিক আইনের ব্যাপ্তিও ছিল সীমিত। যে সমস্ত রাষ্ট্রে একই ধর্ম বা ভাষা ভাষীর লােকেরা বসবাস করত, কেবলমাত্র সে সমস্ত দেশের মধ্যেই এ আইন কার্যকর ছিল। মুসলমানগণ সর্বপ্রথম আইনকে একটি নির্দিষ্ট বিধি ব্যবস্থার মধ্যে নিয়ে আসেন, এর সঙ্গে জুড়ে দেন দায়িত্ব ও অধিকারের বিষয়টি। পর্যালােচনা করলে দেখা যাবে যে, ইসলামের ইতিহাসের শুরুতে যে সমস্ত চুক্তিপত্র বা আইন প্রণীত হয়েছে, সেগুলােতেও আন্তর্জাতিক ধারাসমূহ সন্নিবেশিত হয়েছে। উদাহরণ হিসাবে যায়েদ ইবন আলী এর মাজুমু এর উল্লেখ করা যেতে পারে। যায়েদ ইবন আলী ১২০ হিজরী মুতাবিক ৭৩৭ খৃস্টাব্দে ইন্তিকাল করেন। অতীত কালের যে সমস্ত চুক্তিপত্র আমাদের হাতে এসে পৌছেছে সেগুলাের মধ্যে যায়েদ ইবন আলীর চুক্তিপত্রটি সর্বাধিক প্রাচীন।
প্রসঙ্গক্রমে আরো উল্লেখ্য যে, মুসলমানদের হাতে আন্তর্জাতিক আইন স্বতন্ত্র শাস্ত্র বা বিজ্ঞান হিসাবে বিকাশ লাভ করে। এমনকি ১৫০ হিজরীর পূর্বে প্রণীত বিভিন্ন বিবরণ বা রচনায় এতদসংক্রান্ত বর্ণনা পাওয়া যায়। অবশ্য সে সময়ে আন্তর্জাতিক আইন বলতে স্বতন্ত্র কোন শিরোনাম ছিল না, ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত সিয়ার শীর্ষক শিরোনামে এ আলোচনা স্থান পেয়েছে। ইবন হাজার রচিত ‘তাওয়ালী আত-তাসীস’ গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, আন্তর্জাতিক আইন সম্পর্কে প্রথম গ্রন্থ রচনা করেন ইমাম আবু হানীফা (র)। তিনি ছিলেন যায়দ ইবন আলীর সমসাময়িক। এ গ্রন্থের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য এই যে-
- এখানে সমস্ত বিদেশীকে একই পাল্লায় পরিমাপ করা হয়েছে। অর্থাৎ তাদের মধ্যে কোন রকম তারতম্য বা কারো প্রতি কোনরকম পক্ষপাতিত্ব করা হয়নি।
- মুসলমানদের মধ্যকার পারস্পরিক সম্পর্ক কেমন হবে সে বিষয়ে এখানে কোন উল্লেখ নেই বরং গোটা বিশ্বের অমুসলিম রাষ্ট্রসমূহ এ গ্রন্থের মুখ্য আলোচ্য বিষয়। বস্তুতপক্ষে ইসলাম নীতিগতভাবে স্থান, বর্ণ, ভাষা নির্বিশেষে সকল মুসলমানকে একটি সুতায় গেঁথে দিয়েছে। সবাইকে নিয়ে গড়ে তুলেছে একটি জাতি।
মুসলমানদের গুরুত্বপূর্ণ আরেকটি অবদান রয়েছে তুলনামূলক কেইস ল-এর ক্ষেত্রে। ইসলামী আইনের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ও প্রয়োগ পদ্ধতিকে কেন্দ্র করে মুসলমানদের মধ্যে মতপার্থক্য দেখা দেয়। বিশেষ কোন আইনের ব্যাপারে কেন এ মতপার্থক্য দেখা দেয় অথবা এ জাতীয় মতপার্থক্যের ফলাফল কি হতে পারে তা নির্ধারণ করা জরুরী হয়ে পড়ে। এখান থেকেই তুলনামূলক কেইস ল-এর উদ্ভব ঘটে। এ বিষয়ের উপর দাবসী এবং ইবন রুশদ রচিত পুস্তকগুলো পথিকৃতের ভূমিকা পালন করেছে । সাইমুরী তুলনামূলক আইন বিজ্ঞান বা আইন পদ্ধতির উপর পুস্তক রচনা করেন। আরবি পরিভাষায় এ জাতীয় পুস্তককে বলা হয় উসূলে ফিকহ।
মুসলমানগণই সর্বপ্রথম রাষ্ট্রের জন্য লিখিত সংবিধান প্রণয়ন করেন। বস্তুতপক্ষে নবী করীম (সা) ছিলেন এ সংবিধানের রচয়িতা। তিনি যখন মদীনায় নগর রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেন, তখন এ সংবিধান প্রণয়ন করেন। ঐতিহাসিক ইবন হিশাম এবং আবু উবায়েদের বর্ণনার মধ্য দিয়ে এটা আমাদের হাতে পৌঁছেছে। রাষ্ট্রীয় প্রশাসন, আইন প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন, বিচার ব্যবস্থা প্রতিরক্ষা প্রভৃতি সকল বিষয় সংবিধানে সন্নিবেশিত হয়েছে। রাষ্ট্রনায়ক তথা জনগণের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছে স্পষ্টভাবে। ৫২টি ধারা সম্বলিত এ সংবিধানটি প্রণয়ন করা হয় ৬২২ খৃষ্টাব্দে। এখানে ইসলামী আইনকে প্রধানত তিনটি পর্যায়ে বিভক্ত করা যায়-
- ধর্মীয় আচার আচরণ,
- যাবতীয় চুক্তি সম্পর্কিত বিষয়সমূহ,
- শাস্তি সম্পর্কিত বিষয়াদি।
প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, ইসলাম মানুষের জীবনকে দেখে সামগ্রিকভাবে। এখানে মসজিদ ও দুর্গের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। এখানে রাষ্ট্রের বিধিবিধান বা সংবিধানের ধারাগুলো বিবেচিত হয় ধর্মীয় বিধি-নিষেধের অংশ হিসাবে। কারণ এখানে যিনি রাষ্ট্রের প্রধান, তিনিই ধর্মীয় নেতা ও মসজিদের ইমাম। আবার সরকারের রাজস্ব ও অর্থব্যবস্থাকে গণ্য করা হয় ধর্মের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে। কারণ, নবী করীম (সা)-এর ঘোষণা অনুসারে সালাত, ইসলাম ও হজ্জের মতো এটাও (যাকাত) ইসলামের একটি স্তম্ভ। অনুরূপভাবে আন্তর্জাতিক আইন দণ্ডবিধির একটি অংশ। আর লুটতরাজ, ডাকাতি, রাহাজানি, আইন বা চুক্তি অমান্যকারীদের গৃহীত ব্যবস্থাকে গণ্য করা হয় জিহাদের মর্যাদায়।
ইতিহাস ও সমাজ বিদ্যা
ইতিহাস এবং সমাজ বিদ্যায় মুসলমানদের অবদান প্রধানত দুটি ক্ষেত্রে
- তথ্য নির্ভর এবং বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ পরিবেশন,
- নানান প্রাসঙ্গিক বিষয়ে বিচিত্র ধরনের তথা সংগ্রহ ও সংরক্ষণ।
ইসলামের ইতিহাস অত্যন্ত পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন। এখানে পৌরাণিক কাহিনী বা কল্পলোকের কোন স্থান নেই । ইসলামের ইতিহাস প্রণয়নের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের সূক্ষ্ম ও যুক্তিগ্রাহ্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। হাজার বছর পরেও যাতে এর সত্যতা ও নির্ভরযোগ্যতা সম্পর্কে প্রশ্ন না ওঠে তা নিশ্চিত করাই এর উদ্দেশ্য। এমন একটি সময় ছিল যখন প্রত্যক্ষ সাক্ষী ছিল বিচার বিবেচনার প্রধান বৈশিষ্ট্য। মুসলমানগণ ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে এ বৈশিষ্ট্য গ্রহণ করেন। প্রতিটি বিবরণের জন্য তাদেরকে নির্ভরযোগ্য প্রমাণ উপস্থাপন করতে হত।
ঐতিহাসিক সাক্ষী প্রমাণের বিষয়টি ছিল এ রকম—কোন এক সময়ে হয়ত একটি ঘটনা ঘটে গেল। সমসাময়িকালের বিশ্বাসযোগ্য কোন লোকের নিকট থেকে ঘটনার বিবরণও পাওয়া গেল। এমতাবস্থায় তার দেয়া বর্ণনাকে যথার্থ বলে ধরে নেয়া যায়। কিন্তু দ্বিতীয় প্রজন্মের সময় এ ঘটনা লিপিবদ্ধ করতে হলে আনুক্রমিকভাবে দুটি সূত্রের উল্লেখ করতে হবে। যেমন—আমি ‘ক’-এর নিকট থেকে শুনেছি। আর ক শুনেছে খ-এর কাছে। আর ‘ক’ হলো ঘটনায় সমসাময়িককালের লোক এবং তার বিবরণও বিস্তৃত ও দীর্ঘ। আর তৃতীয় প্রজন্মের ক্ষেত্রে অনুক্রমিকভাবে তিনটি সুত্রের উল্লেখ করতে হবে। ইতিহাস রচনার এ ধারাটি কেবলমাত্র নবী করীম (সা)-এর জীবনী রচনার মধ্যে সীমিত নয়। বরং যুগ যুগান্তর ধরে যে সমস্ত জ্ঞান-বিজ্ঞান আমাদের নিকট পৌছেছে, সেগুলোর ক্ষেত্রে এ কৌশলটি প্রয়োগ করা হয়েছে। এমনকি নিছক রস-কৌতুক ও গল্প-কাহিনীর ক্ষেত্রেও অনুরূপ আনুপূর্বিক বর্ণনাকারীর বিবরণ পাওয়া যাবে।
মুসলমানদের ইতিহাস চর্চার একটি অনন্য বৈশিষ্ট্য হল জীবনীভিত্তিক অভিধান প্রণয়ন। অভিধানগুলো সংকলন করা হয়েছিল বিভিন্ন পেশা, শহর বা স্থান, শতাব্দী বা ঘটনাপ্রবাহ প্রভৃতি বিষয় অনুসারে। অনুরূপভাবে গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছিল বংশ বৃত্তান্তের উপর। বিশেষ করে আরবদের ক্ষেত্রে ইতিহাস রচনার প্রচেষ্টায় এ ধারাটি বেশি প্রযোজ্য। গুরুত্বপূর্ণ অসংখ্য ব্যক্তিত্ব এতে স্থান পেয়েছেন। বিভিন্ন ঘটনার কারণ অনুসন্ধানে এটা ঐতিহাসিক গবেষকগণের জন্য খুবই সহায়ক ছিল।
মুসলমানদের রচিত ইতিহাসের একটি বৈশিষ্ট্য হলো সামগ্রিকতা। ইসলাম পূর্ব যুগের ঐতিহাসিকগণ কেবলমাত্র জাতীয় ইতিহাস রচনা করতেন। তদৃস্থলে মুসলমানগণই সর্বপ্রথম বিশ্বের ইতিহাস রচনার প্রতি মনোনিবেশ করেন। উদাহরণ হিসাবে ইবন ইসহাকের কথা বলা যেতে পারে । তিনি ৭৬৯ খৃষ্টাব্দে ইন্তিকাল করেন এবং ইসলামের প্রথম কালের একজন ঐতিহাসিক। তার বৃহদাকারের ইতিহাস গ্রন্থের শুরুতেই রয়েছে বিশ্ব জগতের সৃষ্টির বিবরণ। এরপরই এসেছে হযরত আদম (আ)-এর বৃত্তান্ত। কালের অন্যান্য জাতি ও গোত্রের বিবরণও স্থান পেয়েছে এ গ্রন্থে। বস্তুতপক্ষে ইবন ইসহাকের উত্তরসূরিগণও ছিলেন একই ধারার অনুসারী। ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে তারাও সামগ্রিকতার প্রতি বিশেষ মনোযোগ দেন। এদের মধ্যে ছিলেন ইবন কাসীর, তাবারী মাসউদী, মিশকাভি, সাইদ আন্দালুসী, রশীদুদ্দীন খান এবং আরো অনেকে। লক্ষণীয় বিষয় এই যে, এ সমস্ত ঐতিহাসিক ইতিহাস রচনার সময় সমসাময়িক কাল সম্পর্কে একটি বিবরণ তুলে ধরেন। বিশেষ করে ইবন খালদুনের দার্শনিক এবং সমাজবিজ্ঞান সম্পর্কিত আলোচনা ছিল খুবই ব্যাপক ও বিস্তীর্ণ। তার রচিত বিশ্ব ইতিহাস বিষয়ক গ্রন্থের ভূমিকায় (মুকাদ্দমা) এ বিষয়টি উঠেছে খুবই স্পষ্টভাবে।
ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে মুসলমানদের মধ্যে দুটি ধারা লক্ষ্য করা যায়। একটি ধারাকে বলা যায় পুরোপুরি ইসলামের ইতিহাস, নবী করীম (সা) এবং খোলাফায়ে রাশেদীনের জীবন ও কর্ম এর প্রধান উপজীব্য। অন্য ধারায় রয়েছে অমুসলিম ইতিহাস। ইসলামপূর্ব যুগের আরব থেকে শুরু করে সমসাময়িককালের বিশ্ব পরিস্থিতি যেমন—রোম, পারস্য এসবই ছিল অমুসলিমদের ইতিহাসের কেন্দ্রীয় বিষয়বস্তু। বস্তুতপক্ষে হিজরী প্রথম শতাব্দীতেই ইতিহাস রচনার এ দুটি ধারা স্বতন্ত্রভাবে বিকাশ লাভ করে। অবশ্য পরবর্তীতে ইতিহাস রচনার এ দুটি ধারা স্বতন্ত্রভাবে বিরাজ করেনি। বরং এ দুটি ধারা মিলে একটি সামগ্রিক রূপ গ্রহণ করে। ঐতিহাসিক রশীদুদ্দীন খানের রচিত ইতিহাস গ্রন্থই এর স্বাক্ষর বহন করে। এখানে আম্বিয়ায়ে কিরাম, নবী করীম (সা) এবং খলীফাগণের জীবন ও কর্ম যত ব্যাপকভাবে আলোচিত হয়েছে, তেমনি স্থান পেয়েছে যাজক সম্প্রদায় তথা রোমান, পারস্য, চীন, ভারত, মঙ্গলীয় শাসকগণের জীবন ও কর্ম। গ্রন্থটি একাধারে আরবি ও ফার্সি ভাষায় রচিত হয়েছে। অবশ্য বৃহদাকারের এ গ্রন্থটির বিরাট অংশ এখানো মুদ্রণের অপেক্ষায় আছে।
সূত্রঃ ডঃ হামীদুল্লাহর বিখ্যাত গ্রন্থ “Introduction to Islam” থেকে সংকলিত।