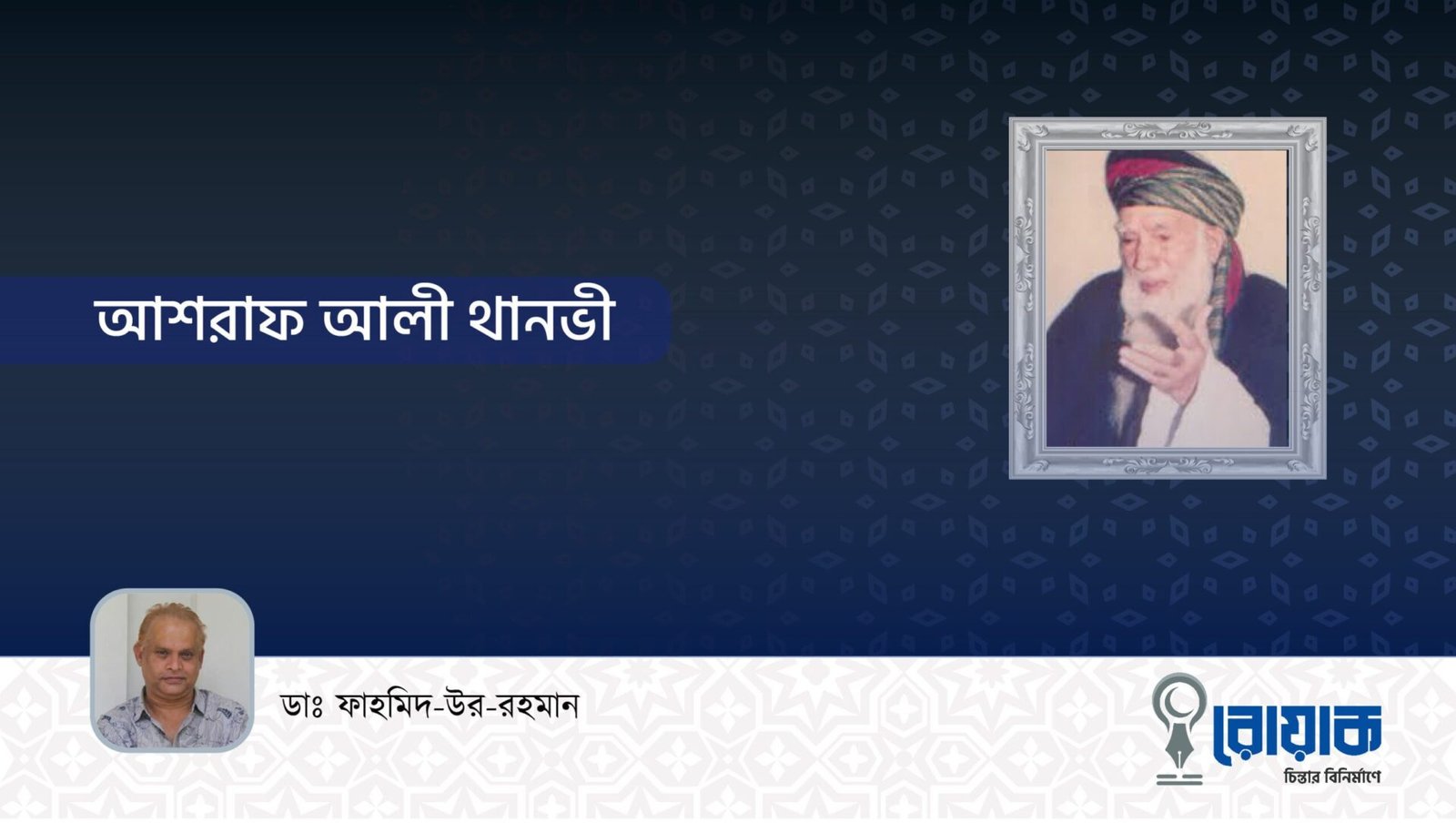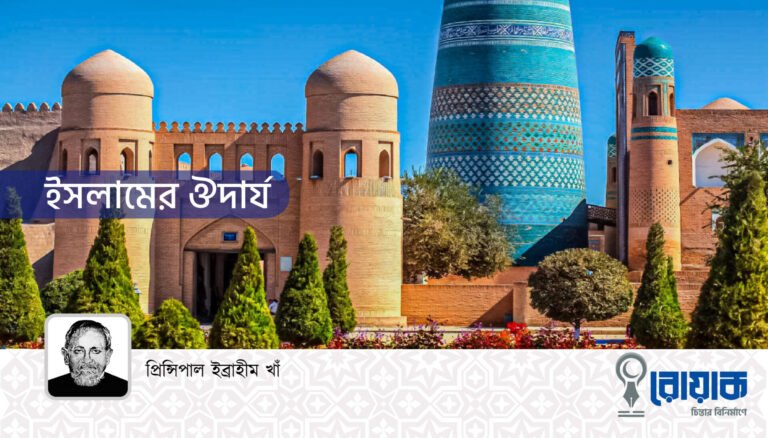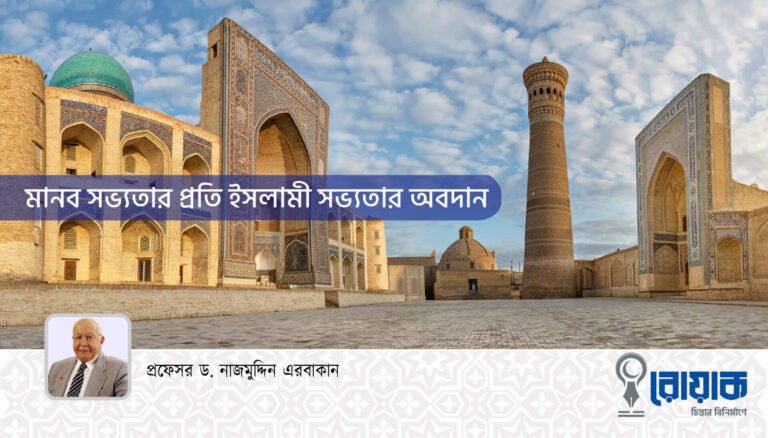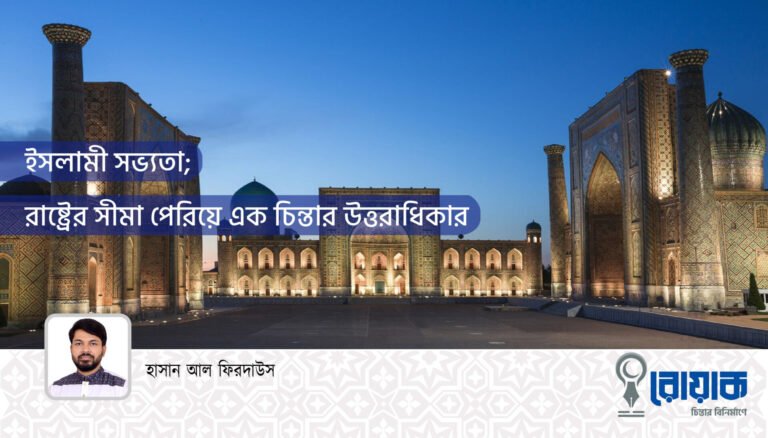এক.
আশরাফ আলী থানভীকে বলা হয় হাকিম উল উম্মত। হাকিম উল উম্মত অর্থ হচ্ছে জাতির চিকিৎসক। চিকিৎসক যেমন তার পেশাগত জ্ঞান দিয়ে অসুস্থ ব্যক্তিকে ধীরে ধীরে আরোগ্য করে তোলেন, তেমনি থানভী ঔপনিবেশিক ভারতে বিধ্বস্ত, পিছিয়ে পড়া, প্রান্তিক মুসলমানদের ভিতরে ইসলামী নৈতিকতার আলো জ্বালিয়ে তাদের আত্মবিশ্বাসকে পুনর্জীবিত করার চেষ্টা করেছিলেন।
ভারতে কয়েকশ বছরের মুসলিম শাসনের অবসান এবং ১৮৫৭ সালের আজাদী আন্দোলনের ব্যর্থতা পরবর্তী ইংরেজের প্রতিশোধকামিতার মধ্যে ১৮৬৭ সালে উত্তর ভারতে বিখ্যাত দারুল উলুম দেওবন্দ মাদরাসা প্রতিষ্ঠিত হয় মাদরাসার প্রতিষ্ঠাতারা ছিলেন ১৮৫৭’র আজাদীর যুদ্ধে বেঁচে যাওয়া কয়েকজন গাজী মুসলমান। এরা মনে করেছিলেন রাজনৈতিক ও সামরিকভাবে পরাজিত মুসলমানদের নৈতিকভাবে যদি শক্তিশালী না করা যায় তবে ভারতের বুকে ইসলাম স্পেনের পরিণতি বরণ করতে পারে। ১৮৫৭’র যুদ্ধে আলেমরা আজাদীর অন্বেষায় বেহিসাব খুন ঝরিয়েছিলেন। কিন্তু সেই আজাদী তখন মেলেনি। নতুন পরিস্থিতিতে আলেমরা তাই ইসলামী নৈতিকতা ও সংস্কৃতির চর্চা করে একদিকে ইংরেজের রাজনৈতিক অভিঘাত, অন্যদিকে খ্রিস্টান মিশনারীদের উপদ্রব এবং ইসলামের বিরুদ্ধে ওরিয়েন্টালিস্টদের নিরবিচ্ছিন্ন বুদ্ধিবৃত্তিক প্রচারণার মোকাবেলা করতে চেয়েছিলেন। দেওবন্দ মাদরাসা এই বিপ্লবী আলেমদের Brain Child ভাব সন্তান। আশরাফ আলী থানভী ছিলেন এই মাদরাসার ছাত্র এবং এর বিপ্লবী সিলসিলার সার্থক ওয়ারিশ। অধ্যাপক কাশিম জামান দেওবন্দ মাদরাসার এই বৈশিষ্ট্যের কথা তুলে ধরেছেন, যা আমরা পরবর্তীকালে থানভীর জীবনে প্রতিবিম্বিত হতে দেখি :
To the early Deobandis, a self-conscious adherence to the teachings of the Qur’an and the hadith, as refracted through the norms of the Hanafi school of law, and a sense of individual moral responsibility were among the best means not only of salvation but also of preserving an Islamic identity in the adverse political conditions of British colonial rule.
আশরাফ আলী থানভী ছিলেন একাধারে দরবেশ ও সুফী, মুফতী, শাস্ত্রজ্ঞ, শিক্ষক, সংস্কারক, লেখক ও প্রচারক। থানভী প্রধানত মুসলমান নারীদের ভিতরে সেইকালে সংস্কার আনবার জন্য লিখেছিলেন তার বিখ্যাত গ্রন্থ বেহেশতী জেওর বা স্বর্গীয় অলংকার। এটি গত শতাব্দীর একটি অন্যতম প্রভাবশালী কিতাব যা উপমহাদেশের সাধারণ মুসলমান জনগণের জীবনকে বিপুলভাবে প্রভাবিত করেছে। ইসলামী শাস্ত্র ও ধর্মতত্ত্ব নিয়ে থানভীর লেখালেখি, বিভিন্ন বিষয়ভিত্তিক তার অসংখ্য ফতওয়া যেমনি জীবদ্দশায় তাকে অত্যন্ত প্রভাবশালী আলেমে পরিণত করেছিল, তেমনি উত্তর ঔপনিবেশিক উপমহাদেশে ইসলামী আইনের কাঠামো নির্মাণে তার চিন্তা এখনও ক্রিয়াশীল রয়েছে । শুধু তাই নয়, লেখালেখির পাশাপাশি তার কয়েকজন স্বনামধন্য ছাত্র দক্ষিণ এশিয়ায় ইসলামের বুদ্ধিবৃত্তির জগতকে রীতিমত রোশনাই করে দিয়েছেন। থানভী ও তার ছাত্ররা আধুনিককালে দক্ষিণ এশিয় ইসলামের একটি রূপ দেয়ার চেষ্টা করেছেন, পাশাপাশি তাদের ধর্মীয় কর্তৃত্ব কীভাবে বুদ্ধিবৃত্তি ও রাজনীতির জগতকে প্রভাবিত করেছে সেটিও চিত্তাকর্ষক আলোচনার বিষয়।
দুই.
আশরাফ আলী থানভী ১৮৬৩ সালের ১৯ নভেম্বর ভারতের উত্তর প্রদেশের ক্ষুদ্র শহর থানাভবনে জন্মগ্রহণ করেন। তার আব্বার নাম ছিল আবদুল হক, যিনি এলাকার একজন প্রতিপত্তিশালী জমিদার ছিলেন। থানভীর ভাষায় তার আব্বা আবদুল হক ছিলেন একজন বৈষয়িক মানুষ যিনি তার ছোট ছেলে আকবর আলীকে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত করে ব্রিটিশ প্রশাসনের চাকুরে বানিয়েছিলেন এবং বড় ছেলে আশরাফ আলীকে দ্বীনি শিক্ষা দেয়ার জন্য দেওবন্দ পাঠিয়েছিলেন। উত্তর ভারতের বড় বড় শহরগুলো থেকে দূরে থানাভবন ছিল সুফী ও বুদ্ধিজীবীদের শহর ও শিক্ষা কেন্দ্র মোগল বাদশাহরা লাখেরাজ সম্পত্তি দিয়ে এটিকে একটি মুসলিম সংস্কৃতির কেন্দ্রে পরিণত করেছিলেন। এই শহরেই বাস করতেন বিখ্যাত সুফী হাজী ইমদাদউল্লাহ মক্কী মুহাজির (মৃ: ১৮৯৯), যিনি ১৮৫৭ সালের ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আজাদীর লড়াইয়ে শরিক হয়েছিলেন। সেই লড়াই ব্যর্থ হলে ব্রিটিশের আক্রোশে পড়ে তিনি মক্কা চলে যান এবং সেখানেই বাকি জীবন জ্ঞান ও তাসাউফ চর্চার মধ্যে কাটিয়ে দেন। হাজী ইমদাদউল্লাহর শিষ্য ছিলেন মোহাম্মদ কাশেম নানুতভী (মৃঃ ১৮৭৭) ও রশীদ আহমদ গঙ্গোহী (মৃ: ১৯০৫), যে দুইজন ব্যক্তিকে দেওবন্দের প্রাথমিক প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে গণ্য করা হয় । আশরাফ আলী থানভীও মক্কায় গিয়ে হাজী ইমদাদউল্লাহর কাছে তাসাউফের দীক্ষা নিয়েছিলেন।
থানভীর প্রাথমিক শিক্ষা শুরু হয় কুরআন শরীফ মুখস্থ করে এবং আরবি ও পারসি ভাষা শিখে যেটাকে সেইকালে উচ্চতর ইসলামী শিক্ষার সূচনাপর্ব হিসেবে দেখা হতো। থানভী ১৮৭৮ সালে দেওবন্দ মাদরাসায় আসেন এবং পরবর্তী পাঁচ বছর এখানে কাটান । এই মাদরাসাকে কেন্দ্র করেই থানভীর চিন্তার কাঠামো নির্মিত হয়। থানভীকে বলা যায় একজন মধ্যপন্থী আলেম। তিনি ইসলামী চিন্তার সংস্কার চাইতেন কিন্তু দ্রুততার পক্ষপাতী ছিলেন না। থানভী মাদরাসা শিক্ষার কারিকুলাম সংস্কারেরও পক্ষপাতী ছিলেন এবং তিনি এটাও বুঝতে পারতেন ধর্মীয় শিক্ষাকে যুগের প্রয়োজন ও চাহিদার সাথে সমন্বয় করা দরকার। তবে থানভী দেওবন্দের যে আবহাওয়ায় বেড়ে উঠেছিলেন সেখানকার আলেমদের একটা সংগত সন্দেহ ছিল সংস্কারের নামে ঔপনিবেশিক চিন্তা যেন শিক্ষাকে কলুষিত না করে ফেলে এবং থানভীও সেই সন্দেহ থেকে মুক্ত ছিলেন না। দেওবন্দের শিক্ষা জীবন শেষ করে তিনি উত্তর প্রদেশের কানপুরের ফয়েজ এ-আম মাদরাসায় শিক্ষকতা শুরু করেন এবং একটানা ১৪ বছর এই পেশায় নিজেকে নিয়োজিত রাখেন। এই সময়ে শিক্ষক ও সুফী হিসেবে তার খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। তার পাঠদানের কৌশল অসংখ্য ছাত্রকে আকর্ষণ করে এবং তার ফতওয়া ও রচনাবলী বিভিন্ন ইসলামী প্রতিষ্ঠানে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। এই সময়ে তিনি বিভিন্ন শহর ও গ্রাম সফর করেন। মানুষকে সংস্কারের জন্য বক্তৃতা করেন এবং ছাপার অক্ষরে তার বক্তৃতা ও আলোচনা বিপুল মানুষের হাতে পৌঁছে যায়।
শিক্ষক হিসেবে থানভী মনে করতেন ঔপনিবেশিক আবহাওয়ায় মুসলমানদের জন্য ধর্মীয় শিক্ষা খুবই প্রয়োজন। কেননা এটি তাদের সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় আত্মপরিচয় টিকিয়ে রাখবে। কিন্তু থানভী শুধুমাত্র হাদিসের শিক্ষক ছিলেন না তিনি একই সাথে ছিলেন সুফী এবং তিনি বিশ্বাস করতেন শুধুমাত্র গ্রন্থগত বিদ্যাই একমাত্র ধর্মীয় জ্ঞান নয়। ১৮৮৪ সালে কানপুর মাদরাসায় শিক্ষকতার প্রথম বছরেই তিনি হজ্বে যান এবং সেখানে সুফী ইমদাদউল্লাহর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। থানভীর সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য জীবনীকার খাজা আযীযুল হাসান লিখেছেন এইভাবে তাঁর তাসাউফ চর্চা শুরু হয় এবং ১৮৯০ সাল থেকে তিনি এটিকে প্রায় জীবনচর্চার অংশ বানিয়ে ফেলেন। দেওবন্দ ঘরানার বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী থানভীকে দেয়া ইমদাদউল্লাহর পরামর্শ কখনোই প্রচলিত সুফীদের মতো শাস্ত্রের সীমানা অতিক্রম করেনি। দেওবন্দের আলেমরা তাসাউফের গুরুত্বকে কখনোই অস্বীকার করেননি। কিন্তু সেটা হানাফী মাজহাবের শাস্ত্রীয় পরিসরের ভিতরে হতে হবে বলে তারা মনে করতেন।
সুফীদের পথ যেমন কষ্টের তেমনি কষ্টের পরিণতিতে আসে এক অনির্বচনীয় আনন্দ। সুফীরা এই কষ্টসাধ্য সাধনার ভিতর দিয়ে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের চেষ্টায় মগ্ন থাকেন এবং প্রতিনিয়ত সংশয়ে থাকেন তাদের কোনো জাগতিক বিচ্যুতি সেই সন্তোষ অর্জনে বাধা হয়ে দাঁড়ায় কিনা। থানভীও এরকম আধ্যাত্মিক সংশয় ও অনিশ্চয়তার মধ্যে পাড়ি দিয়েছেন। এ সময় সুফী ইমদাদুল্লাহ তাকে অবিরাম পরামর্শ ও পথ বাতলে দিয়েছেন । এরকম সংকট ইমাম গাজ্জালীর জীবনেও আমরা দেখি যার কথা তিনি আল মুনকিদ মিন আল দালাল-এ বিস্তারিত লিখেছেন। থানভী এরকম অবস্থায় ১৮৯২-৯৩ সালে আবার মক্কা যান এবং ইমদাদুল্লাহর সাহচর্যে ৬ মাস কাটান।
ইমদাদুল্লাহ ছিলেন চিশতী তরিকার সেই অংশের অনুসারী যারা আন্দালুসিয়ার সুফী ইবনুল আরাবীর অনুরাগী ছিলেন। এই সুফীর চিন্তার মূল কথা ছিল আল্লাহই চূড়ান্ত সত্য এবং এই বাস্তবতা তার সকল সৃষ্টির ভিতর দিয়ে প্রকাশ পায় অনেকে এই চিন্তার সমালোচনা করেছেন এই বলে যে এটি ইসলামের বিশুদ্ধ তৌহীদ ভাবনার সাথে পুরোপুরি বেমানান। বিশেষ করে ভারতের হিন্দু সর্বেশ্বরবাদী চিন্তার আবহাওয়ায় এ আরও বিপজ্জনক। যদিও ইবনুল আরাবীর অনুগ্রাহীরা এই অভিযোগকে স্বীকার করেন না। তাদের মত হচ্ছে ইবনুল আরাবীর চিন্তা তৌহিদের নির্যাস দিয়ে তৈরি।
মক্কায় থাকাকালে থানভীর চিন্তার উপরে ইবনুল আরাবীর চিন্তার প্রভাব কতকটা পড়েছিল। থানভীর সাথে তার দুই উস্তাদ ইমদাদুল্লাহ ও রশীদ আহমদ গঙ্গোহীর চিন্তার কোনো কোনো বিষয়ে ভিন্নমত হতো। ইমদাদুল্লাহ ভারতে মিলাদুন্নবী উদযাপন, এসব অনুষ্ঠানে রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর রুহানী আগমন, তাকে দাঁড়িয়ে ইজ্জত করা, মুসলিম সাধকদের মাযারকে কেন্দ্র করে উরশ প্রভৃতিকে তেমন একটা দূষণীয় মনে করেননি। গঙ্গোহী মনে করতেন এসব প্রথার পক্ষে শরীয়তের কোনো অনুমোদন নেই এবং এর কোনো কোনোটি রীতিমত অবিশ্বাসের পর্যায়ভুক্ত। থানভীর মত ছিল এসব অনুষ্ঠান দূষণীয় নয় যতক্ষণ না এটা ধৰ্মীয় বাধ্যবাধকতায় পরিণত হয়।
আধ্যাত্মিক সংকটের ভিতর দিয়ে থানভীর যে যাত্রা শুরু হয়েছিল ১৮৯৭ সালে তার একটা যবনিকা ঘটে। তিনি মাদরাসা ছেড়ে দেন এবং নিজ পিতৃগৃহ থানাভবনে চলে যান । সেখানে তিনি ইমদাদুল্লাহর নামে খানকায়ে ইমদাদিয়া নামে সুফী আবাস গড়ে তোলেন, যেখানে তার উস্তাদও এক সময় বসবাস করতেন। থানভী ভারতের বিভিন্ন জায়গা পরিভ্রমণ করেন। কিন্তু তার আবাস শেষ পর্যন্ত খানকায়ে ইমদাদিয়াই রয়ে যায়। এই খানকায় বসে থানভী সারা ভারত থেকে আগত অসংখ্য ভক্ত, মুরীদ ও দর্শনার্থীদের দেখা দিতেন। দীর্ঘদিন তিনি দেওবন্দ মাদরাসার একজন পৃষ্ঠপোষক ছিলেন এবং মাদরাসার নীতি নির্ধারণী ব্যাপারে ভূমিকা রাখতেন। ১৯৪০ এর দশকে থানভী দেওবন্দ মাদরাসার ব্যবস্থাপক কমিটি থেকে এটির কংগ্রেস ঘেঁষা আচরণের প্রতিবাদে পদত্যাগ করেন।
খানকাহতে তিনি মুরীদদের দিক নির্দেশনা দিতেন, নানা প্রশ্নের জওয়াব দিতেন নিয়মিত ভক্ত, অনুরাগী ও উৎসাহীদের চিঠি পত্রের উত্তর দিতেন ও তাসাউফ নিয়ে নানা রকম আলোচনা করতেন। প্রশ্ন ও চিঠির উত্তরের বিষয় হতো বিভিন্ন রকম। যেমন বিবাহ, তালাক, উত্তরাধিকার, পারস্পরিক সম্পর্ক, অর্থনৈতিক লেনদেন বিষয়ক ফতওয়া, কিছু ছিল সমকালীন রাজনৈতিক বিতর্ককেন্দ্রিক, কিছু মুরীদদের আধ্যাত্মিক উন্নতি বিষয়ক । থানভীর এসব ফতওয়া, লেখালেখি, বক্তৃতা ও পরামর্শকে সংগ্রহ করে অসংখ্য মালফুজাত (সুফীর বাণী) প্রকাশিত হয়েছে। এর মধ্যে ১০ খণ্ডে প্রকাশিত আল-ইফাদাত আল-ইয়ামিয়া মিন আল-ইফাদাত আল-কিয়ামিয়া (জনগণের কল্যাণে নৈমিত্তিক পরামর্শ) খুবই একটি দরকারী ফতওয়া বিষয়ক বই।
থানতীকে কেন্দ্র করে খানকাহতে একটা উন্নতমানের নৈতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক পরিবেশ গড়ে উঠেছিল। এখান থেকে নিয়মিত আল নূর পত্রিকা প্রকাশিত হতো । যেটি থানভীর চিন্তাভাবনা প্রসারে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখে। এখানে বসে থানভী মওলানা রুমির মসনভির এক গুরুত্বপূর্ণ তাফসির লেখেন। এতে তাকে সাহায্য করেন তার দুই শিষ্য শাব্বির আলী ও হাবিব আহমদ কিয়ারনভি।
থানভীর আর একটি উল্লেখযোগ্য কাজ হচ্ছে কুরআন শরীফের তাফসির যা বায়ানুল কুরআন নামে সমাদৃত হয়েছে। তরজমার পর বাংলায় এটি তাফসিরে আশরাফি নামে প্রকাশিত হয়েছে। থানভী তাফসির থেকে শুরু করে বহু বিচিত্র বিষয়ে লেখালেখি করেছেন। তিনি জীবদ্দশায় ৩৪৫টি বই ও পুস্তিকা লিখেছেন এবং তার বক্তৃতা সংগ্রহ ৩০০ অতিক্রম করেছে। ইংরেজিতে তরজমা হয়েছে থানভীর এরকম কয়েকটি উল্লেখযোগ্য কিতাব হচ্ছে :
1.The wisdom behind the commands of Islam.
2.Perfecting women.
3.The principles and codes of law in Hanafi Fiqh.
4.Answer to modernism.
5.Remedies from the Holy Qur’aan: an abridged translation of Amaale Qur’aani.
6.Maulana Thanwi’s stories of saints: translation, Qisasul Akbir. 4. Philosophy of Islam.
7.The Objective Distinction between the Desirable and the Dreadful.
8.Deed and Retribution: An Islamic Approach to the Question.
9.Islam the Whole Truth.
10.Desire for the Aa-khirah.
11.A Remedy for the Droughts and Calamities.
থানভী যেমন বুদ্ধিবৃত্তির লিখিত ঐতিহ্য সৃষ্টি করেছিলেন তেমনি অসংখ্য বুদ্ধিমান শিষ্য, প্রশিষ্য ও মুরীদ তৈরি করেছিলেন, যারা থানভী বিশেষ করে দেওবন্দী চিন্তাকে বিকশিত করে অনেকদূর এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন। এদের মধ্যে খুবই বিখ্যাত হয়েছেন মুফতী মোহাম্মদ শফী (মৃ: ১৯৭৬), জাফর আহমদ উসমানী (মৃঃ ১৯৭৪), মোহাম্মদ তকী উসমানী এবং বাংলাদেশের শামসুল হক ফরিদপুরী (মৃঃ ১৯৬৯)।
ভারতের মুসলিম ভাবজগতে দেওবন্দের সবচেয়ে বড় অবদান হচ্ছে এটি ভারতের মুসলিম সমাজের নানা অসংগতি, কুপ্রথা ও স্থানীয় আচারকে সংস্কার করে শরীয়তের নৈতিকতা ও আদবকে প্রতিস্থাপন করতে পেরেছিল এবং মুসলিম সমাজের ইসলামায়ণ প্রক্রিয়াকে একটি প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিয়েছিল। শুধু তাই নয় ঔপনিবেশিক ও অমুসলিম অধ্যুষিত ভারতে মুসলমানরা কীভাবে তাদের ধর্ম ও সংস্কৃতিকে বাঁচিয়ে রাখবে তার পথও দেওবন্দ বাতলে দিয়েছিল। থানভীর জীবনীকার আযীযুল হাসান লিখেছেন, তিনি ১৯৪৩ সালের ২০ জুলাই ইন্তিকাল করেন।
তিন.
আশরাফ আলী থানভী রাজনীতির লোক ছিলেন না। তিনি কখনো সক্রিয় রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করেননি। কিন্তু একজন জীবন ঘনিষ্ঠ সুফী ও আলেম হিসেবে রাজনৈতিক চড়াই উতরাই ও সামাজিক সংকটের মুহূর্তে তিনি তার মূল্যবান মতামত দিয়েছেন। তিনি মনে করতেন সম্প্রদায়ের ধর্মীয় নির্দেশনার পাশাপাশি আলেমদের উচিত রাজনৈতিক নেতৃত্বকেও সুপরামর্শ দেয়া যাতে তারা শরীয়ার নির্ধারিত সীমা অতিক্রম না করে।
বিশ শতকের গোড়ার দিকে এই উপমহাদেশে শুরু হয় খেলাফত আন্দোলন। আলেমদের সহযোগিতায় এই আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন আধুনিক মুসলিম এলিট নেতারা। অটোমান খেলাফত প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় বৃটেন ও মিত্রশক্তির বিরুদ্ধে জার্মানীকে সহযোগিতা করে। যুদ্ধে জার্মানী পরাজিত হলে মিত্র শক্তি অটোমান খেলাফতকে টুকরো টুকরো করার সিদ্ধান্ত নেয়। খেলাফত আন্দোলনের উদ্দেশ্য ছিল মিত্র শক্তিকে চাপ দিয়ে অটোমান খেলাফতের ভাঙ্গন রোধ করা এবং মক্কা মদীনাকে অমুসলিম শাসনের কবলে পড়তে না দেয়া।
যখন এশিয়া ও আফ্রিকার মুসলিম জনপদগুলো ইউরোপীয় কলোনীর নিয়ন্ত্রণে চলে গেছে তখন অটোমান খেলাফতই ছিল একমাত্র দৃশ্যমান মুসলিম রাষ্ট্র যে তার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব টিকিয়ে রেখেছিল। অষ্টাদশ শতকের শেষ দিক থেকে অটোমান সুলতানরা তাদের নিয়ন্ত্রিত ভূগোলের বাইরেও যে মুসলমানরা আছে তাদের ধর্মীয় স্বার্থের রক্ষাকর্তা হিসেবে দাবি করতেন এবং সেই থেকে উনিশ শতকের শেষ দিক হতে ভারতীয় মুসলমানরা দুনিয়া জোড়া মুসলমানদের রাজনৈতিক ঐক্যের প্রতীক হিসেবে জুমার খুতবায় সুলতানের নাম উল্লেখ করতেন। যুদ্ধ শেষ হবার পর মুসলমানরা অটোমান খেলাফতের ভাঙ্গনের সম্ভাবনার মধ্যে তাদের পরিচয়গত ঐক্যের ভবিষ্যত নিয়েও উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠে। সেই উদ্বিগ্নতার খবর আমরা দেখি সেইকালের ভারতের দুইজন মুসলিম নেতা সৈয়দ আমীর আলী (মৃঃ ১৯২৮) ও সুলতান মোহাম্মদ আগা খানের (মৃঃ ১৯৫৭) মনোভাবে। ১৯২৩ সালে তারা বলেছিলেন :
…. the elimination of the Caliphate… would mean the disintegration of Islam and its practical disappearance as a moral force in the world.
মজার ব্যাপার হলো ভারতের বাইরে অবস্থিত একটি মুসলিম প্রতীককে রক্ষা করার আন্দোলনে এম কে গান্ধী ও তার দল কংগ্রেস কৌশলগত রাজনীতির সূত্রে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেয়। এভাবে ভারতে হিন্দু-মুসলিম ঐক্যবদ্ধভাবে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে এক প্লাটফরমে লড়াই করার উপযোগী পরিবেশ তৈরি হয় এবং ভারতজুড়ে বিপুল আন্দোলন গড়ে ওঠে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এত বড় আন্দোলনও সফল হয়নি। অটোমানদের সামরিক পরাজয়, তুরস্কে জাতীয়তাবাদী দলের উত্থান ও খেলাফত বিলুপ্তির ঘোষণা আন্দোলনের পিঠে শেষ পেরেক ঠুকে দেয়। উল্টো খেলাফত ও কংগ্রেসের অহিংসা ও অসহযোগ আন্দোলন শেষ পর্যন্ত হিংসাশ্রয়ী হয়ে উঠে এবং বিশৃঙ্খলা ও সাম্প্রদায়িক অসম্প্রীতিতে পর্যবসিত হয়। খেলাফত আন্দোলনের মধ্যে ঘটে মোপালা মুসলমানদের স্বাধীনতাকামী অভ্যুত্থান এবং ব্রিটিশ ও হিন্দু জমিদাররা সেই অভ্যুত্থানকে নির্মমভাবে দমন করে। খেলাফত আন্দোলনে সংশ্লিষ্ট আলেমরা ভারতকে দারুল হরব ঘোষণা দেয়ায় অনেক মুসলমান দেশ ছেড়ে আফগানিস্তানে পাড়ি জমানোয় প্রচুর দুর্ভোগের মধ্যে পড়ে। এই যে এত বড় খেলাফত আন্দোলন পুরো ভারতবাসীকে নাড়িয়ে দিয়েছিল তা কিন্তু থানভীকে মোটেই আকৃষ্ট করেনি। যেমন করেনি মোহাম্মদ আলী জিন্নাহকে (মৃ: ১৯৪৮)। থানভী এই আন্দোলনের নৈতিক দিক নিয়ে প্রশ্ন করেছিলেন। জিন্নাহ এই আন্দোলনের অনিয়মতান্ত্রিক ও বিশৃঙ্খল চরিত্র নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন।
খেলাফত নেতাদের থানভী তীব্র সমালোচনা করেছেন এই বলে যে তারা যেকোনো উপায় ও নীতি অবলম্বন করে লক্ষ্যে পৌঁছতে চায়। গান্ধীর নেতৃত্বের ব্যাপারে তিনি যথেষ্ট সন্দিহান ছিলেন এবং কুরআনের বাগধারা ব্যবহার করে তিনি তাকে তাগুদ হিসেবে উল্লেখ করতেন। গান্ধীর বয়ান ও রাজনীতির মধ্যে তিনি মুসলমানদের জন্য কোনো কল্যাণ খুঁজে পাননি। খেলাফত আন্দোলনের সময় মুসলিম নেতাদের গান্ধীর নেতৃত্ব ও মর্যাদাকে নীরব সম্মতিতে মেনে নেয়াকেও তার ভালো লাগেনি। তার কাছে সবচেয়ে পীড়াদায়ক ছিল ইসলামী আত্মপরিচয়ের সীমানাকে মুসলিম নেতারা রাজনীতির কারণে শিথিল করে ফেলেছিলেন।
খেলাফত আন্দোলনের সময় গান্ধী ও হিন্দু নেতারা মসজিদে যেয়ে বক্তৃতা দিতেন এবং মুসলমান স্বেচ্ছাসেবকরা হিন্দু উৎসবগুলো সংগঠিত করতে সাহায্য করতো। অনেক মুসলমান নেতারা গান্ধীর অহিংসা ও অসহযোগ আন্দোলনের কৌশলকে রসূল (সঃ)-এর প্রাথমিক জীবনের কর্মকাণ্ডের সাথে তুলনা করেন। কেউ কেউ আবার মুসলমানদের গরু খাওয়ার নীতিকে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির স্বার্থে নিরুৎসাহিত করেছেন এই বলে যে, এটা হিন্দুরা পবিত্র মনে করে। থানভীর কাছে এটা ছিল নিছক রাজনৈতিক সুবিধাবাদিতার নমুনা। এটার ভিতর দিয়ে ইসলামী নীতি ও পরিচয়ের ব্যাপারে এক ধরনের নমনীয়তার ইংগিত পাওয়া যায়, যেন প্রয়োজন মাফিক এটা কোনো বিনিময়যোগ্য বিষয় হয়ে উঠতে পারে। ব্যাপারটা এরকম নয় যে, গরুর গোশত খাওয়া বাধ্যতামূলক বিষয়। এখানে মূল জিনিস হচ্ছে ইসলাম যা অনুমতি দিয়েছে তা নিষেধ করার কর্তৃত্ব কারো নেই। থানভী তাই মনে করেন,
….the only proper way for Muslims to act was by firmly adhering to the “limits of the sharia”, that is, in accord with the rules of conduct approved by, or set forth in, the Islamic textual tradition.
থানভীর চোখের সামনে খেলাফত আন্দোলনের বিপর্যয় ঘটে। তিনি মোপালা বিদ্রোহীদের মৃত্যুতে এবং আফগানিস্তানে যাওয়া ভারতীয় মুহাজিরদের দুর্দশায় শোকাহত হন। তার কাছে প্রতীয়মান হয় ইসলামী নীতি বহির্ভূত যেকোনো উদ্যোগই ব্যর্থ হতে বাধ্য এবং মুসলমানদের স্বার্থে হিন্দু নেতাদের সহযোগিতা আশা করা বোকামী। খেলাফত আন্দোলনের সময় যেমন হিন্দু-মুসলিম যৌগ সংগ্রামের কথাটা উঠেছিল তেমনি পরবর্তীকালে দেওবন্দের বিখ্যাত আলেম হোসাইন আহমদ মাদানীর (মৃঃ ১৯৫৭) নেতৃত্বে জমিয়তে উলামায়ে হিন্দ ব্রিটিশ বিরোধী লড়াইয়ে কংগ্রেসের মিত্র হিসেবে কাজ করে। জমিয়ত কংগ্রেসের নীতিকে সমর্থন করবে কিনা এই প্রশ্নে এটি দুভাগ হয়ে যায়। কংগ্রেস দাবি করতো ধর্মনির্বিশেষে এটা সব ভারতবাসীর দল। এই কারণে এটি মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে দাঁড়ায় যা কিনা কেবল মুসলমানদের স্বার্থের কথা বলতো। ১৯৪০ এ মুসলিম লীগ পাকিস্তান প্রস্তাব উত্থাপন করে। কংগ্রেস নেতারা এটা সাম্প্রদায়িক হিসেবে আখ্যা দেয় কেননা এটি ভারতীয় জাতিত্বের মধ্যে বিভক্তি তৈরি করছে এবং ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে সম্মিলিত সংগ্রামকে দুর্বল করে সম্রাজ্যবাদের স্বার্থ রক্ষা করছে। হোসাইন আহমদ মাদানীর মতো জাতীয়তাবাদী উলামারাও এটাই বিশ্বাস করতেন। কংগ্রেস প্রভাবিত উলামারা অস্বীকার করেননি হিন্দুদের থেকে মুসলমানরা একটি ভিন্ন ও পৃথক সম্প্রদায়। কিন্তু তারা একটি ভেদরেখা টেনেছিলেন যার একদিকে ছিল ধর্ম সম্প্রদায় (উম্মা অথবা মিল্লাত) হিসেবে মুসলমানরা, যেখানে তারা দুনিয়ার সব মুসলমানদের সাথে অন্তর্ভুক্ত । আর একদিকে ছিল জাতি (কওম) যা একটি নির্দিষ্ট ভূগৌলিক সীমানার মধ্যে পরিবৃত। এইসব উলামারা মনে করতেন ভারতীয় মুসলমানরা উম্মার অংশ, কিন্তু সেটি তাদেরকে ভারতীয় জাতি রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হতে বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি। জাতীয়তাবাদী উলামাদের এই অবস্থান, একই সাথে ঔপনিবেশিক শাসন ও মুসলিম স্বাতন্ত্র্যবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে কংগ্রেসের সাথে তাদের এক কাতারে এনে দাঁড় করিয়ে দেয়। তারপরেও এই মিত্রতার মধ্যে উলামা ও কংগ্রেস দু’পক্ষ থেকেই এক ধরনের দোদুল্যমানতা ছিল। বিভিন্ন ধর্ম সম্প্রদায়ের শরীকানায় গঠিত ভারতীয় জাতিত্বে মাদানী ও জাতীয়তাবাদী উলামারা মনে করেছিলেন এখানে মুসলমানদের জন্য তাদের পৃথক, স্বশাসিত সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় পরিসর থাকবে, যেখানে উলামারা তাদের যথাযথ দিকনির্দেশনা দিতে পারবেন। বিশেষ করে এখানে মুসলিম পারিবারিক আইনকে যথাযথ সমীহ করা হবে। কিন্তু এটাকেই উত্তর ঔপনিবেশিক ভারতে, ভারতীয় জাতিত্বে মুসলমানদের আস্থার সংকট হিসেবে দেখানো হয়েছে।
বাস্তবে কংগ্রেস নিজেকে পুরোপুরি সেকুলার দাবি করলেও কার্যতঃ এর নেতারা মোটেই সেকুলার ছিলেন না। মুসলমানের দাবি দাওয়াগুলোকেও তারা সহানুভূতির সাথে বিবেচনা করেননি। এই কারণে এক সময় মুসলমান নেতারা দলে দলে কংগ্রেস ছেড়ে দেন এবং মুসলিম লীগে যোগ দিয়ে পাকিস্তান দাবিকে শক্তিমান করে তোলেন। একজন লেখকের চোখে এই বাস্তব চিত্রটি এভাবে উঠে। এসেছে :
…the political language of the congress leaders came to be increasingly suffused with motifs and symbols drawn from the Hindu tradition. In terms of its formal position, the Congress remained strongly committed to secular politics. Yet, when leaders of the congress- and not just Gandhi- spoke of India’s past, of the Indian nation, or of the struggle against foreign rule, they did so in terms of a Hindu imagery. A Hindu idiom was especially pronounced at local levels, in small towns and villages, where it was Hindu festivals that provided occasions for political mobilization by the otherwise secular Congress. Leaders of the Congress seem not to have appreciated the profoundly alienating effects of their political language on Muslims. Gandhis assurance that Hinduism had sufficient room for Islam and Christianity within it was intended, of course, as a statement of Hindu toleration, but it is not hard to see how many Muslims would have interpreted it.
এসব সত্ত্বেও জাতীয়তাবাদী উলামারা কংগ্রেসকে সমর্থন দিয়ে যান এবং উত্তর ঔপনিবেশিক কালেও সেটাই তারা অব্যাহত রাখেন। এ ব্যাপারে তারা তাদের রাজনীতির সমর্থনে ইসলামী ঐতিহ্য থেকে যুক্তি তুলে নিয়ে আসেন। হোসাইন আহমেদ মাদানী এ ব্যাপারে রসূল (সঃ)-এর হিজরতের পর মদীনার ইহুদী ও অমুসলমানদের সাথে তার রাজনৈতিক মিত্রতা ও চুক্তির নজীর দিতেন এবং গান্ধীর প্রিয় কৌশল অহিংসা-অসহযোগকে তিনি তুলনা করতেন মদীনায় হিজরতের আগে রসূলের সাহাবীদের উপর ধৈর্য ধরে নির্যাতন সহ্য করবার পদ্ধতির সাথে। কিন্তু থানভীর কাছে মনে হয়েছে ইসলামী ঐতিহ্যের এই নজীর শুধুমাত্র কংগ্রেসের রাজনীতির যৌক্তিকতা প্রমাণের জন্য হাজির করা হয়েছে। এটা প্রমাণ করে ঐ বিশেষ মুসলিম নেতা কংগ্রেসের হিন্দুয়ানী চরিত্র বুঝতে অক্ষম অথবা ইসলামের প্রকৃত স্বার্থের ব্যাপারে এতখানি উদাসীন যে কংগ্রেসের হিন্দুয়ানী চরিত্র বুঝার পরও এই দলটির সাথে মিত্রতার সম্পর্ক তৈরি করেছে।
মুসলিম লীগ তার রাজনীতির জন্য মোটেই কৈফিয়ৎমূলক (apologetic) কিছু করেনি কিংবা তার রাজনীতির ব্যাপারে কোনো হীনমন্যতায় ভোগেনি। ভারতের মুসলমানদের স্বার্থের ব্যাপারে তারা ছিল নিরাপোষ মুসলিম লীগের নেতারা কোনো আলেম-উলামা ছিলেন না। এর প্রধান নেতারা ধার্মিকতা ও ধর্মীয় শিক্ষার জন্য খ্যাতিমান ছিলেন না আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত এসব নেতারা অনেকটা পশ্চিমের উদার বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক চিন্তাভাবনায় প্রাণিত ছিলেন। মুসলিম লীগ নেতা জিন্নাহও ছিলেন একই চিন্তার ধারক। উপর্যুপরি সুন্নী অধ্যুষিত ভারতে জিন্নাহ ছিলেন শিয়া সম্প্রদায়ভুক্ত। এরকম একটি দল ও তার নেতাকে থানভীর মতো দেওবন্দ ঘরানার উঁচু পর্যায়ের আলেম কীভাবে সমর্থন দিতে এগিয়ে এলেন। সম্ভবতঃ মুসলিম স্বার্থের চিন্তাটা থানভীকে সর্বাগ্রে আলোড়িত করেছিল। হোসাইন আহমদ মাদানীর নেতৃত্বে দেওবন্দ ঘরানার একটা অংশ কংগ্রেসকে সমর্থন দিলে আশরাফ আলী থানভীর নেতৃত্বে দেওবন্দ ঘরানার আরেকটা অংশ মুসলিম লীগকে সমর্থন দেয়। ১৯৩৯ সালে থানভীর শিষ্য জাফর আহমদ উসমানী যখন থানাভবনের সুফী খানকায় বসে হাদিসের তাফসির লিখছেন তখন জাতীয়তাবাদী উলামাদের বিপক্ষে তিনি একটা মতামত দেন। তিনি বলেন, হিন্দুদের সাথে মিলে যৌথ জাতীয়তাবাদের পরিসরে মুসলমানদের সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় আত্মপরিচয় টিকিয়ে রাখা যাবে না। কারণ তারাই হচ্ছে প্রভাবশালী ও সংখ্যাগুরুত্বের দাবিদার। আর এ ধরনের সিদ্ধান্ত শরীয়ত সম্মত নয়। মুসলমানরা কেবল অমুসলমানদের সাথে এক সাথে মুখোমুখি থাকতে পারে যেখানে ইসলাম হচ্ছে প্রভাবশালী।
উসমানীর এই চিন্তাটা আসলে থানভীর চিন্তাও বটে। উসমানী তার ফতোয়ায় গান্ধীকে তাগুত বলেছিলেন, যা থানভীও বলতেন। হিন্দুদের নিয়ে সংখ্যাগুরুত্বের আধিপত্যের যে ভয় থানভী করেছিলেন তা কিন্তু গণতন্ত্র নিয়েও তাকে কিছুটা সন্দিহান করে তোলে । তার এই সন্দেহ অমূলক ছিল না । ভারতে নির্বাচনী ব্যবস্থা প্রবর্তনের পর থেকে সংখ্যাগুরু হিন্দুরা ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করে। যৌথ জাতীয়তাবাদের সমালোচনা করে উসমানী যা বলেছিলেন তা কালে অভ্রান্ত প্রমাণিত হয়েছে । ধর্মনিরপেক্ষ বা গণতান্ত্রিক যে পদ্ধতি হোক না কেন সংখ্যাগুরু ধর্ম সম্প্রদায় শেষ পর্যন্ত ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক সংখ্যালঘুদের গিলে ফেলার চেষ্টা করে । সুতরাং এর থেকে মুসলমানদের মুক্তির পথ হচ্ছে তাদেরকে সংখ্যাগুরু হয়ে যাওয়া। ১৯৩০ এর দশকে থানভীও বলেছিলেন মুসলমানদের একটা মারকাজ (কেন্দ্র) দরকার যেখানে তাদের স্বার্থ যথাযথভাবে রক্ষিত হবে। এমনকি এই কেন্দ্রের অনুপস্থিতি সত্ত্বেও মুসলিম লীগ যখন বললো তারাই ভারতীয় মুসলমানদের যথার্থ প্রতিনিধি তখন তার কাছে প্রতীয়মান হয়েছিল মুসলিম সমাজের ভয়ংকর অনৈক্য থেকে অতিক্রম করার এটা একটা উপায়।
জিন্নাহর রাজনীতির সাথে পরোক্ষভাবে হলেও থানভীর চিন্তার একটা ঐক্যসূত্র ছিল। জিন্নাহ চিরকালই নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতির পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি কোনো প্রকার গণবিদ্রোহ ও রাজনৈতিক উত্তেজনার সমর্থক ছিলেন না। খেলাফত আন্দোলনের কৌশল নিয়ে প্রধানত মতভেদের কারণে জিন্নাহ ঐ আন্দোলন থেকে নিজেকে সরিয়ে আনেন থানভী সরে এসেছিলেন আন্দোলন শরীয়ত সম্মত হয়নি এ কারণে শাসনতান্ত্রিক কাঠামোর ভিতরে রাজনীতি আর শরীয়তের কাঠামোর মধ্যে রাজনীতির মধ্যে এক ধরনের সাদৃশ্য দেখা যায়। ১৯৪০-এর দশকে পাকিস্তান আন্দোলনের সময় উভয়ে হিন্দু অধ্যুষিত ভারতে মুসলমানদের স্বার্থটা আগে দেখেছিলেন সেই দিক থেকে তাদের রাজনৈতিক লক্ষ এক হয়ে গিয়েছিল। থানভীর রাজনৈতিক চিন্তাটা ছিল মধ্যপন্থার এবং অবশ্যই বাস্তবমুখী। তিনি কখনো বিশৃঙ্খল, এলোমেলো, উদ্দেশ্যবিহীন, পরিকল্পনার সমর্থক ছিলেন না। থানভী অত্যাচারী শাসকের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের গুরুত্ব বুঝতেন। কিন্তু এটা সামর্থ্যের আলোকে হওয়া উচিত বলে তিনি মনে করতেন। তার ভাষায় :
….one should challenge an oppressive regime only if one had the means to do so, and that the means should be regulated by sharia norms no less than the ends
এটা কোনো রাজনৈতিক নিষ্ক্রিয়তার কথা ছিল না। এটা ছিল অবস্থার বাস্তব পর্যালোচনা, যা থেকে বুঝা যায় প্রতিরোধ আন্দোলনকে কার্যতঃ কতটুকু এগিয়ে নেয়া যেতে পারে। তিনি অত্যন্ত সচেতন ছিলেন যে একটি প্রকৃত রাজনৈতিক কেন্দ্র ছাড়া এ ধরনের কর্মসূচি বাস্তবায়ন সম্ভব নয়। এই কারণে দেখা যায়, ১৯৪৩ সালে তার মৃত্যুর পরে যখন পাকিস্তান আন্দোলন তুঙ্গে উঠে তখন তার চিন্তার ওয়ারিশরা এই আন্দোলনের পক্ষে মুসলিম জনগণকে জাগিয়ে তোলার চেষ্টা করেন। এদের মধ্যে জাফর আহমদ উসমানী, মুফতী মোহাম্মদ শফী ও শাব্বির আহমদ উসমানী (মৃ: ১৯৪৯) ছিলেন অগ্রগণ্য।
চার.
আশরাফ আলী থানভী বিশ শতকের প্রথম দিকে তার সুবিখ্যাত বেহেশতি জেওর বইটি লিখেছিলেন। বইটিকে ভারতীয় ইসলামের ভিতর সূচিত সমসাময়িক সময়ের ধর্মতাত্ত্বিক সংস্কার আন্দোলনের একটি শক্তিশালী বয়ান হিসেবে ধরা হয়। ভারতীয় ইসলাম সম্পর্কে সুপণ্ডিত অধ্যাপক বারবারা ডালি মেটকাফ একটি দীর্ঘ ভূমিকা ও টীকাসহ বইটির আংশিক তরজমা করেছেন যা ১৯৯২ সালে প্রথম প্রকাশিত হয় মেটকাফ ইংরেজিতে বইটির নাম দিয়েছেন Perfecting Women: Maulana Ashraf Ali Thanawi’s Bihishti Zewar: A Partial Translation with Commentary.
বইটির নামকরণ থেকেই বুঝা যায় থানভী আসলে কি করতে চেয়েছিলেন। মেটকাফ দেওবন্দ ঘরানার ইসলাম সম্পর্কে একজন বিশেষজ্ঞ। দেওবন্দ আন্দোলনের প্রেক্ষাপট, এর রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক লক্ষ, মুসলিম সমাজে এর সংস্কার চেষ্টাসমূহ নিয়ে তিনি বিস্তর লেখালেখি করেছেন। এ সম্পর্কে তার খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি কাজ হচ্ছে Islamic Revival in British India Deobond 1860-1900. মেটকাফ দেখানোর চেষ্টা করেছেন বেহেশতী জেওর বইটি ভারতীয় মুসলিম সমাজের একটি পরিবর্তনকালীন সময়ের প্রতিধ্বনি। কলোনীর শাসকরা যখন মুসলিম প্রতিষ্ঠানগুলোর উপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে ফেললো, তখন দেওবন্দের ভাবুকরা মুসলিম পারিবারিক ও সামাজিক জীবনকে ইসলামী নৈতিকতার ভিত্তিতে সমুন্নত রাখার চেষ্টা করেছিলেন। দেওবন্দের এই সংস্কার প্রচেষ্টার একটা লক্ষ্য ছিল। মুসলিম নারীদেরকেও ইসলামের নৈতিক শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলা। তারা বুঝতে পেরেছিলেন, পারিবারিক জীবনের কেন্দ্রে যেহেতু মেয়েদের স্থান, সে কারণে তাদেরকে ইসলামী শরীয়তের শিক্ষায় আলোকিত না করতে পারলে তাদের এই সংস্কার চেষ্টা মোটেও ফলপ্রসূ হবে না। বেহেশতী জেওরকে এই প্রেক্ষাপটেই পর্যালোচনা করতে হবে। মেটকাফ লিখেছেন :
It strikingly represents significant changes in the themes and emphases in Muslim religious life in recent times. Most important, it illustrates a new concern for bringing mainstream Islamic teachings to women- a departure from the traditional view in which women typically were not expected to have more than a minimal acquaintance with these teachings. Women had not been regarded historically as the guardians of virtue and tradition , as for example, they became in Europe at this time. Rather, it was men, in the public settings of mosque, court, school, and sufi hospice, who preserved and elaborated the tradition. The text itself. therefore, is part of an important cultural transformation. It is also an excellent source for a textured, detailed presentation of the major themes of Islamic reform. Moreover, because the book is directed toward women, its examples and detail provide a rich picture of everyday domestic life and of attitudes about women.38
মেটকাফ দেখানোর চেষ্টা করেছেন বেহেশতী জেওরে নারী ও পুরুষের স্থান সমানুপাতিক। নারী ও পুরুষ মৌলিকভাবে সমান এবং ধর্মীয়, আধ্যাত্মিক ও বুদ্ধিগতভাবে নারীরা পুরুষের মতোই সমান বৈশিষ্ট্যের অধিকারী একথাটা মওলানা থানভী পরিষ্কারভাবে বলেছেন। সে কারণেই সমাজ পুনর্গঠনের জন্য ইসলামী নৈতিক শিক্ষায় তাদেরকেও সমানভাবে শিক্ষিত করে তোলা চাই। সেই সময়ের প্রেক্ষিতে নারী শিক্ষা নিয়ে থানভীর চিন্তাভাবনা রীতিমত ব্যতিক্রমী ও তীক্ষ্ণ সমাজ মনস্ক অনুভূতির পরিচায়ক। বিশেষ করে থানভীর নারী শিক্ষা বিষয়ক ভাবনা লিঙ্গ বৈষম্যের ধারণা দ্বারা প্রভাবিত নয়। থানভীর এই চেষ্টাকে বলতে হবে নবযুগের প্রেক্ষিতে ঐতিহ্যবাহী ইসলামের চোখ দিয়ে ইসলামের সংস্কার ও পুনর্মূল্যায়নের একটা উদ্যোগ। তবে যারা পশ্চিমা আধুনিকতার আলোয় নারী মুক্তির ধারণাকে লালন করেন তাদের কাছে বেহেশতী জেওরে বিধৃত নারীর অবস্থান, অস্তিত্ব, ক্ষমতায়ন ও মুক্তির ধারণা সহজে গ্রহণীয় নাও হতে পারে।
থানভীর লক্ষ্য ছিল মুসলিম সমাজকে ইসলামী শরীয়তের সীমানার মধ্যে নিয়ে আসা, যা তিনি মনে করতেন স্থানীয় প্রথা, রীতি-নীতি ও ঔপনিবেশিক শাসন পুরোপুরি দূষিত করে ফেলেছে। সেই প্রেক্ষিতেই থানভী নারীদেরকে শরীয়তের সীমানার মধ্যে বসবাসের পরামর্শ দেন এবং ইসলামের দেয়া অধিকারগুলোকে সদ্ব্যবহার করার কথা বলেন। থানভীর বেহেশতী জেওর বইটি হচ্ছে একটি দিক নির্দেশনামূলক বই। ইংরেজিতে বলা যায় এক ধরনের গাইডবুক যেখানে হানাফী মাজহাবের ঐতিহ্যবাহী ফিকাহ, মসলা-মাসায়েল ও ফতোয়ার উপর ভিত্তি করে একটি ইসলামী সমাজের ছবি আঁকা হয়েছে। থানভী কলোনীর যুগে এই বই লিখে মুসলিম সমাজে নারীদের অবস্থান ক্রীতদাসীর মতো, ইউরোপের এই নেতিবাচক প্রচারণাকে চ্যালেঞ্জ করেছিলেন। ইউরোপে ইসলামের পর্দা নিয়েও বিস্তর নেতিবাচক কথা হয়। ইউরোপীয়রা প্রচার করতো ইসলামে নারীকে বস্তু বিশেষের মতো মনে করা হয় এবং তারা আসলে তাদের গৃহে এক প্রকার বন্দী জীবন যাপন করে। শুধু তাই নয় মুসলিম সমাজে নারীর অবস্থান নাকি পুরুষের অত্যাচার ও শোষণের প্রতীক হয়ে টিকে আছে। থানভী বেহেশতী জেওরে ইসলামে নারীর প্রকৃত অবস্থান চিহ্নিত করে পশ্চিমা প্রচারণার ধরনকে প্রশ্নবিদ্ধ করেছেন। মেটকাফ লিখেছেন :
The Bihishti Zewar challenges widely held misperceptions and steriotypes of Islamic teachings about women….the Bihishti Zewar, both in what is enjoined and in what is condemned, gives evidence of important roles for women in exercising moral leadership, creating social alliances, and managing economic resources in the society it represents.
এটা সত্য বেহেশতী জেওরে ইসলামী নৈতিকতা শিক্ষার ক্ষেত্রে নারী-পুরুষে প্রভেদ করা হয়নি এবং সামাজিক কুসংস্কারগুলো কীভাবে ইসলামী নীতি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বাধা হয়ে নারীকে তার প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত করছে, তার যথাযোগ্য মর্যাদা থেকে বিচ্ছিন্ন করছে- এসব কথা প্রচুর যুক্তিনিষ্ঠতার সাথে তুলে ধরা হয়েছে। অধ্যাপক মেটকাফের ধারণা এর ফলে মুসলিম নারীদের এক ধরনের সাংস্কৃতিক ক্ষমতায়ণ হয়েছে- যা ইসলামী শরীয়তের মধ্যে নারীদের আইনগত ও অর্থনৈতিক অবস্থানকে শক্তিশালী করেছে। কিন্তু বইটি লেখা হয়েছিল কলোনীর বাস্তবতাকে সামনে রেখে। উত্তর ঔপনিবেশিক কালে মুসলিম নারীরা যখন অধিকতর সামাজিক ভূমিকায় অংশগ্রহণ করছে, আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে আধুনিক যুগ ও জীবনের চাহিদা পূরণ করছে সেই ক্ষেত্রে বেহেশতী জেওর তাদের জন্য কোনো দিকনির্দেশনা দিতে পারেনি।
দেওবন্দের আলেমরা ইসলামী ঐতিহ্যে ইজতেহাদের গুরুত্বকে অস্বীকার করেননি। মওলানা থানভী নিজেও যুগ ও জীবনের চাহিদা অনুযায়ী ইসলামী নৈতিকতার আলোকে নতুন নতুন ফিকাহ তৈরিতে নেতৃত্ব দিয়েছেন। আজকের দিনে মুসলিম নারীর পারিবারিক জীবনের মতো সামাজিক জীবনও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে সেই প্রেক্ষিতে বেহেশতী জেওরের ফিকাহগুলো পুনর্মূল্যায়ন করা চাই এবং এটা করবে থানভীর চিন্তার ওয়ারিশ হিসেবে যারা আছেন তারা। এটা না করতে পারলে বেহেশতী জেওর তার কালোপযোগিতা হারাবে।
পাঁচ.
ইসলামের ইতিহাসে শরীয়ত ও মারেফাতের পাশাপাশি পথ চলা সব সময় মসৃণ হয়নি এবং উভয়ের মধ্যে অনেক সময় একটা দ্বন্দ্ব, প্রতিযোগিতা ও টানাপোড়েনের মতো ঘটনা ঘটেছে। ইসলামী ধর্মতাত্ত্বিক ও তাসাউফের সাধকদের মধ্যে এই পরস্পর বিরোধী অবস্থান কখনো কখনো সহিংসতায় পর্যবসিত হয়েছে। দশম শতাব্দীর সুফী মনসুর হাল্লাজের (মৃ: ৯২২) আধ্যাত্মিক উচ্চারণকে ঐশ্বরিকতার সাথে সংশ্লিষ্ট মনে করায় তাকে হত্যা করা হয়েছিল। সুফীদের আধ্যাত্মিকতা ও ধার্মিকতা প্রকাশের কালচার, ধর্মতাত্ত্বিকরা মনে করেন অনেক ক্ষেত্রে অসংগতভাবে শরীয়তের সীমানা অতিক্রম করে যায়। সুফী তরিকার লোকজন মনে করেন কোনো কোনো মানুষ অনেকের চেয়ে নিজের সাধনার শক্তিতে আল্লাহর কাছাকাছি চলে যান । এরা হচ্ছেন ওয়ালিআল্লাহ- আল্লাহর বন্ধু এরা আবার অনেককে আধ্যাত্মিকতার পথে দিকনির্দেশনা দিতে পারেন। এদের কথা হচ্ছে কুরআন ও হাদিসের দৃশ্যমান (জাহেরী) ও আক্ষরিক অর্থ ও তাৎপর্যের বাইরে এক অদৃশ্য ও গুপ্ত (বাতেনী) অর্থ রয়েছে যা সাধারণ মানুষের কাছে স্পষ্ট নয়। কিন্তু এইসব আল্লাহর বন্ধুদের কাছে তা প্রকাশিত হয়। যারা তাসাউফের পথিক ও সন্ধানী তারা এইসব ব্যক্তিদের কাছে দীক্ষা নিলে কামিয়াব হতে পারবে।
সুফীদের এই চিন্তাটা অনেকের কাছেই অগ্রহণীয় বিশেষ করে ওহাবী এবং কিছু সুন্নী ইসলামবাদী এটিকে রীতিমতো শিরকের মতো অপরাধের সমতুল্য মনে করেন। কারণ তাদের মতে এই চিন্তা আল্লাহর ক্ষমতার সাথে শরীক করার মতো অপরাধ। সুফীদের ধার্মিকতা প্রকাশের সংগত ও অসংগত সীমা নিয়ে প্রচুর বিতর্ক হয়েছে। বিশেষ করে সুফীদের ধার্মিকতার পথ কীভাবে শরীয়তপন্থী ইসলামের ধর্মতাত্ত্বিকতার সাথে কোনো টানাপোড়েন ছাড়াই হাত ধরাধরি করে চলবে এ নিয়েও প্রচুর আলোচনা হয়েছে। কিন্তু মজার ব্যাপার হচ্ছে বহু প্রথিতযশা ফকীহ ও একই সাথে সুফীও ছিলেন এবং এক্ষেত্রে দেখা গেছে তাসাউফ ও শরীয়তের ভিতরকার মতানৈক্য অনেকখানি কমে এসেছে।
আশরাফ আলী থানভী ছিলেন এমন একজন সুফী যিনি একদিকে গভীরভাবে তাসাউফের চর্চা করেছেন, অন্যদিকে উঁচুমাপের ফকীহ, একই সাথে ইসলামী জ্ঞান চর্চার জগতে যিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন। থানভী মনে করতেন তাসাউফ ইসলামী মননের অংশ, কিন্তু তাকে শরীয়তের পথ ধরে হাঁটতে হবে।
কাশিম জামান লিখেছেন :
Ashraf Ali Thanawi belonged to a long line of sufis who insisted that sufism and shari’a norms were in full concord and, indeed, that it was misleading to speak of sufi ideas and practices as anything but integral to shari’a itself.
থানভী তাঁর খানকায় একদিকে কুরআন-হাদিসের তাফসির লিখেছেন, ইসলামী আইনের উপর মতামত দিয়েছেন অন্যদিকে সুফী তরিকা নিয়েও লেখালেখি করেছেন, পরামর্শ দিয়েছেন এবং মুরীদদের বায়াত গ্রহণ করেছেন। এ দুয়ের মধ্যে টানাপোড়েনে তিনি অদ্ভুত দক্ষতায় ভারসাম্য রেখেছেন । থানভী মনে করতেন তাসাউফ কুরআনের চিন্তাপ্রসূত বিষয়। তিনি তার কৃত কুরআনের তাফসির বায়ানুল কুরআনে এটা ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন থানভী তার লেখা The Reality of the Path according to (Prophet’s) Elegant Example অন্ততপক্ষে ৩৩০টি হাদিসের উল্লেখ করেছেন যেখানে তাসাউফের জোরালো স্বীকৃতি রয়েছে।
ব্যক্তিগত জীবনে তিনি পারসিক সুফী কবি জালালুদ্দীন রুমীর অনুরাগী ছিলেন। এবং আগেই বলেছি তিনি তার মসনবীর তাফসির লিখেছেন। শুধু তাই নয় তিনি ইবনুল আরাবী ও মনসুর হাল্লাজের চিন্তাভাবনাকে দৃঢ়তার সাথে সমর্থন করেছেন। যা নিয়ে বিস্তর বিতর্ক হয়েছে এবং বলেছেন এদের উদ্দেশ্যকে (মাকাসিদ) দেখতে হবে, কার্যপ্রণালীকে (তাদাবীর) নয়। অবশ্য এটাও তিনি বলেছেন, এদের সব মত গ্রহণ করতে হবে এমন নয়, তবে সুফী হিসেবে এদের যথার্থ মর্যাদা দিতে হবে। থানভী দুই ধরনের সুফীর কথা বলেছেন। এক ধরনের সুফী আছেন যারা শরীয়ার সীমার মধ্যে থাকেন এবং আরেক ধরনের সুফী আছেন যারা সুফী আধ্যাত্মিকতার এক বিশেষ পর্যায়ে শরীয়ার সীমাকে ছাড়িয়ে যান, যা আদৌ অনুসরণযোগ্য নয়।
ঔপনিবেশিক ভারতে থানভী ইসলামী আইনের একটি কাঠামোগত রূপ দিতে চেয়েছিলেন, যা মানুষ সর্বাবস্থায় অনুসরণ করার চেষ্টা করবে বলে তিনি আশা করেছিলেন। এ আইনের সংস্কার অবশ্যই করা যাবে কিন্তু সেটা অবশ্যই চূড়ান্ত কোনো পরিস্থিতির কারণে হতে হবে। থানভী এটা উপলব্ধি করতেন সুফী বয়ানে যে শিথিলতা আছে তা ইসলামী আইনের সাথে সব সময় খাপ খায় না। তারপরেও তিনি সুফী ঐতিহ্য ও শরীয়তের মধ্যে এক ধরনের সমঝোতা করার পক্ষপাতী ছিলেন দেওবন্দ ঘরানার একজন আলেম হিসেবে এই ঘরানার মধ্যে তিনি মনসুর হাল্লাজ ও ইবনুল আরাবীর মতো সুফীকে পুনর্বাসিত করার চেষ্টা করেছেন, যা তার সমন্বয়বাদী চিন্তার ফসল বলা যায়। এই কারণেই থানভীর মধ্যে একই সাথে আমরা দেখি ফকীহর দৃঢ়তা ও সুফীর উদারতা। সুফীর উদারতা দিয়ে তিনি বিচিত্র মানুষকে কাছে ডেকেছেন আর ফকীহর দৃঢ়তা দিয়ে তিনি ইসলামের ভিতরকার বিকৃতি ও জঞ্জালকে সাফসুতরো করার চেষ্টা করেছেন।
সুফী হিসেবে থানভী ছিলেন দৃঢ় চরিত্রের অধিকারী। তিনি তার কঠোর নিয়ম কানুন ও শৃঙ্খলার জন্য পরিচিত ছিলেন এবং তিনি আশা করতেন তার মুরিদরাও তাকে যথাযথভাবে অনুসরণ করবে। মৌলিকভাবে তাসাউফের চর্চাটাও একটা আত্মনিয়ন্ত্রণ ও শৃঙ্খলার বিষয়। নফসকে নিয়ন্ত্রণ করেই তাসাউফের রাস্তা ধরে হাঁটতে হয় এবং আল্লাহর নৈকট্য বা দীদার পাওয়া যায়। থানভীর হাতে যারা বায়াত নিতেন তাদেরকে ন্যূনতম কুরআন শরীফ জানতে হতো। বেহেশতী জেওরের মসলা-মাসায়েলগুলো মেনে চলতে হতো এবং থানভীর নিয়োগকৃত খলিফার তত্ত্বাবধানে থাকতে হতো। যারা আনুষ্ঠানিক বায়াত গ্রহণ করতেন না, কিন্তু তাদের আধ্যাত্মিক সমস্যার জন্য পরামর্শ চাইতেন তিনি তাদেরকে সরাসরি ও চিঠির মাধ্যমে সাহায্য করার চেষ্টা করতেন। থানভীর এই অসংখ্য চিঠি ও পরামর্শ সংগ্রহ করে The Training of the Wayfarer নামে প্রকাশিত হয়েছে সুফী সাধনচর্চায় নবীন আগন্তুকদের জন্য এ এক অপরিহার্য বই।
থানভীর খানকায় বিচিত্র ধরনের মানুষ জমায়েত হতো। অশিক্ষিত কৃষক থেকে শুরু করে আধুনিক উচ্চ শিক্ষিত পুরুষ। ইসলামের তত্ত্বজ্ঞানী আলেম থেকে নানা পেশা ও শ্রেণির মানুষ এই খানকাকে কেন্দ্র করে স্রোতের মতো আসতে থাকতো। এমনকি হিন্দুরাও এই পীরের দরগা থেকে তাবিজ গ্রহণ করতো। কোনো ধরনের মান ও মাত্রা বিচার না করে সব ধরনের মানুষের আগমনকে সুফীরা সাধারণত তাদের দরগায় স্বাগত জানান। এরকম একটা উদার বহুত্ববাদী পরিবেশ নির্মাণ করে সুফীরা ইসলামের সুমহান লক্ষ পূরণের চেষ্টা করেন। থানভীর মনেও হয়তো এরকম ইচ্ছা কাজ করেছিল ।
ছয়.
আশরাফ আলী থানভীর বহুমুখী চারিত্রক বৈশিষ্ট্য তার জন্য এক বৈচিত্র্যময় উত্তরাধিকার নির্মাণ করেছে। থানভীকে যখন আমরা সুফী হিসেবে দেখি তখন মনে হয় তার সুফী বয়ানই সবচেয়ে বেশি প্রভাবশালী। তার সুফী কথোপকথন বিচিত্র মানুষকে প্রভাবিত করেছে এবং তার ইন্তিকালের পরেও সেটি করে চলেছে। তার সুফী ভাষ্যগুলো এখনও ক্রমাগতভাবে ছাপা হয় এবং তার অসংখ্য মুরীদ তার প্রভাব ও শিক্ষাকে ছড়িয়ে দিতে সদা তৎপর। সুফী জগতে তার প্রধান ভূমিকাটার ব্যাখ্যা করে সাইয়েদ সুলাইমান নদভী লিখেছেন :
He is remembered typically for “reviving” Sufism in the sense of resuscitating its teachings after they had been supposedly buried under layers of dubious devotional practices or occluded by ill- understood theosophical doctrines. More specifically, he is celebrated as a juridical Sufi, one who is demonstrated afresh the concordance between Sufi piety and sharia norms.
প্রকৃতপক্ষে থানভী ঔপনিবেশিক ভারতে তাসাউফকে সকল বিকৃতি থেকে সংশোধন করে তার মৌলিক জায়গায় ফিরিয়ে এনেছিলেন থানভী ছিলেন কানুনী সুফী। তাসাউফকে তিনি শরীয়তসম্মতভাবে প্রবাহিত করতে চেয়েছিলেন। থানভীর হাতে তাসাউফের এই নির্মাণকে মোটাদাগে দেওবন্দের চিন্তার একটি প্রতিফলন বলা যেতে পারে। এখানেই থানভীকে আহলে হাদিস, সালাফী, ব্রেলভী ও ওহাবীদের থেকে পৃথক করে দেখতে হবে। তিনি চিন্তার দিক দিয়ে কোনো প্রান্তিক স্থান নেননি এবং বরাবর মধ্যপন্থা অনুসরণ করে গেছেন। সুফী ধার্মিকতা, শাস্ত্রীয় সীমানা ও ইসলামের মৌলক বয়ানের এক অপূর্ব সমাহার ঘটেছিল তার জীবনে।
ফকীহ হিসেবে ইতিহাসে থানভীর স্থান কি রকম হবে?
হানাফী মাজহাবের উৎস ব্যবহার করে তিনি বেহেশতী জেওরে প্রধানত ইসলামী আইনের একটি সার সংকলন করেছেন এবং খুব দক্ষতার সাথে এই আইনকে স্থানীয় পর্যায়ে ইসলামী জ্ঞানের অংশ বানিয়ে দিয়েছেন। আধুনিককালে উপমহাদেশে প্রচুর ইসলামী আইনের সংকলন বেরিয়েছে। কিন্তু থানভী ছিলেন এই কাজের পথ প্রদর্শক। বেহেশতী জেওরে তার এই ধরনের কাজের গুরুত্বকে পশ্চিমা একাডেমিয়াও স্বীকৃতি দিয়েছে :
…modern forms of objectified, essentialized, religious knowledge, purporting to describe all facets of Islam as a comprehensive system, much more than they are of any recognizable medieval genre.
থানভীর এইসব লেখালেখি ও ফতওয়াগুলো এখনো দেওবন্দ ঘরানার মাদরাসাগুলোতে চর্চা করা হয় এবং দেওবন্দ ঘরানার আলেমরা থানভীর প্রভাবকে কোনোভাবেই অতিক্রম করতে পারেননি। উল্টো উত্তর ঔপনিবেশিক কালে এসেও মুসলিম সমাজের নানা রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও রাষ্ট্রনৈতিক সংকটে থানভীর জ্ঞানতাত্ত্বিক ঐতিহ্য তাদের অশেষ প্রেরণা যোগায়। এর সবচেয়ে বড় উদাহরণ হচ্ছে ১৯৮৫ সালে ভারতের উচ্চ আদালতে দেয়া শাহবানু মামলার রায় নিয়ে ভারতের উলামাদের ঐতিহাসিক লড়াই। এ রায়ে অমুসলিম বিচারক ইসলামী আইনের মৌলিক বয়ানকে প্রশ্নবিদ্ধ করেছিলেন। এতে সেকুলার মুসলমান ও সেকুলারিজমের জামা পরা হিন্দুত্ববাদীরা সায় দিয়েছিল। থানভী এখানে খুব একটা উচ্চারিত হননি সত্য। কিন্তু তার চিন্তাভাবনার দীপ্তিতে আলোকিত হয়ে উলামারা ভারতীয় মুসলিম সমাজকে জাগিয়ে তোলেন। ফলে ভারতীয় পার্লামেন্টে প্রয়োজনীয় আইন পাশ হয়।
তবে আইনের কাজ হিসেবে দেখতে গেলে থানভীর লেখা আল-হিলা আল নাজিজা লিল হালিলাত আল আজিজা – The consummate Stratagem for the Powerless Wife হচ্ছে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য। এখানে তিনি মালেকী মাজহাবের ফকীহদের সাথে মিলে মুসলিম নারীদের তালাক নেয়ার পদ্ধতিকে সহজ করার কথা বলেছিলেন। যার উপর ভিত্তি করে ব্রিটিশ সরকার ১৯৩৯ সালে একটি আইনও পাশ করে এই ধরনের কাজকে যৌথ ইজতেহাদ বলা যায় যার প্রতিধ্বনি আমরা দেখতে পাই রশিদ রিদা (মৃঃ ১৯৩৫) ও ইকবালের (মৃ: ১৯৩৮) মধ্যে। তবে মুজতাহিদ হিসেবে থানভী ঠিক রিদা, ইকবাল কিংবা আজকালকার কারজাভী, তারিক রামাদানদের মতো গতিমান নন। বরং কিছুটা সংরক্ষণশীল। তিনি সবকিছু ধীরে সুস্থে পর্যালোচনা করে এগুনোর পক্ষপাতী ছিলেন।
মুজতাহিদ হিসেবে থানভী কিছু স্থানীয় প্রথা, যা ইসলামের নামে ভারতীয় মুসলিম সমাজে ঢুকে পড়েছিল তার সংস্কারেরও চেষ্টা করেছিলেন। তার কাছে মনে হয়েছিল স্থানীয় প্রথাগুলো শরীয়তের বিকল্প হিসেবে দাঁড়িয়েছে এবং ইসলামী নৈতিকতাকে এমনভাবে দূষিত করে ফেলেছে যে সেটিই সকলের অজান্তে অবিচারের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। থানভী মনে করতেন যা শরীয়ত ভিত্তিক নয় কিংবা শরীয়তের সীমা অতিক্রমকারী তা কখনো ইসলাম সম্মত হতে পারে না। থানভী রাজনীতি সচেতন আলেম ছিলেন। শুধু তাই নয় উপমহাদেশে মুসলমানদের জাতীয় স্বার্থে তিনি পাকিস্তান আন্দোলনকে সমর্থন করেছিলেন। কিন্তু তার মতে, ….religious norms ought never to be subordinated to political ends.
সেই দিক দিয়ে বিচার করলে থানভীকে কি ইসলামী রাজনীতির পক্ষপাতী বলা যায়? যারা আজকাল ইসলামী রাজনীতির কথা বলেন কিংবা পশ্চিমা আধুনিক রাষ্ট্রের ধারণাকে চ্যালেঞ্জ করেন তাদের ব্যাপারে থানভীর মতামত কি ছিল? তার জীবদ্দশায় উপনিবেশ বিরোধী লড়াই যে রকম প্রবল হয়েছিল, ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার লড়াইটা সেভাবে প্রবল হয়নি। সে কারণে থানভী ইসলামী রাষ্ট্র নিয়ে পরিষ্কার করে কিছু বলেননি। কিন্তু গণতন্ত্র নিয়ে তার যথেষ্ট সংশয় ছিল। ইকবালের মতোই তার কাছে মনে হয়েছিল : ….ignorant, willful masses are no match for the singleness of purpose represented by the virtuous ruler.
তবে ইসলামী রাষ্ট্রের প্রবক্তা আবুল আ’লা মওদুদী (মৃঃ ১৯৭৭) কিংবা সাইয়েদ কুতুবদের (মৃঃ ১৯৬৬) মতো এ বিষয়ে দেওবন্দের আলেমদের বয়ানটা আধুনিককালে স্পষ্ট ও কাঠামোগত রূপ নেয়নি বলেই মনে হয়। অথবা আধুনিক ইসলামবাদীদের নকশা করা ইসলামী রাষ্ট্র নিয়ে তাদের ভিতরে একটা টানাপোড়েন কাজ করে।
যাই হোক আশরাফ আলী থানভী ছিলেন দেওবন্দ ঘরানার সবচেয়ে বিদগ্ধ আলেম যার মনীষার দীপ্তিতে উপমহাদেশীয় ইসলামী বুদ্ধিবৃত্তির জগত আলোকিত হয়েছিল। এসব ভেবেই তাকে কেউ কেউ একালে আঠার শতাব্দীর ভারতীয় মুসলিম বুদ্ধিজীবী শাহ ওয়ালিউল্লাহর বুদ্ধিবৃত্তিক ওয়ারিশ হিসেবে সনাক্ত করেন ।
হদিস
১. Muhammad Qasim Zaman, Ashraf Ali Thanawi. Oxford Oneworld Publications, 2008.
২. খাজা আযীযুল হাসান, আশরাফ চরিত (অনুবাদ, গিয়াসুদ্দীন আহমদ)। ঢাকা: মাকতাবাতুল আশরাফ।
৩. Muhammad Qasim Zaman, The Ulama in Contemporary Islam: Custodians of Change. Princeton: Princeton University Press, 2002.
৪.Rethinking in Islam: Mawlana Ashraf Ali Thanawi on Way and Wayfaring.
৫.Hamdard Islamicus, 21 (1), 7-23.
৬. খাজা আযীযুল হাসান, আশরাফ চরিত।
৭. Ernst Carl W. and Bruce B. Lawrence, Sufi Martyrs of Love The Chishti Order in South Asia and Beyond. New York; Palgrave MacMillan, 2002. a. Francis Robinson, Separatism Among Indian Muslims The Politics of the
৮.United Provinces Muslims, 1860-1923. Cambridge: Cambridge University Press, 2007.\
৯. খাজা আমীমুল হাসান, আশরাফ চরিত।
১০. Mahmood Ahmad Ghazi, The Islamic Renaissance in South Asia 1707-1867 The Role of Shah Waliallah and His Successors. Delhi: Adam Publishers and Distributors, 2004, P. 251.
১১. M. Naeem Qureshi, Pan-Islamism in British Indian Politics: A Study of the Khilafat Movement, 1918-1924, Leiden: Brill, 1999.
১২. Muhammad Qasim Zaman, Ashraf Ali Thanawi
১৩. Ozcan Azmi, Pan-Islamism: Indian Muslims, the Ottomans and Britain, 1877-1924, Leiden: Brill, 1997.
১৪. Muhammad Qasim Zaman, The Ulama in Contemporay Islam.
১৫.The Text of Thanawi’s message read out at the annual meeting of the Muslim League in Patna in December 1938, in Muhammad Qasim Zaman 2008.
১৬. William Gould, Hindu Nationalism and the Language of Politics in Late Colonial India. Cambridge: Cambridge University Press, 2004,
১৭. Barbara Daly Metcalf, Perfecting Women: Maulana Ashraf Ali Thanawi’s Bihishti Zewar: A Partial Translation with Commentary.
১৮. Barkeley and Los Angeles: University of California Press, 1992.
১৯. Cited in Muhammad Qasim Zaman, Ashraf Ali Thanawi.
২০ .Eickelman Dale F. and James Piscatori, Muslim Politics.
২১. Princeton:Princeton University Press, 1996.
২২. Patricia Crone, God’s Rule: Government and Islam. New York: ColumbiaUniversity Press, 2004.