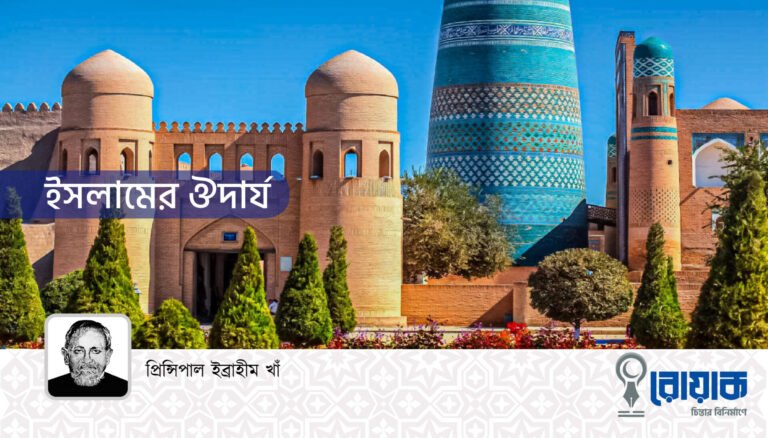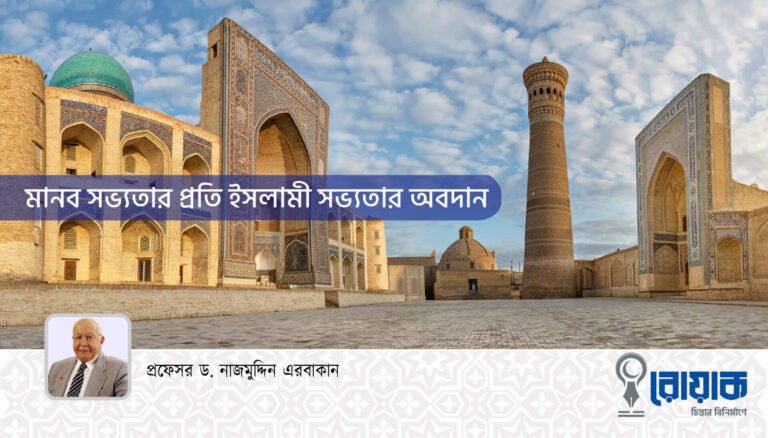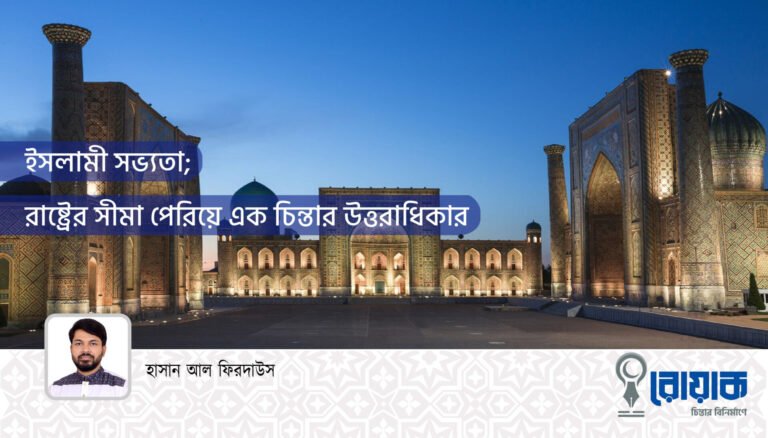পৃথিবীর অতীত ইতিহাসে নজর বুলালে সুগভীর পর্যবেক্ষণ বা তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণ ব্যতীতই স্বাভাবিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচনা করলেও এটাই প্রতীয়মান হয়ে উঠে যে, একটি সভ্যতা তার ধারক-বাহকদের দ্বারা পরিচালিত হবার পূর্বে উক্ত সভ্যতার উত্থান ও বিকাশ হয় হাতেগোনা মাত্র কয়েকজন চিন্তাশীল-দার্শনিকের হাতে।
আল্লামা ত্বহা আব্দুর রহমান তেমনি একজন সুমহান ব্যক্তিত্ব, এ-যুগের ইমাম গাজালী। যার হাত ধরে গড়ে উঠেছে আগামীর বিশ্ব দর্শন। যার ক্ষুরধার লেখনীতে পর্যদুস্ত একালের পাশ্চাত্য সভ্যতার দার্শনিক ভিত্তিসমূহ। গ্রীক থেকে শুরু করে তথাকথিত মধ্যযুগ পেরিয়ে হাল আমলের আধুনিক সব আখলাকবিহীন দর্শনগুলোকে একের পর এক খণ্ডন করে গেছেন তিনি। বিপরীতে উপস্থাপন করে গেছেন আখলাক-সম্পন্ন, আদালাত-সমৃদ্ধ ও মারহামাতপূর্ণ যুগোপযোগী সব বিশ্ব দর্শন। তৈরি করেছেন নিজস্ব এক পরিভাষার ভাণ্ডার, যা দিয়ে বর্ণনা করে গেছেন তাঁর নিজস্ব চিন্তাধারা। তিনি তাঁর চিন্তাধারায় অনন্য। তাঁর প্রতিটি কর্ম বিশ্বব্যাপী সুপ্রসিদ্ধ সব বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর গবেষণার বিষয়বস্তু।
যুগের মহান এই ব্যক্তিত্ব, তাঁর দর্শন, তাঁর চিন্তাধারা ও তাঁর কর্মসমূহ আমাদের সামনে সংক্ষেপে উপস্থাপন করেছেন এই যুগেরই অপর আরেকজন মহান ব্যক্তিত্ব, হাদীস বিশারদ ও মুজতাহিদ প্রফেসর ড. মেহমেদ গরমেজ। অসাধারণ ও সাবলীলভাবে অনুবাদান্তে আমাদের সামনে এনে হাজির করেছেন প্রখ্যাত অনুবাদক ও শিক্ষাবীদ বুরহান উদ্দীন আজাদ। আর, যুগের ইমাম গাজালীকে উম্মাহর সামনে বাংলা ভাষায় পরিচয় করে দিয়েছে জ্ঞানের পুনর্জাগরণ ও নবধারার কাগজ ত্রৈমাসিক মিহওয়ার।
আল্লামা ত্বহা আব্দুর রহমানের চিন্তাধারা ও তাঁর দর্শন নিয়ে সংক্ষিপ্তাকারে আলোচনা করাটা একেবারেই অসম্ভব। কারণ, যে দার্শনিক একইসাথে দ্বীন, রাজনীতি, আখলাক, দর্শন, ফিকহ ও মডার্নিটি নিয়ে একত্রে কাজ করে গেছেন, ত্রিশেরও অধিক গ্রন্থ রচনা করেছেন এবং প্রতিটি বিষয়েই যিনি নিজস্ব পরিভাষার অসাধারণ এক সমাহার তৈরি করেছেন, তাঁকে নিয়ে ক্ষুদ্র একটা প্রবন্ধে বিস্তর আলোচনা কখনই সম্ভব না।
🔷উম্মাহর সংকট উত্তরণে প্রণীত দর্শন
মহান এই দার্শনিকের চিন্তাধারার মূলভিত্তি প্রোথিত আছে পাঁচটি প্রশ্নের ভেতরে, যে প্রশ্নগুলো তিনি নিজেই নিজেকে করেছেন। প্রশ্ন পাঁচটি এমন,
- ১. আমরা কারা?
- ২. পাশ্চাত্য সভ্যতা কারা?
- ৩. পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রকৃতি কেমন?
- ৪. শোষণ ও সাম্রাজ্যবাদের নামে তারা আমাদের কী দিয়েছে?
- ৫. আমাদের বর্তমান অবস্থান কোথায় এসে পৌছেছে?
যেহেতু মহান এই দার্শনিক উম্মাহর স্বার্থে এবং নতুন সভ্যতা বিনির্মাণ বা ইসলামের পুনর্জাগরণের জন্য সামগ্রিক বিশ্ব দর্শন প্রণয়ন করেছেন, নতুন দুনিয়ার উসূল উপস্থাপন করেছেন, তাই মুসলিমদের সংকট উত্তরণে তাঁর প্রদত্ত দর্শন ও প্রস্তাবনাগুলোর উপর একনজর বুলিয়ে নেওয়া উচিত।
তিনি মনে করেন, পাশ্চাত্যের জুলুমের নাগপাশ থেকে মুক্তি পেতে মুসলিমরা দুই ধরনের সংগ্রাম করছে। যথা,
- ১. জুযয়ী তথা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আন্দোলন। এখানে তিনি রাজনৈতিক আন্দোলনগুলোকে অন্তর্ভূক্ত করেছেন।
- ২. কুল্লী তথা সামগ্রিক বা বড় আন্দোলন। এখানে তিনি চিন্তা ও আখলাকী আন্দোলনকে অন্তর্ভূক্ত করেছেন।
এ-দর্শনের মাধ্যমে আল্লামা ত্বহা আব্দুর রহমান চিন্তা ও আখলাক-বিহীন রাজনৈতিক আন্দোলনকে অকার্যকর বলে তুলে ধরেছেন। তাঁর ভাষ্যে,
“মুসলিম উম্মাহর সংকট উত্তরণে সমাজ পরিবর্তনের জন্য মুসলিমদেরকে রাজনৈতিকভাবেই সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে, এছাড়া অন্য কোনো পথ উন্মুক্ত নেই—এই বিষয়টি এখন সবার মাঝে এমন গভীরভাবে গেঁথে গেছে যে, এই পন্থা ব্যতিত আর কোনো পন্থাকেই মুসলিমরা সহজে মেনে নিতে চায় না। কিন্তু, রাজনৈতিক বিষয়াবলি বাদেও যে সমাজ পরিবর্তন করা যায়, এই বিষয়টা উম্মাহকে বুঝানো অত্যন্ত কষ্টসাধ্য ব্যাপার হলেও সবাইকে আখলাকী ও চিন্তাগত পন্থায় সমাজ পরিবর্তনের গুরুত্ব, তাৎপর্য ও সাংস্কৃতিক দৃষ্টিভঙ্গিটা উপলব্ধি করাতে হবে। কারণ, মৌলিক পরিবর্তনের সূচনা হয় চিন্তা ও আখলাকী পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে।”
এই বিষয়কে সামনে রেখেই তিনি তাঁর সকল গ্রন্থ-কে সাজিয়ে নিয়েছেন।
আল্লামা ত্বহা আব্দুর রহমানের এমন দর্শনের পেছনে অন্যতম যে বিষয়টি মুখ্য হিসেবে কাজ করেছে, সেটি হলো, মুসলিম উম্মাহর সংকট উত্তরণে বিগত বছরগুলোয় মুসলিমদের চালানো প্রচেষ্টাগুলোকে বিশ্লেষণ করে তিনি এগুলোকে পাঁচভাগে বিভক্ত করেছন। যথা,
- ১. প্রশাসনিক দৃষ্টিকোণ থেকে সমাধানের প্রচেষ্টা।
- ২. রাজনৈতিক আন্দোলনের মাধ্যমে সমাধানের প্রচেষ্টা।
- ৩. সেক্যুলারিজমের চিন্তাধারাকে কেন্দ্রে রেখে সমস্যা সমাধানের প্রচেষ্টা।
- ৪. পাশ্চাত্যের সৃষ্ট মডারেট চিন্তাধারায় প্রভাবিত হয়ে মডার্ন ধারার মাধ্যমে সমস্যা সমাধানের প্রচেষ্টা।
- ৫. শক্তির মাধ্যমেই শক্তির জবাব দিতে হবে, এমন ধারণা থেকে চরমপন্থা বা প্রান্তিকতার মাধ্যমে সমাধানের প্রচেষ্টা।
এসকল কারণেই তিনি মনে করেন, আমাদের এখন মৌলিক কাজ হলো, চিন্তা ও আখলাকী আন্দোলন গড়ে তোলা। তিনি শুধু এটা বলেই ক্ষান্ত হননি, বরং তিনি এর উপায়ও বাতলে দিয়ে গেছেন।
তাঁর মতে, আমরা যেহেতু আমাদের সংকট উত্তরণ করতে চাই, তাহলে আমাদেরকে প্রথমে এই সংকট নিয়েই পর্যালোচনা করতে হবে। আমরা আমাদের এই সংকটের বাহ্যিক সমস্যাকে চিহ্নিত করতে পেরেছি। কিন্তু, অভ্যন্তরীণ সমস্যাগুলো নিয়ে আমরা তেমন আলোচনা করি না। অভ্যন্তরীণ দৃষ্টিকোণ থেকে পর্যালোচনা করলে দেখি, বর্তমানে আমরা বৃহৎ দু’টি সমস্যার মধ্য দিয়ে আমাদের সময় অতিক্রম করছি। যথা,
- ১. আল আফাতুল বায়ানিয়্যাহ। অর্থাৎ, আমাদের ভাষাগত সমস্যা।
আমাদের কথ্য, লিখিত, চিন্তাগত ও দার্শনিক ভাষার মধ্যে রয়েছে বিস্তর ফারাক। প্রতিটি সেক্টরে আমরা ব্যতিক্রমধর্মী সব ভাষার ব্যবহার ও প্রচলন করে থাকি। আবার ক্ষেত্রবিশেষে একই ভাষার ব্যবহার বা প্রচলন হলেও তার মধ্যে রয়েছে ভাষার ধরনের ভিন্নতা। - ২. আল আফাতুল আমানিয়্যাহ। অর্থাৎ, আমাদের ঈমান, আকল ও চিন্তা একই রেখায় ফাংশন করতে না পারার সমস্যা।
যেহেতু আমাদের সমস্যা এখন চিহ্নিত হয়ে গেছে, অতএব এর সমাধানে আমাদের মনোনিবেশ করতে হবে। মহান এই দার্শনিক এই সমাধানকল্পে দু’টি দর্শনকে সামনে নিয়ে আসেন। যথা,
- ১. আল ফালসাফাতুদ তাদাভুলিয়্যাহ। অর্থাৎ, জ্ঞানের সাথে বিশ্বাসের সমন্বিত একটি দর্শন।
- ২. আল ফালসাফাতুল ই’তিমানিয়্যাহ। অর্থাৎ, আমান ও আমানত সম্বলিত একটি দর্শন।
এদু’টোর মধ্যে তুলনামূলকভাবে তিনি আল ফালসাফাতুল ই’তিমানিয়্যাহ নিয়ে একটু বেশি কাজ করে গেছেন। এর উল্লেখযোগ্য কারণ হলো, এটাকে তিনি শুধু একটা ফিলোসফি হিসেবেই দেখেননি, বরং ফিকহের মতো একটা বিষয়ের সাথেও এটাকে ওতপ্রতভাবে সম্পৃক্ত করেন। পাশাপাশি কালাম ও তাসাওফ—এদু’টি এবং ফিকহ; জ্ঞানের গুরুত্বপূর্ণ এই তিনটি শাখাকে তিনি নতুন করে গঠন করার ব্যাপারে গুরুত্বারোপ করেন।
ফিকহ সম্পর্কে তিনি বলেন, আমাদের ফিকহ অনেকটা আমর ও নাহীর উপর ভিত্তি করে রচিত। বর্তমানে, জ্ঞানের এই শাখায় আমান ও আমানতের বিষয়টি বেশ দুর্বল অবস্থায় রয়েছে। ইলমুল কালাম সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য হলো, মানুষ ও আল্লাহর মধ্যকার সম্পর্ককে শুধুমাত্র ইরাদা ও কুদরাতের উপর ভিত্তি করে নয়, বরং মিসাকের উপর ভিত্তি করে গড়ে তুলতে হবে। আর, তাসাওফকে তিনি উপরোক্ত দু’টি শাখার অবিচ্ছেদ্য অংশ বলে মনে করেন। কারণ, ইসতিদলাল, ইসতিমবাত ও ইসতিবসারকে একত্রে বিবেচনা করে থাকেন তিনি। অর্থাৎ, ফিকহ, কালাম ও তাসাওফ—জ্ঞানের এই তিনটি শাখাকে সদা একই রেখায় রেখে কাজ করে যেতে হবে।
অন্যান্য দর্শনসমূহ:
🔹আল মানহাজ
আল্লামা ত্বহা আব্দুর রহমান তাঁর চিন্তাধারা পাঁচটি মৌলিক বিষয়কে সামনে রেখে তুলে ধরেছেন। তন্মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ একটি হলো আল-মানহাজ, এর অর্থ পদ্ধতি বা পন্থা । তাজদীদুল মানহাজ ফি তাকবিমুত তুরাস-এই গ্রন্থের মাধ্যমে তিনি আমাদের জ্ঞানগত ও সাংস্কৃতিক মীরাস পর্যালোচনা করার জন্য নতুন একটা পন্থার প্রস্তাব দিয়েছেন। আমরা আমাদের ইতিহাস ও ঐতিহ্যকে কীভাবে বুঝবো, সেটার প্রস্তাব উত্থাপন করেছেন তিনি। তাঁর মতে, আধুনিক সময়ে এসে আমরা পাশ্চাত্যের খণ্ডিত চিন্তার প্রভাবে সকল কিছুকেই খণ্ডিতভাবে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করি। সকল কিছুকে খণ্ডিত করে দেখা একটি ভুল পন্থা। এই পন্থাটি আমাদের মাঝে ব্যাপকভাবে প্রভাব বিস্তার করেছে। যার ফলে ইসলামী চিন্তাকে সামগ্রিকভাবে অনুধাবন করার সক্ষমতাকেও আজ হারিয়ে ফেলেছি আমরা।
🔹মডার্নিটি
মডার্নিটি কিংবা আধুনিকতা নিয়ে আলোচনা করার জন্য তিনি রুহুল হাদাসা নামক একটি গ্রন্থ রচনা করেছেন। তাঁর মতে, পাশ্চাত্যের আধুনিকতা নামে একটি আধুনিকতা রয়েছে। অর্থাৎ আধুনিকতা একমাত্র কিংবা অনুপম নয়। প্রতিটি চিন্তাই তার মতো করে তাদের নিজস্ব আধুনিকতা তৈরি করতে পারে। পাশ্চাত্যে আধুনিকতা যে ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে গড়ে উঠেছে, তার কিছু মৌলিক পরিভাষা রয়েছে। যেমন- ধর্মহীন বিশ্বদর্শন (Secular World View), রেশনালিজম, হিউম্যানিজম ইত্যাদি। কিন্তু, আমরা আমাদের নিজস্ব চিন্তা ও পরিভাষার মাধ্যমেই আমাদের জন্য স্বতন্ত্র একটি আধুনিকতার বিকাশ ঘটাতে পারি। অর্থাৎ আধুনিকতার রূহকে বিবেচনায় নিয়ে আমাদের রূহকে বিনির্মাণ করতে পারলে সেই রূহের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ একটি আধুনিকতার উদ্ভব ঘটবে ।
🔹আখলাক
আল্লামা ত্বহা আব্দুর রহমানের চিন্তার মাঝে গুরুত্বপূর্ণ একটি স্থান অর্জনকারী বিষয় হলো আখলাক। বিষয়টিতে তিনি অনেক বেশি গুরুত্বারোপ করেন। বিশেষ করে দ্বীন ও আখলাকের সম্পর্কের ক্ষেত্রে সকল ধরণের বিভাজনকে প্রত্যাখ্যান করেন। দ্বীনকে আখলাক হিসেবে ও আখলাককে দ্বীন হিসেবে অভিহিত করেন। ‘Cogito, ergo sum’ (চিন্তা করি এই জন্যই আছি) চিন্তার বিপরীতে ‘আমি আখলাকসম্পন্ন, এই জন্য আমি আছি’-এই চিন্তার বিকাশ ঘটান।
আখলাকী চিন্তার ক্ষেত্রে মুসলিম আলেমদের চিন্তার সমালোচনা করে বলেন, তাঁদের চিন্তার মধ্যে অনেক ঘাটতি রয়েছে। কেননা, আখলাককে তাঁরা পূর্ণতাদানকারী একটা বিষয় হিসেবে দেখে থাকেন। কিন্তু আখলাক পূর্ণতাদানকারী কোনো বিষয় নয়। এটি অস্তিত্বের সাথে সম্পর্কিত একটি বিষয়। আখলাক ছাড়া আমাদের অস্তিত্ব অকল্পনীয়। আখলাক পূর্ণতার (কামালিয়াত) সাথে সম্পর্কিত কোনো বিষয় নয়, এটা অস্তিত্বের সাথে সম্পর্কিত একটি বিষয়। এটা দ্বীন ও মানুষ উভয়ের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। আখলাক ছাড়া দ্বীন হতে পারে না, আখলাক ছাড়া মানুষ হতে পারে না। মানুষের যে সংজ্ঞা, সেই সংজ্ঞার একাংশ জুড়ে আছে আখলাক, বাকি অংশ হলো দ্বীন। তবে উল্লেখ্য বিষয় হলো, এক্ষেত্রে দ্বীন হলো মূল বিষয়।
তাঁর মতে, রাজনীতি থেকে দ্বীনকে পৃথকীকরণ করার চেয়ে দ্বীনকে আখলাক থেকে পৃথক করা আরো বড় ধরণের হুমকি। আর এ বিষয়কে তুলে ধরার জন্য তিনি দাহরানিয়্যাহ নামক একটি পরিভাষা তৈরি করেছেন। দাহরানিয়্যাহ হলো, দ্বীনকে আখলাক থেকে পৃথক করা। আর এটাই হলো সবচেয়ে বড় বিপদজনক বিষয়।
🔹আকল
একজন মানুষের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়—আকলের উপরেও অনেক গুরুত্বারোপ করেছেন মহান এই দার্শনিক। এ বিষয়ে তিনি স্বতন্ত্র গ্রন্থও রচনা করেছেন। আকলকে তিনি আকলে মুজাররাদ, আকলে মুয়ায্যাদ ও আকলে মুসাদ্দাদ নামে তিন ভাগে বিভক্ত করেন।
তাঁর মতে, আকলে মুজাররাদ হলো বুরহানী আকল। এটি এমন আকল, যা দ্বীনি ক্ষেত্রকে উপেক্ষা করে। এই ধরণের আকল হলো বিমূর্ত (Abstract) ও যান্ত্রিক। এ ধরণের আকল বিজ্ঞানাগারে, কল কারখানায় ও একাডেমিক গবেষণার কাজে লাগতে পারে। কিন্তু, মানুষের সাথে তার রবের ও মহাবিশ্বের যে সম্পর্ক, সেই সম্পর্ক এই আকলের উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়। এ কারণে তিনি আমলের মাধ্যমে সজ্জিত আকলকে আকলে মুসাদ্দাদ নামে নামকরণ করেছেন। আর যে আকল আখলাকী মূল্যবোধের মাধ্যমে অলঙ্কৃত হয়েছে, সেই আকলকে তিনি ‘আকলে মুয়ায়্যাদ’ নামে অভিহিত করেন।
তিনি মনে করেন, আকল শুধুমাত্র একমুখী হিসেবে বিবেচনা করার অর্থ আকলকেই ছোট করা। কেননা, আকল আল্লাহ প্রদত্ত নেয়ামত। এজন্য এই নেয়ামতকে বহুমুখী হিসেবে দেখতে হবে। আকল কোনো জাওহার নয়। আকল হলো একটি কর্ম। এই কারণে তিনি তা’আক্কুলের প্রকারভেদ নিয়ে আলোচনা করেছেন।
🔹ফিতরাত
আল্লামা ত্বহা আব্দুর রহমান ফিতরাতের বিষয়টিকেও গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় হিসেবে বিবেচনা করেন। তিনি তাঁর সকল গ্রন্থেই এ বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন।
কেননা, তাঁর মতে, মানুষের পূর্বে থেকেই দ্বীন বিরাজমান ছিলো। মানুষের সৃষ্টি হয়েছে দ্বীনের পরে। শুধু তাই নয়, খুলক-ও (আলাক) খালকের (সৃষ্টির) পূর্বে সৃষ্টি হয়েছে। মানুষের সৃষ্টির পূর্বেই খুলক-এর অস্তিত্ব ছিলো। পরবর্তীতে এটা ফিতরাতরূপে মূল্যবোধের একটি ভাণ্ডার হিসেবে মানুষের ভেতরে গেঁথে দেওয়া হয়েছে। দ্বীন মানুষের মধ্যে পরবর্তীতে স্থাপিত কোনো বিষয় নয়। বরং, মানুষের সাথে একত্রে অস্তিত্বপ্রাপ্ত মৌলিক একটি হাফিজার (সংরক্ষণশালা) মধ্যে দ্বীনের অর্থের জগত লুক্কায়িত। আর এই হাফিজা বা সংরক্ষণশালার নাম হলো ফিতরাত।
দ্বীন মানুষকে সঙ্গ দানকারী একটি হাকীকত। মানুষ এ হাকীকত থেকে কখনো পৃথক হতে পারবে না। অপর দিকে পয়গাম্বরদের মাধ্যমে যে দ্বীন এসেছে, সেটা মূলত তাজকীর বা স্মারক। অর্থাৎ, মানুষের ফিতরাতের মধ্যে যা রয়েছে, সেটাই মানুষকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া। এ কারণে কোরআনকে যাক্কির (স্মারক) এবং পয়গাম্বরকে মুজাক্কির বলা হয়।
🔹পরিভাষা
পরিভাষা তৈরি করার ক্ষেত্রেও তিনি অতুলনীয়। কিছুদিন আগে এ ব্যাপারে কামুসু ত্বহা নামে প্রায় ৬০০ পৃষ্ঠার একটি বই প্রকাশিত হয়েছে। ত্বহা আব্দুর রহমানের মতে, মুসলিম উম্মাহ পরিভাষাগত একটি আক্রমণের শিকার। এক্ষেত্রে তিনি ‘আল-উদওয়ানুল মাফহুমী’ নামক পরিভাষা ব্যবহার করেন।
তিনি বলেন, পরিভাষা তৈরি করা ও পরিভাষার অধিকারী হওয়ার অর্থ হলো, সবচেয়ে বেশি শক্তিশালী হওয়া। কোনো কিছুকে শক্তি প্রয়োগ করে পরিবর্তন করার চেয়ে পরিভাষার মাধ্যমে পরিবর্তন করা বেশি স্থায়ী হয়ে থাকে। পরিভাষার মধ্য দিয়ে বড় বড় পরিবর্তন করা সম্ভব।
এ কারণেই তিনি পরিভাষার উপর এতো বেশি গুরুত্বারোপ করেছেন, শত শত পরিভাষা তিনি নিজেই তৈরি করেছেন।
🔹দর্শন
দর্শনের বিষয়ে, বিশেষ করে দু’টি ক্ষেত্রে তিনি অনেক বেশি গুরুত্ব প্রদান করেন, ক্ষেত্রের উপরে গুরুত্বপূর্ণ চিন্তাও তুলে ধরেন। তাঁর মতে, দর্শন মানে হলো প্রশ্ন করা। আর প্রশ্ন করার পন্থা দু’টি,
১. অপরপক্ষকে চুপ করানো জন্য প্রশ্ন করা। প্রশ্ন করার এই পন্থা হলো গ্রীক দার্শনিকদের পন্থা। যেমন- সক্রেটিসের প্রশ্ন করার পন্থা।
২. সমালোচনামূলক প্রশ্ন করা। ইম্যানুয়েল কান্ট এই পন্থা শুরু করেন এবং প্রভাবশালী করে তোলেন।
তবে ই’তিমানিয়্যাহ দর্শনের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র সুয়াল বা প্রশ্ন নেই। সুয়াল বা প্রশ্নের উদ্দেশ্য শুধুমাত্র সুয়ালিয়্যাত (প্রশ্ন করা) নয়, এখানে উদ্দেশ্য হলো মাসউলিয়্যাত (দায়িত্ববোধ)। সুয়াল-মাসয়ালা ও মাসউলিয়্যাতের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করে তিনি এই বিষয়কে তুলে ধরেন। তিনি মনে করেন, প্রশ্ন যখন দায়িত্ববোধের চেতনা জাগ্রত করবে, কেবল তখনই সেটা সত্যিকারের প্রশ্ন হিসেবে গণ্য হবে। ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে এ ধরণের প্রশ্নই আমাদের সত্যিকারের দর্শন। এ ক্ষেত্রে তিনি ‘আস-সুয়াল মাসউল’ পরিভাষা নিয়ে আলোচনা করেন।
🔹চিন্তাগ্রহণ
চিন্তার আদান প্রদান নিয়ে তিনি বেশ ভালোভাবেই পর্যালোচনা করেছেন। তাঁর মতে, অন্যের চিন্তা অনুবাদ করে কোনোদিন সত্যিকারের চিন্তা তৈরি করা যায় না। পাশ্চাত্যের দর্শন বিষয়ক যেসব বই অনুবাদ করে আজ সমগ্র বিশ্বে পড়ানো হচ্ছে, সেটার সম্পর্কে মূল্যায়ন করতে গিয়ে তিনি বলেন,
لن تكون الفلسفة رافعة إلا اذا كانت مبدعة
অর্থ : “দর্শন কোনো জাতিকে উচ্চমর্যাদায় আসীন করতে পারে না, যদি না সেটা নিজেদের মূল্যবোধের উপরে প্রতিষ্ঠিত হয়। “
অর্থাৎ, তাকলীদের মাধ্যমে চর্চিত দর্শন কোনোদিন কোনো জাতিকে উচ্চ মর্যাদায় আসীন করতে পারে না। যদি কোনো জাতি চিন্তার মাধ্যমে উচ্চ মর্যাদায় আসীন হতে চায়, তাহলে তাকে নিজ মূল্যবোধের সাথে সম্পর্ক রেখে চিন্তা ও দর্শন তৈরি করতে হবে।
তবে, অন্যের চিন্তা কতটুকু গ্রহণ করা হবে, এ-বিষয়ে আলোকপাত করতে গিয়ে তিনি ‘তাকরীরে তা’বী’ নামে একটি পন্থার কথা উল্লেখ করেছেন। অর্থাৎ এর অর্থ এটা নয় যে, আমরা কারোর কাছ থেকে কোনো কিছুই নেবো না। তবে, অন্যদের কোনো চিন্তা ও দর্শন অনুবাদ করার ক্ষেত্রে আমাদের তাদাভুলিয়্যার দিকে খেয়াল রাখতে হবে। আমরা যে-সকল চিন্তা অনুবাদ করবো, সেই চিন্তার ভাষাগত ও ধর্মীয় ভিত্তিকে ভালোভাবে বুঝতে হবে। কেননা আমাদের ভাষা ও ধর্ম উভয়টিই ভিন্ন। যেমন- তিনি হেগেল ও নিটশে-কে পর্যালোচনা করতে গিয়ে বলেন, এরা অনেক ধর্মতত্ত্বীয় পরিভাষাকে দার্শনিক চিন্তায় রূপান্তরিত করেছে।
এ কারণে অনুবাদের সময় আমাদেরকে তিনটি বিষয়ের দিকে খেয়াল রাখতে হবে। সেগুলো হলো তাহসিলিয়্যাহ, তাওসিলিয়্যান ও তা’সিলিয়্যাহ। তাহসিলিয়্যাহ হলো হুবহু অনুবাদ করা। তাওসিলিয়্যাহ হলো, সতর্কতার সাথে বেছে বেছে অনুবাদ করা। তা’সিলিয়্যাহ হলো, শুধুমাত্র আমার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ বিষয়সমূহকে অনুবাদ করা। আমাকে সেই বিষয়সমূহই অনুবাদ করতে হবে, যেগুলো আমাদের দ্বীন ও ভাষার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ।
🔹দর্শন উদ্ভাবন
মুসলমানদের দর্শন তৈরি করার অধিকার নিয়ে তাঁর এই উক্তিটির উল্লেখ প্রণিধানযোগ্য-
”উম্মতসমূহের ভিন্নতা প্রাকৃতিক একটি বিষয়। যারা নিজের উপর কর্তৃত্ব হারিয়েছে, তাঁরা ছাড়া অন্য কেউই এই অমোঘ বিধানকে অস্বীকার করতে পারে না। এই কারণে, যে জাতি পরাজিত ও পরাভূত হয়েছে, তাঁদেরও পুনরায় নিজ-পায়ে দাঁড়ানোর অধিকার রয়েছে। তাঁদেরও অধিকার আছে তাঁদের নিজেদের দর্শনকে তৈরি করার।”
তাঁর মতে, যে সভ্যতা তাঁর যুগ-জিজ্ঞাসার জবাব নিজের মূল্যবোধের মাধ্যমে দিতে সক্ষম নয়, সেই সভ্যতার পক্ষে নিজের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখা অসম্ভব। যে সভ্যতা যুগ-জিজ্ঞাসার জবাব অন্য সভ্যতা কর্তৃক সৃষ্ট মূল্যবোধ ও জবাবের মাধ্যমে দেওয়ার চেষ্টা করে, সেই সভ্যতা আরও বেশি অধঃপতনের শিকার হয়।
তিনি বলেন, আমাদের সবচেয়ে বড় দুর্বলতা হলো, যুগের জবাবদানের ক্ষেত্রে অন্যদের তৈরি করা জবাবের মাধ্যমে জবাব দেওয়া। আর এই বিষয়টিই আমাদের পথকে রোধ করে দিয়েছে।
আমরা মুসলিম হিসেবে যুগ-জিজ্ঞাসার জবাব কীভাবে দিবো এবং আমাদেরকে কীভাবে কাজ করতে হবে, এ বিষয়ে তিনি যুক্তিপূর্ণ ভাষায় তাঁর অভিমত তুলে ধরেছেন।
🔷গ্রন্থপঞ্জির দর্শন
আল্লামা ত্বহা আব্দুর রহমানের গ্রন্থগুলোকে দু’টি ভাগে বিভক্ত করা যায়। যথা,
- ১. উসূল ও মেথডোলজি
- ২. উসূলের প্রয়োগপদ্ধতি
উসূল ও মেথডোলজি সংক্রান্ত গ্রন্থগুলোকে আবার দুইভাগে ভাগ করা যায়। যথা,
- ১. ফালসাফাতুদ তাদাভুলিয়্যাহ।
- ২. ফালসাফাতুল ই’তিমানিয়্যাহ।
পরিশেষে জ্ঞান ও আকলের পুনর্জাগরণ সম্পর্কে তাঁর মন্তব্য তুলে ধরতে হয়। তিনি বলেন,
“এমন কোনো জ্ঞান ও আমল নেই, যা দ্বীনের সাথে সম্পর্কিত জ্ঞান ও আমলের চেয়ে উত্তম হতে পারে। দ্বীনি কার্যক্রমের দৃষ্টিকোণ থেকে সবচেয়ে বড় হুমকি হলো চিন্তাকে স্থবির করে ফেলা।”
অর্থাৎ, যারা জ্ঞান ও আকলের পুনর্জাগরণের জন্য কাজ করবে, তাঁদেরকে সবসময় জ্ঞানগত ও আমলগত দিক থেকে গতিশীল থাকতে হবে। কোনো আন্দোলন যখন তাঁর চিন্তাগত গতিশীলতাকে হারিয়ে ফেলে, তখনই তা কালের অতল গহ্বরে হারিয়ে যায়।