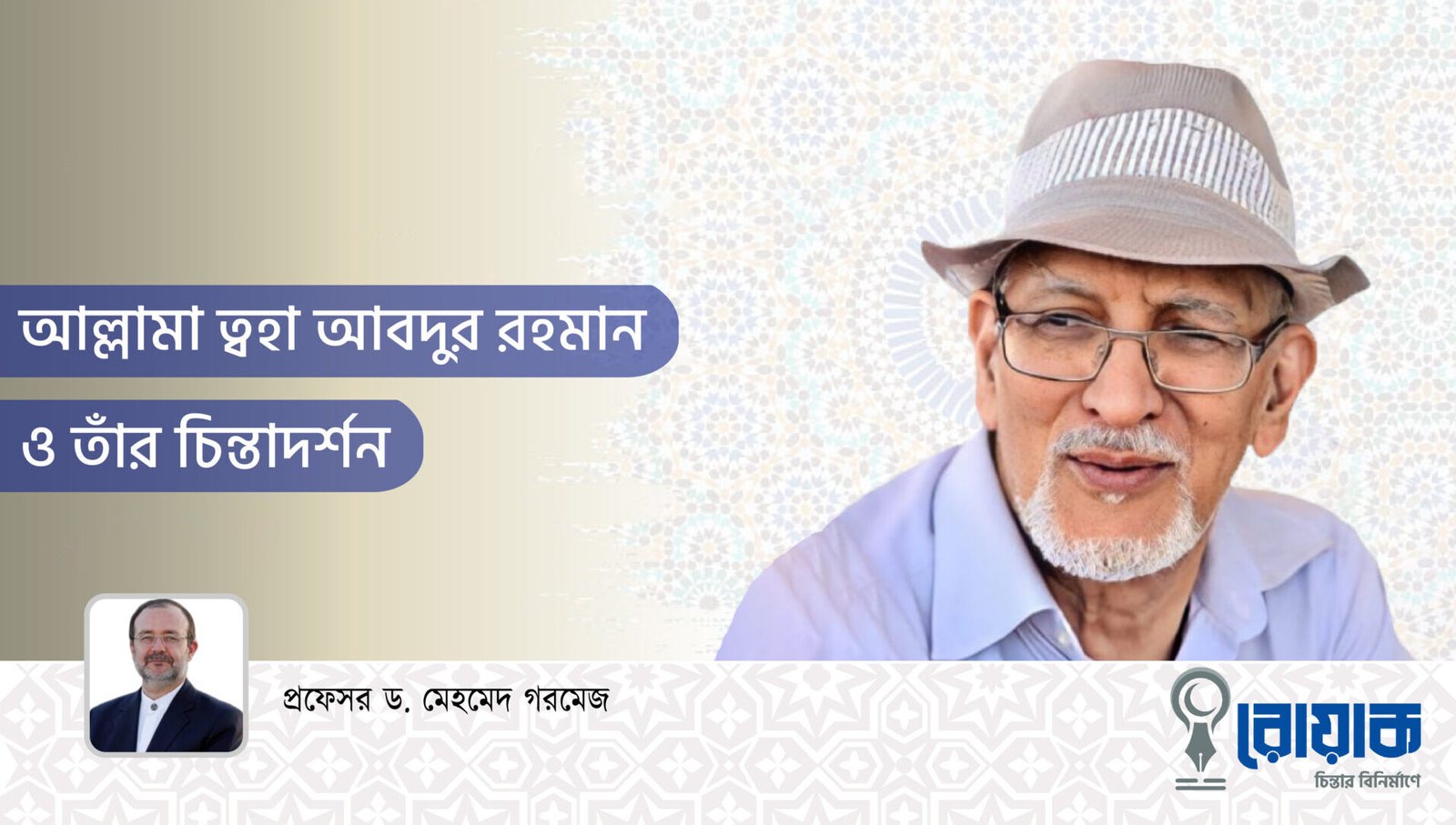আল্লামা ত্বহা আব্দুর রহমান বহুমাত্রিক একজন আলেম ও চিন্তাবিদ। তাঁর মতো চিন্তাবিদের চিন্তাধারা একটি প্রবন্ধের মধ্যে তুলে ধরা নিঃসন্দেহে কঠিন কাজ। বিগত পঞ্চাশ বছরের চিন্তাগত জীবনে তিনি দ্বীন, রাজনীতি, আখলাক, দর্শন, ফিকহ ও মডার্নিটির মতো বিভিন্ন বিষয়ে ত্রিশের অধিক গ্রন্থ রচনা করেছেন। এই সকল গ্রন্থে স্বতন্ত্র একটি ভাষার মাধ্যমে তিনি শত শত পরিভাষা তৈরি করেছেন।
ত্বহা আব্দুর রহমান বিভিন্ন সময়ে আমাদের সামনে তাঁর জীবনের বিভিন্ন দিক তুলে ধরেছেন। ১৯৬৭ সালে আরব-ইসরাইল যুদ্ধের সময়ে তাঁর বয়স ২৩-২৪ বছর। সে সময়ের একজন যুবক হিসেবে তাঁর মানসপট কীভাবে পরিবর্তন হয়েছিল সেটা তিনি আমাদেরকে অবহিত করেছেন। এ সময়ে তিনি সাহিত্য ও কবিতা নিয়ে ব্যস্ত থাকলেও আরব-ইসরাইল যুদ্ধের প্রাক্কালে নিজেকে নিম্নোক্ত প্রশ্নগুলো করেন-
- ১. ما كنه العقل الذي هزم العقل المسلم অর্থাৎ, দৃশ্যমানভাবে হলেও মুসলমানদের আকলকে বিপর্যস্ত করে এমন আকলের প্রকৃতি কী?
- এখানে তিনি পাশ্চাত্যের আকলের প্রকৃতির দিকে ইঙ্গিত করেছেন।
- ২. ماذا صنع الاستعمار بنا অর্থাৎ, শোষণ ও সাম্রাজ্যবাদের সময়কাল আমাদের জন্য কী বইয়ে এনেছে?
- আপনারা জানেন মরক্কো, আলজেরিয়া ও তিউনিসিয়া ফ্রান্সের শোষণাধীন ছিল। ত্বহা আব্দুর রহমান যখন ছোট ছিলেন তখনও মরক্কো-সহ ঐ অঞ্চলে ফ্রান্সের শোষণ ও শাসন অব্যাহত ছিল।
- ৩. من نحن بعد الإستعمار অর্থাৎ শোষণ ও সাম্রাজ্যবাদের পর আমরা কোন অবস্থায় এসে উপনীত হলাম?
তিনি বলেন, এই তিনটি প্রশ্ন আমি নিজেকে করি এবং এর সাথে আরও দু’টি প্রশ্নকে যুক্ত করি।
- ক. من نحن অর্থাৎ, আমরা কারা?
- খ. من هذا الاخر অর্থাৎ, অন্যরা কারা?
তাঁর ভাষ্যমতে, এই পাঁচটি প্রশ্নকে সামনে রেখে তিনি তাঁর চিন্তাজগতকে নতুন করে বিশ্লেষণ করা শুরু করেন। আমরা তাঁর সকল গ্রন্থ সামগ্রিকভাবে পর্যালোচনা করলে দেখতে পাই যে, তিনি কোনো গ্রন্থই পরিকল্পনাহীনভাবে রচনা করেননি।
তিনি তাঁর মানসপটে অঙ্কিত প্রজেক্টকে (কর্ম-পরিকল্পনা) শক্তিশালী চিন্তা ও লেখনীর মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন। বিশেষ করে শোষণ ও পাশ্চাত্যায়ন (Westernization)-কে العباد البنيوية (কাঠামোগত একটি গণহত্যা) হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। কেননা শোষণ, পাশ্চাত্যায়ন মুসলিম উম্মাহর সকল প্রতিষ্ঠান ও চিন্তাকে ধ্বংস করে দেয়। এই অবস্থা থেকে মুসলিম উম্মাহ কীভাবে উদ্ধার হতে পারে এই বিষয় নিয়ে তিনি দীর্ঘ দিন যাবৎ অনুসন্ধান চালিয়ে যাচ্ছেন।
এখন প্রশ্ন হলো, ত্বহা আব্দুর রহমানের চিন্তা ও প্রজেক্টসমূহকে (কর্ম-পরিকল্পনা) বিশেষ করে আধুনিক সময়ে এসে মুসলিম উম্মাহর সৃষ্ট আন্দোলনসমূহের মধ্যে কোথায় স্থান দেবো? ক্ল্যাসিক ইসলামী চিন্তার মধ্যে তাঁর স্থান কোথায়?
শুরুতেই আমরা প্রথম প্রশ্নের উত্তর নিয়ে আলোচনা করবো। তাঁর মতে, শোষণ ও পাশ্চাত্যায়নের বিরুদ্ধে মুসলিম উম্মাহর দু’ধরণের সংগ্রাম অব্যাহত রয়েছে। এর মধ্যে একটি ছোট বা (জুযয়ি) আর অপরটি সামগ্রিক/বড় (কুল্লি)। ছোট (জুযয়ি) আন্দোলনগুলো হলো রাজনৈতিক আন্দোলন। মুসলিম উম্মাহর মধ্যে যতগুলো রাজনৈতিক আন্দোলন আত্মপ্রকাশ করেছে সবগুলোই হলো ছোট বা জুযয়ি আন্দোলন। আর বড় বড় আন্দোলনসমূহ হলো চিন্তা ও আখলাকী আন্দোলন। এ ক্ষেত্রে তাঁর এই বাণীটি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ :
يكاد يكون مستحيلاً اقتناعنا بوجود أداة تغيير غير سياسة في الواقع المعاصر
অর্থাৎ : আধুনিক দুনিয়াতে সমাজ পরিবর্তনের জন্য রাজনীতি ছাড়াও যে অন্য পন্থা রয়েছে এই বিষয়টির ব্যপারে কনভিন্স করা এক প্রকারের অসম্ভব বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে।
অর্থাৎ, যদি কোনো পরিবর্তন আনতে হয় তাহলে রাজনৈতিকভাবেই আনতে হবে, এছাড়া অন্য কোনো পথ নেই। এ বিষয়টি এমনভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে, যেন এর বাহিরে অন্য কোনো পন্থাতেই সমাজ পরিবর্তন করা যেতে পারে না।
ولكن ما من سبيل الا ان نقلب هذا المستحيل
কিন্তু এই অসম্ভবকে সম্ভব করা ছাড়া আমাদের সামনে অন্য কোনো পথ খোলা নেই।
অর্থাৎ রাজনীতি ছাড়াও যে সমাজ পরিবর্তন করা যায় এই বিষয়টি আমাদেরকে মানুষের সামনে তুলে ধরতে হবে এবং তাঁদেরকে এই ব্যপারে কনভিন্স করতে হবে। বিষয়টি অনেক কঠিন হলেও এই কাজে আমাদেরকে সফল হতে হবে।
ত্বহা আব্দুর রহমান বলতে চেয়েছেন, মৌলিক পরিবর্তন চিন্তা ও আখলাকী পরিবর্তনের মধ্য দিয়েই শুরু হয়। বিষয়টিতে তিনি ব্যাপক জোর দেন এবং তাঁর সবগুলো গ্রন্থ এই চিন্তার আলোকে সুসজ্জিত করেন।
এই দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে মুসলিম উম্মাহ শোষণ ও সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে যে সকল তাজদীদ ও ইহইয়া আন্দোলন শুরু করেছিল সেগুলোকে আমরা পাঁচভাবে বিভক্ত করতে পারি :
- ১. সমস্যাকে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে প্রশাসনিক সমস্যা হিসেবে বিবেচনাকারী এবং নতুন করে ইসলামী ঐক্য প্রতিষ্ঠার জন্য প্রচেষ্টাকারী আন্দোলনসমূহ।
- ২. মুসলিম উম্মাহকে রক্ষা করতে হলে ধর্মনিরপেক্ষতাকে (সেকুলারিজম) ধারণ করে সেটার আলোকে চলতে হবে এমন আন্দোলনসমূহ।
- ৩. রাজনৈতিক দলের মাধ্যমে আত্মপ্রকাশকারী ইসলামপন্থী দলসমূহ। তাঁদের স্লোগান হলো, الاسلام هو الحل অর্থাৎ ইসলামই হলো একমাত্র সমাধান।
- ৪. পাশ্চাত্যে সৃষ্ট চিন্তাধারা ইসলামী চিন্তার মধ্যে প্রয়োগকারী মডার্ন ধারাসমূহ। তাঁদেরকে তিনি “তাজদীদুল মানহাজ ফি তাকবিমুত তুরাস” নামক গ্রন্থের মাধ্যমে জবাব দিয়েছেন।
- ৫. শক্তিকে শক্তির মাধ্যমে জবাব দিতে হবে। এই গ্রুপের দ্বারা তিনি বিভিন্ন চরমপন্থী গ্রুপকে বুঝিয়েছেন এবং তাঁদেরকে নিয়ে سؤال العنف নামক একটি স্বতন্ত্র গ্রন্থও রচনা করেছেন।
আচ্ছা! তাহলে এখন মূল কাজ কী? আমাদেরকে কী করতে হবে? এখানে মৌলিক কাজ হলো চিন্তাগত ও আখলাকী একটি চিন্তা গড়ে তোলা। এটা কীভাবে শুরু করতে হবে?
এক্ষেত্রে তিনি বলেন, আমাদেরকে দুটি আপদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে হবে। তাঁর মতে, সমগ্র মুসলিম উম্মাহকে পরিগ্রহকারী দুটি আপদ রয়েছে। প্রথমটি ‘আল-আফাতুল বায়ানিয়্যাহ’, দ্বিতীয়টি ‘আল-আফাতুল ইমানিয়্যাহ’।
প্রথম আপদ তথা আল-আফাতুল বায়ানিয়্যায় শুরুতে যে বিষয়টি আসে তা হলো আমাদের ভাষাগত সমস্যা। অর্থাৎ, আমরা সমগ্র উম্মাহ যে ভাষায় কথা বলি সে ভাষায় চিন্তা করি না। আমরা যে ভাষায় কথা বলি সেই ভাষায় দর্শন তৈরি করি না। কিংবা আমাদের চিন্তায় আমরা কথা বলি না। আমরা যে দার্শনিক চিন্তার অধিকারী সেই চিন্তাকে তুলে ধরি না। এ কারণে তিনি এটাকে ‘আল-আফাতুল বায়ানিয়্যাহ’ বলেন।
আমরা দেখি, ত্বহা আব্দুর রহমান তাঁর জীবনে শুরুর দিকের বড় একটি অংশ ভাষা, মানতিক ও দর্শন শিক্ষায় ব্যয় করেন। ভাষা ও মানতিক নিয়ে তাঁর গবেষণাসমূহ আমাদের দেখিয়ে দেয় যে, স্বতন্ত্র একটি ইসলামী দর্শনের জন্য এ দুটি বিষয়ের বিকল্প নেই।
তাঁর মতে, সর্বশেষ ইলাহী দ্বীন ইসলামকে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সমগ্র মানবতার মুক্তির জন্য প্রেরণ করেছেন। আর এই দ্বীনের মূল গ্রন্থকে তিনি একটি ভাষার মাধ্যমে সমগ্র মানবতার নিকট পৌঁছে দিয়েছেন। যদি এই ভাষার মাধ্যমে চিন্তা ও দর্শনকে তৈরি করা না যায় তাহলে আর কোন ভাষায় করা সম্ভবপর হবে? এই কারণে তিনি এ বিষয়ে ব্যাপক জোর দেন এবং এ সমস্যাকে সমাধানের জন্য প্রচেষ্টা চালান।
তাঁর মতে, কোনো চিন্তা ‘ফিলোসফি’ নামে স্বীকৃতি পাওয়ার জন্য প্রাচীন গ্রীসে কিংবা পাশ্চাত্যে তৈরি হওয়া শর্ত নয়। সকল জায়গার সকল সংস্কৃতির মানুষই দর্শন ও চিন্তা তৈরি করতে পারে। শুধু তাই নয়, চাইলে তারা বিশ্বজনীন ফিলোসফিও সৃষ্টি করতে পারে। এক্ষেত্রে সবচেয়ে অগ্রসর ভাষা হলো আরবী। এ ভাষার মাধ্যমে এমন বড় বড় বিশ্বজনীন চিন্তা তৈরি করা যেতে পারে। আর এ কাজ সবচেয়ে ভালো ও উত্তমভাবে করতে পারে মুসলিম উম্মাহ। এ বিষয়ে তিনি অনেক বেশি জোর দেন।
দ্বিতীয় আপদ হলো, ‘আল-আফাতুল ঈমানিয়্যাহ’। এর মাধ্যমে তিনি কী বুঝাতে চাচ্ছেন? তাঁর উদ্দেশ্য হলো, আমরা আমাদের চিন্তা-ভাবনাকে এখনো জীবনের সাথে মিলিয়ে নেওয়ার ক্ষেত্রে অনেক সমস্যার সম্মুখীন হয়ে থাকি। অর্থাৎ আমাদের ঈমান চিন্তা তৈরি করতে পারছে না। কেননা ঈমান একইসাথে চিন্তাকারী একটি আকল। কিন্তু আমরা ঈমানের মাধ্যমে চিন্তা করি না। একারণে তিনি দ্বিতীয় বড় আপদকে ‘আল-আফাতুল ঈমানিয়্যাহ’ নামে নামকরণ করেন।
এ বিষয়ে তিনি সমাধান হিসেবে কী পেশ করেন?
এই দুটি বিষয়কে অতিক্রম করার জন্য সমাধান হিসেবে তিনি দুটি ফিলোসফি (দর্শন) সম্পর্কে আলোকপাত করেন। প্রথমটি ‘আল-ফালসাফাতুদ তাদাভুলিয়্যাহ’। দ্বিতীয়টি ‘আল-ফালসাফাতুল ই’তিমানিয়্যাহ’।
ত্বহা আব্দুর রহমানকে বুঝতে চাইলে এই পরিভাষাসমূহকে এভাবেই ব্যবহার করতে হবে। এসকল পরিভাষা অনুবাদ করে বুঝা সম্ভব নয়। তাদাভুলিয়্যা’র দ্বারা উদ্দেশ্য, জ্ঞান ও বিশ্বাসকে একত্রিত করে দর্শন তৈরি করা। আমাদের মুসলমানদের জন্য স্বতন্ত্র একটি ফিলোসফির প্রয়োজন যেটাকে তিনি এই নামে অভিহিত করেন। এ বিষয়গুলো তিনি তাঁর গ্রন্থসমূহে অসাধারণভাবে তুলে ধরেন। এই দর্শনের কেন্দ্রে রাখেন ভাষাকে।
অপরদিকে ‘আল-ফালসাফাতুল ই’তিমানিয়্যাহ’ পরিভাষাটি তিনি আমান ও আমানত নামক পরিভাষাদ্বয়কে একত্রিত করে তৈরি করেন। এক্ষেত্রে তিনি ঈমান (বিশ্বাস)-কে কেন্দ্রে স্থাপন করেন এবং এটাকে তিনি মিসাকের উপর ভিত্তি করে গড়ে তুলেন।
ত্বহা আব্দুর রহমানকে বুঝার জন্য এই পরিভাষা দু’টি (তাদাভুলিয়্যাহ, ই’তিমানিয়্যাহ) অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষ করে ভাষাতত্ত্ব, মানতিক ও দর্শনে পারদর্শী বিশেষজ্ঞদের এই বিষয়ে আলোচনা করা উচিত।
তবে আমাকে যে বিষয়টি বেশি আগ্রহী করে সেটা হলো, তাঁর আল-ফালসাফাতুল ই’তিমানিয়্যাহ। আমি এ বিষয় নিয়ে একটু আলোচনা করার চেষ্টা করবো। কেননা বিষয়টি তিনি শুধুমাত্র একটি ফিলোসফি হিসেবে বিবেচনা করেননি। যেমন, ফিকহকেও তিনি এই পরিভাষার উপর ভিত্তি করে দাঁড় করাতে চান। এজন্য তিনি ফিকহুল ইতিমানিয়্যাহ নিয়েও কাজ করেছেন। বিশেষ করে জ্ঞানের তিনটি শাখা তিনি নতুন করে গঠন করার ব্যপারে গুরুত্বারোপ করেন। সেগুলো হলো, ফিকহ, কালাম ও তাসাউফ।
তাঁর মতে, আমাদের ফিকহ অনেকাংশে আদেশ ও নিষেধের উপর ভিত্তি করে গঠিত। একারণে তিনি আমাদের ক্ল্যাসিক ফিকহের নাম দিয়েছেন ‘ফিকহুল ই’তিমান’। এই ফিকহে ই’তিমান তথা আমান ও আমানতের বিষয়টি দুর্বল অবস্থায় রয়ে গেছে। একারণে তিনি তাঁর দ্বীনুল হায়া নামক গ্রন্থের প্রথম খন্ডে ফিকহুল ই’তিমানের উসূলকে তুলে ধরেছেন।
ইলমুল কালামের ক্ষেত্রে তাঁর প্রস্তাবনা হলো, মানুষ ও আল্লাহর মধ্যকার সম্পর্ককে শুধুমাত্র ইরাদা ও কুদরাতের উপর ভিত্তি করে নয়; বরং মিসাকের উপর ভিত্তি করে গড়ে তুলতে হবে। তাজদীদু ইলমুল কালাম নামক গ্রন্থে তিনি এই বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন এবং মানুষ ও আল্লাহর মধ্যকার সম্পর্ককে ই’তিমানী দর্শন সামনে রেখে নতুন করে তৈরি করার প্রস্তাবনা পেশ করেছেন।
অপরদিকে তাসাউফকে তিনি এই দুই জ্ঞানের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে বিবেচনা করে থাকেন। তাঁর মতে, ইসতিদলাল, ইসতিমবাত এবং ইসতিবসারকে একত্রে বিবেচনা করতে হবে। অর্থাৎ, ফিকহ, কালাম ও তাসাউফকে একত্রে বিবেচনা করতে হবে। তবে এখানে তিনি তাসাউফ বলতে বর্তমান সময়ের জ্ঞানহীন তাসাউফের কথা উল্লেখ করেননি। তাসাউফকে তিনি জ্ঞানের একটি শাখা হিসেবে নতুন করে বিন্যস্ত করার চেষ্টা করেছেন। তিনি নিজেও একজন তাসাউফপন্থী আলেম ও একটি তরিকতের সদস্য। তবে তাসাউফকে জ্ঞান হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার জন্য তিনি অনেক বেশি প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন।
এসকল দৃষ্টিকোণ সামনে রেখে আমরা ত্বহা আব্দুর রহমানের গ্রন্থগুলোকে দুটি ভাগে ভাগ করতে চাই। তাঁর রচিত গ্রন্থসমূহের অর্ধেক উসূল ও মেথডোলজি নিয়ে আর বাকি অর্ধেক এই সকল উসূলের প্রয়োগ নিয়ে। অর্থাৎ, তিনি তাঁর রচিত উসূলকে তাঁর নিজের গ্রন্থসমূহেই প্রয়োগ করেছেন। যেমন, ডিজিটালাইজেশনের মাধ্যমে ব্যাপকভাবে প্রসার লাভকারী গায়রে আখলাকী বিষয়টিকে তিনি বিশ্লেষণ করার সময় তাঁর ই’তিমানিয়্যাহ দর্শনকে সামনে রাখেন এবং এর আলোকে সমাধান পেশ করার চেষ্টা করেন। কিংবা আকলের বিষয়টিকে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করার সময় তাদাভুলিয়্যাহ দর্শনকে সামনে রাখেন এবং এর আলোকে উত্তোরণের পথ বাতলে দেওয়ার চেষ্টা করেন।
সুবরু মুরাবিতা নামে তাঁর একটি গ্রন্থ রয়েছে। এখানে তিনি সৌদি আরব ও ইরান নিয়ে তুলনামূলক আলোচনা করেন। মূলত রুহুদ্বীন (দ্বীনের রূহ) নামক গ্রন্থকে এই দুই দেশের প্রশাসনিক ব্যবস্থা সামনে রেখে রচনা করেন এবং এই বইয়ে তিনি দ্বীন ও রাজনীতির মধ্যকার সম্পর্ক নিয়ে সমাধানমূলক তত্ত্ব তুলে ধরেন। একইভাবে আমরা যখন তাঁর সুয়ালুল উনফ নামক গ্রন্থটি পাঠ করি তখন দেখতে পাই, মুসলিম উম্মাহকে পরিগ্রহকারী বিশৃঙ্খলা, চরমপন্থা ও সন্ত্রাসবাদ নিয়ে তিনি আলোচনা করেছেন।
পূর্বে আমি যেমনটা উল্লেখ করেছি আমরা তাঁর গ্রন্থসমূহকে দু’ভাগে বিভক্ত করতে পারি। একভাগ হলো উসূল ও মেথডোলজি সংক্রান্ত আর অপর ভাগ হলো জীবনের বিভিন্ন প্রায়োগিক দিক নিয়ে।
উসূল ও মেথডোলজি সম্পর্কিত গ্রন্থসমূহ আবার দু’ভাগে বিভক্ত করা যায়। এর মধ্যে এক ভাগ হলো ‘ফালসাফাতুল তাদাভুলিয়্যাহ’ সম্পর্কে আর অপরভাগ হলো ‘ফালসাফাতুল ই’তিমানিয়্যাহ’ সম্পর্কে।
আল্লামা ত্বহা আব্দুর রহমান তাঁর চিন্তা পাঁচটি মৌলিক বিষয়কে সামনে রেখে তুলে ধরেছেন। তন্মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ একটি হলো আল-মানহাজ। অর্থাৎ পদ্ধতি বা পন্থা। তাজদীদুল মানহাজ ফি তাকবিমুত তুরাস – এই গ্রন্থের মাধ্যমে তিনি আমাদের জ্ঞানগত ও সাংস্কৃতিক মিরাস (ঐতিহ্য) পর্যালোচনা করার জন্য নতুন একটি পন্থার প্রস্তাবনা দিয়েছেন। আমাদের ইতিহাস ও ঐতিহ্য (মিরাস)-কে কীভাবে বুঝবো? যদিও অনেকেই বলেন যে, এই গ্রন্থটি তিনি মুহাম্মাদ আবিল আল-জাবিরিকে উদ্দেশ্য করে লিখেছেন এবং তাঁর উত্থাপিত বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন। আসলে বিষয়টি এমন নয়। অর্থাৎ ত্বহা আব্দুর রহমান অন্যকে খণ্ডন করার পন্থা অবলম্বন করেন না। তিনি একজন বিনির্মাণকারী। তিনি কাউকে বিরোধী হিসেবে গণ্য করে তাকে খণ্ডন করেন না; বরং যেটা হাকীকত ও সত্য সেটাকেই তিনি সর্বোচ্চ যুক্তি ও দলীল দিয়ে তুলে ধরেন। এ কারণে তিনি একজন অসাধারণ নির্মাতা। তবে তিনি জাবিরি’র বয়ান, বুরহান ও ইরফান নামক ত্রয়াত্মক শ্রেণিবিন্যাস এবং এর উপর ভিত্তি করে ইসলামী চিন্তাধারাকে সরলীকরণের কঠোর সমালোচনা করেন। এই ক্ষেত্রে তিনি তাকামুলী তথা উৎকর্ষতার পন্থাকে প্রস্তাব করেন। এই তিনটিকে তাদাখুলিয়া তথা একে অপরের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে বিবেচনা করেন।
তাঁর মতে, আধুনিক সময়ে এসে আমরা পাশ্চাত্যের খণ্ডিত চিন্তার প্রভাবে সকল কিছুকেই খণ্ডিতভাবে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করি। সকল কিছুকে খণ্ডিত করে দেখা ভুল একটি পন্থা। এই পন্থাটি আমাদের মঝে প্রভাব বিস্তার করার কারণে ইসলামী চিন্তা সামগ্রিকভাবে অনুধাবন করার সক্ষমতাকেও আজ হারিয়ে ফেলেছি। এই পন্থা বা মেথডকে তিনি মানহাজের অংশে ভাষা, মানতিক ও দর্শনের পাশাপাশি উসূলুল ফিকহের দৃষ্টিকোণ থেকেও ব্যাখ্যা করেন।
তিনি অসুস্থ থাকা অবস্থায়ও ৫৮০ পৃষ্ঠার বিশাল একটি গ্রন্থ রচনা করেছেন। গ্রন্থটির নাম হলো, আত-তা’সিসুল ই’তিমানি লি ইলমিল মাকাসিদ। অনুবাদ করলে এর অর্থ দাঁড়ায়, ইলমুল মাকাসিদের ই’তিমানি ভিত্তিসমূহ। আমার মতে, এই গ্রন্থটি মাকাসিদ নিয়ে লেখা বিগত ২০ বছরের সবচেয়ে সেরা গ্রন্থ। আর এই গ্রন্থের পর এই বিষয়ে যারা লেখালেখি করেছেন তাঁরা তাঁদের চিন্তাকে পুনর্বিবেচনা করবেন বলে আমার বিশ্বাস। কেননা তিনি মাকাসিদের শরয়ী গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে আলোচনা করেছেন। অর্থাৎ যেটা শরয়ী সেটা কতটুকু গ্রহণযোগ্য? আর যেটা গ্রহণযোগ্য সেটা কতটুকু শরয়ী? আমরা ইলাহী মাকসাদ বা উদ্দেশ্যকে এত সু-স্পষ্টভাবে কীভাবে উল্লেখ করতে পারি? এই শক্তি আমরা কোথায় পাই? এই বিষয়ে তিনি আলোচনা করেছেন। এসকল দৃষ্টিকোণ থেকে এ গ্রন্থটি গুরুত্বপূর্ণ একটি গ্রন্থ।
আমরা পূর্বেও উল্লেখ করেছি যে, ত্বহা আব্দুর রহমানের অন্যতম একটি গ্রন্থ হলো রুহুদ দ্বীন। এ গ্রন্থে তিনি দ্বীন ও ধর্মের মধ্যকার সম্পর্ককে শুধুমাত্র সেকুলারিজমের দৃষ্টিকোণ থেকেই অর্থাৎ দ্বীনের রাজনীতিকরণ কিংবা রাজনীতির দ্বীনিকরণ নিয়েই আলোচনা করেননি। এ গ্রন্থে একইসাথে তিনি তাদবীর ও তায়াব্বুদের মধ্যকার সম্পর্ক নিয়ে নতুন একটি উসূল দাঁড় করিয়েছেন। তায়ায়্যুশী আমলের সাথে তায়াব্বুদী আমলকে কীভাবে একত্রিত করতে পারি এবং ইসলাম এই বিষয়টি কীভাবে তুলে ধরেছে সে বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন।
তিনি বিভিন্ন পরিভাষার পাশাপাশি যে পরিভাষার ব্যপারে সবচেয়ে বেশি জোর দিয়েছেন সেটি হলো ‘তুরাস’। যে চিন্তা তাঁর অতীতকে অস্বীকার করে সেই চিন্তার পক্ষে নতুন কোনো প্রস্তাবনা দেওয়া সম্ভব নয়। শুধু তাই নয়, তাঁর পক্ষে নতুন কোনো চিন্তাও দাঁড় করানো সম্ভব নয়। এক্ষেত্রে তিনি তাকদীস ও তাহকীর তথা তুরাসকে পবিত্র বলে গণ্য করা থেকেও বিরত থাকেন আবার সেটাকে হেয় প্রতিপন্ন করা থেকেও বিরত থেকে অতীত থেকে শিক্ষা নেওয়ার পন্থা তথা তাকদীরের পন্থাকে বেছে নেওয়ার পক্ষে মত দেন।
মডার্নিটি কিংবা আধুনিকতা নিয়ে আলোচনা করার জন্য তিনি রুহুল হাদাসা নামক গ্রন্থ রচনা করেছেন। তাঁর মতে, পাশ্চাত্যের আধুনিকতা নামে একটি আধুনিকতা রয়েছে। অর্থাৎ আধুনিকতা একমাত্র কিংবা অনুপম নয়। প্রতিটি চিন্তায় তাঁর মতো করে তাঁদের নিজস্ব আধুনিকতা তৈরি করতে পারে। পাশ্চাত্যে আধুনিকতা যে ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে গড়ে উঠেছে তাঁর কিছু মৌলিক পরিভাষা আছে। যেমন, ধর্মহীন বিশ্বদর্শন (Secular World View), রেশনালিজম, হিউম্যানিজম ইত্যাদি। কিন্তু আমরা আমাদের নিজস্ব চিন্তা ও পরিভাষার মাধ্যমে আমাদের জন্য স্বতন্ত্র একটি আধুনিকতার বিকাশ ঘটাতে পারি। অর্থাৎ আধুনিকতার রূহকে বিবেচনায় নিয়ে আমাদের রূহকে বিনির্মাণ করতে পারলে সেই রূহের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ একটি আধুনিকতার উদ্ভব ঘটবে।
ত্বহা আব্দুর রহমানের চিন্তায় অপর আরেকটি বিষয় হলো আখলাক। এই বিষয়েও তিনি অনেক বেশি গুরুত্বারোপ করেন। বিশেষ করে দ্বীন ও আখলাকের সম্পর্কের ক্ষেত্রে সকল ধরণের বিভাজনকে প্রত্যাখ্যান করেন এবং দ্বীনকে আখলাক হিসেবে ও আখলাককে দ্বীন হিসেবে অভিহিত করেন। ‘Cogito, ergo sum’ (চিন্তা করি এই জন্যই আছি) চিন্তার বিপরীতে ‘আমি আখলাকসম্পন্ন, এই জন্য আমি আছি” এই চিন্তার বিকাশ ঘটান। আখলাকী চিন্তার ক্ষেত্রে মুসলিম আলেমদের চিন্তার সমালোচনা করে বলেন, তাদের চিন্তার মধ্যে অনেক ঘাটতি রয়েছে। কেননা তাঁরা আখলাককে পূর্ণতা হিসেবে দেখে থাকেন। কিন্তু আখলাক পূর্ণতাদানকারী কোনো বিষয় নয়। এটি অস্তিত্বের সাথে সম্পর্কিত একটি বিষয়। আখলাক ছাড়া আমাদের অস্তিত্ব অকল্পনীয়। আখলাক পূর্ণতার (কামালিয়াত) সাথে সম্পর্কিত কোনো বিষয় নয়, এটা অস্তিত্বের সাথে সম্পর্কিত একটি বিষয়। এটা দ্বীন ও মানুষ উভয়ের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। আখলাক ছাড়া দ্বীন হতে পারে না, আখলাক ছাড়া মানুষ হতে পারে না। মানুষের যে সংজ্ঞা সেই সংজ্ঞার একাংশ জুড়ে আছে আখলাক আর বাকি অংশ হলো দ্বীন। তবে এক্ষেত্রে দ্বীন হলো মূল।
তাঁর মতে, রাজনীতি থেকে দ্বীনকে পৃথকীকরণ করার চেয়ে দ্বীনকে আখলাক থেকে পৃথক করা আর বড় ধরণের হুমকি। আর এ বিষয়কে তুলে ধরার জন্য তিনি দাহরানিয়্যাহ নামক একটি পরিভাষা তৈরি করেন। দাহরানিয়্যাহ হলো, দ্বীনকে আখলাক থেকে পৃথক করা। আর এটাই হলো সবচেয়ে বড় বিপদজনক বিষয়।
ত্বহা আব্দুর রহমান ফিতরাতের বিষয়টিকেও গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় হিসেবে বিবেচনা করেন। তিনি তাঁর সকল গ্রন্থেই এ বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন। কেননা তাঁর মতে, দ্বীন মানুষের পূর্বে ছিল। মানুষের সৃষ্টি হয়েছে দ্বীনের পরে। শুধু তাই নয়, খুলক-ও (আখলাক) খালকের (সৃষ্টির) পূর্বে। মানুষের সৃষ্টির পূর্বেই খুলক ছিল আর এটা ফিতরাতরূপে মূল্যবোধের একটি ভাণ্ডার হিসেবে মানুষকে দেওয়া হয়েছে। দ্বীন মানুষের মধ্যে পরবর্তীতে স্থাপিত কোনো বিষয় নয়। দ্বীনের অর্থের জগত মানুষের সাথে একত্রে অস্তিত্বপ্রাপ্ত মৌলিক একটি হাফিজার (সংরক্ষণশালা) মধ্যে লুক্কায়িত। আর এই হাফিজা বা সংরক্ষণশালার নাম হলো ফিতরাত। দ্বীন মানুষকে সঙ্গ দানকারী একটি হাকীকত এবং মানুষ এ হাকীকত থেকে কখনো পৃথক হতে পারবে না। অপর দিকে পয়গাম্বরদের মাধ্যমে যে দ্বীন এসেছে সেটা মূলত তাজকীর বা স্মারক। অর্থাৎ, মানুষের ফিতরাতের মধ্যে যা রয়েছে, সেটাই মানুষকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া। এ কারণে কোরআন যাক্কির (স্মারক), পয়গাম্বর মুজাক্কির। মিসাকুর রিসালার সাথে মিসাকুশ শাহাদাকে ত্বহা আব্দুর রহমান সূরা আরাফের ১৭২ নং আয়াতের উপর ভিত্তি করে দাঁড় করিয়েছেন।
(وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ ۖ قَالُوا بَلَىٰ ۛ شَهِدْنَا)
অর্থ : “আর হে নবী! লোকদের স্মরণ করিয়ে দাও সেই সময়ের কথা, যখন তোমাদের রব বনী আদমের পৃষ্ঠদেশ থেকে তাদের বংশধরদের বের করিয়েছিলেন এবং তাদেরকে তাদের নিজেদের ওপর সাক্ষী বানিয়ে জিজ্ঞেস করেছিলেন : ‘আমি কি তোমাদের রব নই?’ তারা বলেছিল, নিশ্চয়ই তুমি আমাদের রব, আমরা এর সাক্ষ্য দিচ্ছি।”
এই আয়াতের উপর ভিত্তি করে তিনি বলেন, আল্লাহ ও মানুষের মধ্যকার সম্পর্ক হলো শাহাদাতের উপর ভিত্তি করে।
আর দ্বিতীয় মিসাক হলো, মিসাকুল আমানা। এটাকে তিনি সূরা আহযাবের ৭২ নং আয়াতের উপর ভিত্তি করে দাঁড় করিয়েছেন।
إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ ۖ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا
অর্থ : “আমি এ আমানতকে আকাশসমূহ, পৃথিবী ও পর্বতরাজির ওপর পেশ করি। তারা একে বহন করতে রাজি হয়নি এবং তা থেকে ভীত হয়ে পড়ে। কিন্তু মানুষ একে বহন করেছে, নিঃসন্দেহে সে বড় জালেম ও অজ্ঞ।”
আর তৃতীয়টি তথা মিসাকুর রিসালাকে তিনি দাঁড় করিয়েছেন সূরা বাকারার ১৫১ নং আয়াতের উপর ভিত্তি করে।
كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ
অর্থ : “যেমনিভাবে (তোমরা এই জিনিসটি থেকেও সাফল্য লাভের সৌভাগ্য অর্জন করেছো যে) আমি তোমাদের মধ্যে স্বয়ং তোমাদের থেকেই একজন রাসূল পাঠিয়েছি, যিনি তোমাদেরকে আমার আয়াত পড়ে শুনায়, তোমাদের জীবন পরিশুদ্ধ করে সুসজ্জিত করে, তোমাদেরকে কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দেয় এবং এমন জ্ঞান তোমাদের শেখায়, যা তোমরা জানতে না।”
মিসাকুশ শাহাদা ফিতরাত হিসেবে মানুষের সাথে একত্রে অস্তিত্ব লাভ করেছে, মিসাকুল আমানা মূলত মূল্যবোধ হিসেবে এসেছে। এ দৃষ্টিকোণ থেকে চিন্তা করলে উভয়টি মূলত মূল্যবোধ। একটি হলো ঈমান অপরটি হলো আখলাক। এগুলো মানুষের মধ্যে একটি সফটওয়্যার হিসেবে মানুষের অস্তিত্ব লাভের সাথে সাথে অস্তিত্ব লাভ করেছে কিন্তু তা আগে থেকেই বিদ্যমান ছিল। আর মিসাকুর রিসালা হলো এটাকে পূর্ণতাদানকারী একটি বিষয়। এ দু’টি বিষয়কে স্মরণ করিয়ে দেওয়ার জন্যই মহান আল্লাহ পয়গাম্বর পাঠিয়েছেন।
ত্বহা আব্দুর রহমানের অপর একটি গ্রন্থ হলো, আল-মানতিক ওয়ান নাহও’স সূরী। এই গ্রন্থে তিনি সূরী মানতিক ও নাহু’র মাধ্যমে ইসলামের মূল্যবোধসমূহকে অপর মানুষের নিকট উত্থাপনকারী একটি ভাষা হিসেবে আরবী ভাষা নিয়ে বিশ্লেষণ করেন।
দর্শনের বিষয়ে বিশেষ করে দু’টি ক্ষেত্রে তিনি অনেক বেশি গুরুত্ব প্রদান করেন এবং এ ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ চিন্তা তুলে ধরেন। তাঁর মতে, দর্শন মানে হলো প্রশ্ন করা। আর প্রশ্ন করার পন্থা দু’টি :
- ১. অপরপক্ষকে চুপ করানো জন্য প্রশ্ন করা। প্রশ্ন করার এই পন্থা হলো গ্রীক দার্শনিকদের পন্থা। যেমন, সক্রেটিসের প্রশ্ন করার পন্থা।
- ২. সমালোচনামূলক প্রশ্ন করা। ইম্যানুয়েল কান্ট এই পন্থা শুরু করেন এবং প্রভাবশালী করে তুলেন।
তবে ই’তিমানিয়্যাহ দর্শনের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র সুয়াল বা প্রশ্ন নেই। সুয়াল বা প্রশ্নের উদ্দেশ্য শুধুমাত্র সুয়ালিয়্যাত (প্রশ্ন করা) নয়, এখানে উদ্দেশ্য হলো মাসউলিয়্যাত (দায়িত্ববোধ)। সুয়াল-মাসয়ালা ও মাসউলিয়্যাতের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করে তিনি এই বিষয়কে তুলে ধরেন এবং মনে করেন, প্রশ্ন যখন দায়িত্ববোধের চেতনা জাগ্রত করবে কেবল তখনই সেটা সত্যিকারের প্রশ্ন হিসেবে গণ্য হবে। ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে এ ধরণের প্রশ্নই আমাদের সত্যিকারের দর্শন। এ ক্ষেত্রে তিনি ‘আস-সুয়ালুল মাসউল’ পরিভাষা নিয়ে আলোচনা করেন।
পরিভাষা তৈরি করার ক্ষেত্রেও তিনি অতুলনীয়। কিছুদিন আগে এ ব্যপারে কামুসু ত্বহা নামে প্রায় ৬০০ পৃষ্ঠার একটি বই প্রকাশিত হয়েছে।
ত্বহা আব্দুর রহমানের মতে, মুসলিম উম্মাহ পরিভাষাগত একটি আক্রমণের শিকার। এ ক্ষেত্রে তিনি ‘আল-উদওয়ানুল মাফহুমী’ নামক পরিভাষা ব্যাবহার করেন।
তিনি বলেন, “পরিভাষা তৈরি করা ও পরিভাষার অধিকারী হওয়ার অর্থ হলো সবচেয়ে বেশি শক্তিশালী হওয়া। কোনো কিছুকে পরিভাষার মাধ্যমে পরিবর্তন করা শক্তি প্রয়োগ করে পরিবর্তন করার চেয়ে বেশি স্থায়ী হয়ে থাকে। পরিভাষার মধ্য দিয়ে বড় বড় পরিবর্তন করা সম্ভব”।
এ কারণেই তিনি পরিভাষার উপর এত বেশি গুরুত্বারোপ করেছেন এবং শত শত পরিভাষা তৈরি করেছেন।
অনুরূপভাবে তিনি আকলের বিষয়েও অনেক গুরুত্বারোপ করেছেন। এ বিষয়ে তিনি স্বতন্ত্র গ্রন্থও রচনা করেছেন। আকলকে তিনি আকলে মুজাররাদ, আকলে মুয়ায়্যাদ ও আকলে মুসাদ্দাদ নামে তিন ভাগে বিভক্ত করেন। তাঁর মতে, আকলে মুজাররাদ হলো বুরহানী আকল। এটি এমন আকল যা দ্বীনি ক্ষেত্রকে উপেক্ষা করে। এই ধরণের আকল হলো বিমূর্ত (Abstract) ও যান্ত্রিক। এ ধরণের আকল বিজ্ঞানাগারে, কল কারখানায় ও একাডেমিক গবেষণার কাজে লাগতে পারে কিন্তু মানুষের সাথে তাঁর রবের ও মহাবিশ্বের যে সম্পর্ক, সেই সম্পর্ক এই আকলের উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়। এ কারণে তিনি আমলের মাধ্যমে সজ্জিত আকলকে ‘আকলে মুসাদ্দাদ’ নামে নামকরণ করেছেন। আর যে আকল আখলাকী মূল্যবোধের মাধ্যমে অলঙ্কৃত হয়েছে সেই আকলকে তিনি ‘আকলে মুয়ায়্যাদ’ নামে অভিহিত করেন। তিনি মনে করেন, আকল শুধুমাত্র একমুখী হিসেবে বিবেচনা করার অর্থ আকলকেই ছোট করা। কেননা আকল আল্লাহ প্রদত্ত নেয়ামত। এজন্য এই নেয়ামতকে বহুমুখী হিসেবে দেখতে হবে। আকল কোনো জাওহার নয়। আকল হলো একটি কর্ম। এই কারণে তিনি তায়া’ক্কুলের প্রকারভেদ নিয়ে আলোচনা করেছেন।
এখন আমি তাঁর গ্রন্থসমূহের একটি সংক্ষিপ্ত পরিচিতি তুলে ধরতে চাই।
প্রথমত, মেথডোলজি সংক্রান্ত গ্রন্থ। এ সম্পর্কে রচিত তাঁর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ হলো ফিকহুল ফালসাফা। চার খণ্ডে বিভক্ত করে তিনি এ গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। কিন্তু পরবর্তীতে তা দুই খণ্ড প্রকাশিত হয়। এ গ্রন্থে তিনি বলেন, অন্যের চিন্তা অনুবাদ করে কোনোদিন সত্যিকারের চিন্তা তৈরি করা যায় না। পাশ্চাত্যের দর্শন বিষয়ক যে সব বইকে অনুবাদ করে আজকে সমগ্র বিশ্বে পড়ানো হচ্ছে, সেটার সম্পর্কে মূল্যায়ন করতে গিয়ে তিনি বলেন,
لن تكون الفلسفة رافعة إلا اذا كانت مبدعة
অর্থ : “দর্শন কোনো জাতিকে উচ্চমর্যাদায় আসীন করতে পারে না, যদি না সেটা নিজেদের মূল্যবোধের উপরে প্রতিষ্ঠিত হয়।”
অর্থাৎ, তাকলীদের মাধ্যমে চর্চিত দর্শন কোনোদিন কোনো জাতিকে উচ্চ মর্যাদায় আসীন করতে পারে না। যদি কোনো জাতি চিন্তার মাধ্যমে উচ্চ মর্যাদায় আসীন হতে চায়, তাহলে তাকে নিজ মূল্যবোধের সাথে সম্পর্ক রেখে চিন্তা ও দর্শন তৈরি করতে হবে। নাসক মাসক নিয়ে আসে। নাসক হলো কোনো কিছুকে ফটোকপি করা। আর ফটোকপি মাসক’কে নিয়ে আসে। মাসক কী? মাসক হলো, ফটোকপির মাধ্যমে অন্যদের অনুবাদ করে তাদের চিন্তাকে নিয়ে আসলে সেটা একটি জাতিকে বিশেষভাবে মুসলিম উম্মাহকে ভেতর থেকে পরিবর্তন করে দিবে।
তিনি ‘তাকরীবে তা’বী’ নামে একটি পন্থার কথা উল্লেখ করেছেন। অর্থাৎ এর অর্থ এটা নয় যে, আমরা কারোর কাছ থেকে কোনো কিছুই নেবো না। তবে আমরা অন্যদের কোনো চিন্তা ও দর্শন অনুবাদ করার ক্ষেত্রে তাদাভুলিয়্যার দিকে খেয়াল রাখতে হবে। আমরা যে সকল চিন্তা অনুবাদ করবো, সেই চিন্তার ভাষাগত ও ধর্মীয় ভিত্তিকে ভালোভাবে বুঝতে হবে। কেননা আমাদের ভাষা ও ধর্ম উভয়টিই ভিন্ন। যেমনঃ তিনি হেগেল ও নিটশে-কে পর্যালোচনা করতে গিয়ে বলেন, এরা অনেক ধর্মতত্ত্বীয় পরিভাষাকে দার্শনিক চিন্তায় রূপান্তরিত করেছে। এ কারণে আমরা যখন অনুবাদ করবো তখন আমাদেরকে তিনটি বিষয়ের দিকে খেয়াল রাখতে হবে। সেগুলো হলো তাহসিলিয়্যা, তাওসিলিয়্যা ও তা’সিলিয়্যা। তাহসিলিয়্যা হলো হুবহু অনুবাদ করা। তাওসিলিয়্যা হলো, সতর্কতার সাথে বেছে বেছে অনুবাদ করা। তা’সিলিয়্যা হলো, শুধুমাত্র আমার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ বিষয়সমূহকে অনুবাদ করা। আমাকে সেই বিষয়সমূহই অনুবাদ করতে হবে, যেগুলো আমাদের দ্বীন ও ভাষার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ।
ফিকহুল ফালসাফার দ্বিতীয় খণ্ড হলো আল-কাওলুল ফালসাফিয়্যু অর্থাৎ দার্শনিক কথন কী? এ গ্রন্থে তিনি পরিভাষা ও এটিমলজি নিয়ে আলোচনা করেছেন। এ গ্রন্থে তিনি বলেন,
فالقول الذي لا يتصل بترثه لا يمكن ان يكون إبداعا
অর্থাৎ, “ইতিহাস ও ঐতিহ্যের (তুরাস) সাথে যে কথার সম্পর্ক নেই, সেই কথার পক্ষে নতুন কোনো প্রস্তাবনা পেশ করা সম্ভব নয়।”
এ ক্ষেত্রে তিনি আল আকলানিয়্যাতুল ইবারিয়্যার সাথে আল আকলানিয়্যাতুল ইশারিয়্যার মধ্যকার সম্পর্ক স্থাপন করার পাশাপাশি কালাম ও তাসাউফের মধ্যেও সম্পর্ক স্থাপন করেন। আল আকলানিয়্যাতুল ইবারিয়্যা ও ইশারিয়্যা নিয়ে আলোচনা করার সময় প্লেটো, দেকার্ত ও হাইডেগারকে উদ্দেশ্য করে কঠিন চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দেন।
তাঁর দ্বিতীয় গ্রন্থ হলো আল-লিসান ওয়াল মিযান ওয়া’ত-তাকাওসুরুল আকল। এ গ্রন্থে তিনি মানতিক ও আকলের প্রকারভেদ নিয়ে আলোচনা করেছেন। এ বইয়ে তিনি বলেন,
ان الاتصال الإنسان باللامتناهي الكامل من جهة ما يدفعه الي دوام طلب الزيادة في التعقل بدرجات تعلو علي واقع تعلقه
অর্থাৎ, “অসীমের (ইনফিনিটি) সাথে মানুষের যে সম্পর্ক, সেটা সর্বদা তার তা’য়াক্কুলী (চিন্তা করার) শক্তিকে বিকশিত করে থাকে এবং চিন্তা করার ক্ষেত্রে সে যে অবস্থায় আছে তাকে সেই অবস্থা থেকে তাঁর অবস্থানকে সর্বদা উচ্চ পর্যায়ের দিকে নিয়ে যায়।”
এ গ্রন্থে তিনি তিনটি ধারার তুলনামূলক পর্যালোচনা তুলে ধরেছেন। গাজালিয়্যা, রুশদিয়্যা ও খালদুনিয়্যা নামে গাজ্জালী, ইবনে রুশদ ও ইবনে খালদুনের তুলনামূলক পর্যালোচনা করেছেন।
একইসাথে তিনি আল-খিতাবিয়্যা, আল-হিজাজিয়্যা ও আল-মাজাজিয়্যার পন্থাকেও বিশ্লেষণ করেছেন।
মেথডোলজি সম্পর্কে তাঁর চতুর্থ গ্রন্থ হলো আল হাক্কুল আরাবী ফি’ল ইখতিলাফিল ফালসাফিয়্যা। এ গ্রন্থে তিনি মুসলমানদের দর্শন তৈরি করার অধিকার নিয়ে আলোচনা করেছেন। এ বিষয়ে তাঁর এই উক্তিটি প্রণিধানযোগ্যঃ
ان الاختلاف الأمم ظاهرة طبيعية لا ينكرها إلا من يري في الاختلاف زوال سلطانه
অর্থাৎ, “উম্মতসমূহের ভিন্নতা প্রাকৃতিক একটি বিষয়। যারা নিজের উপর কর্তৃত্ব হারিয়েছে, তাঁরা ছাড়া অন্য কেহই এই অমোঘ বিধানকে অস্বীকার করতে পারে না।”
لذالك لا بد من اثبات هذا الحق للأمم المهزومة كما المنتصرة
অর্থাৎ, “আর এই কারণে যে জাতি পরাজিত ও পরাভূত হয়েছে, তাঁদেরও পুনরায় নিজের পায়ে দাঁড়ানোর অধিকার রয়েছে। তাঁদেরও অধিকার আছে তাঁদের নিজেদের দর্শনকে তৈরি করার।”
এই গ্রন্থের শুরুতেই তিনি বলেন, যে সভ্যতা তাঁর যুগ-জিজ্ঞাসার জবাব নিজের মূল্যবোধের মাধ্যমে দিতে সক্ষম নয়, সেই সভ্যতার পক্ষে নিজের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখা অসম্ভব। যে সভ্যতা যুগ-জিজ্ঞাসার জবাব অন্য সভ্যতা কর্তৃক সৃষ্ট মূল্যবোধ ও জবাবের মাধ্যমে দেওয়ার চেষ্টা করে, সেই সভ্যতা আরও বেশি অধঃপতনের শিকার হয়।
আমরা মুসলিম হিসেবে যুগ-জিজ্ঞাসার জবাব কীভাবে দিবো এবং আমাদেরকে কীভাবে কাজ করতে হবে, এ বিষয়ে তিনি যুক্তিপূর্ণ ভাষায় তাঁর অভিমত তুলে ধরেছেন।
মেথডোলজি সম্পর্কে তাঁর পঞ্চম গ্রন্থ হলো আল-হাক্কুল ইসলামী ফিল ইখতিলাফিল ফিকরি। এ গ্রন্থে তিনি চিন্তাগত বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোকপাত করেছেন এবং ইসলামী চিন্তাকে কীভাবে নবায়ন করে তুলে ধরা যায় এ বিষয় নিয়েও আলোকপাত করেছেন। এ গ্রন্থেই তিনি বলেছেনঃ
ان من العجز ان نرضي باجوبة غيرنا
“আমাদের সবচেয়ে বড় দুর্বলতা হলো যুগের জবাবদানের ক্ষেত্রে অন্যদের তৈরি করা জবাবের মাধ্যমে জবাব দেওয়া।
التي انتهت بهم طريق مسدود
আর এই বিষয়টিই আমাদের পথ রোধ করে দিয়েছে।
بل طريق يقلب الوسائل والمقاصد الي اضدادها
শুধু তাই নয়, এটা মাকসাদ ও ওসিলার স্থানকে পরিবর্তন করে দিতে পারে, যা আমাদের উদ্দেশ্যের পরিপন্থী হয়ে যেতে পারে।”
অর্থাৎ মাকসাদের স্থান ওসিলা আর ওসিলার স্থান মাকসাদ দখল করে নিতে পারে। যার ফলে আমাদের উদ্দেশ্যই পরিবর্তন হয়ে যেতে পারে।
আত-তাওয়াসুল ওয়াল হিজাজ নামে ভাষাতত্ত্বের উপরে তাঁর আরেকটি গ্রন্থ রয়েছে। এ গ্রন্থে তিনি ভাষাগত যোগাযোগ নিয়ে আলোচনা করেছেন।
আমি মনে করি, ত্বহা আব্দুর রহমানের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ হলো সুয়ালুল আখলাক। একটু পূর্বেই আমি যেমনটা উল্লেখ করেছি, তিনি আখলাককে কামালিয়াত (পরিপূর্ণতা) দানকারী কোনো বিষয় নয়; বরং অস্তিত্বদানকারী একটি বিষয় হিসেবে উল্লেখ করেছেন। এ গ্রন্থে তিনি আখলাককে সামগ্রিকভাবে তুলে ধরেছেন। তাঁর মতে, আখলাককে দ্বীন থেকে এবং দ্বীনকে আখলাক থেকে পৃথক করা সম্ভব নয়। যদি পৃথক করা হয়, তাহলে এর পরিণতি কী হতে পারে -এই সকল বিষয় নিয়ে তিনি বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।
বুয়ুসুদ দাহরানিয়া তাঁর আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ। এ গ্রন্থটিতেও তিনি আখলাক নিয়ে আলোচনা করেছেন এবং দ্বীন থেকে আখলাককে পৃথক করে ফেললে কোন ধরণের সমস্যা তৈরি হতে পারে -এই বিষয়টি তিনি ই’তিমানি দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচনা করেছেন। ই’তিমানি দর্শনের দৃষ্টিকোণ থেকে এ গ্রন্থটি সুয়ালুল আখলাকের ধারাবাহিকতা হিসেবে গণ্য করা যায়।
এ গ্রন্থের সাথে সম্পর্কিত আরও একটি গ্রন্থ রয়েছে, সেটি হলো শুরুদু মা বা’দাদ দাহরানিয়্যা। এ গ্রন্থে তিনি সমগ্র মানবতার আখলাক নিয়ে আলোচনা করেছেন। পাশ্চাত্য চিন্তা সমগ্র মানবতাকে কীভাবে আখলাকের বাহিরে ঠেলে দিয়েছে- এ বিষয় নিয়ে তিনি আলোচনা করেছেন। এ গ্রন্থে বিশেষভাবে তিনি মনোবিশ্লেষকদের নিয়ে আলোচনা-পর্যালোচনা করেছেন। সিগমুন্ড ফ্রয়েড, ফ্রিডরিখ নিটশে, লুইস দি লসাদে, লাকান-সহ আরও অন্যান্য মনোবিশ্লেষকদের চিন্তাকে খণ্ডন করেছেন। কেননা এ সকল চিন্তাবিদরা মানুষকে কামুক একটি জীব হিসেবে অভিহিত করে ইনসানকে শুধুমাত্র চাহিদার মাধ্যমে সংজ্ঞায়িত করার চেষ্টা করেছে। এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি গ্রন্থ। আবার বুঝতেও খুব কঠিন। অর্থাৎ বুয়ুসুদ দাহরানিয়া নামক গ্রন্থে তিনি আলোচনা করেছেন, মানুষ যদি দ্বীন থেকে আখলাককে আলাদা করে ফেলে, তাহলে একদিন সে তাঁর নিজেকেও আখলাক থেকে আলাদা করে ফেলবে। এরই ধারাবাহিকতায় তিনি শুরুদু মা বা’দাদ দাহরানিয়্যা নামক গ্রন্থে আলোচনা করেছেন, মানুষ কীভাবে আখলাক থেকে আলাদা হয়ে যায় এবং এর পর্যায়সমূহ কি হতে পারে।
আল-আমালু’দ দিনিয়্যু ওয়া তাজদিদুল আকল নামেও তাঁর একটি গ্রন্থ রয়েছে। এ গ্রন্থে তিনি আমল ও আকলের পুনর্জাগরণের কথা উল্লেখ করেছেন। এ গ্রন্থ থেকে আমি দু’একটি লাইন পাঠকদের উদ্দেশ্য উল্লেখ করতে চাই-
ليس هناك من علم ولا عمل فائقين مثل المتعلقين بالدين
“এমন কোনো জ্ঞান ও আমল নেই, যা দ্বীনের সাথে সম্পর্কিত জ্ঞান ও আমলের চেয়ে উত্তম হতে পারে।”
لذالك كان الجمود هو العدو الأساسي لفاعلية الدين
“দ্বীনি কার্যক্রমের দৃষ্টিকোণ থেকে সবচেয়ে বড় হুমকি হলো চিন্তাকে স্থবির করে ফেলা।”
অর্থাৎ যারা জ্ঞান ও আকলের পুনর্জাগরণের জন্য কাজ করবে, তাঁদেরকে সবসময় জ্ঞানগত ও আমলগত দিক থেকে গতিশীল থাকতে হবে। কোনো আন্দোলন যখন তাঁর চিন্তাগত গতিশীলতাকে হারিয়ে ফেলে, তখনই তা কালের অতল গহ্বরে হারিয়ে যায়।
তাঁর অপর একটি গ্রন্থ হলো উসূলিল হিওয়ার ওয়া তাজদিদু ইলমিল কালাম। তাঁর এ গ্রন্থটিও খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই গ্রন্থে তিনি আল্লাহ ও মানুষের মধ্যকার সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করেছেন। একইসাথে তিনি এই গ্রন্থে ইলমূল মানতিকের মধ্যকার যে ডায়ালগ রয়েছে, সেই ডায়ালগকে নিয়েও আলোচনা করেছেন এবং এটাকে মানুষ ও আল্লাহর মধ্যকার সম্পর্কের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেছেন।
ত্বহা আব্দুর রহমান শুধু থিওরীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেননি। আমলী দিকের প্রতিও তিনি তাঁর দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছেন। এই বিষয়ে লেখা তাঁর অন্যতম গ্রন্থ হলো সুয়ালুল আমল। সেখানে তিনি বলেন,
كل علم ليس تحته عمل فغير معتبر
অর্থাৎ, “যে জ্ঞান আমল দ্বারা সজ্জিত নয়, সেই জ্ঞান খুব বেশি গ্রহণযোগ্য নয়।”
তাঁর অপর একটি গ্রন্থ হলো মিনাল ইনসানিল আবতার ইলা ইনসানিল কাউসার। অর্থাৎ একমুখী ইনসান থেকে বহুমুখী ইনসানের দিকে। আবতার ইনসান হলো একমুখী ইনসান। সে শুধুমাত্র বস্তুজগত নিয়েই সন্তুষ্ট থাকে। কিন্তু কাউসার ইনসান বস্তুজগত (মুলক) ও আধ্যাত্মিক (মালাকুত) জগতকে একসাথে বিবেচনা করে। এ গ্রন্থটি দু’ভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগে শিক্ষা দর্শন নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে আর দ্বিতীয় ভাগে দার্শনিক ধারণা নিয়ে আলোকপাত করা করা হয়েছে। তবে উভয় অধ্যায়েই ইনসানকে তিনি কেন্দ্রে রেখেছেন।
তাঁর অন্যতম আরেকটি গ্রন্থ হলো দ্বীনুল হায়া। এ গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে তিনি ই’তিমানি আখলাকের দর্শন নিয়ে আলোচনা করেছেন এবং আখলাককে আসমাউল হুসনার উপর ভিত্তি করে বিশ্লেষণ করেছেন। এ খণ্ডে তিনি হুদুদুল্লাহ নিয়েও বিস্তারিত আলোচনা করেন।
দ্বীনুল হায়ার দ্বিতীয় খণ্ডে তিনি ডিজিটালাইজেশনের মাধ্যমে সৃষ্ট গায়রে আখলাকী চ্যালেঞ্জকে কীভাবে মোকাবেলা করা যায় এই বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন। বিশেষ করে হায়ার আখলাকের মাধ্যমে এই সঙ্কটকে আমরা কীভাবে মোকাবেলা করবো সে বিষয়টি দার্শনিক যুক্তি দিয়ে তুলে ধরেছেন।
দ্বীনুল হায়ার তৃতীয় খণ্ড হলো রুহুল হিজাব। এই গ্রন্থটি অসাধারণ একটি গ্রন্থ। হিজাবের ফিতরী ও আধ্যাত্মিক দৃষ্টিকোণকে অসাধারণভাবে তুলে ধরেছেন। তাঁর মতে, শুধুমাত্র শরীর ঢাকার নামই হিজাব নয়। শরীরকে আবৃত করার পাশাপাশি হিজাব একইসাথে রবের নিকটবর্তী কীভাবে হবো,সেই বিষয়টিও শিক্ষা দেয়। তাঁর ভাষায়ঃ
ان الحجاب لباس معنوى يكشف عن اداب التقرب الي الله
অর্থাৎ, “হিজাব হলো আধ্যাত্মিক একটি পোশাক। আমরা কীভাবে আল্লাহর নিকটবর্তী হবো, হিজাব আমাদেরকে সেই শিক্ষা দিয়ে থাকে।”
আল মাফাহিমুল আখলাকিয়্যা নামে দুই খণ্ডের আরও একটি গ্রন্থ রয়েছে।
যুগের গাজ্জালী খ্যাত মহান এই মনীষীর চিন্তা ও দর্শনকে বুঝে আল্লাহ আমাদের কাজ করার তৌফিক দান করুন। আমীন।
অনুবাদঃ বুরহান উদ্দিন আজাদ।