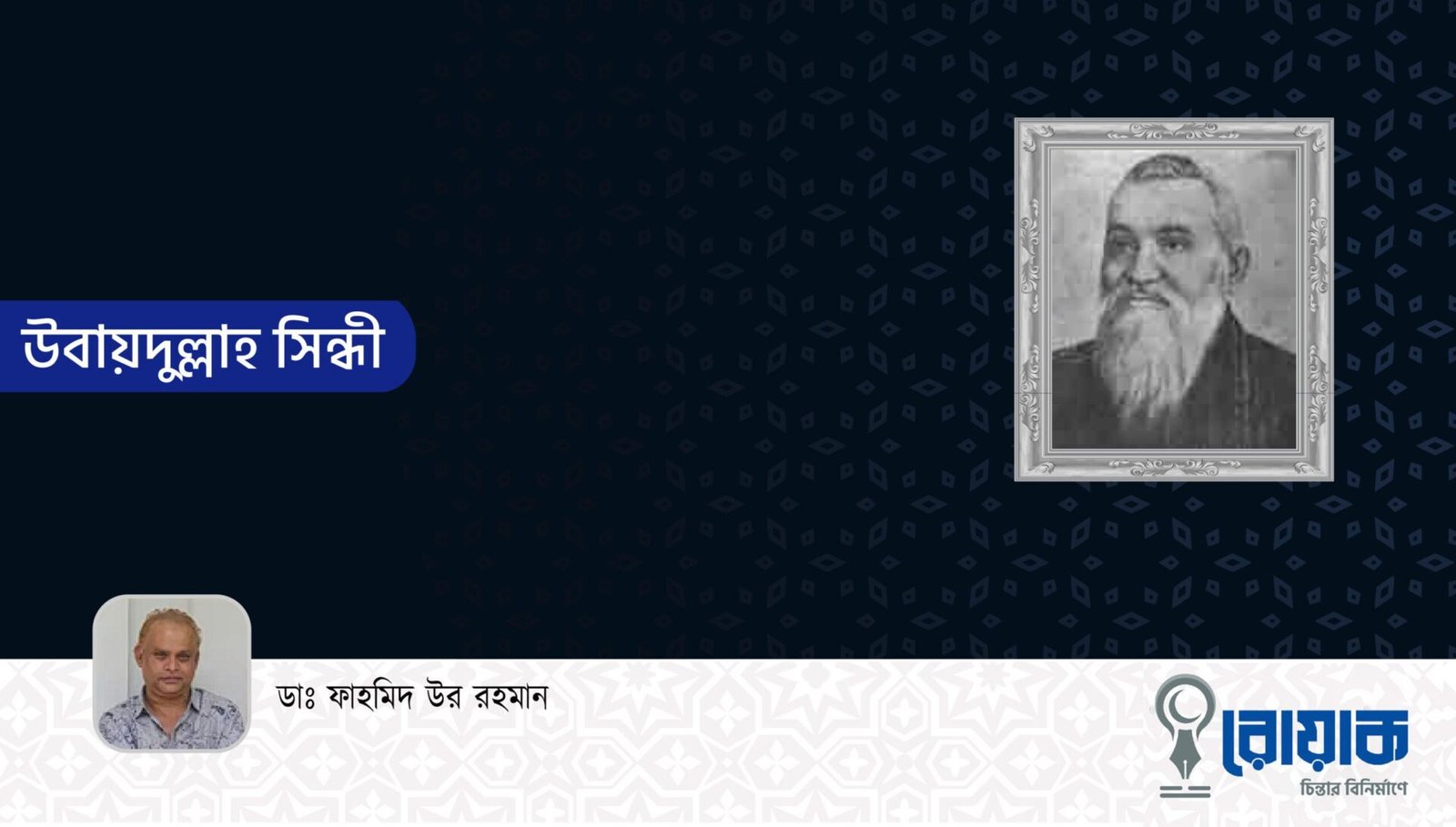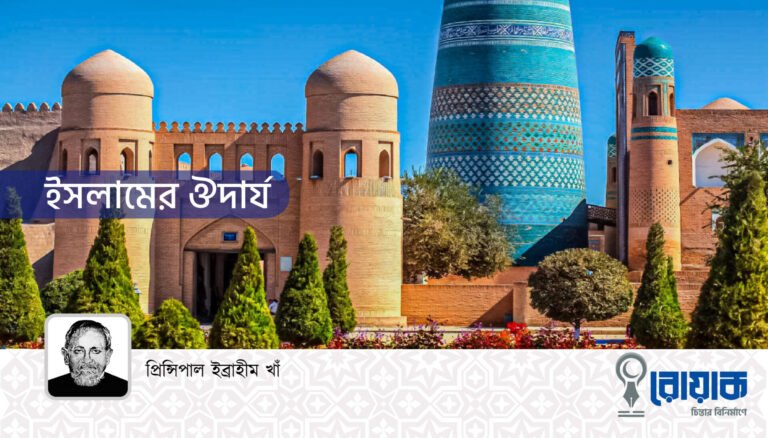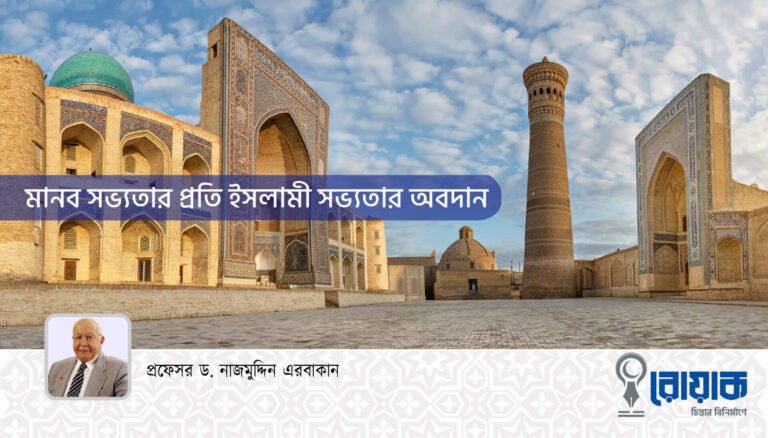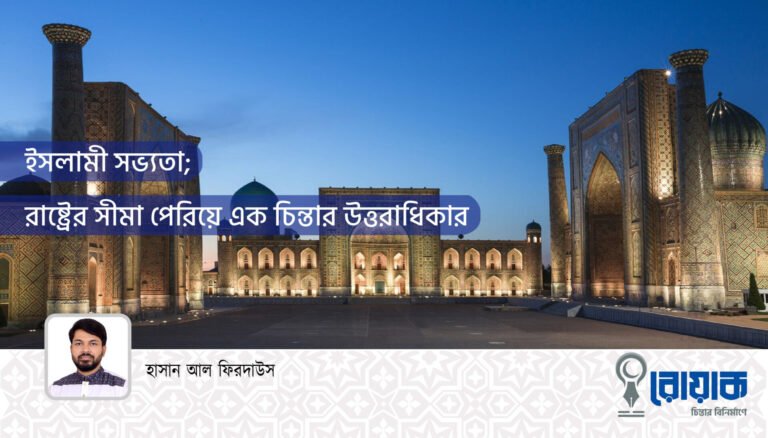এক.
ঔপনিবেশিক ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে আলেমদের লড়াই এক বিপ্লবী ঘটনা। এই বিপ্লবের অন্যতম সূতিকাগার ছিল দেওবন্দ। সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে দেওবন্দের আলেমরা যেমন নৈতিক ও দার্শনিকভাবে দাঁড়িয়েছিলেন, তেমনি তারা এক সশস্ত্র যুদ্ধেও অবতীর্ণ হয়েছিলেন। এরা একদিকে ছিলেন প্রবলভাবে ধর্মনিষ্ঠ, অন্যদিকে বিপ্লবী। ভারতবর্ষের মানুষের মুক্তি ও স্বাধীনতার জন্য এরা জান বাজী রেখেছেন, শহীদ হয়েছেন, দ্বীপান্তর-নির্বাসনে গেছেন এবং দেশান্তরী হয়েছেন । দেওবন্দের সন্তান উবায়দুল্লাহ সিন্ধীকে বলা যায় মুসলিম এম এন রায় ।
বিপ্লবী ও ভাবুক এম এন রায় যেমন করে ভারতবর্ষের মুক্তি ও স্বাধীনতার জন্য দেশ থেকে দেশে ছুটেছেন বিপ্লবের জন্য দূরান্তরে পাড়ি জমিয়েছেন, সবশেষে বিশ্ব মানুষের মুক্তির লক্ষকে আমৃত্যু স্থির হিসেবে নিবদ্ধ করেছেন। মওলানা উবায়দুল্লাহ সিন্ধীও ছিলেন তাই। এম এন রায় প্রথম জীবনে ছিলেন। সন্ত্রাসবাদী-বিপ্লবী, বিদেশে যেয়ে তিনি কমিউনিজমে দীক্ষা নেন, সবশেষে তিনি পরিণত হন রেডিকাল হিউম্যানিস্টে। উবায়দুল্লাহ সিন্ধী প্রথমদিকে ছিলেন প্যান ইসলামিক বিপ্লবী।
মওলানা উবায়দুল্লাহ সিন্ধীর সাথে এম এন রায়ের সাক্ষাত হয়েছিল এবং তাদের মধ্যে মতানৈক্যও ছিল। সিন্ধী কমিউনিজমের লা দ্বীনিয়াত- ধর্মহীনতাকে গ্রহণ করেননি। তবে এর অর্থনৈতিক মুক্তির ধারণা তার কাছে চমকপ্রদ মনে হয়েছিল। কমিউনিজমের অর্থনৈতিক বিষয়ক ভাবনা পরবর্তীকালে সিদ্ধীর চিন্তাভাবনাকে বিপুলভাবে প্রভাবিত করেছিল। শাহ ওয়ালিউল্লাহর অর্থনৈতিক ভাবনার সাথে কমিউনিজমের অর্থনৈতিক ভাবনার সমন্বয় করে তিনি তার নতুন ডিসকোর্স তৈরি করেছিলেন।
উবায়দুল্লাহ সিন্ধী তার আত্মচরিতে লিখেছেন ১৮৭২ সালের ১০ মার্চ পাঞ্জাবের শিয়ালকোট (বর্তমান পাকিস্তান) জেলার চেপানওয়ালি গ্রামে এক শিখ পরিবারে তার জন্ম। জন্মের চার মাস আগে তার পিতা রামসিং এবং জন্মের দু বছর পর পিতামহ যশপত রায় পরলোকগমন করেন। এরপর সিদ্ধীর মা মাতুলালয়ে চলে আসেন এবং মাতামহের মৃত্যু অবধি সিন্ধী তার স্নেহাচ্ছায়ায় বড় হতে থাকেন। এরপর সিন্ধী চলে যান ডেরাগাজী খান জেলার জামপুরে মামার বাড়িতে এবং এখানকার উর্দু মডেল স্কুলে তার লেখাপড়ার শুরু। এই জামপুর স্কুলে অধ্যয়নের ব্যাপারে বলেন-অতঃপর ইসলামের আকর্ষণে আমি গৃহত্যাগ করি।
এ সময় তার এক স্কুল পড়ুয়া বন্ধু তাকে মালের কোটলার সদ্য ইসলামে দীক্ষিত মওলানা উবায়দুল্লাহর লেখা ‘তুহফাতুল হিন্দ’ বইটি পড়তে দেয়, যা তাকে চমৎকৃত করে। এরপরে তিনি পড়েন শাহ ইসমাইল শহীদের ‘তাকবিয়াতুল ইমান’ ‘ও ‘আহওয়ানুল আখিরাত’ নামের দুটি কিতাব। এ কিতাব পাঠ করে তিনি ইসলামের তওহীদ সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান লাভ করেন। ১৮৮৭ সালে ইসলামের প্রতি তার দুর্নিবার আকর্ষণ এই ধর্ম কবুলের ভিতর দিয়ে পূর্ণতা পায়। ঐ বছরই তিনি সিন্ধুর উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন এবং ভাংচুরী শরীফ (মোটকি জেলা, সিন্ধু) ও দীনপুর শরীফের (রহিম ইয়ার খান জেলা, পাঞ্জাব) মাদরাসায় উপস্থিত হন । এ সময় তিনি ভাকুর্তী শরীফের আলেমে দ্বীন হাফিজ মোহাম্মদ সিদ্দিকের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। যদিও পরে তিনি আরো অনেকের আধ্যাত্মিক শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন।
১৮৮৯ সালে উবায়দুল্লাহ সিন্ধী দেওবন্দের দারুল উলুম মাদরাসায় ভর্তি হন। এবং এখানে সরাসরি মওলানা মাহমুদ আল হাসান, যিনি শাইখুল হিন্দ হিসেবে পরিচিত ও রশিদ আহমদ গঙ্গোহীতে শিক্ষক হিসেবে পান। এ সময় তিনি আরবি ভাষা, তাফসির, হাদিস, ফিকাহ (ইসলামী আইন), ফালসাফা (দর্শন) ও মানতেকে (যুক্তিবিদ্যা) প্রকৃত জ্ঞান অর্জন করেন। একই সময় তিনি দিল্লীর বিখ্যাত সুখী বুদ্ধিজীবী শাহ ওয়ালিউল্লাহর লেখালেখির সংস্পর্শে আসেন এবং পরবর্তীকালে সিন্ধীর নানা বৈচিত্র্যময় জীবনে শাহ ওয়ালিউল্লাহর চিন্তাভাবনা তার বিপ্লবী ডিসকোর্স নির্মাণে বড় ভূমিকা রাখে।
১৮৯১ সালে মওলানা সিন্ধী দেওবন্দের গ্রাজুয়েট হন এবং সেখান থেকে সিন্ধুর সুকুরে চলে আসেন। এরপরে শুরু হয় তার শিক্ষকতার জীবন এবং আমরোট শরীফ মাদরাসায় পড়ানোর কাজ শুরু করেন। ১৯০১ সালে সিন্ধুর গোথ পীর ঝান্ডায় তিনি দারুল ইরশাদ নামে একটি মাদরাসা গড়ে তোলেন। এটির সাথে তিনি সাত বছর যুক্ত ছিলেন। শিক্ষকতা ও ধর্মপ্রচারে মওলানা উবায়দুল্লাহ জীবনের বিপুল সময় সিন্ধুতে কাটিয়ে দেন এবং এটিকে তিনি নিজ গৃহ বানিয়ে ফেলেন।
এই কারণে তার নামের শেষে কোনো এক অবলীলায় সিদ্ধী শব্দটি যুক্ত হয়ে যায় । ১৯০৯ সালে তিনি সিন্ধু ত্যাগ করেন এবং মওলানা মাহমুদ আল হাসানের আমন্ত্রণে দেওবন্দে প্রত্যাবর্তন করেন। গুরু-শিষ্যের এই সম্মিলনে ভারতবর্ষের ইতিহাসে এক বিপ্লবী অধ্যায়ের উন্মেষ ঘটে এবং সিন্ধী তার শিক্ষকতার নিভৃত জীবন ত্যাগ করে বিপ্লবী জীবনের এক রোমাঞ্চকর অধ্যায়ে প্রবেশ করেন।
১৮৫৭ সালের বিদ্রোহ পরবর্তী সময় ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা যখন মুসলমানদের সবরকম প্রতিরোধ গুড়িয়ে দেয় সেই হতবিহ্বল অবস্থায় বিপ্লবে অংশগ্রহণকারী আলেমরা ভারতবর্ষে ইসলামের নৈতিক শিক্ষাকে টিকিয়ে রাখার জন্য ১৮৬৭ সালে এই মাদরাসার গোড়াপত্তন করেন। প্রথম দিকে এটি একটি অরাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে উঠলেও মওলানা মাহমুদ আল হাসানের নেতৃত্বে এটি তার বিপ্লবী চরিত্র ফিরে পায় এবং ভারতের রাজনীতিতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখে।
শুরু মাহমুদ আল হাসানের উদ্যোগে এ সময় জমিয়াতুল আনসার নামে একটি সংগঠন গড়ে ওঠে। সিন্ধী এটির সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব নেন এবং ভারতবর্ষ জুড়ে মওলানা মাহমুদ আল হাসানের প্রাক্তন ছাত্রদের এই সংগঠনের পতাকাতলে সংঘবন্ধ করার চেষ্টা করেন । পিটার হারডি লিখেছেন, সিন্ধী নিজেই। এই সংগঠন খাড়া করেছিলেন এবং এটির অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল দেওবন্দ ও আলীগড় স্কুলের মধ্যকার সম্পর্ক বৃদ্ধি করা।
ভারতকে ঔপনিবেশিক শাসনমুক্ত করার সিন্ধীর বিপ্লবী আইডিয়া ও গুপ্ত কার্যক্রমে দেওবন্দ মাদরাসা কর্তৃপক্ষ বিচলিত হন এবং সন্দেহ করতে থাকেন তাদের উপর না জানি কোনো সরকারি দলন নেমে আসে। এই কারণে দেওবন্দ কর্তৃপক্ষের সাথে তার মতান্তর ঘটে। গুরু মাহমুদ আল হাসানের পরামর্শে সিন্ধী দিল্লীতে চলে আসেন এবং এখানে তিনি নাজারাত- আল মাআরিফ আল কুরানিয়া নামে একটি মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন, যার উদ্দেশ্য ছিল ইংরেজি শিক্ষিত মুসলমানদের ধর্মীয় শিক্ষা দেয়া। এ কাজে তাকে সহযোগিতা করেন বিখ্যাত দেশনেতা নওয়াব ভিকারউল মুলক, হাকিম আজমল খান ও ডাঃ মোখতার আহমদ আনসারী। ডাঃ আনসারী সিন্ধীকে মওলানা মোহাম্মদ আলী ও মওলানা আবুল কালাম আজাদের সাথে পরিচয় করিয়ে দেন এবং তিনি রাজনীতিতে আরো সক্রিয় হয়ে ওঠেন । এই নতুন ভূমিকার জন্য মাহমুদ আল হাসানের সাথে তার যোগসূত্র মোটেই ছিন্ন হয়ে যায়নি । বরং প্রথম মহাযুদ্ধের প্রাক্কালে যখন ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান আর্মি বিভিন্ন ফ্রন্টে যুদ্ধ করতে যায় মওলানা মাহমুদ আল হাসানসহ দেওবন্দের কোনো কোনো আলেম মনে করলেন সাম্রাজ্যবাদ উৎখাতের এই হচ্ছে উৎকৃষ্ট মুহূর্ত । এই সন্ধিক্ষণে গুরুর সাথে সিন্ধীর সম্পর্ক আরো নিবিড় হয়ে ওঠে। মাহমুদ আল হাসান তার ছাত্রদের দ্বারা পাঠান উপজাতীয়দের ব্রিটিশের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে উদ্বুদ্ধ করেন। ১৯১৫ সালে সিন্ধীকে আফগান সহযোগিতা প্রাপ্তির জন্য কাবুলে প্রেরণ করা হয় যাতে আফগান বাদশাহ যথাসময়ে ভারত আক্রমণ করে ব্রিটিশ বাহিনীকে সীমান্তে ব্যস্ত রাখতে পারে। অন্যদিকে মাহমুদ আল হাসান ব্রিটিশের চোখ ফাঁকি দিয়ে নিজে হিজাজে পৌঁছেন। হিজাজ তখন ছিল তুরস্কের শাসনাধীন। শাইখুল হিন্দ তার পরিকল্পনা নিয়ে হিজাজের গভর্নর গালিব পাশা ও পরে তুরস্কের যুদ্ধ মন্ত্রী আনোয়ার পাশার সাথে বৈঠক করেন এবং উভয়ের মাঝে সর্বাত্মক সহযোগিতা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। শাইখুল হিন্দ আনোয়ার পাশাকে দিয়ে আফগান সরকারের উদ্দেশ্যে একটি পত্র লিখিয়ে নেন। তাতে লেখা ছিল ‘আফগান সরকারের সম্মতি থাকলে ১৯১৭ সালের ১৯ ফেব্রুয়ারি তুর্কি বাহিনী আফগান সীমান্তের মধ্যদিয়ে ব্রিটিশ ভারত আক্রমণ করবে এবং সাথে সাথে ভারতের অভ্যন্তরেও বিদ্রোহ ঘটবে ।
পত্রটি আফগানিস্তানে অবস্থানরত সিন্ধীর কাছে পৌঁছানো হয়। তার নেতৃত্বে কাবুলে উপস্থিত অন্যান্য ভারতীয় নেতারা আফগান বাদশাহ হাবিবুল্লাহর সাথে সাক্ষাত করেন। বাদশাহ ছিলেন দোদুল্যমান চরিত্রের। তিনি বিষয়টি ভালভাবে গ্রহণ করেননি। তবে পরিস্থিতির চাপে তিনি ভারতীয়দের সাথে এক চুক্তিতে আবদ্ধ হন । মওলানা সিন্ধী ও আমীর নসরুল্লাহ খান চুক্তির বিষয়বস্তু ও ভারত আক্রমণের তারিখ আরবিতে তরজমা করেন। এরপর একজন দক্ষ কারিগর দ্বারা একটি রেশমী রুমালের উপর সেই আরবি ভাষ্য সুতার সাহায্যে অংকিত করে মক্কায় অবস্থানরত শাইখুল হিন্দের কাছে পৌছানোর ব্যবস্থা করেন, যাতে ব্রিটিশ বাহিনীর চোখ ফাঁকি দিয়ে খবরটি নির্বিঘ্নে পৌঁছানো যায়। একজন কাপড় ব্যবসায়ীর মাধ্যমে সিন্ধুর শায়খ আবদুর রহীমের কাছে রেশমী রুমালরূপী এ চিঠিটি পাঠানো হয় যাতে হজ্বে গিয়ে তিনি তা শাইখুল হিন্দের হাতে পৌঁছে দেন । উল্লেখ্য, শায়খ আবদুর রহীম ছিলেন বিখ্যাত কংগ্রেস নেতা আচার্য কৃপালনীর ভাই, যিনি উবায়দুল্লাহ সিন্ধীর হাতে ইতিপূর্বে ইসলাম কবুল করেছিলেন।
অন্যদিকে নতজানু চরিত্রের অধিকারী বাদশা হাবিবুল্লাহ আর্থিক সুবিধার বিনিময়ে এই গোপন তথ্য ইংরেজদের কাছে সরবরাহ করেন। ফলে গোয়েন্দা পুলিশ শায়খ রহিমের বাড়ি তল্লাশী চালিয়ে রেশমী রুমালরূপী পত্রটি উদ্ধার করে। এভাবে ইংরেজ বিরোধী এই কার্যক্রম ফাঁস হয়ে যায়। শুরু হয় নেতাকর্মীদের ধরপাকড়। ইতিমধ্যে ইংরেজের মদদপুষ্ট শরীফ হুসাইন হিজাজে তুর্কি শাসনের অবসান ঘটিয়ে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন। শরীফ হুসাইন শাইখুল হিন্দকে তুর্কিদের বিরুদ্ধে তার খেলাফতের দাবির পক্ষে ফতোয়া দেয়ার জন্য চাপ দেন। শাইখুল হিন্দ শরীফকে স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দেন কুরআন শরীফের কোথাও নেই কুরাইশ বংশের কাউকে খলিফা মনোনীত করতে হবে। এতে শরীফ ক্রুদ্ধ হয়ে শাইখুল হিন্দকে ইংরেজদের হাতে তুলে দেন । তারা তাকে ভূমধ্যসাগরীয় দ্বীপ মাল্টায় নিয়ে বন্দী করে রাখে। এ ঘটনাটি স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে রেশমি রুমাল আন্দোলন, ১৯১৬ (Silk letter movement, 1916) হিসেবে পরিচিতি পেয়েছে।
এটি একটি রুদ্ধশ্বাস গোয়েন্দা কাহিনীর মতই মনে হয় যদিও এই অভিযানের ফলাফল তাৎক্ষণিকভাবে শূন্যই ছিল। কিন্তু কথা হচ্ছে দেওবন্দের এই দুই শীর্ষ আলেমের লক্ষ্যের প্রতি অসাধারণ সততা ও আন্তরিকতা এবং ঔপনিবেশিক শক্তির নিয়ন্ত্রণ থেকে ইসলামকে মুক্ত করার অগ্নিময় ইচ্ছা প্রশ্নোধ হলেও তারা সমকালীন বিশ্ব রাজনীতির জটিল আবর্তকে নিখুঁতভাবে অনুসরণ করতে পারেননি এবং এই ধরনের একটি আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্র কার্যকর করার অভিজ্ঞতাও তাদের ছিল না। উপর্যুপরি ধূর্ত বাদশাহ হাবিবুল্লাহর রাজনৈতিক কূটকৌশল সিন্ধী ধরতে পারেননি। পান ইসলামিক ঐক্যে হাবিবুল্লাহর আস্থা ছিল না এবং তিনি নিজেও ছিলেন ইংরেজের মোসাহেব ।
যাই হোক, রেশমী রুমাল আন্দোলন ব্যর্থ হওয়ার পর ব্রিটিশ সরকারের চাপে আফগান সরকার সিন্ধীর রাজনৈতিক তৎপরতা নিষিদ্ধ করে এবং কিছু সময়ের জন্য তাকে বদখশান দুর্গে আটক করে রাখে। আন্দোলনের ব্যর্থতা এরপর তাকে দীর্ঘ দুই দশকের প্রবাস জীবনের পথে নিয়ে যায়। এটি তার জন্য এক ধরনের উপকারই হয়েছিল। কারণ তিনি দেশ বিদেশ ঘুরেছিলেন। আন্তর্জাতিক রাজনীতির ধরন-ধারণের সাথে তার যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছিল পাশাপাশি সমকালীন রাজনৈতিক মতাদর্শ ও অর্থনৈতিক ধ্যানধারণা সম্বন্ধে তার একটা পরিচয় হয়। তিনি আফগানিস্তানে মোট সাত বছর কাটান (১৯১৫-২২) এবং পরবর্তীতে মক্কায় থাকা অবস্থায় কাবুল জীবনের ইতিকথা লেখেন ‘কাবুল মেই সাত সাল’ নামে । বাংলায় এর তরজমা হয়েছে ‘মওলানা ওবায়দুল্লাহ সিন্ধীর রোজনামচা’ নামে । এই সাত বছরে তিনি ব্রিটিশ প্রভাবিত আফগান সরকারের বিভিন্ন নেতৃপর্যায়ের লোকের সাথে কাজ করেছিলেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় কাবুল ‘এশিয়ার সুইজারল্যান্ড’ হিসেবে পরিচিতি পেয়েছিল যেখানে বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিরা একত্রিত হয়ে এটিকে আন্তর্জাতিক রাজনীতির কেন্দ্রে পরিণত করেছিলেন। আফগান রাজনীতিকদের সাথে মেলামেশার সূত্রেই তার ভাবান্তর হয়েছিল এবং তার প্যান ইসলামিক চিন্তায় ধাক্কা লেগেছিল। তিনি নবতর পরিস্থিতিতে বুঝতে চেষ্টা করেন তৃষ্ণগত জাতীয়তাবাদের বাস্তবতা। তিনি এটাও ভাবতে থাকেন আফগান ও ভারতীয় মুসলমানরা ধর্মে এক হলেও ভূখণ্ডগতভাবে পৃথক জাতি কারণ একজন আরেকজনের অধীনে কখনোই থাকতে চাইবে না ।
ভারত ত্যাগের পূর্বে তার প্যান ইসলামিক ভাবনাটা ছিল প্রকাণ্ড কিন্তু যখন বিশ্বযুদ্ধের মধ্যে আরব, তুর্কি ও আফগানরা নিজেদের স্বার্থ ও প্রয়োজনকে ভিন্ন ভিন্নভাবে উঁচু করে ধরে, তখন তার প্যান ইসলামিক ভাবনা আহত হয়। তারও একটু একটু করে মন ঘুরতে থাকে। তার এই ভাবান্তরের পিছনে দেওবন্দের আলেমদের পরবর্তী ভূমিকার একটা যোগসূত্র আছে। প্যান ইসলামিক ভাবনায় উদ্বুদ্ধ দেওবন্দের আলেমরাও পরবর্তীকালে জাতীয়তাবাদ প্রশ্নে মতান্তরে জড়িয়ে পড়েন । দেওবন্দের বিখ্যাত আলেম শাইখুল হিন্দের ছাত্র হোসেন আহমদ মাদানী জাতীয়তাবাদ প্রশ্নে আল্লামা ইকবালের সাথে তীব্র বাদানুবাদে লিপ্ত হয়েছিলেন- এটা অনেকেরই জানা। শায়খুল হিন্দের আর এক ছাত্র শাব্বির আহমদ উসমানী ভূখণ্ডগত জাতীয়তাবাদ প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। ভূখণ্ডগত জাতীয়তাবাদ প্রশ্নে দেওবন্দ শেষ পর্যন্ত যে জায়গায় থাকুক না কেন মওলানা সিন্ধী অবশ্য তার অবস্থানকে কখনো এক জায়গায় স্থির রাখেননি ।
প্যান ইসলামিক ভাবনা ছেড়ে সিন্ধী গদর পার্টি ও ভারত-জার্মান-তুর্কি মিশনের সহযোগিতায় কাবুলে ডিসেম্বর ১৯১৫তে একটি প্রবাসী সরকার গড়ে তোলেন। গদর পার্টি প্রবাসী ভারতীয়দের দ্বারা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়ায় ১৯১৩, এপ্রিলে প্রতিষ্ঠিত হয়। এর মূল উদ্যোক্তা ছিলেন হরদয়াল। এই সংগঠনটির পত্রিকার নাম ছিল গদর- বিদ্রোহ। এর উদ্দেশ্য ছিল ভারতকে ঔপনিবেশিক শাসন থেকে মুক্ত করা।
এই প্রবাসী সরকারের প্রেসিডেন্ট হন রাজা মহেন্দ্র প্রতাপ, প্রধানমন্ত্রী হন। বরকতুল্লাহ ভূপালী, সিন্ধী হন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী প্রবাসী সরকার আফগান সরকারের সাথে কথা বলতো এবং রাশিয়া,তুরস্ক ও জাপানে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে সাহায্য করার জন্য মিশন পাঠায়। কিন্তু এই মিশন আকাঙ্ক্ষিত সফলতা অর্জন করতে পারেনি। ১১ হিন্দু ও অমুসলিমদের নিয়ে তার এই নতুন রাজনীতি তার চিত্ত পরিবর্তনের লক্ষণ অবশ্যই । যদিও তিনি নিজেই এই রাজনীতির মধ্যেও সাম্প্রদায়িকতার ভূত দেখেছিলেন বলে উল্লেখ করেছেন । তবুও বলতে হবে তুর্কি খলিফার বিরুদ্ধে আরবদের বিদ্রোহ তার মন ভেঙে দিয়েছিল এবং জিয়াউল হাসান ফারুকীর ভাষায় : a rude shock to Sindhi’s Islamism.
১৯১৯ সালে ব্রিটিশের হাত থেকে ভারতকে মুক্ত করার জন্য তিনি জুনদুল্লাহ বা জুনুদ-ই-রব্বানিয়া (Muslim Salvation Army) বলে ১ লাখ সদস্যের একটি আধা সামরিক বাহিনী গড়ে তোলেন, যেখানে তিনি সুফীদেরও অন্তর্ভুক্ত করেন। ১৪ কিন্তু আফগান শাসক হাবিবুল্লাহর পরামর্শে ভারতকে মুক্ত করার জন্য তিনি হিন্দুদের সহযোগিতার কথা ভাবতে থাকেন। এমনিভাবে তিনি ১৯১৯ সালে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসে যোগ দেন, কাবুলে এর একটি শাখা গড়ে তোলেন এবং নিজেই এর প্রেসিডেন্ট হন। পরবর্তীতে তিনি এটিকে ডাঃ মোখতার আহমদ আনসারীর সহযোগিতায় মূল কংগ্রেসের সাথে সম্পৃক্ত করেন। ভারতের বাইরে এটিই কংগ্রেসের প্রথম শাখা ।
দুই.
কাবুলে প্যান ইসলামিক বিপ্লবী থেকে ন্যাশনালিস্টে পরিবর্তিত সিন্ধী ১৯২২ সালে মস্কো যান এবং সেখানে আট মাস অবস্থান করেন। অধ্যাপক আজিজ আহমদ তার সম্পর্কে লিখেছেন : দক্ষিণ এশিয়ার তিনি একমাত্র রাজনীতিবিদ যিনি কমিউনিজমকে এর সূচনাকালেই বুঝবার চেষ্টা করেছিলেন : the only political thinker of any considerable caliber to come directly in contact with Russian Communism at an early stage.
এই সময়ে তিনি জারতন্ত্রের ভগ্নাবশেষ থেকে নতুন রাশিয়ার অভ্যুত্থান দেখেন এবং খুব কাছে থেকে বলশেভিক বিপ্লবের রূপান্তরগুলো বুঝতে চেষ্টা করেন। সিন্ধী এ সময় সমাজতন্ত্র নিয়ে পড়াশুনাও করেন। পরবর্তীকালে সিদ্ধা স্বীকার করেছেন তার সমাজতন্ত্র অধ্যয়ন …enabled him to defend his religious movement, which was a branch of the philosophy of Shah Wali-Allah, against the onslaught of atheism and anti-religious trend of the time.
কমিউনিজম সম্পর্কে এমন কথাও তিনি বলেছিলেন : Communism is not a natural law system but rather is a reaction to oppression, the natural law is offered by Islam
ইসলাম ও কমিউনিজমের পারস্পরিক সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য, একই সাথে একালে তার সম্ভাব্যতা নিয়ে তিনি মস্কোতে বসে রীতিমত আলোচনা করতেন। তিনি রুশ প্রধানমন্ত্রী চেচরেনের সাথে দেখা করে ভারতকে ব্রিটিশমুক্ত করার জন্য সাহায্য চান। ১৯২৩ সালে সিন্ধী রাশিয়া থেকে তুরস্কে যান এবং ইস্তাম্বুলে তিন বছর কাটান। তুর্কি খেলাফত ভেঙে কামাল পাশার উত্থানকে তিনি এ সময় কাছে থেকে দেখেন। তিনি এখানকার রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সাথে কথা বলেন এবং প্রধানমন্ত্রী ইসমত পাশার সাথে দেখা করেন।
ইস্তাম্বুলে বসে সিদ্ধী তার রাজনৈতিক মতাদর্শকে নতুন করে সংহত করেন এবং ন্যাশনালিজম ছেড়ে ইসলামিক সোশালিজমের দিকে ঝুঁকতে থাকেন। এখানে বসে ১৯২৪ সালে তিনি তার রাজনৈতিক দল মহাভারত সর্বরাজ্য পার্টি গড়ে তোলেন। তিনি সভাপতি ও তার একজন ঘনিষ্ঠ সঙ্গী তুর্কি সেনাবাহিনীর সাবেক সদস্য জাফর হাসান আইবাক এই দলের সম্পাদক হন। ১৯২৬ সালে সিন্ধী তুরস্ক। ছেড়ে সৌদি আরবে চলে আসেন এবং মক্কায় তিনি সর্বমোট তের বছর কাটান। এখানে তিনি কুরআনের তাফসির করেন, হাদিসের উপর লেকচার দেন এবং শাহ ওয়ালিউল্লার ম্যাগনাম ওপাস হুজ্জাতাল্লাহ-আল-বালিগার আলোকে কুরআনের শিক্ষাকে ব্যাখ্যা করতে থাকেন । এছাড়া তিনি কিছু বই ও প্রবন্ধও লেখেন। তার এই দীর্ঘ পঠন-পাঠনের ফলেই পরবর্তীকালে বেরিয়ে আসে শাহ ওয়ালিউল্লাহ আওর উনকি সিয়াসি তাহরীক – শাহ ওয়ালিউল্লাহ ও তার রাজনৈতিক চিন্তাধারা নামক বিখ্যাত বই। এ সময় তিনি পুরো মুসলিম ইতিহাসকে পুনর্পাঠ ও পুনর্মূল্যায়ন করেন বিশেষ করে ভারতীয় ইতিহাসকে নির্মোহ সমালোচনা করেন। শেষ পর্যন্ত তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন শাহ ওয়ালিউল্লাহর শিক্ষাই আবার ইসলামী রেনেসাঁর সূচনা করতে পারে। দেশে ফেরার আগেই তিনি ‘যমুনা নরবদা সিন্ধ সাগর পার্টি’ নামে আরেকটি রাজনৈতিক দল খাড়া করেন । ১৯৩৯ সালে তিনি ভারতে ফিরে আসেন। তার এই দেশে প্রত্যাবর্তনকে একজন লেখক এভাবে বিশ্লেষণ করেছেন:
সিন্ধীর পরিকল্পনা অনুসারে এই রিপাবলিকগুলোতে সার্বজনীন ভোটাধিকারের কথা ছিল। কিন্তু মজার ব্যাপার হচ্ছে প্রত্যেক পেশা ও শ্রেণি তাদের নিজ নিজ প্রতিনিধি নির্বাচন করবে। তার মতে এই শ্রেণিগত প্রতিনিধিত্ব শ্রমিক শ্রেণির অধিকারকে সুরক্ষা দেবে।
সিদ্ধীর আর্থ সামাজিক কর্মসূচিগুলো ছিল আরো অভিনব। এগুলো হচ্ছে :
১. জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট সব ব্যবস্থাপনা ও প্রতিষ্ঠান জাতীয়করণ।
২. ব্যক্তিগত সম্পত্তির সীমা নির্ধারণ।
৩. ধনিক শ্রেণির উপর কর নির্ধারণ ৪ জমিদারী ও জোতদারী জাতীয়করণ । এখানে তিনি মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ রিপাবলিকে হযরত ওমর ও ইমাম আবু হানিফার উদাহরণ দিয়ে বলেছেন, জমিদারের জমি রাষ্ট্রকে ফিরিয়ে দিতে হবে এবং বর্গাদারী, ভাগচাষ প্রথার অবসান ঘটবে।
৫. প্রত্যেক কৃষক সেই পরিমাণ জমি রাখবে যা সে চাষ করার ক্ষমতা রাখে।
৬. সুদ নির্মূল হবে এবং শ্রমিকদের সুদমুক্ত ঋণ দেয়া হবে ।
৭. লেবার ইউনিয়নগুলো জাতীয়করণকৃত সম্পত্তি চালাবে এবং শ্রমিকরা লাভের একটি অংশ পাবে।
৮. শ্রমিক শ্রেণিকে বিনামূল্যে বাসস্থান ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হবে।
৯. মধ্যবর্তী স্তর পর্যন্ত শিক্ষাকে নিখরচা করা হবে।
১০. আন্তর্জাতিক বাণিজ্য কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে থাকবে। অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য সমবায় পদ্ধতিতে পরিচালনা করা হবে।
১১. কনফেডারেশনের অধীন রিপাবলিকের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের ধর্ম স্ব স্ব রিপাবলিকের রাষ্ট্রধর্ম হবে । কিন্তু ধর্মের কারণে পার্টি ঘোষিত ও সামাজিক কর্মসূচি ব্যাহত হবে না।।
১২. তিনটি রিপাবলিকের পররাষ্ট্র, প্রতিরক্ষা ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের উপর কোনো নিয়ন্ত্রণ থাকবে না। এটি নিয়ন্ত্রণ করবে কেন্দ্রীয় ফেডারেল সরকার ।
১৩. এটি সাম্রাজ্যবাদ মোকাবেলার জন্য এশিয়ার ভিন্ন ভিন্ন জাতিকে নিয়ে এশিয়াটিক ফেডারেশন গড়ার পক্ষপাতী ছিল । সিন্ধী এই ফেডারেশনে রাশিয়াকেও অন্তর্ভুক্ত করতে চেয়েছিলেন ।
সিন্ধী তার প্রস্তাবিত এই দলে ধর্ম, বর্ণ, লিঙ্গ নির্বিশেষে সকলের অন্তর্ভুক্তির পক্ষে ছিলেন। তবে নিয়ম ছিল যে এই দলে প্রবেশ করবে তাকে অবশ্যই একজন গড়পড়তা কৃষকের জীবনমান গ্রহণ করতে হবে । সুতরাং অতিরিক্ত সম্পত্তি পার্টির হিসাবে জমা দিতে হবে। সিন্ধীর ভাষায় : Under our government, capitalist system may have no possibility of revival and out party programme may not be considered a vain display. or a political weapon.
এতে মনে হয় সিন্ধী এক ধরনের অর্থনৈতিক সমতা প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন । সামাজিক সমতা প্রতিষ্ঠার দিকেও তার নজর ছিল। এ কারণে তিনি হিন্দু সদস্যদের বর্ণবাদ অতিক্রম করে শুদ্রদেরকে ভ্রাতৃত্বের কাতারে নিয়ে আসতে বলেছিলেন । ভারত যেহেতু ছিল বহু ধর্মের দেশ এবং এখানে হিন্দুরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ তাই তৎকালীন পরিস্থিতিতে তিনি হিন্দু-মুসলিম মিশ্র জনসংখ্যা যেখানে আছে সেখানে গরু কুরবানী নিষিদ্ধ করার পক্ষে ছিলেন। তার মতে এতে দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে ঐক্যের পথ প্রশস্ত হবে। এখানে বিশেষভাবে বলতে হয় উবায়দুল্লাহ সিন্ধীর ব্যাপারে বলতে হয়, He had left India as a firebrand agitator and an organizer of revolutionary activities; he came back as a thinker.
জীবনের বাকি সময় তিনি গভীর সংযম ও মিতব্যায়িতার মধ্যে কাটান, বিশেষ করে শাহ ওয়ালিউল্লাহর দর্শন ও চিন্তাকে প্রচার করেন। ১৯৪৪ সালের ২২ আগস্ট তিনি লাহোরে ইন্তিকাল করেন। কংগ্রেস নেতা মওলানা আবুল কালাম আজাদ জানিয়েছেন, ব্রিটিশরা এই বিপ্লবী মওলানাকে বিষপ্রয়োগে হত্যা করেছিল। শুধু তাই নয় এই মওলানাই ভারতবর্ষের আজাদীর জন্য সুভাষ চন্দ্র বসুকে ভারতের বাইরে জার্মানী এবং সেখান থেকে জাপানে পাঠিয়েছিলেন, একই সাথে প্রবাসে তার সব রকমের সাহায্যের ব্যবস্থা করেছিলেন।
উবায়দুল্লাহ সিন্ধীকে বলা হয় ‘ইমাম-ই-ইনকিলাব’-বিপ্লবের পুরোহিত। কারণ তার রাজনৈতিক বিশ্বাস ও দর্শন আজীবন পরিবর্তন ও বিপ্লবের মধ্যেই ঘুরপাক খেয়েছে এবং বিপ্লবী ঘটনা দেখতে দেখতেই তিনি জীবনের বিপুল সময় কাটিয়ে দিয়েছেন। বলশেভিক বিপ্লব, আতাতুর্কের অভ্যুত্থান, সৌদি আরবে ওহাবীদের উত্থান তার চোখের সামনেই ঘটেছিল। এগুলো সমন্নাত্তরে তার দর্শন নির্মাণে বড় ভূমিকা রেখেছে। সর্বোপরি শাহ ওয়ালিউল্লাহর চিন্তাই তার কাছে বাতিঘর হিসেবে কাজ করেছে। তার প্রবাস জীবনের অভিজ্ঞতা বিশ্বব্যাপী পরিবর্তন ও চ্যালেঞ্জকে বুঝতে সাহায্য করেছে এবং ভারতীয় সমস্যা সমাধানে তাকে একটি সিদ্ধান্তে আসতে উদ্বুদ্ধ করেছে। তিনি দেশে ফিরেছিলেন চমকপ্রদ, অভিনব ও সৃষ্টিশীল ধারণা নিয়ে। একারণেই তাকে বলা হয়েছে : One of the most intersting and romantic personalities of the group of early Indian revolutionaries.
তিন.
ভারতের তৎকালীন জটিল রাজনৈতিক ও সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতির উত্তরণে সিদ্ধী তার রাজনৈতিক দলের পক্ষ থেকে যে কর্মসূচি দিয়েছিলেন তা ছিল এরকম: ১. ভারতের পূর্ণাঙ্গ স্বাধীনতা, ২. স্বাধীন ভারতে কনফেডারেশন প্রকৃতির সরকার, ৩. মুসলমানসহ সব সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা, ৪. সরকারের মধ্যে শ্রমিক শ্রেণির প্রাধান্য, ৫. সামন্ততন্ত্র ও পুঁজিবাদের উচ্ছেদ, ৬. একটি বৃহত্তর এশীয় ফেডারেশন গঠন করে সাম্রাজ্যবাদ ও উপনিবেশবাদের মোকাবেলা।
সিন্ধী তার উপস্থাপিত ভবিষ্যত ভারতের সংবিধানকে বলেছিলেন : The Constitution of the Federated Republics of India। এটা নিরিক্ষা করলেই বুঝা যাবে তার রাজনৈতিক ও আর্থসামাজিক মতাদর্শসমূহ। তিনি ভারতীয় জাতীয়তাবাদীদের মতো এক জাতিতত্ত্বের ধারণাকে স্বীকার করেননি। তিনি ভারতকে উত্তর পশ্চিম, পূর্ব ও দক্ষিণ রিপাবলিক হিসেবে দেখতে চেয়েছিলেন। তিনি এ বিভাজন করেছিলেন ভাষা ও সংস্কৃতির ভিত্তিতে । এই তিনটি রিপাবলিক Central Government of the Federated Republics of India’র কাঠামোর মধ্যে কাজ করবে বলে তিনি প্রস্তাব করেছিলেন।
এই সংসদ ভৌগোলিক এলাকাভিত্তিক প্রতিনিধিত্বের ধারণা বাতিল করে এবং পেশা ও শ্রেণিভিত্তিক জনগণের ভিতর থেকে নির্বাচনের মাধ্যমে প্রতিনিধি নির্বাচনের কথা বলে। যাতে কিনা এক ধরনের শ্রমিক শ্রেণির প্রাধান্য থাকার ব্যবস্থা রাখা হয়। তবে আইন সভায় আনুপাতিক হারে কৃষক, শ্রমিক ও বুদ্ধিজীবী শ্রেণির প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থাও রাখা হয়, যাতে তাদের নিজস্ব কথাগুলো সঠিকভাবে উপস্থাপিত হতে পারে। কিন্তু এতে হুবহু মার্ক্সবাদীদের মতো শ্রমিক শ্রেণির একনায়কত্ব’ প্রতিষ্ঠার কথা ছিল না। সিন্ধী আনুপাতিক হারে পুঁজিপতি ও জমিদারদের প্রতিনিধিত্বকেও অনুমোদন করেছিলেন। কিন্তু সংখ্যায় যেহেতু তারা কম স্বাভাবিকভাবেই এই প্রস্তাবিত সংসদে শ্রমিক শ্রেণিরই আধিপত্য করার কথ ছিল । প্রকৃতপক্ষে তিনি মানুষের মর্যাদা ও সমতাকে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন এবং মানুষের কোনো অপমান তিনি সহ্য করতে পারেননি। একবার তিনি যুক্তি দেখিয়েছিলেন- A human being could not be a servant of another; though one could help others.
জাতীয়করণকৃত জমি ও শিল্পে যৌথ সামাজিক উৎপাদনের যে ধারণা তিনি দিয়েছিলেন তার মূলনীতি তিনি মুসলিম আইন ও ফিকাহ থেকেই পেয়েছিলেন বলে অনেকে মনে করেন। যদিও তার সমালোচকরা মনে করেন তিনি এই ভাবনা কমিউনিজম থেকে ধার করেছেন। তার পার্টির গঠনতন্ত্র চরিত্রের দিক দিয়ে কমিউনিস্ট পার্টির মেনিফেস্টোর হুবহু অনুলিপি ছিল না। কমিউনিস্ট পার্টি শ্রমিক শ্রেণির একনায়কত্বে সমাজের অন্যকোন শ্রেণি বা পেশার অধিকারে তারা বিশ্বাস করে না। সিন্ধী কিন্তু জমিদার, শিল্পপতি ও পুঁজিপতিদেরও প্রাপ্য দেয়ার পক্ষে ছিলেন। যদিও তারা সংখ্যায় খুবই কম । সরকারেও তাদের প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা রেখেছিলেন। তাছাড়া সমাজতন্ত্রী দেশগুলোর মতো উৎপাদনের ফলে প্রাপ্ত লাভ রাষ্ট্রের পরিবর্তে শ্রমিকদের পাওয়ার কথা ছিল। অধ্যাপক আজিজ আহমদ কমিউনিজমের সাথে সিন্ধীর চিন্তাভাবনার পার্থক্যটা এভাবে দেখিয়েছেন, The main difference between the communist and Islamic economic philosophies, according to Sindhi, is that while both agree that the process of the distribution of wealth should be ‘from each according to his ability’, Islam would prefer it to be ‘to each according to his need rather than to ‘cach according to his work. In other words Sindhi would like to see Islamic socialism on the lines of a Westem welfare state.
ভারতীয় জাতীয়তাবাদ প্রসঙ্গে কংগ্রেস ও হিন্দু মহাসভাপন্থীদের মতো তিনি ভারতকে একটি জাতির একটি রাষ্ট্র হিসেবে মনে করতেন না। তিনি ভারতীয় ঐক্যের মিথকে ভেঙে দিয়েছেন এবং বলেছেন ভারত হচ্ছে বহু জাতির দেশ। অবশ্য তিনি সংস্কৃতি ও ভাষাকে জাতিত্বের ভিত্তি করে একথা বলেছিলেন এবং এই চিন্তাভাবনা ও প্রস্তাবনায় শাহ ওয়ালিউল্লাহর প্রভাব স্পষ্ট। শাহ ওয়ালিউল্লাহ ছিলেন উপমহাদেশের মুসলিম সমাজের অন্যতম খ্যাতনামা দার্শনিক পণ্ডিত 1 সম্রাট আওরঙ্গজেবের ইত্তিকালের পর উপমহাদেশের মুসলিম শাসনের বুনিয়াদ ধ্বসে পড়ে। সর্বস্তরে মুসলমানের পতন আরম্ভ হয়। শাহ ওয়ালিউল্লাহ আপন সমাজের পতন রোধ করার জন্য বিশেষ তৎপর হন এবং তৎকালীন বিচারে একটি নতুন চিন্তার প্রবর্তন করেন। শাহ ওয়ালিউল্লাহ ঠিক প্রথাগত চিন্তাবিদ ছিলেন না । তিনি সেইকালে শুধু ভারতের রাজনৈতিক মুক্তির কথা ভাবেননি, এখানকার মানুষের আর্থিক ও সাংস্কৃতিক নিরাপত্তার কথাও ভেবেছিলেন। সিন্ধী শেষ জীবনে তার জাতীয়তাবাদী চিন্তাকে শাহ ওয়ালিউল্লাহর সামাজিক চিন্তাগুলোর সাথে সমন্বয় করেছিলেন বলে মনে হয় ।
শাহ ওয়ালিউল্লাহ তার হুজ্জাত আল্লাহ আল বালিগাতে লিখেছেন : পুঁজির বিকাশ হয় শ্রমের ফলে । তাই পুঁজির যথাযথ ব্যবহারের আগেই নতুনভাবে পুঁজি বিকাশের প্রয়োজন নেই । শাহ ওয়ালিউল্লাহ বিশেষ করে কৃষক, শ্রমিক ও বুদ্ধিজীবী শ্রেণির স্বার্থরক্ষার উপর জোর দিয়েছেন । তার মতে এই শ্রেণির উন্নতি প্রয়োজন । এদের উপর বেশি করারোপ করা উচিত নয় । তেমনি এদের কাজের সময়ও নির্দিষ্ট করা প্রয়োজন, যাতে তারা নৈতিক উন্নয়নের সময় পায়। জুয়া বন্ধ হওয়া উচিত । পুঁজিবাদীরা যদি কৃষক ও শ্রমিক শ্রেণির উপর বেশি করারোপ করে তাও বন্ধ হওয়া উচিত । কৃষক ও শ্রমিকদের পরিশ্রম অনুযায়ী বেতন দিতে হবে এবং তাদের সাথে নিয়োগকর্তার সম্পাদিত চুক্তিকে সম্মান দেখাতে হবে। বিলাসী জীবনধারা পরিত্যাগ করতে হবে, যাতে সমাজে সমতা প্রতিষ্ঠিত হয়।
রাজনৈতিক ব্যবস্থা সম্বন্ধে শাহ ওয়ালিউল্লাহ প্রস্তাব করেছিলেন স্বায়ত্তশাসিত কিন্তু শক্তিশালী ইউনিটের সহযোগে একটি আন্তর্জাতিক ব্লক গড়ে তোলার কথা । এছাড়া তিনি মনে করতেন সব ধর্মের তলায় যে মৌলিক সত্য আছে তার ভিতরে এক ধরনের ঐক্য আছে। সুতরাং সব ধর্মীয় নেতাদের শ্রদ্ধা করা উচিত। শাহ ওয়ালিউল্লাহর এই আর্থসামাজিক কর্মসূচিগুলো গভীরভাবে নিরিক্ষা করলে বুঝা যায় সিন্ধী তার চিন্তাভাবনা নির্মাণে এর থেকে অনেক কিছু ধার করেছিলেন। অধ্যাপক আজিজ আহমদ লিখেছেন : …the basis of Sindhi’s concept of an Islamic socialist theocracy is derived piecemeal from Wali-Allah.
সিন্ধীর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তিনি শাহ ওয়ালিউল্লাহর চিন্তাকে আধুনিক ভাষায় প্রকাশ করেছেন এবং সমকালীন সমস্যার সাথে এটাকে মিলিয়ে দেখেছেন । এটা করতে যেয়ে কমিউনিস্ট রাষ্ট্রের সংগঠন প্রক্রিয়াকেও তিনি কিছুটা ব্যবহার করেছেন। সিন্ধী তার রাজনৈতিক দর্শনে জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতার এক অপূর্ব সমন্বয় করেছিলেন। সর্বোপরি তিনি প্রথম একটি বিকল্প ও অভূতপূর্ব সংসদীয় ব্যবস্থা ও ফেডারেল রিপাবলিকের কথা বলেছিলেন। তখনকার সাম্প্রদায়িক রাজনীতির উত্তাপের মধ্যে এ ধরনের রিপাবলিকান ব্যবস্থা একটা উত্তম বিকল্প বলেই মনে হয় ।
জাতিত্বের ধারণার দিক দিয়ে তিনি ছিলেন স্থানভিত্তিক (space-bound) । এক্ষেত্রে তিনি পশ্চিমা চিন্তার মতো জাতিত্ব বিচারে ভৌগোলিক বাস্তবতাকে মনে রেখেছিলেন। তিনি মনে করতেন মুসলমানদের মধ্যেও নৃতাত্ত্বিক, সাংস্কৃতিক ও ভাষিক পার্থক্য রয়েছে । এই কারণে তার পার্টি ভারতকে একটি বহুজাতিক রাষ্ট্র হিসেবে ঘোষণা করেছিল । সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যের দিক দিয়ে চিন্তা করলে ভারত ছিল ইউরোপের মতই যেখানে ইংলিশ, ফ্রেন্স, জার্মান ও ইটালিয়ানরা ভিন্ন ভিন্ন জাতি হিসেবে স্বীকৃত । যদিও তিনি ভাষা ও সংস্কৃতিকে শেষ পর্যন্ত জাতিত্বের ভিত্তি ধরেছিলেন এবং সেই হিসেবে ভারতের কয়েকগণ্ডা জাতি রাষ্ট্র হিসেবে বিভক্ত হয়ে যাওয়ার কথা ছিল, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তিনি ভারতকে টুকরো টুকরো করতে চাননি এর সমাধান হিসেবে তিনি প্রত্যেকটি রিপাবলিকান ইউনিটকে যথেষ্ট পরিমাণ স্বাধীনতা ও স্বায়ত্তশাসন দিতে চেয়েছেন যা কিনা কেন্দ্রের আওতায় ঐক্যবদ্ধ থাকবে।তিনি অবশ্য বলেছেন, বিভিন্ন ধর্ম ও কমিউনিজমের মতো আদর্শ কখনো কখনো বিভিন্ন ভাষা ও সংস্কৃতির মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করতে পারে এবং এগুলোর চরিত্র জাতীয় নয়, আন্তর্জাতিক। সিদ্ধী মনে করতেন ইসলামের বিশ্বজনীনতা জাতি রাষ্ট্রের বিরোধী নয়, কিন্তু প্রত্যেক জাতিকেই বিশ্ব মানবতার অংশ হিসেবে দেখতে হবে ।
সিন্ধী সাম্রাজ্যবাদ প্রতিরোধের জন্য এশিয়াটিক ফেডারেশনের কথাও বলেছিলেন তিনি সাম্রাজ্যবাদকে বিভিন্ন দুর্বল দেশের জন্য সাধারণ শত্রু হিসেবে মনে করতেন এবং তার এই সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতার কৌশল হিসেবে এশিয়াটিক ফেডারেশন গড়ে তোলার ভাবনা একটি জাতীয়তাবাদ অতিক্রমকারী (Supra- Nationalist) চিন্তা বলেই মনে হয় অধ্যাপক আজিজ আহমদ লিখেছেন, সিন্ধীর যৌথ জাতীয়তাবাদী ধ্যান ধারণা ঠিক দেওবন্দের আলেমদের মতো ছিল না। এটি ছিল তার ভাষায় far more restricted।
সিন্ধীর চিন্তাভাবনা মওলানা আবুল কালাম আজাদ ও মওলানা হোসেন আহমদ মাদানীর থেকে পৃথক ছিল । ভারতের বিভিন্ন নৃতাত্ত্বিক ও ভাষিক গোষ্ঠী যেহেতু খুব সমৃদ্ধ ও বৈচিত্র্যময় ছিল তাই তাদেরকে নিয়ে ভিন্ন ভিন্ন জাতি রাষ্ট্র তিনি গড়তে চাননি । সুতরাং এর সমাধান হচ্ছে ভারতীয় স্বায়ত্তশাসিত প্রজাতান্ত্রিক ফেডারেশন গড়ে তোলা । এখানে এসে সিন্ধী জাতিত্বের প্রশ্নে ভারতীয় মুসলিম লীগ ও ভারতীয় কংগ্রেসের চিন্তাভাবনার এক ধরনের সমন্বয় করেছেন বলে মনে হয় এবং এই জন্য তার চিন্তাভাবনাগুলোকে কিছুটা বিপরীত ধর্মী হিসেবেই ধরা যেতে পারে। এছাড়া তার জাতিত্ব বিষয়ক চিন্তাভাবনা কিছুটা কমিউনিজম দ্বারা প্রভাবিত, যা মূলস্রোতের ইসলামী শাস্ত্রজ্ঞদের দ্বারা কতটুকু অনুমোদিত হবে সেটিও একটি প্রশ্ন । এটা অবশ্য সত্য তার পরিকল্পনার মধ্যে মুসলিম অধ্যুষিত উত্তর-পশ্চিম ভারতকে ভারতীয় ফেডারেশনের ভিতরে একটি পৃথক স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল হিসেবেই ধরা হয়েছিল।
সিন্ধীর পরিকল্পনা অনুযায়ী কেন্দ্রীয় সরকারকে সেকুলার হওয়ার কথা ছিল । ফেডারেশনে অন্তর্ভুক্ত রিপাবলিকগুলোর নিজস্ব রাষ্ট্রধর্ম থাকলেও, ধর্ম ব্যাপারে কেন্দ্রের কোনো এক্তিয়ার রাখা হয়নি। অন্তর্ভুক্ত রিপাবলিকগুলোর ধর্ম ব্যাপারে কেন্দ্র কোনো হস্তক্ষেপ না করলেও পার্টি ঘোষিত আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক ব্যাপারে রিপাবলিকগুলোর জওয়াবদিহি করার ব্যবস্থা রাখা হয়েছিল। এটা সত্য ধর্ম, এ ব্যাপারে তিনি উদারনীতিক চিন্তক ও রাজনীতিবিদ হিসেবেই নিজেকে উপস্থাপন করেছেন। বাদশাহ আকবর সম্বন্ধে তিনি একটি কৌতুহুলদীপক মন্তব্য করেছিলেন :
আকবরকে ঠিক মতো পরিচালনা করা গেলে তার উদারতা দিয়ে পুরো ভারতকে ইসলামে দাখিল করা যেতো। এসব কথা অবশ্য সিন্ধীর জীবদ্দশায় বহু রকমের সংশয় ও বিতর্ক তৈরি করেছিল। সিন্ধী তার দেশবাসীকে বলেছিলেন তাদের জীবন ধারা, সাংস্কৃতিক ও আইনী বৈশিষ্ট্য সবকিছুই পশ্চিমা অভিঘাতে তলিয়ে গেছে। পুরনো ব্যবস্থা আর হুবহু ফিরে আসবে না। সুতরাং তাদের নতুন ব্যবস্থা সৃষ্টির জন্য উঠে পড়ে লাগতে হবে ।
এছাড়াও তিনি পশ্চিমের বৈজ্ঞানিক বিপ্লবের সমঝদার ছিলেন। তিনি মনে করতেন ভারতীয়দের এগিয়ে যেতে হলে এই বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তিকে আয়ত্ত করতে হবে। উনিশ শতকের শেষ ও বিশ শতকের প্রথম দিকে উপমহাদেশে সৈয়দ আহমদ খান, সৈয়দ আমীর আলী ও মোহাম্মদ ইকবাল ইসলামের মধ্যে এক ধরনের বুদ্ধিবৃত্তিক আধুনিকতার কথা বলেছিলেন। উবায়দুল্লাহ সিন্ধী ইসলামী ঐতিহ্যবাহী শিক্ষার ভিতর থেকে বেরিয়ে এসেও সমকালীন রাজনৈতিক, সামাজিক ও ধর্মীয় সমস্যাগুলোকে আধুনিক দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করেছিলেন এবং ঐতিহ্যবাহী পথ কিছুটা ছেড়ে দিয়ে ভিন্ন আঙ্গিকে পরিস্থিতিকে মোকাবেলা করার চিন্তা করেছিলেন। তৎকালীন উলামারা পশ্চিমের অভিঘাতে বিধ্বস্ত জনগণের আর্থসামাজিক অবস্থাকে পুনরুদ্ধার করার চেষ্টা না করে শুধু ব্রিটিশ মিশনারীদের মোকাবেলায় ব্যস্ত ছিলেন। সিন্ধী উলামাদের এই ভূমিকাকে পলায়নবৃত্তির সাথে তুলনা করেছেন এবং তাদেরকে দ্রুত পরিবর্তনশীল সময়ের সাথে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। শাহ ওয়ালিউল্লাহর আদর্শের নিশান বরদার হিসেবে তিনি জনগণের ভিতরকার পার্থক্যকে কমিয়ে আনার চেষ্টা করেছেন এবং নতুন ও পুরাতনের সমন্বয় ভাবনার উপর জোর দিয়েছেন। তিনি উলামাদের দ্বারা খেলাফত পুনরুজ্জীবন চেষ্টাকে কোনো রকম ফলপ্রসূ কাজ বলে মনে করতেন না । সিন্ধী মনে করতেন পুণ্যবান খলিফাদের সময়কে আজকের দিনে ফিরিয়ে আনা সম্ভব নয়। এককালের উপযোগী রাজনৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থা পরবর্তীকালে প্রয়োজনীয়তা হারায়। সিন্ধী মনে করতেন পুণ্য খলিফাদের মৌলিক নীতির আলোকে আজকের সামাজিক রাজনৈতিক ব্যবস্থার পুনর্গঠন সাপেক্ষে নতুন ধরনের ‘কুরআনী সরকার’ প্রতিষ্ঠা করা যেতে পারে । তিনি তার জীবনের ইসলামী সমাজতন্ত্রের পর্যায়ে প্যান ইসলামী ধারণাকে আর কখনো কবুল করেননি । এক্ষেত্রে তার ধারণাকে সৈয়দ আহমদ খানের ধারণার অনুরূপ মনে হয়, যিনি মনে করতেন ইমাম হাসানের মৃত্যুর পর খেলাফত শেষ হয়ে গেছে । পরবর্তীকালের উমাইয়া, আব্বাসীয়া ও অটোমানরা স্রেফ বাদশাহী করেছে। এরা কেউ খলিফা হতে পারেনি, যদিও খেলাফতির খেতাব নিতে তাদের একটুও বাধেনি । একজন ইসলামিক আধুনিকতাবাদী হিসেবে সিন্ধী কিন্তু সমকালীন উলেমাদের মতো সমাজতন্ত্রকে পুরোপুরি অস্বীকার করেননি। তিনি বলেছেন, মানুষের মুক্তির জন্য অবশ্যই এর একটা ভূমিকা আছে। তবে ইসলামকে তিনি মার্ক্সবাদের চেয়ে উচ্চতর আদর্শ মনে করতেন ।
সিদ্ধী খেলাফতকে কার্যকরী ব্যবস্থা হিসেবে মনে না করলেও জিহাদের গুরুত্বকে খুবই মূল্য দিয়েছেন। আলীগড়ের আধুনিকতাবাদীদের মতো সিন্ধী জিহাদ নিয়ে কোনো হীনমন্যতায় ভোগেননি, যাকে শাহ ওয়ালিউল্লাহও খুবই মর্যাদা দিয়েছেন। সিন্ধী তার ইসলাম গ্রহণের অন্যতম কারণ হিসেবে জিহাদের কথা বলেছেন : His conversion to Islam from Sikhism was motivated by his appreciation of two values of the Islamic faith, absolute monotheism and the doctrine of Jihad.
জিহাদকে তিনি মনে করতেন, এটি হচ্ছে ইসলামী সমাজ বিপ্লবের বুনিয়াদ; অন্যদিকে মার্ক্সবাদকে তিনি মনে করতেন athiestic counterpart of the thiestic Jihad. সিন্ধী সাম্প্রদায়িকতার বিরোধী ছিলেন এবং আন্তর্জাতিকতাবাদ প্রচার করেছেন। তিনি প্রথমে মুসলমানদের ভিতরে ঐক্যের কথা বলেছেন। তিনি দেওবন্দ ও আলীগড়ের ভিতর সমঝোতার কথা যেমন বলেছেন তেমনি ঐতিহ্যবাহী ও আধুনিকতাবাদীদের ভিতরেও ঐক্যের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেছেন । একইভাবে তিনি তৎকালীন পরিস্থিতিতে হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের কথাও বলেছেন। এই কারণে তিনি কংগ্রেসের বিরোধী ছিলেন না। কেননা এটি অসাম্প্রদায়িকতার কথা বলতো। কিন্তু তিনি কংগ্রেসে গান্ধী নেতৃত্ব পছন্দ করেননি কেননা গান্ধী একই সাথে রাজনৈতিক ও ধর্মীয় নেতৃত্ব দাবি করতেন । যদিও সিঙ্গী কাবুলে কংগ্রেসের শাখা তৈরি করেছিলেন, কিন্তু দেশে ফিরে এর সাথে তেমন সম্পর্ক রাখেননি। সিন্ধীই প্রথম ঐক্য বজায় রেখে ভারত ভাগের একটা চমৎকার পরিকল্পনা দিয়েছিলেন যার সাথে অনেকটা ক্যাবিনেট মিশন প্লানের সাদৃশ্য আছে, যেটি নাকি জিন্নাহ গ্রহণ করেছিলেন।
সিঙ্গীকে সমকালে তার প্রচারিত ইসলামী সমাজতন্ত্রের জন্য স্বধর্মীয়দের কাছে ব্যাপক সমালোচিত হতে হয়েছিল। কিন্তু সমাজতন্ত্রকে তিনি ব্রিটিশ বিরোধী জাতীয় মুক্তি সংগ্রামে একটি কার্যকরী ব্যবস্থা হিসেবে গ্রহণ করতে চেয়েছিলেন। তাছাড়া সমাজতন্ত্রের যে মানবিক দিকগুলো সাধারণত মুসলিম নেতারা উপেক্ষা করে থাকেন যেমন দরিদ্রদের প্রতি অসাধারণ দরদ, পুঁজিবাদ, সাম্রাজ্যবাদের নিষ্ঠুর শোষণের প্রতি ইংগিত এবং এর থেকে পরিত্রাণের উপায় এসব বিষয়গুলো সিন্ধীকে বিপুলভাবে আকর্ষণ করেছিল। এসব বিষয়গুলো ইসলামী ভাবাদর্শ দিয়েও ব্যাখ্যা করা যায় । ইসলামী নৈতিকতা কখনোই লুণ্ঠন ও শোষণকে সমর্থন করে না। দরিদ্র মানুষের মুক্তির জন্য হাত বাড়িয়ে দেয়াই ইসলামের নীতি সুতরাং সিন্ধী যদি এসব ব্যাপারগুলোকে গুরুত্ব দিতে চান তবে তাকে ইসলাম বিরুদ্ধ বলা যাবে না মোটেই ।
অনেক মুসলিম সমাজতন্ত্রীর মতো সিন্ধী কিন্তু ইসলাম ত্যাগ করেননি। বরং সমাজতন্ত্রকে ইসলামী কাঠামোর মধ্যে আনতে চেয়েছিলেন বলেই মনে হয়। সর্বোপরি সমাজতন্ত্রকে তিনি শাহ ওয়ালিউল্লাহর দর্শন দিয়ে ব্যাখ্যা করেছিলেন। তার সমাজতন্ত্র আধ্যাত্মিকতাকে বাদ দিয়ে নয়। এটাকে এক ধরনের ধর্মীয় সমাজতন্ত্রও বলা যায় ।
সিন্ধী ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারের মডেলটিকে সেক্যুলার আঙ্গিকে সাজাতে চেয়েছিলেন। শাহ ওয়ালিউল্লাহর নৈতিকতাকে কীভাবে সেক্যুলার কাঠামোর মধ্যে তালুবন্দী করা যায় সেটাও একটা প্রশ্ন। এসব নিয়ে তার সমালোচনা হয়েছে । ভারতকে ঐক্যবদ্ধ রাখতে হলে তখনকার পরিস্থিতিতে এর চেয়ে উত্তম বিকল্প কি ছিল? কেবিনেট মিশন প্লান যদি তখন ভারতবর্ষের দুই দল মেনে নিত তাহলেও তো এই ঘটনা ঘটতো। সংখ্যালঘু হিসেবে একটি দেশে টিকে থাকতে অনেক বিকল্পের কথাই ভাবতে হয় । আজকে ইউরোপে সংখ্যালঘু মুসলমানদের টিকে থাকার জন্য তারিক রামাদান তাদেরকে ইউরোপীয় সংস্কৃতির সাথে বুঝাপড়া করার জন্য পরামর্শ দিচ্ছেন। ট্রাডিশনাল দারুল হরবকে বলা হচ্ছে দারুল দাওয়া। এসব ধারণাও তো অনেকটা সিন্ধীর ধারণার অনুরূপ। এটা সত্য সিন্ধীর এসব চিন্তাভাবনা সমকালে তেমন কোনো গুরুত্ব পায়নি। সেকালের প্রধান দুই রাজনৈতিক দল কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ কেউ এভাবে চিন্তা করেনি। তার এসব চিন্তাভাবনা কি কিছুটা ইউটোপিয়ার মতো লাগে। সব বিপ্লবী আদর্শেই হয়তো কিছুটা ইউটোপিয়ার গন্ধ থাকে। কারণ বিপ্লবীরা তো কিছুটা স্বপ্নের মধ্যেও বসবাস করেন । পাকিস্তানী ঐতিহাসিক আয়শা জালাল তার সম্পর্কে লিখেছেন :
He remained a voice on the margins, and he himself knew that very few people understood his mission and philosophy. He remained outside the mainstream politics in India represented by the two major political parties, Indian National Congress and All India Muslim Leage.
আরেকজনের মতামত তার সম্পর্কে :
much ahead of his time…He ploughed a lonely furrow in the country of his birth… He combined too much and harmonized too much. He was drawn and attracted by widely diverse movements of thought. But he seems to have had a highly integrating faculty and a deep sense of history.
চার.
শাহ ওয়ালিউল্লাহর চিন্তাভাবনার প্রস্রবণ থেকেই তৈরি হয়েছিল ভারতজুড়ে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী মুজাহিদ আন্দোলন। ১৮৫৭ সালের বিপর্যয়ের পর সেই প্রস্রবণ দুই ভাগ হয়ে যায়। একটি যায় আলীগড়ের দিকে, আরেকটি দেওবন্দের উদ্দেশ্যে। আলীগড় মুসলিম আধুনিকতার পথ নেয়। দেওবন্দ নেয় ইসলামী নৈতিকতার পথ। প্রত্যেক চিন্তাই বিবর্তনমুখর। সময়ের সাথে তা পরিবর্তনও হয় । দেওবন্দের বিপ্লবী আদর্শ বিশ শতকের প্রথম দিকে এসে বড় রকমের টানাপোড়েনের ভিতর দিয়ে অগ্রসর হয়। প্যান ইসলামবাদী দেওবন্দ থেকে জাতীয়তাবাদ প্রশ্নে নতুন নতুন ধারার জন্ম হয়। এক ভাগ যায় ভারতীয় জাতীয়তাবাদের দিকে ( হোসেন আহমদ মাদানী), এক ভাগ যায় মুসলিম জাতীয়তাবাদের দিকে (শাব্বির আহমদ উসমানী, আর এক ভাগ যায় ইসলামিক সমাজতন্ত্রের দিকে (উবায়দুল্লাহ সিন্ধী)। প্রত্যেক ভাগের নেতৃত্বেই থাকেন বড় বড় আলেম । এরা ইসলামী নৈতিকতা, ইতিহাস ও শাস্ত্র দিয়ে তাদের গৃহীত পথকে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন। এসব ব্যাখ্যা পরস্পরের কাছে গ্রহণীয় হয়নি। বরং নানা তিক্ততার জন্ম দিয়েছে। আবার যেমন ঔপনিবেশিকতার অভিঘাতে দেওবন্দকে নানা চড়াই উৎরাইয়ের ভিতর দিয়ে যেতে হয়েছে তেমনি নতুন নতুন চিত্তারও ক্ষুরণ ঘটেছে। এই স্ফুরণ সৃষ্টিশীলতার পরিচয়। সেই চিন্তারই একজন উজ্জ্বল রত্ন উবায়দুল্লাহ সিন্ধী। সিন্ধীর চিন্তা ভাবনায় কিছুটা অসংগতি ও দোদুল্যমানতা আছে। আছে নানা রকম সংযোজন, বিয়োজন ও সমন্বয়ের চেষ্টা। প্রত্যেক মতাদর্শই এভাবে ভাঙা গড়ার ভিতর দিয়ে এগিয়ে চলে । প্রত্যেক মতাদর্শের যেমন শক্তির দিক থাকে, তেমনি দুর্বলতার দিকও থাকে। সিন্ধীরও ছিল।
আবার যে প্রেক্ষাপটে তিনি তার থিসিস উপস্থাপন করেছিলেন তাও আজকে অনেক কিছুই অনুপস্থিত। ভারতীয় উপমহাদেশ থেকে ব্রিটিশ চলে গেছে। দেশ ভাগ হয়ে গেছে। ফলে তার চিন্তার অনেক কিছুই আজ কার্যকারিতা হারিয়েছে। অন্যদিকে ইতিহাসও সমাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে রায় দিয়েছে। তবে তার পুঁজিবাদ সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতা, মানুষের মুক্তির জন্য তার চিন্তাভাবনা, নিপীড়িত মানুষের জন্য অপরিসীম মানবিক উপলব্ধি আজও গুরুত্ব হারায়নি। এসব সমস্যা আজও আছে সেই প্রেক্ষিতেই সিন্ধীর চিন্তাভাবনা পুনর্মূল্যায়নের দাবি রাখে ।
হদিস
K. H. Ansari, Pan Islam and the Making of the Early Indian Muslim Socialist. Cambridge: Cambridge University Press, 1986.
মওলানা মুজীবুর রহমান অনূদিত, মওলানা ওবায়দুল্লাহ সিন্ধীর রোজনামচা। ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৮৪
Peter Hardy. The Muslims of British India. Cambridge: Cambridge University Press.
ইমতিয়াজ বিন মাহতাব, রেশমি রুমাল আন্দোলন : পেরিয়ে গেল একশ বছর। দৈনিক নয়াদিগন্ত, ২१ জানুয়ারি, ২০১৩।
M. Naeem Qureshi, Pan Islamism in British Indian Politics: A Study of the Khilafat Movement, 1918-24. Leiden: Brill.
Tanvir Anjum. A voice from the Margins: An Appraisal of Ubaid-Allah Sindhi’s Mahabharat Sarvrajia Party and its Constitution.
Journal of Political Studies, vol. 20, issue-1, 2013, 165-183.
উত্তর আধুনিক মুসলিম মন ১৩০
Ansari, Pan Islam. >. Ziyaul Hassan Faruqui. The Deoband School and the Demand for Pakistan.
Bombay Asia Publishing House, 1963.
Mahendra Pratap, My Life Story of Fifty Five Years. Dehradun: World Federation, 1947.
Muhammad Hajjan Shaikh, Maulana Ubaid Allah Sindh: A Revolutionary Scholar. Islamabad: National Institute of Historical and Cultural Research, 1986.
মওলানা মুজীবুর রহমান অনূদিত, মওলানা ওবায়দুল্লাহ সিন্ধীর রোজনামচা।
Faruqui, The Deoband School.
Hajjan Shaikh, Ubaid Allah Sindh.
Aziz Ahmad, Islamic Modernism in India and Pakistan, 1857-1964. London: Oxford University Press, 1967.
Hajjan Shaikh, Ubaid-Allah Sindh.
Internet: Wikipedia. Sb. Faruqui. The Deoband School.
গোলাম আহমাদ মোর্তজা, চেপে রাখা ইতিহাস। বর্ধমান বিশ্ববঙ্গীয় প্রকাশন, ১৯৯৮।
Shaikh Muhammad Hajan, The Political Thought of Maulana Ubaidullah Sindhi. In The Quest for Identity voll III. Eds. Waheed-uz-zaman and A H Dani. Islamabad: University of Islamabad Press, 1974.
Tanvir Anjum, A Voice from the Margins.
Hajjan Shaikh, Ubaid-Allah Sindh.
Aziz Ahmad, Islamic Modernism.
M. Moizuddin, Maulana Obaidullah Sindhi. The Muslim Luminaries: Leaders of Religious, Intellectual and Political Revival in South Asia. Islamabad: National Hijra Council.
Ayesha Jalal, Partisans of Allah: Jihad in South Asia. Cambridge, MA: Harvard University Press.
0Abdullah Khan, Maulana Ubayd Allah Sindhi’s Mission to Afghanistan and Soviet Russia. Peshwar: Area Study Center, 2000.