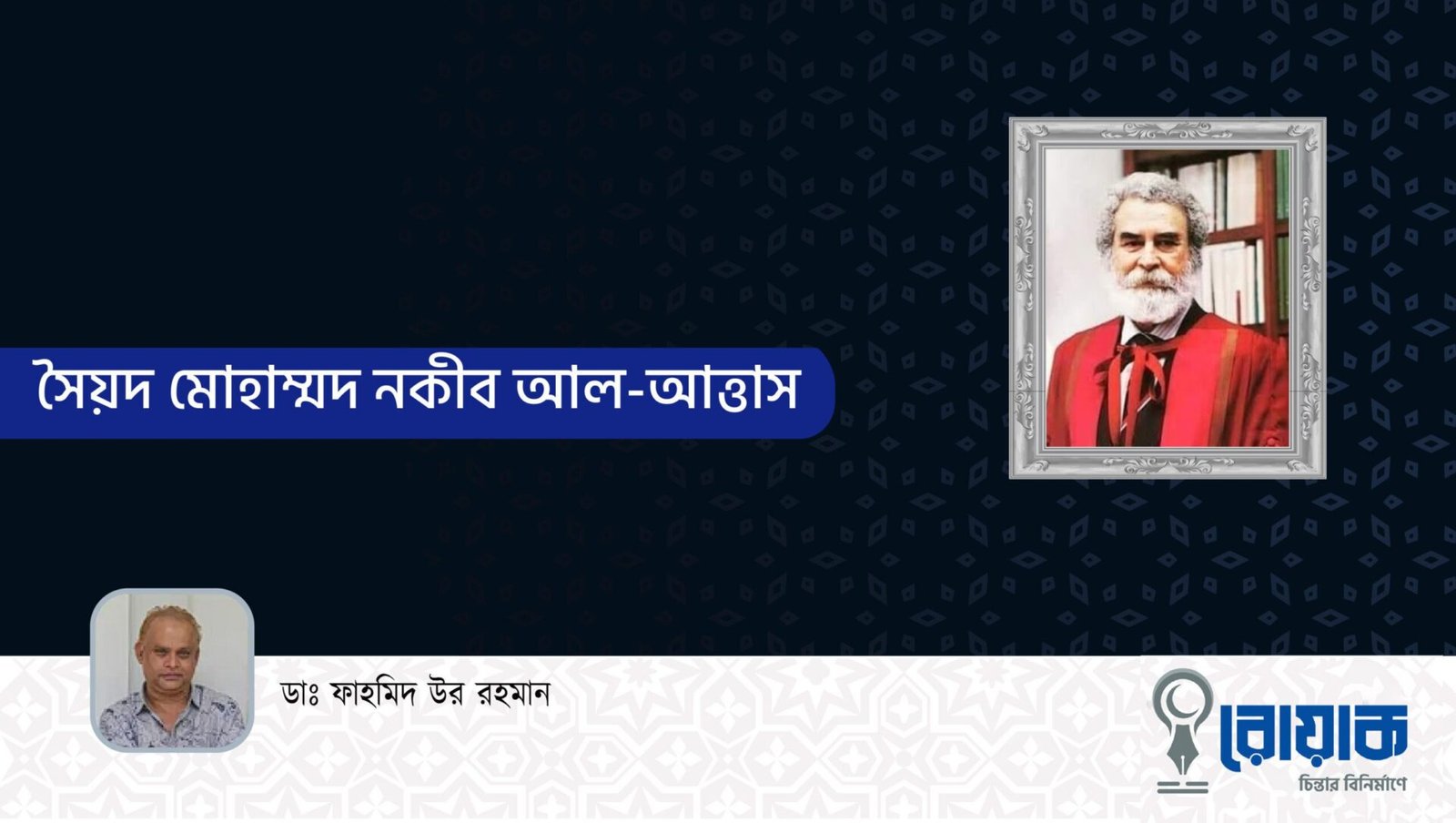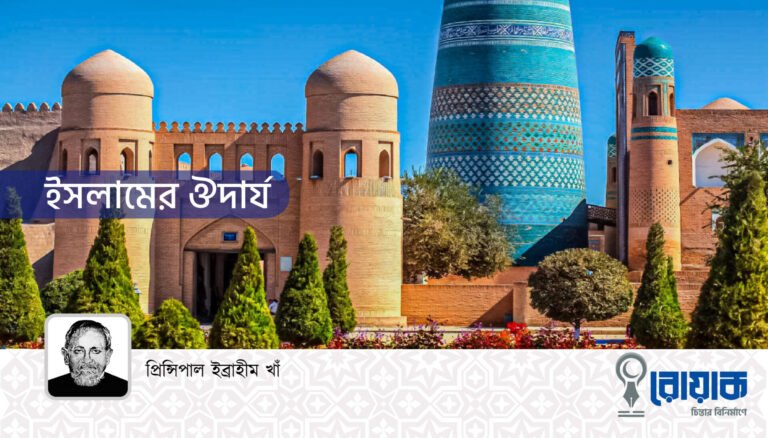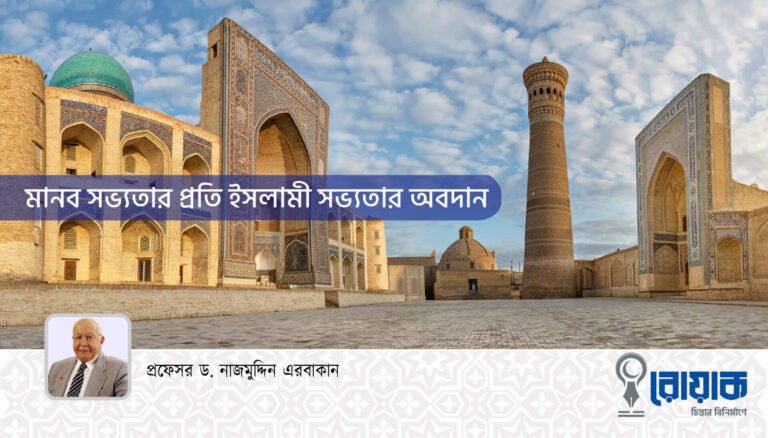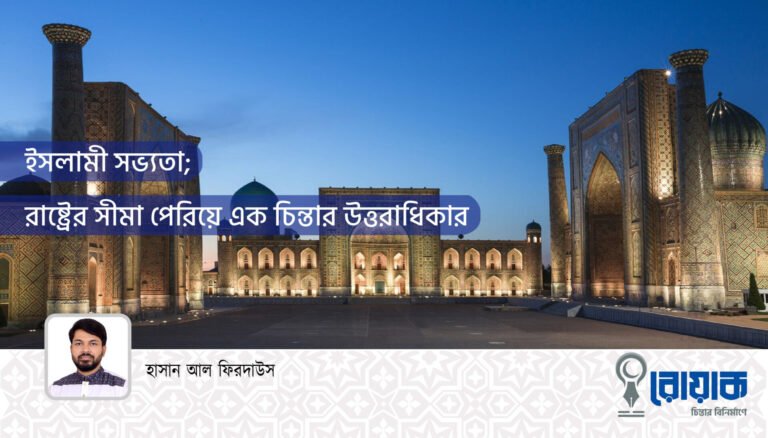এক.
দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে বাহাসা ভাষাভাষী জনগোষ্ঠীর বসবাস। এরা প্রধানতঃ ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, ব্রুনাই, থাইল্যান্ড, ভিয়েতনাম ও সিঙ্গাপুরে বসবাস করে এবং বাহাসা ও বাহাসার বিভিন্ন আঞ্চলিক রূপে কথা বলে । এদের বড় অংশ হচ্ছে মুসলমান এবং সংখ্যাতাত্ত্বিকভাবে নিখিল মুসলিম উম্মাহর এরা একটি বড় শরিকদার ।
মুসলিম সংস্কৃতি ও ইতিহাসের কথা আলোচনা করতে গেলে আমরা সাধারণত মধ্যপ্রাচ্যের মুসলিম জনপদের দিকে তাকাই। এটি অস্বাভাবিক নয়। কারণ ইসলামের উত্থান ও বিকাশ এই জনপদকে ঘিরেই পল্লবিত হয়েছে । তাই উৎসের দিকে তাকিয়ে আমরা হয়তো এক ধরনের প্রেরণা পেতে চাই । কিন্তু এই উৎস থেকে বহুদূরে বাহাসাভাষী মুসলমানরা শত শত বছর ধরে মুসলিম সংস্কৃতির একটি বৈচিত্রময় রূপের বিকাশ ঘটিয়েছে যার স্বাদ ও ঘ্রাণ একেবারেই অনন্য ও বিশিষ্ট । দীর্ঘদিন ধরে এই জনপদের অধিবাসীরা পর্তুগীজ, ডাচ ও ইংরেজ ঔপনিবেশিক শক্তির নিয়ন্ত্রণাধীন ছিল। ঔপনিবেশিকতার বিরুদ্ধে এদের দীর্ঘ লড়াই-সংগ্রাম ছিল পৃথিবীর অন্যান্য অনেক অঞ্চলের মানুষের মতোই আয়াসসাধ্য, একই সাথে গৌরবময়। উপনিবেশ বিরোধী লড়াইয়ে ইসলাম বাহাসা মুসলমানদের দিয়েছে অনিঃশেষ প্রেরণা। উপনিবেশ মুক্তির পর এরা এখন ঘুরে দাঁড়িয়েছে এবং একটি ক্রমজাগ্রত শক্তিতে পরিণত হতে চলেছে। বিশেষ করে বাহাসা মুসলমানদের ইসলামকে নিয়ে চিন্তাভাবনা, আধুনিককালে ইসলামের পুনর্জীবন ও পুনর্গঠন এবং রাজনৈতিক ও সামাজিক শক্তি হিসেবে একালে ইসলামের ভূমিকা নিয়ে এদের বুদ্ধিজীবী ও রাজনীতিবিদদের মূল্যায়ন অনেকের ভাবনার খোরাক যোগাবে। এদের এই সাংস্কৃতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক অর্জনের খবর আমরা তেমন কিছুই রাখি না । এর কারণ হয়তো ভাষার দূরত্ব, কিছুটা ভূগোলের দূরত্ব। এদের সাথে আমাদের সাংস্কৃতিক ভাব পরিমাণও কম। বাহাসা মুসলমানদের সাথে আমাদের সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক ও কৌশলগত মিত্রতা গড়ে তোলা দরকার, প্রথমত আমাদের কৌশলগত ভৌগোলিক রাজনীতির স্বার্থে এবং বিশেষ করে মুসলিম উম্মাহর প্রেক্ষাপটে, না হলে উম্মাহর ভাবনা নিছক কথার কথা হয়ে থাকবে । সমসাময়িক কালে বাহাসা মুসলিম সংস্কৃতির এক প্রধান মুখপত্র হচ্ছেন সৈয়দ মোহাম্মদ নকীব আল-আত্তাস। একালে মুসলমানের পরাজয়, হতাশা ও বিচ্ছিন্নতা তাকে গভীরভাবে ভাবিয়েছে এবং নিরন্তর এর থেকে উত্তরণের পথ তিনি খুঁজেছেন । তার কাছে মনে হয়েছে দীর্ঘ ঔপনিবেশিকতা মুসলমানের আত্মাকে দূষিত করে ফেলেছে এবং তার বিশ্বাস, মূল্যবোধ ও শিক্ষার দর্শনের মধ্যে ঘটে গেছে মহাবিপর্যয় ও বিকৃতি এবং এর থেকে সূচনা হয়েছে মুসলমানের ভাটার টান । এটাকে তিনি বলেছেন মুসলিম সংস্কৃতির আদবের খেলাফ এই সাংস্কৃতিক আদবকে তিনি মুসলিম জগতে ফিরিয়ে আনতে চান এবং সেই প্রেক্ষাপটে মুসলিম ভাব জগতের কাছে তিনি তার নতুন লিবারেশন থিওলজি- মুক্তিতত্ত্ব হাজির করেন ।
দুই.
সৈয়দ মোহাম্মদ নকীব আল-আত্তাসের জন্ম ইন্দোনেশিয়ায় কিন্তু তার সৃষ্টিমুখর জীবনের কেন্দ্র হচ্ছে মালয়েশিয়া। এটিকে কেন্দ্র করে তিনি তার বুদ্ধিবৃত্তি ও জ্ঞান চর্চার ধারা বিকশিত করেছেন এবং মালয়েশিয়ার সীমানা পেরিয়ে মুসলিম ভাবজগতে এক নব তরঙ্গের সৃষ্টি করেছেন ।
নকীব আল-আত্তাস ১৯৩১ সালের ৫ সেপ্টেম্বর ইন্দোনেশিয়ার জাভার বোগোরে জন্মগ্রহণ করেন। সেই কালে জাভার নাম ছিল ডাচ ইস্ট ইন্ডিজ। আত্তাসের আব্বার নাম সৈয়দ আলী আল-আত্তাস ও আম্মার নাম শরিফা রাকাউন আল আয়দারুস । আত্তাসের বিখ্যাত পূর্ব পুরুষরা ছিলেন সুফী ও আলেম, যাদের বংশধারা যেয়ে মিশেছে সৌদি আরবের হাজরামাউতের বা আলাভী সৈয়দদের সাথে । সেখান থেকে সেই ধারা পৌঁছে গেছে ইমাম হোসেনের রক্ত ধারার সাথে । আল-আত্তাসের আনুষ্ঠানিক লেখাপড়া শুরু হয় ৫ বছর বয়সে মালয়েশিয়ার জহরে । কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালে জাপানীরা মালয়েশিয়া দখল করে নিলে তিনি জাভায় ফিরে যান এবং সেখানকার মাদরাসা উরওয়াতুল উস্কায় আরবি শিক্ষা করেন। ১৯৪৬ সালে যুদ্ধ শেষে তিনি জহরে ফিরে আসেন এবং প্রবেশিকা পরীক্ষা শেষ করেন। এ সময় তিনি মালয় ভাষা, সাহিত্য, ইতিহাস, ধর্মতত্ত্ব ও পশ্চিমা ক্লাসিক নিবিষ্ট মনে অধ্যয়ন করেন যা তার ভিতরে শিল্প সংস্কৃতি সম্পর্কে একটি সূক্ষ্ম সৌন্দর্যানুভূতি তৈরি করে। এই শিল্প ও সংস্কৃতি চেতনা পরবর্তীকালে তার মালয় ভাষায় লেখালেখিতে একটি নিজস্ব ধারা ও শৈলী নির্মাণে প্রভূত সাহায্য করে।
প্রবেশিকা পরীক্ষার পর আল-আত্তাস ১৯৫১ সালে মালয় সেনাবাহিনীতে ক্যাডেট অফিসার হিসেবে যোগদান করেন এবং সেখান থেকে বিলাতের বিখ্যাত স্যান্ডহারস্ট রয়াল মিলিটারি একাডেমিতে উচ্চ শিক্ষার জন্য গমন করেন (১৯৫২-৫৫) । এখানে অধ্যয়নকালে তিনি ব্রিটিশ সমাজের শক্তি ও কাঠামো সম্বন্ধে গভীর ধারণা পান। আবার এখানে থাকতেই তিনি সুফী চিন্তাভাবনায় প্রাণিত হন। বিশেষ করে ইরানের বিখ্যাত কবি জামীর রচনা তার মন ছুঁয়ে যায়, যা তিনি একাডেমির কুতুবখানায় খুঁজে পেয়েছিলেন।
এ সময় তিনি ভ্রমণে বের হন বিশেষ করে উত্তর আফ্রিকা ও স্পেনের ইসলামী ঐশ্বর্যের ভাণ্ডার ও বিশালতা তার উপরে দারুণ প্রভাব ফেলে, যা তিনি নির্দ্বিধায় বহন করেন এবং এটি থেকে তিনি আর কখনোই মুক্ত হননি। সেনাবাহিনীর বাঁধাধরা জীবন এই তরুণ বিদ্যাব্রতীকে আটক করে রাখতে পারে না । তিনি অধিকতর লেখাপড়ার জন্য উদগ্রীব হন, সেনাবাহিনীর চাকরি ছেড়ে দেন এবং সিঙ্গাপুরের মালর বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে ভর্তি হন (১৯৫৭-৫৯)।
এখানে অধ্যয়নকালে তিনি মালয় ভাষায় রঙ্গকাইয়ান রুবাইয়াত নামে একটি বই লেখেন যা তার প্রথম সাহিত্য প্রচেষ্টা এবং মালয় সুফীদের বিশ্বাস ও আচরণের ধারা নিয়ে একটি বই লেখেন যার নাম Some Aspects of Sufism as Understood and Practised Among the Malays.
এরপর তিনি কানাডার ম্যাকগিল বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগে কানাডা কাউন্সিলের দেয়া ৩ বছরের ফেলোশিপ পান। এখান থেকে ১৯৬২ সালে ইসলামী দর্শনে ব্যুৎপত্তিসহ এম এ ডিগ্রি পান। এখানে তার অভিসন্দর্ভের বিষয় ছিল Raniri and the Wujudiyyah of 17th Century Acheh কানাডা থেকে তিনি লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন স্কুল অফ অরিয়েন্টাল অ্যাও আফ্রিকান স্টাডিজে এসে পিএইচডি কোর্সে ভর্তি হন এবং অধ্যাপক আর্থার জন আরবেরী ও মারটিন লিংসের মতো মশহুর ইসলামবিদদের অধীনে কাজ করেন। তার পিএইচডি অভিসন্দর্ভের বিষয় ছিল The Mysticism of Hamzah Fansuri। এটি হচ্ছে মালয় অঞ্চলের মশহুর সুফী ও বুদ্ধিজীবী হামজা ফানসুরীর চিন্তাভাবনার উপর সবচেয়ে মূল্যবান ও তথ্য সমৃদ্ধ গবেষণামূলক কাজ। ১৬ ও ১৭ পুরনো মালয় পুঁথিপত্র ঘেঁটে আল-আত্তাসই প্রথম আল রানিরি ও হামজা ফানসুরীর মতো মালয় সুফীদের চিন্তাভাবনাকে একালে তুলে এনেছেন । মালয় সুফীদের উপর কাজ করতে যেয়ে হয়তো তিনি কিছুটা সুফী চিন্তা ও সাধনপ্রণালী দ্বারা আলোড়িত হয়েছেন এবং এসব চিন্তাভাবনা তার ভবিষ্যৎ চিন্তা ও তত্ত্ব নির্মাণে ভূমিকা রেখেছে।
১৯৬৫ সালে আল-আত্তাস দেশে ফেরেন এবং কুয়ালালামপুরের মালয় বিশ্ববিদ্যালয়ে মালয় ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের প্রধান হিসেবে যোগদান করেন । পরবর্তীকালে তিনি এ বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা বিভাগের ডীনও হন।
এরপর তিনি নবপ্রতিষ্ঠিত মালয়েশিয়ার জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে মালয় ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের প্রধান হিসেবে যোগ দেন এবং এখানকার কলা বিভাগের ডীনের পদও অলংকৃত করেন ।
আল-আত্তাসই প্রথম মালয় ভাষাকে বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে ব্যবহারিক ভাষা হিসেবে গ্রহণ করার কথা বলেন এবং মালয় ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতিকে এমনভাবে অন্তর্ভুক্ত করার কথা বলেন, যাতে ইসলামের প্রভাব ও ভূমিকা এবং অন্যান্য ভাষা ও সংস্কৃতির সাথে এর সম্পর্ক আরো সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। এ লক্ষ্যে তিনি ১৯৭৩ সালে মালয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন ইনস্টিটিউট অফ মালয় ল্যাংগুয়েজ, লিটারেচার অ্যান্ড কালচার প্রতিষ্ঠায় নেতৃত্ব দেন। মালয় ভাষা নিয়ে তার বিশিষ্ট চিন্তাভাবনা বিশেষ করে জাতিগঠনে মালয় ভাষার ভূমিকা নিয়ে ১৯৬৮ সালে রাজনীতিবিদদের সাথে সংলাপ ও বিতর্কে তিনি বড় ভূমিকা রাখেন। তার এসব কার্যক্রম পরবর্তীকালে মালয়েশিয়ার জাতীয় ভাষা হিসেবে মালয়ের প্রতিষ্ঠা ও সংহতির জন্য কাজ করে। শুধু তাই নয় বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন প্রভাবশালী শিক্ষক ও একাডেমিসিয়ান হিসেবে মালয় ভাষাকে বুদ্ধিবৃত্তি ও জ্ঞান চর্চার ভাষা হিসেবে নির্মাণ করবার জন্য ছাত্র ও ফ্যাকাল্টির সদস্যদের উদ্বুদ্ধ করেন। প্রকৃতপক্ষে মালয় ভাষায় ইসলাম বিষয়ের উপর আল-আত্তাসের লেখালেখি, ভাষার শৈলী ও প্রসাদগুণে এক অর্থে অনন্য এবং মালয়েশিয়ার বুদ্ধিজীবী ও সাহিত্যব্রতীদের জন্য একটি মডেলও বটে। শুধু তাই নয় বুদ্ধিবৃত্তি ও দার্শনিকতার ভাষা হিসেবে আধুনিক মালয় ভাষায় এটি প্রথম নিরীক্ষামূলক কাজ যার মাধ্যমে এই ভাষায় একটি নতুন স্টাইল বা ধরনের সূচনা হয়েছে।
আল-আত্তাসের আর একটি জরুরি কাজ হচ্ছে তিনি ১৯৮৭ সালে কুয়ালালামপুরে International Institute of Islamic Thought and Civilization (ISTAC) প্রতিষ্ঠায় প্রধান ভূমিকা পালন করেন। আল-আত্তাস হচ্ছেন আধুনিককালে জ্ঞানের ইসলামীকরণ তত্ত্বের একজন বড় পণ্ডিত ও প্রবক্তা। এই তত্ত্বের মূলকথা হচ্ছে – মন, শরীর ও আত্মার ইসলামীকরণ এবং মুসলমানের ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনকে এই আদলে নির্মাণ করা । এই প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থী ও বিদ্যাব্রতীদের মনন ও চিন্তায় ইসলামের বিশ্বদর্শন ও বয়ানকে অগ্রগামী করে রাখবার পরিকল্পনা আল-আত্তাসের মধ্যে ছিল। তিনি নিজেই এই প্রতিষ্ঠানটির পরিকল্পনা ও ডিজাইন তৈরি করেন এবং এটির স্থাপত্য শৈলীতে ইসলামের স্থাপত্যকলার প্রভাবকেই গ্রহণ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে আল-আত্তাসের যৌবনে দেখা আন্দালুসিয়ার মুসলিম ঐতিহ্য ও সৌন্দর্য চেতনা বড় একটা প্রভাব ফেলেছে তাতে কোনো অতিশয়োক্তি নেই। আল-আত্তাস ব্যক্তিগতভাবে একজন দক্ষ ক্যালিগ্রাফার । ক্যালিগ্রাফীর সূক্ষ্ম সৌন্দর্যানুভূতিরও প্রকাশ ঘটেছে ISTAC-এর ডিজাইনে।
তিন.
সৈয়দ নকীব আল-আত্তাস আধুনিককালে ইসলামী চিন্তা, বিশেষ করে ইসলামী শিক্ষার ক্ষেত্রে তাৎপর্যপূর্ণ অবদান রেখেছেন। এক্ষেত্রে সৈয়দ আলী আশরাফ ও ইসমাইল রাজি আল ফারুকী যেভাবে জ্ঞানের ইসলামীকরণের তত্ত্বকে ফলবান ও সমৃদ্ধ করেছেন আল-আত্তাসের অবদান তার চেয়ে মোটেই কম নয় । ১৯৭৭ সালের মার্চে মক্কায় অনুষ্ঠিত প্রথম বিশ্ব মুসলিম শিক্ষা সম্মেলনে আল আত্তাস একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ পাঠ করেন যার শিরোনাম হচ্ছে The Concept of Education in Islam । এই প্রবন্ধে তিনি তার ইসলামী শিক্ষা নিয়ে মৌলিক চিন্তাভাবনা প্রথমবারের মতো উপস্থাপন করেন। এখানে তিনি ইসলামী শিক্ষাকে আদব (শৃঙ্খলা) শব্দ দ্বারা বুঝানোর চেষ্টা করেন এই শব্দটির তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে তিনি দেখানোর চেষ্টা করেন ইসলামী ঐতিহ্যে আদব মানে হচ্ছে একই সাথে জ্ঞান ও কর্ম। কিন্তু শিক্ষা বলতে মুসলিম সমাজে যে তারবিয়া ও রবুবিয়া শব্দটা প্রচলিত আছে তা নিয়ে ঠিক ঐ অর্থকে বুঝানো যায় না। আল-আত্তাসের লেখালেখিতে আদব শব্দটা বারবার এসেছে এবং তিনি তার সমগ্র চিন্তাভাবনাকে আদব শব্দ দিয়ে প্রকাশ করতে বেশ স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেছেন। এই আদবকে তিনি কখনো জ্ঞান, নৈতিকতা, ইনসাফ ও সমাজ অর্থেও ব্যবহার করেছেন । কেন তার কাছে আদব শব্দটা এত গুরুত্বপূর্ণ? কারণ তিনি মনে করেন ইসলামী শিক্ষার মৌল উদ্দেশ্য রাষ্ট্রের জন্য সুনাগরিক তৈরি করা নয়, বরং ভালো মানুষ তৈরি করা । ভালো মানুষ তৈরি করতে হলে আদবের প্রয়োজন । তার ভাষায় :
The end of education in Islam is to produce a good man, and not as in the case of western civilization- to produce a good citizen. By ‘good’ in the concept of good man is meant precisely the man of adab in the sense here explained as encompassing the spritual and material life of man.
আদবকে আল-আত্তাস শিক্ষার সমার্থক হিসেবে দেখেছেন এবং এরকম শিক্ষা যেখানে জাগতিক জ্ঞান আধ্যাত্মিক জ্ঞানের নিয়ন্ত্রণাধীন থাকবে। মানুষের রূহের নজীর দিয়ে আল-আত্তাস দেখিয়েছেন এর দুটো প্রকৃতি রয়েছে। একটি হচ্ছে সৎকর্মশীল, অন্যটি অসৎ স্বভাবের দিকে আকৃষ্ট। প্রথমটিকে আমরা বলি আল নাফস আল নাতিকা- ন্যায়ানুগ আত্মা এবং অন্যটি আল নাফস আল হাইওয়ানিয়া পাশবিক আত্মা । ন্যায়ানুগ আত্মা পাশবিক আত্মাকে নিয়ন্ত্রণ করবে এবং এভাবেই মানুষ নিজেকে নিজের প্রেক্ষাপটে স্থাপন করবে এবং সৃষ্টির এই ধারাকে রক্ষা করে মানুষ নিজের প্রতি আদব পালন করবে। আদবকে এইভাবে ব্যাখ্যা করার মধ্যে আত্তাসের চিন্তার অভিনবত্ব এবং মৌলিকত্ব বুঝা যায় । আদবকে আমরা সাধারণত মানবিক শৃঙ্খলাবোধ হিসেবে দেখতে অভ্যস্ত। কিন্তু আবাস সেটিকে সৃষ্টির শৃঙ্খলার সাথে একাকার করে দেখেছেন এবং এই শৃঙ্খলার জ্ঞানকেই বলেছেন শিক্ষা ।
আল-আত্তাস ১৯৯৫ সালে লেখেন Prolegomena to the Metaphysics of Islam An Exposition of the Fundamental Elements of the World view of Islam । এ বই আত্তাসের জীবনব্যাপী চিন্তাভাবনার সারাৎসার। এখানে তিনি ইসলামী বিশ্বদর্শনের একটি রূপরেখা হাজির করেছেন। এখানে তিনি আদব সম্পর্কে তার চিন্তাভাবনার কথা বিস্তারিতভাবে বলেছেন। তার ভাষ্য উদ্ধার করছি,
আদব-এর তাৎপর্য হচ্ছে জ্ঞান; এ জ্ঞান প্রজ্ঞা (হিকমাহ) থেকে উৎসারিত; জ্ঞান অন্বেষণের লক্ষও এতে প্রকাশ পাচ্ছে; এটি আত্মার অভ্যন্তরীণ ও বহির্মুখীকাণ্ডও বটে যা নৈতিক মূল্যবোধ ও নিষ্ঠার ফলশ্রুতি। আর এর উৎস ধারা দর্শনও নয়, বিজ্ঞানও নয়, বরং প্রত্যাদিষ্ট সত্য যা ধর্ম থেকে প্রবাহিত হয়।
আত্তাস এখানে আদবের উৎস হিসেবে ঐশী জ্ঞান বা ওহীর কথা বলেছেন যার অনুপস্থিতি মানে হচ্ছে আদবের অসংগতি ও মানব শৃঙ্খলার বিপর্যয়। আত্তাস আদবের বিপর্যয় ঘটলে মানব সমাজে যা ঘটে থাকে তারও একটি ছবি আমাদের সামনে তুলে ধরেছেনঃ
আদবের অসংগতি ও অসমন্বয়, যা জ্ঞানে দুর্নীতিরই ফল, এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি করে যাতে জীবনের সর্বক্ষেত্রে মিথ্যা ও কপট নেতাদের উদ্ভব ঘটে। এর তাৎপর্য এই যে, এতে শুধু জ্ঞানে দুর্নীতি বা দুর্বৃত্তায়নই ঘটে না, এতে উপরন্ত সত্যিকার নেতাদের জানা ও স্বীকার করার ক্ষমতা ও যোগ্যতাও বিনষ্ট হয়ে যায়। এ পরিস্থিতির একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে বুদ্ধিবৃত্তিক অরাজকতা। ফলে সাধারণ জনতা বুদ্ধিবৃত্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের হর্তাকর্তা বনে যায় এবং জ্ঞানের ক্ষেত্রে তারা কর্তৃত্ব গ্রহণের পর্যায়ে আরোহণ করে। প্রকৃত ও সঠিক সিদ্ধান্তসমূহ অকার্যকর হয়ে যায় এবং এসবের স্থলে আমাদের সামনে থাকে গভীর ধারণার ছদ্মবেশে ঠুনকো, অস্পষ্ট শ্লোগানের মিছিল। ফলে সমস্যাবলীর সংজ্ঞায়ন, চিহ্নিতকরণ ও বাছাইকরণের অক্ষমতা এবং এভাবে সঠিক সমাধান দানের ব্যর্থতা, মেকি সমস্যার সৃষ্টি, সমস্যাসমূহকে রাজনৈতিক, সামাজিক-অর্থনৈতিক ও আইনগত গণ্ডীতে সীমিতকরণ ইত্যাদি বড় হয়ে দেখা দেয়।
আধুনিক মুসলিম সমাজের বিপর্যয়ের কারণ হিসেবে আদবের পশ্চাদপসরণকে যেমন উল্লেখ করেছেন তেমনি মুসলিম সমাজের দুর্গতির জন্য একটি ভাষাতাত্ত্বিক (Semantic) ব্যাখ্যাও হাজির করেছেন। আল-আত্তাস একজন ভাষাতাত্ত্বিক। শুধু মালয় ভাষা নয়, আরবি ভাষা ও ব্যাকরণের উপরও রয়েছে তার যথেষ্ট কর্তৃত্ব। আরবি যেহেতু কুরআনের ভাষা এবং এই ভাষাতে ইসলামের মৌলিক বিশ্বাসগুলোর তত্ত্বায়ন হয়েছে, তাই এটিকে ধরে রাখা জরুরি এবং এর বিকৃতি মানে ইসলামী বিশ্বাসের বিকৃতি। আত্তাস লিখেছেনঃ
মুসলিম জাতিসমূহের ভাষাগুলোতে বিদ্যমান মৌলিক ইসলামী অভিধানে নিহিত বহু অত্যধিক গুরুত্বপূর্ণ মূল শব্দকে বর্তমানে বিকৃত করা হয়েছে এবং অবান্তরভাবে অচেনা বিদেশি শব্দ অর্থবোধক ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হচ্ছে যা অনৈসলামী জীবনদর্শন ও বিশ্বদর্শনসমূহের দিকে পিছিয়ে পড়ার নামান্তর আমি এ ঘটনাকে বলে থাকি ভাষার অনৈসলামীকরণ (Deislamization of language)।
একালে ইসলামের সাথে সংশ্লিষ্ট শব্দগুলো তার তাৎপর্য হারিয়েছে। যেমন আদবের অর্থ হয়েছে শুধুমাত্র লৌকিক ভদ্রতা, কিংবা আদলের অর্থ দাঁড়িয়েছে এক ধরনের সাম্য। কিন্তু মূলে এর অর্থ অনেক গভীর। ভাষার এই বিকৃতির ফলে মুসলমানের মন-মানসিকতায় বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়েছে এবং তাদের ভিতরকার বুদ্ধিবৃত্তিক ও আধ্যাত্মিক ঐক্য দুর্বল হয়ে পড়েছে। আত্তাস লিখেছেন,
“সঠিকভাবে ভাষা প্রয়োগের ব্যর্থতা এবং সঠিক অর্থ প্রকাশের অপারগতা সত্য ও বাস্তব অবস্থার যথাযথ প্রেক্ষাপট সম্পর্কে সচেতনতার অভাবকেই নির্দেশ করে । ওই প্রেক্ষাপটের সচেতনতা শুধু ভাষাকে বুঝাই নয়, এতে নিহিত বিশ্ব দর্শনকেও বুঝা যায় । ইসলাম যে একটি সত্যিকার আসমানী ধর্ম, সভ্যতা রূপে এর বিকাশ লাভ এবং বিশ্ব দর্শন হিসেবে সত্য ও বাস্তবতা নিয়ে এর দৃষ্টিভঙ্গি প্রভৃতি সম্পর্কে অজ্ঞতার ও মূর্খতার কারণে সংঘটিত বুদ্ধিবৃত্তিক সেকুলারাইজেশনের ব্যাপক বিস্তৃতি আমাদের বেশির ভাগ চিন্তাবিদ ও বুদ্ধিজীবী এবং তাদের অনুসারীদের আধুনিকতার পরিবর্তনশীল শ্লোগানসমূহ অনুকরণে ভীষণভাবে বিভ্রান্ত করেছে যা আমাদের মূল্যবোধ ব্যবস্থার অর্থ প্রতিনিধিত্বকারী মৌলিক পরিভাষাসমূহের অর্থ পরিবর্তন ও সীমিতকরণে ভূমিকা রাখে।
আল-আত্তাস মনে করেন ইসলাম একটি ধর্ম, একই সাথে সভ্যতা। তবে এটি হচ্ছে ওহী ভিত্তিক সভ্যতা। এটাকে তাই তিনি দীনী পরিভাষা দিয়ে বুঝাতে চান। কিন্তু পশ্চিমা সভ্যতা ওহী ভিত্তিক নয়। ধর্মকেও তারা স্বীকার করে না। পশ্চিমাদের জ্ঞানের ভিত্তি হচ্ছে ধর্মহীন যুক্তিবাদ। সুতরাং এ জ্ঞানের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা সভ্যতার বিশ্বদর্শন, বুদ্ধিবৃত্তিক জ্ঞান ও মনোবৃত্তিক ধারণা মুসলিম সমাজের মৌলিক চরিত্রে আঘাত হেনেছে। আল-আত্তাসের ভাষায়,
“আমি সাহস করেই বলছি যে, আমাদের সময়ে বৃহত্তম যে চ্যালেঞ্জটি গোপনভাবে মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে তা হচ্ছে জ্ঞানের চ্যালেঞ্জ । অবশ্য তা অজ্ঞতার বিরুদ্ধে নয়, বরং তা হচ্ছে পাশ্চাত্য সভ্যতা কর্তৃক সারাবিশ্বে দেয়া জ্ঞান।”
আমার মতে এ বিষয়টির উপর গুরুত্বারোপ করা উচিত যে, জ্ঞান নিরপেক্ষ নয় । বরং একে কোনো একটি স্বভাব বা বৈশিষ্ট্য ও বিষয়াদি দিয়ে মনের ভেতর ঢুকিয়ে দেয়া যায় যা তখন জ্ঞানের মুখোশ ধারণ করে উপস্থিত হয় ৷ বস্তুত একে সামগ্রিকভাবে গ্রহণ করা হয়, সত্য জ্ঞান হিসেবে নয়। বরং রঙিন চশমা বা কাচের ভেতর দিয়ে এর প্রকাশ ঘটে। এ জ্ঞানের ভিত্তিতেই গড়ে ওঠা সভ্যতার বিশ্বদর্শন, বুদ্ধিবৃত্তিক জ্ঞান ও মনোবৃত্তিক ধারণা বর্তমানে নিজস্ব সংগঠন ও প্রচারের প্রধান ভূমিকা পালন করছে যা নির্মিত ও প্রচারিত হয়েছে তা হচ্ছে উক্ত সভ্যতার স্বভাব ও ব্যক্তিত্ব বিশিষ্ট জ্ঞান । এ জ্ঞানকে এমন চাতুর্য ও ছদ্মবেশের সাথে তুলে ধরা হয়েছে যে, অসচেতন লোকেরা মনে করবে যে, তাই বাস্তব জ্ঞান।
আজকের দিনে মুসলিম সমাজের সেকুলারাইজেশন হচ্ছে ইসলামের জন্য সবচেয়ে বড় দুর্যোগের কারণ- এটা আল-আত্তাস আমাদের চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়েছেন এবং পশ্চিমা সভ্যতাকে তার নিজের জায়গায় রেখেই বিশ্লেষণ করেছেন। তিনি মনে করেন পশ্চিমাদের জ্ঞান বাস্তব সম্মত ও অব্যর্থ হওয়ার ভান করলেও তা নিছক দ্বিধা, দ্বন্দ্ব ও উৎপাদন করেছে মাত্র। পশ্চিমা জ্ঞান মানুষকে মনে করে বড় জোর একটি বুদ্ধিবৃত্তিক প্রাণী। আর এই প্রাণীর বুদ্ধিবৃত্তিক ক্ষমতাকেই জীবন ও পৃথিবীর সব রকমের গূঢ়তত্ত্ব আবিষ্কারের প্রধান হাতিয়ার হিসেবে বেছে নেয়া হয়েছে এবং এভাবেই সংগৃহীত তথ্য ও উপকরণাদি দিয়ে পশ্চিমারা জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করতে চায় ।
ফলে এখানে নিশ্চয়তা বলে কিছু নেই, সবই সম্ভাব্য। কিন্তু ইসলামে সম্ভাব্যতার পাশাপাশি নিশ্চয়তারও স্থান রয়েছে। সেই নিশ্চয়তাকে ইসলামী পরিভাষায় বলা হয় ইলমুল ইয়াকিন। এই জ্ঞান হচ্ছে আধ্যাত্মিক জ্ঞান। ইসলাম এই জ্ঞানকে জাগতিক জ্ঞানের সাথে সমন্বয় করে মানুষের জন্য মুক্তিতত্ত্ব হাজির করেছে। আধুনিক পাশ্চাত্যের জ্ঞানতাত্ত্বিক কাঠামোর বাইরে এসে আল-আত্তাস এই ইলমুল ইয়াকিন ভিত্তিক বিকল্প বয়ান- Counter discourse হাজির করেছেন। মুসলিম ভাবজগতে আল-আত্তাসের এটাই হচ্ছে সবচেয়ে বড় অবদান।
চার.
সেকুলারাইজেশনকে আল-আত্তাস এক ধরনের De-islamization (বি-ইসলামীকরণ) হিসেবে সাব্যস্ত করেন। এটি মুসলিম সমাজের Colonization (উপনিবেশিকরণ) প্রক্রিয়ার ফল হিসেবে সম্ভবপর হয়েছে। আত্তাস বি-ইসলামীকরণকে ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে,
“Deislamization is the infusion of alien concepts into the minds of Muslims, where they remain and influence thought and reasoning. It is the causing of forgetfulness of Islam and of the Muslim’s duty to God and to His Messenger, which is the real duty assigned to his true self and hence it is also injustice to the self. It is tenacious adherence to pre-islamic beliefs and superstitions, and obstinate pride and ideologization of one’s own preislamic cultural traditions, or it is also secularization.”
মুসলিম সমাজে পশ্চিমা আধিপত্য ও জ্ঞান বিস্তারের নেতিবাচক দিকগুলো নিয়ে আল-আত্তাস বিস্তর ভেবেছেন এবং প্রচুর লেখালেখিও করেছেন। তার লেখা Islam, Secularism and the Philosophy of the Future ও Islam and Secularism এ যাবৎ মুসলিম জগতের পক্ষ থেকে পশ্চিমা জ্ঞান ও তার আগ্রাসীরূপের মোকাবেলায় এক বুদ্ধিবৃত্তিক জওয়াব । এখানে তিনি দেখানোর চেষ্টা করেছেন পশ্চিমা জ্ঞান কীভাবে মুসলিম সমাজের তৌহিদী ঐক্যকে ভেঙে চুরমার করে ফেলেছে । তার ওহীভিত্তিক জ্ঞানতাত্ত্বিক কাঠামো নাড়িয়ে দিয়েছে । যার ফলে মুসলিম সমাজে বিভ্রান্তি, সংশয়, স্বেচ্ছাচারিতা ও নানা রকমের দুর্নীতির সয়লাব চলেছে।
সেকুলারাইজেশন মুসলমানের ধর্ম, সংস্কৃতি, রাজনীতি, আইন, বিচার ব্যবস্থা, বিশ্বাস, মূল্যবোধ, বিনোদন সবকিছুকে কব্জা করে ফেলেছে। সেকুলারাইজেশনের এই গতি ও মাত্রাকে তারা নাম দিয়েছে Disenchantment of nature, Desacralization of Politics ও Deconsecration of values । এর লক্ষ হচ্ছে সমাজে-সংস্কৃতিতে সবরকমের ধর্মীয় প্রভাবের একরকম বিলুপ্তি । এটি তারা করতে চায় ধর্ম ও আখেরাতমুখী বিশ্ব দর্শনকে প্রভাবহীন করে দেয়ার লক্ষ্যে যার ফলে মানুষ এক পরিবর্তনমান প্রক্রিয়ার মধ্যে নিমজ্জিত হয় এবং ধীরে ধীরে তাদের দাবি অনুযায়ী পরিপক্ক হয়ে উঠতে পারে। কিন্তু ইসলাম এই ধরনের পরিবর্তন, উন্নতি ও প্রগতিকে অনুমোদন করে না। বরং ইসলামের কাছে প্রগতির মানে হচ্ছে রসুল (সঃ)-এর দেখানো ইসলামের ফলিত রূপের দিকে প্রত্যাবর্তন । এই কারণেই আল-আত্তাস ধর্মনিরপেক্ষতাকে পুরোপুরি ইসলামী বিশ্বাসের এক বিপরীত পন্থা হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। তার ভাষায়,
“Not only is secularization as a whole the expression of an utterly unislamic world view, it is also set against Islam, and Islam totally rejects the explicit as well as implicit manifestation and ultimate significance of secularization, and Muslims must therefore vigorously repulse it wherever it is found among them and in their minds, for it is as deadly poison to true faith.”
মুসলিম সমাজের ধর্মনিরপেক্ষ পুরুষরা একটি ধর্মনিরপেক্ষ ইসলাম গড়তে চায় । এরা মুসলিম সমাজে জন্মগ্রহণ করেও ইসলামের রীতিনীতি, আইনকানুনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল নয় বরং পশ্চিমা সভ্যতার বিশ্বাস ও মূল্যবোধগুলোকেই তারা নিজেদের জন্য যেমন আদরণীয় করে তুলেছে তেমনি এটি তারা জবরদস্তিমূলকভাবে সমাজের অন্য অংশের উপরও চাপিয়ে দিতে চায়। মুসলিম ইতিহাসের অগ্রণী পুরুষরা আর এদের অনুপ্রেরণাস্থল নয়। রুশো, কমতে, মিল, স্পেনসার, মার্কস হচ্ছে পথ প্রদর্শক । এদের চিন্তার কেন্দ্রে ইসলাম নেই । উল্টো এদের চিন্তার মধ্যে ইসলামকে তালুবন্দী করতে চায়। তারা মুসলিম হিসেবে দাবি করলেও পশ্চিমাদের প্রতি তাদের আনুগত্য । সংখ্যায় কম হলেও পশ্চিমাদের সাথে ওঠাবসার কারণে এরা অত্যন্ত প্রভাবশালী এবং সমাজের নিয়ন্ত্রণ কতকটা তাদের হাতেই চলে গেছে । যতক্ষণ না তারা তাদের চিন্তাভাবনার পরিবর্তন ঘটাচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত মুসলিম সমাজের জন্য এরা বড় রকমের হুমকি হিসেবে রয়ে যাবে । মুসলিম সমাজের এই সমস্যার জন্য আল-আত্তাস ইসলামী শিক্ষার অনুপস্থিতি এবং ঔপনিবেশিক শিক্ষা বা পশ্চিমা শিক্ষার কুফলকে দায়ী করেছেন এটি মুসলমানের ভাব জগতে বিকৃতি ও বিভ্রান্তি সৃষ্টি করেছে মাত্র এবং আদবের অবক্ষয় ঘটিয়ে দিয়েছে । এ অবস্থাটাকে আল-আত্তাস সংক্ষেপে এভাবে বর্ণনা করেছেনঃ
“Our present general dilemma is caused by
1.Confusion and error in knowledge,
creating the condition for
2. The loss of adab within the Community.
The condition arising out of (1) and (2) is
3. The rise of leaders who are not qualified for valid leadership of the Muslim Community, who do not possess the high moral, intellectual and spiritual standards required for Islamic leadership, who perpetuate the condition in (1) above and ensure the continued control of the affairs of the community by leaders like them who dominate in all fields.”
এই নেতারাই আজকের মুসলিম সমাজের কর্ণধার এবং এরা তাদের ক্ষমতাকেন্দ্রিক কায়েমি স্বার্থকে বিভিন্ন নামে ও মুসলিম সমাজের স্বার্থ বলে চালিয়ে দিচ্ছে । তাতে সমস্যার সমাধান মিলছে না। উল্টো মুসলিম সমাজ এক প্রবল ঘূর্ণাবর্তের দিকে ধেয়ে চলেছে। আদবের অবক্ষয় শুধু জ্ঞানের অবক্ষয় ঘটায়নি । সত্যিকার নেতৃত্ব চিহ্নিতকরণ ও নির্বাচনের ক্ষমতাও লুপ্ত করে দিয়েছে।
পাঁচ.
মুসলিম সমাজের পচনরোধের কি কোনোই উপায় নেই? আল-আত্তাস মনে করেন মন ও সমাজের জন্য এই মুহূর্তে জরুরি প্রয়োজন হচ্ছে এর decolonization বা বি-উপনিবেশীকরণ এবং একই সাথে de-westernization (অপশ্চিমীকরণ)। ঔপনিবেশিক শক্তির জোরে যে জ্ঞান আমরা এতদিন প্রকৃত জ্ঞান বলে হজম করেছি, আত্তাস মনে করেন সেটি আসলে প্রকৃত জ্ঞান নয় । সেটি মূলতঃ পশ্চিমা সংস্কৃতি ও মূল্যবোধ জারিত জ্ঞান, যা প্রকৃতপক্ষে পশ্চিমাদের স্বার্থেই নিবেদিত। আল-আত্তাস লিখেছেন,
“So that the knowledge that is now systematically disseminated throughout the world is not necessarily true knowledge, but that which is imbued with the character and of western culture and civilization, and charged with its spirit and geared to its purpose.”
মুসলিম জগতে প্রতিষ্ঠিত একালে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর উদাহরণ দিয়ে আত্তাস বলেছেন, এটা আসলে পশ্চিমা জ্ঞানচর্চার পরিপুরক কেন্দ্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে । এটার উদ্দেশ্য এমন ধরনের মানুষ তৈরি করা যার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে : rational animal devoid of soul, like a circle with no centre.
এটা বিশ্বজনীনতার ভান করলেও এটার কোনো বৈশ্বিক উদ্দেশ্য নেই। যেমন নেই চূড়ান্ত কোনো নীতিগত উদ্দেশ্য । এর সবকিছুই সম্ভাব্য ও জায়মান । কারণ সেকুলার জ্ঞানতত্ত্ব প্রকৃতি ও সমাজকে নিয়ন্ত্রণ করবার এবং জৈবিক প্রয়োজন পূরণের লক্ষ্যে পরিচালিত। কিন্তু এর বাইরে যে একটি ঐশী ব্যবস্থাপনা রয়েছে যে ব্যবস্থাপনা মানুষকে মানুষ হিসেবে নির্মাণ করতে চায় সেটি এখানে অনুপস্থিত । ইসলাম যেমন মনে করে সকল জ্ঞানের উৎস হচ্ছে আল্লাহতায়ালা এবং এই জ্ঞান হবে শিক্ষা ব্যবস্থার ভিত্তি সেটা আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলো দিতে অক্ষম । এ কারণে এসব বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা দক্ষ মানুষ হলেও বিভ্রান্ত মানুষ। কারণ তাদের সামনে জাগতিকতার বাইরে কিছু নেই। তাই জ্ঞান সম্পর্কে ইসলামের ধারণার সাথে পশ্চিমা দার্শনিকদের ধারণার মধ্যে মৌল তফাৎ রয়েছে। সেই তফাতের দিকটা আল-আত্তাস এভাবে তুলে এনেছেন :
“Thus we see that, already in this most fundamental concept in life the concept of knowledge- Islam is at variance with Western civilization, in that for Islam (a) knowledge includes faith and true belief (iman ); and that (b) the purpose for seeking knowledge is to inculcate goodness or justice in man as man and individual self, and not merely in man as citizen or integral part of society it is man’s value as a real man, as spirit, that is stressed, rather than his value as a physical entity measured in terms of the pragmatic or utilitarian sense of his usefulness to state and society and the world.”
এই কারণে আল-আত্তাস শিক্ষা ব্যবস্থায় ইসলামীকরণের উপর জোর দেন। কারণ ভাবজগতে পরিবর্তন না ঘটলে বি-উপনিবেশীকরণ সম্ভব নয়। আর সেটি সম্ভব না হলে মুসলিম জগতের অসুস্থতার নিরাময় হবে না। জ্ঞানের ইসলামীকরণ বলতে তিনি বুঝিয়েছেন:
“The islamization of knowledge means the deliverance of knowledge from its interpretations based on secular ideology and from meanings and expressions of the secular”
জ্ঞানের ইসলামীকরণ করতে হলে প্রথমে শিক্ষা ব্যবস্থায় পশ্চিমা প্রভাবের দিকগুলো অপসারণ করতে হবে। বিশেষ করে মানবিক জ্ঞানকে পশ্চিমা প্রভাবমুক্ত করতে হবে । তারপরে ইসলামী জ্ঞান ও মানবিক জ্ঞানের সমন্বয় করে শিক্ষা ব্যবস্থা। গড়ে তুলতে হবে। এ ব্যাপারে জ্ঞানের ইসলামীকরণের একটি মৌলিক নীতিও তিনি হাজির করেছেন যেটা এরকম-
১ ইসলামী প্রেক্ষাপটে তুলনামূলক ধর্মতত্ত্ব ।
২. ইসলামী প্রেক্ষাপটে পশ্চিমা সংস্কৃতি ও সভ্যতাকে বুঝা।
৩. ইসলামী জ্ঞানের ভাষা আরবির উপর দক্ষতা ।
৪. ইসলামী ধর্মতত্ত্ব, সংস্কৃতি, সভ্যতা, ইসলামী জ্ঞানের দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক রূপ ও পটভূমি এবং বিশ্ব ইতিহাস হিসেবে ইসলাম অধ্যয়ন।
আল-আত্তাস মনে করেন শিক্ষা ব্যবস্থায় এই ইসলামী বৈশিষ্ট্যকে যদি কার্যকরী করা যায় তাহলেই আমরা ঔপনিবেশিকতার কুফল থেকে মুক্তিপাবো এবং সমাজের ইসলামীকরণ বলতে যা বুঝায় তা তখন দৃশ্যমান হবে। সেকুলারাইজেশনের বিপরীতে তিনি ইসলামীকরণের একটি চমৎকার সংজ্ঞা দিয়েছেন যা তার উত্তর ঔপনিবেশিক চিন্তাভাবনার একটি উজ্জ্বল হীরক খণ্ড বলা যায়। এটি হচ্ছে,
“Islamization is the liberation of man first from magical, mythological, animistic, national-cultural tradition, and then from secular control over his reason and his language.”
আল-আত্তাস মুসলিম সমাজের সেকুলারাইজেশনের বিরুদ্ধে কলম ধরেছেন । তিনি জ্ঞান জগতে এক সর্বাত্মক ইসলামী বিপ্লব চান সত্য কিন্তু তিনি কি কোনো ইসলামী রাষ্ট্র চান আজকের ইসলামবিদদের যা আরাধ্য। আল-আত্তাস তার দীর্ঘ জীবনের লেখালেখিতে ইসলামী রাষ্ট্রের কোনো রূপকল্প তুলে না ধরলেও, ইসলামী রাষ্ট্র তার মনোরাজ্যে ছায়াপাত করেছে। ইসলাম তার কাছে একই সাথে ধর্ম ও সভ্যতা আবার যেমন ব্যক্তিগত ধর্ম তেমনি সামাজিক ধর্মও বটে। আল-আত্তাস লিখেছেন:
ইসলাম যেমন ব্যক্তিগত ধর্ম তেমনি সামাজিক ধর্ম । একই দীন বা আসমানী ধর্ম ব্যক্তি মানুষকেও জীবন বিধান দিয়েছে আবার সামগ্রিকভাবে সমাজবদ্ধ মানুষগুলোর জন্যও বিধি-বিধান নিয়েছে। প্রকৃতপক্ষে ইসলাম ধর্ম ব্যক্তি ও সমাজকে বিভক্ত করে দেখে না। ব্যক্তিগত ধর্ম ও সামাজিক ব্যবস্থা এখানে ভিন্ন ও আলাদা নয় । একটি আরেকটির সম্পূরক ও পরিপূরক এবং অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। ইসলামের ব্যক্তিগত বিধি-বিধান সমাজের প্রতিটি ব্যক্তির জন্য যেমন প্রযোজ্য তেমনি সামাজিক বিধি বিধান বা ব্যবস্থাও প্রতিটি মানুষের জন্য প্রযোজ্য। একই ইসলাম ব্যক্তি ও সমাজকে লক্ষ করেই প্রদত্ত হয়েছে।
আল আত্তাস তাই ইসলামকে দীন হিসেবে দেখেন এবং দীন শব্দ দিয়ে ইসলামকে সভ্যতা হিসেবে বুঝার চেষ্টা করেন। এ ব্যাপারে তার একটি ভাষাতাত্ত্বিক ব্যাখাও রয়েছে। দীন শব্দটা মদীনা শব্দের সাথে জড়িত। যা জড়িত তমুদ্দুন শব্দের সাথে। আর তমুদ্দুন মানে হচ্ছে সভ্যতা। সে দিক দিয়ে চিন্তা করলে দীন শব্দের ভিতর ইসলামী সভ্যতাই প্রতিফলিত হয়।
এরকম একটা ব্যবস্থা বা সভ্যতা তাই শেষ বিচারে রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার দিকে এগুবে এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু সেই রাষ্ট্র কিরকম হবে আল-আত্তাস সেটা লিখেছেন:
ইসলামের সমাজ ব্যবস্থা হচ্ছে পৃথিবীতে আল্লাহতায়ালার রাজ্য । কারণ এ ব্যবস্থায় চূড়ান্ত সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী হচ্ছেন আল্লাহ, মানুষ নয়। তাঁর আদেশ-নিষেধ, আইন-কানুন ও বিধি বিধানেরই সর্বোচ্চ প্রভাব ও প্রাধান্য। মানুষ কেবল তার খলিফা বা প্রতিনিধি যাকে পরিচালনার ট্রাস্ট বা আমানত দেয়া হয়েছে । সে আল্লাহর ইচ্ছা ও সন্তুষ্টি অনুসারে প্রশাসন চালাবে ।
কিন্তু মুসলিম সমাজে যদি এরকম রাষ্ট্রের উপস্থিতি নিশ্চিত না হয় তাহলে আল-আত্তাস মুসলমানদের করণীয় সম্পর্কেও দিক নির্দেশ করেছেন :
যদি তেমনটি না হয় তাহলে ইসলামী ব্যক্তির দায়িত্ব হচ্ছে এমন রাষ্ট্র ও সমাজের বিরোধিতা এবং এমন বিভ্রান্ত সমাজকে সংশোধনের জন্য চেষ্টা চালানো।
তবে এটা মনে করা সংগত আল-আত্তাস যে ধরনের রাষ্ট্রের কথা বলেছেন তা মানবিকতা বর্জিত কৃত্রিম ও আইনের বেড়াজালে আটকানো রসকসহীন কোনো রাষ্ট্র নয় । এ কারণে আল-আত্তাস মুসলমানদেরকে তাসাউফের গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতন করেছেন । তাসাউফ হচ্ছে ইসলামের সেই ধারা যার মূল কথা হচ্ছে মানুষের সাথে স্রষ্টার অন্তরঙ্গতা এবং মানুষে মানুষে অন্তরঙ্গতা । এই নিবিড়তার সম্পর্ক আল-আত্তাস ফিরিয়ে আনার কথা বলেছেন যাতে ইহসানই (মনুষ্যত্ব) শেষ পর্যন্ত বিজয়ী হয়। আল-আত্তাসের ইসলামী রাষ্ট্র তাই ইহসান বর্জিত নয়। অবশ্য আল-আত্তাস যথেষ্ট সচেতন তাসাউফের নামে মুসলিম সমাজে অনেক ধরনের বিদআত ও বিকৃতি ঢুকে পড়েছে। এটাকে তিনি বিশুদ্ধ তাসাউফ চর্চার প্রতিবন্ধক হিসেবে মনে করেন। এর উদাহরণ হিসেবে তিনি তাসাউফকে নির্ভর করে কোনো কোনো তাত্ত্বিক যেমন প্রচার করেছেন উচ্চতম ঐশী পর্যায়ে ধর্মসমূহের একতার (Transcendent unity of religions) তত্ত্ব তাকে তিনি বিভ্রান্তিমূলক বলেছেন। কারণ তিনি মনে করেন ঐশী পরিকল্পনা অনুযায়ী পৃথিবীতে একটির পর একটি ধর্ম এসেছে এবং সেই ধারাবাহিকতায় ইসলামকে সবশেষ ও পরিপূর্ণ ধর্ম হিসেবে সাব্যস্ত করা হয়েছে এই ধর্মের বাণী কোনো গোত্রের জন্য নয়, বরং সমগ্র মানবজাতির জন্য এর আগমন। এর বাইরে আর কোনো ঐক্যের প্রয়োজন নেই । ধর্ম নির্বিশেষে মানুষে মানুষে সম্প্রীতি থাকা উচিত । ধর্মের ঊর্ধ্বে ধর্মসমূহের একতার কথা উদ্দেশ্যমূলকভাবেই প্রচার করা হয়েছে।
ছয়.
সৈয়দ নকীব আল-আত্তাস হচ্ছেন সত্যিকার অর্থেই একালে জ্ঞানের ইসলামীকরণ তত্ত্বের এক অন্যতম নকীব। বিশেষ করে শিক্ষা ক্ষেত্রে তার মূল্যবান চিন্তাভাবনা মৌলিকত্বের দাবি রাখে।
একালে মুসলিম শিক্ষা ব্যবস্থার সংকটকে তিনি নিপুণভাবে চিহ্নিত করেছেন । শুধু তাই নয় সংকট মুক্তির জন্য তিনি প্রচলিত শিক্ষা প্রকল্পের বাইরে মুসলিম সমাজ ও সংস্কৃতির প্রেক্ষাপটকে সামনে রেখে বিকল্প ইসলামী শিক্ষার মডেলকে হাজির করেছেন। মুসলিম জগতে আজকে যারা পশ্চিমা আধিপত্য মোকাবেলার জন্য পশ্চিমা জ্ঞানতাত্ত্বিক বয়ানের বাইরে নতুন বয়ান হাজির করার কথা বলছেন তাদের কাছে আল-আত্তাস এক অনিঃশেষ প্রেরণার জায়গা হতে পারেন।
আল-আত্তাসের চিন্তার আরেকটি দিক হলো মুসলিম জ্ঞান তত্ত্বে আদবের স্থানকে কেন্দ্রীয় স্থানে নিয়ে আসা। আদব শব্দের ভিতর দিয়ে তিনি যেভাবে তার চিন্তাভাবনাকে প্রকাশ করেন তার পিছনে সুফীদের সাধন প্রক্রিয়ার একটা প্রভাব দেখা যায় এবং তার ভাবনায় সুফীবাদ যে একটা বড় রকমের শিহরণ তুলেছে তাতে সন্দেহ নেই । এই পৃথিবীতে মানুষের অস্তিত্ব আল্লাহর দান এবং এই কারণে মানুষের উচিত ক্রমাগতভাবে আল্লাহর প্রতি শুকরিয়া আদায় করা- সুফীরা মনে করেন এটাই মানুষের সবচেয়ে বড় আদব । এই জন্যই আল-আত্তাস বলতে পারেন মুসলমানরা রুশোর Social Contract দ্বারা আবদ্ধ নয়। মানুষ পৃথিবীতে অস্তিত্ববান হবার আগে রুহানী জগতে সব মানুষের আত্মা আল্লাহকে রব হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছিল। আল্লাহর সাথে মানুষের এই চুক্তির কথা স্মরণ করিয়ে তিনি বলেছেন, মানুষের জন্য সবচেয়ে বড় আদব হচ্ছে এই চুক্তির বরখেলাফ না করা। আত্তাস লিখেছেন :
“The man of Islam is not bound by the social contract, nor does he spouse the doctrine of the social contract.”
আব্বাসের এই চিন্তার সাথে ব্রিটিশ মুসলিম সুফী চার্লস লা গায় ইটনের চিন্তার একটা মিল দেখা যায়। তিনিও আদবকে ইসলামী নীতির সারাৎসার হিসেবে দেখেছেন এবং আল্লাহর প্রতি শুকরিয়া আদায়কে মানুষের সবচেয়ে বড় আদব হিসেবে উল্লেখ করেছেন।
এইভাবে একজন মালয় সুফী আল্লাহর সামনে দাঁড়িয়ে আর একজন ব্রিটিশ সুফীর সাথে একাকার হয়ে গেছেন এবং আল্লাহর প্রতি শুকরিয়া আপন করে তারা তাদের কৃতজ্ঞতার অশ্রুমাল্য হাজির করেছেন ।
হদিসঃ
- Syed Muhammad Naquib Al – Attas, The Concept of Education in Islam, Kualalampur Muslim Youth Movement of Malaysia, 1980.
- সাইয়েদ মুহাম্মদ নাকিব আল-আত্তাস (অনুবাদ: মুহাম্মদ ফরিদ উদ্দিন খান), ইসলামী বিশ্বদর্শনের রূপরেখা । ঢাকা : র্যামন পাবলিশার্স, ২০০৯।
- Syed Muhammad Naquib Al-Attas, Islam, Secularism and the Philosophy of the Future, New York Mansell Publishing Limited, 1985.
- Syed Muhammad Naquib Al-Attas, Islam and Secularism, Kualalampur International Institute of Islamic Thought and Civilization, 1993.
- Syed Muhammad Naquib Al-Attas, Islam, Secularism and the Philosophy of the Future.
- সাইয়েদ মুহাম্মদ নাকিব আল-আত্তাস, ইসলামী বিশ্বদর্শনের রূপরেখা।
- Halstead, J. M. (2004), An Islamic Concept of Education’, Comparative Education Vol 40, No. 4, 517-529.
- Syed Muhammad Naquib Al-Attas, Islam, Secularism and the Philosophy of the Future.
- Gai Eaton, A Bad Beginning and the Path to Islam. Cambridge Archetype, 2010.