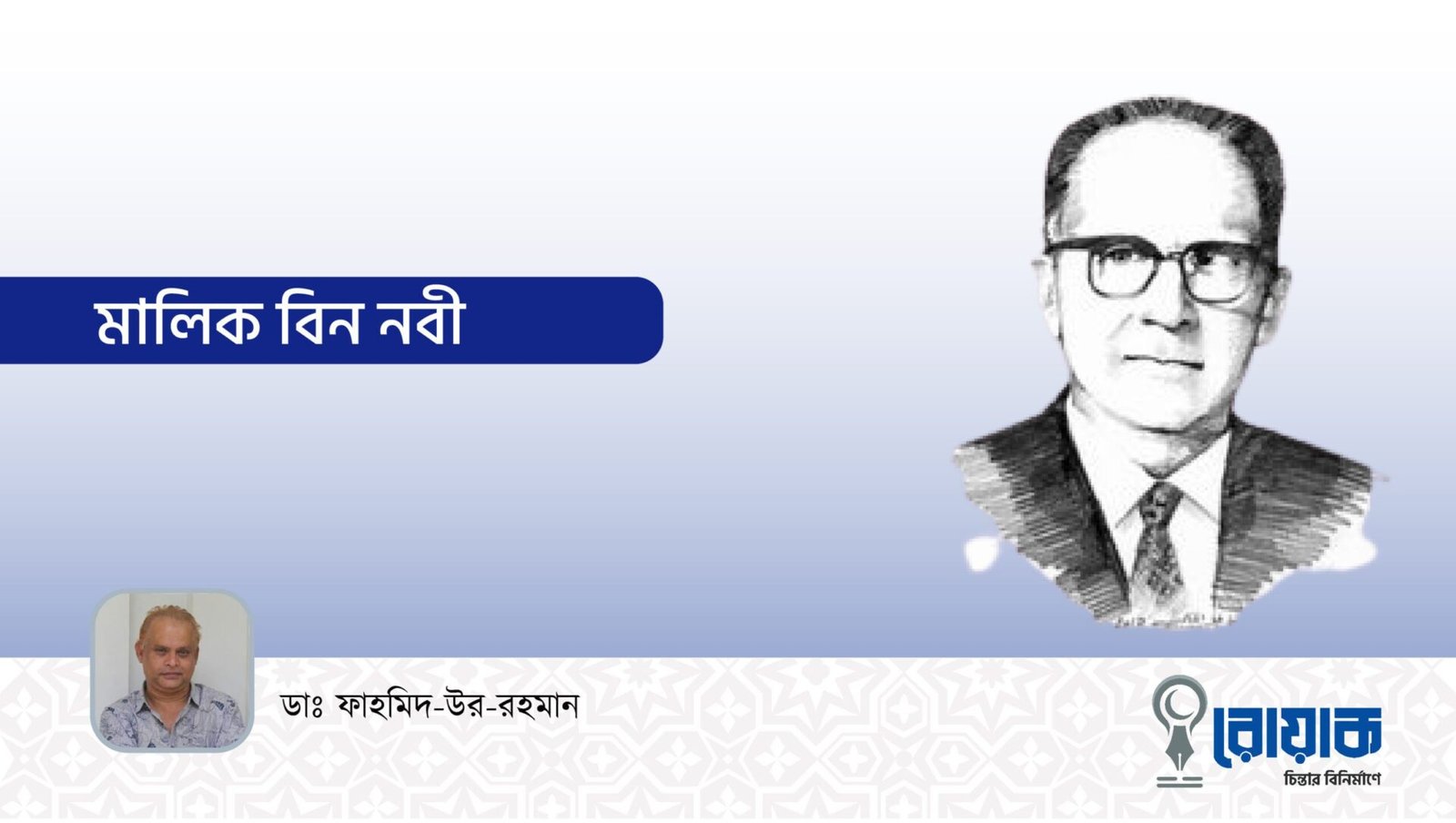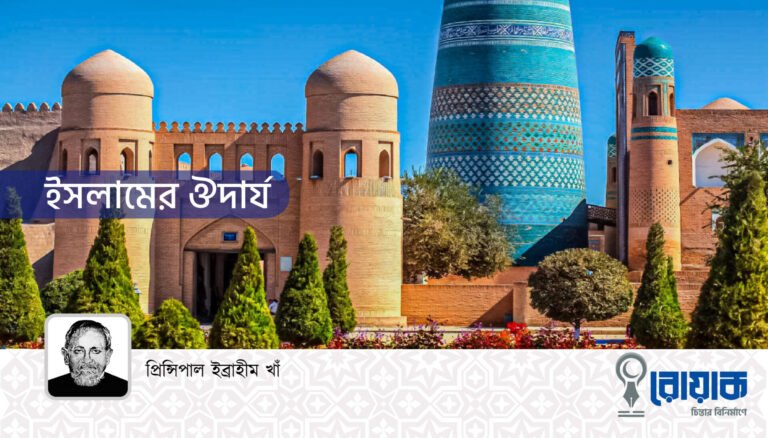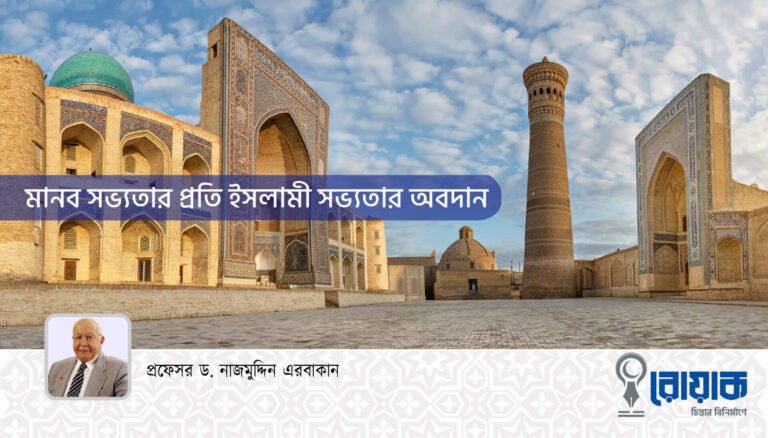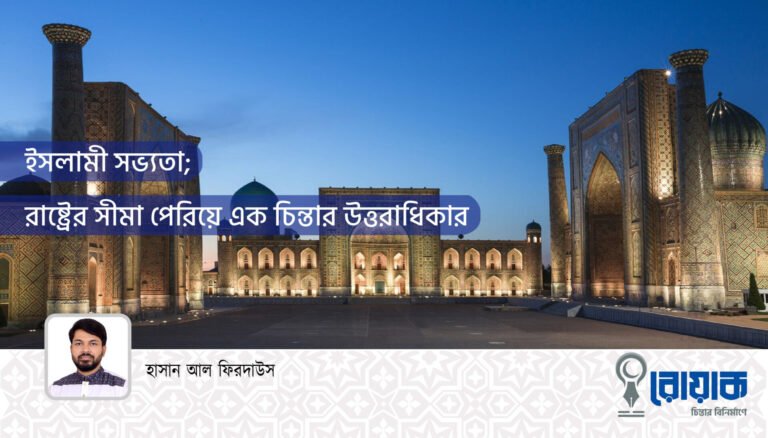আলজেরিয়ার দার্শনিক, সমাজবিজ্ঞানী বুদ্ধিজীবী মালিক বিন নবীর নাম বাংলাদেশে আমরা তেমন একটা কেউ জানি না। ফরাসী ঔপনিবেশিকতার বিরুদ্ধে আলজেরিয়ার মুক্তি সংগ্রামের এই অকুতোভয় তাত্ত্বিক পুরুষকে এ কালের আরব দুনিয়ার প্রধান দার্শনিক ও সমাজ বিজ্ঞানীর মর্যাদা দেয়া যায়। যদিও তার খ্যাতি ও যোগ্যতা এখনও অপরিচয়ের অন্ধকারেই ডুবে আছে। তার এই স্বল্প পরিচয়ের একটা প্রধান কারণ হচ্ছে তিনি প্রধানতঃ ফরাসী ভাষায় লেখালেখি করেছেন। যার তরজমা বিশেষ করে ইংরেজি ও আরবীতে আজও অপ্রতুল রয়ে গেছে। মুসলিম চিন্তার জগতে তার যথাযথ স্বীকৃতি না পাওয়ার এটা একটা অন্যতম কারণ হতে পারে।
কিন্তু তারচেয়েও বড় কারণ মনে হয় ইসলামপ্রধান জনগোষ্ঠীর নিজস্ব সমস্যা, নানাবিধ ঐতিহাসিক সংকট, সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলোর ভয়ানক শত্রুতা, সর্বোপরি মুসলিম সমাজের অজ্ঞতা, কৃপমন্ডুকতা ও মোহাচ্ছন্নতা এমন স্তরে পৌঁছেছে যে, মুসলমানরা আজ নিজেদের মঙ্গলের পথ নিজেরাই চিহ্নিত করতে পারছে না। মালিক বিন নবীর চিন্তা ও দর্শনকে যথাযথভাবে তুলে ধরার দায়িত্ব ছিল মুসলমানদের। বিশেষ করে তার স্বভূমি আলজেরিয়ার মানুষের, সেখানকার সরকারের। কিন্তু সেই কাজটিই যথাযথভাবে হয়নি। সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আলজেরিয়ার মুক্তি সংগ্রামে অনেক বুদ্ধিজীবি, সংস্কৃতিসেবীর ভূমিকার কথা আমরা জানি। বিশেষ করে বামধারার বুদ্ধিজীবীরা সেসময় আলজেরিয়ার মুক্তি আন্দোলনের স্বপক্ষে বেশ ভূমিকা রেখেছিলেন। যেমন ফ্রানজ ক্যানন, একবাল আহমদ প্রমুখ। কিন্তু এই ধারা যে ভূমিকাই পালন করুক না কেন তা ছিল অধিকতর দুর্বলতার ধারা এবং আলজেরিয়ার মূল স্রোত থেকে দূরে। সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আলজেরিয়ার মুক্তি সংগ্রামে ইসলাম এক ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেছিল। যেমন পালন করেছিল আমাদের এই উপমহাদেশে। সেই ঐতিহাসিক ভূমিকার পটভূমিতেই মালিক বেনারী তার সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী দার্শনিকতার ভিত প্রস্তুত করেছিলেন। কিন্তু আলজেরিয়ার মুক্তি সংগ্রামের ট্রাজেডী হলো অন্যান্য অনেক মুসলিম রাষ্ট্রের মতো ঔপনিবেশিকতার শিকল থেকে বেরিয়ে আসার পর আলজেরিয়া সেকুলার জাতিরাষ্ট্রের ধারণার দিকে ঝুঁকে পড়ে। ইসলামকে অবলম্বন করে যে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে আলেজেরিয়ার মানুষ একদিন বিজয়ী হয়েছিল, তারাই স্বাধীনতা পরবর্তীকালে সাম্রাজ্যবাদের ফেলে যাওয়া নীতি ও দর্শনের ফাঁদে ও ধন্ধে পড়ে যায়। সেকুলারিজম হয় নতুন স্বাধীন রাষ্ট্রের মূলমন্ত্র। আজও আলজেরিয়া এই সংকট ও টানাপড়েন থেকে রেহাই পায়নি। স্বাভাবিকভাবেই মালিক বেন্নাব পরিস্থিতিতে উপেক্ষা ছাড়া তেমন কিছু পাননি।
বিন নবীকে চেনা ও তার কর্মকান্ড এবং চিন্তার সঙ্গে পরিচিত হওয়ার আগে মানুষটি কি অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে বড় হয়েছেন সেটা জানার দরকার আছে। ফিলিস্তিনের অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে যেমন এডওয়ার্ড সাঈদ ও ঈসমাইল রাজী আল ফারূকীকে পাঠ করতে হয় তেমনি বিন নবীকে বুঝতে হবে আলজেরিয়ার ইতিহাসের ভিতর থেকে। আলজেরিয়ার মুক্তি আন্দোলন ও তার রক্তাক্ত অধ্যায়ের ভিতরে বিন নবীর মুখ লুকিয়ে আছে। সাম্রাজ্যবাদের সাথে আলজেরিয়ার মুখোমুখি হওয়ার অভিজ্ঞতা এক অভূতপূর্ব ঘটনা। এই অভিজ্ঞতার দুঃখবহ স্মৃতিকে আলজেরিয়া যেমন তার ভিতরে ধারন করেছে, তেমনি এর ফলদায়ক ও আশাবাদী দিকটিও আলজেরিয়ার শিরে কখনো কখনো ঝলসে উঠেছে। মালিক বিন নবী মনস্তাত্ত্বিক ও আদর্শগতভাবে এসব অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে অগ্রসর হয়েছেন। তার চিন্তার বিবর্তনও ঘটেছে আলজেরিয়ার এই বৈপ্লবিক টানাপড়েনের ভিতর দিয়ে। জীবনের অভিজ্ঞতাই তাকে দার্শনিকতা ও বুদ্ধিজীবিতার মধ্যে টেনে নিয়ে গেছে ।
মালিক বিন নবী তার জন্মের পর বড় হয়ে ওঠার অভিজ্ঞতা, সেই সাথে তার রাজনৈতিক সামাজিক ও সাংস্কৃতিক চিন্তার বিবর্তনের কথা আমাদের শুনিয়েছেন তার অসাধারণ সুখপাঠ্য আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ The Memoirs of the Witness of the Century তে। তার জন্ম ১৯০৫ সালে পূর্ব আলজেরিয়ার কনস্টানটাইন শহরে। নিজের জন্মের মুহূর্তকে তিনি এক ভাবুকতার সাথে বর্ণনা করেছেন “The current of consciousness was connected to the past with its last witnessess, and to the future with its first architects.” তিনি তার জন্মের শহরে বসে দেখেছিলেন এক অতীত হারিয়ে যাচ্ছে এবং আর এক ভবিষ্যৎ উদিত হতে চলেছে। বিন নবীর বাপ-দাদারা ছিলেন গরীব। এই গরিবিকে আরো নির্মম করে তুলেছিল ঔপনিবেশিক শাসন। বিন নবী তার নানীর কাছ থেকে প্রথম উপনিবেশের হৃদয়হীনতার কথা শুনেছিলেন। কিভাবে ফরাসী সৈন্যরা তাদের শহর দখল করে নেয় আর সবকিছু শুঁড়িয়ে দেয় তার রক্তাক্ত ইতিহাস। কিভাবে মুসলমানরা তাদের পরিবারকে রক্ষার জন্য শহর থেকে পালিয়ে যায় আর কিভাবে অসহায় পিতারা তাদের কুমারী কন্যাদের অসম্মান থেকে বাঁচানোর জন্য দড়ি দিয়ে বেঁধে পানিতে ভাসিয়ে দেয় তার গা শিউরে ওঠা যত কাহিনী। বিন নবী এতে মুষঢ়ে পড়েননি। ফরাসী নির্মমতার দুঃখ তিনি একাকী বয়ে বেড়িয়েছেন এবং এই দুঃখই তাকে পথ দেখিয়েছে ভবিষ্যতের, শক্তি যুগিয়েছে প্রতিরোধের।
বিন নবী মেধাবী ছাত্র ছিলেন। তার পিতা ক্ষুদে সরকারি চাকুরে হওয়া সত্ত্বেও ছেলের মেধা আঁচ করে তাকে স্থানীয় আল জালিস স্কুলে ভর্তি করেন। এই সময় বিন নবীর দাদা। ত্রিপোলিতে ইটালির সৈন্য ঢুকে পড়ায় কনস্টানটাইনে ফিরে আসেন এবং পৌত্রের মনের উপর বড় রকমের প্রভাব ফেলেন। তিনি তাকে তুর্কী খেলাফতের প্রতি আগ্রহী করে তোলেন যখন নাকি এটি সাম্রাজ্যবাদীদের ষড়যন্ত্রে ভেঙ্গে যাচ্ছে পাশাপাশি নিয়মিত খবরের কাগজ পড়ার জন্য তাকে উৎসাহিত করেন।
আলজালিস স্কুলে থাকার সময় বিন নবী বৃত্তি পান। পরে তিনি মাদরাসায় ঢোকেন। মাদরাসায় এসে তার চিন্তা ভাবনার দিগন্ত বিস্তৃত হয়। সেই তরুণ বয়সেই তিনি বিপুল পঠন পাঠন আর অধ্যয়নের দিকে ঝুঁকে পড়েন। মাদরাসায় একদিকে অধ্যয়ন অন্যদিকে তৎকালীন মুসলিম রাজনীতির ইটিমাটি আর সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলোর পরিকল্পনা নিয়ে সতীর্থদের সাথে ছুটিতে আলোচনা এভাবে বিন নবীর দিন কাটতে থাকে। পত্রিকার পাতায় আমীর খালেদ ও মোস্তফা কামালের রণাঙ্গনের বীরত্বের কাহিনী কিংবা জগলুল পাশার ইংরেজবিরোধী লড়াইয়ের খবর তার চিত্ত চাঞ্চল্য বাড়িয়ে দেয়।
একদিন তিনি মোহাম্মদ আবদুহু আর রশিদ রিদার লেখালেখির খবর পান। এদের লেখা তার তরুণ মনে ঝড় তোলে । এই লেখা তাকে মুসলিম সংস্কৃতির অতীত গৌরব সম্বন্ধে যেমন উজ্জীবিত করে তেমনি বর্তমানের জরাজীর্ণ চেহারা ও মুসলিম মনীষার জগতের আকাল তাকে ব্যাথাচ্ছন্ন করে দেয়।
মাদরাসায় অধ্যয়নকালীন তিনি দুজন নওমুসলিম ইসাবেল এবারহার্ট ও ইউজিন জুং এর খবর পান। এদের লেখা The Warm Shadow of Islam ও Islam Between the Whale and the Bear পড়ে তিনি দারুণ মুগ্ধ হন এবং ইসলাম নিয়ে তাদের নবতর দৃষ্টিভঙ্গি ও বিশ্লেষণে চমকিত হন। কিন্তু এ সময় সবচেয়ে বেশি তাকে নাড়া দেয় আবদুল রহমান কাওকাবীর উম-উল-কুরা বইটি, যা কিনা ইসলামের তাৎক্ষণিক আত্মরক্ষা ও রেনেসাঁসের ইংগিত দেয়।
তার মাদরাসার ফরাসী শিক্ষক একবার তাকে রবীন্দ্রনাথ পড়তে দেন। এটি পড়ে তার মনে হয় সীন ও টেমস নদীর ধারেই কেবল প্রতিভা জন্মায় না, কলোনিতেও প্রতিভাধররা আবির্ভূত হতে পারে। পরাধীনতার মর্মজ্বালা কিভাবে বিন নবীকে পরাধীনতার বিরুদ্ধে লড়তে এগিয়ে দিয়েছে এইসব ক্ষুদ্র ঘটনা তার প্রমাণ। বিন নবীর মাদরাসার কাছেই ছিল ক্যাফে বেন ইয়ামিনা। এখানে নিয়মিত হাজিরা দিতেন সেকালের আলজেরিয়ার প্রতিথযশা বুদ্ধিজীবী, সংস্কারক ও রাজনীতিবিদ শাইখ আবদুল হামিদ বেন বাদিস। ১৯৩১ সালে বেন বাদিস জমিয়তুল মুসলেমিনের প্রতিষ্ঠা করেন এবং আলজেরিয়ার মুক্তি আন্দোলনে এক সুদূরপ্রসারী প্রভাব ফেলেন। এই বেন বাদিসকে ঘিরে ক্যাফে ইয়ামিনাতে মাদরাসা ছাত্রদের এক চক্র গড়ে ওঠে, যারা আলজেরিয়ার মুসলিম সংস্কৃতি, রাজনীতি, বুদ্ধিবৃত্তির উপর নিয়মিত আলোচনা পর্যালোচনা করতেন। এর সংস্কার-বিবর্তনের পথ ধরে বাদিসের অনুগামীরা যা চেয়েছিলেন তা হল একদিকে আজানী, অন্যদিকে আল নাহদা-মুসলিম সমাজের রেনেসাঁ। মালিক বিন নবী এই আন্দোলনের সাথে কিছুটা হলেও জড়িয়ে পড়েন। মাদরাসার ফরাসী পরিচালক বিন নবীর মতিগতি টের পেয়ে যান। তার জীবনীকার লিখেছেন :
All this did not escape the notice of the French Director of the madrasah who, as a rule, preferred the apathy of the turbans to the turbulence of the ‘young turks’, and Bennabi’s activities and reading were put under strict surveillance
কিন্তু যে মানুষ তার নিজের দেশের মুক্তি সংগ্রামের তাত্ত্বিক ভিত্তি রচনা করবেন তাকে কি পরিচালকের হুমকি ও চোখ রাঙানি বেধে রাখতে পারে। বিন নবী তার লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যান। এসব সংকট, টানাপড়েন, অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিপর্যয়ের মাঝে ব্যক্তিত্ব ও চিন্তা ভাবনা পরিণতি লাভ করতে থাকে। তিনি খেয়াল করেন সাম্রাজ্যবাদী শাসন কিভাবে তার দেশের অর্থনীতিকে ঝাঝরা করে দিচ্ছে। গরীব আরও গরীব হচ্ছে। দেশের ধন সম্পত্তি গচ্ছিত হচ্ছে মুষ্টিমেয় কিছু ইহুদী ও ইউরোপিয়ান শাইলকদের হাতে। এর সাথে সাম্রাজ্যবাদী প্রভুদের প্রশ্রয়ে চলছে আলজেরিয়া তথা আফ্রিকায় খ্রিস্টানীকরণের মহড়া। এভাবেই তার ব্যক্তিত্বের মধ্যে একটি বিদ্রোহী সত্তা জন্ম দেয়, যা কিনা সবরকমের জুলুম-অবিচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী হয়ে উঠতে উন্মুখ হয়ে ওঠে। বিন নবী লেখাপড়া শেষ হলে পরিবারের অর্থনৈতিক অবস্থার কথা চিন্তা করে চাকরির কথা ভাবেন। কিন্তু তার কাছে মনে হয় ঔপনিবেশিক প্রভুদের কাছে নেটিভদের জন্য চাকরি পাওয়া এক দুর্লভ সৌভাগ্যের ব্যাপার। এমনকি সাহারা মরুভূমির দুর্গম কোন প্রান্তেও যদি সেটা হয়। ভাগ্য ফেরানোর জন্য তিনি ফ্রান্সে পাড়ি জমান। কিন্তু মার্সাই বন্দরে পৌঁছে সেখানকার প্রবাসী আলজেরীয়দের দুরবস্থা, নিষ্ঠুর ঔপনিবেশিক বর্ণবাদের কথা তাকে পুনরায় স্মরণ করিয়ে দেয়। এরপর তিনি যখন দেখেন একই জাহাজে আগত একজন আলজেরীয় ইহুদী ও আলজেরীয় ফরাসী তার চেয়ে যথেষ্ট কম যোগ্যতা সত্ত্বেও চাকরি পেয়ে যায় তখন বিন নবীর কাছে সাম্রাজ্যবাদের বর্ণবাদী চেহারা আরও ভাল করে ফুটে ওঠে। বেকার বিন নবীকে ফ্রান্সে তার আলজেরীয় সমব্যথীরা আশ্রয় দিয়ে এবং খাইয়ে পরিয়ে টিকিয়ে রাখে। তার কাছে তখন মনে হয় :
despite all the disgrace that had inflicted Muslim society, Islam still maintained, therein, a sense of humanity, on a level still unattained by many civilised nations.
অনন্যোপায় বিন নবী দেশে ফেরেন। এখানে তিনি শিক্ষকতা থেকে শুরু করে ময়দার কল ও নির্মাণসামগ্রীর ব্যবসায় জড়িয়ে নিজের ভাগ্য পরখ করেন। কিন্তু ভাগ্যই তাকে আবার টেনে নিয়ে যায় ফ্রান্সে। সালটি ছিল ১৯৩০। সেখানে তিনি এবার অনেক চেষ্টা করে একটি যন্ত্র প্রকৌশল স্কুলে ভর্তি হন এবং প্রকৌশলী হিসেবে বের হন। এর আগে তিনি ভর্তি পরীক্ষায় ভাল ফলাফলের পরও প্যারিসের ইনস্টিটিউট অব অরিয়েন্টাল স্টাডিজে ভর্তি হতে ব্যর্থ হন, সেখানে তিনি আইন পড়তে চেয়েছিলেন। এর কারণ একজন আলজেরীয় মুসলিম ছাত্রের ভর্তির জন্য মেধার চেয়ে রাজনৈতিক ও ঔপনিবেশিক নীতি অনুসরণ করাই ছিল সেদিনের ফরাসী সরকারের মূল বিবেচনার বিষয়।
১৯৩১ সালে প্যারিসে ফরাসী উপনিবেশ ও তার জনগণকে নিয়ে একটি প্রদর্শনী হয়। বিন নবী লক্ষ্য করেন মুসলিম জনগণকে নিন্দা ও বদনাম করবার জন্য উদ্দেশ্যমূলক প্রদর্শনীও এখানে রাখা হয়েছে । বিশেষ করে তিনি মর্মাহত হন রসুল (স.)কেও নিন্দা ও কটূক্তির বিষয় বানানো হয়েছে । তিনি এর বিরুদ্ধে কিছু প্রতিবাদ সংগঠনের বার্থ চেষ্টা করে যখন ক্লান্ত দেহে ঘরে ফিরে আসেন তখন তার বুক ভেঙ্গে যায় । তিনি বিছানায় শুয়ে চিৎকার করে ওঠেন : Oh God, they dare sully the name of the Prophet and yet the earth does not tremble…..”
অকস্মাৎ তার বিছানা কেপে ওঠে। পরবর্তী সকালে তিনি সংবাদপত্রে দেখতে পান প্যারিসে ভূমিকম্প হয়েছে। এ সময় বিন নবীর আলজেরীয় মাদরাসার পুরনো বন্ধু হামুদা বিন সাই ও খালিদী এসে প্যারিসে উপস্থিত হয়। হামুদা বরাবর কুরআন শরীফের সমাজ বিশ্লেষণ করে বর্তমানকালের মুসলমানদের দুর্দশাকে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করতো। তার সাহচর্যই বিন নবীকে দর্শন, সমাজবিজ্ঞান ও ইতিহাসের প্রতি আকর্ষিত করে এবং পরবর্তীতে মুসলিম দুনিয়ার সমস্যাকে দার্শনিক ও সমাজতাত্ত্বিক পটভূমিতে বিশ্লেষণ করতে উজ্জীবিত করে। খালিদী ছিল রাজনৈতিক সংগঠক। দ্রুত সে প্যারিস প্রবাসী উত্তর আফ্রিকার ছাত্রদের নিয়ে একটি সংগঠন গড়ে তোলে এবং আলজেরিয়ার মুক্তি আন্দোলনের পক্ষে জনমত তৈরিতে ভূমিকা রাখে। খালিদীর গড়া সংগঠনে বিন নবী একবার Why We are Muslim শীর্ষক বক্তৃতা দেন, যা সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এর ফলাফল হয় মারাত্মক। ফরাসী নিরাপত্তা কর্মীরা তাকে ধরে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করে এবং এর অব্যবহিত পর তিনি খবর পান আলজেরিয়ায় তার আব্বাকে এক দুর্গম স্থানে বদলি করে দেয়া হয়েছে। প্রকৌশল স্কুল থেকে বের হওয়ার পর ফ্রান্সে তার চাকরি পাওয়ার সব চেষ্টা ব্যর্থ হয় এমনকি তাকে অন্য দেশে যাওয়ার ভিসাও দেয়া হয় না। তার অন্তরের ভিতরে ঝড় চলতে থাকে। ঔপনিবেশিক নির্মমতা তাকে মানবীয় সম্পর্কের পারস্পরিক দিকগুলো নিয়ে নতুন করে ভাবায়। তার কাছে মনে হয় :
human relations are not fashioned in accordance with objectivelaws but are born among the individuals of a society whose destiny has been demarcated by history as a ‘whole’.
শেষমেষ তিনি তার এক বন্ধুর পরিচালিত প্রবাসী আলজেরীয় শ্রমিকদের একটা স্কুলে পাঠদান শুরু করেন। এই নতুন বৃত্তিতে বিন নবী শুধু শিক্ষকতার পেশায়ই নিজেকে সীমিত রাখেন না, আলজেরীয় শ্রমিকদের অধিকার বিশেষ করে আলজেরিয়ার আজাদীর জন্য এই সব শ্রমিকদের উজ্জীবিত করেন। ফলে কর্তৃপক্ষ একদিন স্কুলটিই বন্ধ করে দেয়। বিন নবী এবার নিজের জীবনের এই সংগ্রামের সাথে মিলিয়ে বিশ্বরাজনীতির উত্থান পতন, সাম্রাজ্যবাদের নিষ্ঠুর আয়োজন ও ইউরোপীয় সভ্যতার শক্তি এবং দুর্বলতার দিকগুলো ভাল করে বোঝার চেষ্টা করেন। এর ভিতরে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের দামামা বেজে ওঠে এবং ইউরোপীয় সভ্যতার দেউলিয়াপনাও তার নজর এড়ায় না। নাজী বর্বরতা তার কাছে মনে হয় : Nazi barbarism was merely an extension of the colonial spirit in the heart of colonialism itself.
আলেজেরিয়ায় ১৯৪৫ সালের সেটিফ হত্যাকান্ড (setif massacre), অন্যত্র স্বাধীনতা আন্দোলনকারীদের উপর দমন-পীড়ন বিশেষ করে ফিলিস্তিনে একই শক্তির দ্বারা হত্যাযজ্ঞ, যারা নাকি মুক্ত দুনিয়ার পথিকৃৎ হিসেবে দাবিদার, তাকে সভ্যতা সম্বন্ধে খুব শক্তভাবে সচেতন করে তোলে। তিনি বুঝতে পারেন সাম্রাজ্যবাদকে রুখতে রাজনৈতিক ও সামরিক প্রতিরোধই যথেষ্ট নয়, আদর্শগত ও বুদ্ধিবৃত্তিকভাবেও সাম্রাজ্যবাদকে পরাজিত করা দরকার। একালে সাম্রাজ্যবাদকে একহাত নিয়েছেন বা তাকে প্রতিরোধ করার নানা উপায়ের কথাও বলেছেন অনেক বুদ্ধিজীবী। কিন্তু একথা মনে করার সংগত কারন আছে সাম্রাজ্যবাদের অন্তর্ভেদী পর্যালোচনায় মালিক বিন নবীর জুড়ি আজও নেই। সাম্রাজ্যবাদকে তিনি ভেতর থেকে বোঝার চেষ্টা করেছেন। কেন সাম্রাজ্যবাদ ঔপনিবেশিক দেশগুলোর উপরই ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং কি তার দুর্বলতা, তার এক সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ হাজির করেছেন তিনি । এটাও তিনি বুঝতে চেষ্টা কেন মুসলিম দেশগুলো শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে এক বুদ্ধিবৃত্তিক ও সামাজিক জড়তার ভিতর দিয়ে এগিয়ে চলেছে। একই সাথে জনগণের জাগরণ ও উত্থানকে ঠেকিয়ে রাখার যাবতীয় সাম্রাজ্যবাদী অভিসন্ধিকে অকার্যকর করার প্রয়োজনীয়তার কথাও তিনি বলেছেন।
অনেকে মনে করেন, সভ্যতার বিশেষ করে মুসলিম সভ্যতার উত্থান-পতনের যে সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ বিন নবী করেছেন, তার মধ্যে সমাজবিজ্ঞানী ইবনে খালদুনের বিশ্লেষণভঙ্গি একালে পুনরুজ্জীবিত হয়েছে। এটাও সত্য, মুসলিম চিন্তার জগতে ইবনে খালদুনের পরে একালে মালিক বিন নবীকেই আমরা একমাত্র মৌলিক ও প্রতিভাধর সভ্যতা বিশ্লেষক হিসেবে পাই, যার অন্তর্বর্তী ৫০০ বছর মুসলিম চিন্তার আকাল ও নির্জীবতার সাক্ষ্য হয়ে আছে।বিন নবীর মধ্যে সমন্বয় ঘটেছিল একই সাথে দ্রষ্টা ও বৈজ্ঞানিক মননের। একই কারণে তিনি যেমন করে আজাদীর জন্য লড়াই করেছেন, তেমনি এর পথের বাধাগুলো উন্মোচন করেছেন। তিনি এর লক্ষ্যকে নির্ধারণ করার কথা ভেবেছেন এবং লক্ষ্যের পথকেও পরিশ্রুত করার চিন্তা করেছেন। সাম্রাজ্যবাদী কুয়াশা ভেঙ্গে তিনি দিগন্তকে সাফ সুতরো করেছেন এবং শেষ পর্যন্ত পরবর্তী প্রজন্মকে এমন একটা সংস্কৃতি উপহার দিয়েছেন যা একান্তই নিজের ইতিহাস ও মূল্যবোধ থেকে আহরিত।
মালিক বিন নবীর সভ্যতা বিশ্লেষণের নমুনা পাওয়া যায় তার দুটি বিখ্যাত বইতে। প্রথমটির নাম The Conditions of Renaissance এখানে তিনি আলজেরিয়ার সমস্যাকে এক সামাজিক দর্শনের পটভূমিতে স্থাপন করেন। তার এই চিন্তার পরিণতি ঘটে Islam in History and society তে। মূলত বই দুটি একে অপরের পরিপূরক এবং একই চিন্তার গভীর থেকে গভীরতর বিশ্লেষণ। এ বইতে বিন নবী ইতিহাসের বিভিন্ন স্তরের অগ্রগতি ও বিবর্তনের একটি চিত্র তুলে ধরেছেন। ইবনে খালদুনের বিখ্যাত আসাবিয়া তত্ত্বকে একধাপ এগিয়ে নিয়ে বিন নবী তার সভ্যতার বিবর্তনের তত্ত্ব হাজির করেছেন। তিনি বলতে চেয়েছেন প্রত্যেকটি সভ্যতাই নানা রকম রূপান্তরের ভিতর দিয়ে এক অনিশ্চিত অভিযাত্রায় নিজেকে সংহত করে এবং এই সংহতি আসে নির্দিষ্ট মাটি, মানুষ ও সময়ের যথার্থ সমন্বয়ের মাধ্যমে। সভ্যতার এই চক্রকে সামনে রেখে মালিক বিন নবী মুসলিম ইতিহাস ও সভ্যতাকে তিনটি স্তরে ভাগ করে দেখিয়েছেন। প্রথমটি হচ্ছে- কুরআনের আদর্শে উজ্জীবিত এক সমাজ, যা রসুল (স.)-এর হাতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এই জীবন্ত সমাজের ধারাবাহিকতা নষ্ট হয়ে যায় সিফফিনের যুদ্ধের ভিতর দিয়ে। যা নাকি মুসলিম সমাজের ভ্রাতৃত্বের বন্ধনকেও ছিন্নবিচ্ছিন্ন করে দেয়। সিফফিনের যুদ্ধ, যা কিনা হযরত আলী ও হযরত মাবিয়ার মধ্যে অনুষ্ঠিত হয় এবং সত্যিকার অর্থে মুসলিম সমাজের সংহতি তখন থেকেই দুর্বল হতে শুরু করে।
দ্বিতীয় স্তরে মুসলিম সভ্যতা ও সংস্কৃতির অভূতপূর্ব বিকাশ ঘটে। যা তার ভাষায় আল মুসলিম সভ্যতার বিকাশ ঘটিয়েছিল। মালিক বেনাৰী সর্বশেষ স্তরকে বলেছেন উত্তর আল মুয়াহিদ যুগ (Post Al-Muwahid Era), যে যুগ কিনা আমাদের এ কাল পর্যন্ত। বিস্তৃত হয়েছে এবং জড়তা, অবক্ষয় ও বুদ্ধিবৃত্তিক পচন যার বৈশিষ্ট্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। ইতিহাস বিচারের এই পর্যায়ে এসে বেদারী ইউরোপীয় সভ্যতার উত্থান, বিবর্তন ও এর গাঠনিক উপাদানগুলো বিশ্লেষণ করে দেখান যে, এর নগরগুলো থেকে সংগঠিত বস্তুবাদের বিকাশ ঘটেছে। খ্রীস্টান ধর্ম এর একটি স্থিতিশীল মেজাজের সাথে গতিশীল আবহ তৈরি করেছে এবং আধিপত্য বিস্তারের নৈতিক শক্তি যুগিয়েছে। যা কিনা ক্রুসেড ও পরবর্তীকালের সাম্রাজ্যতন্ত্রকে উসকে দিয়েছে। এ সভ্যতা Cartesianism, যাকে বলা যায় গ্রীক সভ্যতার ধারা, তার স্পর্শে জ্বলে উঠেছে এবং শিল্প বিপ্লবের দিকে অগ্রসর হয়েছে এবং সবশেষে নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধের চূড়ান্ত বিকৃতি ঘটিয়েছে।
এ পর্যায়ে বিন নবী ইতিহাসের এক সন্ধিক্ষণে এই দুই সভ্যতার মুখোমুখি হওয়ার কথা বলেছেন। সভ্যতার ধর্ম বিচ্যুৎ হওয়ায় মুসলিম সভ্যতা আজ কঙ্কালে পরিণত হয়েছে। এর জীবন্ত বিশ্বাস শুধু শুকনো কথার মরুভূমিতে রূপ নিয়েছে। অন্য সভ্যতাকে প্রতিরোধ করার ক্ষমতা এর নেই। বিন নবীর নিজের কথায় ,
in its preoccupation with the apology of the past, the culture takes on a character of archaeology where the intellectual effort is not forward but backwards. This retrograde tendency imprints on the entire teaching a retrospective character, incompatible with the exigencies of the present and the future.
এরকম একটা অবস্থায় মুসলিম দুনিয়া উপনিবেশিত হওয়ার আগেই হয়ে পড়েছে Colonisable-উপনিবেশপ্রবণ। অর্থাৎ যে ভূমিতে অন্য কেউ এসে সহজেই পা দাবিয়ে দিতে পারে। অন্যদিকে ইউরোপ তার সভ্যতার বিবর্তনের ধারায় এগিয়ে এসেছে এবং উপনিবেশবাদ ও বিজ্ঞানবাদে (Scientism and Colonism) এসে মিলিত হয়েছে। এমন পরিস্থিতিতে পাশ্চাত্য আজ মুসলিম দুনিয়ার উপর জাঁকিয়ে বসেছে। মালিক বিন নবীর এই COLONISIBILITE (উপনিবেশ প্রবণ) এবং COLONISATION (উপনিবেশায়ন)-এর এই তত্ত্বের সাথে ইবনে খালদুনের চিন্তাভাবনার সাদৃশ্য রয়েছে। খালদুন তার আল মুকাদ্দিমায় লিখেছেন : The conquered people adapt the forms, ideas, and the manners of the conquering people.” বিজিত জাতি বিজেতাকে অনুসরণ করে, কারণ বিজিত জাতির প্রতিরোধ শক্তি ফুরিয়ে যায়। প্রতিরোধের অস্ত্র চিন্তা, বিশ্বাস, মূল্যবোধ এতখানি ঝাঁঝরা হয়ে যায় যে, তা দিয়ে বিজেতাকে মোকাবিলা করা সম্ভব হয় না। তখন বিজেতা এসে বিজিতের ঘাড়ে চেপে বসে মূল্যবোধ ও সংস্কৃতি বিজিতের উপর চপিয়ে দেয়। আমরা ইকবালের এবং তার উক্তিকে স্মরণ করতে পারি : enormous rapidity with which the world of Islam was moving towards the West.
কেন এই পশ্চিমানুসরণ। কারণ ইসলামের মধ্যে অনেক দিন ধরে রিভাইভাল আসেনি। রেনেসাঁর সূত্রপাত হয়নি। তাই শক্তিমানের দিকে তাকিয়ে থাকাই স্বাভাবিক। জামালউদ্দীন আফগানী বলেছিলেন ইসলামের মধ্যে রিফরমেশন দরকার। মালের বিন নবী এই রিভাইভাল আনতে চান এক নৈতিক শক্তির উত্থানের ভিতর দিয়ে। কারণ তিনি মনে করেন মুসলিম উম্মাহর শক্তি হচ্ছে কুরআনী নৈতিকতা। এই নৈতিক শক্তি দিয়েই সে বরাবর জাহেলী শক্তিকে পর্যুদস্ত করে এসেছে এবং ইতিহাসের ধারায় সব রকমের সংকট থেকে ত্রাণ পেয়েছে। এর কারণ হিসেবে তিনি লিখেছেন :
because of what remained in it of the impulsion and living force of the Quran. It were men like Uqbah, Umar ibn Abd al-Aziz, and Imam Malik, who maintained it, not because one was a great conqueror, the other a great monarch, and the third the head of juridical school; but because they incarnated under different titles, the simple and great virtues of Islam.
বিন নবী মনে করেন সভ্যতা কোন কুড়িয়ে পাওয়া বা অনুকরনের বিষয় নয়। এমনকি এটা কোন সংগ্রহশালাও নয়। এটি একটি নির্মাণের বিষয়। এটি একটি পুরোপুরি স্থাপত্য। তার ভাষায় : Civilization is not an accumulation but a construction, an architecture.
সুতরাং ঝাঁঝরা হয়ে যাওয়া ইসলামী সভ্যতার পুনঃনির্মাণ চাই। কেমন হবে সেই নির্মাণশৈলী তার একটি ধারণা তিনি আমাদের দিয়েছেন :
Any attempt for the reconstruction of Muslim culture must begin with the re-establishment of pure doctrine over the political power. This reconstruction implies a return to Islam, in particular the extrication of the Quranic text from its triple matrix of theology, jurisprudence and philosophy.
মুসলিম চিন্তা জগতের উষরতা, মুসলিম সমাজের গতিহীনতা বিন নবীকে কিন্তু হতবিহ্বল করতে পারেনি। তিনি মুসলিম সমাজের উপর যে ঝড় ঝাপটা এগিয়ে আসছে তাকে সুস্বাস্থ্যের লক্ষণ মনে করতেন। কারণ এই ঝড়ঝাপটাকে জয় না করতে পারলে মুসলিম সমাজ কখনো জাগবে না ফিলিস্তিনের বিপর্যয় সম্পর্কে তিনি বলেছিলেন, এই বিপর্যয় মুসলিম সমাজের ঘুম ভাঙ্গাবে। বিন নবী আরেকটি ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। ইসলামী শক্তির ভরকেন্দ্র আরব দুনিয়া থেকে একদিন এশিয়ায় চলে যাবে। সেখানেই নতুন সভ্যতার পত্তন ঘটবে। সেই সভ্যতার প্রতিত্ব হিসেবে তিনি ইকবালকে চিহ্নিত করেছেন।
এ সময় বিন নবী আরো দুটি গুরুত্বপূর্ণ বই লেখেন। একটি হচ্ছে The Quranic Phenomenon, অপরটির নাম In the Whirlwind of the Battle । প্রথমটিতে বিন নবী বলতে চেয়েছেন কুরআন অধ্যয়ন ও ব্যাখ্যার চিরাচরিত ও ঐতিহ্যবাহী ধারাটি সংস্কার করা দরকার। কারণ আজকের মুসলিম তরুণরা পশ্চিমী শিক্ষায় প্রভাবিত হয়ে এক ধরনের বিশ্বাসের সংকটে ভুগতে শুরু করেছে এবং ইসলামকে বোঝার জন্য পশ্চিমী প্রাচ্যতত্ত্ববিদদের উপর ভর করছে। এই আত্মঘাতী ধারা থেকে তরুণদের ফিরিয়ে রাখতে হলে কুরআন ব্যাখ্যার নতুন পদ্ধতি চালু করতে হবে। প্রচলিত ব্যাখ্যাশৈলীতে জোর দেয়া হয় কুরআনের Rhetoric ও style এর উপর। বেনারী মনে করেন যদি এই ধারার সাথে Astrophysics, Archaeology’s প্রেক্ষাপট যুক্ত করা যায় তাহলে কুরআন ব্যাখ্যার নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হবে এবং বিভ্রান্ত তরুণদের বিশ্বাসহীনতার বিরুদ্ধে লাগসই লাগাম হিসেবে কাজ করবে। ঐতিহ্যবাদী ও গতানুগতিকপন্থীরা যদিও এই বই নিয়ে কিছুটা শোরগোলের চেষ্টা করেন কিন্তু মুসলিম বুদ্ধিবৃত্তির জগতে এ বই একটা নতুন দৃষ্টান্ত হিসেবে বিবেচিত হয়। অন্যদিকে বিন নবীও এ বইয়ের মাধ্যমে বুদ্ধিজীবীর স্বীকৃতি আদায় করে নেন। In the Whirlwind of the Battle বইটি লেখা হয়েছিল আলজেরীয় বিপ্লব ও স্বাধীনতার প্রাক্কালে । এতকাল বিন নবী মুসলিম সভ্যতার অবক্ষয়ের বিরুদ্ধে প্রতিশেধক হিসেবে যে আইডিয়ার জাগরণের কথা বলে আসছিলেন তার বাস্তব ও প্রয়োগিক দিকটি তিনি এখানে পর্যালোচনা করেছেন এবং সমকালীন রাজনৈতিক, সামাজিক, আদর্শিক প্রেক্ষাপটে এর সম্ভাবনাকে বিচার করে দেখার চেষ্টা করেছেন। বিশেষ করে সমকালের কয়েকটি ঘটনা তাকে খুব আলোড়িত করেছিল। ইরানের প্রধানমন্ত্রী মোসাদ্দেকের সাম্রাজ্যবাদবিরোধী জাতীয়তাবাদী প্রচেষ্টাসমূহ, ১৯৫২ সালের মিসরীয় বিপ্লব এবং শেষমেষ ১৯৫৫ সালের বান্দুং-এ আফ্রো-এশিয়ান কনফারেন্স। তার ধারণা জন্মেছিল এসব প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে আফ্রো-এশিয়ার মানুষ মাথা তুলে দাঁড়াবে। তারা এক নতুন সভ্যতার পত্তন ঘটাবে ; বিশেষ করে তৃতীয় বিশ্বের এই উত্থানের পথ ধরে সাম্রাজ্যবাদী দেশসমূহ সভ্যতার ধর্ম মর্মে মর্মে অনুধাবন করতে শিখবে। এই প্রেক্ষাপটকে সামনে রেখে তিনি একটি বই লেখেন Afro-Asiatism যদিও বার বছর পর এই বইয়ের দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকায় তিনি তার চিন্তাভাবনাকে কিছুটা পুনর্বিন্যস্ত করতে বাধ্য হন এবং স্বীকার করেন বান্দুং কনফারেন্সে যে সম্ভাবনা উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল, তৃতীয় বিশ্বের নেতারা তাকে কাজে লাগাতে পারেননি। এখানকার মানবসম্পদ ও বস্তুগত সম্পদকে ব্যবহার করে পশ্চিমের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক আধিপত্যকে ভাঙ্গতেও তারা ব্যর্থ হয়েছেন।
আলজেরিয়ার স্বাধীনতার প্রাক্কালে তিনি তার সাংস্কৃতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক লড়াইকে আরো জোরদার করেন। শুধু এ কারণেই তিনি কায়রোতে এসে বসবাস শুরু করেন। আলজেরিয়ায় ঔপনিবেশিক শক্তির নির্মম দমন ও পীড়নের দিকে বিশ্ববাসীর দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য তিনি এসময় লেখেন S.O.S. Algeria । এখানে একটা জিনিস বোঝা দরকার, আলজেরিয়ার সমস্যাকে তিনি বিরাট মুসলিম ক্যানভাসে আলোকপাত করার চেষ্টা করেছিলেন। কারণ তার কাছে মনে হয়েছিল আলজেরিয়ার সমস্যা মূলত মুসলিম জাতি ও সংস্কৃতির সমস্যা। এটাকে বিচ্ছিন্নভাবে ব্যাখ্যা করার কোন সুযোগ নেই। সেরকম ব্যাখ্যা করতে গেলে সাম্রাজ্যবাদই সুযোগ নেবে মাত্র। মালিক বিন নবী এ সময় মুসলিম সংস্কৃতির উত্থান-পতন, মুসলিম জগতের সাংস্কৃতিক ও নৈতিক পুনরুত্থান, সাম্রাজ্যবাদী ষড়যন্ত্র ও আধিপত্যের মুখে মুসলমানদের আদর্শিক সংকট ও সম্ভাবনাকে পুনর্মূল্যায়ন করে আরো লেখালেখি করেন ও বিভিন্ন স্থানে বক্তৃতা দেন। এই বিষয়কে সামনে রেখে তার কয়েকটি বই প্রকাশিত হয়। এগুলো হচ্ছেঃ The Problem of Culture The Ideological Struggle in Colonised Countries, The New social Edification, The Idea of an Islamic Common Wealth
মালিক বিন নবী স্বাধীনতা উত্তরকালে মুসলিম দেশগুলোর যেরকম সামাজিক সাংস্কৃতিক বিকাশের কথা ছিল তা কেন হয়নি তার কারনও খুঁজেছেন। তিনি বলতে চেয়েছেন সামাজিক ও অর্থনৈতিক মুক্তির জন্য আগে দরকার আদর্শের ভিত প্রস্তুত করা। সদ্য স্বাধীনতাল মুসলিম দেশগুলোতে এই আদর্শিক সংগ্রাম সফল সামাজিক ও অর্থনৈতিক মুক্তির লক্ষ্যও অর্জিত হয়নি। তিনি বরাবরই কোরআনে বর্ণিত সামাজিক সুবিচার ও ইনসাফের নীতিকে প্রতিষ্ঠার কথা বলেছেন। তিনি বিশ্বাস করতেন এটা ছাড়া মুসলিম দেশগুলোর অর্থনৈতিক ও সামাজিক বঞ্চনা কাটার সম্ভাবনা কম। বিন নবী শেষ জীবনে দামেস্ক বিশ্ববিদ্যালয়ে আমন্ত্রিত হয়ে একটি বক্তৃতা দেন। এর প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল : The Role of Muslim in the last third of the 20th century। এখানে তিনি বলতে চেয়েছিলেন পরাশক্তিসমূহের প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুধু ক্ষমতার নয়, এর সাথে আদর্শ ও সংস্কৃতির প্রতিদ্বন্দ্বিতাও রয়েছে। এই প্রতিদ্বন্দ্বিতার পরিণাম হচ্ছে যুগযুগান্তের মূল্যবোধকে অপসারিত করে নতুন মূল্যবোধ দ্রুত যায়গা করে নিচ্ছে এবং এর ফলশ্রুতিতে আসছে ভয়াবহ শূন্যতা। এই শূন্যতার পটভূমিতে মানুষ তার মনুষ্যত্ববোধকে বিসর্জন দিচ্ছে। সভ্যতা হারাচ্ছে তার ধর্ম।
এইভাবে মালিক বিন নবী আমৃত্যু সবরকমের চেতনাগত ও বস্তুগত দাসত্বের বিরুদ্ধে লড়াই করে গেছেন। ফলাফলের কথা চিন্তা না করে তিনি ন্যায় ও কল্যাণের পথে নিজেকে বরাবর নিয়োজিত রেখেছেন। তার বলার ও লেখার ভঙ্গি কখনোই দুর্বল হয়ে পড়েনি। এবং তার দৃঢ়প্রত্যয়ের সামনে সবরকমের মিথ্যা ও ভন্ডামি ভেঙ্গে পড়েছে। এই মনস্বী ভাবুক ১৯৭৩ সালের ৩১ অক্টোবর ইন্তেকাল করেন। বিন নবীর কাছে মনে হয়েছে ইতিহাস তার প্রান্তিকে আর একবার পৌঁছে গিয়েছে এবং সেখান থেকে ইতিহাস তার নতুন যাত্রা শুরু করবে। বিন নবী কুরআন শরীফের এ আয়াতকে পরম সত্য হিসেবে ধরে নিয়েছেন তিনিই তার রসুলকে পথনির্দেশ ও সত্যধর্ম দিয়ে প্রেরণ করেছেন, যাতে একে সব ধর্মের উপর প্রবল করে দেন।
কিন্তু জানতেন, মুসলমানরা ইতিহাসের এ সত্যকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে যদি তা তাদের উপর আরোপিত শর্ত পূরণ করতে পারে। অন্যকে বাঁচাতে হলে আগে নিজেদের আত্মরক্ষা করতে হবে। তাদের নিজেদের আগে সভ্যতার ধর্মে উন্নীত করতে হবে। তারপর সেই সভ্যতাকে তুলে ধরতে হবে আল্লাহর প্রতিশ্রুতির কাছাকাছি। বিন নবী আমৃত প্রতিশ্রুতি পালনের শর্ত পূরণ করে গেছেন।
গ্ৰন্থঋণ :
Asma Rashid, Malek Bennabi : His life Times and Thought. Islamabad: Islamic Research Institute, 1987.
Malek Bennabi, Islam in History and Society Islamabad Islamic Research Institute, 1987. ৮. Ibn Khaldun, The Muqaddimmah An Introduction to History, Translated by Franz Rosenthal. Princeton: Princeton University Press, 1969. Speeches and Statements of Iqbal, edited by Shamloo, Lahore, 1948.
Malek Bennabi Islam in History and Society.