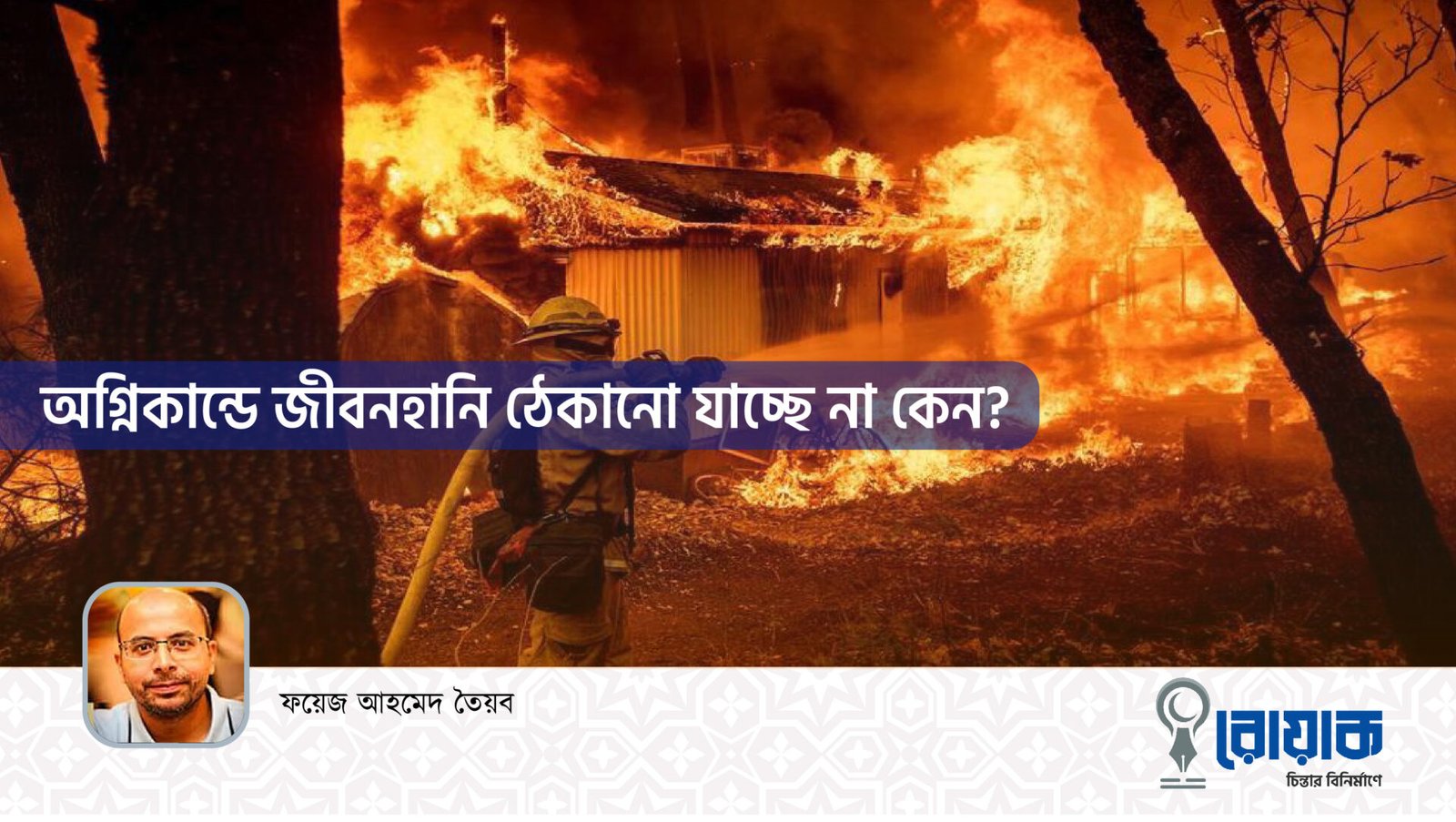রাজউকের বহুতল ভবনসংখ্যার বিপরীতে ফায়ার সার্ভিসের ছাড়পত্র মিলিয়ে দেখা যায়, ২০১৮ পর্যন্ত প্রায় ১২ হাজার ভবন ছাড়পত্রহীন। ফায়ার সার্ভিসের তথ্যানুযায়ী, গত ছয় বছরে সারা দেশে মোট অগ্নিকাণ্ড ঘটেছে ১ লাখ ১৭ হাজার ৬০টি, তার মধ্যে শিল্পকারখানায় ৬ হাজার ৮১টি। আগুন লাগলে কোনো ভবনেরই নিরাপত্তাব্যবস্থা কাজ করে না। কিন্তু কেন?
- পদ্ধতিগত ত্রুটি
দেশের বাণিজ্যিক ও শিল্প ভবনে যেসব অগ্নিনিরাপত্তা ব্যবস্থাপনা নেওয়া হয়, তার প্রায় সবই পরোক্ষ (প্যাসিভ) এবং দুর্ঘটনা ঘটা সাপেক্ষে দায়িত্বরতকে পদক্ষেপ নিতে হয়। এসব প্রতিক্রিয়াশীল ব্যবস্থা স্মোক ডিটেক্টর, ফায়ার ডিটেক্টর, অগ্নিনির্বাপক সিলিন্ডার এবং অগ্নিনির্বাপক হোস পাইপকেন্দ্রিক। ডিটেক্টরগুলো অগ্নিসতর্কতা তৈরি করে, তারপরও প্রশিক্ষিত ব্যক্তিকে গিয়ে সঠিক সময়ে সঠিকভাবে অগ্নিনির্বাপক সিলিন্ডার ও অগ্নিনির্বাপক হোসপাইপ ব্যবহার করে আগুন নেভাতে হয়। মূল বিষয়টা হচ্ছে, বড় দুর্ঘটনার প্রাণঘাতী আগুন, ধোঁয়া ও অতি উচ্চ তাপে প্রশিক্ষিত ব্যক্তির পক্ষেও ভবনের অভ্যন্তরে থেকে এসব পরোক্ষ অগ্নিনিরাপত্তা ব্যবস্থা পরিচালনা অসম্ভব। মাঝারি ও বৃহৎ পরিসরের বাণিজ্যিক ও শিল্প ভবনে দরকার প্রত্যক্ষ ও স্বয়ংক্রিয় অগ্নিনিরোধক ব্যবস্থা, যা নিজে থেকেই আগুন শনাক্ত করে পরিমাণমতো পানি কিংবা গ্যাস নিজেই স্প্রে করে আগুন নিয়ন্ত্রণ করে ফেলে। বর্তমানে ফায়ার বল জনপ্রিয় হচ্ছে, এসব কার্ব বল আগুনে বিস্ফরিত হয়ে আগুন নিভিয়ে ফেলে। বাস্তবায়ন কিছুটা ব্যয়বহুল বলে বাংলাদেশের স্বল্পব্যয়ী শিল্প উৎপাদন মডেলে, কর্মী-অবান্ধব কাজের পরিবেশে এসব নিরাপদ কারিগরি সমাধান একেবারেই গুরুত্ব পায় না।
- পরোক্ষ অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা জালিয়াতিপূর্ণ
পরোক্ষ অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা যেসব রয়েছে, তাতে অপব্যবস্থাপনা রয়েছে। তলাপ্রতি একটি করে লোকদেখানো অগ্নিনির্বাপক সিলিন্ডার বসানো থাকে, যা ফ্লোর স্পেস ও মাথাপিছু ক্যাপাসিটির বিপরীতে সক্ষম করে স্থাপিত নয়। অনেক ক্ষেত্রেই সেগুলো মেয়াদোত্তীর্ণ থাকে। এগুলো বছরে দুবার পরিদর্শন করে তার ওপর দিনক্ষণ উল্লেখসহ যাচাইকারী কর্তৃপক্ষের স্টিকার থাকার কথা। বিল্ডিং কোডের নাজুকতার দিক থেকে বিপজ্জনক মাত্রার বিপরীতে পর্যাপ্ত সংখ্যায় মজুত থাকার কথা। কিছু বহুতল ভবনে হোসপাইপ বসানো থাকে, বাস্তবে এগুলো লোকদেখানো, বাস্তবে পাম্প সংযোগহীন।
- পৃথক জরুরি বাহিরপথ রাখার বাধ্যবাধকতা নেই
জরুরি বা অগ্নিজনিত বাহিরপথ অধিকাংশ ভবনে থাকে না প্রায়ই। উপরন্তু জরুরি বাহির, লিফট ও বৈদ্যুতিক লাইনের জায়গা পৃথক থাকে না। একই সিঁড়িঘরেই পাশাপাশি জরুরি বাহির ও সাধারণ সিঁড়ি, লিফট এবং বৈদ্যুতিক তার টানার স্থান রাখা হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই স্থান বাঁচাতে জরুরি সিঁড়ি বাদ দেওয়া হয়, কোথাও থাকলে সেটা বেশ সংকীর্ণ, তাও বন্ধ থাকে। ভবনের স্পেস ও লোকসংখ্যার অনুপাতে হলওয়ে, মূল সিঁড়ি ও তার সামনের স্থান বরাদ্দ নকশায় গুরুত্ব রাখে না।
- শীতাতপ নিয়ন্ত্রণযন্ত্র অগ্নিঝুঁকি বাড়ায়
কেন্দ্রীয় শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত বহুতল ভবনের আরেকটি সমস্যা সিঁড়ির আশপাশেই থাকা জেনারেটর রুম, অগ্নিকাণ্ডে যা সিঁড়ি ব্যবহারের বাধা হয়ে ওঠে। কেন্দ্রীয় শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ না থাকা ভবনের বাইরে থাকা সারি সারি ডিস্ট্রিবিউটেড এসিতে ভবন একেবারেই অনিরাপদ হয়ে ওঠে। অত্যন্ত ভয়ংকর দিক হচ্ছে, ভবনের প্রাথমিক বৈদ্যুতিক ড্রাফটিং অর্থাৎ পরিবাহী তার, সার্কিট ব্রেকার ও অন্যান্য সরঞ্জামের বৈদ্যুতিক লোড সক্ষমতার সঙ্গে এসিসহ অন্য সব বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতির সক্ষমতা সামঞ্জস্যপূর্ণ থাকে না। ফলে, দুভাবে আগুন লাগে:
- অতি লোডে বৈদ্যুতিক শর্টসার্কিটে।
- এসির এগজস্ট থেকে। বুয়েটের গবেষণা বলছে, দেশের অন্তত ৭০ শতাংশ অগ্নিকাণ্ড বৈদ্যুতিক শর্টসার্কিট থেকে ঘটে। নতুন সমস্যা যত্রতত্র কেমিক্যালের গুদাম।
ফায়ার সার্ভিসের উচ্চতা সক্ষমতা
ভবনের উচ্চতা ফায়ার সার্ভিসের পানি পৌঁছানোর সক্ষমতার সঙ্গে সমন্বিত নয়। ফায়ার সার্ভিস সর্বোচ্চ ১০ থেকে ১২ তলা পর্যন্ত পানি স্প্রে করতে পারে। একটি শহরে ফায়ার সার্ভিস যদি ১২ তলার ওপরে পানি, গ্যাস বা রাসায়নিককেন্দ্রিক অগ্নিনিরোধে অক্ষম হয়, তাহলে সেখানে ১২ তলার বেশি উচ্চতার ভবন করতে যাওয়ার কথা না। অগ্নিনির্বাপণের জন্য শহরের একটি নির্দিষ্ট দূরত্বে (ধরুন ৪০০ মিটার) ওয়াসার ওয়াটার হাইড্র্যান্ট থাকার কথা, যা নেই। বিকল্প হচ্ছে জলাধার রাখা। অর্থাৎ বেশি পরিমাণে পানির নিকটস্থ উৎস না থাকলে ভবন ওপরে ওঠানো যাবে না। উচ্চ ঘনবসতির শহরে বহুতল ভবন দরকার, বিপরীতে ফায়ার সার্ভিসকে কারিগরিভাবে সক্ষম করার চেষ্টাটাই নেই।
ফায়ার হাইড্র্যান্ট কিংবা নির্দিষ্ট দূরত্বে জলাধার না থাকায় প্রায়ই দেখা যায় বিভিন্ন বাসাবাড়ি বা মসজিদের পানির ট্যাংক থেকে পানি সংগ্রহের অক্ষম চেষ্টা। বিষয়টা বেশ হতাশার। কেননা, এসব ছোট ট্যাংকের পানি দিয়ে অগ্নিনির্বাপণের কাজ হয় না। আমাদের নগরে চলছে জলাধার ও খাল দখলের রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক উৎসব। হতাশার ব্যাপার, ওপর থেকে লাফ দেওয়ার জন্য একটা বাতাসভর্তি জাম্পিং প্যাডও থাকে না ফায়ার ডিফেন্স ও ভবনমালিকের।
২০০৯ সালে বসুন্ধরায় আগুন লেগেছে ৯ তলায়, ফায়ার সার্ভিসের পানি ওঠেনি। ১০ বছর পরে ফারুক রূপায়ণ টাওয়ারে আগুন লেগেছে, সেখানেও ১০ তলার ওপরে পানি ওঠেনি। ফাটা পাইপের লিক সারাতে বিবেকের ডাকে সাড়া দিয়ে একটি ছোট ছেলে পলিথিন মুড়িয়ে ধরে ছিল। অন্যদিকে, হেলিকপ্টারে লেকের পানি আনার উদ্যোগ বাবমি বাকেটের তলা ফুটো থাকার কারণে ভেস্তে গেছে। অর্থাৎ সক্ষমতা তো বাড়েইনি, বরং হাতে থাকা যন্ত্রপাতি কিংবা টুলগুলো কাজ করে কি না, তার তদারকিও ঠিকঠাক নেই।
ফায়ার ডিফেন্স কাজের প্রকৃতির দিক থেকে খুব মানবিক কাজ হলেও কাজের প্রতিকূলতার দিক থেকে খুব বেশি শ্রমঘন, বিপজ্জনক। কিন্তু ‘আমাদের লোক’ হিসেবে নিয়োগপ্রাপ্ত ব্যবস্থাপকদের তোষামুদি, অদক্ষতায় ফায়ার ডিফেন্সের কারিগরি সক্ষমতা আসে না।
- অটেকসই নির্মাণ
দেশে স্থপতি ও প্রকৌশলীদের বিভিন্ন পেশাজীবী প্রতিষ্ঠান আছে। আছে ভবন নির্মাতাদের প্রতিষ্ঠান রিহাব। আছে রাজউক, গণপূর্ত মন্ত্রণালয়, স্থাপত্য বিভাগ ও সিটি করপোরেশনের প্রকৌশল শাখা। কিন্তু সবার কাজ দেখলে মনে হয়, পরিবেশ ঝুঁকি, জলবায়ু নিরাপত্তা, এমনকি নাগরিক নিরাপত্তার কোনো বোধ তাদের মধ্যে প্রতিষ্ঠানগতভাবেই গড়ে ওঠেনি। ঢাকার রাস্তায় জরুরি সেবাকর্মীদের পথ নেই, দরকারে পথ দেওয়ার চর্চাটাও নেই। মোটকথা, ঢাকা শহরের অধিকাংশ বহুতল ভবন নিয়ম মেনে নির্মাণ করা হয় না। অথচ কারও কোনো শাস্তি নেই, কারণ আছে ঘুষের দফারফা। নিয়মবহির্ভূত ভবন নির্মাণ করলে পানি, গ্যাস, বিদ্যুৎ ও পয়:নিষ্কাশনের সংযোগ পাওয়ার কথা নয়। আবার নিয়ম মেনে ভবন নির্মাণ করা হয়েছে কি না, তা পরিদর্শন করেই সংযোগগুলো দেওয়ার কথা। এমনকি ভাড়াটে পরিবর্তিত হলেও নতুন ইন্সপেকশন হওয়ার কথা। বহু খাতের রেগুলেটরি পরিদর্শনে বহু কর্মসৃষ্টির সুযোগ রয়েছে। পরিদর্শনের কিছুই হয় না, যেটা হয় সেটা হচ্ছে ঘুষ, ওপরতলার ফোন আর তদবিরে দফারফা।
- অগ্নিনিরাপত্তার সমন্বিত পরিদর্শন ও অগ্নিনিরাপত্তা মহড়া (ফায়ার ড্রিল)
প্রতিটি ভবনের ফায়ার অ্যালার্ম সিস্টেম এবং ফায়ার ডিফেন্স প্রসেস ও টুলস কাজ করে কি না, তা বছরে দুবার পরিদর্শন করার কথা। বছরে দুবার ফায়ার ড্রিল হওয়ার কথা, যা ডকুমেন্টেড হবে এবং ফলাফল অনলাইনে দেখা যাবে, যাতে সাধারণ ভাড়াটে, ব্যবসায়ী বা করপোরেট অফিসের ভাড়াটেরা জেনে-বুঝে ভাড়া নিতে পারেন, কোনো চাকরিজীবী তাঁর কর্মস্থলের নিরাপত্তা নিয়ে সচেতন থাকতে পারেন। ফায়ার ড্রিলের উদ্দেশ্য থাকে যেকোনো অগ্নিদুর্বিপাকে ঠিক কত সময়ের মধ্যে একটি ভবনকে (সাধারণত ১০ থেকে সর্বোচ্চ ২০ মিনিট) জনশূন্য করা যাবে। জনশূন্য করার দিক থেকে বলতে হয়, দেশের প্রতিটি শিল্প ভবনের বাইরে উন্মুক্ত জরুরি বাইরের সিঁড়ি রাখা উচিত। পাশাপাশি জাম্পিং প্যাডও বাধ্যতামূলক করা যেতে পারে, সাধারণ সময়ে জাম্পিং প্যাড ফাঁকা থাকবে, কিন্তু তাৎক্ষণিক প্রয়োজনে নিকটস্থ বিদ্যুতের উৎস থেকে মোটর দিয়ে জাম্পিং প্যাড ফুলিয়ে বাতাসভর্তি করা হবে।
হতাশার বিষয় হচ্ছে উৎপাদন কমে যাবে বলে দেশে ফায়ার ড্রিল করা হয় না। বাংলাদেশের তৈরি পোশাকসহ অধিকাংশ শ্রমঘন শিল্পের অগ্নিকাণ্ডে অনেক বেশি প্রাণহানি হয়। শ্রমিকেরা যাতে ফ্যাক্টরি থেকে বেরোতে না পারেন, সে জন্য জেলখানার মতো বন্ধী করে রাখা হয়। মানসম্মত ফায়ার ড্রিল ও পরিদর্শন হলে বিষয়গুলো বেরিয়ে আসত। রেগুলেটরি শাস্তির আওতায় আনা দরকার হীন-অপব্যবস্থাপনাকে। শুধু রেগুলেটরি পরিদর্শন নিশ্চিত করে কমপ্লায়েন্স ও সাসটেইনেবেলিটি আনা যায় অধিকাংশ ঝুঁকিপূর্ণ ভবনে। এতে কমে যাবে অগ্নিকাণ্ড, বেঁচে যাবে বহু প্রাণ, বাংলাদেশের শিল্প ও বৈদেশিক রপ্তানিও হবে অধিক টেকসই।
টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি-৮) অর্জনে কর্মস্থল নিরাপদ করার বাধ্যবাধকতা রয়েছে সরকারের, সেখানে সবার জন্য মানসম্মত নিরাপদ কর্মস্থলের ব্যাপারে সুস্পষ্ট লক্ষ্য দেওয়া আছে। শিক্ষা নির্বাসনে দিয়ে শিল্পে শিশুশ্রম জারি রেখে, ছুটিহীন, নিরাপত্তা সুরক্ষা ভাতাহীন দীর্ঘ শ্রমঘণ্টার আর স্বল্প বেতনের অনিরাপদ কাজের পরিবেশে চূড়ান্তভাবে ‘ঘাতক’ পরিস্থিতিতে ১৭টি টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন আদৌ সম্ভব কি?