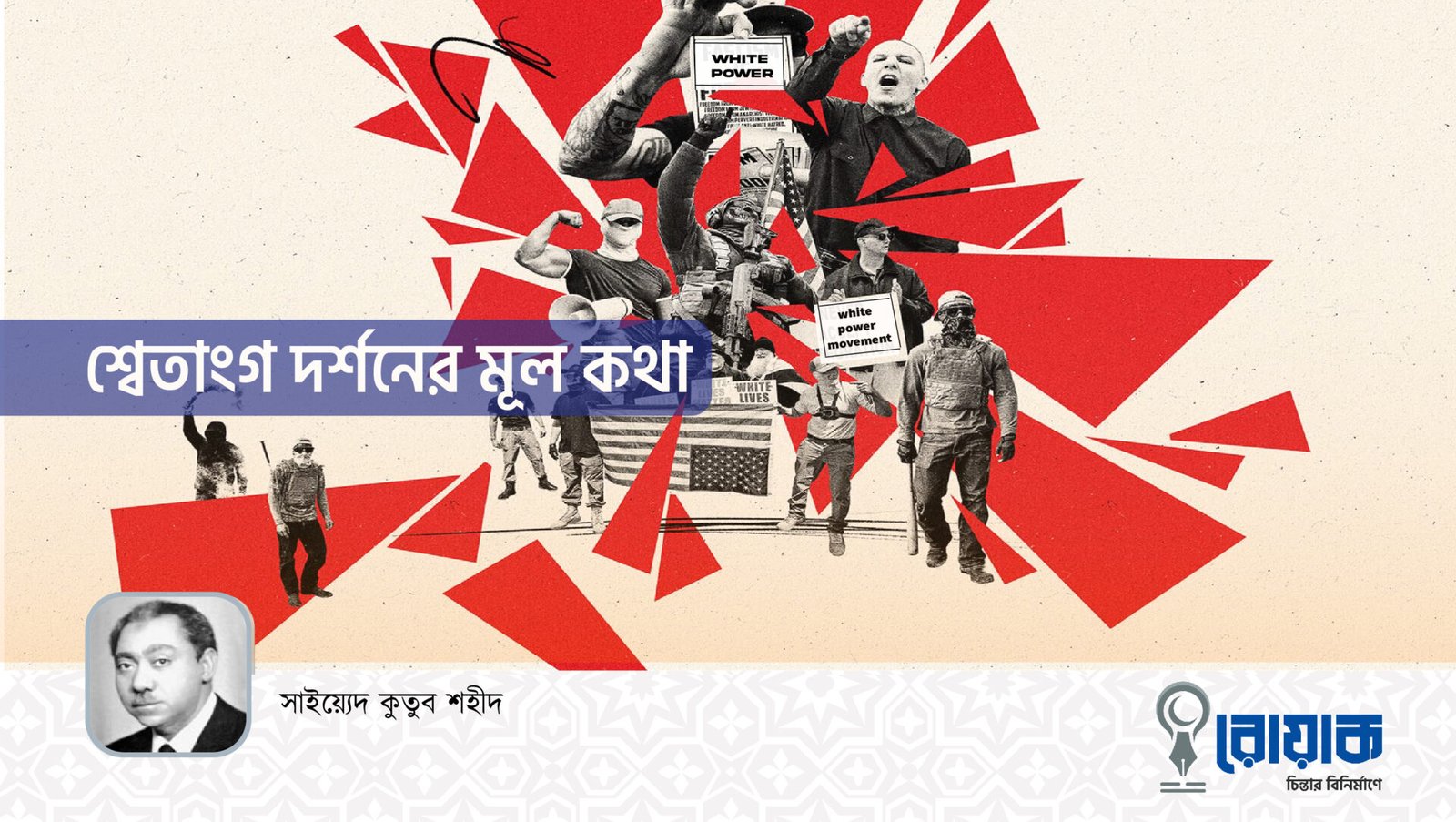ইংরেজ দার্শনিক বার্ট্রান্ড রাসেল বলেছেন যে শ্বেতাংগদের প্রতিপত্তির যুগ শেষ হয়ে গেছে। শ্বেতাংগ জাতিগুলো অনির্দিষ্ট কালের জন্য তাদের প্রাধান্য অক্ষুণ্ন রাখতে পারে না। কারণ এটা স্বাভাবিক নিয়মের খেলাফ। রাসেল বিশ্বাস করতেন যে বিগত চার শতকের মতো সুখের সময় শ্বেতাংগদের জন্যে আর আসবে না। তার মতে শ্বেতাংগ জাতিগুলোর মধ্যে কেবল রাশিয়ানরাই হয়তো এশিয়ার ওপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে। এশিয়ার লোকেরা সাম্রাজ্যবাদ ঘৃণা করে এবং তাদের ধারণা রাশিয়ার সাম্রাজ্যবাদী উদ্দেশ্য নেই। এশিয়ার লোকেরা পাশ্চাত্য জাতিগুলোর শাসনাধীন ছিলো। এরা পাশ্চাত্যবাসীদের রাজনৈতিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার শিকার ছিলো। রাশিয়ার হাতে এভাবে ব্যবহৃত হবার অভিজ্ঞতা তাদের নেই। এসব কারণে রাসেল সাহেব ভাবতেন যে এশিয়ায় পাশ্চাত্য দেশগুলোর প্রাধান্যকাল শেষ হয়ে গেছে। তিনি অবশ্য মনে করতেন যে ভারত পাশ্চাত্য ঘেঁষা হয়েই থাকবে। তিনি ধারণা করেছিলেন যে আরব জাহান- মিসর ও পাকিস্তানসহ- কমিউনিস্ট শিবিরে যোগ দেবে।
রাসেল সাহেব এই ভবিষ্যদ্বাণী ব্যক্ত করেছিলেন ১৯৫০ খৃস্টাব্দে। চীনে কমিউনিস্ট সরকার কায়েম হওয়া এবং অপরাপর ঘটনার কারণে এই ভবিষ্যদ্বাণী সত্য বলে মনে হতে পারে। কিন্তু আমাদের অভিমত এই যে এটা হচ্ছে পাশ্চাত্যের বস্তুবাদী মানসিকতার একটা অগভীর বিশ্লেষণ। বার্ট্রেন্ড রাসেল উদার চিন্তাধারার জন্যে খ্যাত ছিলেন। কিন্তু তিনি তাঁর পরিবেশ, পারিপার্শ্বিকতা, এর আদর্শবাদিতা এবং সভ্যতা দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন। এগুলো একজন চিন্তাবিদের বস্তুনিষ্ঠ ও সর্বব্যাপক পর্যালোচনার পথে বাধা হয়ে থাকে এবং নতুন কোন দৃষ্টিকোণ নিয়ে এগুলোর বিচার-বিশ্লেষণ করার পথে অন্তরায় সৃষ্টি করে।
শ্বেতাংগদের শাসনকাল সমাপ্ত। কারণ তাদের সভ্যতার সীমিত প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে। অনুসন্ধিৎসু মানব মনকে দেবার মতো কোন বাস্তবধর্মী ধারণা, চিন্তা, নীতি ও মূল্যমান এই সভ্যতার কাছে আর বাকী নেই। প্রকৃত উন্নতি ও অগ্রগতির পথে পরিচালিত করার জন্যে মানব জাতিকে এই সভ্যতা আর কিছু দিতে সক্ষম নয়। গ্লেট ব্রিটেনে ম্যাগনাকার্টার ফলশ্রুতি-কালে ফ্রান্স বিপ্লবের পরিণতি এবং আমেরিকাতে গণতান্ত্রিক পরীক্ষার ফল হিসেবে ব্যক্তিস্বাধীনতা প্রদানের পর এই সভ্যতা বন্ধ্যা হয়ে গেছে। এই মূল্যবোধ যদিও অর্ধবিকশিত নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে সমৃদ্ধ হচ্ছিলো। কিন্তু এগুলো গতিশীল মানব সমাজের জন্যে যথেষ্ট ছিলো না। ইউরোপে এসব মূল্যবোধের বাস্তবায়নের পরও দেখা গেলো এগুলো মানুষের চলার পথের পাথেয় হিসেবে যথেষ্ট নয়।
এই সভ্যতা তার মূল উৎস হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিলো যে উৎসের সাথে সংযোগ রক্ষা না করতে পারলে সমাজ ব্যবস্থা, নীতিমালা এবং মূল্যবোধ দীর্ঘকাল বেঁচে থাকতে পারে না। আর সেই উৎসটি হলো আল্লাহর প্রতি ঈমান। এই ঈমানই সামগ্রিক অস্তিত্বের ব্যাখ্যাদান করে। বিশ্লেষণ করে মানুষের পজিশন এবং মানব জীবনের উদ্দেশ্য। মূল উৎস হতে বিচ্ছিন্ন এই সভ্যতাটি তাই একটা সাময়িক সভ্যতা। মানব প্রকৃতির গভীরে যা কোনদিন তার শিকড় গাড়তে পারেনি।
স্বর্গীয় উৎস হতে উৎসারিত না হওয়ার কারণে এই সভ্যতা এমন সব ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো যেগুলো মানব-অস্তিত্ব ও প্রকৃতির সাথে সাংঘর্ষিক ছিলো। মৌলিকত্ব ও পদ্ধতির দিক থেকে এই সভ্যতা মানুষের প্রকৃত প্রয়োজনগুলোকে অবহেলাই করেছে যেসব প্রয়োজন মানব-সৃষ্টি ও গঠনের বিশেষত্বের কারণে স্বাভাবিকভাবে বিদ্যমান। যেসব প্রাথমিক মূল্যবোধ মানুষকে মানুষ হিসেবে স্বীকৃতি দেয় সেগুলো করা হলো অবহেলা। এগুলো যে কেবল অবহেলাই করা হয়েছে তাই নয়, বরং এগুলো ভীষণভাবে পদদলিত করা হয়েছে।
এই পরিস্থিতিতেই জন্ম নিলো নেতিবাচক আচরণের প্রচণ্ডতা- একটা মানসিক ব্যাধি। এই ব্যাধির ফলে ধর্মকে অস্বীকৃতি জ্ঞাপনের ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠেছে আজকের সভ্যতা। মানব জীবনের বাস্তবতার প্রতি বৃদ্ধাংগুল দেখিয়ে মানবীয় প্রয়োজনকে উপেক্ষা করে এবং ন্যায়নিষ্ঠ মূল্যবোধ বিসর্জন দিয়ে এই সভ্যতা সম্মুখে এগুতে থাকলো।
এথেকেই বুঝা যায় এই সভ্যতাকালে মানবতার দুর্গতির কারণ। গোড়ার দিকে এই সভ্যতা মানবতার সেবা, উন্নতি ও কল্যাণের অভিপ্রায় নিয়েই অগ্রসর হচ্ছিলো। পরে তা গতিপথ হারিয়ে ফেলে। কোন সভ্যতা যখন মানব প্রকৃতি বিরোধী হয়, তখন একটা সংঘাত শুরু হয়। এই সংঘাতের পরিণতি সেজে আসে বিপত্তি, জান-মালের ক্ষতি, হতাশা-নিরাশা, ধ্বংস ও মৃত্যু। এই সংঘাতের শেষ পর্যায়ে অবশ্যম্ভাবী রূপে এই সভ্যতাই হয় পরাজিত। মানব প্রকৃতি হয় বিজয়ী। কারণ সভ্যতার ক্রমবিকাশমান পর্যায়গুলোর চেয়ে মানব প্রকৃতি আরো বেশী উন্নত ও স্থায়ী।
এই মানদণ্ডে বিচার করলে সুস্পষ্টভাবে বলা যায় যে রাশিয়ান, ব্রিটিশ, ফরাসী, সুইডিস, আমেরিকান এবং অন্যান্য সব সাদা আদমীরা একই পর্যায়ের। রাশিয়ানরা বরং বেশী পেছনে। কেননা তাদের স্বৈরাচারী ব্যবস্থাটাই তো পুলিশী নিয়ন্ত্রণ, রক্তপাত, শুদ্ধি অভিযান এবং শ্রম শিবিরে শাস্তি-ব্যবস্থা ছাড়া টিকে থাকতে পারে না। অন্য সব ব্যবস্থার চেয়ে এই ব্যবস্থা মানব প্রকৃতির অধিকতর বিরোধী। অস্তিত্ব, জীবন রহস্য ও বিশ্বজগত সম্বন্ধে মার্কসবাদের অজ্ঞতার কথা না-ই বা বললাম। মার্কসবাদ মানবাত্মা, এর প্রকৃতি এবং ইতিহাস সম্পর্কে অজ্ঞ। বস্তুগত লাভ ও জৈবিক ক্ষুধা নিবৃত্তির সংগ্রামে সার্বিক মানবিক কর্মোৎসাহ নিয়োগ করতে মার্কসবাদ চেষ্টিত। মার্কসবাদ সব ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর পেছনে কেবলমাত্র উৎপাদন পদ্ধতিকেই ক্রিয়াশীল মনে করে। এই মতবাদ ওসব মানবিক মূল্যবোধ বাতিল করে দেয় যেগুলো পশুর ইতিহাস এবং মানুষের ইতিহাসকে পৃথক রূপ দিয়েছে। এই মতবাদ মানুষের সবচে’ বড়ো কাজটিকে অস্বীকার করে। মার্কসবাদ স্বীকার করে না যে মানব সত্তাই ইতিহাস বিবর্তনের সর্বপ্রধান ইতিবাচক শক্তি। এই মতবাদ ভবিষ্যতকে মানবিক উত্তরাধিকার বিবর্জিত রূপে অংকন করেছে। ধারণা দেয়া হয়েছে মানুষগুলো সব ফিরিশতা সেজে সামর্থ্য অনুসারে উৎপাদন করবে এবং শুধু নিজের প্রয়োজন মতো পরিমিত সম্পদ গ্রহণ করবে। এই মতবাদ এই ধারণাও ব্যক্ত করেছে যে সব ক্রিয়াকাণ্ড সরকার বা নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা ব্যতিরেকেই সম্পন্ন হবে। এর জন্য জাহান্নামের ভয় প্রদর্শন এবং জান্নাতের সুসংবাদ দেবার কোন প্রয়োজন নেই। বুর্জোয়া ব্যবস্থা উৎপাটিত হলে এবং সর্বহারাদের নেতৃত্ব কায়েম হলেই মানব-প্রকৃতি ও চরিত্রে এই বিরাট বিপ্লব আপনা আপনি ঘটে যাবে।
মার্কসীয় ঐতিহাসিক মতবাদ মানব-প্রকৃতি এবং মানব-ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষাগুলোকে অবোধগম্য করে তুলেছে। যতদিন পর্যন্ত মানব-প্রকৃতি সম্বন্ধে এই নিরেট অজ্ঞতা বিরাজ করবে এবং যতদিন মার্কসবাদে ওই পৌরাণিক কাহিনী গৃহীত থাকবে, ততদিন কোন বাস্তবমুখীন জীবন ব্যবস্থা আমরা এই মতবাদ থেকে আশা করতে পারি না। আর তাই এই মতবাদ স্বৈরতান্ত্রিক উপায়েই মানুষের উপর চাপিয়ে দিতে হবে।
মার্কসীয় মতবাদ এবং বাস্তব রূপের মাঝেও আছে আকাশ-পাতালের পার্থক্য।
মূলনীতিগুলো থেকে অনুসৃত নীতিগুলো ভিন্ন মার্কসবাদীরা মার্কসবাদের অতি ‘পৰিত্ৰ’ বক্তব্যকেও বর্জন করেছে। অবশ্য তারা এই বর্জনকে যুক্তিযুক্ত প্রমাণ করার আপ্রাণ কোশেশ করেছে। এই প্রসঙ্গে তারা এই খোঁড়া যুক্তি দাঁড় করিয়েছে যে মার্কসবাদ ক্রমবিকাশধর্মী। অথচ মার্কসবাদের মতো কড়া গতিহীন ও স্বৈরাচারী মতবাদ পৃথিবীতে আর একটিও নেই। প্রাকৃতিক আইনের অমোঘ দাবীর কাছে মার্কসবাদের প্রধান নীতিগুলোকে মাথানত করতে হয়েছে। শেষ পর্যন্ত স্বৈরতান্ত্রিক রাষ্ট্র ছাড়া আর কিছু অবশিষ্ট থাকেনি এবং এই জাতীয় রাষ্ট্রের নাগরিক হবার সৌভাগ্য জার আমলেও রাশিয়ানদের হয়েছিলো।
মার্কসবাদ অনুযায়ী রাষ্ট্র উবে যাবার কথা ছিলো। বিগত অর্ধ-শতাব্দীতে সে প্রক্রিয়ার অন্ততঃ সূচনা তো হওয়া উচিত ছিলো। কিন্তু রাষ্ট্র এখনো আছে। দিনের পর দিন তা মোটা হচ্ছে। জনগণের ও তাদের সর্বস্ব রাষ্ট্র গ্রাস করে ফেলছে। মার্কসবাদ অনুসারে স্বাভাবিক পন্থায় সরকার-ব্যবস্থা বিলীন হয়ে যাবার কথা ছিলো। অথচ আজ একটা শক্তিশালী সরকার অবলম্বন করেই মার্কসবাদকে বেঁচে থাকতে হচ্ছে। এখন তো বেঁচে আছে শুধু সরকার। ব্যক্তি, জনগণ এবং মানব- প্রকৃতির বিশেষ অধিকার বেঁচে নেই। এগুলো মার্কসবাদের স্টীম রোলারের নীচে পিষ্ট হয়ে মৃত্যুবরণ করেছে।
মার্কসবাদ অবোধগম্য ‘বৈজ্ঞানিক’ ভুল ছাড়া আর কিছুই নয়। রাশিয়ায় যে পুলিসী সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তা জার আমলেরই পুনরাবৃত্তি। এই পুলিশী ব্যবস্থা সীমিত কালের জন্যে কোন অনুন্নত দেশে প্রবর্তন করা সম্ভব। যেসব দেশ ও জাতি স্বীয় সত্তা সম্বন্ধে সচেতন, তারা এমন ব্যবস্থা বেশী দিন বরদাশত করতে পারে না। যেসব জাতি এই ব্যবস্থার অবিচারের শিকার তারা সহজাত প্রবৃত্তির তাকিদেই মার্কসবাদ বিরোধী। যদিও তারা অতীতে জার ও অন্যান্য ডিকটেটরদের অধীনে অনেক দিন ছিলো। শক্তি প্রয়োগ না করে এবং দমননীতি অবলম্বন না করে মার্কসবাদ টিকে থাকতে পারে না। কমিউনিস্ট রাষ্ট্রে জীবনাযাত্রার সব উৎস রাষ্ট্রের কুক্ষিগত করা হয় এবং প্রশাসনিক যন্ত্রের ওপরে কমিউনিস্ট পার্টির সর্বোচ্চ চক্রটি হয় সব ক্ষমতার মালিক। বিশেষ শিক্ষাব্যবস্থার মাধ্যমে তরুণ মনকে মার্কসীয় ভাবধারায় গড়ে তোলা হয়। তথ্য বিভাগ ও প্রচার যন্ত্রগুলোও রাষ্ট্রের কঠোর নিয়ন্ত্রণাধীন থাকে। কমিউনিস্ট ছাড়া অন্য কোন লোককে শিক্ষালয়গুলোতে শিক্ষক নিযুক্ত করা হয় না। কমিউনিজমের প্রতি আনুগত্যশীল নয় বলে যাকে মনে হয় তাকে দুনিয়া থেকে বিদায় দেয়া হয়। এই ধরনের অনেক কিছুই সেই সমাজে প্রচলিত রয়েছে। কিন্তু এতো কড়াকড়ি ও নির্যাতনের মুখেও মানব প্রকৃতি সে মতবাদের প্রতি ঘৃণাভাব প্রদর্শন করে এবং বিদ্রোহী মনোভাব প্রকাশ করে। মানব প্রকৃতি দীর্ঘকালের জন্যে এই স্বৈরাচারী ব্যবস্থা মেনে নিতে পারে না। ভীতি প্রদর্শন ও নির্যাতন ছাড়া এই মতবাদ বাঁচতে পারে না, এটাই তো এই মতবাদের ব্যর্থতার উজ্জ্বল প্রমাণ।
এই বিশ্লেষণের আলোকে আমরা বলতে পারি যে বাট্রেন্ড রাসেলের ভবিষ্যদ্বাণী এক নড়বড়ে ভিত্তির ওপর নির্ভরশীল। বাস্তব সত্য সীমিত বস্তুবাদী মানসিকতার গণ্ডী ডিংগিয়ে সম্মুখে প্রবাহিত হচ্ছে।
অবশ্য সমস্যাটা সুগভীর এবং সিরিয়াস। আল্লাহ ও তাঁর নির্দেশিত পথ থেকে দূরে অবস্থিত একটা সভ্যতার সমস্যা এটি। এটা সামাজিক ব্যবস্থা, চিন্তাধারা এবং জাগতিক মতবাদের সমস্যা। স্বর্গীয় উৎস হতে বিচ্ছিন্ন, মানবজীবনের সঠিক ব্যাখ্যাদানে ব্যর্থ এবং বিশ্বলোকের সাথে মানবজীবনের সম্পর্ক নির্ণয়ে অপারগ মতবাদের সমস্যা এটি।
এটা ভয়ানক নেতিবাচক আচরণের সমস্যা। এই মানসিক ব্যাধিটা, রাশিয়ান, আমেরিকান, ইংরেজ, ফরাসী, সুইস, সুইডিস ইত্যাদি জাতিসমূহের এবং তাদের পদাঙ্ক অনুসরণকারীদের এটা সাধারণ ব্যাধি। এই জাতিগুলো আজ এক বিপজ্জনক স্থানে পা রেখে দন্ডায়মান।
এসব দেশে যে সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত এগুলোর সাধারণ উৎস ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ। পুঁজিবাদী আমেরিকায় গীর্জার দ্বার মুক্ত রাখা, কমিউনিস্ট রাশিয়ায় গীর্জা বন্ধ করে দেয়া অথবা সুইডেনের মতো সমাজবাদী দেশে নাস্তি কতাবাদের অবাধ প্রচার ব্যবস্থা করে গীর্জার প্রতি উদাসীনতা দেখানোর মধ্যে বড়ো রকমের কোন পার্থক্য নেই। স্বর্গীয় মতবাদের অণুপ্রেরণায় এগুলোর কোনটাই গড়ে উঠেনি। কাজেই এগুলোর বাহ্যিক পার্থক্য ও সমাজ ব্যবস্থার নানা ঢং আমাদের কাছে খুব তাৎপর্যপূর্ণ নয়। কারণ ধর্মীয় মতবাদই তো সঠিক পথের দিশা দিয়ে থাকে, অন্য কোন মতবাদ নয়।
এই মৌলিক উৎস থেকেই সমাজ-ব্যবস্থা ও চিন্তার সঠিক মানদণ্ড পাওয়া সম্ভব। কারণ এটা মানব-প্রকৃতির গঠন-বৈশিষ্ট ও তার প্রকৃত চাহিদাসমূহ পূরণ করতে সক্ষম। এই হলো সমস্যার গভীর ও ব্যাপক বাস্তবতা। এই বাস্তবতা বার্ট্রেন্ড রাসেলের বর্ণিত বাস্তবতা থেকে ভিন্ন। রাসেল ছিলেন প্রচলিত বস্তুবাদী সভ্যতার হাতে বন্দী। পাশ্চাত্যের সব দার্শনিকই তাঁদের পরিবেশ ও নেতিবাচক চিন্তাধারা দ্বারা প্রভাবিত। পাঁচটি শতাব্দীর প্রভাব তাদের চিন্তা ও দর্শনকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে।
এই দুর্বলতা পাশ্চাত্য সংস্কৃতির কাঠামোকে নড়বড়ে করে ফেলেছে। এর ফলে আত্মা শ্বাসরুদ্ধকর অবস্থায় নিপতিত। মানবতাবাদী মূল্যবোধ লাঞ্ছিত। জীবনে বস্তুগত সমৃদ্ধি অর্জিত হওয়া সত্ত্বেও কতগুলো অর্থহীন মূল্যবোধ প্রকৃত ও কল্যাণকর মূল্যবোধগুলোকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। এর ফলে মানবজীবন পশ্চাদমুখীনা অথবা স্থবিরতার শিকারে পরিণত হয়েছে এবং তার ক্রমোন্নতি বাধার সম্মুখীন হয়ে পড়েছে। বস্তুগত জীবনে বিপুল সমৃদ্ধি অর্জন করেও মানব জীবন তার স্বাভাবিক বর্ধন ও ক্রমবিকাশ-বঞ্চিত। বর্তমান সভ্যতা মানব- প্রকৃতিকে উপেক্ষা করছে। একে এড়িয়ে চলছে। এ জন্যে এই মারাত্মক পরিণতি আত্মপ্রকাশ করেছে।
বস্তুবাদী সংস্কৃতির বাহ্যিক চাকচিক্য যাতে আমাদের চোখ ধাঁধিয়ে না দিতে পারে সেদিকে আমাদের লক্ষ্য রাখা উচিত। এই চাকচিক্যের প্রভাবে বিহ্বল হয়ে আমরা যেন মানব জীবনের নিদারুণ যন্ত্রণা উপেক্ষা না করি। মিসাইল এবং কৃত্রিম উপগ্রহের সমারোহের আড়ালে উঁকি মেরে তাকালে আমরা দেখতে পাবো মানব জাতি কত দ্রুত ধ্বংসের দিকে ছুটে চলছে।
মানুষ আল্লাহর অতি প্রিয় সৃষ্টি। আশরাফুল মাখলুকাত। সে পৃথিবীতে আল্লাহর প্রতিনিধি। পৃথিবীর সবকিছু তারই জন্যে সৃষ্ট। মনুষ্যত্বের মাপকাঠি দিয়ে মানুষের অগ্রগতি বা পশ্চাৎগতি পরিমাপ করতে হয়। তার আত্মিক সুখ মানেই হচ্ছে তার প্রকৃতির সাথে সভ্যতার উপাদানগুলোর সংগতি।
কাজেই আমরা যদি মানবতা এবং মানবিক মূল্যবোধগুলোকে নিম্নগামী, দেখি, মানুষকে প্রেরণা, বৃদ্ধিবৃত্তি ও নৈতিকতার ক্ষেত্রে অধোগামী দেখি, মানুষের মূল দায়িত্ব পালন যদি নিশ্চল দেখি, মানুষকে যদি যন্ত্রণা, উদ্বেগ ও সংশয়বাদে হাবুডুবু খেতে দেখি তাকে যদি মনস্তাত্বিক বিপর্যয়, উন্মাদনা ও অপরাধ-প্রবণতার শিকার দেখি, তাকে যদি উদ্দেশ্যহীন জীবন-যাপন করতে দেখি, মদ-আফিম খেয়ে একঘেয়েমী তাড়াবার প্রচেষ্টায় লিপ্ত দেখি এবং তাকে যদি স্বীয় সন্তানদের হত্যা অথবা বিক্রি করে রিফ্রিজারেটার অথবা ওয়াশিং ম্যাসিন ক্রয় করতে দেখি তখন আমরা কোন্ সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি? মানবতার এই করুণ অবস্থা দেখে আমাদেরকে অবশ্যই বলতে হয় যে এই বিলাস-প্রিয় সভ্যতা মানুষের আত্মিক প্রয়োজন উপক্ষো করে বস্তুগত ও যান্ত্রিক সমৃদ্ধি অর্জন করে মানবতার অবক্ষয় ঠেকাতে পারেনি। মানবতাকে প্রকৃত সুখ দিতে পারেনি। বৈজ্ঞানিক ও বস্তুগত অগ্রগতি এই সভ্যতার ব্যর্থতা ঢাকতে পারেনি। এই সভ্যতা তার সম্মুখে দেখতে পাচ্ছে এক মহাবিপর্যয়। এই সত্যটি অপরিবর্তনীয় থাকছে যে
মানবগোষ্ঠী আরেকটি জীবন-ব্যবস্থার প্রয়োজন তীব্রভাবে অনুভব করছে, যে ব্যবস্থায় ভুল-ভ্রান্তি থাকবে না, যা মানুষের জীবনকে কলুষিত করবে না এবং বিজ্ঞানের অগ্রগতি, পরিণতি এবং জ্ঞানকেও পণ্ড করে দেবে না। মানুষের জন্যে আজ এমন এক ব্যবস্থা প্রয়োজন যা মানুষকে তার অস্তিত্বের সঠিক উপলব্ধি দান করবে এবং মানুষের উপযোগী ও তার প্রকৃতির সাথে সমিল সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে তার চিন্তা, বিজ্ঞান ও পরীক্ষণ-পরিণতির সদ্ব্যবহার করবে।
শ্বেতাঙ্গদের দিন ফুরিয়েছে। তারা আর সভ্যতার অঙ্গনে বিশেষ কোন ভূমিকা পালনের অবস্থায় নেই। রাশিয়ান, আমেরিকান, ব্রিটিশ, ফরাসী, সুইস, সুইডিস- সব শ্বেতাঙ্গের জন্যে একই কথা। পাশ্চাত্য মতবাদসমূহ এবং ইউরোপীয় মানসিক ব্যাধি স্কিজোফ্রেনিয়ার পরিণতিরূপেই এই ভূমিকা সমাপ্ত হয়েছে।
যেসব মতবাদ, ব্যবস্থা, সংগঠন ও পরিকল্পনার ওপর মানুষের জীবন গড়ে ওঠে সেগুলোকে অবশ্যই যুক্তিনির্ভর হতে হবে। এগুলোতে অবশ্যই মানুষের সঠিক মর্যাদা ও জীবনের চূড়ান্ত লক্ষ্য নির্ণীত থাকতে হবে। মতবাদের উপস্থাপিত ব্যাখ্যা আর বাস্তব জীবনের স্বাভাবিক ধারার মধ্যে থাকতে হবে মিল। নির্ভুল ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ মানব জীবনের অত্যাবশ্যকীয় বিষয়গুলোর অন্যতম। একে শ্বেতাঙ্গগণ উপেক্ষা করেছে। বরং এর বিরুদ্ধে প্রাণপণ লড়াই করেছে। এদিক থেকে পশ্চিম অথবা পূর্বের মানব রচিত সব ব্যবস্থাই একই ধরনের।
কিন্তু মানুষ অতীতে যা ছিলো আজো তাই আছে। তার চিন্তার উন্মেষ, হৃদয়ের প্রশান্তি, বিশ্বজগত ও জীবনের ব্যাখ্যা এবং স্রষ্টার সাথে সম্পর্ক নির্ণয়ের জন্যে সে সবসময় একটা প্রত্যয়ের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছে। সে এমন এক প্রত্যয় বা বিশ্বাস অনুসরণ করতে চায় যা তার স্বীয় সত্তা, তার কাল ও তার জেনারেশন হতে বৃহত্তর এবং তার বাস্তবতা হতে মহত্তর লক্ষ্যের স্বীকৃতি দেয়। সে চায় যে তার প্রত্যয়বাদ তাকে এমন এক সত্তার সাথে সম্পর্কিত করুক যিনি তাকে পদনির্দেশ ও নিরাপত্তা দান করতে সক্ষম। সে ওই সত্তাকে ভয় করতে চায়, ভালবাসতে চায়। সেই সত্তা থেকে সে তুষ্টি কামনা করবে এবং তাঁর কাছে সব উত্তম কাজ করার সাহায্য লাভের প্রার্থনা জানাবে। তাঁর কাছে পাপ নিয়ে উপস্থিত হতে সে লজ্জাবোধ করবে। এমন এক সত্তার প্রতি বিশ্বাস মানুষের অতীব প্রয়োজন। এথেকেই মানুষ অর্জন করে চিন্তার বিশেষ ধারা; আচরণের নীতিমালা এবং উপাসনার নিয়ম-কানুন। এটা অর্জিত হলে তার সামগ্রিক জীবন সংগতিপূর্ণ হয়। জীবন হতে দূর হয় সব বৈসাদৃশ্য।
দৈহিক ক্ষুধা, বস্তুগত সমৃদ্ধির নেশা ও ইন্দ্রিয় সুখের মাঝে একজন মানুষ কিছুকাল ডুবে থাকতে পারে। কিন্তু মানব সত্তা এই বস্তুগত প্রয়োজন ও প্রয়োজন পূরণের মাঝে নিঃশেষ হয়ে যায় না। বস্তুগত প্রয়োজন মিটে যাবার পরও আরো কিছু প্রয়োজন বাকী থেকে যায়। বরং বস্তুগত প্রয়োজন মিটে যাবার পরে পানাহার, পোশাক-পরিচ্ছদ ও সম্পদ দ্বারা পূরণ করা সম্ভব নয় এমন একটা ক্ষুধা মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। এই ক্ষুধা ভিন্ন রকমের। এটা হচ্ছে মানুষের চেয়েও বৃহত্তর এক শক্তি, ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বিশ্ব হতে বৃহত্তর এক বিশ্ব এবং পার্থিব জগত হতে ভিন্নতর এক জগতের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের ক্ষুধা। মানুষের মন চায় বাস্তব জীবনের আইন এবং তার বিবেকের আইনের মাঝে একটা সম্প্রীতি। তার মন কামনা করে মানুষের ব্যক্তিগত বাস্তবতা এবং বিশ্বলোকের বাস্তবতার মধ্যকার একটা মিল। মনের গভীরে প্রতিটি মানুষ এক আল্লাহর অনুসন্ধান করে ফিরে যিনি একাধারে তাকে নৈতিক এবং সামাজিক আইন নির্দেশ করবেন।
মানব সত্তার গভীরে লুক্কায়িত বিভিন্ন রকমের ক্ষুধার নিবৃত্তি ঘটাবার ব্যবস্থা না। দিয়ে কোন জীবনব্যবস্থাই মানুষের প্রকৃত ও সঠিক সুখ নিশ্চিত করতে গারে না। শ্বেতাংগদের সভ্যতায় এই গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্টটির অভাব রয়েছে। আর প্রধানতঃ এই কারণে মানব সভ্যতায় শ্বেতাংগদের বিশেষ ভূমিকা পালনের দিন শেষ হয়ে গেছে।
অনুবাদঃ এ. কে. এম. নাজির আহমদ।