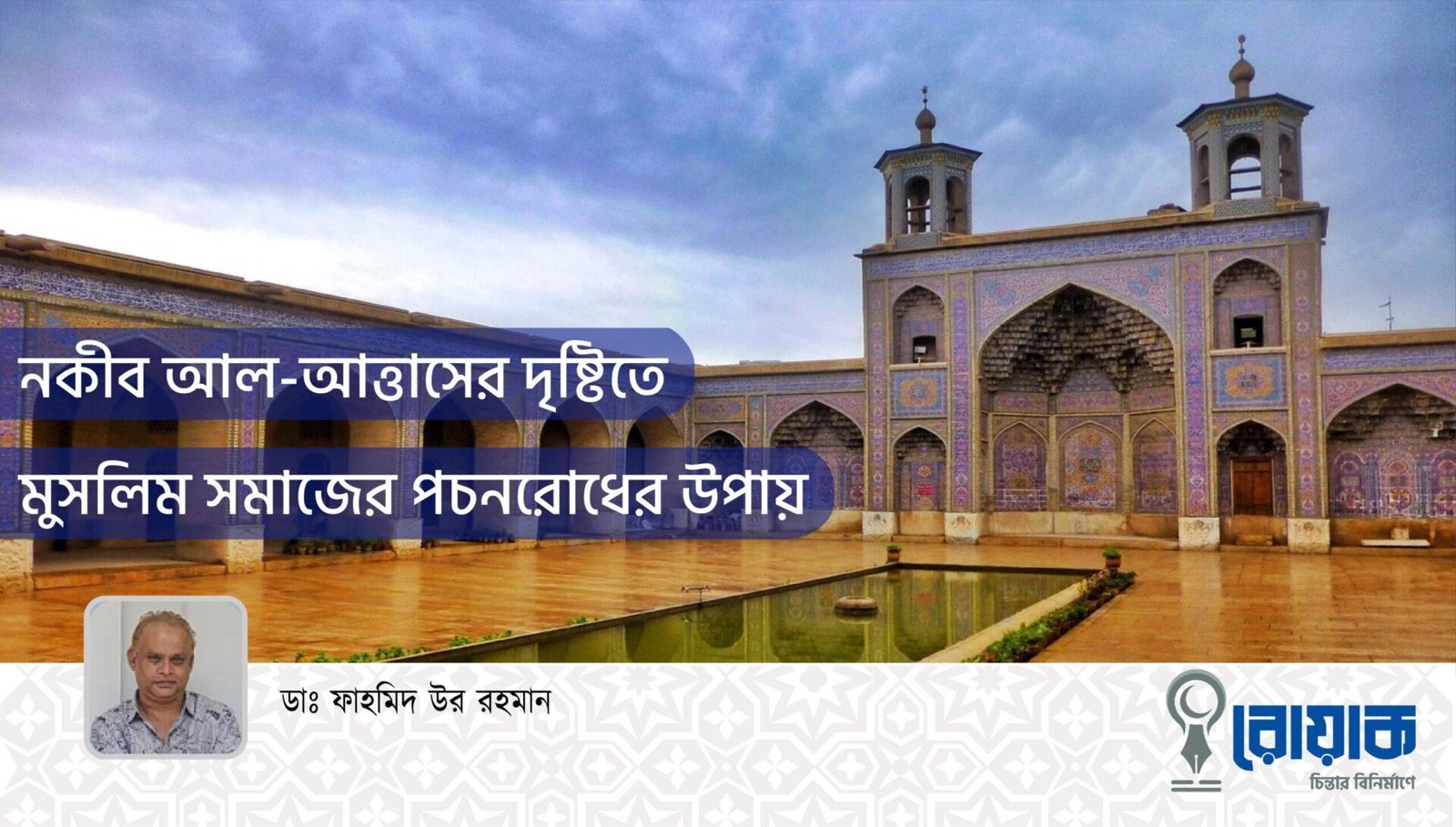মুসলিম সমাজের পচনরোধের কি কোনোই উপায় নেই? আল-আত্তাস মনে করেন মন ও সমাজের জন্য এই মুহূর্তে জরুরি প্রয়োজন হচ্ছে এর decolonization বা বি-উপনিবেশীকরণ এবং একই সাথে de-westernization (অপশ্চিমীকরণ)। ঔপনিবেশিক শক্তির জোরে যে জ্ঞান আমরা এতদিন প্রকৃত জ্ঞান বলে হজম করেছি, আত্তাস মনে করেন সেটি আসলে প্রকৃত জ্ঞান নয় । সেটি মূলতঃ পশ্চিমা সংস্কৃতি ও মূল্যবোধ জারিত জ্ঞান, যা প্রকৃতপক্ষে পশ্চিমাদের স্বার্থেই নিবেদিত। আল-আত্তাস লিখেছেন,
“So that the knowledge that is now systematically disseminated throughout the world is not necessarily true knowledge, but that which is imbued with the character and of western culture and civilization, and charged with its spirit and geared to its purpose.”
মুসলিম জগতে প্রতিষ্ঠিত একালে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর উদাহরণ দিয়ে আত্তাস বলেছেন, এটা আসলে পশ্চিমা জ্ঞানচর্চার পরিপুরক কেন্দ্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে । এটার উদ্দেশ্য এমন ধরনের মানুষ তৈরি করা যার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে : rational animal devoid of soul, like a circle with no centre.
এটা বিশ্বজনীনতার ভান করলেও এটার কোনো বৈশ্বিক উদ্দেশ্য নেই। যেমন নেই চূড়ান্ত কোনো নীতিগত উদ্দেশ্য । এর সবকিছুই সম্ভাব্য ও জায়মান । কারণ সেকুলার জ্ঞানতত্ত্ব প্রকৃতি ও সমাজকে নিয়ন্ত্রণ করবার এবং জৈবিক প্রয়োজন পূরণের লক্ষ্যে পরিচালিত। কিন্তু এর বাইরে যে একটি ঐশী ব্যবস্থাপনা রয়েছে যে ব্যবস্থাপনা মানুষকে মানুষ হিসেবে নির্মাণ করতে চায় সেটি এখানে অনুপস্থিত । ইসলাম যেমন মনে করে সকল জ্ঞানের উৎস হচ্ছে আল্লাহতায়ালা এবং এই জ্ঞান হবে শিক্ষা ব্যবস্থার ভিত্তি সেটা আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলো দিতে অক্ষম । এ কারণে এসব বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা দক্ষ মানুষ হলেও বিভ্রান্ত মানুষ। কারণ তাদের সামনে জাগতিকতার বাইরে কিছু নেই। তাই জ্ঞান সম্পর্কে ইসলামের ধারণার সাথে পশ্চিমা দার্শনিকদের ধারণার মধ্যে মৌল তফাৎ রয়েছে। সেই তফাতের দিকটা আল-আত্তাস এভাবে তুলে এনেছেন :
“Thus we see that, already in this most fundamental concept in life the concept of knowledge- Islam is at variance with Western civilization, in that for Islam (a) knowledge includes faith and true belief (iman ); and that (b) the purpose for seeking knowledge is to inculcate goodness or justice in man as man and individual self, and not merely in man as citizen or integral part of society it is man’s value as a real man, as spirit, that is stressed, rather than his value as a physical entity measured in terms of the pragmatic or utilitarian sense of his usefulness to state and society and the world.”
এই কারণে আল-আত্তাস শিক্ষা ব্যবস্থায় ইসলামীকরণের উপর জোর দেন। কারণ ভাবজগতে পরিবর্তন না ঘটলে বি-উপনিবেশীকরণ সম্ভব নয়। আর সেটি সম্ভব না হলে মুসলিম জগতের অসুস্থতার নিরাময় হবে না। জ্ঞানের ইসলামীকরণ বলতে তিনি বুঝিয়েছেন:
“The islamization of knowledge means the deliverance of knowledge from its interpretations based on secular ideology and from meanings and expressions of the secular”
জ্ঞানের ইসলামীকরণ করতে হলে প্রথমে শিক্ষা ব্যবস্থায় পশ্চিমা প্রভাবের দিকগুলো অপসারণ করতে হবে। বিশেষ করে মানবিক জ্ঞানকে পশ্চিমা প্রভাবমুক্ত করতে হবে । তারপরে ইসলামী জ্ঞান ও মানবিক জ্ঞানের সমন্বয় করে শিক্ষা ব্যবস্থা। গড়ে তুলতে হবে। এ ব্যাপারে জ্ঞানের ইসলামীকরণের একটি মৌলিক নীতিও তিনি হাজির করেছেন যেটা এরকম-
১ ইসলামী প্রেক্ষাপটে তুলনামূলক ধর্মতত্ত্ব ।
২. ইসলামী প্রেক্ষাপটে পশ্চিমা সংস্কৃতি ও সভ্যতাকে বুঝা।
৩. ইসলামী জ্ঞানের ভাষা আরবির উপর দক্ষতা ।
৪. ইসলামী ধর্মতত্ত্ব, সংস্কৃতি, সভ্যতা, ইসলামী জ্ঞানের দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক রূপ ও পটভূমি এবং বিশ্ব ইতিহাস হিসেবে ইসলাম অধ্যয়ন।
আল-আত্তাস মনে করেন শিক্ষা ব্যবস্থায় এই ইসলামী বৈশিষ্ট্যকে যদি কার্যকরী করা যায় তাহলেই আমরা ঔপনিবেশিকতার কুফল থেকে মুক্তিপাবো এবং সমাজের ইসলামীকরণ বলতে যা বুঝায় তা তখন দৃশ্যমান হবে। সেকুলারাইজেশনের বিপরীতে তিনি ইসলামীকরণের একটি চমৎকার সংজ্ঞা দিয়েছেন যা তার উত্তর ঔপনিবেশিক চিন্তাভাবনার একটি উজ্জ্বল হীরক খণ্ড বলা যায়। এটি হচ্ছে,
“Islamization is the liberation of man first from magical, mythological, animistic, national-cultural tradition, and then from secular control over his reason and his language.”
আল-আত্তাস মুসলিম সমাজের সেকুলারাইজেশনের বিরুদ্ধে কলম ধরেছেন । তিনি জ্ঞান জগতে এক সর্বাত্মক ইসলামী বিপ্লব চান সত্য কিন্তু তিনি কি কোনো ইসলামী রাষ্ট্র চান আজকের ইসলামবিদদের যা আরাধ্য। আল-আত্তাস তার দীর্ঘ জীবনের লেখালেখিতে ইসলামী রাষ্ট্রের কোনো রূপকল্প তুলে না ধরলেও, ইসলামী রাষ্ট্র তার মনোরাজ্যে ছায়াপাত করেছে। ইসলাম তার কাছে একই সাথে ধর্ম ও সভ্যতা আবার যেমন ব্যক্তিগত ধর্ম তেমনি সামাজিক ধর্মও বটে। আল-আত্তাস লিখেছেন:
ইসলাম যেমন ব্যক্তিগত ধর্ম তেমনি সামাজিক ধর্ম । একই দীন বা আসমানী ধর্ম ব্যক্তি মানুষকেও জীবন বিধান দিয়েছে আবার সামগ্রিকভাবে সমাজবদ্ধ মানুষগুলোর জন্যও বিধি-বিধান নিয়েছে। প্রকৃতপক্ষে ইসলাম ধর্ম ব্যক্তি ও সমাজকে বিভক্ত করে দেখে না। ব্যক্তিগত ধর্ম ও সামাজিক ব্যবস্থা এখানে ভিন্ন ও আলাদা নয় । একটি আরেকটির সম্পূরক ও পরিপূরক এবং অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। ইসলামের ব্যক্তিগত বিধি-বিধান সমাজের প্রতিটি ব্যক্তির জন্য যেমন প্রযোজ্য তেমনি সামাজিক বিধি বিধান বা ব্যবস্থাও প্রতিটি মানুষের জন্য প্রযোজ্য। একই ইসলাম ব্যক্তি ও সমাজকে লক্ষ করেই প্রদত্ত হয়েছে।
আল আত্তাস তাই ইসলামকে দীন হিসেবে দেখেন এবং দীন শব্দ দিয়ে ইসলামকে সভ্যতা হিসেবে বুঝার চেষ্টা করেন। এ ব্যাপারে তার একটি ভাষাতাত্ত্বিক ব্যাখাও রয়েছে। দীন শব্দটা মদীনা শব্দের সাথে জড়িত। যা জড়িত তমুদ্দুন শব্দের সাথে। আর তমুদ্দুন মানে হচ্ছে সভ্যতা। সে দিক দিয়ে চিন্তা করলে দীন শব্দের ভিতর ইসলামী সভ্যতাই প্রতিফলিত হয়।
এরকম একটা ব্যবস্থা বা সভ্যতা তাই শেষ বিচারে রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার দিকে এগুবে এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু সেই রাষ্ট্র কিরকম হবে আল-আত্তাস সেটা লিখেছেন:
ইসলামের সমাজ ব্যবস্থা হচ্ছে পৃথিবীতে আল্লাহতায়ালার রাজ্য । কারণ এ ব্যবস্থায় চূড়ান্ত সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী হচ্ছেন আল্লাহ, মানুষ নয়। তাঁর আদেশ-নিষেধ, আইন-কানুন ও বিধি বিধানেরই সর্বোচ্চ প্রভাব ও প্রাধান্য। মানুষ কেবল তার খলিফা বা প্রতিনিধি যাকে পরিচালনার ট্রাস্ট বা আমানত দেয়া হয়েছে । সে আল্লাহর ইচ্ছা ও সন্তুষ্টি অনুসারে প্রশাসন চালাবে ।
কিন্তু মুসলিম সমাজে যদি এরকম রাষ্ট্রের উপস্থিতি নিশ্চিত না হয় তাহলে আল-আত্তাস মুসলমানদের করণীয় সম্পর্কেও দিক নির্দেশ করেছেন :
যদি তেমনটি না হয় তাহলে ইসলামী ব্যক্তির দায়িত্ব হচ্ছে এমন রাষ্ট্র ও সমাজের বিরোধিতা এবং এমন বিভ্রান্ত সমাজকে সংশোধনের জন্য চেষ্টা চালানো।
তবে এটা মনে করা সংগত আল-আত্তাস যে ধরনের রাষ্ট্রের কথা বলেছেন তা মানবিকতা বর্জিত কৃত্রিম ও আইনের বেড়াজালে আটকানো রসকসহীন কোনো রাষ্ট্র নয় । এ কারণে আল-আত্তাস মুসলমানদেরকে তাসাউফের গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতন করেছেন । তাসাউফ হচ্ছে ইসলামের সেই ধারা যার মূল কথা হচ্ছে মানুষের সাথে স্রষ্টার অন্তরঙ্গতা এবং মানুষে মানুষে অন্তরঙ্গতা । এই নিবিড়তার সম্পর্ক আল-আত্তাস ফিরিয়ে আনার কথা বলেছেন যাতে ইহসানই (মনুষ্যত্ব) শেষ পর্যন্ত বিজয়ী হয়। আল-আত্তাসের ইসলামী রাষ্ট্র তাই ইহসান বর্জিত নয়। অবশ্য আল-আত্তাস যথেষ্ট সচেতন তাসাউফের নামে মুসলিম সমাজে অনেক ধরনের বিদআত ও বিকৃতি ঢুকে পড়েছে। এটাকে তিনি বিশুদ্ধ তাসাউফ চর্চার প্রতিবন্ধক হিসেবে মনে করেন। এর উদাহরণ হিসেবে তিনি তাসাউফকে নির্ভর করে কোনো কোনো তাত্ত্বিক যেমন প্রচার করেছেন উচ্চতম ঐশী পর্যায়ে ধর্মসমূহের একতার (Transcendent unity of religions) তত্ত্ব তাকে তিনি বিভ্রান্তিমূলক বলেছেন। কারণ তিনি মনে করেন ঐশী পরিকল্পনা অনুযায়ী পৃথিবীতে একটির পর একটি ধর্ম এসেছে এবং সেই ধারাবাহিকতায় ইসলামকে সবশেষ ও পরিপূর্ণ ধর্ম হিসেবে সাব্যস্ত করা হয়েছে এই ধর্মের বাণী কোনো গোত্রের জন্য নয়, বরং সমগ্র মানবজাতির জন্য এর আগমন। এর বাইরে আর কোনো ঐক্যের প্রয়োজন নেই । ধর্ম নির্বিশেষে মানুষে মানুষে সম্প্রীতি থাকা উচিত । ধর্মের ঊর্ধ্বে ধর্মসমূহের একতার কথা উদ্দেশ্যমূলকভাবেই প্রচার করা হয়েছে।