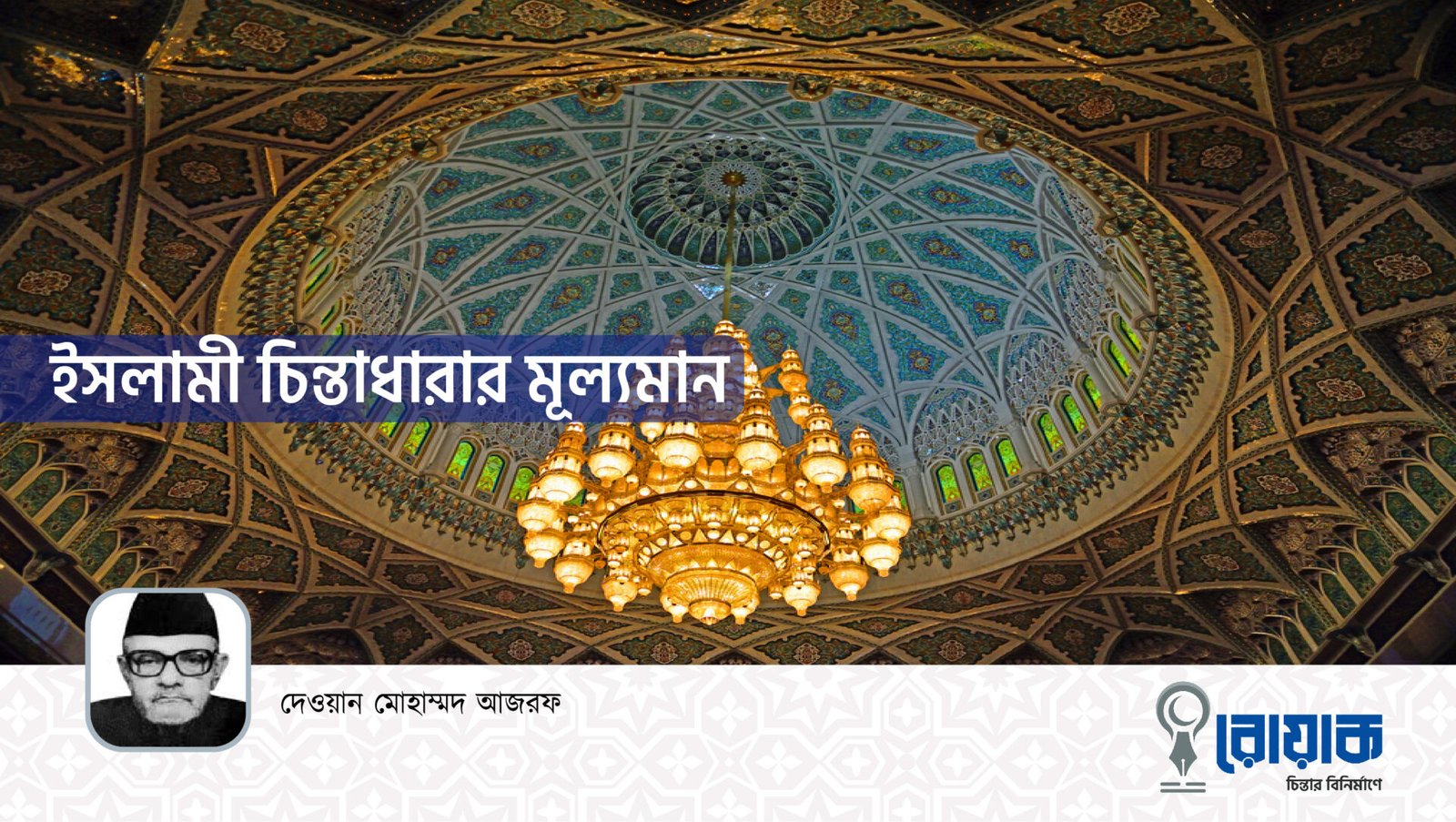এক.
অখণ্ড সামগ্রিক সত্তা হিসাবে এর মধ্যে এক অনিবার্য গতি আছে বলেই সে এক পর্যায় থেকে অন্য পর্যায়ে অপ্রতিহত শক্তিতে অগ্রসর হচ্ছে এবং মৃত্যুতে তার জীবনের লয় হয় না বরং জীবন অন্যরূপে রূপান্তরিত হয়। যে মূল্যমানবলে এ জীবনে মহত্তর বলে পরিগণিত, জীবনান্তরে মানুষ তাদের মধ্যে সে মহত্তর গুণেরই সন্ধান পাবে ।
বিভিন্ন স্থানে “মূল্যমান” শব্দটি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়। কথাবার্তায় বা অর্থনীতি শাস্ত্রে ‘মূল্য’ শব্দটি কোন বস্তুর দাম হিসাবে ব্যবহৃত হয়। তবে প্রায়োগিক উপযোগিতা ব্যতীত নানাবিধ দৃশ্য ও সুরকে মূল্যবান বলে গ্রহণ করা হয়। কারণ, সেগুলো মানব-মানসে সুখদায়ক সংবেদনের সৃষ্টি করে। গোলাপকে অথবা কোন সঙ্গীতের সুরকে মূল্যমান বলা হয়, কেননা তাদের দ্বারা আমাদের মানসে প্রীতিকর সংবেদনের উৎপত্তি হয়। এগুলো ব্যতীত ন্যায়-বিচার, দান, প্রেম, দয়া, সহানুভূতি প্রভৃতিকেও মূল্যমান বলা হয়। এগুলোর মাধ্যমে প্রীতিপ্রদ সংবেদনের উৎপত্তি হয় না সত্যি, তবুও সমাজ জীবনের সুষ্ঠু গতি ও উর্ধ্বতনের জন্য ওগুলোকে অপরিহার্য বলে গণ্য করা হয় ।
বুদ্ধিবৃত্তিক বিচারে ঐক্য, সংহতি ও সুসামজ্ঞকে মূল্যমান বলে গণ্য করা হয়। মানব সভ্যতার ইতিহাসে এগুলোর উদ্ভব হয়েছে, এবং চিন্তারাজ্যে তাদের উচ্চতর মূল্যমান বলে গণ্য করা হয়। আধুনিককালে এসব মূল্যমানকে তিন শ্রেণিতে বিভক্ত করা হয়।
- বুদ্ধিজাত
- সৌন্দর্যভিত্তিক
- নৈতিক
এ তিন বিভাগে তারা বিভক্ত। ধর্ম জগত ও দর্শনের আলোচনায় দেখা যায় এগুলোর মানব-মানসে ক্রমশ অভ্যুদয় হয়েছে এবং এগুলোর মধ্যে সমন্বয় সাধনেরও প্রয়াস হয়েছে।
প্রাচীনকালের দর্শনের আলোচনা করলে দেখা যায়, প্লেটোর দর্শনের পূর্ববর্তী চিন্তানায়কদের ধ্যান-ধারণাজাত অবদানের সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করা হয়েছে। তার ফলে মানবজাত সৌন্দর্য বৃত্তিজাত ও নৈতিকজ্ঞান-সঞ্জাত মূল্যমানের সমন্বয় তাতে দেখা দিয়েছে। বিভিন্ন ধর্মের তুলনামূলক আলোচনা করলে দেখা যায়, ভগবানের ধারণার মধ্যে বিভিন্ন যুগে পরিবর্তন দেখা দিয়েছে এবং তার কারণ রয়েছে বিভিন্ন কালের মূল্যমানের উৎপত্তিতে সত্য, শিব ও সুন্দরকে এখন সর্বপ্রধান মূল্যমান হিসাবে গণ্য করা হয়। তবে এগুলো হঠাৎ এসে মানব-মানসে উপস্থিত হয়নি। এগুলোর আবিষ্কারে মানব-মন দীর্ঘকাল নিয়োজিত ছিল। এ সবের আলোকে ভগবানের ধারণাকে পুনর্গঠনে দীর্ঘতর কাল অতিবাহিত হয়েছে এ ক্ষেত্রেও ভাববার বিষয় এই, এসব অতি প্রয়োজনীয় মূল্যমানকে সমান মর্যাদা দান করা হয়নি। কোথাও সত্যের উপর, কোথাও সৌন্দর্যের উপর, আবার কোথাও শুভ বা শিবের উপর গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। তাদের মধ্যে সম্বয়ের সূত্র আবিষ্কারের চেষ্টা করা হয়েছে সত্যি, তবে সে সমন্বয় স্থায়ী হয়নি।
সৌন্দর্যজ্ঞানের তরফ থেকে সৌন্দর্যকে চরম মূল্যমান বলে রোমান্টিক যুগের কবিরা ধারণা করেছেন। সে যুগের প্রতিনিধি স্বরূপ কীটস ঘোষণা করেছেন, ‘সৌন্দর্যের আধার বিষয়বস্তু চিরন্তন আনন্দ স্বরূপ ‘(A thing of beauty is a joy for ever)’।
সূক্ষ্মভাবে বিচার করলে-এ উক্তির মধ্যে দুর্বলতা দৃষ্ট হয়। মানব মানসে ইতিহাসের সূক্ষ্ম আলোচনা করলে দেখা যায়, কোনো এক বিশেষ শ্রেণির মূল্যমানকে প্রাধান্য দেওয়ার মূলে রয়েছে মানব ব্যক্তিত্বের খণ্ডিতকরণের ফল। ধর্মজীবনের বৈশিষ্ট্য এই যে, এতে মানবজীবনের প্রত্যেকটি দিকে সন্তোষ দানের চেষ্টা রয়েছে । ধর্মীয় মূল্যমানের ক্রমবিকাশের ইতিহাস পাঠে দেখা যায় এতে ঐক্য, ন্যায়-বিচার ও প্রেম একে একে অভ্যুদিত হয়ে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে অন্য মূল্যমানগুলো এদের পরে বিবর্তিত হয়েছে।
ভগবানের ধারণারই আলোচনা করা যাক। সর্বপ্রথম Animism, তারপর বহু দেবতাদের Polytheism স্তর থেকে দ্বৈতবান ও সর্বশেষে একেশ্বরবাদের উৎপত্তি হয়েছে মানব জীবনে। বিচার-বুদ্ধির উৎপত্তিতে মানুষ স্পষ্টই বুঝতে পারে, গাছ, বৃক্ষ পাথর অথবা প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলী স্বয়ংনির্ভর নয়। তারা সামাজিক মানুষের মত পরস্পরের উপর নির্ভরশীল। এজন্য মূলে মানুষ বহু দেবতাবাদে দীক্ষা গ্রহণ করে বহু দেবতাবাদের প্রাকৃতিক আইন-কানুন ও শক্তিগুলোকে স্বতন্ত্র দেবতা হিসাবে পূজা করার নীতি গ্রহণ করা হয়। তবে বহু দেবতাবাদে ঐক্য ও ন্যায়নীতি নামক মূল্যমানের সন্তোষ বিধান সম্ভবপর হয়নি পরস্পরের সঙ্গে কোন্দলরত বহু দেবতাদের কি করে পূজা করা যায়? কিসেই বা তাদের সমান করা সম্ভবপর? এজন্য-ই বহু দেবতবাদ দ্বৈতবাদে পরিণত হয়। এ নতুন ধর্মের আবিষ্কারক জরথুস্ত্রই দুজন পরস্পর-বিরোধী দেবতার ব্যক্তিত্বে, মঙ্গল ও অমঙ্গলের সবগুলো গুণ একত্রিত করে তাদের স্বকীয় আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। আহরা-মাজদার মধ্যে রয়েছে সবগুলো মহৎ গুণের সমাবেশ। তিনি এ দুনিয়াকে মহত্তর পর্যায়ে উত্তোলন করতে সতত প্রয়াসী। আহরিমান কিন্তু সর্বদাই এ দুনিয়াকে অতল তলে তলিয়ে দিতে তৎপর। তবে এ ধর্মে ধারণা করা হয় পরিশেষে আহুরা- মাজদার জয়ই অনিবার্য। তার ফলে তৎকালীন মূল্যমানগুলোর বিচার ও পুনর্গঠনও অনিবার্য হয়ে পড়ে যদি সত্যিই মহৎ গুণের প্রতিষ্ঠাতা আহরা-মাজদার জয়ই হয় এবং অমঙ্গল বিধানকারী আহরিমনের পরাজয় হয়, তাহলে একই ভগবানের দুটো গুণের দ্বারা তা বাস্তবায়িত হবে না কেন? তিনিই-তো এ পরস্পর বিরোধী গুণাবলীর আধার রূপে তাদের একটির অপরটির নিরসন সম্পন্ন করতে পারেন।
বিশ্বের চিন্তাধারায় ইসলামের বিশিষ্ট অবদান হচ্ছে এই ইসলাম মানব জীবনকে দ্বিখণ্ডিত করেনি। এতে আধ্যাত্মিক ও জাগতিক বলে দু’টো বিভাগ ইসলামে জীবনকে ধারণা করা হয়েছে।
দুই.
ইসলামী চিন্তাধারার মূল উৎস আল-কোরআন। কোরআনের সূরা থেকেই আল্লাহ সম্বন্ধে পূর্ণাঙ্গ ধারণা গ্রহণ করা হয়েছে। এ আল্লাহর ধারণা থেকে ইসলাম-জগতে অন্যান্য মূল্যমানের উৎপত্তি হয়েছে ফলে এ ধারণার মধ্যেই মূল্যমানগুলো উহ্য ছিল বলে স্বীকার করে নিতে হয়। তবে স্বয়ং আল্লাহ-ই আল কোরআনে মানুষকে চেষ্টা করে হিকমত বা বৈজ্ঞানিক জ্ঞান অর্জন করতে এবং প্রকৃতি ও ইতিহাস থেকে জ্ঞানার্জন করার জন্য আদেশ করেছেন।
আল্লাহর ধারণা থেকে মুসলিম চিন্তানায়কেরা বহু সিন্ধান্ত গ্রহণ করেছেন এবং বহু মূল্যমান স্বীকার করে নিয়েছেন। তাঁরা আল-কোরআনের নির্দেশ মত প্রকৃতি ও ইতিহাসের ধারা পাঠ করেছেন তার ফলে মুসলিম-জীবনে বহু মূল্যমানের উৎপত্তি হয়েছে। তাদের যথাক্রমে কোরআনিক ও মৌলিক মূল্যমানগুলোর সঙ্গে কোরআনিক মূল্যমানের কোন সংঘর্ষ দেখা দেয়নি। বরং, তাদের মধ্যে পারস্পরিক ঐক্য পরিলক্ষিত হয়। প্রকৃতপক্ষে, ব্যক্তিগত গবেষণাপ্রসূত মূল্যমানগুলো ছিল কোরআনিক মূল্যমানের সহায়ক ও দীর্ঘস্থায়িত্ব দানে সম্পূরক।
এ কথা অবশ্য ঐতিহাসিক সত্য যে, ইসলাম গ্রীক চিন্তাধারার সংস্পর্শে এসেছিল তার ফলে মুসলিমেরা ইসলামকে যুক্তিবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করেছিলেন। তবে এ সংযোগের পূর্বে মুসলিম জগতে কতকগুলো রাষ্ট্র নৈতিক মূল্যমানের অভ্যুদয় হয়েছিল। আধুনিক জগতে প্রজাতন্ত্রকে সর্ব সাধারণ মানুষের জন্মগত অধিকার বলে স্বীকার করা হয়। একে গ্রীক চিন্তাধারার অবদান বলেই গ্রহণ করা হয়। এক্ষেত্রে বিশেষ লক্ষণীয় বিষয় এই- গ্রীকদের সভ্যতায় যে গণতন্ত্র দেখা দিয়েছিল তার দৃষ্টিভঙ্গি ছিল অত্যন্ত অপরিসর। ফরাসী রাষ্ট্র-বিপ্লবে তা আবার পুনর্জীবন লাভ করে। তবে পরবর্তীকালে এ গণতন্ত্রে তার মূল আত্মাই বিনষ্ট হয়।
প্রকৃত গণতন্ত্রের কিছুটা সন্ধান পাওয়া যায় খোলাফায়ে রাশেদীনের যুগে বিশেষ করে দ্বিতীয় খলীফা উমর ফারুক (রা)-এর শাসনকালে। যদিও প্রচলিত প্রথায় খলীফাকে হয়ত বা নির্বাচিত অথবা মনোনীত করা হতো, বাইয়াত প্রথাতে প্রমাণিত হয় খলীফার নির্বাচন বা মনোনয়ন সর্বসাধারণ মুসলিম কর্তৃক গৃহীত হওয়া প্রয়োজনীয় ছিল। এতে প্রমাণিত হয় খিলাফতের ভিত্তিমূলে খলীফার জনপ্রিয়তা থাকা অত্যাবশ্যক। খলীফা নির্বাচন সংক্রান্ত হযরত উমরের নির্দেশে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, গণতন্ত্রই সে সুবর্ণ যুগে মুসলিমদের আদর্শ ছিল। এতে ফরমান জারি করা হয়েছে-
“যদি কেউ কারো কাছে সমগ্র মুসলিম সমাজের সম্মতি ব্যতিরেকে বাইয়াত গ্রহণ করে, তাহলে যে সরকারের দায়িত্ব গ্রহণ করে এবং যে বশ্যতা স্বীকার করে, তাদের উভয়েরই মৃত্যুদণ্ড হওয়া উচিত” ।
গণতন্ত্রের প্রতি মুসলিমদের এ শ্রদ্ধা পরবর্তীকালে আরও বিকশিত হয়। এ শ্রদ্ধারই চরম প্রকাশ পাওয়া যায় সিফফিনের যুদ্ধে হঠাৎ হযরত আলী (রা) মুয়াবিয়া (রঃ)-এর সঙ্গে সন্ধির প্রস্তাবে সম্মত হওয়াতে খারেজিদের বিদ্রোহে। যদিও গোড়াতে খারেজিরা হযরত আলীর মহাভক্ত ছিল, তবুও দুই পক্ষের নেতাদের সন্ধিতে তাদের অনুসারীদের পক্ষে সে সন্ধি স্বীকার করাতে কোন বাধ্যবাধকতা তারা স্বীকার করেনি। যদিও ধর্মীয় জীবনে তারা অত্যন্ত গোড়া ছিল এবং অন্যান্য মতাবলম্বী মুসলিমদের উপর অভিসম্পাত বর্ষণ করতো, তবুও গণতন্ত্র সম্বন্ধে তাদের ঐ অনমনীয় শ্রদ্ধা আজও আমাদের কাছে বিস্ময়ের বিষয়। গণতন্ত্র ব্যতীত আল্লাহর সার্বভৌমত্বও মুসলিম সমাজের উপর ছিল বিশেষভাবে কার্যকরী কোরআনের ধারণা অনুসারে আসমান-যমীনের একমাত্র সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ এবং এ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে একই সার্বভৌমত্ব কেবল মাত্র তাঁরই এতে ব্যক্তিগত মালিকানা লোপ পায় এবং মানুষের পক্ষে কেবল তাদের অধিকারে পাওয়া জিনিসের উপর আমানতকারী হিসেবে সুষ্ঠুভাবে রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব বর্তে।
পরবর্তীকালে মুসলিম অধ্যুষিত স্পেনে জাহেরী মতবাদের ইমাম ইবনে হাযম এ মূল্যমানের আলোকে ইসলামী রাষ্ট্র মুসলিমদের অধিকার বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেছেন-
প্রত্যেক নাগরিককে এমন খাদ্য পরিবেশন করতে হবে যাতে হবে সে বেঁচে থাকতে পারে ও তার কাজ করার সামর্থ্য থাকে, তাদের এমন পোশাক-পরিচ্ছদ সরবরাহ করতে হবে, যাতে বিভিন্ন ঋতুর প্রকোপ থেকে তারা আত্মরক্ষা করতে পারে। তাদের এমন সব বাসগৃহ দিতে হবে, যাতে তার সকল ঋতুতে সুখে বাস করতে পারে।
এ নীতির অনুসিদ্ধান্ত অনুসারে বলা যায়-এতে রাষ্ট্রের পক্ষে এবং বহুবিধ বিষয়াদি সরবরাহ করা কর্তব্য হয়ে পড়ে। তবে এতে বিলাসিতার মূলে কুঠারাঘাত করা হয়। এ নীতির মুখ্য উদ্দেশ্য রাষ্ট্রের বাসিন্দা সকল নাগরিকের জন্য একই মানের জীবনযাত্রা নির্বাহ করার ব্যবস্থা করা। একে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের নীতির অগ্রসূরী স্বচ্ছন্দেই বলা যায়।
মানুষের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠায় আধুনিক যুগের শোষণমূলক উগ্র স্বদেশিকতার স্থলে ভ্রাতৃত্বমূলক মনোভাব সৃষ্টির জন্য ইসলাম গোড়াতেই চেষ্টা করেছে। তত্ত্বজ্ঞানী ইবনে খালদুন সমাজের উৎপত্তি বিকাশ, ধ্বংসাবস্থা ও মৃত্যু সম্বন্ধে স্বাধীনভাবে চিন্তা করেছেন। তার মতবাদ অনুসারে বিলাসিতাই সমাজ জীবনের ধ্বংসের মুখ্য কারণ। ‘কাজেই সমাজ-জীবনকে সুস্থ ও সবল রাখতে হলে সর্বতোভাবে বিলাসিতাকেই বর্জন করতে হবে’ ; তার এ মতবাদে ত্রুটি থাকতে পারে, তবে সমাজ-জীবনের বিকাশের সূত্র বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে পথপ্রদর্শক বলা যায়।
তিন.
সর্বপ্রথম গ্রীক চিন্তাধারার সংস্পর্শে আসার পরে মুসলিমরা তাদের প্রত্যাদেশকে যুক্তিসম্মত করার সাধনায় আত্মনিয়োগ করে। তবে এ সংযোগের পূর্বেও ইচ্ছার স্বাধীনতা সংক্রান্ত বাকবিতণ্ডায় প্রত্যেক পক্ষই তার মন্তব্য প্রতিষ্ঠায় যুক্তির সাহায্য গ্রহণ করে জাবরিয়া বা নিশ্চয়তাবাদীরা আল্লাহর সর্বশক্তির উপর নির্ভর করে মানব-ইচ্ছার স্বাধীনতা সম্পূর্ণ অস্বীকার করে। অপরদিকে নৈতিক জীবনকে অক্ষুন্ন রাখার জন্য কাদরিয়াগণ মানব-ইচ্ছার স্বাধীনতা মুক্ত কণ্ঠে ঘোষণা করে। গ্রীকদের চিন্তাধারা দ্বারা সর্বপ্রথমে অনুপ্রাণিত হয়ে মুতাযিলারা। নৈতিক মূল্যমানের রক্ষাকল্পে তারা ইচ্ছা স্বাধীনতার পক্ষে রায় দান করে। এক্ষেত্রে তাদের আচরণ থেকে মনে হয় ইসলামে বিশ্বাসী হলেও তাদের মতবাদে প্লেটোর প্রভাব ছিল অত্যন্ত গভীর। ইখওয়ান-উস-সাফার দার্শনিক গুরুত্ব ছিল সমধিক। প্রয়োগাবলী (Empiricists) ও যুক্তিবাদীদের (Rationalists) দ্বন্দ্বের বহু পূর্বে তারা জ্ঞানের ক্ষেত্রে ইন্দ্রিয় ও যুক্তির দানকে স্বীকার করেছিলেন। পূর্বোক্ত ইমাম ইবনে হাযম জ্ঞানবিদ্যা (Epistemology) সংক্রান্ত মতবাদে তাদের অনুসরণ করেছিলেন। এজন্যই তিনি ইন্দ্রিয়জ জ্ঞান (শাহদাতুল হাওয়াজ) ও প্রাথমিক যুক্তির (আউয়াল আল আাকল) অর্থাৎ অভিজ্ঞতা-নিরপেক্ষ জ্ঞানের (A Priori Reason) উপর সমান গুরুত্ব প্রদান করেছিলেন। তিনি এগুলোর সঙ্গে প্রমাণকে (বুরহান) যোগ করেছেন । প্রমাণের সঙ্গে একদিকে ইন্দ্রিয় নিচয়ের অপর দিকে প্রাথমিক জ্ঞানের যোগ রয়েছে।
দার্শনিকেরা প্রধানত এরিস্টটলের দর্শনের ভাষ্য রচনা করাতেই লিপ্ত ছিলেন। তাদের সম্বন্ধে আলোচনাকালে আমাদের ভুললে চলবে না, যদিও নিও-প্লেটোনিজম বা নব্য-প্লেটোবাদের মতানুসারে তারা বিচ্ছুরণবাদ (Theory of Emanation)-কে স্বীকার করে নিয়েছিলেন, তবুও তার মধ্যে তারা মস্ত বড় ফাটলও আবিষ্কার করেছিলেন। পরম ব্রহ্ম থেকে অকস্মাৎ এ পৃথিবীর উৎপত্তি তাদের কাছে ছিল আকস্মিকতারই এক নিদর্শন। আল্লাহ ও পৃথিবীর মধ্যবর্তী কোন কিছুর অস্তিত্বের স্বীকৃতি তাদের কাছে ছিল অপরিহার্য। এজন্য নব্য প্লেটোবাদের এ মতকে তাঁরা সংশোধন করে আল্লাহ ও পৃথিবীর মধ্যবর্তী নানা বিষয়ের স্থিতি স্বীকার করেছেন তাদের মতানুসারে সৃষ্টিকর্তার মধ্য থেকে প্রথম বিচ্ছুরিত হয় প্রাথমিক বুদ্ধি। তা থেকে দ্বিতীয় বুদ্ধি।
এ দ্বিতীয় বুদ্ধি থেকেই জড় পদার্থের উৎপত্তি। তাদের এ সমাধানের মধ্যেই তাদের প্রকৃত গুণের পরিমাপ হয় না বরং ভগবান ও এ পৃথিবীর মধ্যে একটা প্রকাণ্ড উপসাগরের মত যে ব্যবধান মুখব্যাদন করে রয়েছে সে সম্বন্ধে অন্তর্দৃষ্টি ছিল বলেই তাদের প্রতিকার প্রশংসা করতে হয়।
তবে দার্শনিকদের মধ্যে সকলেই এরিস্টটলের দর্শনের ভাষ্য রচনাতেই কিন্তু ছিলেন না। তাদের মধ্যে নিজস্ব ধ্যান-ধারণাও ছিল। ইবনে মিসকাওয়া বহু পূর্বেই ক্রমবিকাশবাদের চারটি স্তরের সন্ধান পেয়েছিলেন। ‘খনিজ পদার্থ, বনস্পতি, প্রাণী ও মানুষ’ -এ চারটে পর্যায়ে তিনি বিবর্তনকে ভাগ করেছেন। তিনি পর্যায়ক্রমে মারজান (coral), খেজুর ও বানর এ তিন স্তরে ভাগ করেছেন। খনিজ পদার্থ ও বনস্পতি ও প্রাণীর মধ্যবর্তী এবং প্রাণী ও মানব রাজ্যের মধ্যবর্তী বলে তিনি তাদের লক্ষ্য করেছেন।
বিবর্তনের ধারণা বর্তমানে আর তেমন জোরালো নয়। বিবর্তনের এখন অনেকেই ব্যাখ্যার একটা সুবিধাজনক মাধ্যম মনে করেন। তবু এ দুনিয়ার বিভিন্ন প্রজাতির উৎপত্তি সম্বন্ধে ব্যাখ্যা দান করে বিবর্তনের ধারণা একটা মস্ত কাজ সমাধা করছে। বাস্তবে বিবর্তন সত্য নাও হতে পারে। তা সত্ত্বেও অন্য কোন শক্তির সাহায্য নিয়ে এবং বিভিন্ন প্রজাতির মধ্যে একটি যোগসূত্র স্বীকার করে বিভিন্ন প্রজাতির উৎপত্তির ব্যাখ্যা করে এ ধারণা এখনও আমাদের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করতে সমর্থ। মিসকাওয়াকে তাই ডারউইন ও লেমার্কের পূর্বসূরী বলা যায়। জালালউদ্দীন রূমীকে সাধারণত কবি বলেই গ্রহণ করা হয়। তা সত্ত্বেও ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে তার ধারণা মনীষার রাজ্যে এক অভিনব অবদান। মুসলিম হিসাবে তিনি ছিলেন আল্লাহর অস্তিত্বে বিশ্বাসী। তাঁর দৃঢ় প্রত্যয় ছিল আল্লাহর অস্তিত্ব থেকেই এ দুনিয়ার সব কিছুর উৎপত্তি। তবে তিনি আল-কোরআনের সৃষ্টিতত্ত্বকে হবহু আক্ষরিক অর্থে গ্রহণ করেন নি। তিনি প্লটিনাসের মতবাদ দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন। তার ধারণা ছিল, এ দুনিয়ার সব কিছুই স্বর্গীয় আত্মার স্থিতি থেকে উৎসারিত। কিন্তু প্রত্যেকটি বিষয় বা প্রত্যেকটি আত্মা অনিবার্যভাবে তার মূল উৎসের পানে প্রত্যাগমনের জন্য ব্যাকুল। এ ব্যাকুলতাকেই রূমী নাম নিয়েছেন প্ৰেম।
এ ব্যাকুলতাই ক্রমবিকাশের মূলসূত্র। এ দুনিয়ার স্থিতির মধ্যে রয়েছে স্তর ভেদ এক পর্যায়ের আত্মাগুলো অন্য পর্যায়ের আত্মার চেয়ে হয় হীনতর না হয় উন্নততর। সবগুলো আত্মার সার আধ্যাত্মিক। কারণ একই দিব্য জীবন থেকে তাদের উৎপত্তি। রূমীর দর্শনে তাই আদমের পতনের পূর্ণ ব্যাখ্যা দান করা হয়েছে। যে মৌলিক অবস্থা থেকে আদমের পতন হয় তা ফিরদাউস বাগান বা কোন স্রোতস্বিনী নয়, সেটা হচ্ছে দিব্য জীবনের একক পরিস্থিতি। তাকে রূপকের আকারে বর্ণনা করা যায় যে, জড় পদার্থের রাজ্যে উদ্ভিদের ক্ষেত্রে অথবা প্রাণীজগতে বিদ্যমান আত্মাগুলো ভূপতিত ফেরেশতাগণ। তারা প্রাণপণ চেষ্টা করে আবার তাদের দিব্য জীবনে ফিরে যাওয়ার জন্যে প্রয়াস করছে। বাস্তবিক পক্ষে বিবর্তন ও ব্যষ্টিকরণ সম্বন্ধে এ ধারণা এক অপূর্ব অবদান। গ্রীক এসব ভারতীয় চিন্তাধারায় জৈববিবর্তনের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় তবে ‘কেন এ বিবর্তন’ তার ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না, অথবা জাগতিক বিবর্তনেরও কোন উদাহরণ পাওয়া যায় না। রূমী সর্বপ্রথমে বিবর্তনবাদের অপর দিক এবং তার ব্যাখ্যা দান করে এক অভিনব চিন্তাধারার প্রবর্তন করেছেন।
সুফীরা ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানের উপরও প্রত্যয়শীল ছিলেন না। বুদ্ধিবৃত্তির সূক্ষ্ম বিশ্লেষণেও তাদের আস্থা ছিল না। তাদের কাছে ‘কলব’ বা ‘দিল’ই ছিলো জীবনের উচ্চতর মূল্যমান গ্রহণের স্থল। প্রথমে আল্লাহর ক্রোধের ভয়ে ভীত হয়ে তারা এই দুনিয়ার সকল বিষয়-বস্তুর সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করেন এক সমাজের অন্যান্য লোকদের নিকট থেকে দূরে সরে পড়েন। প্রথম পর্যায়ে তাদের মূল লক্ষ্য ছিল আত্মনির্যাতনের মাধ্যমে মোক্ষলাভ। তবে কালে জীবন-সমস্যা কল্পে গভীর চিন্তায় মগ্ন হয়ে তারা বুঝতে পারেন যে, সব মাধ্যম বা ধারণার দ্বারা মননশীল ক্ষেত্রে অথবা বাস্তব অভিজ্ঞতায় মনের ভাব ব্যক্ত করা যায় সেগুলো যথোপযুক্ত ও পর্যাপ্ত নয়। এজন্য এক্ষেত্রে প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে রাবেয়া বসরী একটি নতুন মাধ্যম প্রবর্তন করেন। তার ধারণা ছিল কেবলমাত্র আত্মসম্পর্কের মাধ্যমেই মানুষ সেই চিরন্তন সত্য আল্লাহর সান্নিধ্য লাভ করতে পারে। চিন্তাধারার বিকাশের ফলে সুফীদের ধারণা জন্মে চারটে বিভিন্ন মাধ্যমে আল্লাহর ওহদানীয়ত সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান লাভ হয়। শাকিক বলখী ও ইব্রাহিম আদহম তাকে পরম ইচ্ছা শক্তি- রূপে; মনসুর হাল্লাজ, সবিস্তাবী, রূমী ও হাফিম তাকে পরম সৌন্দর্যরূপে; ইশরাকী তাকে আলোকরূপে গ্রহণ করেছেন। এক্ষেত্রে মুহিউদ্দিনের অবদানই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। কারণ তিনি অন্য সুফীদের পথ পরিত্যাগ করে সারসত্য সম্বন্ধে তাঁর ধারণা যুক্তির আলোকে আলোচনা করেছেন। তার মতে দিব্য জীবনের সারকে দুটো দিক থেকে দেখা যেতে পারে,
- তাকে খাঁটি সরল সার রূপে ধারণা করা যায়
- তাকে নানাবিধ গুণের আধার রূপে ধারণা করা যায়
অন্য-নিরপেক্ষভাবে ধারণা হলে আল্লাহর সঙ্গে কোন কিছুরই সম্বন্ধ নেই। সুতরাং, তার সম্বন্ধে কোন জ্ঞানলাভেরও সম্ভাবনা নেই। তিনি সেই নব্য প্লেটোনিক অচিন্তনীয় ও অনির্বচনীয় সত্ত্বা। এই দৃষ্টিতে থেকে বিচার করলে তিনি আল্লাহই নন। এ প্রসঙ্গে তিনি ইমাম গাযালীয় মতবাদের কঠোর সমালোচনা করে বলেছেনঃ গাযালীর ধারণা ছিল এ পৃথিবীর সঙ্গে সংশ্রববিবর্জিত হিসাবে আল্লাহর ধারণা করা সম্ভব। চিরন্তন সার সম্বন্ধে মানুষের জ্ঞানলাভ সম্ভবপর তবে তাকে আল্লাহ বলে অর্থাৎ আরাধনার পাত্র বলে জানা যায় না-যতক্ষণ পর্যন্ত না তার যৌক্তিক প্রতিপক্ষ মলুহকে জানা না যায়। আল্লাহ তাঁর সত্তার দিক থেকে তাঁর সৃষ্টজীবের উপর নির্ভরশীল নন। তবে তাঁর দিব্য জীবনের জন্য সৃষ্টজীবের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। তাঁর অস্তিত্ব অন্য-নিরপেক্ষ অপরপক্ষে তার সৃষ্ট সবকিছুই আপেক্ষিক ও অন্য নির্ভর । অর্থাৎ আল্লাহর সত্ত্বাই নানাবিধ সম্বন্ধে আবদ্ধ হয়ে একক বস্তু বা বিষয়ে প্রতিভাত হয়। এজন্যই সকল বিষয় আল্লাহর গুণাবলী। এক্ষেত্রে শায়খ মুমহীউদ্দীন আমাদের সামনে যান্ত্রিক ন্যায়শাস্ত্রের সূত্র প্রবর্তন করেছেন। এ দ্বান্দ্বিক ন্যায়শাস্ত্রই পরবর্তীকালে আমরা ব্রাডলি ও বোসাষফের মধ্যে পূর্ণ বিকশিত দেখতে পাই। যদিও আল্লাহর ধারণা সম্বন্ধে সুফীদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে এবং মনসুর নিজকেই ‘সত্য’ বলে ধারণা করেছেন, তা সত্ত্বেও তাদের মধ্যে এক জায়গায় ঐক্য রয়েছে। তারা সকলেই প্রার্থনার কার্যকারিতা সম্বন্ধে একই ধারণা পোষণ করেছেন। তবে তাদের প্রার্থনা সাধারণ প্রার্থনা থেকে সম্পূর্ণ পৃথক ধরনের। তারা সকলেই আল্লাহকে এক অসীম শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিসত্তারূপে ধারণা করেছেন। এজন্যই সত্যিকার প্রার্থনা সর্বাবস্থায়ই কার্যকরী বলে তারা স্বীকার করেছেন। খুব সম্ভবত সত্যের জন্য তাদের আন্তরিক অন্বেষণের ফলে তারা সত্যের কোনও একটি দিকের সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন এবং সেদিককেই আল্লাহর সর্বপ্রধান গুণ বলে উপস্থাপিত করেছেন। তবে তাদের কেউই অন্বেষণজাত অভিজ্ঞতার সমন্বয় করেন নি।
গাযালী এদের প্রত্যেকের অবদানের যথাযথ মূল্য নির্ণয় করেছিলেন। তিনি তাদের অবদানের সার সংগ্রহ করে তারই ভিত্তিতে এক অভিনব জীবন দর্শন গড়ে তুলেছিলেন। তিনি মুসলিম দার্শনিকদের স্থান-কাল সম্বন্ধীয় মতবাদের মধ্যে ত্রুটি আবিষ্কার করে তাদের মতবাদ থেকে পৃথক মতবাদ গঠন করেন। তিনি স্পষ্টতই বুঝতে পারেন, দার্শনিকেরা যে ভাবে মনে করেন, এ পৃথিবী স্থানের দিক থেকে সসীম অথচ কালের দিক থেকে অসীম তা কিছুতেই সম্ভবপর নয়। তার স্পষ্ট ধারণা ছিল স্থান-কাল বলে কোন স্বতন্ত্র সত্তা কিছুই নেই। তিনি অঙ্গুলি নির্দেশ করে প্রমাণ করেন, স্থান-কাল হচ্ছে বস্তুর সম্বন্ধ মাত্র। তাদের উৎপত্তি স্থল বস্তুরাজি। বর্তমান কালে ওয়াইট হেডের মতবাদে তার মতের পোষকতা পাওয়া যায়। ওয়াইট হেডের মতবাদ অনুসারে স্থান হচ্ছে ঘটনাবলীর সুশৃঙ্খলার-ই অপর এক নাম। তার নিজস্ব কোন সত্তা নেই। তিনি স্থান-কালকে অভিজ্ঞতার আকার বলেই ধারণা করেছেন এবং এ ক্ষেত্রে তিনি কান্টের পূর্বসুরী। দার্শনিকদের মতের বিরুদ্ধে তার ধারণা ছিল কার্যকরণ পরম্পরা নীতিকে সময়ের এক ধারা বলে ব্যাখ্যা করা যায় না। তাঁর মতে-তাকে প্রত্যেকের ব্যক্তিসত্তার মাধ্যমে উপলব্ধি করতে হয়। দার্শনিকদের মতানুসারে বাসনা বা ইচ্ছাশক্তির মূলে রয়েছে অভাব। কাজেই আল্লাহর কোন অভাব নেই। সুতরাং গতিকে তার সারসত্ত্বা চিন্তা বলেই ধারণা করতে হবে। গাযালী ইচ্ছাশক্তিকে আবার স্ব-মহিমায় প্রতিষ্ঠিত করেন এবং একে মানব-জীবনের প্রাথমিক বৃত্তি হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য চেষ্টা করেন। তার এ প্রচেষ্টায় তিনি ছিলেন ভুন্ডের পূর্বসুরী। গাযালীর বক্তব্যের প্রকৃত মূল্য রয়েছে পঞ্চেন্দ্রিয়ালব্ধ জ্ঞান ও যুক্তির আপেক্ষিকতা প্রদর্শনের মধ্যে। প্রথম দিকে তাঁর এ প্রচেষ্টার উদ্দেশ্য ছিল, নাস্তিকদের মতের প্রতিবাদ স্বরূপ তার নিজস্ব মতবাদের প্রতিষ্ঠা। তাদের বক্তব্য ছিল, “যুক্তির মাধ্যমেই সত্যের অন্তঃস্থলে প্রবেশ করা যায়”। তবে উদ্দেশ্য যাই হোক, এতে দর্শন পাঠের পক্ষে একটা বিশেষ পটভূমির প্রস্তুতির পক্ষে সুবিধা হয়েছে। ইতিপুর্বে দার্শনিকগণ তত্ত্বজ্ঞান সম্বন্ধীয় নানাবিধ আলোচনায় প্রবৃত্ত হতেন। গাযালীর এ অন্বেষণকে তাই জ্ঞানতত্ত্ব সংক্রান্ত বিশ্লেষণ বলা যেতে পারে । এ বিশ্লেষণেই পরবর্তীকালে হিউম প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। এ ক্ষেত্রে গাযালীর উদ্দেশ্য ইন্দ্রিয়জাত অথবা যুক্তিলব্ধ জ্ঞানের উপর নির্ভর করা একদেশদর্শিতা বই আর কিছুই নয় এ সত্যটি প্রমাণ করা। চিন্তা-জগতের এ ত্রুটির প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করাই ছিল গাযালীর মুখ্য উদ্দেশ্য। তিনি সুফীদের সঙ্গে এ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ একমত ছিলেন যে, ইন্দ্রিয়জাত জ্ঞান ও যুক্তিলব্ধ জ্ঞান ব্যতীত জ্ঞানের অপর একটি তৃতীয় উৎস রয়েছে এবং সে উৎসের জ্ঞানই সবচেয়ে নিশ্চিত জ্ঞান।
গাযালীর বহুবিধ রচনা থেকে এ কথাটিই বিশেষভাবে প্রমাণিত হয় মুসলিমদের চিন্তাধারায় যে উৎসারণবাদ (Theory of Emanation) অনুপ্রবেশ করেছে তা প্রকৃতপক্ষে একটি নেতিবাচক ধারণা। এতে আল্লাহর ইচ্ছা ও কর্মশক্তিকে অস্বীকার করা হয়। গ্রীক চিন্তাধারায় উত্তরাধিকার-সূত্রে প্রাপ্ত এ উৎসারণকে ত্যাগ করে আল্লাহকে চিরন্তনভাবে নতুন মূল্যমান সৃষ্টিতে ব্যস্ত বলে ধারণা করা ন্যায়সঙ্গত। অতি আধুনিককালে পরলোকগত অধ্যাপক আলবার্ট আইনস্টাইনও বস্তুর স্থানুত্ব থেকে ঘটনা বা কর্মের প্রতি আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন। তাঁর মতে এ জগতে স্থানু পদার্থ বলে কিছু নেই। এতে রয়েছে অনেকগুলো ঘটনার সমাবেশ। এদিক আবার ঘটনাগুলোর চিন্তা থেকে ইচ্ছা শক্তির সঙ্গে সাযুজ্য রয়েছে। হুবহু না হলেও আইনস্টাইনের চিন্তাতে গাযালীর মতবাদের সমর্থন পাওয়া যায়। যদিও গাযালী সৃষ্টিতত্ত্ব পরিত্যাগ করার জন্য দার্শনিকদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছেন, তা সত্ত্বেও তিনি সব বস্তুকে একই সারিতে বসিয়ে দেন নি। তাঁর মতবাদ অনুসারে সৃষ্টিতে বিভিন্ন পর্যায় রয়েছে। প্রত্যেকটি পর্যায়কেই তার স্বকীয় বৈশিষ্ট্যের আলোকে বুঝতে হবে এবং বিশ্বসত্তায় তার স্থান নির্দেশ করতে হবে। গাযালীর মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল-মানবের ব্যক্তিসত্তার সবগুলো দিকের পুনর্মিলন এবং প্রত্যেকটি দিকের স্থান ও মূল্য নির্দেশ। গ্রীক চিন্তাধারার সমালোচক হিসাবে তাঁর আবির্ভাব হলেও তাঁর আসল উদ্দেশ্য ছিল আদর্শ মানব বা ইনসান-ই-কামিল সৃষ্টি করা।
উপসংহারে চুম্বকভাবে বলা যায়, ইসলামী চিন্তাধারার সর্বপ্রধান মূল্য হচ্ছে সৃষ্টিকর্তা, বিবর্তনকারী ও প্রতিপালক ও সার্বভৌম সত্তা হিসাবে আল্লাহর ধারণা। এগুলো থেকেই ন্যায়নীতি, সকল মানুষের সমান মর্যাদা, দয়া প্রভৃতি মূল্যমানের উৎপত্তি হয় এবং পৃথিবীর সম্পদের উপর সকল মানুষের সমান অধিকার বর্তে।
অন্য যেসব মূল্যমান মুসলিম চিন্তাধারা থেকে উদ্ভূত তাদের যথাক্রমে জ্ঞান আহরণের জন্য বিভিন্ন উৎসের স্বীকৃতি, আরোহ পদ্ধতির স্বীকৃতি ও ব্যবহার বলা যেতে পারে। এগুলো থেকে সামাজিক ও জৈবিক বিবর্তন সম্ভবপর। মানব-জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ হিসেবে ইনসান-ই-কামিলকে গ্রহণ করা হয়েছে। তার জীবনে ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশ হয়। তারই ব্যক্তিত্বে দিব্য জীবনের গুণাবলী সম্যকভাবে বিকাশ লাভ করে।
কাজেই একথা ন্যায়সঙ্গতভাবে বলা যেতে পারে যে, আল্লাহর ধারণা থেকেই ইসলামী চিন্তাধারার সবগুলো মূল্যমানের উৎপত্তি হয়েছে। তাদের দুভাবেই উৎপত্তি সম্ভবপর। আল্লাহর ধারণা থেকে তাদের উদ্ভব সম্ভবপর। না হয় স্বাধীনভাবে চিন্তা করার ফলেই তারা মানবমানসে প্রতিভাত হয়েছে আধুনিক দর্শনের পরিভাষায় বলতে গেলে ইসলামী চিন্তাধারায় আল্লাহর ধারণা সবগুলো মূল্যমানের উৎস, ভিত্তি ও মূল।
তথ্য সংকেতঃ
১, Shaik Mushir Hussain Kidwai-Pan-Islamism and Balshevism
২, Ibn Hazam, Mahalla, Vol 6
৩, History of Muslim Philosophy Vol 1
৪, History of Musim Philosophy Vol 2
৫, Bertrand Russell- The New Hopes for a Changing World
৬, Charles Laswai- An Arab Philosophy of History
সূত্রঃ “ইসলাম ও মানবাতাবাদ” গ্রন্থ থেকে সংকলিত।