বাংলাদেশের বেকার সমস্যা ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক সময়কাল থেকেই প্রকট একটি সমস্যা। এ সমস্যা হুট করেই সৃষ্টি হয়নি, বাংলা অঞ্চলে ইসলামী সভ্যতার পতন পরবর্তী ঔপনিবেশিক শোষণের ফলেই মূলত এটি সৃষ্টি হয়। আজ স্বাধীন বাংলাদেশের পঞ্চাশ বছর বয়সে এসেও দেশের অঘোষিত প্রধান সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করতে হচ্ছে যুব সম্প্রদায় ও কর্মক্ষম মানুষের এ বেকারত্বকে। বর্তমানে এটি এমন এক বিস্ফোরণ উন্মুখ আগ্নেয়গিরি হয়ে দাঁড়িয়েছে যে, সমাধান না করতে পারলে তার অগ্নুৎপাত হয়তো আমাদেরকে ধ্বংস করে দেবে। অথচ স্বাধীনতা উত্তর এ যাবৎকালের সরকারি পরিসংখ্যানগুলো এবং বেকারত্ব নিরসনের পদক্ষেপগুলো দেখলে মনে হবে, আগ্নেয়গিরি কিংবা জ্বালামুখের অস্তিত্বও নেই, অগ্নুৎপাত তো সেখানে অযাচিত আলাপ!
বাংলাদেশে বেকারের সংখ্যা প্রকৃতপক্ষে কত তা নিয়ে সব সময়ই একটি ধোঁয়াশা সৃষ্টি হয়। এটি কাকতালীয় কোনো ঘটনা নয়, মূলত পরিকল্পিতভাবেই বেকারের প্রকৃত সংখ্যা গোপন করা হয়। সরকারি পরিসংখ্যানগুলো কখনোই, কোনোদিনই বেকারের প্রকৃত সংখ্যা প্রকাশ করেনি; বরং পরিসংখ্যানগুলোর তথ্য অনুযায়ী মনে হয়, বাংলাদেশ আরো শত বছর আগেই উন্নত দেশের কাতারে পৌঁছে গেছে!
বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) সর্বশেষ শ্রমশক্তি জরিপ, ২০১৬-১৭ অনুসারে দেশে বেকারের সংখ্যা মাত্র ২৬ লাখ ৮০ হাজার বা প্রায় ২৭ লাখ! এক্ষেত্রে শ্রমশক্তির বাইরে আছে, কিন্তু কর্মক্ষম এমন মানুষদের বেকারের আওতায়ই নিয়ে আসা হয়নি।
২০১৯ সালে বাংলাদেশের বেকারত্বের হার ছিলো ৪ দশমিক ২২ শতাংশ। ২০২০ সালের করোনাকালীন ভগ্ন পরিস্থিতিতে কাগজে-কলমে বেকারত্বের হার ছাপানো হয় ৫ দশমিক ৩ শতাংশ। এ সময়ে করোনা পরিস্থিতির কারণে সারা বিশ্বেই মন্দার সৃষ্টি হয় এবং উন্নত দেশগুলোতেও বেকারত্ব ব্যাপক হারে বেড়ে যায়। এ হার কানাডায় ছিলো প্রায় ১০ শতাংশ, যুক্তরাষ্ট্রে ৮ শতাংশ, অস্ট্রেলিয়ায় প্রায় ৭ শতাংশ। এছাড়া দক্ষিণ আফ্রিকায় ছিলো ৩০ শতাংশ, জর্জিয়ায় ১৮ দশমিক ৫ শতাংশ, গ্রিসে ১৬ দশমিক ৩ শতাংশ, স্পেনে ১৫ দশমিক ৫ শতাংশ, কলম্বিয়ায় ১৫ শতাংশ, ব্রাজিলে ১৪ শতাংশ। অথচ বাংলাদেশে মাত্র ৫ দশমিক ৩ শতাংশ! অর্থাৎ বাংলাদেশ মন্দা রোখার সক্ষমতায় এবং বেকারত্বের হার কম রাখার ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, অস্ট্রেলিয়াকেও ছাড়িয়ে গেছে! ২০২১ সালের হিসাব অনুযায়ী বেকারত্বের হার আরো কমে ৫ দশমিক ২৩ শতাংশে এসে দাঁড়িয়েছে। এ হার বেকারত্বের স্বাভাবিক বা প্রাকৃতিক হারের আশেপাশেই। অধিকাংশ মত অনুযায়ী বেকারত্বের স্বাভাবিক হার ৪-৫ শতাংশ। তার মানে বাংলাদেশে বেকারত্ব এখনো স্বাভাবিকতার পর্যায় উতরে যায়নি! কিন্তু সত্যিকার অবস্থা কী? চর্মচক্ষুর বিচারও তার বিপরীতটাই বলছে, চুলচেরা বিচার-বিশ্লেষণ তো আরো পরের ব্যাপার! মিল্টন ফ্রিডম্যান ও এডমন্ড ফেল্পস বাংলাদেশের এ অবস্থা দেখলে হয়তো বিস্মিত হতেও ভুলে যেতেন!
এ হলো সরকারি পরিসংখ্যানের তথ্য। এ তথ্যকে নিদেনপক্ষে সঠিক বা পক্ষপাতহীনতার মানদণ্ডে দশে আট দেওয়া যেতো, যদি দেশের বেসরকারি সংস্থাগুলো এবং আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর তথ্যের সাথে তার খুব একটা পার্থক্য না থাকতো; কারণ বেকারের সংখ্যা কাঁটায় কাঁটায় হিসাব করা স্বাভাবিকভাবেই সম্ভবপর নয়। কিন্তু এক্ষেত্রেও আকাশ-পাতাল তফাৎ! অবস্থা এমন, কোন তথ্য যে সঠিক, সেটিই বোঝা মুশকিল হয়ে দাঁড়িয়েছে।
আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার (আইএলও) প্রতিবেদন অনুযায়ী ২০২১ সালে বাংলাদেশে ১৫-২৪ বছর বয়সী কর্মক্ষম বেকারের সংখ্যা ৭ কোটি ৫০ লাখ এবং কয়েক বছরে তা দ্বিগুণ হবে, যা হবে মোট জনসংখ্যার প্রায় অর্ধ শতাংশ। এ সংস্থার আঞ্চলিক কর্মসংস্থান নিয়ে এক প্রতিবেদনে উঠে এসেছে, এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের উচ্চ শিক্ষিতদের মধ্যে বেকারত্বের হারের দিক থেকে বাংলাদেশের অবস্থান ২৮ টি দেশের মধ্যে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ, ১০ দশমিক ৭ শতাংশ। সবচেয়ে বেশি পাকিস্তানে, ১৬ দশমিক ৮ শতাংশ। পর্যবেক্ষকরা এ সংস্থার প্রতিবেদনে প্রকাশিত সংখ্যাকেই বাংলাদেশের প্রকৃত বেকারের সংখ্যা বলে মনে করেন। দৈনিক প্রথম আলোর একটি নিবন্ধ অনুযায়ী দেশে প্রকৃত বেকারত্বের হার ২৫ শতাংশের উপরে। এছাড়াও পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ এর জরিপ অনুযায়ী দেশে প্রচ্ছন্ন বেকারের সংখ্যা ১ কোটি ৩৮ লাখ, যাদের ৪৫ দশমিক ৩ শতাংশ সেবা খাতে, ৩০ দশমিক ৬ শতাংশ কৃষি খাতে ও ২৪ দশমিক ১ শতাংশ শিল্প খাতে নিয়োজিত আছেন। এক্ষেত্রে উল্লেখ্য, কোনো ব্যক্তির প্রান্তিক উৎপাদনক্ষমতা শূন্য অথবা ঋণাত্মক হলে তাকে প্রচ্ছন্ন বেকার বলা হয়। আপাতদৃষ্টিতে সে কর্মরত থাকলেও বা উৎপাদন ক্ষেত্র থেকে তাকে সরিয়ে নেওয়া হলেও মোট উৎপাদনের পরিবর্তন ঘটে না।
মূলত বাংলাদেশে বেকারের সত্যিকার সংখ্যা আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার নিরূপিত সংখ্যা থেকে আরো অনেক বেশি এবং বেকারত্বের পরিস্থিতি খুবই ভয়াবহ।
বেকারত্ব নিয়ে এ প্রহসনের মূল কারণগুলোর প্রধান একটি হলো বেকারত্ব মাপার অযৌক্তিক পদ্ধতি। এটির কারণেই মূলত বেকারের সংখ্যা হাস্যরসের বিষয়বস্তুতে পরিণত হয়েছে।
বাংলাদেশের শ্রমশক্তি সম্পর্কিত জরিপ ২০০২ অনুযায়ী ১৫ বছরের অধিক বয়সী কর্মক্ষম, কিন্তু কর্মের অভাবে ভোগা ব্যক্তিকে বেকার বলা হয়। আর দেশের মোট বেকারের সংখ্যা নির্ধারণ করা হয় আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার (আইএলও) সংজ্ঞার একটি অংশ অনুসারে। এ অনুসারে কোনো ব্যক্তি কর্মপ্রত্যাশী হওয়া সত্ত্বেও সপ্তাহে এক ঘণ্টা কাজের সুযোগ না পেলে তাকে বেকার হিসেবে ধরা হচ্ছে। এক্ষেত্রে মজুরি পরিশোধ হচ্ছে কি হচ্ছে না তা ধর্তব্যের বিষয় নয়। এটি কি বাংলাদেশের আর্থসামাজিক অবস্থার সাথে আদৌ সামঞ্জস্যপূর্ণ? মূলত এ কারণেই পরিসংখ্যান অনুযায়ী বেকারের সংখ্যা এত কম। আবার বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর তথ্য অনুসারে প্রকৃত কর্মহীন মানুষের সংখ্যা ৪ কোটি ৮২ লাখ ৮০ হাজার, এর মধ্যে কর্মক্ষম, কিন্তু শ্রমশক্তির বাইরে আছে এমন মানুষের সংখ্যা ৪ কোটি ৫৬ লাখ। শ্রমশক্তির বাইরে থাকা মানুষদের বেকারই বলা হচ্ছে না, বেকার বলা হচ্ছে শুধুমাত্র শ্রমশক্তির সাথে যুক্ত হতে চাওয়া, কিন্তু কর্মহীন ২৬ লাখ ৮০ হাজার মানুষকে!
আবার কেউ সেই এক ঘন্টা কাজ থেকে প্রাপ্ত মুজুরি দিয়ে জীবনধারণ করতে পারছে কিনা তাও এক্ষেত্রে ধর্তব্য নয়। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর তথ্য অনুসারে বাংলাদেশে একজন কৃষিশ্রমিকের দৈনিক মজুরি গড়ে ৩৬৬ টাকা, অর্থাৎ তিনি ঘণ্টায় ৪৮ টাকা মজুরি পান। তাই কোনো কৃষিশ্রমিক যদি সপ্তাহে শুধুমাত্র এক দিনে এক ঘণ্টা কাজ করার সুযোগ পান, তাহলে তার সপ্তাহিক আয় হবে মাত্র ৪৮ টাকা। আর এ পরিমাণ টাকা আয় করার মানে তিনি বেকার নন! কী নির্মম পরিহাস!
যুক্তরাষ্ট্রের শ্রম পরিসংখ্যান ব্যুরো বিএলএস এর নিয়ম অনুযায়ী কোনো কর্মক্ষম ব্যক্তি কমপক্ষে চার সপ্তাহ ধরে কর্মের সন্ধানে থাকলে তাকে বেকার বলা হয়। সেখানে প্রতি মাসে পর্যাপ্ত জরিপের মাধ্যমে বেকারের সংখ্যা প্রকাশ করা হয়, যাতে সরকার ও কেন্দ্রীয় ব্যাংক সে অনুযায়ী পদক্ষেপ নিতে পারে। এছাড়া প্রতি মাসে সৃষ্ট কর্মসংস্থানের তথ্যও প্রকাশিত হয়।
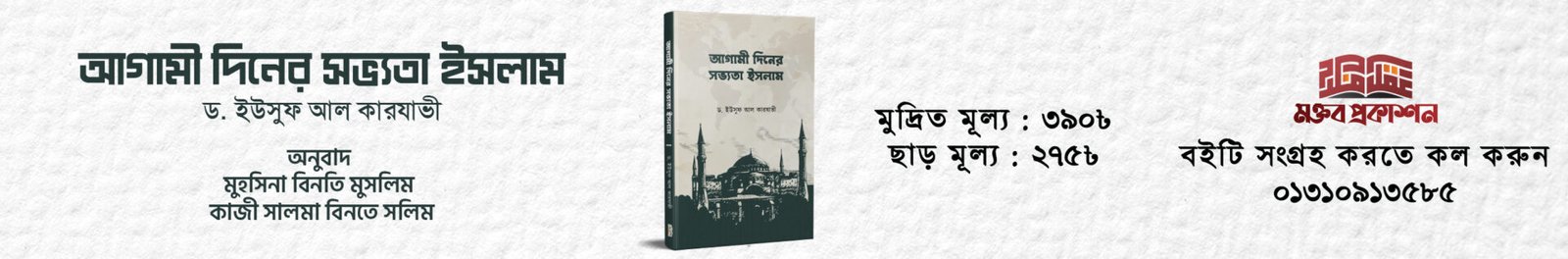
এই যে দেশের সামগ্রিক অবস্থা বিবেচনায় নিয়ে সমস্যা নিরূপণের মানদণ্ড নির্ধারণ, তা বাংলাদেশের ক্ষেত্রে পরিলক্ষিত হয় না! বাংলাদেশের সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ভৌগোলিক অবস্থান অন্যান্য দেশের তুলনায় অনেকাংশেই ভিন্ন, সেই সাথে বাংলাদেশের সম্ভাবনার জায়গা অনেক বেশি। তাই দেশের সামগ্রিক অবস্থা বিবেচনায় নিয়ে যদি বেকারের সংখ্যা নিরূপণ করা না হয়, তবে কখনোই বেকারের প্রকৃত সংখ্যা জানা সম্ভব হবে না। আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার সংজ্ঞা অনুযায়ী বেকারের সংখ্যা কম হওয়ায় বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো আরেকটি নতুন মানদণ্ড ঠিক করেছে, তা হলো যারা সপ্তাহে ৪০ ঘণ্টা কাজের সুযোগ পান না, তারা সম্ভাবনাময়, কিন্তু তাদেরকে কাজে লাগানো যাচ্ছে না। তারা প্রচ্ছন্ন বা ছদ্ম বেকার। দেশে এখন এমন মানুষের সংখ্যা ১ কোটি ৩৮ লাখ। তারা পছন্দমতো কাজ না পেয়ে টিউশনি, ফাস্টফুডের দোকানের বিক্রয়কর্মী, রাইড শেয়ারিং, কল সেন্টারের কর্মীসহ বিভিন্ন ধরনের খণ্ডকালীন কাজে নিয়োজিত আছেন। আর তাদের এসব কাজ থেকে অর্জিত আয়ও তাদের জীবনমান বৃদ্ধির জন্য যথেষ্ট নয়। সার্বিক বিবেচনায় বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো বেকারের প্রকৃত সংখ্যা নিরূপণে সচেষ্ট নয়। অথচ প্রকৃত সংখ্যা নিরূপণ করা না হলে আমরা কখনোই সঠিক সমাধানে পৌঁছাতে পারবো না, কারণ সমস্যা সমাধানের পূর্বশর্তই হলো সমস্যাকে সঠিকভাবে চিহ্নিত করা।
অর্থনীতিবিদদের মতে এ যাবতকালের সরকারের এহেন প্রকাশ্য লুকোচুরির কারণ হলো রাজনৈতিক প্রাসঙ্গিকতা হারানোর ভয়। এ ভয়েই সরকার, পরিসংখ্যান ব্যুরো এবং অন্যান্য জরিপ সংস্থা বরাবরই বেকারের প্রকৃত সংখ্যা অস্বীকার করেছে এবং জনগনকে অসত্য তথ্য দিয়ে বিভ্রান্ত করেছে। স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছর পার হওয়ার পরও এ সমস্যা মোকাবেলার জন্য সঠিক প্রস্তাবনা এবং কর্মোদ্যোগ আমরা দেখতে পাচ্ছি না।
বেকার যুবকদের চিত্র যদি পর্যবেক্ষণ করি, তাহলে ভয়াবহ সংকটে নিমজ্জিত এক বাংলাদেশের চিত্র আমাদের সামনে ফুটে উঠবে। বেকারত্ব নিরসনে প্রচেষ্টারত যুবকদের অবস্থা বর্ণনাতীত। শিক্ষিত বেকাররা যেন শোষণের অন্যতম ক্ষেত্র। আবার যারা বেকার নন, তাদের অধিকাংশও মানসম্মত জীবন যাপনে সক্ষম নন।
বাংলাদেশের সত্যিকার অবস্থা বোঝা যায় শহরের অলিগলি, মফস্বল ও গ্রাম-গঞ্জের পথঘাট, দোকানপাট দেখলে। এসব জায়গায় যুবকরা দলে দলে বসে থাকে, আড্ডা দেয়, অলস সময় পার করে। একাকীত্ব কাটাতে বা সময় পার করতে তারা মোবাইল, ভিডিও গেইম নিয়ে ব্যস্ত থাকে। হতাশাগ্রস্থ এ যুবকদের অনেকেই মাদক, নানাবিধ সন্ত্রাস, নারী নির্যাতন, সামাজিক অস্থিতিশীলতা, নৈতিক বিকৃতি, ধর্ষণ, খুন, আত্মহত্যা, চাঁদাবাজি, পর্ণোগ্রাফি, চুরি-ডাকাতি, ইভটিজিং থেকে শুরু করে নানাবিধ অপরাধে জড়িয়ে পড়ে। আর এসব অপরাধের হার ফি বছর বৃদ্ধি পাচ্ছে। প্রতি বছরই পূর্বের বছরের রেকর্ড ভাঙছে, নতুন নতুন রেকর্ড সৃষ্টি হচ্ছে।
বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর জরিপ অনুযায়ী বাংলাদেশের কর্মরত অথবা বেকার কর্মক্ষম জনশক্তি (১৫ থেকে ৬৪ বছর) ৫৮ দশমিক ২৩ শতাংশ। হিসাবের বাইরে থেকে যাচ্ছে শ্রমবাজারের বাইরে থাকা বাকি ৪১ দশমিক ৭৭ শতাংশ! এর অধিকাংশই নারী। উন্নত দেশগুলোতে কর্মরত অথবা বেকার কর্মক্ষম জনশক্তি গড়ে ৭২ দশমিক ৮ শতাংশ এবং শ্রমবাজারের বাইরে আছে গড়ে ২৭ দশমিক ২ শতাংশ। বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির এক গবেষণা অনুযায়ী দেশে বছরে ২২ লাখ মানুষ শ্রমবাজারে প্রবেশ করছে, এদের মধ্যে কাজ পাচ্ছে মাত্র ৭ লাখ। এদের অনেকেই ডিগ্রীধারী, ছাত্রসমাজের গুরুত্বপূর্ণ অংশ। ইউরোপীয় ইন্টেলিজেন্স ইউনিটের (ইআইইউ) ২০১৬ সালের এক পরিসংখ্যান অনুযায়ী বাংলাদেশে ৪৭ শতাংশ স্নাতক হয় বেকার, না হয় তিনি যে কর্মে নিযুক্ত, তার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক ডিগ্রিধারী হওয়ার কোনো প্রয়োজন ছিলো না! এক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক একটি প্রশ্ন হলো মোট শিক্ষার্থীর কত শতাংশ স্নাতক পাশ করে? এদের বড় একটি অংশই তো স্কুল-কলেজ পর্যায়ে ঝরে পড়ে। ঝরে পড়ার ক্ষেত্রে নারীদের হার প্রায় ৫০ শতাংশ, যার মধ্যে ১৩-২০ শতাংশ বাল্য বিবাহের কারণে স্কুল-কলেজের গন্ডিও পার হতে পারেন না। আরো ২০ শতাংশ পড়াশোনা শেষে চাকুরিতে ঢোকেন না।
প্রতি বছরই শিক্ষিত জনশক্তি বের হচ্ছে, তাদের সংখ্যার তুলনায় কাজের ক্ষেত্র কিন্তু বাড়ছে না। কাজের বাজারের চাহিদার সাথে শিক্ষাব্যবস্থার বিরাট অসংগতি এবং শিক্ষাব্যবস্থার সাথে অর্থনীতির ভারসাম্যহীনতার ফলে এ শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা বেড়েই চলেছে। কর্মসংস্থান এবং যোগ্যতার অভাবে তারা বেকারত্ব বয়ে বেড়াতে বাধ্য হচ্ছেন। প্রতি বছর সর্বোচ্চ সংখ্যক জিপিএ ৫ ধারীদের উল্লাস, শতকরা সর্বোচ্চ সংখ্যক পাশের খবর পাওয়া যায়। অতঃপর তারা বিভিন্ন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ, মাদরাসায় ভর্তি হন এবং তাদের অনেকেই ফার্স্ট ক্লাস লাভ করে শিক্ষাজীবন শেষ করেন। কিন্তু ফার্স্ট ক্লাস লাভের পরেও তাদের অধিকাংশকেই কোনো চাকরী না পেয়ে গৃহশিক্ষকতা করে কোনোমতে দুই বেলার খাবার জোগাড় করতে হয়। আর এ সংখ্যা তো বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ছেলেদের, মেয়েদের অবস্থা আরো করুণ। দৈনিক ইনকিলাবের সেপ্টেম্বর, ২০২২ এর একটি নিবন্ধের বরাত অনুযায়ী দুই বছর আগে এক ইংরেজি দৈনিকে প্রকাশিত প্রতিবেদনে দেখানো হয়েছে, দেশে উচ্চ শিক্ষিত বেকার প্রায় পৌনে ১ কোটি। এদের মধ্যে যারা চাকরির জন্য চেষ্টা করছে, তাদের সংখ্যাও অনেক। ২০১৮ সালের বিসিএসে পদের চেয়ে দুইশো গুণ বেশি প্রার্থী আবেদন করেছিলেন। মাত্র ছয়টি সরকারি খাতের চাকরির নিয়োগ পরীক্ষায় আবেদন করেন মোট ৫০ লক্ষেরও বেশি প্রার্থী। মাদক নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরে আবেদনকারীর সংখ্যা ছিলো পদের তুলনায় ৮৯৭ গুণ বেশি। খাদ্য অধিদপ্তরে আবেদনকারীর সংখ্যা ছিলো পদের তুলনায় ১৩৬৪ গুণ বেশি। কয়েকটি বিসিএস উত্তীর্ণ হয়েও চাকরি মেলেনি প্রায় ৩২ হাজার প্রার্থীর। বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠানের (বিআইডিএস) তথ্য অনুযায়ী এসএসসি উত্তীর্ণদের ২৮ শতাংশ, এইচএসসি উত্তীর্ণদের ৩০ শতাংশ, স্নাতকদের ৩৬ শতাংশ, স্নাতকোত্তরদের ৩৪ শতাংশ, সার্বিকভাবে এ জাতীয় শিক্ষিতদের ৩৩ দশমিক ১৯ শতাংশ বেকার। এ শিক্ষিত বেকার শ্রেণি চাইলেই যে কোনো পেশার সাথে জড়িত হতে পারে না। একজন দিনমজুরের একদিনের আয় ৬০০-১০০০ টাকা। শিক্ষিত বেকার শ্রেণি তো দিনমজুরও হতে পারছে না! বেকারত্ব নেই বলে প্রচারণা চালানো সুবিধাবাদীরা বলেন, দেশে ধান কাটার জন্য কৃষিশ্রমিকও পাওয়া যায় না। অথচ এ না পাওয়ার কারণও সেই শিক্ষিত শ্রেণির দ্বিধা! এ কাজ তাদের জন্য সম্মান হানির কারণ। আবার এ শ্রেণির অনেকেই ভালো রোজগারের আশায় জায়গা-জমি, বসতভিটা বিক্রি করে প্রবাসে পাড়ি জমান। অমানুষিক শ্রম আর হেয় দৃষ্টি সহ্যের বিনিময়ে তারা দেশে টাকা পাঠান, অর্থনীতির ভাষায় যাকে আদর করে নাম দেওয়া হয়েছে রেমিটেন্স। এ রেমিটেন্সই দেশের রিজার্ভের যোগান দেয়। প্রতিবারই রিজার্ভ লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের উচ্ছসিত ঘোষণা আসে সরকারের পক্ষ থেকে, অথচ তাদের প্রবাস গমন বা অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিতকরণে সরকারের কোনো ভূমিকাই নেই। উপরন্তু তাদের মধ্যে যারা দালাল চক্রের খপ্পরে পড়ে নিঃস্ব হয়ে যান কিংবা বিদেশে জেল-জরিমানার শিকার হন, নির্যাতন বা দুর্ঘটনার শিকার হয়ে লাশ হয়ে বা পঙ্গু হয়ে দেশে ফিরেন, তখন সরকার ক্ষতিপূরণ বা সাহায্য-সহযোগিতা নিয়ে তাদের পাশে দাঁড়ায় না। অন্যদিকে যারা অর্থের অভাবে প্রবাসেও যেতে পারছেন না, দেশেও কাজ করতে পারছেন না, তাদের অনেকেই হতাশায় নানা ধরনের অপরাধে জড়িয়ে পড়ছেন, লোকলজ্জার ভয়ে বেছে নিচ্ছেন আত্মহত্যার পথও। প্রতিদিন খবরের কাগজ কিংবা মিডিয়ায় এসব খবর দেখতে দেখতে তা আমাদের কাছে ডালভাতের মতো হয়ে গেছে।
প্রতি বছর উচ্চ শিক্ষা নিয়ে শ্রম বাজারে আসা শিক্ষার্থীদের অর্ধেকই বেকার থাকছেন বা নিজের যোগ্যতা অনুযায়ী চাকরি পাচ্ছেন না। রাষ্ট্রীয় পর্যায় থেকে এ সমস্যার সমাধান করা তো হচ্ছেই না, বরং তাদের থেকে শুষে নেওয়া হচ্ছে। তাদের বেকারত্বের অসহায়ত্বকে পুঁজি করে চুটিয়ে ব্যবসা করা হচ্ছে। শিক্ষিত বেকার যুবকদের নিয়োগ, চাকরির পরীক্ষায় আবেদন করানোর মাধ্যমে কোটি কোটি টাকা আয় করা হচ্ছে। মাত্র দুই বা তিনটি পদের জন্য আবেদন ফি নেওয়া হয় কয়েক হাজার জন থেকে। সম্প্রতি একটি ব্যাংকে ৮০ টি পদের বিপরীতে আবেদন করে প্রায় ১ লক্ষ প্রাথী! আবার অনেক ক্ষেত্রেই কিছু পদ খালি রেখে সার্কুলার দেওয়া হয়, প্রথম বার বাছাইয়ের পরবর্তীতে আবার খালি পদের জন্য সার্কুলার দেওয়া হয়৷ এভাবে বার বার সার্কুলার দিয়ে কোটি কোটি টাকা আয় করা হয়। এসব নিয়োগ পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য প্রতি সপ্তাহে লক্ষ লক্ষ যুবক গ্রাম থেকে যাতায়াত ভাড়া দিয়ে শহরে আসছেন। থাকা-খাওয়ার খরচ, সময় ও শক্তির বিপুল অপচয় হয় তাদের। চাকরি প্রার্থীদের এ বিড়ম্বনা, দুর্ভোগ, মানসিক যন্ত্রণা কি আমাদের হৃদয়ে একটুও নাড়া দেয়? যে যুবকরা আজ রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য, রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ উন্নয়নের জন্য, সমাজ ও সংস্কৃতিকে ঢেলে সাজানোর জন্য প্রস্তুতি নেওয়ার কথা ছিলো, সে যুবকরাই আজ হতাশাগ্রস্ত হয়ে দৌড়াতে বাধ্য হচ্ছেন। স্বাধীনতার ৫০ বছর পার হওয়ার পরেও বাংলাদেশের বেকার যুবকদের শুধুমাত্র একটি নিয়োগ পরীক্ষা দেওয়ার জন্য টেকনাফ, তেতুলিয়াসহ দূর-দূরান্ত থেকে ঢাকায় আসতে হয়, নিজ জেলায় বসে পরীক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থাটাও নেই। আবার প্রশ্ন ফাঁসসহ নানা ধরনের জালিয়াতির কারণে একই পরীক্ষা তাদেরকে দুই-তিনবার করেও দিতে হচ্ছে, তবু তাদের মুক্তি মিলছে না! চাকরির পরীক্ষার প্রস্তুতির জন্য বহু সংখ্যক প্রার্থী শহরগুলোতে মেস, হোস্টেলে থেকে পরীক্ষার প্রস্তুতির গাইড-নোটে মুখ বুজে আছেন খেয়ে না খেয়ে। প্রচন্ড স্থবির এ শহরগুলোর এ যুবকদের ভার কীভাবে বইবে বাংলাদেশ?
আবার বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শিক্ষিত হয়ে বের হওয়া যুবকদের কতজন সত্যিকার যোগ্যতা অর্জন করেছেন সেটিও আলোচনার দাবি রাখে। জনশুমারি ও গৃহগণনা, ২০২২ এর প্রাথমিক প্রতিবেদন অনুযায়ী বর্তমানে দেশে সাক্ষরতার হার ৭৪ দশমিক ৬৬ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। আদতে এ এক অন্তঃসার শূন্য বিপ্লব। উন্নত দেশগুলোতে দক্ষ ও অতি দক্ষ জনশক্তির পরিমান ৫০ শতাংশেরও বেশি। যেমন– জার্মানিতে ৭৩ শতাংশ, জাপানে ৬৬ শতাংশ, সিঙ্গাপুরে ৬৫ শতাংশ, অস্ট্রেলিয়াতে ৬০ শতাংশ, চীনে ৫৫ শতাংশ, দক্ষিণ কোরিয়ায় ৫০ শতাংশ, মালয়েশিয়ায় ৪৬ শতাংশ মানুষ দক্ষ। বাংলাদেশের সার্বিক জরিপ অনুসারে দেশে দক্ষ এবং মধ্যম মানের জনশক্তি মাত্র ১৪ শতাংশ! বাস্তবে এ সংখ্যা আরো কম। বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরোর তথ্য অনুযায়ী এটি মাত্র ৮ দশমিক ৪৪ শতাংশ!
বাংলাদেশে সাধারণ, প্রকৌশল, মেডিকেল, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, কৃষি বিজ্ঞান, ভেটেনারি, টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং, ইসলামী, ধর্মতত্ত্ব, ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, বিশেষ বিশ্ববিদ্যালয় মিলিয়ে মোট ৫৮ টি সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা ১০৭ টি। রয়েছে ৪৯ টি পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট এবং কয়েক হাজার মাদ্রাসা। সরকারি-বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ৮২ হাজার ৯৮১ টি, মাধ্যমিক বিদ্যালয় ৫৩ হাজার ৫৮৯ টি, নিন্ম মাধ্যমিক বিদ্যালয় ৩ হাজার ৪৯৪ টি। এত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থাকা সত্ত্বেও শ্রমবাজার উপযোগী দক্ষ জনবল তৈরি হচ্ছে না! শিক্ষাজীবন শেষে শিক্ষার্থীরা জাতির জন্য আশীর্বাদ না হয়ে বোঝা হয়ে উঠছে। অর্জিত শিক্ষার মান নিয়ে দেশের বাইরে গিয়ে তারা অন্য দেশের শিক্ষার্থীদের মতো সম্মান পাচ্ছে না। দৈনিক প্রথম আলোর মে, ২০২২ এর একটি নিবন্ধের বরাত অনুযায়ী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দেওয়া পিএইচডি ডিগ্রির বেশির ভাগ বাংলা সাহিত্য ও ধর্মশিক্ষায়, যার সত্যিকার অর্থে বাস্তব প্রয়োগের সম্ভাবনা খুবই কম। মৌলিক বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, চিকিৎসাশাস্ত্রসহ মূল মূল ক্ষেত্রগুলোর কোথাও বাংলাদেশের কোনো অবদান নেই, এক্ষেত্রে শুধু কৃষিবিজ্ঞানীদের অবদানের কথা উল্লেখ করা যায়। আগে মালয়েশিয়া থেকে শিক্ষার্থীরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে আসতেন, এখন ঘটছে উল্টোটা।
এ ব্যর্থতার দায়ভার কিন্তু আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার। শিক্ষার গুণগত মান ঠিক নেই, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পর্যাপ্ত কম্পিউটার ল্যাব, বিজ্ঞানাগার সুবিধা নেই। রয়েছে যোগ্য শিক্ষকের প্রবল সংকট, সুবিধাবঞ্চিত শিক্ষার্থীদের জন্য পর্যাপ্ত সহযোগিতার ঘাটতি ইত্যাদি। সঠিকভাবে উচ্চ শিক্ষা অর্জনে যে ব্যর্থতা, তা নিয়েও কিন্তু প্রশ্ন উঠছে না! শিক্ষার্থীদের ভাষাগত দিক থেকে শুরু করে কারিগরি দক্ষতা অর্জন করানোর কোনো জোর প্রচেষ্টা পরিলক্ষিত হয় না! বাংলাদেশের জনপ্রসাশন, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, শ্রম মন্ত্রণালয় শিক্ষার্থীদের ক্যারিয়ার প্রশিক্ষণের জন্য ভালো মানের কোনো আয়োজন করছে না, ফান্ড দিচ্ছে না। অথচ বেকারত্বের সাথে এ বিষয়গুলো ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এসবের সমাধান না করলে আমরা কখনই বেকারত্ব থেকে মুক্তি পাবো না।
এ গেলো শুধু শিক্ষিত যুবকদের কথা। তাদের পাশাপাশি যে বিশাল সংখ্যক মানুষ অশিক্ষিত থেকে যাচ্ছে, কিংবা যাদের যোগ্যতার ঘাটতি থেকে যাচ্ছে, তাদের অবস্থা তো কল্পনাতীত!
আবার বেকারত্বে জর্জরিত বাংলাদেশের বিভিন্ন কোম্পানিসহ মাল্টিন্যাশনাল প্রতিষ্ঠানগুলোতে প্রচুর সংখ্যক বিদেশি কর্মকর্তা-কর্মচারি কাজ করছে। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের তথ্য অনুযায়ী বাংলাদেশে অবস্থানকারী মোট বৈধ বিদেশির সংখ্যা ১ লাখ ১১ হাজার ৫৭৫ জন। অথচ বিভিন্ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান, পত্র-পত্রিকার প্রতিবেদনে অনুযায়ী এ সংখ্যা প্রায় ১০ লাখ! দৈনিক ইনকিলাবের সেপ্টেম্বর, ২০২২ এর একটি নিবন্ধে উল্লেখ করা হয়েছে, একেকজন বিদেশি কর্মকর্তার বেতন পাঁচজন বাংলাদেশি কর্মকর্তার মোট বেতনের চেয়েও বেশি! অর্থাৎ একজন বিদেশি কর্মকর্তা পাঁচজন দেশীয় কর্মপ্রত্যাশীর জায়গা দখল করে নিয়েছেন এবং এ হিসেবে বিদেশি কর্মকর্তা নিয়োগকৃত প্রতিষ্ঠানগুলো প্রায় ৫০ লাখ বাংলাদেশিকে বেকারত্বের দিকে ঠেলে দিয়েছে! তাদের নিয়োগকৃত এ কর্মকর্তাদের অধিকাংশ ভারতীয়। বেসরকারি সংস্থা সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের (সিপিডির) এক গবেষণা অনুযায়ী বাংলাদেশে প্রায় ৫ লাখ ভারতীয় কাজ করছে, যারা বছরে ৩ দশমিক ৭৬ বিলিয়ন ডলার বা প্রায় ৪০ হাজার কোটি টাকা তাদের দেশে নিয়ে যাচ্ছে। ভারতের পঞ্চম রেমিট্যান্স প্রদানকারী দেশ বাংলাদেশ! এভাবেই বেকারত্ব জর্জরিত বাংলাদেশের এ দৈন্যদশার মধ্যেও হাজার হাজার কোটি টাকা বিদেশে চলে যাচ্ছে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই বাংলাদেশি চাকরিপ্রার্থীদের যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও প্রতিষ্ঠানগুলো বিদেশিদের নিয়োগ দিচ্ছে, এমনকি এজন্য তারা বাংলাদেশি কর্মীদের ছাঁটাইও করছে। এক্ষেত্রে তারা বিনিয়োগ বোর্ডের নীতিমালাকেও তোয়াক্কা করছে না। এ নীতিমালা অনুযায়ী একজন বিদেশি কর্মকর্তা বা কর্মচারী নিয়োগ দিতে হলে তার বিনিময়ে পাঁচজন বাংলাদেশিও নিয়োগ দিতে হবে। সেই সাথে নিযুক্ত বিদেশি নাগরিকের কাজের ক্ষেত্রে বাংলাদেশিকে প্রশিক্ষণ দিয়ে তৈরি করতে হবে, অতঃপর বিদেশিকে বিদায় দিতে হবে। প্রতিষ্ঠানগুলো যেমন এ নীতিমালা মানছে না, তেমনি বিনিয়োগ বোর্ডও পরখ করে দেখছে না যে প্রতিষ্ঠানগুলো নীতিমালা মানছে কিনা! ফলশ্রুতিতে দেশের বেকার যুবকদের হতাশাকে বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়ে দেশের টাকা, দেশের সম্পদ নিয়ে যাচ্ছে অন্য দেশ, যা এ বেকারত্বকে আরো প্রকট করে তুলছে।
এক্ষেত্রে কথা হলো বিশ্বের উন্নত দেশগুলোতেও বেকারত্ব রয়েছে। কিন্তু এসব দেশের বেকারত্বের ধরনের সাথে আমাদের দেশের বেকারত্বের ধরনের মিল নেই। উন্নত দেশগুলোতে বেকারদের সরকারি ভাতা প্রদান করা হয়। আবার এ দেশগুলোর অধিকাংশেরই জনসংখ্যা কম হওয়ার কারণে কর্মক্ষেত্রে নিয়োগ দেওয়ার মতো জনশক্তির অভাব রয়েছে। ফলশ্রুতিতে দেশগুলো বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে জনশক্তি আমদানি করে। এসব দেশের শ্রমবাজারের কাঠামো শক্তিশালী হওয়ার কারণে তারা চাকুরিরতদের পর্যাপ্ত বেতন দিতে পারে, যা তাদের জীবনমান উন্নত করার জন্য যথেষ্ট। অন্যদিকে আমাদের দেশে রয়েছে বিপুল সংখ্যক কর্মক্ষম জনশক্তি। কিন্তু আমাদের দেশে কর্মসংস্থানের অভাব যেমন প্রকট, তেমনি এ বিপুল সংখ্যক কর্মক্ষম জনশক্তিকে দক্ষ জনশক্তিতে পরিণত করার উপর্যুক্ত প্রচেষ্টার অভাবও প্রকট। আবার দেশের কর্মক্ষেত্রগুলোর বেশিরভাগই অনানুষ্ঠানিক এবং বেতনভাতাও নির্দিষ্ট নয়, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তা চাকুরিরতদের জীবনমান উন্নত করতে পারে না।
অথচ মুসলিম সালতানাতে এ বাংলা ছিলো অর্থনৈতিকভাবে বিপুল শক্তিমত্তার অধিকারী। ২৩ শতাংশ জিডিপির সমৃদ্ধ বাংলা অঞ্চলে বেকারত্ব ছিলোই না, বরং কর্মক্ষেত্রে পর্যাপ্ত লোকবলের অভাব ছিলো। জাহাজের ফ্যাক্টরিগুলোতে পর্যাপ্ত লোক নিয়োগ করতে না পারার কারণে উন্নতির কাঁচামাল থাকা সত্ত্বেও জাহাজ শিল্প বিশ্বে উল্লেখযোগ্য স্থান দখল করে নিতে পারেনি। কৃষি, মৎস খাতেরও একই অবস্থা, বিপুল সম্ভাবনা থাকলেও তুলনামূলকভাবে কর্মদক্ষ লোকের অভাব ছিলো। রেশম, মসলিন, কাঠের কাজ, তুলোজাত পণ্য সামগ্রি, ধান, গম, পাট, তেলবিজ, আখ, মসলাসহ কৃষি ও শিল্পে সর্বোচ্চ সমৃদ্ধির পথে হাঁটতে থাকা বাংলাকে শুষে নিয়ে শিল্পায়ন ঘটানো সাম্রাজ্যবাদী ঔপনিবেশিক শক্তি রেখে গেছে শুধু তাদের রচিত ব্যবস্থা, যে ব্যবস্থার অন্যতম ফসল এ ভয়াবহ বেকারত্ব এবং দৈন্যদশা।
আমরা যদি বেকারত্ব মোকাবেলা করতে না পারি, তাহলে তা বাড়তেই থাকবে এবং ভবিষ্যৎ বাংলাদেশের অবস্থান কোথায় গিয়ে ঠেকবে তা কল্পনাতীত। বেকারের প্রকৃত সংখ্যা নিয়ে কথা বলছেন না দেশের কর্ণধাররা, নেতারা; বেকারত্ব নিরসনের আলাপও উঠে আসছে না তাদের ভাষণে। উপরন্তু তারা দেশীয় বেসরকারি সংস্থাগুলো আর আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর জরিপে যখন সত্যিকার অবস্থা ফুটে উঠতে দেখছেন, তখন এ জরিপগুলোকে ‘রাজনৈতিক প্রতিহিংসা’র কাতারে ফেলতেও দ্বিধা বোধ করছেন না! অথচ এ সমস্যা নিরসনে তাদেরই সবচেয়ে বেশি ভূমিকা পালন করা উচিত ছিলো।
এখন এ সার্বিক পরিস্থিতির সমাধানের প্রশ্নে যদি আসি, সমাধানকল্পে কিছু প্রশ্নের উত্তর আমাদের সামনে রাখতে হবে। আমাদের পরবর্তী প্রজন্মের ভবিষ্যৎ কী? শিক্ষায় ঝরে পড়া যুবকরাসহ বিশাল এ বেকার শ্রেণি নিয়ে আমাদের ভাবনা কী?
এক্ষেত্রে প্রথমতই বেকারের প্রকৃত সংখ্যা এবং সার্বিক অবস্থা নিরূপণের জন্য বাংলাদেশের উপযোগী পদ্ধতিতে জরিপ পরিচালনা করতে হবে এবং এজন্য সরকারি সংস্থার পাশাপাশি কয়েকটি স্বাধীন, পক্ষপাতহীন বেসরকারি সংস্থা চালু করতে হবে।
সকল ধরনের দুর্নীতি থেকে মুক্ত হয়ে আমাদের অভ্যন্তরীণ উন্নয়ন ঘটাতে হবে। বেকারত্ব নিরসণে এটিই সবচেয়ে জরুরী। এক্ষেত্রে আমাদের শিল্প খাত, কৃষি খাত, খনিজ খাতসহ সর্বোচ্চ সম্ভাবনাময়ী জনশক্তিকে ভালোভাবে কাজে লাগাতে পারলে আগামী ২০ বছরে ২০ কোটিরও বেশি মানুষের কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা সম্ভব।
গত কয়েক বছরে শিল্প খাতে বিনিয়োগ এবং এ খাতের সার্বিক অবস্থা নিম্নমুখীই হয়েছে। বেসরকারি খাতে কাঙ্ক্ষিত বিনিয়োগ হচ্ছে না এবং সরকারি খাতে বিনিয়োগের কার্যকর ব্যবহার হচ্ছে না। নতুন শিল্প-কারখানা গড়ে উঠার সংখ্যা হাতে গোনা, অন্যদিকে অনেক শিল্প-কারখানা বন্ধ হয়ে গেছে। গ্যাস, বিদ্যুতের অভাবে অনেক কারখানা নতুন করে চালু কর সম্ভব হচ্ছে না। প্রায় পাঁচশত পোশাক কারখানা বন্ধ হয়ে গেছে, বেকার হয়েছেন পনেরো লাখেরও বেশি কর্মজীবী। এ খাতকে সবচেয়ে বেশি জোর দিয়ে সর্বোচ্চ অবস্থানে নিয়ে যেতে হবে। সেই সাথে দেশের ভারী শিল্পগুলো সরকারি খাতে রেখে অন্যান্য হালকা শিল্পে বেসরকারি বিনিয়োগের ব্যবস্থা করতে হবে।
বাংলার আবহমানকালের ঐতিহ্য কৃষিকে সর্বোচ্চ প্রযুক্তির সমন্বয়ে সর্বোচ্চ সমৃদ্ধ করে তুলতে হবে। অবহেলা আর সুবিধাভোগী শ্রেণির শিকার হওয়ার দরুণ এক কালের সমৃদ্ধ পাট শিল্প হারিয়ে গেছে। কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করে ধান, চা, পাটসহ উল্লেখযোগ্য ফসলগুলো সংরক্ষণ এবং ফলনের ধারা অব্যাহত রাখতে হবে। এখন পর্যন্ত দেশের চাষযোগ্য জমির ৩০ শতাংশ সেচ কর্মসূচির আওতায় আনা হয়েছে। পতিত জমি আবাদ ও আরো অধিক পরিমাণে জমি সেচের আওতায় আনা হলে দেশে কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পাবে। পাহাড়ি ও হাওড় এলাকাসহ বেশ কিছু এলাকায় এখনো চাষযোগ্য অনেক জমি পতিত পড়ে আছে, এ জমিগুলো চাষের আওতায় আনতে হবে। কৃষি বিষয়ে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ ও পর্যাপ্ত গবেষণার ব্যবস্থা করতে হবে এবং উচ্চতর গবেষণালব্ধ ফলাফল প্রয়োগ করতে হবে। মাছ চাষের নদীগুলোকে পুনরায় দূষণমুক্ত করে চাষের পরিধি বাড়াতে হবে। কৃষি খাতে সরকারি অনুদান ও ব্যবস্থাপনাসহ সর্বোপরি সামগ্রিক উদ্যোগের বাস্তবায়ন বেকারত্বের হার অনেকাংশেই কমিয়ে আনবে।
আমাদের দেশের রয়েছে ৫০ এর উপরে খনিজ সম্পদ, যার সবই বিদেশীদের হাতে ইজারা দেওয়া। ইউরেনিয়ামের মতো দামী সম্পদও আমরা সাম্রাজ্যবাদীদের বিনা পয়সায় দিয়ে যাচ্ছি! এশিয়ার দ্বিতীয় বৃহত্তম গ্যাস ক্ষেত্র আমাদের, সেটিরও সুবিধা ভোগ করছে সাম্রাজ্যবাদীরা। এসব সম্পদ যথাযথভাবে ব্যবহার ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য দেশে মানসম্মত কোনো উদ্যোগ নেই, পরিসংখ্যানও নেই, সেই সাথে এ খাতে নিয়োগ করার মতো সুদক্ষ জনশক্তি সৃষ্টির প্রচেষ্টাও নেই। অথচ শুধুমাত্র খনিজ সম্পদের মাধ্যমেই অনেক বেশি কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা সম্ভব, যা বেকারত্ব নিরসনে অত্যন্ত কার্যকরী ভূমিকা রাখতে পারে।
যুবকদের নতুন উদ্যমে জাগিয়ে তুলতে হবে। আমাদের দেশের সবচেয়ে সম্ভাবনাময়ী খাত এ যুবশক্তি। দেশের জনসংখ্যার একটি বৃহদাংশ যুবক, যা মোট জনসংখ্যার ৩০ শতাংশ। যুবক জনগোষ্ঠীকে কাজে লাগানোর সব ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ না করতে পারলে এবং তাদেরকে বোঝায় পরিণত করলে এ সম্পদ চোখের পলকেই হারিয়ে যাবে। আর তাই স্বর্নালী আদিল সভ্যতার উত্তরসূরি যুবকদের মনে সভ্যতার চেতনার সুপ্ত বীজকে জাগিয়ে তুলে বৃক্ষে রূপান্তর করা, তাদের সামনে সুদমুক্ত, ন্যায়ভিত্তিক সভ্যতার ভিশন তুলে ধরা এবং সে আলোকে আত্মবিশ্বাসী করে তোলা অত্যাবশ্যক। ভিশন এবং অর্থবহ জীবনের মানেই দক্ষ হওয়া– এ কথা তাদেরকে খুব ভালোভাবেই উপলব্ধি করাতে হবে। তাদের মধ্যে সচেতনতা তৈরি এবং তাদেরকে সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করা ছাড়া অভ্যন্তরীন উন্নয়ন অসম্ভব এবং বেকারত্ব দূরীকরণও অসম্ভব।
শিক্ষাব্যবস্থাকে ঢেলে সাজিয়ে ঔপনিবেশিক গোলামীর নিগড় থেকে মুক্ত করতে হবে, শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়ন করতে হবে। শুধুমাত্র এ পদ্ধতিতেই ফাঁপা মস্তিষ্কের প্রজন্ম হয়ে বৃটিশ আজ্ঞাবহ কেরাণিতে পরিণত হওয়া এবং যুবক শ্রেণির তারুণ্যদীপ্ত পুনর্জাগরণ রোধে তাদের কর্মস্পৃহা, উদ্ভাবন কৌশল ও চিন্তা-চেতনা লোপ করার চক্রান্ত থেকে যুবক শ্রেণি মুক্তি পাবে। আর যখন তারা আত্মশক্তিপ্রবুদ্ধ ব্যক্তিতে পরিণত হবে, তখনই তারা হবে দেশ ও জাতির জন্য সুদক্ষ জনসম্পদ।
বর্তমানে নানা ক্ষেত্রে কর্মরতদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রতিনিয়ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।
সার্বিকভাবে কর্মসংস্থান বাড়াতে হবে। বেকারের প্রকৃত হার যে কোনো কৌশলে ধামাচাপা দেওয়া হচ্ছে ঠিকই, কিন্তু প্রবৃদ্ধির ক্ষেত্রে ঘটছে ঠিক উল্টোটা। দেশের মন্ত্রী বলেন, প্রবৃদ্ধি ৭ ভাগ, অন্যদিকে বিশ্বব্যাংক, আইএমএফ বা এডিবি বলে ৬ ভাগ! জিডিপি প্রবৃদ্ধির সাথে অবশ্যই কর্মসংস্থানের সমন্বয় ঘটাতে হবে, কারণ প্রবৃদ্ধি যে হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে বলা হচ্ছে, সে হারে কিন্তু কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পাচ্ছে না। যার কারণে এ প্রবৃদ্ধি কর্মসংস্থান তৈরিতে তেমন কোনো ভূমিকা রাখছে না।
আত্ম-কর্মসংস্থান সৃষ্টি খুব জরুরী৷ বর্তমানে যুবকদের বেশিরভাগই উচ্চ মাধ্যমিকের পরে কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে আগ্রহী, কারিগরি বা কর্মদক্ষতা বাড়ানোর শিক্ষায় তেমন আগ্রহী নয়। আবার প্রায় সবাই-ই চাকরির প্রত্যাশা করে, প্রয়োজনে ঘুষ দিয়ে, চামচামি করে চাকরি জুটাবে, তবু কেউ চাকরি সৃষ্টির কথা চিন্তা করে না। খুব কম সংখ্যক শিক্ষিতই উদ্যোক্তা হতে চায়। সরকারের উচিত প্রতি বছর নতুন নতুন প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠায় প্রয়াসী না হয়ে দক্ষ জনসম্পদ ও উদ্যোক্তা তৈরির সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা চালানো। এতে আত্ম-কর্মসংস্থান সৃষ্টি গতিশীলতা পাবে। এছাড়াও বিশেষত গ্রামীন যুবকরা বাড়ির আঙ্গিনায় গবাদি পশু পালন, হাঁস-মুরগির খামার স্থাপন, মাছ চাষ প্রভৃতির মাধ্যমে সহজেই আত্ম-কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করতে পারে, এক্ষেত্রেও সহায়তার জন্য সরকারকেই এগিয়ে আসতে হবে। ক্ষুদ্র শিল্পে বিনিয়োগ থেকে শুরু করে নানাবিধ অনানুষ্ঠানিক খাতে কর্মসংস্থান বাড়ানোর লক্ষ্যে কর্জে হাসানা, সরকারি প্রণোদনা প্রদান করতে হবে এবং আইনী ও নিরাপত্তা সুবিধা প্রদান করতে হবে।
ব্যাপক সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টি করতে হবে, সরকারি, বেসরকারি ও ব্যক্তিগত পর্যায় থেকে উৎসাহ ও দিকনির্দেশনা প্রদান করতে হবে। যেমন– মৎস শিল্পের ক্ষেত্রে সুযোগ-সুবিধার কমতি, রাষ্ট্রীয় প্রণোদনার অভাব, প্রশিক্ষণের অভাব, উৎসাহ ও পর্যাপ্ত দিকনির্দেশনার অভাব লক্ষণীয়। এ অভাব দূর করতে হবে।
বেসরকারি খাতগুলো উন্মুক্ত করতে হবে, বিদেশীদের নিয়োগের ক্ষেত্রে অন্যান্য দেশের সাথে সম্পর্ক বৃদ্ধির সাথে সাথে বাংলাদেশীদের জন্য বিশাল বাজার সৃষ্টি করতে হবে।
মুক্তির দাবি এবং পর্যালোচনা করে ৯০ শতাংশ মুসলমানের দেশে আল্লাহর রাসূলের (স.) দেখিয়ে যাওয়া মুক্তির পথ অনুযায়ী আমাদের আর্থ-সামাজিকব্যবস্থাকে ঢেলে সাজাতে হবে।
ঋণ ও সুদ নির্ভর অর্থনীতির নিগড় থেকে বের হয়ে, উন্নয়নের ঔপনিবেশিক মূলনীতি বাদ দিয়ে আমাদের সামগ্রিক ব্যবস্থাকে উন্নত করতে হবে।
বন্দর, প্রতিরক্ষা, বৈদেশিক আয়সহ সবকিছু নিয়েই কথা বলতে হবে। সমাধানকল্পে সকল অবস্থান থেকে সংগ্রাম করে যেতে হবে৷
জাতীয় কর্মসংস্থান কৌশল কমিটির জন্য সরকারকে চাপ দেওয়া, নিজেদের অবস্থান থেকে, প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দাবী পেশ করা, জাতীয় স্বার্থ রক্ষা কমিটি, প্রতিরক্ষা কমিটি, নগর কমিটি এবং উন্নয়ন কমিটি গঠন করে সমাজ ও রাষ্ট্র মিলেমিশে আগানোর কোনো বিকল্প নেই। আর এ প্রত্যেকটি প্রস্তাবনা প্রতিটি ধর্ম, বর্ণ, রাজনৈতিক দলের জন্যই জরুরী। এগুলো কোনোভাবেই নির্দিষ্ট কোনো দলের দাবী নয়, নির্দিষ্ট কোনো দলের বিরোধিতাও নয়, বরং প্রতিটি মানুষের জন্য প্রয়োজন।
সর্বোপরি বেকারত্বকে প্রধান সমস্যা হিসেবে স্বীকৃতি দিয়ে এ সমস্যা নিরসনে সকল পর্যায় থেকে সম্মিলিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে উদ্যোগ গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করতে হবে। তা না হলে ‘বেকারত্ব’ শুধুমাত্র একটি শব্দ হয়ে বাংলা রচনার পাতায় আর স্বপ্নালু চোখের যুবকদের তীব্র হতাশায় নিমজ্জিত মুখাবয়ব ও অধোগামী জীবনমানেই ঘুরপাক খাবে; আর একের পর এক স্পষ্ট হবে পাঁচশত বছরের মুসলিম সালতানাতের সমৃদ্ধ ইতিহাসের স্বাক্ষী বাংলার পশ্চাৎপদতার লজ্জিত পদচিহ্ন।





