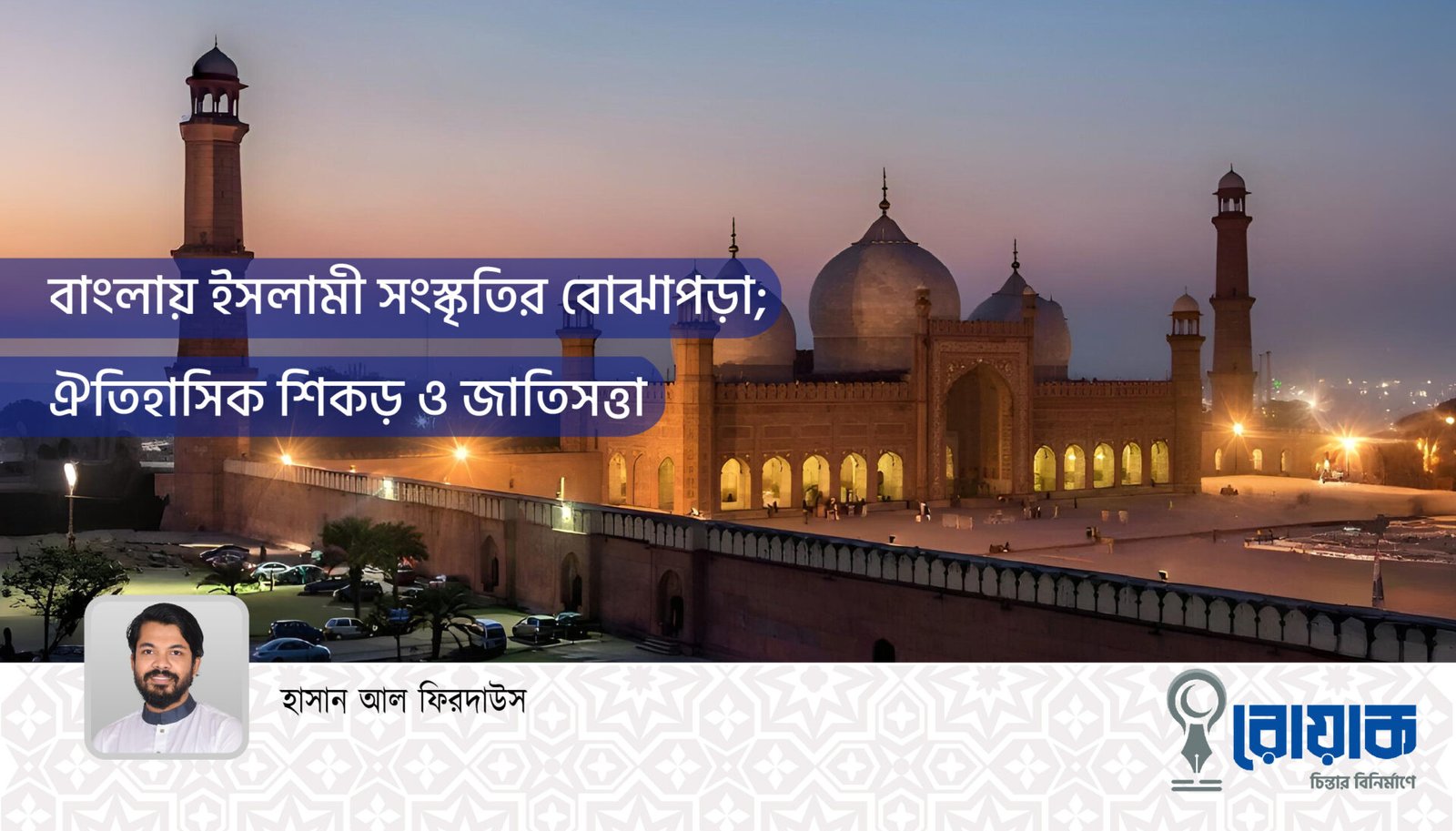ইসলামী সভ্যতায় সাংস্কৃতিক দৃষ্টিভঙ্গি
মানবমুক্তির একমাত্র জীবনব্যবস্থা দ্বীনে মুবীন ইসলামের যে মূলনীতি, মূলভিত্তি বা স্থায়ী নীতিসমূহ রয়েছে, যেগুলোকে আমরা উসূল বা আসাসুল কুল্লিয়া নামে জানি, এই মূলনীতিগুলোর ওপরই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ইসলামের ধর্মীয় বিধান, আকিদা, শরিয়াহ এবং ইবাদতের অপরিবর্তনীয় কাঠামো। আজকের আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু আসলে সেই ভিত্তিগুলিই। কারণ, এসব বিষয়ে প্রশ্ন তোলার, কিংবা অঞ্চলভেদে ভিন্নভাবে চিন্তা করার কোনো অবকাশ নেই। এগুলোই ইসলামী চিন্তাধারা ও শরীয়তের কেন্দ্র, যার বাইরে ইসলামকে কল্পনা করা যায় না।
তবে আমার প্রশ্নটি কিছুটা ভিন্ন। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মানুষকে সৃষ্টি করেছেন নানা ভাষা, জাতি ও সংস্কৃতির বৈচিত্র্যে। আমরা দেখি, প্রতিটি জাতিসত্তার রয়েছে নিজস্ব সাংস্কৃতিক আবহ, ঐতিহ্য ও মানসিক গঠন। এই বাস্তবতাকে সামনে রেখে প্রশ্ন আসে, ইসলামী ব্যবস্থা কীভাবে এই বৈচিত্র্যের সঙ্গে সমন্বয় ঘটিয়ে একটি সার্বজনীন সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠা করেছে?
ইসলামের মৌলিক নীতিমালা ও সভ্যতাগত দৃষ্টিভঙ্গি লক্ষ্য করলে দেখা যায়, কোনো অঞ্চল ইসলাম গ্রহণ করলে সেখানে শুধু ধর্মীয় বিধান নয়, সেই অঞ্চলের সাংস্কৃতিক জীবনও ইসলামের সঙ্গে একীভূত হয়ে যেত। রাসুলুল্লাহ ﷺ নিজ জীবনে তিনভাবে সাংস্কৃতিক উপাদানগুলিকে মূল্যায়ন করেছেন,
প্রথমত, সরাসরি গ্রহণ।
যেসব প্রথা ইসলামের মৌলিক নীতির বিরোধী নয় এবং নৈতিকতার ক্ষেত্রেও আপত্তিকর নয়, সেগুলো তিনি গ্রহণ করতেন। সমাজের জন্য কল্যাণকর ও ক্ষতিহীন উপাদানগুলোকে তিনি অনুমোদন দিতেন।
দ্বিতীয়ত, সংযোজন বা সংস্কার করে গ্রহণ।
যে প্রথাগুলোর কিছু অংশ ইসলামের মূলনীতির সঙ্গে সাংঘর্ষিক ছিল, সেগুলোর নেতিবাচক দিক বাদ দিয়ে, ইতিবাচক অংশকে ইসলামী নৈতিকতা যোগ করে নতুনভাবে প্রয়োগ করতেন। এর ফলে সমাজে এক নতুন ও কল্যাণকর সাংস্কৃতিক ধারা তৈরি হতো।
তৃতীয়ত, সরাসরি প্রত্যাখ্যান।
যেসব প্রথা ইসলামের মূলনীতির বিপরীত, শিরক বা কুসংস্কারের পর্যায়ে পড়ে- সেগুলো তিনি সম্পূর্ণভাবে প্রত্যাখ্যান করতেন।
অতএব, ইসলামের উসুল বা আসাসুল কুল্লিয়া, অর্থাৎ মৌলিক নীতিগুলোই ইসলামী সংস্কৃতির মূল ভিত্তি। এই ভিত্তি সঠিকভাবে বোঝা ও প্রতিষ্ঠা করা না গেলে, সংস্কৃতির ধারাটি বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে। তাই সমাজে এই নীতিগুলোকে প্রতিষ্ঠিত করা আলেম ও প্রজ্ঞাবানদের দায়িত্ব।
ইসলামী সভ্যতার আলেমগণ সর্বদা এই নীতিগুলোকে শক্তিশালী ভিত্তির ওপর স্থাপন করতেন। ফলে ইসলামের স্থায়ী ও অপরিবর্তনীয় মূলনীতি টিকে থাকত, আর পরিবর্তনশীল বিষয়ে স্থানীয় প্রেক্ষাপটে অভিযোজন ঘটত।
যেসব বিষয়ে সময় ও সমাজের প্রয়োজনে পরিবর্তন আসত, সেখানে ইসলাম নমনীয়তা ও প্রজ্ঞা দেখিয়েছে। তবে “বিদআত” ধারণাটি এখানে প্রায়ই ভুলভাবে বোঝা হয়।
অনেকে মনে করেন, নবী করিম ﷺ এর যুগে না থাকা যেকোনো নতুন কিছুই বিদআত। কিন্তু তা সঠিক নয়। বিদআত হচ্ছে সেই কাজ, যা সুন্নতের বিপরীতে, ইসলামের মূলনীতির পরিপন্থী, এবং কেউ সেটিকে ইবাদতের অংশ বা সওয়াবের কাজ হিসেবে মনে করে।
অন্যদিকে, কোনো কাজ যদি ইসলামের স্থায়ী নীতির বিপরীত না হয়, বরং আঞ্চলিক প্রয়োজনে সমাজে উপকারী ভূমিকা রাখে, তবে সেটি ইসলামী সংস্কৃতির বিপরীত কিছু নয়। বরং এটি সেই সমাজের স্বাভাবিক সাংস্কৃতিক প্রকাশ হিসেবেই টিকে থাকে।
সংস্কৃতিতে ইসলামের বিশ্বজনীনতা
ইসলামী সভ্যতার ইতিহাসে কোনো আলেম বা সুলতান কখনোই এমন প্রথাগুলো নিষিদ্ধ করেননি।
ইতিহাসের আলোকে দেখা যায়, ইসলামী সভ্যতা ও সংস্কৃতি (তুরাস ও তামাদ্দুন) সবসময়ই ছিল বিস্তৃত, গভীর ও মানবিক। মুসলমানরা যখন বিভিন্ন ভূখণ্ডে গিয়েছে, তারা সেই অঞ্চলের ভাষা ও সংস্কৃতিকে আপন করে নিয়েছে। যেমন তারা মানুষের অন্তর জয় করেছে, তেমনি গড়ে তুলেছে রাজধানী ও নগর, স্থাপত্য, শিক্ষা ও প্রশাসনিক কাঠামো, এবং সমাজজীবনের বিভিন্ন রূপ।
প্রশ্ন হল, তারা এটি কীভাবে করতে পেরেছিল?
ইতিহাসের পৃষ্ঠা উল্টালে দেখা যায়, মদিনা ব্যতীত প্রায় সব ইসলামী রাজধানীতেই মুসলমানদের তুলনায় অমুসলিমদের সংখ্যা ছিল বেশি। তবুও তারা সেখানে সম্পূর্ণ নিরাপত্তা ও মর্যাদার সঙ্গে বসবাস করেছে। নিজেদের আত্মপরিচয়, ধর্মীয় পরিচয় ও ভাষা সযত্নে রক্ষা করেছে। আশ্চর্যের বিষয়, তারা কখনো একে হুমকি হিসেবে দেখেনি; বরং ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থার প্রতি ছিল তাদের পূর্ণ আনুগত্য, এবং শত শত বছর তারা রাষ্ট্রের কল্যাণে অবদান রেখেছে।
এটি কোনো সাধারণ ঘটনা নয়; বরং এর পেছনে ছিল ইসলামী সভ্যতার সুনির্দিষ্ট সাংস্কৃতিক বোঝাপড়া এবং উৎকৃষ্ট সাংস্কৃতিক সংমিশ্রণ। এ ধরনের গভীর সহাবস্থান কেবল তখনই সম্ভব, যখন সভ্যতা তার মূল নীতিতে অবিচল থেকে পারিপার্শ্বিক বৈচিত্র্যকে আলিঙ্গন করে।
একইভাবে, মুসলমানদের উসূলী ভিত্তি, সাংস্কৃতিক কাঠামো, ইবাদত ও শরীয়তের কোনো দিকই এতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি বা সংকটে পড়েনি। বরং তারা নিজেদের স্বাতন্ত্র্য অটুট রেখেই ইসলামী আদর্শের সীমার মধ্যে থেকে সবকিছু সুচারুভাবে পালন করতে পেরেছে। এভাবেই ইসলাম, একদিকে তার চিরন্তন নীতিতে অবিচল থেকেছে, অন্যদিকে মানবজাতির সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যকে গ্রহণ করে এক বিশ্বজনীন সভ্যতার রূপ ধারণ করেছে।
আমাদের ভারতীয় উপমহাদেশের ইতিহাসের দিকে তাকালে দেখা যায়, ৬৯ হিজরিতে লালমনিরহাটে সাহাবী মসজিদ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। অর্থাৎ, ইসলামের আগমন এই ভূখণ্ডেও ঘটেছিল প্রাচীনকালেই। সাহাবীগণ, আলেম ও সুফিগণ এ অঞ্চলে এসে মসজিদ, খানকা ও অন্যান্য ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।
তবে এসব প্রতিষ্ঠান কেবল মুসলমানদের আকৃষ্ট করা, তাদের নিরাপত্তা দেওয়া কিংবা অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের ইসলাম গ্রহণে উৎসাহিত করার উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়নি। বরং এসব উদ্যোগের মূল উদ্দেশ্য ছিল সমাজে সুস্থ সংস্কৃতি, প্রকৃত ভ্রাতৃত্ব, নৈতিকতা, আখলাক ও মানবিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা করা। খানকা ও দরগাগুলোর দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যায়, সেখানে সব ধর্ম ও সম্প্রদায়ের মানুষ আশ্রয় গ্রহণ করতে পারতেন এবং নিরাপদ বোধ করতেন। সেখানে খাবারের ব্যবস্থা ছিল, বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কর্মসূচিতে অংশগ্রহণের সুযোগও ছিল সবার জন্য। একইভাবে, মুসলমানরা যেমন নামাজ-রোজা সকলের জন্য বাধ্যতামূলক করেননি, তেমনি ইসলামী সংস্কৃতির গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচিগুলোর ক্ষেত্রেও অংশগ্রহণের সুযোগ সবার জন্য উন্মুক্ত রেখেছিলেন। এভাবেই ইসলামী সংস্কৃতি এখানে বিকশিত হয়েছিল এক মানবিক, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও সহাবস্থানমূলক রূপে।
বৈচিত্র্যেই ঐক্যের সৌন্দর্য
মুসলমানরা খাদ্য, পোশাক, স্থাপত্য ও শিল্পের ক্ষেত্রে বিভিন্ন অঞ্চল থেকে উপকারী ও নান্দনিক উপাদান গ্রহণ করেছে, কিন্তু কোনো অঞ্চলের সংস্কৃতিকে অন্য অঞ্চলের সঙ্গে একরকম করে দেয়নি। যেমন, নোয়াখালীর বাজরা মসজিদ ও ইস্তাম্বুলের সুলতান ফাতিহ মসজিদ এক নয়,
দিল্লির জুমা মসজিদ ও ইস্পাহানের মসজিদও একই কাঠামোয় নির্মিত নয়।
কিন্তু সবগুলোতেই দেখা যায় এক অসাধারণ বৈশিষ্ট্য; উচ্চ রুচিবোধ, নান্দনিকতা, পরিচ্ছন্নতা ও ভারসাম্য।
এই সৌন্দর্যপূর্ণ সাংস্কৃতিক মেলবন্ধনই ইসলামী সভ্যতার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। ফলে বলকান থেকে মধ্যপ্রাচ্য ও দক্ষিণ এশিয়ার মুসলমানদের জীবনধারা আজও রুচিশীল, পরিচ্ছন্ন ও ভারসাম্যপূর্ণ।
এর কারণ একটাই, তারা ইসলামের স্থায়ী মূলনীতির প্রতি অনুগত থেকেও, প্রতিটি সমাজে কল্যাণকর, রুচিসম্পন্ন ও উপযোগী সংস্কৃতি বিকাশ করেছে। এটাই ইসলামী সংস্কৃতির মহত্ত্ব ও সাফল্যের আসল রহস্য।
খাদ্যের ক্ষেত্রেও একই নীতি প্রযোজ্য ছিল। ইসলামী সভ্যতায় খাদ্যের স্থায়ী নীতি ছিল, এটি যেন হালাল, স্বাস্থ্যকর ও উপকারী হয়। বাকিগুলো অঞ্চল, জলবায়ু ও সংস্কৃতির ভিত্তিতে বৈচিত্র্যময় রূপ পেয়েছে। এর মাধ্যমে ইসলাম একদিকে বৈশ্বিক হলেও, অন্যদিকে স্থানীয়ভাবে মানানসই একটি সংস্কৃতির ধারা তৈরি করতে পেরেছে— যা আজও টিকে আছে।
বাংলা অঞ্চল, মালয় অঞ্চল, ভারতীয় উপমহাদেশ এবং পূর্ব আফ্রিকার বিভিন্ন অঞ্চলে লক্ষ্য করলে দেখা যায়, মুসলমানরা প্রতিটি স্থানে স্থানীয় স্বতন্ত্রতা ও সংস্কৃতি রক্ষা করেই এক সুন্দর, পরিচ্ছন্ন ও রুচিশীল সংস্কৃতি উপহার দিয়েছে। ইসলামের আঞ্চলিক অভিযোজন সর্বত্র সুরক্ষিত ছিল। স্থানীয় খাবার, পোশাক, স্থাপত্য, উৎসব— সবকিছুই নিজস্ব আঙ্গিকে টিকে থেকেছে, আবার ইসলামের স্থায়ী নীতি ও নৈতিক শিক্ষা একই সঙ্গে বাস্তবায়িত হয়েছে।
ইসলামী সংস্কৃতিতে সামগ্রিক অবস্থান
এখানে প্রশ্ন আসে, ইসলামী সভ্যতার সংস্কৃতিতে সামগ্রিক অবস্থান কীভাবে কার্যকর ছিল? এটি বুঝতে হলে প্রথমেই আমাদের উপলব্ধি করতে হবে যে ইসলামী সংস্কৃতি এবং আজকের পাশ্চাত্য সংস্কৃতির মধ্যে একটি মৌলিক পার্থক্য রয়েছে।
পাশ্চাত্য সংস্কৃতি মূলত নিয়ন্ত্রণ, ভোগবাদ এবং কিছু গোষ্ঠীর শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠার স্বার্থে গড়ে উঠেছে। তারা সংস্কৃতিকে এক ধরনের বিনোদন বা সাময়িক খোরাক হিসেবে ব্যবহার করে, যা মানুষের অন্তরকে নয়, কেবল ইন্দ্রিয়কে তৃপ্ত করে। তাদের সংস্কৃতি ব্যক্তিকেন্দ্রিক ও ভোগবাদী; তাই তা শক্তিশালী হলেও আত্মিক নয়।
কিন্তু ইসলামী সংস্কৃতি এর সম্পূর্ণ বিপরীত। এটি সামষ্টিক, আত্মিক ও রুহানিকেন্দ্রিক। ইসলামী সংস্কৃতি মানুষের আত্মা, নৈতিকতা এবং সামাজিক ভ্রাতৃত্বকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছে।
যেমন ঈদের সংস্কৃতিতে আমরা দেখি, সবাই একসঙ্গে মাঠে নামাজ আদায় করছি, কোলাকুলি করছি; কোরবানির ঈদে একই গোশতের ঘ্রাণ চারদিকে ছড়িয়ে পড়ছে, সবাই একে অপরকে গোশত বিলিয়ে দিচ্ছি। রমজান মাসে সৃষ্টি হয় এক বিশেষ আধ্যাত্মিক পরিবেশ। শবে মেরাজ, শবে বরাত প্রতিটি উপলক্ষেই আমরা প্রতিবেশীদের, এমনকি অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদেরও খাবার দিই। এখানেই নিহিত ইসলামী সংস্কৃতির মানবিকতা ও সহাবস্থান।
আমাদের কবিতার আসর, মিলাদ, জিয়াফত, খানকা ও দরগার বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান সবই ছিল উন্মুক্ত, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও সমাজকেন্দ্রিক। এখানে সব শ্রেণি, ধর্ম ও সম্প্রদায়ের মানুষ অংশগ্রহণ করতে পারতেন। এই সাংস্কৃতিক পরিবেশ সমাজে পারিবারিক বন্ধন, পারস্পরিক সহমর্মিতা ও নৈতিক মূল্যবোধকে দৃঢ় করেছিল।
অন্যদিকে পাশ্চাত্য সংস্কৃতি এমন নয়। তাদের চলচ্চিত্র, সংগীত বা বিনোদনমূলক উপাদানগুলো প্রায়ই অশ্লীলতা, অনৈতিকতা ও মূল্যবোধহীনতার দিকে ধাবিত করে। তাদের সংস্কৃতি পরিবার ভাঙে, সমাজকে বিভক্ত করে। তারা সাময়িক আনন্দ পায়, কিন্তু দীর্ঘমেয়াদে তা আত্মিক ক্ষয় ডেকে আনে। যেমন মদ্যপান বা অতিরিক্ত ভোগবিলাস সাময়িক আনন্দ দিলেও তা শেষ পর্যন্ত ধ্বংস ডেকে আনে।
আবার, ইসলামী সংস্কৃতির প্রতিটি অনুষ্ঠান ও ইভেন্ট সার্বজনীন ও কল্যাণমুখী। এটি কেবল ধর্মীয় নয়, সামাজিক দিক থেকেও বিশাল প্রভাব সৃষ্টি করেছে। আমাদের অঞ্চলে খানকা ও দরগাগুলো ছিল আধ্যাত্মিক বলয়, যেখানে মানুষ আত্মিক প্রশান্তি, নৈতিক শিক্ষা এবং সমাজসেবার অনুশীলন করত। এখান থেকে মানুষ রুহানী শক্তি অর্জন করত, আত্মশুদ্ধির পথ খুঁজে পেত।
এই আধ্যাত্মিক সংস্কৃতি একটি ভ্রাতৃত্বপূর্ণ, সহিংসতামুক্ত ও নিরাপদ সমাজ গঠনে অবদান রেখেছিল। এটাই ছিল ইসলামী সংস্কৃতির মৌলিক সাফল্য—যা কেবল ধর্ম নয়, মানবিক ও সামাজিক উন্নয়নের ভিত্তি তৈরি করেছিল।
কিন্তু আজ আমরা যদি ইতিহাসকে ছোট করে দেখি, তবে এই গভীর সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে অনুধাবন করা সম্ভব হবে না।
উপনিবেশিক আগ্রাসন ও সাংস্কৃতিক ক্ষয়
পাশ্চাত্য ও ওরিয়েন্টালিস্ট অনেক লেখক ইসলামের এতোসব প্রসারকে বিকৃতভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। কিন্তু সত্য হল, ইসলামী সংস্কৃতি সামাজিক ন্যায়, মানবিক মর্যাদা, পরিছন্নতা, আতিথেয়তা, অপচয়ের বিরোধিতা, পারস্পরিক বন্ধন ও প্রতিবেশীর অধিকার; এই মূল্যবোধগুলোর মাধ্যমে সমাজকে প্রভাবিত করেছে।
যেখানেই মুসলমানরা গিয়েছে, তারা পরিছন্নতা শিখিয়েছে, পারিবারিক বন্ধনকে শক্ত করেছে, সমাজবদ্ধ জীবনধারা তৈরি করেছে। ভারতীয় উপমহাদেশে, কুর্দ অঞ্চলে বা আফ্রিকার অনেক স্থানে দেখা যায়- মুসলমানদের সংস্পর্শে থাকা হিন্দু, বৌদ্ধ ও খ্রিস্টান পরিবারগুলোও পরিচ্ছন্নতা ও পারিবারিক নৈতিকতার দিক থেকে উন্নত হয়েছে।
যেখানে মুসলমানদের উপস্থিতি ছিল না, সেখানে সমাজ অনেক বেশি অব্যবস্থাপূর্ণ ও বিশৃঙ্খল। এই বাস্তবতা প্রমাণ করে যে ইসলামী সংস্কৃতি কেবল ধর্মীয় নির্দেশনা নয়, বরং একটি নৈতিক ও সামাজিক শক্তি, যা মানবিক উন্নয়নের পথে সমাজকে পরিচালিত করেছে।
দুঃখজনক হলেও সত্য, এই সাংস্কৃতিক ও সভ্যতাগত ধারাবাহিকতা সবচেয়ে বেশি বাধাগ্রস্ত হয়েছে উপনিবেশিক শাসনের কারণে। আফ্রিকার উপকূল, মালয় অঞ্চল, ভারতীয় উপমহাদেশ কিংবা বলকান; সর্বত্র মুসলমান সমাজ কখনও ব্রিটিশ, কখনও ফরাসি, কখনও কমিউনিস্ট আগ্রাসনের মুখোমুখি হয়েছে।
এসব আগ্রাসনের ফলে ইসলামী সভ্যতার মূল্যবোধনির্ভর সংস্কৃতি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ইসলামী সভ্যতার অন্তর্গত মূল্যবোধগুলোই ছিল সেই সাংস্কৃতিক উপাদান, যেগুলোর মাধ্যমে মুসলমানরা সমাজে প্রভাব বিস্তার করেছিল।
কেবল খাবার, পোশাক বা ভাষা দিয়ে কোনো সভ্যতা গঠিত হয় না; এগুলো সভ্যতার উপাদানমাত্র। আসল সভ্যতা গঠিত হয় প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে সঞ্চারিত নৈতিকতা, মূল্যবোধ ও সামষ্টিক মানসিকতার মাধ্যমে। এই মূল্যবোধ আইন দিয়ে চাপিয়ে দেওয়া যায় না; এগুলো বিকশিত হয় শিক্ষা, খানকা, মসজিদ ও সাংস্কৃতিক কর্মসূচির মাধ্যমে। মুসলমানরা ঠিক এইভাবেই সমাজে সভ্যতার ভিত স্থাপন করেছিল।
উদাহরণস্বরূপ, খাদ্যসংস্কৃতি আরবে এক রকম, এশিয়ায় এক রকম, তুরস্কে এক রকম, আর বাংলায় একেবারে ভিন্ন। কিন্তু মূল্যবোধ একটাই। একজন মুসলমান খাবার নষ্ট করবে না, অপরিচ্ছন্ন রাখবে না, হালাল ও স্বাস্থ্যকর খাবার গ্রহণ করবে।
একজন আফ্রিকান মুসলমান, কেরালার মুসলমান বা বাঙালি মুসলমান; সবাই একই নীতিতে বিশ্বাসী। তারা খাবার অপচয় করবে না, অতিথিকে সম্মান করবে এবং ন্যায্য বণ্টনের নীতি মেনে চলবে।
এই যে একই মূল্যবোধ, একই নৈতিকতা, জাতপাত বা শ্রেণিভেদ অতিক্রম করে মানুষের মর্যাদা প্রতিষ্ঠার চেতনা; এটাই ইসলামী সংস্কৃতির মূল।
মানুষ মানুষ হিসেবে সম্মান পায়, এই নীতিতেই সমাজে নিরাপত্তা আসে। বাংলায় ইসলাম গ্রহণের প্রবণতা এত বেশি হওয়ার কারণও এটিই। এখানে কাউকে জোর করে মুসলমান বানানো হয়নি; বরং মানুষ ইসলামী সংস্কৃতির মানবিক রূপে আকৃষ্ট হয়েছে।
বাংলার ইসলামী সংস্কৃতি বোঝাপড়ায় আমাদের অবস্থা এমন কেন?
আমাদের মনে রাখতে হবে—প্রায় পাঁচশ বছরের এক অবিচ্ছিন্ন রাষ্ট্র কাঠামো মুসলমানরা এই উপমহাদেশে প্রতিষ্ঠা করেছিল। এটি কোনো সাধারণ বিষয় নয়।
ভারতীয় উপমহাদেশে হিন্দু সমাজে দেবদেবীর উপাসনা প্রচলিত ছিল। কিন্তু মুসলমানরা এর বিপরীতে নামাজকে জোরপূর্বক চাপিয়ে দেয়নি। একইভাবে, পারস্যে ইসলাম প্রতিষ্ঠার পরও স্থানীয় সাংস্কৃতিক প্রথাগুলো নিষিদ্ধ করা হয়নি। বরং সবাই যেন নিজের ধর্ম ও সংস্কৃতি পালন করতে পারে, সেই নিশ্চয়তা দেওয়া হয়েছে।
এই প্রেক্ষাপটে মুসলমানরা তৈরি করেছিলেন কমন সামাজিক ক্ষেত্র, যেখানে সবাই অংশ নিতে পারত। যেমন, খাবারের সংস্কৃতিতে বিরিয়ানি এমন এক খাবার, যা মুসলমানদের সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য ধর্মাবলম্বীরও গ্রহণযোগ্য হয়ে ওঠে। শিক্ষাদান, আড্ডা, জিয়াফত, খানকা ও মসজিদ; এসব স্থান ছিল উন্মুক্ত সামাজিক পরিসর, যা পারস্পরিক বন্ধন ও সহাবস্থানকে আরও দৃঢ় করেছে।
এসব কারণেই বাংলায় ইসলামী সংস্কৃতির বোঝাপড়া আমাদের কেমন হওয়া উচিত, সেই নিয়েও ভাবনা জরুরি। মূলধারার ইসলামী সংস্কৃতি কি এদেশীয় মুসলমানের সংস্কৃতি থেকে আলাদা হবে? নাকি মুসলিম বিশ্বের অন্যান্য অঞ্চলের মতোই একরূপ সাংস্কৃতিক আবহ ও এজেন্ডা আমাদেরও অনুসরণ করতে হবে? নাকি বরং ইসলামের সীমারেখার ভেতর থেকেই আমাদের নিজস্ব সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য রক্ষা করা উচিত?
একটি রাষ্ট্র শতাব্দীর পর শতাব্দী টিকে থাকতে পারে কেবল তখনই, যখন তার সংস্কৃতি শক্তিশালী, গভীর এবং জনগণের জীবনের সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকে। তাই ইসলামী সাংস্কৃতিক ধারাবাহিকতাকে আমাদের গভীরভাবে উপলব্ধি, নতুন করে বিশ্লেষণ ও আলোচনা করতে হবে।
পাঁচশ বছরের সেই দীর্ঘ রাষ্ট্র, সাংস্কৃতিক আবহাওয়া, সামাজিক সিলসিলা ও ধর্মীয় সম্প্রীতির যে শক্তি—আমরা আজ তা প্রায় হারিয়ে ফেলেছি। প্রশ্ন হলো—কখন এবং কীভাবে এই ক্ষয় ঘটল?
আমাদের ভালোভাবে বুঝতে হবে, দুইশ বছরের ব্রিটিশ শাসন আমাদের সভ্যতা, সংস্কৃতি ও শিক্ষা ব্যবস্থায় গভীর আঘাত হেনেছিল। প্রথমত, তারা আমাদের স্মৃতি (মেমোরি) ধ্বংস করেছে। আমাদের নিজস্ব শিক্ষা, ইতিহাস ও সংস্কৃতির পরিবর্তে তারা এমন এক শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক কাঠামো প্রতিষ্ঠা করেছে, যা সম্পূর্ণভাবে ঔপনিবেশিক স্বার্থে নির্মিত।
তারা ইসলামী সংস্কৃতির বিপরীতে বিকল্প সাংস্কৃতিক কর্মসূচি তৈরি করেছে এবং সেগুলোকে রাষ্ট্রীয়ভাবে পৃষ্ঠপোষকতা দিয়েছে। ইসলামের সাংস্কৃতিক ভিত্তিকে দুর্বল করার লক্ষ্যে তারা অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের জন্য নতুন উৎসব সৃষ্টি করেছে। আমাদের ভাষাকে বিকৃত করেছে, বিদেশি ভাষা চাপিয়ে দিয়েছে এবং নিজেদের সংস্কৃতিকে “আধুনিকতা”র নামে আমাদের ওপর আরোপ করেছে।
যখন আমরা স্বেচ্ছায় তা গ্রহণ করিনি, তখন তারা শক্তি ও সহিংসতার মাধ্যমে ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়েছে। এর ফলশ্রুতিতে আমরা পরিণত হয়েছি এক আত্মপরিচয়হীন জাতিতে। আমাদের স্মৃতি হারিয়ে গেছে, আমাদের সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার বিলীন হয়েছে, আমরা এক গভীর পরিচয় সংকটে নিপতিত হয়েছি।
আজও সেই সংকট আমাদের মধ্যে বিদ্যমান। আমরা আমাদের ইতিহাস জানি না, আমাদের সংস্কৃতির মূল পদ্ধতি (মেথডোলজি) ও উপকরণ সম্পর্কে অজ্ঞ। আমরা বিশ্বজনীন সংস্কৃতি ও আঞ্চলিক সংস্কৃতির পার্থক্য বুঝি না; আবার আধুনিক পাশ্চাত্য সংস্কৃতি ও ইসলামী সংস্কৃতির মৌলিক পার্থক্য সম্পর্কেও আমাদের জ্ঞান সীমিত।
আমরা আল্লাহর রাসূল ﷺ এর রিসালাত (বার্তা)-এর মূল দায়িত্ব এবং একজন মানুষ (বাশার) হিসেবে তাঁর সাধারণ মানবিক অভ্যাসগুলোর মধ্যে পার্থক্য করতেও ব্যর্থ। এই কারণেই আজ ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকেও আমরা এক গভীর আত্মপরিচয় সংকটে ভুগছি।
অন্যদিকে পাশ্চাত্য সভ্যতা ও ব্রিটিশ একাডেমিয়া, কলকাতাকেন্দ্রিক এক সাংস্কৃতিক উত্থানের মধ্য দিয়ে আমাদের অঞ্চলের সংস্কৃতিকে প্রদর্শনমূলক ও পূজ্য রূপে উপস্থাপন করতে চেয়েছিল। তারা চেয়েছিল, আমরা যেন নিজেদের সংস্কৃতিকে কেবল বাহ্যিক সাজে উপস্থাপন করি, কিন্তু তার ভেতরের আত্মা, দর্শন ও নৈতিক ভিত্তি হারিয়ে ফেলি।
ফলস্বরূপ, আমাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ধীরে ধীরে এক প্রাণহীন প্রদর্শনীতে পরিণত হয়েছে—যেখানে রয়ে গেছে কেবল বাহ্যিকতা, কিন্তু হারিয়ে গেছে ইসলামী সংস্কৃতির সেই আত্মিক ও নৈতিক মহিমা, যা একসময় এই উপমহাদেশকে আলোকিত করেছিল।
তাদের অর্থনীতি, শিক্ষা, প্রশাসন, আইন, পররাষ্ট্রনীতি, এমনকি প্রতিরক্ষা কাঠামো— সবকিছুই ছিল তাদের নিয়ন্ত্রণে। তবে তারা একটি ক্ষেত্রকে আঞ্চলিক আবহের ছোঁয়া দিয়েছিল, আর সেটি হলো সংস্কৃতি। কিন্তু সেটিও প্রকৃতপক্ষে আমাদের সংস্কৃতিকে নিয়ন্ত্রণ ও বিকৃত করার কৌশল মাত্র ছিল। এভাবেই আমাদের ইসলামী সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য— যা একসময় আত্মিক শক্তি, মানবিক ঐক্য ও সামাজিক সংহতির উৎস ছিল— ধীরে ধীরে পরাধীনতার মানসিক শৃঙ্খলে বন্দি হয়ে পড়ে।
তারা সংস্কৃতিকে মূলত ব্রাহ্মণ্যবাদী দৃষ্টিভঙ্গি থেকে চাপিয়ে দেয়। বিভিন্ন চিন্তাধারাকে জোর করে আমাদের সাংস্কৃতিক চর্চার মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে তারা তৈরি করে এক কলকাতা-কেন্দ্রিক সাংস্কৃতিক মানসিকতা। এই উদ্দেশ্যে তারা প্রচুর লেখালেখি করেছে, বড় বড় কবি ও সাহিত্যিক গড়ে তুলেছে, বিশ্ববিদ্যালয়, ইনস্টিটিউট, সংসদ, মিডিয়া ও সংবাদপত্র প্রতিষ্ঠা করেছে, যার ফলে এই ধারাই ধীরে ধীরে আমাদের নিজস্ব আত্মপরিচয়কে বিকৃত ও বিলুপ্ত করে দেয়।
এর ফলস্বরূপ আমরা এমন এক বিভ্রান্ত ধারণায় অভ্যস্ত হয়েছি যে, বাঙালি মুসলমান এক স্বতন্ত্র সত্তা, যা আরব, তুর্কি, ইরানীয়, আফ্রিকান, মালয় বা ইন্দোনেশীয় মুসলমানদের থেকে মৌলিকভাবে আলাদা। অথচ এটি একটি কৃত্রিম ও কলকাতা-কেন্দ্রিক ব্রাহ্মণ্যবাদী চিন্তাধারার ফল, যার ভেতরে ইসলামের প্রকৃত রূহ অনুপস্থিত।
প্রকৃতপক্ষে, এই চিন্তাধারার প্রভাবে এক রূহবিহীন ইসলাম তৈরি হয়েছে, যা মুসলমানদের সংস্কৃতির আত্মা থেকে বিচ্ছিন্ন করেছে। তারা চেয়েছিল, মুসলমানদের পোশাক, গান, খাবার, পারিবারিক সম্পর্ক ও জীবনযাপন যেন ব্রিটিশ উপনিবেশ বা কলকাতার ধ্যানধারার আদলে গড়ে ওঠে। অথচ আমাদের পাঁচ শতাব্দীর নিরবচ্ছিন্ন সাংস্কৃতিক সিলসিলা আজ ভুলে যাওয়া হয়েছে।
অন্যদিকে, এক শ্রেণির মুসলমান আবার ইসলামী সংস্কৃতির মূল ধারণা না বুঝে আরবদের সংস্কৃতিকেই ইসলামী সংস্কৃতি হিসেবে পুরোপুরি গ্রহণ করার চেষ্টা করেছে। কিন্তু এই দুই প্রান্ত, কলকাতাকেন্দ্রিক ব্রাহ্মণ্যবাদী সংস্কৃতি ও অনুলিপিকৃত আরবীয় সংস্কৃতি; কোনোটিই ইসলামের প্রকৃত সাংস্কৃতিক কেন্দ্র নয়।
তাই বাংলায় ইসলামী সংস্কৃতির সঠিক বোঝাপড়া এখন অত্যন্ত জরুরি।
বাংলায় ইসলামী সংস্কৃতির নমুনা
এই আলোচনায় এটা স্পষ্ট যে, ইসলামী সভ্যতা স্থানীয় সংস্কৃতিকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিতো। সেই ধারাবাহিকতায় বাংলায়ও এর প্রমাণ পাওয়া যায়। নিচে বাংলা অঞ্চলের প্রেক্ষিতে কয়েকটি ক্ষেত্রে ইসলামী সভ্যতার সাংস্কৃতিক বিশ্বজনীনতার কতক উদাহরণ তুলে ধরা হলো।
০১. ভাষা ও সাহিত্য
আমাদের এই অঞ্চলের ভাষার ধারাবাহিকতায় পাল আমলে যে বাংলা ছিলো, তা একেবারে ধ্বংস করে দিয়েছিলো সেনরা। বাংলার পরিবর্তে সেনরা সংস্কৃত-কে সামনে এনেছিলো। এমনকি, বাংলা ভাষাকেই তারা নিষিদ্ধ করে দিয়েছিলো। মুসলিমরা এসে সে বাংলাভাষাকে আবারো গতিশীল করে দিয়েছিলো। শুধু বাংলাই নয়, মুসলিমরা এতোটা উদার ছিলো যে, বাংলা ও সংস্কৃত—দুই ভাষাকেই একইসাথে সামনে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিলো।
বাংলার সুলতানরা উদারভাবে হিন্দু কবি সাহিত্যিকদের পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। সুলতান জালালউদ্দীন মোহাম্মদ শাহ কবি বৃহস্পতি মিশ্রকে “রায় মুকুট” উপাধী প্রদান করেন। হোসেন শাহী বংশের সুলতানদের উদার পৃষ্ঠপোষকতায় হিন্দু ও সাহিত্যিকরা বাংলায় “রামায়ণ” ‘মহাভারত’ অনুবাদ করেন। সুলতানি আমলে সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যেরও অসামান্য উন্নতি হয়। বাংলার সুলতান আলাউদ্দীন হোসেন শাহের মন্ত্রী রূপগোস্বামী ২৫টি সংস্কৃত গ্রন্থ রচনা করে সংস্কৃত ভাষাকে সমৃদ্ধ করেন। বিজয়গুপ্ত, বিপ্রদাশ, মালাধর, পরমেশ্বর কবীন্দ্র, শ্রীকর নন্দীর রচনার দ্বারা ঐ যুগে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রভূত উৎকর্ষ সাধিত হয়েছিলো। মুঘল শাসনামলেও হিন্দু-মুসলিম সম্পর্ক আরো জোরদার হয়। সাহিত্য সংস্কৃতি ক্ষেত্রে বাংলা-সংস্কৃত ভাষার উন্নতিতে মুঘলরা যথেষ্ট অবদান রাখে। এসবই বাংলায় হিন্দু মুসলিম শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের প্রমাণ করেন। অতএব, এটা সত্য যে, মুসলিম সুলতানদের জামানায় বাংলা ভাষার বিশেষ বিকাশ ঘটেছিলো। সুলতানদের সাহায্য ছাড়া বাংলা ভাষা আজকে সংস্কৃত ভাষার মতো একটি মৃত ভাষায় পরিণত হতো।
বাংলা ভাষার প্রতি মুসলমান সুলতানদের উদার পৃষ্ঠপোষকতার প্রশংসা করতে গিয়ে ড. দীনেশ চন্দ্র সেন বলেন,
❝ব্রাহ্মণগণ প্রথমদিকে বাংলা ভাষা গ্রহণ ও প্রচারের বিরোধী ছিলো। কৃত্তিবাস ও কাশীদাসকে তারা ‘সর্বনেশে’ উপাধি প্রদান করেছিলো। যদি হিন্দু রাজাগণ স্বাধীন থাকতো, তাহলে কদাচিৎ বাংলা ভাষা তাদের দরবারে প্রবেশ করার সুযোগ লাভ করতো। আমাদের বিশ্বাস, মুসলমান কর্তৃক বঙ্গবিজয়ই বঙ্গভাষার এই সৌভাগ্যের কারণ হয়ে দাড়িয়েছিলো। মুসলমানগণ ইরান, তুরান প্রভৃতি যে স্থান হতেই আসুক না কেনো, এ’দেশে এসে তারা সম্পূর্ণরূপে বাঙ্গালি হয়েছেন।❞
আর প্রখ্যাত ঐতিহাসিক স্যার যদুনাথ সরকার বলেন, ❝দিল্লি সাম্রাজ্যের অধীনে শান্তি ও আর্থিক উন্নতির ফলস্বরূপই দেশীয় ভাষা সাহিত্যের সমৃদ্ধি ঘটেছে।❞
ড. লক্ষ্মীধর বলেন,
❝আমাদের এটা ভুললে চলবে না যে, দেশীয় ভাষা হিন্দিকে সর্বপ্রথম মুসলমানগণই সাহিত্য সৃষ্টির উদ্দেশ্যে ব্যবহার করেছেন। অথচ আমরা জানি যে, ব্রাহ্মণগণ ইতর ভাষা বলে এই ভাষাকে অবহেলা করেছেন।❞
মুসলিমরা যে এভাবে বাংলা ও সংস্কৃতিকে পুনরায় সামনে নিয়ে এলো, তা আবার ধ্বংস হয়ে যায় পলাশীর বিপর্যয়ের পর। ইংরেজদের “ডিভাইড এন্ড রূল” পলিসির ক্ষেত্রে এই ভাষার বিনির্মাণটাকেই কাজে লাগিয়েছে ইংরেজরা। ম্যাক্স মুলার ভারতের হিন্দুদেরকে আর্য বলে তাদের মাঝে সেনদের সেই পুরাতন মানসিকতা তুলে এনেছিলো। যার ফলে বহমান যে বাংলা ছিলো, সেটাকে সমূলে ধ্বংস করে সংস্কৃতকে জোর করে বাংলায় প্রবেশ করানো হয়েছে, যেনো মুসলিম শাসনামলের বাংলা এবং হিন্দুদের নতুন সংস্কৃত বাংলার মাঝে পার্থক্যের সৃষ্টি হয়; আর শেষমেশ এ-নিয়েও যেনো হিন্দু-মুসলিম দ্বন্দ্বের সূচনা হয়। এবং, হয়েছেও তাই-ই।
নতুন এই বাংলাকে প্রতিষ্ঠিত করতে ইংরেজরা প্রতিষ্ঠা করে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ; নিজেরাই লিখেছে বাংলা ভাষার ব্যাকরণ, যেসব ব্যাকরণের মাধ্যমেই নতুন বাংলার সূচনা করা হয়। কেননা, এসব ব্যাকরণে সংস্কৃতকে সামনে রেখেই বাংলার নতুন রূপ দেওয়া হয়। আর এসবকে পরিচিত করাতে কলকাতাকেন্দ্রিক বুদ্ধিজীবী সমাজকে কাজে লাগিয়েছে ইংরেজরা; এবং নতুন এই বাংলাকে লেখ্য ভাষায় রূপ দিয়েছে কলকাতার সাহিত্যিকরা। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের লেখাগুলো পড়লেই এসব বুঝা যায়। ঠিক এজন্যই কবি নজরুল ইসলাম, ফররুখ আহমদ এবং কবি গোলাম মোস্তফার চেয়েও এই জেন-জি প্রজন্ম রবী-শরৎ-বঙ্কিম-বিভূতিদেরকে ভালোভাবে চিনে।
এখানে এই প্রশ্নও উঠে আসে যে, ৫০০ বছর আগের মহাকবি আলাওল-এর বহমান বাংলাকে আমরা যেভাবে বুঝি না, তেমনি আমরা কেন প্রায় ২৫০ বছর আগের ঈশ্বরচন্দ্র ও বঙ্কিমচন্দ্রকে বুঝি না? ভাষা যদি বহমান হয়, তাহলে আলাওলেরও ২৫০ বছর পরের বাংলা-তো অনেকটাই বুঝতে পারার কথা। কিন্তু, তা কেন হয় না?
যাকগে, এখান থেকে এই সিদ্ধান্তই পাওয়া গেলো যে, ইসলামী সভ্যতায় ভাষার সংস্কৃতিকে যদি বিশ্বজনীন হিসেবে গ্রহণ করা না হতো, তাহলে হয়তো আমাদের এই বাংলাকে এভাবেই পেতাম না; অথবা হয়তো একেবারেই হারিয়ে যেতো।
০২. উৎসব ও গ্রামীণ সংস্কৃতি
ভারত ও বাংলার উৎসব সংস্কৃতি কতোটা শক্তিশালী ছিলো তা ইতিহাসই সাক্ষ্য দেয়।
যেমন- জহির উদ্দিন বাবর, ইলতুৎমিশ ২০% মুসলিম জনসংখ্যা নিয়ে গোটা উপমহাদেশ চালিয়েছেন, তার অন্যতম ভিত্তি ছিল স্থানীয় সাংস্কৃতিক বলয় ও তার উৎসব গুলো। ব্রিটিশরা এসে যখন দেখল কোনভাবেই জনগণ থেকে ইসলামের প্রাণসত্তাকে সরানো যাচ্ছে না, বলয়কে নষ্ট করা যাচ্ছে না, তখন তারা বুঝতে পারলো শুধু জ্ঞান, ক্ষমতা, অর্থনীতি, নষ্ট করলেই হবে না বরং বিকল্প সাংস্কৃতিক ধারা তৈরি করতে হবে। তাই তারা বঙ্কিম, বিবেকানন্দ, ঈশ্বরচন্দ্রদের দিয়ে মিরাজ, মিলাদুন্নবী ইত্যাদির বিপরীতে স্বরস্বতী, হলি, দেওয়ালী উৎসবকে ব্যাপকভাবে হাইলাইট করতে শুরু করলো, মক্কা বিজয় দিবসের দিন থার্টি ফার্স্টনাইট জাতীয় ভোগবাদী উৎসব নিয়ে এলো।
মুসলিম বাংলার গ্রামীণ সংস্কৃতিতে রমজান, ঈদ, জন্ম, আকিকা, শবে বরাত, শবে মেরাজ, ঈদে মীলাদুন্নবী, মহররম বেশ আয়োজনের সাথে পালিত হতো।
এম এ রহিমের ভাষায়,
“ঈদে মীলাদুন্নবীতে নবাব মুর্শিদকুলী খান রবিউল আউয়ালের প্রথম বারোদিন ভোজের আয়োজন করতেন। পুরো মুর্শিদাবাদ আলোকমালায় সজ্জিত করতেন। সেনাবাহিনী দিয়ে তোপধ্বনি দিতেন। গুজরাটের সুলতান দ্বিতীয় মুজাফফর আলেম ওলামাদরে আপ্যায়ন করতেন। পরবর্তী বছরের জীবন ধারনের খরচের জন্য আলেম ও বিজ্ঞজনদের বিশাল অঙ্কের মুদ্রা উপহার দিতেন। গুজরাটের সুলতান দ্বিতীয় মাহমুদ প্রথম বারোদিন আলেমদের নিয়ে সীরাত চর্চা করতেন। সীরাত চর্চার পাশাপাশি উন্মুক্ত ভোজের আয়োজন করতেন। তিনিও বিদ্বান ও অতিথিদের জন্য এতোবেশি পরিমাণ উপহার দিতেন যে, যেন ওলামায়ে কেরামগণ পরবর্তী বছর স্বাচ্ছন্দ্যে জীবন কাটাতে পারে।”
শবে বরাত নিয়ে এম এ রহিম তার বইয়ে বলেন, “উপমহাদেশের মুসলমানগণ শবে বরাত বহু আচার অনুষ্ঠান ও আমোদ স্ফূর্তির ব্যবস্থা করে এবং অসাধারণ আড়ম্বরের সঙ্গে তা উদ্যাপন করতো। আলোকসজ্জা ও আতশবাজি পোড়ানো এই উৎসবের একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য অঙ্গ ছিল। শামস সিরাজ আফিফের বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, সুলতান ফিরোজ শাহ তুগলক চারদিনব্যাপী এই উৎসব উদ্যাপন করতেন এবং এতবেশি আতশবাজি পোড়াতেন যে, রাত্রিকালও প্রকাশ্য দিবালোকের রূপ ধারণ করত। সমসাময়িক উৎসগুলো থেকে জানা যায় যে, শের শাহের একজন বিখ্যাত সেনাপতি ও তার জ্যেষ্ঠ পুত্র আদিল খানের সমর্থক খাস খান ফতেহপুর সিকরীর শেখ সলিম চিশতীর সঙ্গে শব-ই-বারাতের দিন সারারাত এবাদত বন্দেগি করেন। ‘বাহারিস্তান-ই-গায়েবীতে’ এই উৎসব উদযাপনের উল্লেখ পাওয়া যায়। বাংলার নবাবগণ বিরাট জাঁকজমকের সঙ্গে ‘শব-ই-বারাত’ উদ্যাপন করতেন। বাড়িঘর আলোকমালায় সজ্জিত করা হতো এবং নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলে মসজিদে ও বাড়িতে সারারাত নামাজ অদোয় করতেন। ভোজানুষ্ঠানের ব্যবস্থা হতো দ্রব্যসামগ্রী বিতরণ করা হতো। আতশবাজির প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হতো।”
রমজান নিয়ে বলেন, “উপবাস, সংযম, প্রার্থনা ও সামাজিক সম্মেলনের সময় হিসেবে সে যুগের মুসলমানগণ ‘রমজান’ পালন করত। তারা রমজানকে পবিত্র ও মঙ্গলজনক মাসরূপে গণ্য করত এবং খুশির সঙ্গে একে স্বাগত জানাত। বাংলায় মুঘল সৈন্যদের রমজান পর্ব পালনের উল্লেখ করে মীর্জা নাথান বলেন, ‘রমজান মাসের শুরু থেকে এর শেষদিন পর্যন্ত ছোটবড় প্রত্যেকে প্রত্যহ তার বন্ধুর তাঁবুতে মিলিত হতো। এটা একটা স্বাভাবিক রীতিতে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল যে প্রত্যেক দিন সকলে পর্যায়ক্রমে একজন অভিজাত বন্ধুর তাঁবুতে তাদের সময় কাটাত। সেই অনুসারে শেষের দিন রাত্রে মুবারিজ খানের দেওয়া ভোজের পালা ছিল। সকলে সেদিন তার তাঁবুতে সময় কাটায়’।”
ঈদুল ফিতরে নিয়ে মুসলিম বাংলার উৎসবমূখর আয়োজন নিয়ে বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস বইয়ে আছে, “সেই যুগে খুব আমোদ-স্ফূর্তির সঙ্গে ঈদের নতুন চাঁদকে স্বাগত জানানো হতো। মীর্জা নাথানের ভাষায় এটা বর্ণনা করা যেতে পারে। তিনি লিখেছেন, ‘দিনের শেষে সন্ধ্যা সমাগমে নতুন চাঁদ দেখা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রাজকীয় নাকারা বেজে উঠতো এবং গোলন্দাজ সেনাদলের সকল আগ্নেয়াস্ত্র থেকে ক্রমাগত তোপ দাগানো হতো। রাত্রির শেষভাগে, কামানের অগ্নি উদগীরণ শেষ হতো এবং এর পর শোনা যেতো ভারি কামানের আওয়াজ। এটা ছিল দস্তুরমতো একটা ভূমিকম্প’।”
“এথেকে বুঝা যায়, ঈদের আগমনে মুসলমানরা কতটা খুশি হতো। ঈদের দিনে সমস্ত মুসলমান আনন্দস্ফূর্তিতে মসগুল থাকত। স্ত্রী পুরুষ, বালক বালিকা নির্বিশেষে প্রত্যেকে নতুন এবং উৎকৃষ্ট কাপড় পরিধান করত। চমৎকার পোশাক পরিচ্ছদে সজ্জিত হয়ে মুসলমানগণ প্রভাতে ঈদগাহ ময়দান বা ঈদের নামাজের স্থানে শোভাযাত্রা করে গমন করত। অবস্থাপন্ন ব্যক্তিরা পথেপথে টাকা পয়সা ও উপহার দ্রব্য ছড়িয়ে দিত এবং সাধারণ অবস্থার মুসলমানগণ গরিবদেরকে ভিক্ষা দিত। ‘নওবাহার-ই-মুর্শিদকুলী খানী’ গ্রন্থের লেখক আজাদ হোসেন বিলগ্রামীর বর্ণনায় এর উল্লেখ রয়েছে। তিনি বলেন যে, নবাব শুজাউদ্দিনের অধীনে ঢাকার সহকারী শাসনকর্তা ‘ঈদগাহ’ ময়দানের দিকে শোভাযাত্রা করে যাওয়ার সময় দুর্গ থেকে এক ক্রোশপথে প্রচুর পরিমাণে টাকাপয়সা ছড়িয়ে যেতেন। এক বড় জামাতে মুসলমানগণ তাদের নামাজ পড়ত এবং আনন্দ আবেগে একে অন্যকে উৎসাহের সঙ্গে অভিবাদন জানাতো। গোলাম হোসেন তাবাতাবাঈয়ের বর্ণনায় ঈদ উৎসবে মুসলমানদের খুশি ও আনন্দস্ফূর্তির বিষয় প্রকাশ পেয়েছে।”
আর কুরবানীর ক্ষেত্রে, মুসলমানগণ ঈদুল আজহার প্রভাতে সুন্দর কাপড়-চোপড় পরিধান করে এবং ‘তাকবীর’ উচ্চারণ করতে করতে ঈদগাহ ময়দানের দিকে শোভাযাত্রা করে গমন করতো। সেখানে জামাতে তারা নামাজ আদায় করে এবং ভ্রাতৃত্বপূর্ণ মনোভাব নিয়ে আনন্দ প্রকাশ করতো, পরস্পরকে আলিঙ্গন করতো ও সম্ভাষণ জানাতো। অতঃপর তারা গৃহে প্রত্যাবর্তন করে এবং তাদের সাধ্যানুসারে তারা কোনো পশু, যেমন, গরু, ছাগল, মহিষ বা উট কোরবানি করতো। তারা গরিব-দুঃখী, বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যে মাংস বিতরণ করে এবং গৃহে ভোজের অনুষ্ঠান করতো। প্রত্যেক গৃহ ভোজানুষ্ঠান ও আনন্দ ‘স্ফূর্তিতে মুখরিত হয়ে উঠতো এবং সকল গৃহে আদর আপ্যায়ন চলতো। শুভেচ্ছা বিনিময়ের জন্যে তারা বাড়ি বাড়ি ঘুরে বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয় স্বজনদের সঙ্গে মিলিত হতো এবং এই মহান উৎসবে তারা সকলে একত্রে আনন্দ করতো। মীর্জা নাথান লিখেছেন যে, “নামাজান্তে খতিবের খুতবাহ পাঠ শেষ হলে, লোকেরা তাকে কাপড়-চোপড় ও টাকাপয়সা উপহার দেয়। গরিব দুঃখীদের সাহায্যের জন্য তার সম্মুখে টাকাপসয়া ছড়িয়ে দেওয়া হতো। দুঃস্থ লোকদের অনেকে এর দ্বারা তাদের অভাব দূর করে সুখি হতো। এই দিনে বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়-স্বজন ও রাজকর্মচারীগণ একে অন্যের জায়গায় গমন করতো এবং ঈদের শুভেচ্ছা জানাতো।
এছাড়াও, বিয়ের অনুষ্ঠান হতো খুবই জাঁকজমকভাবে। হিন্দু-মুসলিম দুই জাতি তাদের রীতিনীতি অনুযায়ী বিবাহের কাজ সম্পন্ন করতো। পোশাক-পরিচ্ছদেও শালীনতা বজায় থাকতো। এক্ষেত্রে মুসলিমরা হিন্দুদেরকে জোর করতো না। অতএব, মূল কথা হচ্ছে, বাংলায় অঞ্চলে ইসলামী সভ্যতা প্রতিষ্ঠিত হলেও স্থানীয় সংস্কৃতিকে কখনই দূরে ঠেলে দেয়নি। স্থানীয় আয়োজনের ধরনের সাথে মুসলিমরাও নিজেদেরকে খাপ খাইয়ে নিয়েছিলো।
০৩. খাদ্য
ড. এম এ রহিম বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতি ইতিহাস বইয়ে এই অঞ্চলের মুসলিমদের খাদ্যের আলোচনা করতে গিয়ে বলেন,
“মুসলমান সমাজের উচ্চশ্রেণী সম্পর্কে আলোচনায় খাদ্যদ্রব্য ও পোশাক-পরিচ্ছদে তাদের বিলাসিতার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। সিবাস্তিয়ান মানরিক এবং চীনা দূতগণের বর্ণনা থেকে মুসলমানদের খাদ্য সম্বন্ধে কিছুটা আভাস পাওয়া যায়। তাদের খাবার টেবিলে মুরগী, ভেড়া, গরু প্রভৃতির মাংসের তৈরি বিভিন্ন প্রকারের খাদ্য পরিবেশন করা হতো। অনেক রকমের মিষ্টি ও ফলমূল খাদ্য-তালিকার অন্তর্ভুক্ত ছিল। শসা, লেবু, মুলা, কাঁচা লঙ্কা ইত্যাদির তৈরি নানা জাতীয় আচার ছিল মুসলমানদের খাদ্যের বিশিষ্ট অঙ্গ।”
“সিবাসতিয়ান মানরিক বলেন, এগুলো ক্ষুধা বৃদ্ধি করত এবং আবার খাবারের দিকে আকৃষ্ট করতো। হিন্দুরা এ ধরনের উপাদেয় খাদ্য প্রস্তুত করতে এবং ক্ষুধা উদ্রেকের জন্য আচারের ব্যবহার জানত না। হিন্দুদের ভোজ ও সাধারণ খাদ্যদ্রব্যের বর্ণনায় কোথাও আচারের কোনো উল্লেখ দেখা যায় না।বাংলা সাহিত্যে খাদ্য সম্বন্ধে বহু উল্লেখ আছে। জানা যায় যে, বাংলার মুসলমানরা মুরগী, মেষমাংস ও অন্যান্য মাংসের উপাচার পছন্দ করতো।”
“বাঙ্গালি মুসলমানদের খাদ্য হিসেবে রুটিরও উল্লেখ আছে। তাছাড়া মাছ ও শাক-সবজি লোকের সাধারণ খাদ্য ছিল। বাংলার নদ-নদী ও জলাশয়ে নানা জাতীয় মৎস্য প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যেতো। এর মাটিতে জন্মাত বিভিন্ন প্রকারের শাক-সবজি। তাতে করে, এমনকি, মুসলমানদের মধ্যে সাধারণ লোকেরা ও তাদের খাবারের জন্য রকমারি মাছ, শাক-সবজির তরকারি প্রস্তুত করতে পারতো।”
“খিচুড়ি (সাধারণত ঘি বা তেলের সঙ্গে চাল ও লঙ্কা দিয়ে প্রস্তুত খাদ্যদ্রব্য) ছিল লোকের প্রিয় খাদ্য। এমনকি, উচ্চশ্রেণীর লোকদেরও খিচুড়ির প্রতি বিশেষ আকর্ষণ ছিল। বার্ণিয়ারের মতে, খিচুড়ি সম্রাট শাহজাহানের খুবই প্রিয় ছিল। ইউসুফ আলীর বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, নবাব আলিবর্দী খান ও তাঁর আমির ওমরাহ প্রায়ই তৃপ্তির সহিত খিচুড়ি খেতেন।”
“নানা প্রকার মাংসের উপাচার ও নানা রকমের আচার মুসলমানদের খাদ্যের, বিশেষ করে, উৎসব অনুষ্ঠানে খাদ্য তালিকার অন্তর্ভুক্ত ছিল। উৎসবাদিতে, যেমন বিবাহ ইত্যাদি উপলক্ষে হিন্দুরা সাধারণত মাছ, শাক-সবজি ও মিষ্টান্ন তৈরি করত। হিন্দুদের ভোজে মিষ্টান্ন ও দধি ছিল খাদ্য তালিকার একান্ত প্রয়োজনীয় উপাদান। ‘মনসামঙ্গল’ কাব্যগুলোতে লক্ষ্মীন্দরের বিয়ের ভোজের বর্ণনা থেকে উৎসবাদি উপলক্ষে হিন্দুদের খাবার সম্বন্ধে আভাস পাওয়া যায়। সিবাসতিয়ান মানরিক ও চীনা দূতদের বর্ণনানুসারে, মুসলমানদের খাদ্য তালিকার সঙ্গে এর তুলনা করা যেতে পারে।”
বাংলায় মুসলিম শাসনামলে যেসব খাবার আবিষ্কার, প্রচলন বা বিশেষ রূপে বিকশিত হয়েছে—তার সংখ্যা অনেক। তুর্কি, আফগান, আরব, পারসিক, মুঘল ও মধ্য এশীয় রন্ধনশৈলীর প্রভাবে উপমহাদেশের খাবারে এক বিশাল পরিবর্তন আসে।
বাংলা অঞ্চলে মুসলিমদের আনিত বা উন্নত করা খাবারের মধ্যে রয়েছে,
- ১. বিরিয়ানি (ঢাকাই/কাচ্চি)। ঢাকার কাচ্চি বিরিয়ানির মূল শিকড় মুঘল রন্ধনশৈলীতে। মুসলিম নবাবরা বিশেষভাবে এটিকে জনপ্রিয় করেন।
- ২. কাবাবের বিভিন্ন ধরন। যেমন- সিক কাবাব, বটি কাবাব, টিক্কা কাবাব, শামী কাবাব, রেশমি কাবাব; এসবই তুর্কি–পারসিক উৎস থেকে এসে বাংলায় জনপ্রিয় হয়।
- ৩. নেহারি। মূলত দিল্লি–লখনউ থেকে বাংলায় আসে এবং মুসলিম শাসনকালে নবাবদের টেবিলের খাবার হিসেবে পরিবেশিত হতো।
- ৪. মোরগ পোলাও/চাপলি পোলাও। মুঘল দরবারে পোলাওয়ের বিভিন্ন রূপ ছিল। এর বাংলা রূপ হলো মোরগ পোলাও
- ৫. হালিম। আরব/পারস্যে এর উদ্ভব হয়েছে। মুসলিম শাসনকালেই বাংলায় বিশেষভাবে ছড়িয়ে পড়ে।
- ৬. কোরমা/কোর্মা। পারসিক “কুরমাহ” থেকে এসেছে। মুসলিম শাসকরা এর দুধ-বাদাম-ঘৃতসমৃদ্ধ বিলাসী রূপ প্রতিষ্ঠা করেন।
- ৭. রোস্ট (বাংলা মুসলিম স্টাইলে)। নবাবি-আওয়াধি রান্নার প্রভাবে বাংলায় রোস্টের নিজস্ব রূপ তৈরি হয়।
- ৮. শাহী টুকরা/শাহী টোস্ট। পারসিক ‘শিরমাল–ডেজার্ট’ থেকে রূপান্তরিত। এটি ছিলো মুসলিম নবাবদের প্রিয় মিষ্টি।
- ৯. ফিরনি। আরব–পারসিক দুধ-চালভিত্তিক ডেজার্ট থেকে এই অঞ্চলে অভিযোজিত।
- ১০. সেমাই/শিরখুরমা। আরবীয় সেমোলিনা ডেজার্টের মতো করে তৈরি হতো; মুসলিম শাসনামল থেকেই ঈদের প্রধান খাবার হিসেবে পরিচিত।
- ১১. বাকরখানি। ঢাকায় নবাব বংশের আমলে এটি তৈরি হয়।কাশ্মীর-লখনৌ-এর নান-বাইদের হাত ধরে পরিচিতি লাভ করে।
অর্থাৎ, ইসলাম উন্নত সাংস্কৃতিক উপাদান গ্রহণ করেছে। বাংলায় বা ভারতীয় উপমহাদেশে কোনো জিনিস না থাকলেও পারস্যে থাকলে, যদি তা ইসলামী নীতির বিরোধী না হয়, তবে সেটি এখানেও গ্রহণ করা হয়েছে। উদ্দেশ্য ছিল মানুষের জীবনমান ও সাংস্কৃতিক মান উন্নত করা।
মোদ্দাকথা হচ্ছে, স্থানীয় খাবার সংস্কৃতির পুরোটাই যেমন ইসলামী সভ্যতায় জারি ছিলো, তেমনি অন্যান্য অঞ্চলের স্থানীয় খাবারও এখানে এসে পরিচিত হয়ে ইসলামী সভ্যতায় খাদ্য সংস্কৃতিতে অন্তর্ভূক্ত হয়েছে। তবে এখানে বলাই বাহুল্য যে, হারাম খাবারের বিষয়গুলো তো অবশ্যই পরিত্যাজ্য।
০৪. সংগীত
মুসলিম শাসনামলে বাংলা সংগীত তিনটি দিক থেকে পরিবর্তিত হয়। যথা,
- (ক) মধ্য এশীয়–পারসিক সুরের প্রভাব।
এর ফলে তুর্কি, পারসিক, আরবীয় সুর ও রাগ-রাগিনীর ধরণ বাংলায় প্রচলিত হতে থাকে। পারসিক মাহফিল, দরবারি সংগীত, সুফি সঙ্গীত—এসব বাংলায় নতুন রূপে গড়ে ওঠে। - (খ) কবিতা–গান–দর্শনের সংমিশ্রণ।
মুসলিম শাসকেরা কবিতা, সঙ্গীত, মুশায়েরা, কীর্তন-সদৃশ কণ্ঠসঙ্গীতকে উৎসাহ দিতেন। ফলে বাংলা কবিগান, মুর্শিদী, মারফতি, বাউলধারা—এসব এক নতুন বিকাশ লাভ করে। - (গ) সুফি সঙ্গীতের আগমন।
দরবেশ–সুফিদের মাধ্যমে কাসিদা, হামদ, নাত, গওয়ালিবর্ণী জিকির, এমনকি চিশতি ও সুফি দরবারের সঙ্গীতধারা বাংলায় প্রতিষ্ঠা পায়। বাংলার ফোক গানের অর্ধেক সুফি-মুসলিম প্রভাবে গড়া—এটা ইতিহাসে প্রতিষ্ঠিত সত্য। কাজী নজরুল ইসলাম, দুলাল শাহ, মজনু শাহ, কুতুবুদ্দিন, আউল শাহ—এরা কবিগান, পালাগান, মারফতি গানকে চালিত করেছেন।
এরপর, মুসলমানদের সমাজে সংগীতের গুরুত্বের কারণে সংগীতপ্রীতি দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যথা,
- (১) রাজদরবার ও নবাবি দরবারে সংগীত।
এটি ছিলো বাংলার সুলতান, মুঘল সুবেদার, নবাবদের দরবারে সংগীত ছিল রাজকীয় বিনোদনের অংশ। তারা দাদরা, ঠুমরি, গজল, কাওয়ালী, দরবারি রাগ, কিরানা, রাম্পুর–সাহাসওয়ান ঘরানা-কে বিশেষভাবে পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। বাংলার নবাব সিরাজউদ্দৌলার দরবারেও সঙ্গীতজ্ঞদের বিশেষ মর্যাদা ছিল। - (২) সুফি-দরবেশদের সমাজে সংগীত।
এসব সংগীত ছিল আধ্যাত্মিক সাধনার অংশ। চিশতিয়া, কাদেরিয়া, সুফি দরবেশরা সংগীতকে মানুষের অন্তর জাগ্রত করার মাধ্যম হিসেবে দেখতেন। সুফিদের অবদানে বাংলায় মারফতি গান, মুর্শিদী গান, নবী-বন্দনা, কাওয়ালী ও ধর্মীয় জিকিরের সুরধারা ধারাগুলো বিকশিত হয়। বাংলায় মুসলমানদের বৃহৎ একটি অংশ এই গানগুলোকে ধর্মীয়, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক চর্চার সঙ্গে জড়িত বলে মনে করতো।
বাদ্যযন্ত্রে মুসলমানদের অবদান নিয়ে বলতে গেলে তাদের কয়েকটি অবদানের কথা সামনে রাখতে হয়। যথা,
- (১) নতুন বাদ্যযন্ত্র উপহার বা প্রচলন।
শুরুতেই আসবে তবলার কথা। তবলা আজ সারা ভারত–বাংলার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বাদ্যযন্ত্র। ইতিহাস অনুযায়ী এটি মধ্য এশীয় মুসলিম বাদ্যযন্ত্র “তব্বল” থেকে এসেছে। তবলার পেছনে আমীর খসরু (১৩শ শতক)–এর অবদান সবচেয়ে আলোচিত। এরপর আসবে সর্মিন্দল বা সেতার। সেতার শব্দটি “সেহ-তার” (পারসিক: তিন তার) থেকে এসেছে। মুসলমান সঙ্গীতজ্ঞদের হাত ধরেই এই যন্ত্রটি ভারতীয় রূপ পায়। তৃতীয়ত, রুদ, তানপুরা বা রুবাব। মধ্য এশীয় মুসলিম সুরে ব্যবহৃত এই যন্ত্রগুলি বাংলা-মুসলিম দরবারে জনপ্রিয় হয়। - (২) বিদ্যমান যন্ত্রের উন্নয়ন।
মুঘল দরবারের উস্তাদরা সরোদ, সারেঙ্গি, তানপুরা—এসবকে পরিশীলিত করে তোলেন। তারের সংখ্যা বৃদ্ধি, টোনের গাম্ভীর্য, মৃদু সুরের পরিশুদ্ধতা—এসব উন্নয়ন মুসলিম উস্তাদদের অবদান। - (৩) যন্ত্রসঙ্গীতে নতুন ঘরানা তৈরি।
মুসলিম উস্তাদরা নতুন নতুন, যেমন- গয়তরী (গায়েকী) আঙ্গ, মীন্ড-যুক্ত বাদন, মুঘলাই আলাপ, দরবারি স্টাইল ইত্যাদি বাদন-শৈলী সৃষ্টি করেন। এই শৈলীগুলোই পরবর্তীতে ভারতীয় ক্লাসিক্যাল সঙ্গীতের মূল ভিত্তিতে স্থান পায়। আবার, দরবারি সঙ্গীতের ঘরানায় বাংলায় মুসলমান সঙ্গীতশিল্পীরা পাটিয়ালা ঘরানা ও রাম্পুর-সাহাসওয়ান ঘরানা তৈরি করেন। বিশনপুর ঘরানাতে মুসলিম উস্তাদদের প্রভাব ছিল বিশাল। এগুলোই পরে ভারতীয় শাস্ত্রীয় সঙ্গীতকে স্থায়ী কাঠামো দেয়। - (৪) রাগ-রাগিনীর নতুনত্ব আনয়ন।
বাংলায় মুসলমানরা মালকোষ, ইয়ামন, দারবারি কানাড়া, কৌশিকি, মালহার, তোড়ি ইত্যাদি রাগ উন্নত করে তোলেন। এসব রাগ মধ্য এশীয় প্রভাবে সমৃদ্ধ ও জনপ্রিয় হয়।
ইসলামী সংস্কৃতির সাথে যেহেতু সুফী ঘরানাটা বেশ ভালোভাবে জড়িত, তাই এটা নিয়ে দুয়েকটা কথা বলা প্রয়োজন। মুসলিম শাসনামলে বাংলায় সুফি সাধক, দরবেশ, ফকিরদের মাধ্যমে যে সংগীতধারা গড়ে ওঠে, তাকেই সাধারণত বাংলার সুফি সঙ্গীত বলা যায়। এই সঙ্গীত মূলত পারসিক–আরবি আধ্যাত্মিক কবিতা, ইসলামি দর্শন, এবং বাংলার লোকজ সুরের এক অসাধারণ মিশ্রণ। ইশকে-মাজাজি, ইশকে-হাকিকি, নফসের পরিশুদ্ধি, মানবতার ধর্ম ইত্যাদি এসব গানের মূল প্রাণ।
শাহ জালাল ইয়েমেনী, শাহ নেসার বাহাদুর, শিকার সুলতান, দাতা কর্নি—এদের মতো বহু সুফি বাংলায় সুফি সঙ্গীত নিয়ে আসেন। তাঁরা জিকির, কাওয়ালী, হামদ-নাত, ফারসি মর্শিয়া, রব্বানি কবিতা–এসব সুরধারা সামনে আনেন। এরপর সময়ে সময়ে বাংলার লোকগানের সাথে সুফি দর্শনের মেলবন্ধন ঘটে। গ্রামবাংলার পালাগান, বাউল সুর, ঢোল-একতারা—এসবের সঙ্গে সুফিরা তাওহিদ, ইশক, নফস, পরকাল মুর্শিদ–ভক্তি মিশিয়ে দেন। ফলে তৈরি হয় বাংলার নিজস্ব সুফি লোকসঙ্গীত।
মুর্শিদী গানে সাধারণত মুর্শিদের প্রতি ভালোবাসা, মানবতার শিক্ষা, আত্মশুদ্ধি—এসব বলা হয়। এসব গানের ক্ষেত্রে গাজী আব্দুল করিম, আব্দুল লতিফ ও হাছন রাজার নাম উল্লেখযোগ্য। মারফতি গানের ভেতরে রুহানি ইশক, আত্মজিজ্ঞাসা, দেহতত্ত্ব, নফস ও কল্পনার যুদ্ধ, মানবিকতার দীক্ষা ইত্যাদি থাকে। কেননা, এখানে ‘মারফত’-এর অর্থ পরিচয়—অন্তরের আল্লাহকে চিনে নেওয়া। এরপর সুফি প্রভাবিত বাউল সংগীত ও সুরে আরবি–ফারসি শব্দ ও ধর্মীয় রূপক স্পষ্টভাবে পাওয়া যায়। এছাড়াও, হামদ, নাত, কাওয়ালী তো আছেই। বাংলায় কাওয়ালী ভারতের মতো বিশাল নয়। সৈয়দ মোহাম্মদ মেহেদী এবং চিশতি দরবেশরা কাওয়াল দল নিয়ে বাংলায় এসেছিলেন। ঢাকায় মুঘল যুগে কাওয়ালদের মর্যাদা ছিল।
০৫. মুসলিম বাংলার সংস্কৃতিতে নারীদের অবস্থা
ইসলামী সভ্যতায় মুসলমানগণ তাদের মেয়েদের ব্যাপারে শিক্ষার প্রয়োজনীয়তাকে উপলব্ধি করে এবং তা স্বীকারও করে। বালিকারা যাতে করে তাদের ধর্মের মূলনীতি, কোরআন পাঠ ও ধর্মের ক্রিয়া-কর্ম সঠিকভাবে পালন করতে পারে, সেজন্যে পিতারা তাদের কন্যাদেরকে শিক্ষিত করে তোলা ধর্মীয় কর্তব্য বলে মনে করতেন। বালিকাদেরও বালকদের মতো ‘বিসমিল্লাহখানি’ অনুষ্ঠান দ্বারা অক্ষর-পরিচয় শুরু হতো এবং তারা একই মক্তবে বালকদের সঙ্গে একত্রে পড়াশোনা করতো।
গদাই মল্লিকের পুথি বা ‘মল্লিকার হাজার সওয়াল’ (মল্লিকার হাজার প্রশ্ন) নামে অভিহিত কাব্য থেকে জানা যায় যে, মল্লিকা নাম্নী মুসলমান বালিকা জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় বিশেষ বুৎপত্তি অর্জন করেছিলেন। তিনি প্রকাশ্যে ঘোষণা করেন যে, যে পুরুষ তাকে সাহিত্য-বিষয়ক বিতর্কে পরাজিত করতে পারবে, তাকেই বিয়ে করবেন। বহু রাজপুত্র ও বিদ্বান ব্যক্তি তার সঙ্গে বিতর্কে অবতীর্ণ হন, কিন্তু সকলেই মল্লিকার নিকট পরাজয় বরণ করেন। অবশেষে জনৈক সুফি পণ্ডিত আবদুল হাকিম গদা তার হাজার প্রশ্নের উত্তরদান করে তাকে বিতর্কে পরাজিত করেন। অতঃপর মল্লিকা তাঁর বিজয়ীকে বিয়ে করেন।
ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, মুসলমান রমণীগণ যুদ্ধক্ষেত্রেও স্বামীদের সহগমন করেছেন। এই উপমহাদেশে মুসলমানদের ইতিহাসে মুসলমান রমণীদের এরূপ বীরত্বব্যঞ্জক কার্যক্রম মোটেই বিরল কিছু ছিলো না। বাংলার মুসলমান শাসনামলে বহু রমণী ছিলেন যারা তাদের সাহস, শক্তি ও বীরত্বের জন্যে খ্যাতি লাভ করেন।
নবাব অলীবর্দী খানের বেগম শরফুন্নেসা ছিলেন একজন উচ্চ সংস্কৃতিসম্পন্না ও গুণান্বিতা মহিলা। তিনি তার গুণের মহিমায় সে যুগের রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনের উপর গভীর ছাপ রেখে গেছেন। তিনি স্বামীর যুদ্ধাভিযানে অংশ গ্রহণ করেন এবং তার সঙ্গে যুদ্ধক্ষেত্রের কঠোরতা ভোগ করেন। রাজ্যশাসন ব্যাপারে তিনি তার স্বামীর একজন মূল্যবান উপদেষ্টা ছিলেন।
নবাব আলিবর্দীর কনিষ্ঠা কন্যা ও সিরাজদ্দৌলাহর মাতা আমিনা বেগম তার সুরুচি ও শিষ্টাচারের গুণে সে যুগের সমাজজীবনের উপর গভীর ছাপ রেখে গেছেন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত কোমল হৃদয়া মহিলা এবং অনাথ ও গরিব-দুঃখীদের আশ্রয়স্থল। কোমল হৃদয়া আমিনা বেগম অন্যায়কারীর প্রতিও কোনোরূপ কঠোরতা সহ্য করতে পারতেন না। ইংরেজদের বিবরণ থেকে জানা যায় যে, সিরাজদ্দৌলাহ্ আলিবর্দীর পীড়িত অবস্থায় প্রশাসন সংক্রান্ত বিষয়াদি দেখাশুনা করেন। সে সময় তিনি রাজস্বের হিসাবে বহু অনিয়ম এবং জাহাঙ্গীরনগরে ঘষেটি বেগমের দিউয়ান রাজা রাজবল্লভ কর্তৃক বিপুল অর্থ আত্মসাতের তথ্য আবিষ্কার করেন। রাজা রাজবল্লভ সঠিক হিসাব না দেওয়ায় এবং তসরূপকৃত অর্থ রাজকোষে প্রত্যর্পণ না করায়, সিরাজদ্দৌলাহ্ তাকে মুর্শিদাবাদে কঠোর পাহারায় আবদ্ধ করে রাখেন। আমিনা বেগম পুত্রের নিকট তার পক্ষে মধ্যস্থতা করেন। মায়ের আদেশ রক্ষার্থে সিরাজদ্দৌলাহ্ রাজবল্লভকে মুক্ত করে দেন।
সিরাজদ্দৌলাহর সহধর্মিণী লুৎফুন্নেসা ছিলেন রমণীদের আদর্শ। কিভাবে সামান্য মর্যাদার একজন নারী স্বীয় গুণাবলীর বলে মুসলমান সমাজে খুব সম্মানিত মর্যাদায় আরোহণ করতে পারেন, তা তার জীবনে প্রতিভাত হয়েছে। সামান্য পরিচারিকার অবস্থা থেকে লুৎফুন্নেসা একজন যুবরাজের সহধর্মিণী এবং নবাবের বেগমের মর্যাদা লাভ করেছিলেন। তিনি ছিলেন কোমল হৃদয়া ও উচ্চ অন্তঃকরণ সম্পন্না মহিলা।
এছাড়াও, দারাশিকোর কন্যা ও যুবরাজ মুহম্মদ আজমের স্ত্রী জাহানজেব বানু বেগম মরাঠাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। গউস খানের বিধবা স্ত্রী একদল মারাঠা লুণ্ঠনকারীদের আক্রমণের বিরুদ্ধে ভাগলপুরে তার গৃহ রক্ষা করেন। আহমদনগরের চাঁদসুলতানার বীরত্বগাঁথা সুবিদিত। মহব্বত খাঁর বিরুদ্ধে নূরজাহানের বীরত্বপূর্ণ যুদ্ধ ইতিহাসের একটি সুপরিচিত ঘটনা। এর বাইরে মহিলারা বিবাহ অনুষ্ঠানাদি ও শোভাযাত্রায়ও যেতেন।
এ-সমস্ত দৃষ্টান্ত থেকে দেখা যায় যে, মুসলমান নারীরা গৃহের চার দেয়ালের মধ্যে আবদ্ধ ছিলেন না। তারা গৃহের বাইরেও যেতে পারতেন। কিন্তু তাদের পর্দা পালন করতে হতো এবং গৃহের বাইরে চলতে অবগুণ্ঠন ব্যবহার করতে হতো। পর্দান্তরালে বসবাস করলেও মুসলমান রমণীরা সমাজে যথেষ্ট সম্মানের অধিকারিণী ছিলেন। মুগল সমাজের রমণীগণ, তাদের পূর্ববর্তী ভগ্নীদের তুলনায় যথেষ্ট পরিমাণ স্বাধীনতা ভোগ করেছেন।
মূলত, মুসলিম বাংলায় এভাবেই নারীগণ তাদের শিক্ষা, সাহিত্য চর্চা, পৈত্রিক সম্পত্তি ও রাজনীতির অধিকার পেয়েছিলো। অতএব, উপরোক্ত ঘটনা থেকে বুঝা যায় যে, মুসলমান শাসনযুগে বাংলার রমণীরা হারেমে সাধারণ পর্দা প্রথার মধ্যে থেকেও এবং পুরুষদের উপর নির্ভরশীল থাকা সত্ত্বেও তারা এই প্রদেশের সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।
০৬. হিন্দু-মুসলিম সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি
ইসলামী মূল্যবোধ ঠিক রেখেও যে ইসলামী সভ্যতা স্থানীয়দের স্বকীয়তা বজায় রেখেছিলো, তার অন্যতম একটি উদাহরণ হচ্ছে মুসলিম বাংলায় হিন্দু-মুসলিম সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি। এক্ষেত্রে প্রাক-মুসলিম সময় ও মুসলিম সময়ের মাঝে তুলনা করা প্রয়োজন।
প্রাক মুসলিম ভারতীয় সমাজে জাতিভেদ প্রথা ছিলো খুবই ভয়ংকর। হিন্দু সমাজে জাতিভেদ প্রথা প্রকট আকার ধারণ করে। ৮ম শতাব্দীতে হিন্দু সমাজ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র—এ’চার শ্রেণিতে বিভক্ত হয়ে পড়ে। সমাজে নিম্ন শ্রেণির লোকদের বিশেষ করে শূদ্রদের দুরাবস্থার কোনো সীমা ছিলো না। শূদ্ররা সমাজে অপবিত্র ও অস্পৃশ্য বলে বিবেচিত হতো। এমন কি ধর্ম-কর্ম পর্যন্ত তাদের জন্য নিষিদ্ধ ছিলো। ঐতিহাসিক আল বেরুনী তার “কিতাবুল হিন্দ” নামক গ্রন্থে বলেন যে,
❝কোনো বৈশ্য এবং শূদ্র বেদ-গীতা পাঠ করলে, এমনকি বেদবাক্য শুনলেও শাস্তি হিসেবে তার জিহ্বা কেটে দেওয়া হতো। ভিন্ন জাতির লোকদের মধ্যে অন্তঃবিবাহ ও পানাহার নিষিদ্ধ ছিলো। এমনকি শূদ্রদের স্পর্শও অপবিত্র ছিলো। সমাজে বহু বিবাহ প্রচলিত ছিলো। জাতিচ্যুতদের ভাগ্য আরও খারাপ ছিলো। বেদ শ্রবণ করলে কর্ণে উত্তপ্ত সীসা ঢেলে দেওয়া হতো।❞
প্রাক মুসলিম আমলে এই ছিলো সমগ্র ভারতের ধর্মীয় সহাবস্থানের নমুনা। বিপরীতে মুসলিম বাংলায় ধর্মীয় ধ্যান-ধারণা ও বিশ্বাসের ক্ষেত্রে ব্যাপক পরিবর্তন আসে। মুসলিম শাসকরা উদার ধর্মীয় নীতি গ্রহণ করেন। মুসলিম শাসনামলে ভারতের হিন্দুরা শান্তিপূর্ণভাবে বসবাস করতো। তাদেরকে দেওয়া হয় ধর্মীয় স্বাধীনতা। ফলে, এই অঞ্চলের অমুসলিমরা তাদের নিজ নিজ ধর্ম স্বাধীনভাবে পালন করতে পারতো। বখতিয়ার খিলজির সেই অভিযানের পর এই অঞ্চলের প্রচলিত সামাজিক রীতি-নীতির উপর ইসলামের যথেষ্ট প্রভাব পড়ে। ভারতের হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ই খাদ্য, পোশাক পরিচ্ছেদ ও সামাজিক রীতি-নীতির ক্ষেত্রে একে অন্যের সাথে ভাবের আদান-প্রদান করে।
হিন্দু ও মুসলিম সম্পর্কের ক্ষেত্রে এস. এ. এ. রিজভী বলেন যে, ❝ভারতে তুর্কি শাসন প্রতিষ্ঠা হিন্দু-মুসলিম সম্পর্ক স্থাপনে অনেক সুযোগ-সুবিধাকে উন্মোচিত করেছিলো।❞
রোমিলা থাপার মতে, ❝ব্রাহ্মণরা তাদের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখার ক্ষেত্রে সচেষ্ট হলেও হিন্দু-মুসলিম মিলনের স্রোত ক্রমশ গতিশীল হয়ে ওঠে।❞
অতএব, বুঝা গেলো যে, মধ্যযুগে বাংলায় হিন্দু মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান ছিলো। আবার, সরকারি চাকরি করবার সুবাদে কিংবা মুসলমান শাসনকর্তাদের সভাসদ ও রাজকর্মচারী হিসেবে অথবা মুসলিম জনগণের প্রতিবেশী রূপে হিন্দুরা মুসলমানদের সংস্পর্শে আসে। যার ফলে তারা মুসলমানদের মহৎ আদর্শ সংস্কৃতি এবং শিষ্টাচার ও জীবন পদ্ধতি দ্বারা যথেষ্ট প্রভাবান্বিত হয়। পাশাপাশি, মুসলিম শাসক ও সুলতানদের গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা মধ্যযুগে বাংলায় হিন্দু-মুসলিমের মধ্যে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের পরিবেশ সৃষ্টি করে।
এজন্যই, সাধারণ হিন্দুদের উপর ইসলাম ধর্ম দারুণভাবে প্রভাব বিস্তার করে। অথচ, সাধারণ হিন্দুদের কোনো মর্যাদাই ছিলো না। সমাজে উচ্চ ধর্মের হিন্দুর সাথে নিম্ন বর্ণের হিন্দুর মধ্যে অনেক পার্থক্য ছিলো। নিম্ন বর্ণের হিন্দুরা তাদের ধর্মগ্রন্থও পাঠ করতে পারতো না। ব্রাহ্মণ ও কায়স্থরা শিক্ষা অর্জন করতো। কিন্তু বাংলার মুসলিম শাসকরা উদারনৈতিক শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। বাংলায় মুসলিম সমাজ প্রতিষ্ঠার ফলে উচ্চ শ্রেণীর ব্রাহ্মণদের একচেটিয়া প্রাধান্য খর্ব হয়। নিম্ন বর্ণের হিন্দুরাও শিক্ষা অর্জন করেন। সমাজে ব্যাপক পরিবর্তন সাধন ঘটে। তারা সংস্কৃতের পাশাপাশি ফার্সি ভাষাও শিক্ষা অর্জন করে উচ্চ রাজ কার্যে নিয়োজিত হয়ে তাদের প্রতিভা বিকাশের সুযোগ লাভ করে।
অন্যদিকে, হিন্দু সমাজে ব্রাহ্মণদের পরেই ছিলো কায়স্থদের স্থান। মুসলমানদের দ্বারা তারাও প্রভাবান্বিত হয়। তারা শিল্প ও সাহিত্যে যথেষ্ট যোগ্যতার পরিচয় দেয়। মুসলিম শাসকরা উদারভাবে তাদের পৃষ্ঠপোষকতা করেন। এসব বিখ্যাত কবিদের মধ্যে ছিলেন-মালাধর বসু (গুণরাজ খান), কবিন্দ্র পরমেশ্বর, শ্রীকর নন্দী, যশোরাজ খান, বিজয় গুপ্ত, কৃষ্ণ দাস কবিরাজ। মুসলিম শাসনামলে কায়স্থরা জমিদারি ও রাজস্ব আদায়ের দায়িত্ব লাভ করে। মুসলিম শাসক কর্তৃক এসব কায়স্থরাই পরবর্তীতে রায়, চৌধুরী, মজুমদার, অধিকারী উপাধী লাভ করে। এটি পরবর্তীকালে বংশ পরম্পরায় চলতে থাকে এবং আরো পরবর্তীতে গিয়ে দেখা যায় যে, এসব পদবী মানুষের নামের সাথেও যুক্ত হয়ে যায়।
আবার, বাংলার সুলতানরা ছিলেন উদার সংস্কৃতিমনা। তারা হিন্দু কবি সাহিত্যিকদের উদারভাবে পৃষ্ঠপোষকতা করেন। হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে মুসলিম শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান এবং হিন্দুদের প্রতি মুসলিমদের প্রতিবেশী সুলভ মনোভাব মধ্যযুগে বাংলা হিন্দু মুসলিম শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের আরেকটি কারণ। মূলত, এসব কারণেই যুগ যুগ ধরে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে একটি সম্প্রীতি্র সম্পর্ক গড়ে ওঠে।
এসবের পাশাপাশি প্রশাসনিক ক্ষেত্রেও হিন্দু-মুসলিম সমন্বয় ছিলো। এটা বললে মোটেও অত্যুক্তি হবে না যে, যেখানে ধর্মীয় সহাবস্থান থাকে, সেখানেই অবশ্যই প্রশাসনিক সহাবস্থানও থাকবে। এর অন্যতম একটি উদাহরণ হচ্ছে মুসলমান আমলে হিন্দু শাসক ও সেনাপতি নিয়োগ।
বাংলায় মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠার সাথে সাথে মুসলমান শাসকগণ স্থানীয় হিন্দুদের শাসনকার্যে সংম্পৃক্ত করেন। শাসনকার্যে সুযোগ পেয়ে এসব হিন্দুরা যথেষ্ট যোগ্যতার ও বিশ্বস্ততার পরিচয় দেয়। মুসলিম সুলতানগণ প্রতিভাবান হিন্দুদেরকে গুরুত্বপূর্ণ পদ, রাষ্ট্রীয় উপাধী এবং সরকারি জমি দান করেন। হিন্দুরা খুবই বিশ্বস্ততার সাথে মুসলমানদেরকে সহযোগিতা করে। বাংলার সুলতান ইলিয়াস শাহ দিল্লীর সুলতান ফিরোজ শাহ তুঘলকের বিরুদ্ধে যখন যুদ্ধে লিপ্ত হন, তখন বাংলার হিন্দুরা বাংলার সুলতানের হয়ে যুদ্ধ করেছিলো। হিন্দু সেনাপতি সহদেব এ-যুদ্ধে যথেষ্ট বীরত্ব ও সাহসিকতার পরিচয় দেন। নবাবী আমলে আমরা দেখি যে, পলাশীর যুদ্ধের সময় নবাব সিরাজের সেনাপতি মীর মর্দন ও মোহনলাল দেশের স্বাধীনতার জন্য জীবন দান করে।
শুধু এতোটুকুই নয়, মুসলিম শাসকদের পৃষ্ঠপোষকতাতেই হিন্দু জমিদার শ্রেণীরও উৎপত্তি হয়। দুর্গাচন্দ্র সান্যাল তার বিখ্যাত গ্রন্থ “বাঙালার সামাজিক ইতিহাসে” লিখেন যে, ইলিয়াস শাহী শাসকদের পৃষ্ঠপোষকতায়ই রাজশাহী জেলায় বিখ্যাত ‘সান্যাল’ এবং “ভাদুড়ী পরিবারের” উৎপত্তি হয়। সুলতান গিয়াস-উদ-দীন আযম শাহের রাজত্বকালে ভাতুড়িয়ার জমিদার কংস (রাজা গণেশ) যথেষ্ট শক্তিশালী হয়ে ওঠে।
আবার, এর বিপরীতে হিন্দু রাজা ও জমিদারদের অধীনে মুসলিম কর্মচারীও নিয়োগ হয়। মুসলিমদের শাসকদের মতো হিন্দু সামন্ত রাজা ও জমিদাররাও তাদের শাসনকার্যে মুসলিম কর্মচারী নিয়োগ করতেন। মীর্জা নাথানের বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, ভুলুয়ার (নোয়াখালি) হিন্দু জমিদার অনন্তমানিক্য মীর্জা ইউসুফ নামক এক ব্যক্তিকে উজির পদে নিয়োগ দেন। এছাড়াও, চাঁদ রায় ও কেদার রায় সোলায়মান লোহানী নামে এক মুসলিমকে সেনাপতি হিসেবে নিয়োগ দান করেন। মহারাজা প্রতাপাদিত্যের পিতা এবং “কালাপাহাড়” নামে খ্যাত শ্রীহরি ছিলো দাউদ খান কররানীর অন্যতম উপদেষ্টা ও সেনাপতি।
অতএব, এটাও সত্য যে, ধর্মীয় সহাবস্থানের পাশাপাশি প্রশাসনিক ক্ষেত্রেও হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতি ও সহাবস্থান বজায় ছিলো। যেহেতু তৎকালীন ইতিহাসই এসব সাক্ষ্য দেয়, তাই এটা পুরোপুরি সঠিক যে, স্থানীয় সমাজ, মানুষ ও সংস্কৃতিকে মূল্যায়ন করেছে বিধায়ই ইসলামী সভ্যতা আজও মানুষের মনে স্থান দখল করে রয়েছে; এবং এটাও প্রমাণ হয়ে যায় যে, ইসলামী সভ্যতা প্রকৃত অর্থেই বিশ্বজনীনতাকে গ্রহণ করে থাকে।
জাতিসত্তা ও ইসলামী সংস্কৃতির বোঝাপড়া
সবশেষে, আমাদের জাতিসত্তার ভিত্তিতে ইসলামী সংস্কৃতির বোঝাপড়া কেমন হবে, সেটিই এখন মূল প্রশ্ন। আমাদের ঐক্য ও সম্প্রীতির সমাজ গড়তে হলে এমন একটি ইশতেহার প্রণয়ন করতে হবে, যেখানে ধর্মীয় বিশ্বাস, সামাজিক ন্যায়, পারিবারিক ঐক্য, শিক্ষা, নৈতিকতা ও মানবিক মূল্যবোধ একে অপরের পরিপূরক হিসেবে কাজ করবে।
ইসলামী সংস্কৃতি তখনই পূর্ণতা পাবে, যখন তা জাতিসত্তার ভেতরের মানবিক সৌন্দর্যের সঙ্গে মিলে যাবে। আমরা বাঙালি মুসলমানদের ইসলামী সংস্কৃতির যে বোঝাপড়া গড়ে তুলতে চাই, তার সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হওয়া উচিত মানবিক মর্যাদা ও পারস্পরিক সম্মান।
এই অঞ্চলে যুগ যুগ ধরে বিভিন্ন ধর্ম, জাতি ও উপজাতির মানুষ একসাথে বসবাস করছে। তাই আমাদের উচিত, সবার প্রতি সমান দৃষ্টিতে তাকানো, সবার অধিকার ও মানুষ হিসেবে মর্যাদা স্বীকার করা। একই সঙ্গে আমাদের আহ্বান থাকবে; আমরা যারা বাঙালি মুসলমান, আমরা যেন নিজেদেরও মানুষ হিসেবে মর্যাদাপূর্ণ অবস্থানে কল্পনা করি। প্রত্যেকে নিজের আঞ্চলিক পরিচয় আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে ধারণ করবে এবং নিজের সাংস্কৃতিক স্বকীয়তাকে বজায় রাখবে।
সাংস্কৃতিক পুনর্জাগরণের দায়িত্ব
মুসলমানদের সভ্যতার ইতিহাসে একসময় যে মূল্যবোধ, ঐতিহ্য, সামাজিক নৈতিকতা ও আধ্যাত্মিকতা গড়ে উঠেছিল, সেগুলোকে আবার নতুন করে ফিরিয়ে আনা দরকার। আমাদের দায়িত্ব হবে এই মূল্যবোধগুলোকে পুনরুজ্জীবিত করা, সমাজে তুলে ধরা ও এর চর্চা অব্যাহত রাখা।
বিশেষভাবে খেয়াল রাখতে হবে, ব্রিটিশ উপনিবেশের সময় কলকাতা-কেন্দ্রিক যে বয়ান আমাদের ওপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল, তা যেন আমাদের হীনমন্য, আত্মবিশ্বাসহীন বা পরিচয়হীন জাতিতে পরিণত না করে।
কথিত ন্যাশনালিস্ট ইসলাম, সেকুলার ইসলাম বা লিবারেল ইসলাম; এসব নামে যে বিভ্রান্তি তৈরি হচ্ছে, সেগুলো আত্মঘাতী চিন্তা। এর পরিবর্তে আমাদের গড়ে তুলতে হবে মূলনীতিনির্ভর একটি নতুন বয়ান, যা ইসলামের উসূল ও মৌলিক নীতির ওপর ভিত্তি করে দাঁড়াবে।
আরব, আফ্রিকা, তুরস্ক বা ভারতের সংস্কৃতি এক নয়, কিন্তু তারা সবাই ইসলামের স্থায়ী নীতির মধ্যে থেকেই টিকে আছে। তাই আমাদেরও প্রয়োজন, ইসলামী মূলনীতিগুলোর সঙ্গে ঐতিহ্য ও আঞ্চলিক সংস্কৃতির একটি ভারসাম্যপূর্ণ বোঝাপড়া তৈরি করা। আমাদের সাংস্কৃতিক কর্মসূচি সেই ভারসাম্যের ভিত্তিতেই চালিয়ে যেতে হবে।
এর বাইরে গেলে বিচ্ছেদ তৈরি হবে, যেমনটি আমরা ইতিমধ্যে দেখতে পাচ্ছি। ব্রিটিশ আমলের পর থেকে আমাদের সংস্কৃতিতে এক ধরনের আত্মবিচ্ছেদ দেখা দিয়েছে। আমরা অন্যদের খাদ্যাভ্যাস, পোশাক, বিনোদন, স্থাপত্য, শহর পরিকল্পনা, এমনকি মসজিদের ডিজাইন পর্যন্ত নকল করছি। এগুলো আমাদের নিজস্ব সংস্কৃতিকে বাধাগ্রস্ত করছে।
তবে একে পুরোপুরি বর্জন করাও অবাস্তব। কারণ, বিশ্ব পরিবর্তনের ঢেউকে উপেক্ষা করা সম্ভব নয়। তাই পাশ্চাত্যের ইতিবাচক দিকগুলো গ্রহণ করতে হবে, একই সঙ্গে আমাদের অঞ্চলের ভালো দিকগুলোও সংযোজন করতে হবে।
অর্থাৎ, ইসলামের স্থায়ী মূলনীতি বুঝে, পাশ্চাত্যের তৈরি দুনিয়াকে বুঝে, আমাদের ইতিহাস ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের আলোকে একটি ভারসাম্যপূর্ণ সংস্কৃতি গড়ে তুলতে হবে। এই ভারসাম্যপূর্ণ সাংস্কৃতিক বয়ানই হতে হবে আমাদের পথনির্দেশ। এর বিপরীতে কোনো বিশৃঙ্খল, পক্ষপাতদুষ্ট বা বিভাজনমূলক বয়ান তৈরি করা যাবে না, যা অন্য কোনো গোষ্ঠীর শিকড় কেটে দেয়।
বাঙালি মুসলমান সংস্কৃতি কখনোই পুরনো সংস্কৃতির অন্ধ অনুকরণ হবে না, আবার আধুনিকতার নামে মূল থেকে বিচ্ছিন্নও হবে না। ইসলামী সংস্কৃতির মূল ভিত্তিকে কেন্দ্র করে, সামাজিক বাস্তবতার আলোকে, আমাদের সাংস্কৃতিক এজেন্ডা ও পরিবেশ তৈরি করতে হবে।
এর মধ্য দিয়েই ভবিষ্যৎ প্রজন্ম যেন বেড়ে উঠতে পারে, সেটিই হবে আমাদের প্রধান লক্ষ্য।
আমাদের সংস্কৃতি গড়ে উঠবে বিশ্ব কাঠামো, ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতা, শিকড়, ইসলামের উসুল ও পদ্ধতিগত বোঝাপড়ার সমন্বয়ে। এই সবকিছু বুঝে ও ধারণ করেই আমাদের কাজ করতে হবে। এটাই হোক বাঙালি মুসলমানের সাংস্কৃতিক কর্মসূচির প্রথম ধাপ।