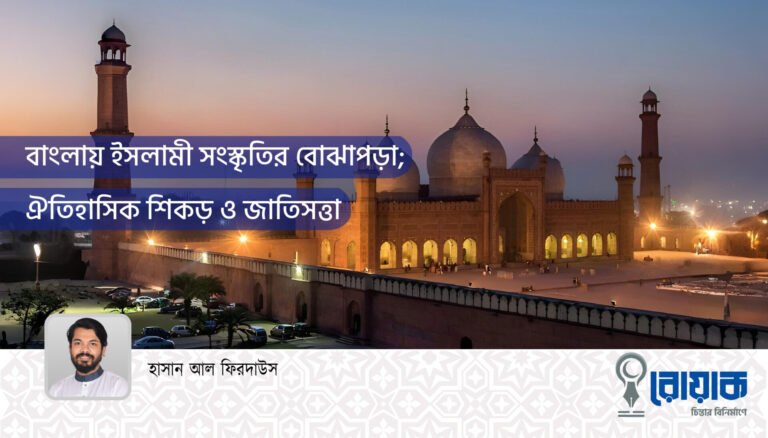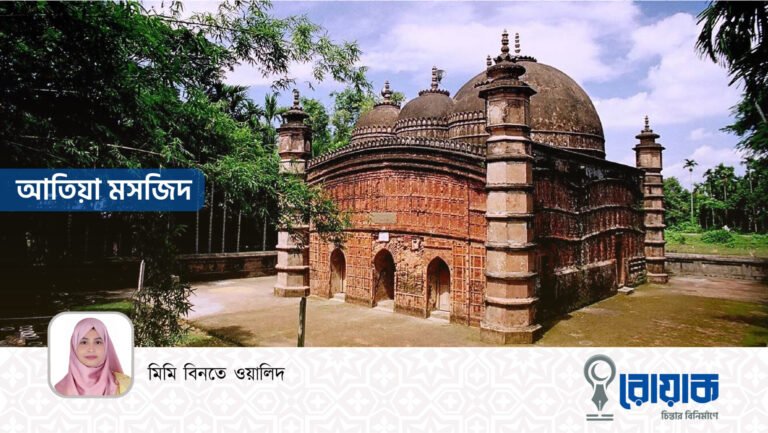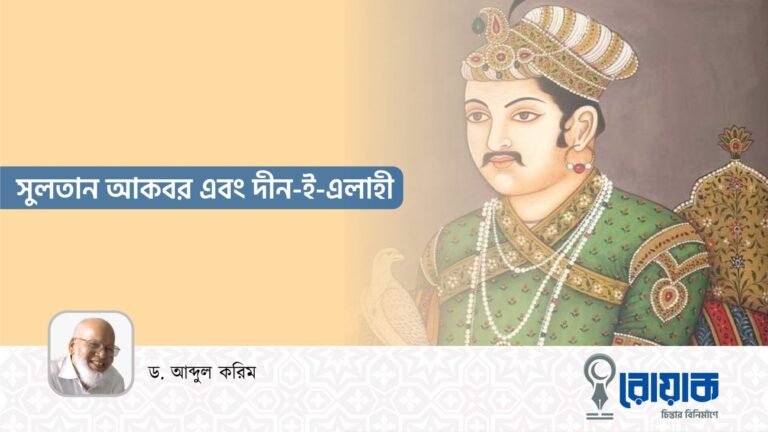দ্বীনের সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত জ্ঞানসমূহের উৎপত্তি কীভাবে হলো তা আপনারা সকলেই কম বেশি জানেন। আপনারা মাদরাসা বা বিশ্ববিদ্যালয়ের থিওলজি বিভাগে যারা পড়েছেন তারা তাফসীর, হাদীস এবং ফিকহসহ জ্ঞানের অন্যান্য শাখার ইতিহাস সম্পর্কেও পড়েছেন। আজকে আমি এই ক্লাসে আমাদের মাদরাসা বা বিশ্ববিদ্যালয়ে যেভাবে পড়ানো হয় সেভাবে নয়; বরং ভিন্ন একটি দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচনা করব। অর্থাৎ কোন কোন মৌলিক সমস্যাগুলো দ্বীনি জ্ঞানের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের ক্ষেত্রে অনুঘটকের ভূমিকা পালন করেছে সেই সকল বিষয় নিয়ে আলোচনা করবো।
মূল আলোচনায় প্রবেশ করার পূর্বে কয়েকটি বিষয়ে আমাদের সুস্পষ্ট ধারণা থাকতে হবে-
১. রাসূলে আকরাম (স.)-এর জীবদ্দশায় নস (কোরআন) এবং মানুষের জীবন ধারার মধ্যে কোনো ধরণের অসঙ্গতি ছিল না।
অর্থাৎ নস এবং ঘটনা প্রবাহের মধ্যে পূর্ণসঙ্গতি বজায় ছিল। অসঙ্গতি না থাকার অর্থ হলো, সেই সময়ে সংঘটিত ছোট কিংবা বড় যে কোনো ঘটনা প্রবাহ নিয়ে ওহী নাযিল হতো, দ্বীনি বিষয়ে যে কোনো সমস্যায় সিদ্ধান্ত দানকারী ব্যক্তি (Authority) রাসূল (স.) জীবিত ছিলেন। রাসূলে আকরাম (স.) জীবিত থাকার কারণে যখনই কেউ কোনো বিষয়ে কোনো সমস্যায় পড়ত, তারা রাসূলে করীম (স.)-এর কাছে আসতেন এবং রাসূলও (স.) তাদের সেই সকল সমস্যার সমাধান ওহীর মাধ্যমে, কিংবা তার নিজের ইজতিহাদের মাধ্যমে অথবা সাহাবীদের সাথে পরামর্শ করে সমাধান করে দিতেন।
২. রাসূলে আকরাম (স.)-এর ওফাতের পরে ইসলামী রাষ্ট্রের সীমানা সম্প্রসারিত হয়। হযরত আবু বকর (রা.)-এর সময় সমগ্র জাযিরাতুল আরব ইসলামী শাসনের অধীনে আসে, হযরত উমর (রা.)-এর সময়ে বিলাদ-ই শাম, মিশর, পারস্য সাম্রাজ্য সহ অর্ধ পৃথিবী ইসলামী শাসনের অধীনে আসে। হযরত উসমান (রা.)-এর শাসনামলের প্রথম ছয় বছরের মধ্যে উত্তর আফ্রিকার বিশাল একটি অঞ্চল, সাইপ্রাস ও মধ্য এশিয়াসহ প্রাচীন সংস্কৃতির অধিকারী সমগ্র অঞ্চল ইসলামী শাসনাধীনে আসে। এই বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বলতে গেলে,
ইসলাম এমন একটি অঞ্চলে আসে সেই অঞ্চল মূলত তুলনামূলকভাবে কম গুরত্বপূর্ণ ছিল। যদিও হিজায অঞ্চল ধর্মীয় ধারার দিক থেকে অনেক শক্তিশালী ছিল, সমগ্র আরব অঞ্চলের কেন্দ্র ছিল। কিন্তু সেসময়ে সভ্যতা ও সংস্কৃতিগতভাবে অগ্রসর কোনো অঞ্চল ছিল না। তৎকালীন সময়ে গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল সমূহের মধ্যে ছিল মিশর, কালদানী ও ব্যবিলনীয়দের সংস্কৃতি সমৃদ্ধ মেসোপটেমিয়া অঞ্চল, গ্রীস ও সাসানী। এ অঞ্চলগুলো গুরুত্বপূর্ণ হওয়ার কারণ হলো, খ্রিষ্টপূর্ব ৩০০০ সাল থেকে নিয়ে ধীরে ধীরে এই অঞ্চলে জ্ঞান-বিজ্ঞানের একটি ধারা তৈরি হয়। যেমন, মিশরীয়গণ গণিত ও জ্যোতির্বিদ্যায় পারদর্শী ছিল, মেসোপটেমিয়ানরা জ্যোতিষীবিদ্যায় (Astrology) পারদর্শী ছিল। মেসোপটেমিয়াতে গণিত বা গণিতের শক্তিশালী কোনো ধারা ছিল না। মিশর থেকে তারা গণিতবিদ্যা শিক্ষা করে মেসোপটেমিয়াতে নিয়ে আসে। মেসোপটেমিয়ানরা গণিতবিদ্যা ও জ্যোতিষীবিদ্যাকে একত্রিত করে জ্ঞানের নতুন একটি ধারা তৈরি করে এবং পরবর্তীতে গ্রীকরা জ্ঞানের এই নতুন ধারাকে গ্রহণ করে উন্নত করে।
গ্রীকরা জ্ঞান-বিজ্ঞানকে সম্পূর্ণ নতুন একটি ধারায় নিয়ে যায় এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানকে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করে সবশেষে এরিস্টটলের সময়ে অন্টোলজি (Ontology), জ্ঞানতত্ত্ব (Epistemology), সৃষ্টিতত্ত্ব (Cosmology) সহ আরও অনেক মৌলিক বিষয়ে পরিভাষা সৃষ্টি করে। আজকে দুনিয়াকে বুঝার জন্য যে সব পরিভাষা ব্যবহার করে থাকি এজন্য আমরা এরিস্টটলের কাছে ঋণী। অর্থাৎ বস্তুগত দুনিয়াকে (Material World) চিত্রায়িতকারী পরিভাষা সমূহের গুরুত্বপূর্ণ একটি অংশ প্লেটো ও এরিস্টটলের কাছ থেকে এসেছে।
আপনারা সকলেই জানেন এই দুই দার্শনিক গ্রীক দর্শনকে গঠনগত ভাবে বিন্যাস করেন। এই দুই দার্শনিকের পরে আর কেউ তাদের চিন্তাগত প্রভাব এড়াতে পারেনি। পরবর্তীতে রোম সাম্রাজ্যের বিস্তৃতির পরে হেলেনিস্টিক সময়ে প্রবেশ করে। ইসলামী চিন্তার ধারাবাহিকতাকে বুঝার জন্য হেলেনিস্টিক সময় খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ হেলেনিস্টিক পিরিয়ডে ভোগবাদ (Epicureanism) এবং বৈরাগ্যবাদ (Stoicism) এর মতো বিভিন্ন ধারার উৎপত্তি হয়। এ সময়ে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটে। সেটা হলো, এরিস্টটল ও প্লেটোর দর্শনকে একত্রিত করে বড় একটি মেটাফিজিক্যাল থিওরী উৎপত্তি হয়, আর এর নাম দেয়া হয় Neoplatonism।
Neoplatinism নিয়ে এখন পর্যন্ত সত্যিকারের কোনো গবেষণা হয়নি। এই Neoplatinism এর একটি বড় বৈশিষ্ট্য হলো “সকল প্রাচীন সংস্কৃতিকে একত্রিত করে বৈজ্ঞানিক পরিভাষার মাধ্যমে ধারণ করা।” অর্থাৎ, Neoplatinism এর মধ্যে জরাথুস্ত্র দর্শন রয়েছে, ভারতীয় দর্শন ও সংস্কৃতি রয়েছে, প্লেটোনিক মেটাফিজিক্স রয়েছে, এরিস্টটলের ফিজিক্স রয়েছে। এ সকল চিন্তার অস্তিত্ব ও প্রভাবকে একত্রে Neoplatinism বলা হয়। ফলশ্রতিতে প্রাচীন দুনিয়ার সকল চিন্তাকে সমন্বয়কারী উচ্চ একটি মেটাফিজিক্যাল থিওরীর প্রতিনিধিত্ব করে Neoplatinism। পরবর্তীতে খৃষ্টধর্মের প্রচার ও প্রসারের ফলে এই জ্ঞান (দর্শন) সাসানীদের কাছেও চলে আসে। এরপর সাসানীরা একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নতির জন্য প্রচেষ্টা চালায় এবং হেলেনিস্টিক সময়ে সাসানীদের হাত ধরে উত্তর আফ্রিকা থেকে শুরু করে ভারতীয় উপমহাদেশ পর্যন্ত জ্ঞানভিত্তিক একটি সংস্কৃতি গড়ে ওঠে।
এই সব তথ্য খুব ভালোভাবে মাথায় রাখুন। কারণ ইসলাম যে অঞ্চলেই গিয়েছে সেই অঞ্চলেই সাসানী সাম্রাজ্যের সংস্কৃতির আলোকে গড়ে ওঠা বৈজ্ঞানিক পরিভাষার অধিকারী সংস্কৃতিসমূহের মুখোমুখি হয়েছিল। তবে এই বৈজ্ঞানিক সংস্কৃতি খুব একটা শক্তিশালী ছিল না, ফলশ্রুতিতে সাসানী সাম্রাজ্যের অধীনে গড়ে ওঠা এই সংস্কৃতি আস্তে আস্তে দুর্বল হয়ে পড়ে।
এই সব বিষয় উল্লেখ করার কারণ হল-
- ইসলাম যে সব অঞ্চলে গিয়েছিল সেই সব অঞ্চল শক্তিশালী একটি রাজনৈতিক ধারার অধিকারী ছিল।
- এই সব অঞ্চল ভিন্ন ভিন্ন ধারার হলেও প্রতিষ্ঠিত আইন ও কানুন ছিল।
- সেই সময়ের আলোকে তাদের মধ্যে একটি বৈজ্ঞানিক ধারণা ছিল, যেই ধারণার আলোকে তারা এই দুনিয়াকে ব্যাখা বিশ্লেষণ করতো।
ফলশ্রুতিতে মুসলমানগণ এসব অঞ্চলে যাওয়ার পর এসব সংস্কৃতি ও জ্ঞানকে মোকাবেলা করতে বাধ্য হয়। এটা ছিলো বহির্গত একটি চ্যালেঞ্জ। এছাড়া অন্য একটি বিষয় আছে সেটা হল আভ্যন্তরীণ সমস্যাসমূহ। আমাদের চিন্তার ইতিহাস রচনার সময় ‘বহির্গত’ ও ‘অন্তর্গত’ কারণকে বিবেচনায় রাখতে হবে।
তাছাড়া আমরা যদি কেবল বহির্গত কারণ বা ইসলামের বাহির থেকে আসা চ্যালেঞ্জকে বিবেচনায় নিয়ে আমাদের চিন্তার ইতিহাস রচনা করি, তাহলে ইসলামী চিন্তা ও জ্ঞানের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশকে পূর্ববর্তী সংস্কৃতিসমূহের একটি ফলাফল হিসেবে বিবেচনা করা শুরু করবো। আর এটা হবে সম্পূর্ণ ভুল।
যদি আমরা মুসলিমদের আভ্যন্তরীণ কারণগুলোকে বিবেচনায় নিয়ে আমাদের চিন্তার ইতিহাস রচনা করি, তাহলে আমরা বলতে পারব যে, ইসলামী চিন্তা ও জ্ঞান তার নিজের মধ্যকার গতিশীলতার কারণেই সৃষ্টি হয়েছে। ফলশ্রতিতে আমাদের সামনে সামগ্রিকভাবে ইসলামী চিন্তার ইতিহাসকে দাঁড় করাতে পারবো।
কোরআন, হাদীস ও ফিকহের ইতিহাসের দিকে যদি তাকাই তাহলে আমরা দেখতে পাই যে এসব জ্ঞান আলাদা একটি শাখা হিসেবে উৎপত্তি হওয়ার ক্ষেত্রে কিছু গুরুত্বপূর্ণ টার্নিং পয়েন্ট রয়েছে। কোরআন সংকলনের ইতিহাস, কোন কারণে কোরআনকে সংকলন করতে হয়, এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি কারণ। অথবা উমর (রা.)-এর সময়ে পারস্য সাম্রাজ্য ও সিরিয়া বিজিত হওয়ার পর সেই সকল বিজিত ভূমিকে মুজাহিদদের মধ্যে বণ্টন না করা ফিকহের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ টার্নিং পয়েন্ট ইত্যাদি।
ইসলামের ইতিহাসে কিছু কিছু ঘটনা রয়েছে যা সমগ্র ইতিহাসকে প্রভাবিত করেছে। এর মধ্যে সর্বপ্রথম ও সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ হলো হযরত উসমান (রা.)-এর শাহাদাতের মাধ্যমে শুরু হওয়া মুসলমানদের মধ্যকার গৃহযুদ্ধ। এই গৃহযুদ্ধের বিষয়টি খুবই ক্রিটিক্যাল একটি বিষয়। কারণ হলো, মুসলমানদের মধ্যে এই প্রথম এমন একটি দলের উৎপত্তি হয় যারা একে অপরকে হত্যা করছে কিন্তু কেউ তওবা পর্যন্ত করছে না! মুসলমানগণ গুনাহ করতে পারে, এটা স্বাভাবিক একটি বিষয়। মুসলমানগণ যে কবীরা গুনাহ করতে পারে ও করার সম্ভাবনা রয়েছে এটা কোরআন হাদীসে রয়েছে এবং এই সম্ভাবনা কে সামনে রেখেই ইসলামে হুদুদের বিধান রয়েছে। কিন্তু মুসলমানদের নিকট চাওয়া হলো, সে যখনি কোনো গুনাহ করবে তখনই তওবা করবে। আল্লাহর কাছে তওবা করতে দেরি করলেও সে তার কাজকে অপরাধ হিসেবে স্বীকৃতি দিবে। কিন্তু হযরত উসমান (রা.)-এর শাহাদাতের পরে মুসলমানদের মধ্যকার সংগঠিত গৃহযুদ্ধগুলোতে (জামাল ও সিফফিন) অংশগ্রহণকারী উভয় দলই নিজেদেরকে হক্বপন্থী হিসেবে দাবি করে মানুষ হত্যার মতো কাজকেও গুনাহ হিসেবে না ধরে তওবা করা থেকে বিরত থাকে। এদের মধ্যে সকলেই যে এমন ছিল তা নয়, এই যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের অনেকেই পরবর্তীতে দূরে সরে গিয়ে ভিন্ন একটি দল গঠন করে। মুসলমানগণ প্রথম বারের মতো এমন একটি সমস্যার সম্মুখীন হয়। বড় বড় গুনাহ করার পরেও কোনো প্রকার অনুতপ্ত না হওয়ার মত একটি গ্রপের সৃষ্টি হয়। অল্প সময়ের মধ্যে এই সমস্যাটি বড় একটি সমস্যায় রূপ নেয়।
সেই সমস্যাটি হল ‘মুরতাকিবে কাবীরা কি’? মুরতাকিবে কাবীরা (কবীরা গুনাহকারী) কি মু’মিন নাকি ফাসিক?
আমরা যদি আরো গভীরে যাই তাহলে দেখতে পাই যে, কবীরা গুনাহকারী মু’মিন নাকি ফাসিক এটি খুব বড় কোন সমস্যা নয়। এখানে মূল সমস্যা হল, মহাগ্রন্থ আল কোরআন মানুষ এবং আল্লাহর মধ্যকার সম্পর্ককে বিনির্মাণকারী কিছু পরিভাষা ব্যবহার করেছে। যেমন মু’মিন, মুনাফিক, ফাসিক, কাফির, দাল্লুন ইত্যাদি। এই সকল পরিভাষাসমূহ মানুষকে ওহীর মাধ্যমে আগত হাকীকতসমূহের সাথে সম্পৃক্ত করে থাকে। এই সকল পরিভাষাগুলো যদি কারোর উপর প্রয়োগ করা হয় তখন এগুলো সেই ব্যক্তিকে নামকরণ করার সাথে সাথে তার পরিচয়ও দান করে। যেমন, যখন আমরা কাউকে মু’মিন বলি তখন আমরা বুঝে নেই, তিনি ঈমান এনেছেন। ফলে তাকে আমরা মু’মিন বলে গণ্য করতে পারি। তারা ভাবতেন যে, রাসূলে করীম (স.)-এর সময় থেকে মু’মিন, মুনাফিক, কাফির কে বা কি এটা তারা জানেন। প্রথম বারের মত এই সকল ঘটনা (গৃহযুদ্ধ) পরিভাষাগত বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে। এই কারণে ইসলামী চিন্তার ইতিহাসে উদ্ভূত সবচেয়ে বড় সমস্যাগুলো হলো,
- মানুষ পরিচয়দানকারী কোরআনী পরিভাষাসমূহের অর্থের অস্পষ্টতা (Ambiguity of Meaning).
- স্বাধীনতার সমস্যা। অর্থাৎ, মানুষ তার নিজের কর্মসমূহের কর্তা (ফায়িল) কিনা? অর্থাৎ নিজের কাজের ক্ষেত্রে স্বাধীন কিনা?
কোরআনুল কারীমে কিংবা হাদীসে নববীতে আল্লাহর সাথে সম্পর্কিত আয়াত ও হাদীসকে যদি সামগ্রিকভাবে চিন্তা করি, তাহলে সত্যিকার অর্থেই কী মানুষকে আমরা তার কর্মের কর্তা (ফায়িল) বলতে পারি? তবে এক্ষেত্রে আমার একটি অনুরোধ, আপনারা প্রথমেই এই চিন্তাকে কোনো মাজহাবের সাথে সম্পৃক্ত করবেন না। এখানে ভাবনার বিষয় হলো, আল্লাহ যদি কর্তা (ফায়িল) হয়, তাহলে মানুষ কী? কর্তা হিসেবে তার কতটুকু স্বাধীনতা রয়েছে?
যেমন আমি ব্যক্তি নিজেকে আমার তৈরি করা বাক্যসমূহের সাবজেক্ট বানিয়ে কথা বলতে পারি, ভাষা আমাদেরকে এই সুযোগ দিয়ে থাকে কিন্তু এটা কি মাজাজ নাকি হাকীকত? এখানে মূল বিতর্ক হলো এই বিষয় নিয়ে। এটাকে যদি আমরা এভাবে না বুঝি তাহলে এসব চিন্তাগত সময়ের ব্যবধানে খুবই নগণ্য বলে গণ্য করা শুরু করবো। ইসলামী চিন্তার গঠন পর্যায়ে যে কোনো থিওরীর সমর্থককে নগণ্য বা ছোট বলে ধারণা করা সঠিক হবে না। এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি বিতর্ক, এই বিতর্কে জাবরিয়া, কাদরিয়া এবং মু’তাযিলাগণ অনেক গ্রহণযোগ্য দলীল প্রমাণ দিয়ে তাদের যুক্তি তুলে ধরেছিলেন। আমি আমার আজকের এই আলোচনায় এর বিস্তারিত ব্যাখ্যায় যাব না। আমি শুধুমাত্র এই সমস্যাটিকে ভালোভাবে তুলে ধরার জন্য এত কথা বলছি। অন্য কথায় বলতে গেলে,
মানুষ কি তার কর্মের ক্ষেত্রে স্বাধীন কিনা?
মূলত মানুষ সম্পর্কিত পরিভাষা সমূহের অর্থের অস্পষ্টতার (Ambiguity of Meaning) কারণে মানুষ সম্পর্কিত একটি বিতর্কের সূচনা হয়। আর এই বিতর্কের মূল কথা হলো, মানুষ তার কর্মের ক্ষেত্রে স্বাধীন কিনা? আপনারা জানেন স্বাধীনতার সমস্যা সাধারণ একটি সমস্যা।
- আমরা দ্বীনের ক্ষেত্রে স্বাধীন কিনা?
- প্রাকৃতিক ঘটনা প্রবাহ সমূহের ক্ষেত্রে আমি স্বাধীন কিনা?
- কোনো অথরিটির ক্ষেত্রে আমরা স্বাধীন কিনা? ইত্যাদি।
এই সময়ে বিতর্কের মূল বিষয়বস্তু ছিল ইলাহি ইরাদা (আল্লাহর ইচ্ছা) থেকে মানুষ কি স্বাধীন? নাকি স্বাধীন নয়?
এই বিতর্ক খুব অল্প সময়ের মধ্যে আরেকটি বিষয় সামনে নিয়ে আসে সেটা হল,উপরোক্ত সমস্যা নিয়ে আলোচনা করার জন্য ইলাহি যাত কে বুঝা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। আল্লাহ কেমন একটি যাত বা সিফাত অর্থাৎ আল্লাহ কেমন এক সত্তা যার থেকে আমরা স্বাধীন কি অধীন এটা নিয়ে কথা বলছি। আল্লাহকে আমরা কীভাবে তাসাব্বুর করবো? যার প্রেক্ষিতে আমরা মানুষকে কর্তা (ফায়িল) বলব অথবা কর্তা (ফায়িল) নয় এই কথা বলব। মানুষের স্বাধীনতা নিয়ে বিতর্ক খুব অল্প সময়ের মধ্যে মুসলমানদেরকে তৃতীয় পর্যায়ে নিয়ে আসে সেটা হলো ইলাহি সিফাতসমূহ। আপনারা আবার মনে করবেন না যে এই সকল বিতর্ক হিজরী ১৫০ কিংবা ২০০ হিজরীতে হয়েছে। ৭০ এবং ৮০ হিজরীর দিকে মুসলমানগণ এই সব বিষয় নিয়ে বিতর্ক করেছে।
ইলাহি সিফাতসমূহঃ
আপনারা জানেন যে, পরবর্তীতে এ বিষয়ে আরও অনেক সিস্টেমেটিক চিন্তার উদ্ভব হয়। যেমন, মু’তাযিলাগণ বলেন, والله عالم والعلم نفسه অর্থাৎ আল্লাহ জ্ঞানী এবং তিনি নিজেই জ্ঞান। অথবা, والله عالم بمعني ليس بجاهل (আল্লাহ সর্বজ্ঞ, এটার অর্থ হল, তিনি কোনো বিষয়েই অজ্ঞ নন) ইত্যাদি।
তবে এই চিন্তা সমূহ সিস্টেমেটিকভাবে গঠিত হওয়ার পূর্বে মুসলমানগণ অন্য একটি সমস্যার সম্মুখীন হয়। সেটা হল,
ইলাহি সিফাতসমূহ নিয়ে আমরা কিসের ভিত্তিতে কথা বলি?
কোনো বিষয়ে কথা বলার জন্য আগে সেই বিষয়ে জানা প্রয়োজন, অর্থাৎ কোনো বিষয়ে জানা ছাড়া সেই বিষয়ে কোনো কিছু বলা সম্ভব নয়। গায়েবি বিষয়ে আমরা কীভাবে কথা বলব? জানা বিষয়সমূহকে ভিত্তি হিসেবে ধরে অজানা বিষয়ে জানার চেষ্টা করবো। ইলাহি সিফাত সমূহ গায়েবি এটা মোটামুটি নিশ্চিত, তাহলে আমরা কিসের ভিত্তিতে এই সকল সিফাত সমূহ নিয়ে কথা বলবো? আমাদের হাতে দুইটি ডাটা রয়েছে আমাদেরকে এই দুইটি ডাটার আলোকে কথা বলতে হবে।
প্রথমটি হলো পঞ্চেন্দ্রিয়। এর মাধ্যমে আমরা বাহ্যিক জগতকে জানতে ও চিনতে পারি।
দ্বিতীয়টি হলো ওহী। ওহীর মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে তাঁর নিজের সম্পর্কে জানিয়েছেন।
এই দুটি প্রকারের তথ্যের উপর ভিত্তি করে আল্লাহ সম্পর্কে আলোচনা শুরু হয়। পরবর্তীতে এদের নামকরণ করা হয় কালামবিদ নামে । প্রথমে এই সকল বিষয় নিয়ে যারা আলোচনা করেন তারা কালামবিদ নন। এই সব চিন্তা মূলত ১১০ হিজরী সালের দিকে ইলমুল কালাম রূপে আত্মপ্রকাশ করে এবং এসব বিষয় নিয়ে যারা কথা বলতেন তাদেরকে মুতাকাল্লিম নামে অভিহিত করা হয়।
জ্ঞানের সমস্যাঃ
মুসলমানগণ এরপর যে সমস্যাটির সম্মুখীন হয় সেটি হল, দুনিয়ার (ফিজিক্যাল ওয়ার্ল্ড) ক্ষেত্রে ব্যবহৃত দলীল সমূহকে যখন আমরা স্রষ্টাতত্ত্বের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করব তখন আমরা আল্লাহকে কীভাবে জানবো? এই বিতর্ক মুসলমানদেরকে জ্ঞানগত একটি সমস্যার সামনে এসে দাঁড় করিয়ে দেয়। অর্থাৎ,
- জ্ঞান কি সম্ভব?
- একটি বিষয়কে আমরা কীভাবে জানবো? কোন কোন ক্ষেত্রে জ্ঞানের উৎপত্তি হয়?
ফলশ্রুতিতে যে বড় সমস্যাটি এরপর মুসলমানদের সামনে এসে দাঁড়ায় সেটা হল জ্ঞানের সমস্যা। ওয়াসিল বিন আতা এই বিষয়ে একটি গ্রন্থ রচনা করেন এবং এর নাম দেন, كتاب الطريق الي معرفة الحق (কিতাব আত তারিক ইলা মা’রিফাতিল হাক্ব)। ওয়াসিল বিন আতা ১৩০ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন। জ্ঞানের ইতিহাসের দিকে যদি তাকাই তাহলে দেখতে পাই যে ‘জ্ঞানতত্ত্ব’ তথা এপিস্টেমোলজি নিয়ে সর্বপ্রথম লিখিত গ্রন্থ। এই প্রশ্নের তিনি জবাব দেন এইভাবে ‘দৃশ্যমান (শাহীদ) বিষয় সমূহের উপর ভিত্তি করে আমরা গায়েব বা অদৃশ্যমান বিষয় সমূহকে জানতে পারি’। এইভাবে জবাব দেয়া কারণে এই বিষয়কে দালীলিকভাবে মানুষের সামনে তুলে ধরার জন্য ‘থিওরিক ফিজিক্স’ (Theoretical Physics) নিয়ে কাজ করা শুরু করেন।
‘থিওরিক ফিজিক্স’ (Theoretical Physics)-
অর্থাৎ প্রকৃতিকে বিশ্লেষণ করা। জ্ঞানের সমস্যাকে সমাধান করার জন্য তারা প্রকৃতিকে নিয়ে গবেষণা করতে বাধ্য হন।
- আমরা যে দুনিয়ায় বসবাস করছি এটা কেমন একটি দুনিয়া?
- এই দুনিয়াকে আমরা কীভাবে চিনি ও জানি?
এই জন্য কালামবিদগণের নিকট ফিজিক্যাল দুনিয়াকে প্রথমত, جوهر ও عرض তথা যাত ও সিফাত এই দুই ভাগে ভাগ করেন এবং এটা নিয়ে আলোচনা করেন। এরপর, দৃশ্যমান, শ্রবণযোগ্য, স্পর্শযোগ্য, স্বাদযোগ্য, গন্ধযোগ্য সমগ্র বস্তুগত বিশ্বকে এই গ্রুপসমূহে ভাগ করেন। অর্থাৎ চক্ষু, কর্ণ, জিহ্বা, নাসিকা, ত্বকের মাধ্যমে অর্জিত বিষয়সমূহকে আলাদাভাবে বিভাজিত করেন। এই জন্য কালামের গ্রন্থসমূহ শুরু থেকে নিয়ে দৃশ্যমান বিষয়সমূহের মধ্য থেকে ‘রঙ’ নিয়ে আলোচনা করে আসছে, শ্রবণযোগ্য বিষয়সমূহ থেকে ‘আওয়াজ বা সুর’ নিয়ে আলোচনা করে আসছে। যেমন, স্বাদ নিয়ে। স্বাদ কেমন? আমরা স্বাদ কীভাবে পাই? কি কি ধরণের স্বাদ আছে? শরহে মাওয়াকিফ এবং তার পূর্বে লিখিত গ্রন্থসমূহে ঝাল, মিষ্টি, টক ইত্যাদি তথা স্বাদের প্রকারভেদসমূহ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। অর্থাৎ প্রকৃতিকে (Material World) কে মানুষের পঞ্চেদ্রিয়ের আলোকে শ্রেণিবিন্যাস করেন এবং এর উপর ভিত্তি করে আমরা কীভাবে দলীল প্রণয়ন করব এটার ভিত্তি স্থাপন করেন করেন।
ইলাহি যাত ও সিফাতঃ
প্রকৃতিকে বিশ্লেষণ করার পরে পুনরায় তারা ইলাহি যাত ও সিফাতের দিকে ফিরে আসেন। এখন আসুন আমরা পুনরায় প্রথম সমস্যার দিকে ফিরে যাই, সমস্যা কোথা থেকে শুরু হয়েছিল? সমস্যা শুরু হয়েছিল ‘মানুষের পরিচয়দানকারী বা সংজ্ঞায়নকারী কোরআনী পরিভাষাসমূহের অর্থের অস্পষ্টতা (Ambiguity of Meaning)’ থেকে। অর্থাৎ, মু’মিন, মুনাফিক এবং কাফের থেকে তথা এই সব পরিচয়কে বলা হয় আসমায়ে শারইয়্যা। সমস্যা এটা থেকে শুরু হয়েছিল। এই সমস্যার মূল উৎস হলো ইমামতের সমস্যা।
এ কারণে কালাম বিষয়ক সকল গ্রন্থকে এভাবে সাজানো হয়েছে। ইলাহি যাতের সাথে সম্পৃক্ততার কারণে নবুয়ত ও আখেরাতকে আলাদাভাবে উল্লেখ করা হয়নি। হিজরী ১৩০ সালে পৌঁছার পর মুসলমানগণ এই সব বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন এবং এই সব বিষয়ে থিওরী প্রস্তুত করেন। তবে ইলমুল কালামকে এইভাবে সিস্টেম্যাটিক অবস্থায় নিয়ে আসেন আবুল হুজাইল আল-আল্লাফ (তিনি ১৩৫ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন এবং ২৩৫ হিজরীতে মৃত্যু বরণ করেন)।
ইলমুল কালামের প্রতিষ্ঠাকালীন সময়ে তথা ২০০ হিজরী পর্যন্ত কালামবিদগণ কিছু কিছু থিওরীকে সামনে নিয়ে আসেন। যেমন, ইলাহি সিফাত সংক্রান্ত বিষয়ে তিনটি থিওরী আবিষ্কার করেন। মূলত প্রথম দিকে থিওরিক ফিজিক্স সবচেয়ে দোদুল্যমান বিষয়ের সমূহের একটি ছিল। অর্থাৎ ফিজিক্স দুনিয়াকে কীভাবে ব্যাখ্যা করবে? থিওরিক ফিজিক্সে যে সব তত্ত্ব আবিস্কৃত হয়-
১. যৌগিকতা (এটা ছিল আমর বিন দিরারের থিওরী)।
২. এটমিজম তথা পরমাণুবাদ (এটা ছিল আবুল হুজাইলের থিওরী)।
৩. যুহুর-কুমুন (নাজ্জাম এবং জাহজ)।
পরবর্তীতে মুসলিম চিন্তাবিদদের মধ্যে এটমিজম থিওরী গ্রহণ যোগ্যতা লাভ করে। নাজ্জাম এবং জাহজের জন্ম হলো ১৪০-১৫০ হিজরীর দিকে। ১৬০ এর দিকে জাহজ জন্মগ্রহণ করেন। ২০০ হিজরী সালের দিকে নাজ্জামের বয়স ৫০ বছর। পরিপক্ক একজন আলেম বলা চলে। সিস্টেমেটিক অনুবাদের যুগে আবুল হুজাইলের বয়স ৭৫ বছর।
ইবনুল মুকাফফা পাহলভি ভাষা থেকে ঈসাগুজি এবং এরিস্টটলের বই অনুবাদ করেন। কিন্তু এই সব বই কতটা প্রচারিত ও প্রসারিত হয়েছিল সেটা জানা যায় না। তবে একটি বিষয় ছিল সেটা হল এই সকল থিওরীকে ডেভলপ করার সময় মুসলিম আলেমগণ তাদের আগের থিওরীসমূহ সম্পর্কে জানতেন। কারণ তাদের ব্যবহৃত এটমিজম হয় ভারতীয় এটমিজম (পরমাণুবাদ) না হয় গ্রীক এটমিজম। তবে গ্রীক হওয়ার সম্ভাবনা বেশি।
তবে এখানে আরও একটি বিষয় রয়েছে, সেটা হল এই সব চিন্তাবিদগণ দীর্ঘদিন বেঁচে ছিলেন। জাহজ ২৫০ হিজরি পর্যন্ত বেঁচে ছিলেন। নাজ্জাম ২৪০ হিজরি পর্যন্ত। আবুল হুজাইল ২৩৫ হিজরি পর্যন্ত বেঁচে ছিলেন। ফলশ্রতিতে গ্রীক দর্শনের সকল অনূদিত বই পুস্তক সমূহ অনুবাদ হওয়া পর্যন্ত তারা বেঁচে ছিলেন। তারা তাদের থিওরির জবাব দেন, ব্যাখ্যা করেন। তবে তারা নিজেদের জ্ঞানের উপর ভিত্তি করে জবাব দিয়েছেন নাকি অন্য কোনো থিওরির উপর ভিত্তি করে দিয়েছেন সেটা আমরা জানি না। তবে আমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ হল এই বিষয়সমূহ তথা-
১.মানুষ পরিচয়দানকারী বা সংজ্ঞায়িতকারী কোরআনী পরিভাষা সমূহের অর্থের অস্পষ্টতা (Ambiguity of Meaning)
২.স্বাধীনতার সমস্যা। অর্থাৎ, মানুষ তার নিজের কর্মসমূহের কর্তা (ফায়িল) কিনা?
৩.ইলাহী সিফাতসমূহ
৪.জ্ঞানের সমস্যা
৫.থিওরিক ফিজিক্স’ (Theoretical physics),
৬.ইলাহি যাত ও সিফাত,
৭.ইমামতের বিষয়।
২০০ হিজরীর মাঝামাঝি সময়ের মধ্যেই এগুলো নিয়মতান্ত্রিক অবস্থায় চলে আসে। যদি চিন্তা করে দেখেন তাহলে দেখতে পাবেন যে, এই সব বিষয়ের প্রায় সবগুলোই মানুষের স্বাধীনতার বাহিরের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব (ওজুদ) সমূহ নিয়ে আলোচনা করে ।
প্রাথমিক সময়ের তথা হিজরি ১৫০ এবং হিজরি ১৬০ এর দিকে যদি তাকাই তাহলে দেখতে পাই যে, কালামবিদগণ ওজুদের (সৃষ্টি, অস্তিত্ব) সমগ্র বিষয়কে নিয়ে আলোচনা শুরু করেন। আল্লাহর যাত ও সিফাত থেকে শুরু করে রং, গন্ধ, স্বাদসহ সকল কিছুকে নিয়ে তারা নিয়মতান্ত্রিকভাবে গবেষণা শুরু করেন।
ইলমুল কালাম কি নিয়ে আলোচনা করেঃ
মানুষের ইচ্ছা সংক্রান্ত অধ্যায়সমূহ যেন আপনাদেরকে ভ্রমের মধ্যে ফেলে না দেয়। মানুষের ইচ্ছার ফলে যে সব বিষয় সৃষ্টি হয় সে সব বিষয় নিয়ে ইলমুল কালাম আলোচনা করে না। অর্থাৎ ইলমুল কালাম আখলাক এবং রাজনীতি নিয়ে আলোচনা করে না। কালামের গ্রন্থসমূহে ইমামত নিয়ে আলোচনা করার মূল কারণ হচ্ছে শিয়ারা ইমামতকে আকীদার সাথে সম্পৃক্ত একটি বিষয় হিসেবে উপস্থাপন করার কারণে বাধ্য হয়ে অনিচ্ছাকৃতভাবে ইমামতকে স্থান দিতে হয়েছে। সত্যিকার অর্থেই মানুষের ইচ্ছায় যে সব বিষয় সৃষ্টি হয়ে থাকে সে সব বিষয় নিয়ে কালাম আলোচনা করে না। অর্থাৎ ইলমুল কালাম একেবারেই সুস্পষ্টভাবে পরিপূর্ণভাবে নাজারি (তত্ত্বীয়) একটি ডিসিপ্লিন হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই নাজারি ডিসিপ্লিন মানুষের ইচ্ছাকৃতভাবে করার ফলে যে সব কাজ সৃষ্টি হয় এর বাহিরের যত ধরনের মওজুদ (সৃষ্টি, অস্তিত্ব) রয়েছে সে সব বিষয়সমূহকে নিয়ে কাজ করে থাকে।
দ্বিতীয়ত, কালামের মূলতত্ত্বকে বুঝা খুবই জরুরী। কারণ হচ্ছে, কালাম এমন একটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করে যার মাকসাদ বা উদ্দেশ্য হচ্ছে জ্ঞান বা ইলম। অর্থাৎ আচার আচরণ নয় যার মাকসাদ হচ্ছে জ্ঞান এমন একটি বিষয় নিয়ে ইলমুল কালাম আলোচনা করে থাকে।
ক্ল্যাসিক দুনিয়ায় ইলমুল কালাম এর মূল উদ্দেশ্য ছিল, সে যে বিষয়টি নিয়ে গবেষণা হচ্ছে, সে বিষয়টি সম্পর্কে সঠিক কোনো তথ্য উপাত্ত বের করা। সঠিক একটি তথ্য কিংবা সেই ব্যাপারে সঠিক একটি বিশ্বাসে উপনীত হওয়া। কালাম এর মূল উদ্দেশ্য হলো এটাই। এজন্য ফিজিক্স সংক্রান্ত অধ্যায় হোক কিংবা মেটাফিজিক্সের অধ্যায় হোক অথবা সমগ্র সৃষ্টিকে বৈশিষ্ট্যমন্ডিতকারী অন্টোলজির অধ্যায় হোক না কেন কালামের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে সে সব বিষয় সম্পর্কে একটা সিদ্ধান্ত বা জ্ঞানে উপনীত হওয়া।
এক অর্থে বলতে গেলে ইলমুল কালাম মোটামুটি দ্বিতীয় হিজরী শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে এই বিষয়গুলোকে পূর্ণতায় পৌঁছে দেয়। আবুল হুযাইল ইলমুল কালামের জ্ঞান, নাজার (তত্ত্ব), উমুরে আম্মা বা অন্টোলজি, জাওহার, আরায, ইলাহি যাত ও সিফাতসমূহ, নবুয়ত, মায়া’দ, আসমায়ে শারইয়্যা এবং ইমামত এই সব বিষয়কে পূর্ণতায় পৌঁছে দেন। মূলত ইলমুল কালাম এর সঠিক ধারাবাহিকতা এটাই। আর এই ধারাবাহিকতাকে সুন্দরভাবে সুনিপুণভাবে সাজান হচ্ছে আবুল হুযাইল আল-আল্লাফ। দ্বিতীয় হিজরীর শেষের দিকে তিনি এটাকে সম্পন্ন করে লিপিবদ্ধ করেন।
আপনারা এটা জানেন যে, মু’তাযিলা চিন্তাধারায় ওয়াসিল বিন আতার পরে সবচেয়ে বড় চিন্তাবিদ হলেন আবুল হুযাইল আল্লাফ। ফলশ্রতিতে দ্বিতীয় হিজরীর মধ্যেই মুসলিম কালামবিদগণ এই সকল ডিসিপ্লিন কে সুন্দরভাবে বিশ্লেষণ করার জন্য একটি ধারাকে তৈরি করতে সক্ষম হন।
তবে এই নাজারি (তাত্ত্বিক) ডিসিপ্লিনের একটা দাবি রয়েছে। মূল বিষয়টিকে সঠিকভাবে বুঝার জন্য এই দাবিকে খুব ভালোভাবে উপলব্ধি করতে হবে। এই নাজারি ডিসিপ্লিন বলে থাকে যে, দ্বীন মূলত দুটি বিষয়ের সমন্বয়ে গঠিত। একটি হচ্ছে ঈমান আরেকটি হচ্ছে আমল। আমি ঈমান সম্পর্কিত অধ্যায়ে বিশ্বাস করা প্রয়োজন এমন বিষয় সমূহকে নির্ণয় করছি একইসাথে এই সব বিষয়সমূহ ঈমান সম্পর্কিত বিষয়ে কোন কোন শর্তের আলোকে বোঝা যাবে এগুলো আমি লিপিবদ্ধ করছি। লক্ষ্য করুন; এই অর্থের দিক থেকে ইলমুল কালাম একইসাথে তাফসীর। এই বিষয়টিকে ভালোভাবে বোঝা ছাড়া তাফসীরের ইতিহাস থেকে এমন এমন বিষয় বের করা সম্ভব, যা বুঝা খুবই কঠিন হয়ে যাবে। যেমন, একজন মুফাসসির হওয়ার অর্থ কি এটা বুঝতে পারবেন না।
এটি খুবই ইন্টারেস্টিং একটি বিষয়। আপনারা জানেন যে, আহলুস সুন্নতের ‘কাসব’ থিওরী রয়েছে। এই ‘কাসব’ থিওরী মুতাযিলাদের তৈরি করা একটি থিওরী। দিরার বিন আমর এই থিওরীর প্রবক্তা। দিরার বিন আমরের কাসব থিওরির মূল কথা হচ্ছে, কোরআনে কারীমে মানুষ সম্পর্কিত সকল ক্রিয়া (ফে’ল) সমূহ আমরা এই থিওরীর আলোকে বুঝব।
ইলাহি সিফাত সম্পর্কিত বিষয়গুলোও এর আলোকে বুঝতে হবে। যেমন, ওয়াল্লাহু আলিমুন ওয়াল ইলমু বি নাফসুহু, এই কথাটি। এখানে বলা হচ্ছে যে, কোরআনে কারীমে এবং হাদীসে, যেভাবেই উল্লেখ করা হোক না কেন, আল্লাহর সিফাত সম্পর্কিত সব আয়াত কিংবা নসকে এই মূলনীতির আলোকে বুঝব। এই অর্থে ইলমুল কালাম সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করতে হবে, এমন অবজেক্টসমূহ সম্পর্কে থিওরিসমূহের সামগ্রিকতার মতো। কালাম নিজেকে এই সব বিষয় সম্পর্কে ব্যাখা দান করতে সক্ষম বলে দাবী করে থাকে। সিফাত সংক্রান্ত থিওরী, যাত-সিফাত অন্টোলজি, নবুয়ত সম্পর্কিত থিওরী,, মানুষের কাজ সম্পর্কিত থিওরী এবং একইসাথে নসসমূহকে বুঝার জন্য চাবিকাঠি দিয়ে থাকে। কিন্তু এই বোধগম্যতা হলো ইসতিদলালী।
ইসতিদলালী বোধগম্যতা হলো, মুতাকাল্লিমগণ চিন্তা করেন যে তাদের হাতে কিছু ডাটা রয়েছে, সেই ডাটাকে একটি ভাষায় প্রকাশ করা হয়েছে তথা ওহীকে একটি ভাষায় প্রকাশ করা হয়েছে। আর ভাষা বুঝার শর্ত হল অভিজ্ঞতা। যদি অভিন্ন কোনো অভিজ্ঞতা না থাকে তাহলে ভাষা বুঝা সম্ভব নয়।
অভিজ্ঞতার আবার দুটি ক্ষেত্র আছেঃ
- আমাদের দৈনন্দিন ভাষায় ব্যবহার করে থাকি এমন অভিজ্ঞতা।
- অভিজ্ঞতাকে ব্যবহার করে বের করা আকলী ফলাফলসমূহ। অর্থাৎ আকলের নির্দিষ্ট কিছু অভিজ্ঞতার দরকার। কালামবিদগণ বলেন, আল্লাহ ও আলমের (জগত) মধ্যকার সম্পর্ক, আল্লাহ এই আলমের সাথে কেমন ব্যবহার করেন, এই সম্পর্কিত বিষয়ে এবং আখেরাত সম্পর্কিত আয়াতসমূহকে ইলমুল কালামে যে ফ্রেম তৈরি করেছি সে ফ্রেমের আলোকে বুঝতে হবে।
ইলমুল কালামে এই কাঠামো কিসের আলোকে তৈরি করা হয়েছে?
মূলত নসকে বুঝতে হলে নস যে বিষয়ে কথা বলেছে সেই বিষয়কে বুঝতে হবে। যেমন আল্লাহকে না চিনে, আল্লাহ সম্পর্কিত একটি নসকে সঠিকভাবে বুঝতে পারব না। ফলশ্রতিতে আয়াতসমূহ এক দিক থেকে মুভমেন্ট পয়েন্ট, অন্য অর্থে আয়াতের উল্লিখিত বিষয় মুভমেন্ট পয়েন্ট হয়ে বিষয়টিকে বুঝতে সাহায্য করে। এই হল ইসতিদলালী একটি আকল।
আচ্ছা, এখন কথা হল, দ্বীনকে কি ইসতিদলালী আকলের মাধ্যমে বুঝা সম্ভব?
প্রশ্ন এখানেই। আমরা দ্বীনকে কি ইসতিদলালী আকলের মাধ্যমে বুঝব নাকি অন্য কোনো পন্থা আছে? অনেক ঐতিহাসিক কারণও রয়েছে, আপনারা জানেন যে, ইলমুল কালামের সাথে সমান্তরালভাবে যুহুদ আন্দোলনের সৃষ্টি হয়। শুরুতে যুহুদ আন্দোলনকে একটি বিদ্রোহী আন্দোলনের মতো দেখা যায়। অর্থাৎ, ইসলামী রাষ্ট্রের তৈরি করা সিস্টেম কোনো কোনো শ্রেণির ধনী হওয়ার কারণ হয়। যেমন আপনারা জানেন যে, রাসূল (স.) গনীমতকে বণ্টন করার সময় বদরের সাহাবীদেরকে প্রাধান্য দিতেন। বিভিন্ন বিজিত অঞ্চল থেকে গণীমতের মাল আসার ফলে মদিনা অনেক সমৃদ্ধশালী একটি স্থানে পরিণত হয়। অনেক কঠিন সময়ে জিহাদে অংশগ্রহণকারী সাহাবীদের নাতি নাতনীরা সম্পদশালী হয়ে ওঠে। বলা হয়ে থাকে, মদিনার আশেপাশে বিনোদন কেন্দ্র গড়ে ওঠে। এমন কি আস্তে আস্তে জীবন ধারায় দুনিয়াদারী ব্যাপক বিস্তার লাভ করে। এই অবস্থা থেকে উত্তোরণের জন্য যুহুদ আন্দোলনের উৎপত্তি হয়।
তবে যুহুদ আন্দোলনকে যদি শুধুমাত্র আখলাকী একটি আন্দোলন হিসেবে বিবেচনা করি তাহলে পরবর্তীতে এটাকে সামগ্রিকভাবে ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়। যুহুদ আন্দোলন শুরু থেকেই ফুকাহা এবং মুতাকাল্লিমদেরকে চ্যালেঞ্জ করে বলেন- এসব চিন্তার মাধ্যমে মা’রেফাতুল্লাহয় পৌঁছা সম্ভব নয়। তাহলে কীভাবে বুঝব? তারা জবাবে বলে এর একটাই সূত্র আছে। এই দ্বীনের নসসমূহকে ভালোভাবে কে বুঝেছেন? রাসূল (স.) বুঝেছেন। এটা ফিলোসফির ধারায় মেটাফিজিক্স আর দ্বীনের ক্ষেত্রে পয়গাম্বর একই বিষয়। এটা অনেক বড় একটি বিষয়। বাক্যের অর্থ কে সঠিকভাবে বুঝে? কাউকে না কাউকে সঠিকভাবে বুঝা প্রয়োজন। আর দ্বীনের ক্ষেত্রে সবচেয়ে ভালো বুঝেন পয়গাম্বর। আর দ্বীনের তত্ত্বীয় ও কার্যগত হায়াতকে পরিচালনা করার জন্য জ্ঞানের উত্তরাধিকারী হওয়া প্রয়োজন। কালামের কথা হলো, এটা ইসতিদলালের মাধ্যমে তৈরি/অর্জিত হয়ে থাকে। ইসতিদলালের মাধ্যমে তৈরি হওয়া জ্ঞানকে আমাদের জীবনের সাথে মেলবন্ধন করে দিতে পারি। কালামবিদগণ বলেন, এক দিকে হল ঈমান, আর এই ইসতিদলালের মাধ্যমেই সহীহ একটি ঈমানে আমরা পৌঁছাতে পারি। অপরদিকে ঈমানের দাবিসমূহকে জীবনে বাস্তবায়ন করা। এটাই হল মুমিন হওয়ার মূল অর্থ। এর বিপরীতে যুহুদ আন্দোলনের যারা তারা বলেন, “এরকম ইসতিদলালের মাধ্যমে আল্লাহকে জানা সম্ভব নয়। এটা সঠিক কোনো পন্থা নয়, এর মাধ্যমে তোমরা শুধুমাত্র শব্দ নিয়ে খেলা করতে পারবে।” দর্শনের ইতিহাসে নমিনালিজমের মতো একটি সমালোচনা তাদের সামনে দাঁড় করায়। তারা বলেন, “তোমাদের হাতে যা আছে এগুলো শুধুমাত্র ওয়াসিফ বা গুণবাচক বিষয়। ভাষা দিয়ে বর্ণনা করে যাচ্ছ! এর অর্থ কোথায়?” অর্থ কেবলমাত্র অভিজ্ঞতার মাধ্যমেই অর্জিত হতে পারে। কোনো ব্যক্তি আল্লাহর সাথে কথা বলা ছাড়া, (আল্লাহর সাথে কথা বলার অর্থ এখানে অস্পষ্ট) এটা কীভাবে বুঝবে? যাইহোক এটা অভিজ্ঞতার মাধ্যমে অর্জন করতে হবে। আল্লাহর সাথে কথা বলার বিষয়টি পয়গাম্বরের ক্ষেত্রে ওহী, তবে কারো কারো ক্ষেত্রে বা মানুষের ক্ষেত্রে ইলহাম। অথবা কারোর ক্ষেত্রে স্বপ্ন হতে হবে। রাসূল (স.) বলেছেন আমার উম্মাহর মধ্যে সাদিক স্বপ্ন অব্যাহত থাকবে। এরকম হতে হবে। অর্থাৎ কোনো না কোনোভাবে রাসূল (স.)-এর অভিজ্ঞতার অংশীদার হতে হবে। এই জন্য অংশীদার হতে হবে যেন রাসূল (স.) যে সকল বিষয় যেভাবে বুঝছেন সেটাকে ধারণ করতে পারি। তা না হলে এই দুনিয়াতে ইহসানের পর্যায়ে উপনীত হওয়া সম্ভব নয়। পরবর্তীতে এটা তাসাউফে পরিণত হয়।
যুহুদ আন্দোলনের শুরু থেকেই দুটি মৌলিক দাবি ছিল-
- পদ্ধতি বা পন্থা, হাকীকতে পৌঁছার পন্থা কি হবে? এই প্রশ্নের জবাব।
- এই পন্থার মাধ্যমে যে জ্ঞান অর্জিত হবে এর নাম কি হবে? এই প্রশ্নের জবাব। এই দ্বিতীয় বিষয়টি হল মেটাফিজিক্স।
অর্থাৎ একই সাথে ওজুদ বা অস্তিত্ব সম্পর্কে কুল্লি ইদরাক (সামগ্রিক উপলব্ধি) সম্পর্কে একটি দাবির মালিক এই যুহুদ আন্দোলন, একইসাথে এই কুল্লি ইদরাক কীভাবে অর্জন করতে হবে এই সম্পর্কিত পদ্ধতির দাবিকারী।
একটি উদাহরণের মাধ্যমে এই দাবিকে আরও ভালোভাবে বুঝা সম্ভব। ইমাম মালিকের সময়ে ওমরী নামে একজন যাহিদ লোক ছিলেন। তিনি ইমাম মালিকের নিকট একটি চিঠি লেখেন। চিঠিতে বলেন, “আপনার সম্পর্কে অনেক কথা শুনে থাকি যতটুকু জানি আপনি অনেক বড় একজন আলেম। কিন্তু আল্লাহকে সঠিকভাবে জানা এবং রাসূলুল্লাহ (স.) ইসলামের সঠিকভাবে অনুসরণ এর মাধ্যমে সম্ভব নয়। আপনি যে সব কাজ করছেন এগুলোর মাধ্যমে আসলে আল্লাহকে সঠিকভাবে চেনা সম্ভব নয়। ফিকহের মাধ্যমে ইসলামকে সঠিকভাবে বোঝা সম্ভব নয়। আমার মত জীবনযাপন করুন, তাহলে এভাবে আপনি মা’রেফাতুল্লাহ-এ পৌঁছাতে পারবেন’।
ইমাম মালেকও তার এই কথার জবাব দেন,
“প্রথমে তাকে ধন্যবাদ দিয়ে বলেন, আপনি আমার সম্পর্কে ভালো বলেছেন এজন্য আপনাকে ধন্যবাদ তবে আল্লাহতে পৌঁছার জন্য বা মা’রেফাতুল্লাহর জন্য অসংখ্য পথ রয়েছে। আল্লাহ প্রতিটি মানুষকেই তার সাথে সম্পর্ক স্থাপন করার জন্য একটি পন্থা দিয়ে থাকেন, এটি তার অনেক বড় একটি রহমত। আল্লাহ আমাকে এই পথের মাধ্যমে তাকে চেনার একটি পথ দিয়েছেন, আমি এই পথের মাধ্যমে আল্লাহকে চিনতে পারবো বলে আশা করি। তিনি আপনাকে ওই পথ দান করেছেন”।
তবে ইমামের শেষের কথাটি খুবই সুন্দর। ইমাম মালেক তাকে বলেন, তবে জেনে রাখুন এই পথসমূহের কোনোটাই কারোর চেয়ে শ্রেষ্ঠ নয়। এখানে মূল হচ্ছে মাকসাদ। মাকসাদ বা উদ্দেশ্য অর্জিত হওয়ার পরে এসব পথের প্রতিটিই সমান।
এই যুহুদ আন্দোলন দ্বিতীয় হিজরী শতাব্দীর মধ্যবর্তী সময় থেকে নিয়ে ইলমুল কালামের মতই নিয়মতান্ত্রিকভাবে তার পরিভাষাসমূহকে আস্তে আস্তে উন্নত করতে থাকে। তাদের দাবি অভিজ্ঞতা হওয়ার কারণে, যুহুদ আন্দোলনের পরিভাষাসমূহ মানুষ সম্পর্কিত পরিভাষা ছিল। কারণ আল্লাহর সামনে মানুষের অবস্থাসমূহকে পর্যবেক্ষণ করার মাধ্যমে বা পর্যবেক্ষণ করেই কোন ধরনের জ্ঞান অর্জিত হচ্ছে এটা বের করা সম্ভব। এক্ষেত্রে তাঁরা ইখলাসকে, ইহসানকে, হাসরাতকে পর্যবেক্ষণ করেন।
অর্থাৎ ইবাদতসমূহ কীভাবে তার নিজস্বরূপে বহিঃপ্রকাশ ঘটাবে এটা কে জানার জন্য তারা এই পন্থা অবলম্বন করে। কোনো কাজ বা আচরণের মধ্যে যদি অন্য কেনো কিছু প্রবেশ করে তার বিকাশকে তার নিজস্বতা থেকে দূরীভূত করে, যেমন, কোন বিষয়সমূহ নামাজকে নামাজ হওয়া থেকে দূরে করে দেয়, রোজাকে রোজা হওয়া থেকে দূরীভূত করে দেয়, যাকাতকে যাকাত হওয়া থেকে বঞ্চিত করে এই বিষয়গুলো ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করেন। কোন সময় ঐ সব ইবাদতকে তার সত্যিকার রূপে ধরা যাবে এটাকেই তারা নির্দিষ্ট করার চেষ্টা করেছেন ।
এজন্য প্রথম যুগের লেখা তাসাউফের বই মূলত মানুষের অবস্থা সম্পর্কে। খেলার ছলে কিংবা কোনো কারণ ছাড়া এমনিতেই তারা এই সব অবস্থাকে পর্যবেক্ষণ করতেন না। আর এই অবস্থা কোন ধরনের জ্ঞানকে সৃষ্টি করে এটাকেই তারা মূলত সামনে নিয়ে আসে। যেমন, ইখলাসের অবস্থা আমাদের মধ্যে কোন ধরনের জ্ঞানের সৃষ্টি করে? ইত্যাদি। ক্রিয়ার কর্তা হিসেবে সেই ক্রিয়া সংগঠিত করার সময় আল্লাহর সামনে আমাদের কোন কোন অবস্থার সৃষ্টি করে? আর এই অবস্থাসমূহ আমাদের মধ্যে কোন ধরণের জ্ঞানের সৃষ্টি করে?
সুলুক মূলত প্রথমে এটাই পর্যবেক্ষণ করে। সুলুক হলো; সম্পাদিত ইবাদতসমূহে, ইবাদতের সাথে ইবাদত কর্তৃক সৃষ্ট মা’রেফাতের মধ্যে সম্পর্ককে পর্যবেক্ষণ করা। কাশফুল মাহজুব হল, মুতাকাদ্দিমুন সময়ে লেখা সবচেয়ে সেরা বইসমূহের একটি। সকল ধারাকে তাদের কেন্দ্রে স্থাপিত পরিভাষাসমূহের মাধ্যমে বুঝানো হয়েছে এই বইয়ে। কোন পরিভাষা কোন ধরণের জামায়াত সৃষ্টি করে এবং কোন মা’রেফাত তৈরি করে। তাসলিম, সাহু, সাকার ইত্যাদি। তারা মূলত, কুরবুল নাওয়াফিল হাদীসের উপর ভিত্তি করে তাদের চিন্তাকে তুলে ধরে। এটাই হল তাদের মূল চিন্তা।
হক্বের মাধ্যমে হক্ব হওয়া। সবকিছুর পূর্বে হক্বকে দেখা এবং সবকিছুতেই হক্বকে দেখা। সবকিছুর পরও হক্বকে দেখা। সকল যুহুদ আন্দোলনের মাকসাদ/উদ্দেশ্যকে এবং অবস্থাকে সংক্ষিপ্তকারী একটি বাক্য এটি। এই বাক্যটি হযরত আবু বকর (রা.) নিকট থেকে এসেছে।
যুহুদ আন্দোলন আল্লাহ এবং মানুষের মধ্যকার সম্পর্কের ক্ষেত্রে এটাকে মূল উদ্দেশ্য হিসেবে নিয়ে থাকে। বান্দার অবস্থা হিসেবে, আওয়াল, আখের, যাহের, বাতেন সর্বাবস্থায় আল্লাহ’ই হবেন সাথী। এটা এই অর্থে আসলে সকল ধরণের দ্বীনি পরিভাষা, সকল ধরণের দ্বীনি উপলব্ধি, ঐ পরিভাষা এবং ইদরাক সম্পর্কিত অভিজ্ঞতা থেকে তৈরি হতে পারে। অভিজ্ঞতা থেকে উৎসারিত হওয়ার আগ পর্যন্ত মাখলুক সম্পর্কিত ইদরাককে (উপলব্ধি) আল্লাহর নিকটে নিয়ে যাই।
তাসাউফ কালাম থেকে ভিন্ন, এর দুটি ধারা রয়েছে। একটি হল মানুষের ইরাদা/ইচ্ছার বাহিরে অবস্থানরত অস্তিত্ব সম্পর্কে। আল্লাহ ও মহাবিশ্বের মধ্যকার সম্পর্ক। মা’রেফাতুল্লাহ এর অন্তর্গত একটি বিষয়। এখানে মূল বিষয় হল আল্লাহ আলম তথা মহাবিশ্বের সাথে কেমন আচরণ করে এটাকে বুঝা। এখানে মূল পরিভাষা কি? যেমন মুতাযিলাগণ বলেন,
আলেমদের সাথে আল্লাহর আচরণের মূল পরিভাষা হল ‘আদালত’। আশয়ারীগণ বলেন, ‘কুদরত’, ইমাম মাতুরিদি বলেন, ‘হিকমত’, হাসান বসরি বলেন ‘মারহামাত’। কোন পরিভাষার আলোকে আল্লাহ ও মহাবিশ্বের মধ্যকার সম্পর্ককে বুঝব? এর অর্থ হল এই পরিভাষাকে কেন্দ্রে স্থাপন করে সকল নসকে এই পরিভাষার আলোকে ব্যাখ্যা করবো। এই পরিভাষা কেন্দ্রে নেই এমন সকল নসকে মাজায হিসেবে ব্যাখা করবো।
আমরা যে পরিভাষাকে কেন্দ্রে স্থাপন করবো সেটা একইসাথে সৃষ্টিকে বোঝার জন্য এবং আল্লাহ ও আলমের মধ্যকার সম্পর্ককে বুঝার ক্ষেত্রে নসসমূহকে বুঝার জন্য চাবিকাঠি স্বরূপ। এই খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি পয়েন্ট। এটা দ্বীনি জ্ঞানকে হাকিকতের সন্ধানী জ্ঞান হিসেবে স্থাপন করে। দ্বীনি জ্ঞান শুধুমাত্র নসসমূহকে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করার জ্ঞান নয়। এটা একই সাথে নস আমাদেরকে যে দুনিয়া সম্পর্কে খবর দিয়েছে সেই দুনিয়া সম্পর্কে গবেষণাকারী ঐ সব বিষয়ের হাকীকত সম্পর্কে চিন্তাকারী একটি জ্ঞানে রূপান্তরিত হয়। হাদীসশাস্ত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ওয়া সাল্লাম এর কথাকে নিয়ে, তার কথার বিশুদ্ধতাকে নিয়ে কাজ করা হয়। ফলশ্রতিতে হাদীস একইসাথে মুতলাকভাবে এই কথাকে বর্ণনা করার শর্তসমূহে বিশ্লেষণ করে আবার একই সাথে রাসূলের নিকট থেকে আসা নাকিল শর্তসমূহকে বিশ্লেষণ করে। অথবা, ফকীহ, আফয়ালে মুকাল্লাফিন সম্পর্কে আল্লাহর হুকুম কি সেটাকে নিয়ে গবেষণা করে। একইসাথে মুতলাকভাবে আফয়ালে মুকাল্লাফের (দায়িত্বপ্রাপ্ত) গুরুত্ব নিয়ে গবেষণা করে।
এর দ্বিতীয় যে বিষয়টি তাসাউফকে কালাম পৃথক করে তা হলো, মানুষের ইচ্ছার ফলে সৃষ্ট অবস্থাকে বিশ্লেষণ করে। এই কারণে তাসাউফকে যদি প্রথম দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করা হয় তাহলে মেটাফিজিক্স, দ্বিতীয় দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করলে আখলাকে রূপান্তরিত হয়। আর এই আখলাককে যদি সুলতানের সাথে সম্পর্কিত করে তাহলে রাজনীতিতে পরিণত হয়। তবে সাধারণত দুটি ধারা রয়েছে, আখলাক ও মেটাফিজিক্স।
এখন প্রশ্ন হলো, ইলমুল কালামের আখলাক কোথায়? কালাম এরকম কোনো দাবি করেনি। তবে ভালো ও খারাপ কি? এই বিষয়ে কথা বলেছে। মূলত কালামের আখলাকী ধারাকে প্রতিনিধিত্ব করেছে ফিকহ। ইসলামে ফিকহ হলো, পূর্ববর্তীদের আখলাক এবং হিকমত সম্পর্কিত বিষয়ের অনুরূপ বিষয়। ফকীহদের ক্ষেত্র হল আফয়ালে মুকাল্লিফীন। মানুষের ইচ্ছায় সৃষ্ট বিষয়সমূহ। আপনারা জানেন ফিকহের বিষয় হলো আফয়ালে মুকাল্লিফীন। আফয়ালে মুকাল্লাফ হল মানুষের ইচ্ছায় সৃষ্ট বিষয়সমূহ।
দ্বিতীয় শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে পৌঁছলে মুসলমানগণ দুই ধরণের ডিসিপ্লিন (ধারা) তৈরি করে। প্রথম ধারা হলো, মানুষের ইচ্ছার বাহিরে সৃষ্ট বস্তু সমূহকে নিয়ে গবেষণাকারী ধারা বা ডিসিপ্লিন। দ্বিতীয় ধারা মানুষের ইচ্ছার মাধ্যমে সৃষ্ট বিষয়সমূহ যেমন আখলাক, রাজনীতি এবং অর্থনীতির মতো বিষয়সমূহ নিয়ে গবেষণাকারী ডিসিপ্লিন।
এই দুই ধারাকে বিশ্লেষণকারী কালাম ও ফিকহ নিজেকে মডেল জ্ঞান বলে দাবি করে। অন্য সকল ডিসিপ্লিন এদেরকে সাহায্যকারী ডিসিপ্লিন দাবি করে। মূলত এই উভয় ডিসিপ্লিনের পদ্ধতি একই। উভয়েই ইসতিদলালের পন্থা ব্যবহার করে থাকে। এই উভয়কে একত্রিত করে নতুন একটি ধারা তৈরি হয় সেটা হল যুহুদ আন্দোলন। একদিকে আখলাক অপরদিকে মেটাফিজিক্স হওয়ার কারণে পরবর্তীতে এটা তাসাউফ নাম ধারণ করে। ফলশ্রতিতে মুসলমানগণ নিজেদের অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখার জন্য সকল সৃষ্ট বস্তু তথা অস্তিত্বকে ডিসিপ্লিনাইজ করে। অর্থাৎ নির্ণয় করা সম্ভব এমন সকল কিছুকে বিশ্লেষণকারী ডিসিপ্লিন উদ্ভাবন করে।
যেমন, ইলমুল হাদীসের বিষয় হলো একজন মানুষ ও তার অবস্থাসমূহ। হাদীসের মূল কাজ হলো রাসূল (স) কে বিশ্লেষণ করা। অর্থাৎ সকল মানুষকে প্রতিনিধিত্বকারী হিসেবে পয়গাম্বরকে মূল হিসেবে ধরে তাকে বিষয়ে পরিণত করা। অপরদিকে তাফসীর হয় সৃষ্ট থিওরীর বাস্তবায়ন অথবা থিওরি তৈরি করার জন্য ক্ষেত্র প্রস্তুতকারী নসসমূহের ভাষাগত ব্যাখ্যাকে নিশ্চিত করে থাকে, অন্য কিছু নয়। মৌলিকভাবে বলতে গেলে মুসলমানগণ সমগ্র সৃষ্টিকে নির্দিষ্ট কাঠামোতে নিয়ে আসতে সক্ষম হয়। এটা অনেক বড় একটি সফলতা। লক্ষ্য করুন তখন মুসলমানদের কাছে ছিল ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ’ আর আল-কোরআন।
ইলাহী কালাম তাদেরকে যে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছিল সেই শ্রেষ্ঠত্ব দিয়ে তারা প্রাচীন বড় বড় দার্শনিক ধারাকে চ্যালেঞ্জ করে এই সকল জ্ঞানের উৎপত্তি ও বিকাশ ঘটাতে সক্ষম হন। সেই সময়ে মুসলমানগণ সমগ্র দুনিয়ার চিন্তাকে প্রতিনিধিত্বকারী একটি জাতিতে পরিণত হয় এবং এই ভাবে প্রাচীন সভ্যতার বিজ্ঞানকে চ্যালেঞ্জ করার জন্য নিজেদেরকে প্রস্তুত করেন।
অনুবাদঃ বুরহান উদ্দিন।