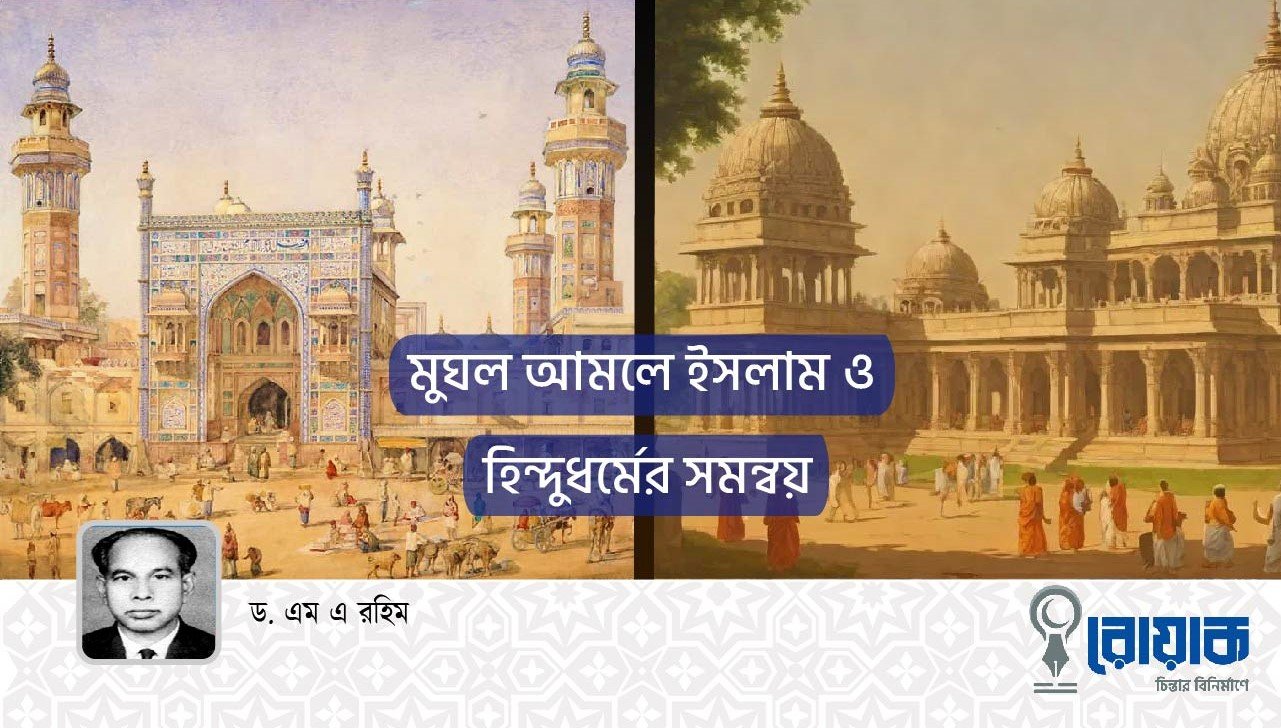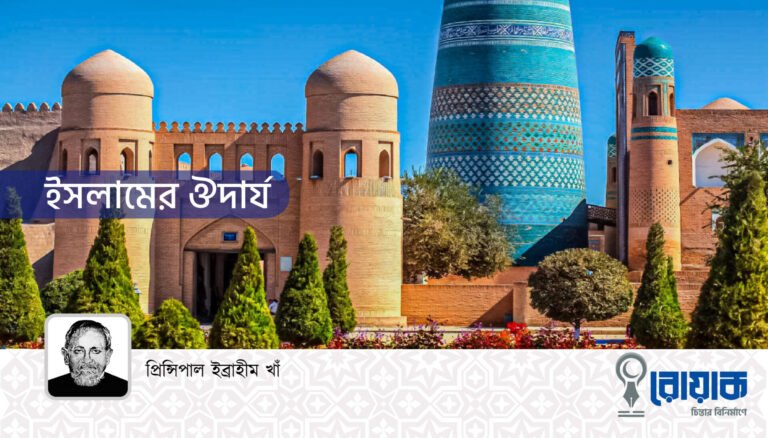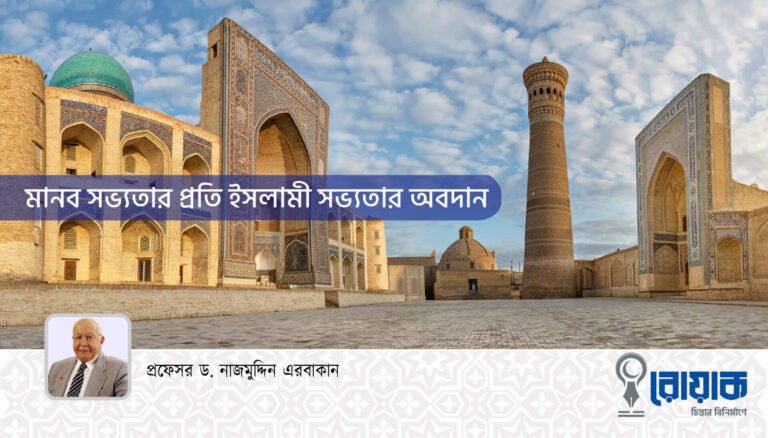মুসলমানগণ এই উপমহাদেশে এক উদারনৈতিক শক্তির সূত্রপাত করে। তাঁদের ধর্মীয় সারল্য, সামাজিক সাম্যবোধ এবং প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গী ও সংস্কৃতি হিন্দুসমাজকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে। জাতিধর্ম নির্বিশেষে হিন্দু ও অপরাপর প্রজাসাধারণের প্রতি মুসলিম শাসকবর্গের নীতি ছিল উদার ও সহনশীল। আওরঙ্গজেবের রাজত্বকালে আলেকজান্ডার হামিলটন নামক এক পরিব্রাজক বলেন “ইসলাম বাংলার আইন স্বীকৃত ধর্ম হলেও একজন মুসলমানের অনুপাতে ভিন্নধর্মাবলম্বী লোকের সংখ্যা হচ্ছে একশত জন। সরকারি কাজে উভয় সম্প্রদায় হতে লোক নিয়োগ করা হয়ে থাকে। প্রত্যেকে নিজ নিজ বিশ্বাস অনুযায়ী ধর্মাচারণ করতে পারেন এবং ধর্মের নামে নির্যাতন তাদের মধ্যে সম্পূর্ণ অনুপস্থিত।”
মুসলিমগণের সারল্য এবং সহিষ্ণুতা হিন্দুদের সঙ্গে তাদের সম্পর্ককে ঘনিষ্ঠতর করে এবং উভয়ের জন্য জীবনের সকল ক্ষেত্রে সমান সুযোগ-সুবিধার পথ প্রশস্ত করে। ফলে ব্রাহ্মণশ্রেণির প্রাধান্য বিশেষভাবে হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। কৃষ্টিসম্পন্ন এবং প্রভাবশীল শ্রেণি হিসেবে সমাজে কায়স্থগণের অভ্যুদয় ঘটে। উচ্চশ্রেণির হিন্দুগণ মুসিলম সংস্কৃতি, পোশাক-পরিচ্ছদ ও আচার-আচরণের প্রভাবে প্রভাবিত হন। সমকালীন সাহিত্যে বর্ধমান ও নবদ্বীপের জমিদারগণের রাজদরবারের যে চিত্র অঙ্কিত হয়েছে তাকে মুর্শিদাবাদ নবাব দরবারে ক্ষুদে সংস্করণ বলা যেতে পারে। হিন্দু জমিদারবৃন্দ তাদের দরবারের রীতিতে নিপুণ মুসলিম কর্মচারী নিয়োগ করতেন এবং যাদের দিক হতে নবাব দরবারের পদসমূহের সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান করা হতো, যেমন বকসি, মুন্সি, রানা সঙ্গীতজ্ঞ, আমিন, পেশকার এবং এমনি আরো অনেক, বহু হিন্দু উচ্চপদস্থ কর্মচারী, সমাজ প্রধান এবং শিক্ষক খান, মুস্তফা, মহালনবশ, খান সাহেব, সরকার শিকদার, তরফদার, কানুনগো, মজুমদার ইত্যাদি মুসলিম পদবি ব্যবহার করতেন। বস্তুত এরূপ পদবি ধারণকে তাঁরা ব্যক্তি এবং পারিবারিক জীবনে বিশেষ গৌরবের বলে মনে করতেন। এমনকি বর্তমানেও বহু হিন্দু পরিবার এসব সম্মানসূচক মুসলমানি পদবি ধারণ করে থাকেন। মুসলিম শাসনামলে এই প্রদেশে হিন্দু সমাজ যে কি বিপুলভাবে মুসলিম সংস্কৃতি দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল এসব বিষয় তা আমাদেরকে স্মরণ করিয়ে দেয়।
সম্ভ্রান্ত হিন্দু সম্প্রদায়ের উপর মুসলিম সংস্কৃতির প্রভাব ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে কয়েকটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ করা যেতে পারে।
জনৈক হিন্দু জমিদারের বর্ণনা করতে গিয়ে অষ্টাদশ শতাব্দীর কবি জয় নারায়ণ বলেন, “রাজা (জমিদার) দরবার কক্ষের মধ্যস্থলে স্বর্ণসিংহাসনে উপবিষ্ট। তাঁর মাথার উপর রাজছত্র বিধৃত। মূল্যবান উষ্ণীষ মুক্তার মতো ঝলমল করত। উষ্ণীষের উপরিভাগে কলিকা পাখির উজ্জ্বল পালক সূর্যালোকে দোলায়মান এবং দীপ্তিমান। তিনি পরিধান করতেন সোনার ঝালর দেয়া চাপকান ও বর্ম। পরিচ্ছেদের উপর দিয়ে বৃহৎ মুক্তার একখণ্ড রজ্জু ঝুলানো। কটিদেশে বেষ্টন করে প্রশস্ত কটিবন্ধে সোনার ঝালরের সজ্জা। কবির বর্ণনা থেকে এটা সুস্পষ্ট হয় যে জমিদার মুসলমানি পোশাক চাপকান ও পাগড়িতে সুসজ্জিত হতো। নবাব আলীবর্দী খানের সময় নবদ্বীপের জমিদার রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের রাজসভার যে দৃশ্য কবি ভারতচন্দ্র বর্ণনা করেছেন তাতে এটা প্রতীয়মান হয় যে, হিন্দু জমিদারগণ মুসলমান শাসক ও রাজন্যবর্গের আদর্শ অনুযায়ী দরবারের কার্যাবলী নিষ্পন্ন করতেন। কবি লিখেছেন “দরবার কক্ষে শাস্ত্রিগণ পরস্পর হাত ধরে শ্রেণিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে থাকত। তাদের বক্ষদেশে বর্ম ও কটিবন্ধে ঝোলানো থাকত তরবারি। ঘড়িয়ালগণ (রাজকীয় সময় রক্ষক) উভয় পার্শ্বে দাঁড়িয়ে থাকত। চাপদার অথবা চাপরাশিগণ হাতে সুবর্ণ লাঠি নিয়ে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে থাকত প্রকাশ্যস্থলে আরবিজি তথা জনসাধারণের নিকট হতে আবেদন পত্র গ্রহণকারী কর্মচারী মাসাধিককাল দাঁড়িয়ে থাকত। ভাঁড় বা রাজধবি রাজস্তুতি গাইতেন। মোসাহেবরাও সভাস্থলে থাকতেন। তাদের কাজ ছিল জমিদারের মতিগতির প্রতি নজর রাখা। সেখানে মুন্সিগণ (সচিববৃন্দ), বকসি (সৈন্যদের বেতন প্রদানকারী), বৈদ্য (চিকিৎসক), কাজি (বিচারক) কানুনগো ও অপরাপর অনেকেই উপস্থিত থাকতেন। রাজকীয় বাদকবৃন্দের জন্য রাবাব, তানপুরা, বীণা, মৃঙ্গ ও অন্যান্য বাদ্যযন্ত্র যথাযথভাবে রক্ষিত থাকত। নকিবের (রাজসভার ঘোষক)। কাজ ছিল দর্শনার্থীদের নাম ঘোষণা করা এবং তাঁদেরকে উচ্চস্বরে রাজসভার পালনীয় রীতিনীতি বিষয় অবিহিত করা। উজাক বা উনাবক্য কাজালবাস বা কিজেলবাস, লালটুপীধারী (বাহিদী), হাফসি (হাবসি) এবং জল্লাদ তাদের নিজ নিজ স্থানে দাঁড়িয়ে থাকত।”
আনুষ্ঠানিক রীতিনীতির দিক থেকে কৃষ্ণচন্দ্রের রাজসভা ছিল মুসলিম দরবারের ক্ষুদ্র সংস্করণ। মুসলিম শাসকবর্গের আচরণ প্রথার অনুকরণে দর্শনার্থীরা রাজা কৃষ্ণচন্দ্রকে তিনবার কুর্ণীশ করত। ডি. সি. সেনের মতে মুসলিম শাসনামলে হিন্দু রাজন্যবর্গ এবং জমিদারগণ সম্ভ্রান্ত মুসলমানগণের মতো পোশাক-পরিচ্ছদ ব্যবহার করতেন এবং শুধু কপালে চন্দনের ফোটা এবং পবিত্র ভষ্মচিহ্ন ব্যবহার করে। নিজেদেরকে হিন্দু বৈশিষ্ট্যে ভূষিত করতেন।
মধ্যবিত্ত হিন্দুগণ মুসলিম জীবনধারা দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হতেন। স্বল্পশিক্ষিত কায়স্থ ভাড়ুদত্তকে পাগড়ি পরিহিত অবস্থায় ব্যাধরাজ কালকেতুর রাজদরবারে যেতে দেখা যায়। নরসিংহ বসু মুর্শিদাবাদের নওয়াব দরবারে বীরভূমের জমিদার রাজা আসাদউল্লাহর দূত হিসেবে নিয়োগকালে জমিদারের নিকট থেকে একটি জামা ও পাগড়ি উপঢৌকনরূপে লাভ করেছিলেন। সমকালীন হিন্দু লেখকগণের লেখায় হিন্দু রমনীগণকে মুসলিম পোষাকে চিত্রিত করা হয়েছে। তাঁরা ঘাঘরা (সায়া), ওড়না, কাচলী (বক্ষবন্ধনী) ব্যবহার করতেন। মুসলমানগণের অভ্যস্ত ব্যবস্থা হিন্দুগণের নিকট ফ্যাসনে পর্যবসিত হয়েছিল। সপ্তদশ শতকের মধ্যভাগে থমাস বাউরী নমক একজন ইংরেজ বণিকের মতে মুসলমান ও হিন্দু উভয় সম্প্রদায়ে নারীগণকে গৃহের চারিদেয়ালের ভিতর নপুংসক ও কুমারীগণের তত্ত্বাবধানে রাখা হতো।
ঘনিষ্ঠতর সামাজিক সম্পর্কের ফলে বহু হিন্দু ও মুসলমানগণের ধর্মাচারণ ও ধর্মপূজার প্রতি শ্রদ্ধাবান হয়ে পড়েন। সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে, বিরচিত ক্ষেমানন্দের মনসামঙ্গল কাব্যের একটি স্তবকে উল্লেখ আছে যে, সর্পদেবী মনসার কোপদৃষ্টি থেকে লক্ষ্মীন্দরকে বাঁচাবার জন্য যে লৌহ প্রকোষ্ঠ নির্মাণ করা হয়েছিল সেখানে তান্ত্রিক অন্যবিধ ব্যবস্থাদির সঙ্গে একখণ্ড পবিত্র কোরআন শরীফ রক্ষিত ছিল। অনেক হিন্দু বণিক পুত্রলাভের জন্য প্রার্থনা করবার উদ্দেশ্যে একদল ব্রাহ্মণকে আমন্ত্রণ করেন। ব্রাহ্মণগণ কোরআন পাঠান্তে উক্ত বণিককে আল্লাহর নাম জেকের করতে উপদেশ প্রদান করেছিলেন। শুভদিন নির্ধারণের জন্য ব্রাহ্মণগণ কোরআন আলোচনা করেন এবং বণিকগণ বাণিজ্য যাত্রার পূর্বে আল্লাহর নিকট নিরাপত্তার জন্য প্রার্থনা করতেন।
হিন্দুগণ যে কোরআনকে একটি পবিত্র গ্রন্থ হিসেবে শ্রদ্ধা করতেন এসমস্ত দৃষ্টান্ত হতে তা বিশেষ ভাবে প্রতীয়মান হয়। মুসলমানগণের ধর্মীয় উৎসবাদিতে হিন্দুরাও যোগদান করতেন। দৌলতরাও সিদ্ধিয় ও তাঁর পদস্থ কর্মচারীবৃন্দ মুলসমানদের মতো সবুজ পোশাক পরিধান করে মহরম মিছিলে যোগদান করেছিলেন। এমনকি ১৮১১ খ্রিষ্টাব্দেও হ্যামিলটন বুকানম ভাগলপুরে লক্ষ্য করেছিলেন যে, হিন্দুগণ মুসলমানগণের একান্তভাবেই মহরম উৎসবে ব্যাপৃত হতেন। মুসলমান পিরের প্রতি ভক্তি জ্ঞাপন তাঁদের আর্শীবাদ কামনা ও দরগায় সিন্নি প্রদান হিন্দুগণের মধ্যে বিশষভাবে প্রচলিত ছিল। হিন্দুগণ কর্তৃক বংশপরস্পরায় শাহজামাল (শেখ জামাল সামদীর তাবরিজী) এর উদ্দেশ্যে প্রদর্শিত ভক্তির বিষয় শেষ শুভোদরায় বিশেষভাবে উল্লেখিত আছে। ইহার লেখক হলায়ুধ মিত্র লিখেছেন- ‘সর্বজন খ্যাত মরহুম শেখ জামাল, তোমার পদযুগলে আমি আমার অন্তরের শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদন করি।। আমার জীবন ও ধনসম্পদ রক্ষার জন্য তোমার কাছে প্রার্থনা জানাই। গৃহে প্রত্যাবর্তন করে আমি আমার সম্পত্তির অর্ধাংশ তোমার উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করবো।” কবির কথায় আরো জানা যায় যে বহু লোক সেই পুণ্যাত্মার নিকট সন্তান লাভ কিংবা রোগ মুক্তির জন্য প্রার্থনা জানাত। তৎকালীন বহু হিন্দু কবিকে পিরের অনুরাগী ভক্তরূপে নিজের পরিচয় দিতে এবং আধ্যাত্মিক মুসলিম সাধকের স্তুতি করতে দেখা যায়। তাঁর পুস্তকের মুখবন্ধে তিনি প্রখ্যাত মুসলিম সাধক বড়খান গাজির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। অপর একজন হিন্দু লেখক রূপরাম তাঁর ধর্মমঙ্গল গ্রন্থে সেলিমাবাদের পির বড়খানের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেছেন। রূপরাম বিশ্বাস করতেন যে, এই পিরের পুণ্যনাম জপের মাধ্যমে বিপদগ্রস্ত ব্যক্তিও বিপদমুক্ত হতে পারে। কৃষ্ণহরিদাস তাহির মামুদকে তাঁর আধ্যাত্মিক গুরু বলে গ্রহণ করেছিলেন। বাঙালি কবি বিদ্যাপতি তাঁর রচনায় বড়খান গাজি, জাফর খান গাজি, ইসমাইল খান গাজি প্রমুখ বহু মুসলিম পিরের স্তুতি গেয়েছেন। কৃষ্ণরাম দাসের রামায়ণ কাব্যে বাঙালি হিন্দু বণিক ও নাবিকবৃন্দের বড় খা গাজির প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধার প্রকাশ রয়েছে। দুটি সম্প্রদায়ের বহু শতাব্দী ব্যাপী প্রতিবেশী হিসেবে বলিষ্ঠ অবস্থানের ফলে দৈনন্দিন জীবনে একে যে অপরের দ্বারা প্রভাবিত হতো তা নিতান্তই স্বাভাবিক। পাঁচ শতাধিক বৎসর ঘনিষ্ঠ সাহচর্যে বসবাস করবার ফলে বস্তুত বাংলার হিন্দু-মুসলমানগণের মধ্যে তাই ঘটেছে। কিন্তু লক্ষণীয় বিষয় যে, হিন্দু সম্প্রদায়ের উপর মুসলিম প্রভাব গভীরতর। হিন্দুগণের মৌলিক ধর্মীয় বিশ্বাসে তাঁদের সাংস্কৃতিক ও সামাজিক জীবনের এ প্রভাবের ফল বিশেষভাবে অনুভূত হয়। ইহা হিন্দু জীবনের ভিত্তিমূলে নাড়া দিয়েছিল। পক্ষান্তরে ধর্মীয় সারল্য ও গণতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার দরুন মুসলমানগণকে জটিল হিন্দু সমাজ থেকে কিছুই গ্রহণ করতে হয় নি। এতদসত্ত্বেও বহু শতাব্দীর সহাবস্থানের ফলে মুসলিম সমাজে কিছু কিছু হিন্দু প্রভাব এসে পড়ে। এই প্রভাব আধ্যাত্মিক স্তরের। মৌলিক ধর্মীয় বিশ্বাসে নয় বরং বাহ্যিক আচার আচরণে এ প্রভাব সীমিত। নানাবিধ হিন্দু কুসংস্কার ও আচার আচরণ মুসলিম সমাজে অনুপ্রবিষ্ট হয়। এই ঘটনার জন্য হিন্দু সান্নিধ্য একান্তভাবে দায়ী নয়। বাঙালি মুসলমানগণের দৈনন্দিন জীবনে বহু অনৈসলামিক সংস্কার ও আচার-আচরণের জন্য ইসলাম ধর্ম নবদীক্ষিত হিন্দু ও বৌদ্ধগণের ভূমিকা সমধিক। ধর্মান্তরিত বৌদ্ধগণ মুসলিম সমাজে নাথ যোগী ও মুণ্ডিত মস্তক সন্যাসিগণের নানা বিশ্বাস ও আচরণ আমদানি করেন।
ভিন্ন সম্প্রদায়ের বহুল প্রচলিত ও লৌকিক বিশ্বাস ও স্থানীয় আচার-আচরণ মুসলিম সমাজে বহুকাল ধরে প্রচলিত থাকে। বিজয়গুপ্ত নামক ষোড়শ শতাব্দীর জনৈক কবির মতে হাসান ও অপরাপর মুসলমানগণ যমশত্রু সাপের আক্রমণ ভয়ে সর্পকূলের অধিষ্ঠাত্রী দেবী মনসাকে পূজা করত।
কবি কম্পিত মুসলমান কর্তৃক মনসাপূজার এই কাহিনী স্বীকৃত সত্যের মর্যাদা নাও পেতে পারে কিন্তু ইহা স্বীকার্য যে হিন্দুগণের বহুকিছু মুসলমান সাধারণভাবে বিশ্বাস করতেন যে একজন আদি ভৌতিক শক্তি সর্পকূলের আচরণ নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। বহু মুসলমান হিন্দু দেবদেবী এবং পীঠস্থানের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতেন এবং তাদের অনুগ্রহের কার্যকারিতায় বিশ্বাসী ছিলেন। কথিত আছে, মীরজাফর মৃত্যুশয্যায় তার মন্ত্রী নন্দকুমারের পরামর্শে কৃতিকাভরী মূর্তি ধোয়া কয়েক ফোটা পানি পান করেছিলেন। বহু মুসলমান কবি তাহার পুস্তকের মুখবন্ধে আল্লাহ রসুল ও পির মুর্শিদগণের সঙ্গে সঙ্গে হিন্দু দেবতার প্রশস্তিও গেয়েছেন। বহু মুসলিম কবি রাধাকৃষ্ণের স্তুতিমূলক গান রচনা করেছেন। ‘সমশের গাজির পৃথি’ নামক কাব্যে উল্লেখিত আছে যে একদা রাত্রে এক দেবী স্বপ্নে কবির নিকট তিনবার আবির্ভূতা হন এবং দেবীর আদেশ অনুযায়ী অনুগত কবি পরবর্তী প্রভাতেই ব্রাহ্মণগণের সহায়তায় হিন্দু প্রথায় দেবীর পূজা সমাপণ করেন। একজন গাজি যে হিন্দু দেবীর পূজা করেছেন তা বিশ্বাসযোগ্য নয়। যাহোক এ ঘটনা হিন্দু দেবীর প্রতি মুসলমান সম্প্রদায়ের সাধারণ ভক্তি শ্রদ্ধার পরিচয় বহন করে।
মুসলমান হিন্দুদের ধর্মীয় উৎসবাদিতে অংশ গ্রহণ করতেন। মুর্শিদাবাদ নবাবের আমলে মুসলমান শাসক ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গ, হিন্দু সম্প্রদায়ের হোলি উৎসবকে বিশেষ আনন্দের উৎসবের পরিণত করেছিলেন। সাহায্য নয়, সিরাজদ্দৌলা ও মীরজাফর মহা আনন্দের সঙ্গে এই উৎসব পালন করতেন। বহু মুসলমান হিন্দু জ্যোতির্বিদ্যায় বিশ্বাসী ছিলেন এবং শুভক্ষণ নির্ধারণে হিন্দুর মতো নিষ্ঠার সঙ্গে আচারাদি পালন করতেন। বিষয়টা এতই সাধারণ ছিল যে ক্রাফটনের মতে, “হিন্দু ও মুসলমানদের জ্যাতির্বিদদের সমবেত গণনার ফলে বৎসরের প্রায় অর্ধেক দিন অশুভ বলে পরিগণিত হতো। সকল পরামর্শ সভার প্রধান গণৎকারের উপস্থিতি অপরিহার্য। নতুন কোনো কাজে হাত দেবার পূর্বে তার পরামর্শ সর্বাগে গ্রহণীয় এবং তার নিষেধবাণী রোমান সিনেটের একজন ট্রিবিউনের ভক্তির মতো অপ্রতিরোধ্য। নবাব সরফরাজ খান ও আলিবর্দী খান গণৎকারগণের পরামর্শক্রমে ভ্রমণ কিংবা অভিযানের শুভলগ্ন নির্ধারণ করতেন। নবাব মীরকাসিমও জ্যোতির্বিদ্যায় বিশ্বাসী ছিলেন। ব্রাহ্মণ জ্যোতির্বিদদের দ্বারা তিনি তার নবজাত সন্তানের ঠিকজ্জী বাকুলজী প্রণয়ন করে নিয়েছিলেন।
এইভাবে হিন্দু মুসলমানগণ পরস্পরের সমাজ জীবনকে প্রভাবিত করেছে। সামগ্রিক অর্থে বলতে গেলে মুসলমান শাসন আমলে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে একটা সমঝোতা ও সৌহার্দ বিদ্যমান ছিল। কিন্তু উচ্চবর্ণের হিন্দুগণ মনের গভীরে মুসলমান বিদ্বেষ পোষণ করতেন। বাংলার মুসলিম শাসন আমলে পরবর্তী পর্যায়ে সে অনুভূতির প্রকাশ ঘটে। কিন্তু এই সম্প্রদায়ভূক্ত সাধারণ মানুষ প্রতিবেশী সুলভ পারস্পরিক সু-সম্পর্কে বিশ্বাসী ছিলেন এবং উচ্চবর্ণের হিন্দুদের বিরূপ মনোভাবের দ্বারা তারা প্রভাবিত হন নি। ক্রাফটন বলেন, “তবু একজন ইংরেজের পক্ষে বিস্মিত হওয়া ছাড়া গত্যন্তর থাকে না যখন তিনি দেখতে পান যে সরাকারি পর্যায়ে বিপ্লবের প্রভাব সাধারণ মানুষের জীবনে কি নগণ্য। বস্তুত ইহা দরবার কক্ষের ক্ষুদ্র গণ্ডীর বাইরে আদৌ অনুভূত হয় না।
হিন্দু মুসলমানগণের পারস্পরিক সমঝোতা ও সৌহার্দ বহু সাধারণ সাংস্কৃতিক প্রথার প্রশস্ত করেছে। পির, পাঁচপির, সত্যপিরের সেবা বাংলা সাহিত্য এবং আধ্যাত্ম মাইজ বাউল গোষ্ঠী এই প্রদেশে দুই প্রধান সম্প্রদায়ের সাধারণ সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানসমূহের অন্যতম কয়েকটি।
সত্যপির ভক্তি
সত্যপির বাংলার মুসলমানগণের এক সাধারণ সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার। এতে হিন্দু মুসলমানগণের ধ্যানধারণা ও আচার প্রথার সমন্বয় ঘটেছে। উভয় সম্প্রদায়ের সামাজিক সম্পর্কের ফলশ্রুতি হিসেবে সত্যপির ভক্তি মুসলমানগণের অদ্বৈতবাদ ও সামাজিক ন্যায় বিচারের উজ্জ্বল দাগ বহন করে। ইহার উৎপত্তি বিধায় নানা গল্প প্রচলিত আছে। বিষয়বস্তুর পার্থক্য এবং নানাযুগে নানা ব্যক্তিকে সত্যপিরের উদ্ভবের সঙ্গে জড়িত করলেও গল্পগুলোতে একটি যুগ সত্য বিধৃত তা হচ্ছে সত্যপির ভক্তির উপর মুসলমানগণের একেশ্বরবাদের ধারণা এবং সামাজিক ন্যায় বিচারে প্রাধান্য। একটি গল্পে ময়মনসিংহের কানকা নামে সমাজচ্যুত এক ব্রাহ্মণ সন্তান জনৈক মুসলমান সাধককে তার ধর্মগুরু হিসেবে বরণ করেন। পিরের আদেশে কানকা বিদ্যাসুন্দর কাহিনী নামক এক মহাকাব্য রচনা করেন। সত্যপিরের মাহাত্ম্য একটি প্রচার-ই ছিল এ কাব্যের উদ্দেশ্য। ১৫০২ খ্রিষ্টাব্দে হোসেন শাহের শাসন আমলে ইহা রচিত হয়। ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে অপর একজন মূলসমান কবি ফরিদ আন্নাহ সত্যপিরের স্তুতিমূলক কাব্য রচনা করেন। এই ধর্মীয় পদ্ধতির উপত্তি সম্বন্ধে ভারতচন্দ্রের বক্তব্য এই যে একদা এক ফকির জনৈক ব্রাহ্মণের সামনে উপস্থিত হয়ে তার উদ্দেশ্যে শিরনি দাবি করেন। ব্রাহ্মণ ইহা প্রদানে অস্বীকার করলে ফকির অদৃশ্য হয়ে যান। এই ঘটনা হতে ব্রাহ্মণ উপলব্ধি করতে পারলেন যে হিন্দুদেবতা হরি (সত্য) এবং মুসলমান ফকির মূলত এক এবং অভিন্ন। অতএব উক্ত ব্রাহ্মণ সত্যপিরের উদ্দেশ্যে শিরনি প্রদান পূর্বক তার পূজা করেন।
আবার এক গল্পে সত্যপিরকে সত্যনারায়ণরূপে ইঙ্গিত করা হয়েছে। কিন্তু এ কাহিনীটিতে উপরোক্ত ঘটনার মর্ম বিধৃত। এই কাহিনী অনুসারে এক বণিক সত্যনারায়ণের আর্শীবাদে এক কন্যা সন্তান লাভ করেন। কন্যার বিবাহের পর বণিক ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে বিদেশ যাত্রা করেন। তার জামাতাও তার অনুগামী হয়। কিন্তু সত্যনারায়ণের পূজা না করে বিদেশে তারা ভয়ানক বিপদে পড়েন। বণিক পত্নী সত্যনারায়ণের পূজা করেন, বণিক বিপদমুক্ত হন। প্রত্যাবর্তনের পথে যখন তারা গৃহের সন্নিকটে আসলেন বণিক তনয়া সত্যনারায়ণের নৈবদ্যের প্রতি ঘৃণা প্রদর্শন করে। ফলে বণিকের পণ্যবাহী জাহাজসমূহ জলমগ্ন হয়। সত্যনারায়ণের উপাসনার মাধ্যমে তারা আবার সবকিছু ফিরে পান। কাহিনীসমূহ হতে এই সত্য প্রতীয়মান হয় যে সত্যপির সংক্রান্ত ধর্মীয় পদ্ধতি মুসলিম প্রভাবিত হিন্দু সমাজ হতে উৎপত্তি লাভ করেছে। সত্যপির ভক্তির উৎসে রয়েছে অসাধরণ আধ্যাত্মিক ক্ষমতা সম্পন্ন মুসলমান সাধকগণের প্রতি হিন্দু জনগণের শ্রদ্ধাবোধ। সুফি ও পীরের প্রতি হিন্দুদের স্বাভাবিক ভক্তির ফলশ্রুতিরূপে ইহাকে গণ্য করা যেতে পারে। হিন্দুগণ পীরের অলৌকিক শক্তিতে বিশ্বাসী ছিলেন এবং তাদের কৃপা লাভের উদ্দেশ্যে প্রার্থনা করতেন। কালক্রমে হিন্দুদের এই পিরপূজা প্রথা সত্যপির পূজা পদ্ধতিতে রূপ লাভ করে। সত্যপিরের উপাসনা দ্বারা কাম্য বস্তু লাভ করা যায় এ সাধারণ বিশ্বাসের বহু দৃষ্টান্ত সমসাময়িক সাহিত্যে চিত্রিত। কবির কাব্যে হিন্দু দেবতার সঙ্গে মুসলিম পিরের সমন্বয় ঘটতে দেখা যায়। অন্য কথায় মুসলমানের পির হিন্দুগণ কর্তৃক দেবত্বমণ্ডিত হতেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর কবি বিদ্যাপতি সত্যপিরের উদ্দেশ্যে নৈবেদ্য নিবেদন করে বলেছেন যে পিরের স্মৃতি জগতে অমর করে রাখবার জন্য তার আদেশে তিনি কাব্য চর্চা করতেন। দুঃখী জনের দুঃখ মোচনের জন্য সত্যপিরের আবির্ভাব। বিদ্যাপতি এ সত্য প্রচার করতেন। বহু হিন্দু ও মুসলমান কবি সত্যপিরের স্তুতিমূলক কাব্য রচনা করেন। শ্রী কবি বল্লভ বিরচিত ‘মদন সুন্দর পাচালী’তে প্রধান যে হিন্দুদের মধ্যে সত্যপির ভক্তিপ্রথা নিতান্তই সাধারণ ছিল এবং তারা শিরনি সহযাগে উক্ত পিরের পূজা করতেন। শরিফ নামক একজন মুসলমান কবি সত্যপিরের উদ্দেশ্যে ভক্তিমূলক কাব্য রচনা করেন। অপর একজন বাঙালি কবি শঙ্করাচার্য তার কাব্য সৃষ্টির মাধ্যমে সত্যপির ভক্তি প্রচার করেন। এমনকি উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে একজন হিন্দু নিজেকে সত্যপিরের ভক্ত হিসেবে প্রকাশ্যে স্বীকার করতেন এবং এই হিতৈষী অবতারের পূজার প্রেরণা দান করতেন। ইপ্সিত ফল তার ক্ষমতার ব্যাখ্যায় দৃষ্টান্ত স্থাপন করতেন। কিছু সংখ্যক ব্রাহ্মণ কোরআনশরিফ পাঠ করাকে ধর্ম বিগর্হিত কাজ বলে আখ্যায়িত করেন। তখন ব্রাহ্মণ বালকরূপে আবির্ভূত হয়ে সত্যপির একখানি পবিত্র কোরান গ্রন্থ হাতে তুলে নেন। তার অভিভাবকবৃন্দ উহাকে মানতে নিষেধ করে এবং তাকে সাবধান করে দেয়া হয় যে কোরআনশরিফ পাঠ করলে সে তার নিজস্ব ধর্ম বিশ্বাস হারিয়ে ফেলবে। কিন্তু ব্রাহ্মণ বালক ঈশ্বরের একত্ব প্রচার করেন এবং দাবি করেন যে বিষ্ণু এবং আল্লাহর মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই।
সত্যপিরের ভক্তি বাঙালি সামাজজীবনে বিপুল শক্তি হিসেবে বহু শতাব্দী প্রচলিত ছিল। এই ঘটনা থেকে তার প্রভাব প্রমাণিত হয় যে, সত্যপির বিষয়ে বাংলায় একটি সমৃদ্ধ সাহিত্য রচিত হয়েছে এবং এই সাহিত্যকে বৈষ্ণব সাহিত্যের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। সত্যপির মতবাদ বাস্তবিকই এরূপ একটি প্রভাবশালী ধর্মীয় বুদ্ধি বৃত্তিক আন্দোলন ছিল যা সে যুগের লোকের মনে গভীর রেখাপাত করেছিল। ইহা হিন্দুদের ধর্মীয় সামাজিক বিশ্বাসসমূহেরও আচার অনুষ্ঠানগুলোর জটিলতাসমূহ অপসারণ করে সেখানে সহজ ও সরল বিশ্বাস প্রবর্তন করেছিল এবং উদারতার ভিত্তিতে হিন্দু সমাজের উন্নতির পথ উন্মুক্ত করে দিয়েছিল। সত্যপিরের উপর রচনাসমূহ বাংলা সাহিত্য ঐশ্বর্যশালী করেছিল। ইহা সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে হিন্দু মুসলমানের মধ্যে সমঝোতা ও সহযোগিতার আবহাওয়া সৃষ্টি করে। তা এখনও বাংলায় কোনো কোনো অঞ্চলে বিদ্যমান আছে। উত্তর ও পশ্চিম বঙ্গে অনেক হিন্দু ও মুসলমান এখন আনুষ্ঠানিকভাবে সত্যপিরের পূজা করে। তারা একটি তক্তার উপর সত্যপিরের আসন প্রতিষ্ঠা করে এবং ইহা ফুল দ্বারা সজ্জিত করে। পূর্ণিমার দিন তারা সত্যপিরের আরাধনার শিরনী দেয়। মোল্লা মন্ত্র পাঠ করেন এবং তারপর লোকের মধ্যে শিরনি বিতরণ করা হয়। রাজশাহী জেলায় সত্যপিরের ভিটা নামক একটি স্থান আছে। এর তত্ত্বাবধায়কগণ এখনও নিষ্কর জমি ভোগ করে।