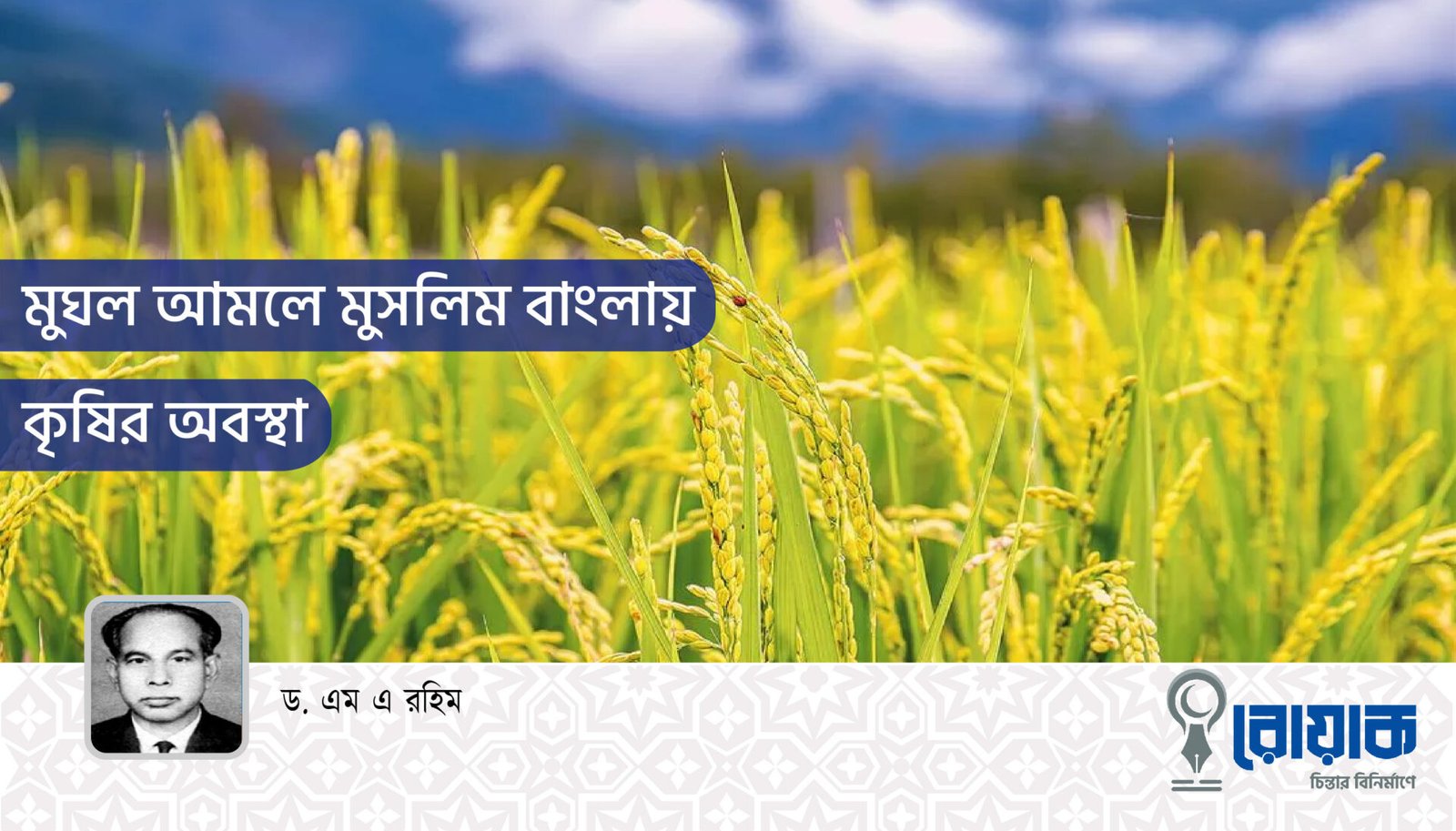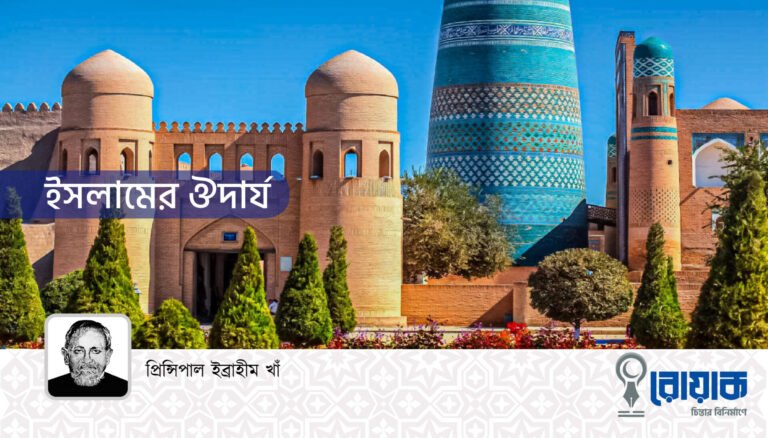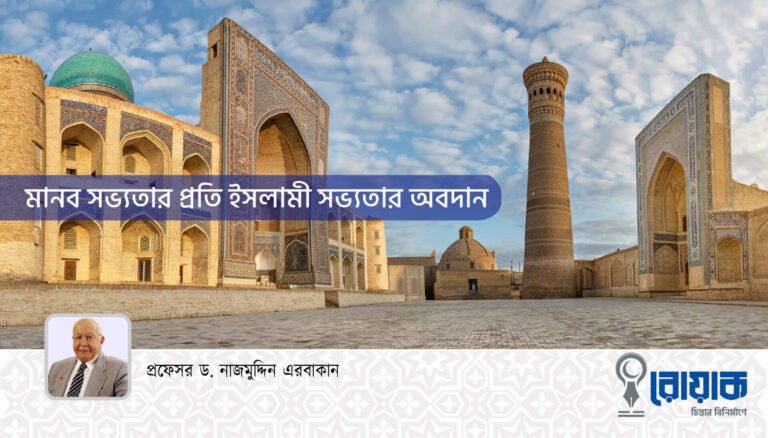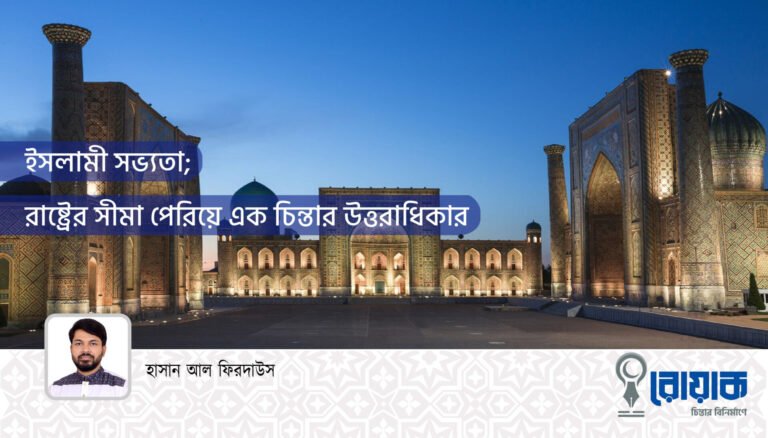বর্তমানের ন্যায়, মুসলিম আমলেও বাংলা প্রধানত একটি কৃষিপ্রধান দেশ ছিল এবং কৃষি-সম্পদে ইহা সমৃদ্ধিশালী ছিল। কৃষি সমৃদ্ধি ছিল বাংলার মাটির উর্বরতার অবদান। আবহমান কাল ধরে এর মাটির উর্বরতার খ্যাতি ছিল। প্রকৃতি এই প্রদেশের প্রতি সদয় ছিল। অসংখ্য নদ-নদী ও স্রোত-স্বিনীর জলে বিধৌত একটি উর্বরা দেশ বাংলা স্বাভাবিক জলসেচের সুযোগ-সুবিধা ভোগ করেছে; ফলে এই প্রদেশে প্রচুর শস্য শাকসব্জি, ফল-মূল ইত্যাদি উৎপন্ন হয়েছে। প্রাকৃতিক জলসেচের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে মৌসুমী বৃষ্টিপাতের আশীর্বাদ। এ সবই বাংলাকে পরিচিত করেছে পৃথিবীর সবচেয়ে উর্বর অঞ্চলরূপে। সমসাময়িক লেখকগণ এবং বিদেশী পর্যটকগণ এর প্রাচুর্য ও ঐশ্বর্য দৃষ্টে বিস্ময়াবিষ্ট হয়ে পড়েছেন। ইবনে বতুতা লিখেছেন যে, তিনি মেঘনার উভয় তীরে উদ্যানরাজি, শস্যপূর্ণ মাঠ ও জনবহুল সমৃদ্ধ গ্রামসমূহ দেখতে পান। পঞ্চদশ শতকের গোড়ার দিকে বাংলায় আগত চৈনিক দূতগণও এর উর্বরতা শক্তি ও প্রাচুর্য লক্ষ্য করেছেন। এদের একজন মন্তব্য করেছেন, “সপ্তস্বর্গ এই রাজ্যে পৃথিবীর স্বর্ণরাজি ছড়িয়ে রেখেছে।” বাংলার উর্বরতার কাহিনী এত বেশি প্রচলিত ছিল যে, আবুল ফজল লিখেছেন যে, ধানের গাছ গুলো এক রাতেই ৬ হাত বেড়ে উঠতো এবং বাংলার মাটিতে বছরে তিনটি ফসল জন্মাতো। সপ্তদশ শতকের মধ্যভাগে বাংলার পরিদর্শন করে বার্ণিয়ার লিখেছেন যে, তিনি সমগ্র প্রদেশব্যাপী বহু নদীনালা ও খাল-বিল দেখতে পেয়েছেন এবং এগুলোর চতুর্দিকে শস্য ও ফলে ভরা উর্বর ও সবুজ মাঠ এবং শ্রেণিবদ্ধ ঘন বসতিপূর্ণ বহু শহর ও গ্রাম সাজানো ছবির মতো শোভা পাচ্ছিল। বিদেশীরা বাঙালি জনসাধারণের বুদ্ধিমত্তা ও পরিশ্রমী প্রকৃতির উল্লেখ করেছেন। চৈনিক দূতগণ লিখেছেন যে, বাংলায় পুরুষ রমণী উভয়ে মাঠে কাজ করে, তাদের শস্যের মৌসুম শেষ হলে, অবসর সময়ে তারা কাপড় বুননের কাজে নিয়োজিত হয়। বাঙালি কৃষকদের পরিশ্রমী প্রকৃতির প্রশংসা করে আলেকজান্ডার ডোউ লিখেছেন যে, পঞ্চদশ মিলিয়ন পরিশ্রমী লোক অধ্যুষিত বাংলাকে প্রকৃতি কৃষির জন্য পৃথিবীর সবচেয়ে সুবিধাজনক অঞ্চলরূপে নির্বাচিত করেছে।
চাউল
মাটির অসাধারণ উর্বরতা শক্তি ও অধিবাসীদের পরিশ্রমী প্রকৃতি বাংলায় শস্য, শাক-সব্জি ও ফলমূলের প্রাচুর্য সৃষ্টিতে সহায়তা করেছে। এগুলো এত বেশি পরিমাণে উৎপন্ন হতো যে, বাংলার অধিবাসীদের চাহিদা মেটানোর পরও বিপুল পরিমাণ উদ্বৃত্ত থাকত। মিঃ ওরম বলেন যে, বঙ্গভূমি এত প্রচুর পরিমাণ খাদ্যশস্য উৎপাদন করত যে তা’ তারা এক ফার্দিং মূল্যে (সস্তা দামে) বিক্রয় করে দিত। চাউল ছিল প্রদেশের প্রধান কৃষিজ উৎপন্ন দ্রব্য। বাংলাদেশে সরু, মধ্যম ও মোটা বিভিন্ন প্রকার চাউল জন্মাতো। বিভিন্ন প্রকার চাউলের উল্লেখ করে আবুল ফজল বলেন, “যদি প্রত্যেক প্রকারের শস্যের একটি করে কণাও সংগ্রহ করা যায়, তাহলে তাতেও একটা বিরাট ভাণ্ড ভরে উঠবে।” সমসাময়িক বাংলা সাহিত্যে উল্লেখিত ধান্যের অসংখ্য নাম থেকে এর বৈচিত্র্যে এবং প্রদেশের কৃষিজীবনে এর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার ইঙ্গিত মিলে। এ সবের কিছু সংখ্যকের নাম ছিল আমলো, আষাঢ়ে, আশাঙ্গ, উড়াশালী, কাকচী, কনকচুর, কাঙ্গাদ, কামা, তুজনা, কালাকরিৎ, মুসুমালী, খিরাকম্বা, খেজুরসারি, খাইমরাই, গুজুরা, গুনতামপালাল, গোপালজুরী, গোপালভোগ, ছিছড়া, ঝিঙ্গাশাল মুক্তাহার, মাওকালো, লাউসালী, পর্বতীজিরা, ফেরফেরী, ভোদোলী, মইপল, শানাখারকী, সলছটি, সীতাসালী, হালিপাঞ্জর, মাউকলাস, লালকামিনী, বাঁশমতি, বোয়ালী ইত্যাদি। চাউল এত প্রচুর পরিমাণ উৎপন্ন হতো যে, এটা রপ্তানির একটি প্রধান পণ্যরূপে পরিগণিত হতো। বার্নিয়ার মন্তব্য করেছেন, “বাংলায় এত বেশি চাউল উৎপন্ন হয় যে, ইহা কেবল প্রতিবেশী রাজ্যগুলোতেই তাহা সরবরাহ করে না, বরং দূরবর্তী রাজ্যেও প্রেরণ করে থাকে। গঙ্গার উপর দিয়ে বহন করে চাউল পাটনায় নিয়ে আসা হয় এবং সেখান থেকে সমুদ্রপথে মসুলীপত্তন ও করোমণ্ডলের অন্যান্য বহু বন্দরে রপ্তানি করা হয়। বিদেশী রাজ্য প্রধানত সিংহল ও মালদ্বীপেও এই চাউল পাঠানো হতো।” মিঃ বার্থলোমিউ পাইসটেড ১৭৫০ খ্রিষ্টাব্দে লিখেছেন যে, বালীসোরের ইউরোপীয় বাণিজ্য কেন্দ্রগুলো মালদ্বীপের সঙ্গে চাউল ও অন্যান্য শস্যের খুব ভালো ব্যবসা চালিয়েছিল।
বিভিন্ন প্রকার শস্য, যেমন জনার, তিলতিষি, শিম বা বরবটি এবং নানা প্রকার শাক-সব্জি, পেয়াজ, রসুন, শসা, লাউ ইত্যাদি প্রচুর পরিমাণে জন্মাত। নারিকেলও প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হতো বলে পাশ্ববর্তী দেশগুলোতে তা’ রপ্তানি করা হতো। লঙ্কা, আদা ও হলুদ বিপুল পরিমাণে জন্মাতো। এবং এগুলো উপমহাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলসমূহে ও পশ্চিমে পারস্য উপসাগর, লোহিত সাগর ও আফ্রিকার বিভিন্ন দেশে এবং পূর্বদিকে ম্যানিলা ও চীন পর্যন্ত রপ্তানি করা হতো।
গম
মুসলিম শাসনামলে বাংলায় ভালো ধরনের গম উৎপন্ন হতো। এর গম উৎপাদন অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। ডাচ পরিব্রাজক স্ট্যাভোরিনাস ১৭৬৯-১৭৭১ খ্রিষ্টাব্দে বাংলা পরিভ্রমণ করে লিখেছেন যে, বাংলায় উৎকৃষ্ট গম উৎপন্ন হতো এবং পূর্বে এসব গম বাটাভিয়ায় পর্যন্ত পাঠানো হতো। পরবর্তীকালে উত্তমাশা অন্তরীপের গম শস্যের ব্যবসায়ের জন্য অনুকূল অবস্থা সৃষ্টির জন্য ঈস্টইণ্ডিয়া কোম্পানি বাংলার গম রপ্তানি নিরুৎসাহিত করে।
ইক্ষু
ইক্ষু ছিল বাংলার আর একটি প্রধান কৃষিজ উৎপন্ন দ্রব্য। উহার উৎপাদন ছিল ব্যাপক। ষোড়শ শতকের ‘বেঙ্গালা’ শহর পরিদর্শন করে বারবোসা এই এলাকার চিনি উৎপাদনের কথা ‘উল্লেখ করেন। তিনি লিখেছেন, এই শহরে ভালো ধরনের চিনি তৈরি হলেও তারা এ দিয়ে চিনির তাল তৈরি করতে জানে না। বেঙ্গালা থেকে চিনি রপ্তানির প্রশংসা করে তিনি লিখেছেন, “চিনি দিয়ে তারা বহু জাহাজ বোঝাই করে এবং বিক্রির জন্য অন্যান্য অঞ্চলে রপ্তানি করে।” ইতালীয় বণিক লিউইচ বার্থেমা ১৫০৩ খ্রিষ্টাব্দে বাংলা পরিভ্রমণ করেন এবং এর চিনি উৎপাদন লক্ষ্য করেন। বাংলায় সমগ্র মুসলিম আমলব্যাপী ইক্ষু একটি সমৃদ্ধিশালী কৃষিজ পণ্য ছিল। সপ্তদশ শতকে চিনি সম্পর্কে বার্নিয়ার বলেন, “বাংলা প্রচুর চিনি উৎপাদন করে এবং তা’ গোলকুণ্ডা ও কর্ণাটি রপ্তানি করে থাকে। এছাড়া মোকা ও বসোরা শহরের মাধ্যমে আরব ও মেসোপটেমিয়া প্রভৃতি রাজ্যে এবং এমন কি বন্দর আব্বাসের মধ্য দিয়ে পারস্যে চিনি রপ্তানি করা হয়ে থাকে। ” ১৭৫৭ খ্রিষ্টাব্দের পূর্বে ডাচ বণিকদের একটি প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, “চিনির বার্ষিক রপ্তানির পরিমাণ ছিল প্রায় ৮০,০০০ মণ; এতে প্রায় শতকরা ৫০ ভাগ লাভ হতো এবং সাধারণত এর মূল্য স্বর্ণ মুদ্রায় দিতে হতো।” পরবর্তীকালে এই উপমহাদেশের পশ্চিমাংশের বাজারে ডাচ ব্যবসায়ীগণ কর্তৃক আমদানিকৃত জাভা চিনির প্রতিযোগিতার ফলে বাংলার চিনি রপ্তানি বাণিজ্য হ্রাস পায়।
পাট
চতুর্দশ শতক থেকে বাংলা সাহিত্যে পাট ও পাটজাত বস্ত্রের উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায়। এতে প্রতীয়মান হয় যে, মুসলিম শাসনের প্রারম্ভ কাল থেকে বাংলায় পাটের উৎপাদন বিদ্যমান ছিল। এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে এ শস্যের একটি বিবরণ প্রদান করা হয়েছে।
আবুল ফজল ষোড়শ শতকে বাংলায় পাট উৎপাদন, যেমন পট্টবস্ত্র ইত্যাদির উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, “বাংলার গোড়াঘাট সরকারে রেশম এক প্রকার চটের কাপড়ের উৎপাদন ছিল।” পাটের তত্ত্ব দিয়ে তৈরি সেযুগো চটের থলে এবং মোটা বস্ত্র তৈরি হতো। ষোড়শ শতকের বাংলা সাহিত্যে পার্শ্ববর্তী দেশগুলোতে প্রদেশের পট্টবস্ত্র রপ্তানির প্রমাণ রয়েছে। ‘মনসামঙ্গল’ গ্রন্থ থেকে জানা যায় যে, চাঁদসওদাগর পাটের শাড়ি ও ধুতি ইত্যাদি বহু পণ্য দ্রব্য নিয়ে একটি দেশে ব্যবসায় করতে যান। তিনি চাতুর্যের সঙ্গে সেই দেশের রাজার নিকট এই পট্টবস্ত্রের গুণের উচ্চ প্রশংসা করেন। অতঃপর রাজা তদীয় রাণী ও নিজের জন্য কয়েকখানা বস্ত্র ক্রয় করতে প্রলুব্ধ হন। ফরাসি ব্যবসায়ী টাভার্নিয়ার সর্বপ্রথম বাংলার পাট উৎপাদনের বিষয় ইউরোপীয়দের নজরে আনেন। এরপর থেকে চটের থলে রপ্তানির একটি প্রধান বিষয় হিসেবে পরিগণিত হয়। ঈস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানির প্রথম দিককার দলিলপত্রে পাটের চট রপ্তানির উল্লেখ পাওয়া যায়। ১৭৫৩ খ্রিষ্টাব্দের ১২ অগাস্ট তারিখের একটি পত্রে বোম্বাইয়ে কোম্পানির সভাপতি এবং পরিষদ পাটের চটের জন্য এক চুক্তিপত্রে আবদ্ধ হন। ১৭৫৯ খ্রিষ্টাব্দে ২১শে জুলাই তারিখের মাদ্রাজ কাউন্সিলের অন্য একটি দলিলে পাটের চটের জন্য অনুরূপ আর একটি চুক্তি পত্রের সন্ধান পাওয়া যায়। ১৭৫৫ খ্রিষ্টাব্দের পাবলিক প্রোগ্রেস ভলুমে ১,২০০ বস্তা সরু চাউল ও ২,০০০ চটের থলের জন্য আর একটি ফরমাস পত্রের উল্লেখ রয়েছে। উনিশ শতকের মধ্যবর্তী সময়ে পর্যন্ত হাতে বোনা কাপড় ও পাটের তৈরি বস্তার রপ্তানি-বাণিজ্য অব্যাহত ছিল। ঈস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানির দলিলপত্র থেকে জানা যায় যে, ১৮৪০-৫১ খ্রিষ্টাব্দে কলিকাতা থেকে রপ্তানিক্ত চটের থলে ও কাপড়ের সংখ্যা ছিল ৯০,৩৫,৭১৩ এবং এর মূল্য হয়েছিল ২১,৫৯,৭৮২ টাকা। হাতে বোনা পাটজাত পণ্যদ্রব্য পাটের কল-কারখানা স্থাপনের পর হ্রাস পেয়ে যায়।
নীলচাষ
প্রাচীনকাল থেকে উপমহাদেশের অন্যান্য কিছু এলাকার মতো বাংলায়ও নীলের চাষ বিদ্যমান ছিল। সপ্তদশ শতকের মধ্য ভাগে এটা ইউরোপীয় বণিকদের নজরে আসে। এই সময় থেকে ইউরোপীয় বাজারে নীল রঙ প্রদেশের একটি রপ্তানিযোগ্য পণ্যদ্রব্য ছিল। ফরিদপুর, ঢাকা, রাজশাহী, পাবনা, নদীয়া, মুর্শিদাবাদ ও যশোহর জেলায় নীলের চাষ হতো। ইংরেজরা আমেরিকা হারানোর পর বাংলাকেই তারা নীল রঙের প্রধান সরবরাহকারী রূপে পরিগণিত করে, ফলে এই সমস্ত জেলায় নীলের চাষ বৃদ্ধি পায়। ইংরেজ নীলকররা কৃষকদেরকে অগ্রিম দাদন দিয়ে নীল চাষের অধীনে বেশি জমি আনয়ন করার জন্য বাধ্য করে। কিন্তু তারা চাষীদেরকে এরূপ মূল্য দিত যা’ দিয়ে এই শস্যের চাষাবাদের খরচও সংকুলান হতো না। ইংরেজ নীলকররা তাদের নিজস্ব সরকারের অধীনে হতভাগ্য কৃষকদেরকে নীলের চাষ অব্যাহত রাখতে বাধ্য করত। তারা কৃষকদের উপর অবিচার ও উৎপীড়ন করত। এরূপে নীল চাষ প্রদেশের কৃষকদেরকে সর্বশান্ত করে ফেলে।
আফিম
আফিম গাছের চাষ উত্তর বাংলা ও বিহারের কতিপয় জেলায় প্রচলিত ছিল। বহু লোক এই মাদক ঔষধের প্রতি আকৃষ্ট ছিল। আফিম অন্যান্য দেশে রপ্তানির অন্যতম পণ্য ছিল। চীন বাংলার আফিমের প্রধান ক্রেতা ছিল। প্রদেশে আফিম ক্রয়ের উপর বাধা নিষেধ ছিল। কৃষকগণ কেবল সরকার অনুমোদিত ব্যবসায়ীদের নিকট বিক্রি করতে পারত। সপ্তদশ শতক থেকে ইউরোপীয় কোম্পানিগুলো আফিম ক্রয় ও রপ্তানি বাণিজ্যে একচেটিয়া মুনাফা করে। ঈস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানির সরকার রাজস্ব লাভের উদ্দেশ্যে আফিম চাষীদের থেকে আফিম ক্রয়ের উপর কড়া বিধিনিষেধ আরোপ করেন। প্রায় সমস্তটা আফিমই রপ্তানি করা হতো। রাষ্ট্র কর্তৃক নিয়োজিত ঠিকাদাররা চাষীদের প্রতি অত্যাচার উৎপীড়ন করে মূল্য কমিয়ে দিত এবং মূল্য প্রদানেও তাদেরকে ঠকাত। কৃষকরা হয় চোরা কারবারিদের নিকট বিক্রি করত অথবা আফিমের চাষ পরিত্যাগ করত। ফলে বাংলায় আফিমের চাষ ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়ে যায়।
লাক্ষা
প্রাচীনকাল থেকে উত্তর বঙ্গের কয়েকটি জেলাতে লাক্ষার চাষ করা হতো। এটা গালা ও রঙ হিসেবে ব্যবহৃত হতো। আঠালো লাক্ষা ছিল গালা এবং এর সঙ্গে পোকা-মাকড় অথবা এর ডিম্ব মিশ্রিত করে তা থেকে রঙ বানানো হতো। রঙ করার অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশগুলো আলাদা করা হতো এবং রঙে পরিণত করা হতো। আঠা দিয়ে পাতগালা তৈরি করা হতো। লাক্ষা রঙ উজ্জ্বল লাল রঙ্গের বস্ত্রাদি রঙ করার জন্য ব্যবহৃত হতো। লাক্ষা আবার বার্নিশরূপেও ব্যবহৃত হতো। উপমহাদেশের বিভিন্ন অংশে এবং বিদেশে এর ব্যাপক চাহিদা ছিল। বাংলায় উত্তম লাক্ষা উৎপাদিত হতো এবং এই পণ্যের ক্ষেত্রে কার্যত বিদেশী বাজারের একচেটিয়া ব্যবসা ছিল তাদের। ষোড়শ শতকে বাংলাদেশ পরিভ্রমণ করে বার্থেমা ও বারবোসা এই প্রদেশ থেকে বেশ উল্লেখযোগ্য পরিমাণ লাক্ষা রপ্তানি ব্যবসায় লক্ষ্য করেন।
সুতা
বাংলার বিশেষ কিছু এলাকায় উত্তম ধরনের সরু সুতা উৎপাদিত হতো। এই তত্ত্ব বিশ্ববিখ্যাত সূক্ষ্ম বস্তু মসলিন তৈরির কাজে ব্যবহৃত হতো। জনৈক ইংরেজ বাণিজ্যিক প্রতিনিধি জে, বি. টেলর অষ্টাদশ শতকের শেষার্ধে বাংলাদেশে বিশেষত ঢাকায় বহু বছর বসবাস করেছিলেন। তিনি প্রদেশের এ অংশে উৎপাদিত তত্ত্বর উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন। তাঁর মন্তব্য উদ্ধৃতিযোগ্য। তিনি বলেন,
“ঢাকার ১২ মাইল দক্ষিণ-পূর্বে ফিরিঙ্গি বাজার থেকে বিস্তৃত মেঘনা নদীর তীর ধরে ইদিলপুর পর্যন্ত, সাগরের ২০ মাইল উত্তরে দৈর্ঘ্যে প্রায় ৪০ মাইল এবং প্রস্থে কোনো কোনা স্থানে তিন মাইল এবং কেদারপুর, বিক্রমপুর, রাজেন্দ্রপুর, কার্তিকপুর, শ্রীরামপুর ও ইদিলপুর পরগণায় অবস্থিত। ঢাকা প্রদেশের এই অঞ্চলে উৎকৃষ্টতম কার্পাস উৎপন্ন হয়; এবং আমি বিশ্বাস করি যে, পৃথিবীর অন্য কোথাও এরূপ উৎকৃষ্ট কার্পাস উৎপন্ন হয় না। ভারতের অন্য কোনো অঞ্চলের অথবা মরিটানিয়া দ্বীপপুঞ্জের অথবা বোর্বেনের যেখানের কার্পাসের খ্যাতি আছে এবং আমি যতটুকু খবর রাখি পৃথিবীর কোনো স্থানে উৎপন্ন কার্পাস ঢাকা অঞ্চলে উৎপন্ন কাপাসের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে না এবং গুণের ভিত্তিতে সমকক্ষ হতে পারে না। উপরোক্ত কার্পাসের শ্রেষ্ঠত্বের কারণ এই যে এই অঞ্চল সমুদ্রের নিকট অবস্থিত; স্রোতের প্রবাহের সঙ্গে সমুদ্রের পানি মেঘনার পানির সঙ্গে মিশে এই এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে; বছরের তিন মাস এরূপ হয়; এতে জমিতে বালি ও লবণের কণার পলিমাটির পাতলা আবরণ পড়ে এবং তা’ জমি উন্নত ও উর্বর করে তোলে। এটাও মনে করা হয় যে, বিশুদ্ধ সমুদ্র-বায়ু কাপাস চারা বৃদ্ধির অনুকূলে কাজ করে। ফিরিঙ্গিবাজার থেকে ইদিলপুর, লক্ষ্যা নদীর ও ধলেশ্বরী নদীর তীরভূমি রূপগঞ্জের কিছুটা উপর পর্যন্ত ১৬ মাইল বিস্তৃত এবং ছোট ব্রহ্মপুত্রের তীরভূমির ধলেশ্বরীর উত্তর কয়েক মাইল এলাকা ঢাকা প্রদেশে (বর্তমান ঢাকা জেলা) ব্যবহৃত অধিকাংশ কার্পাস সরবরাহ করে। অবশিষ্টাংশ কার্পাস বলদাখাল (ঢাকা জেলার একটি পরগণা), ভাওয়াল ও আলেপসিংহ (ময়মনসিংহের পরগণা) এলাকায় উৎপন্ন হয় এর কতক ভূষণা (যশোহর জেলার পরগণা) এবং পার্শ্ববর্তী রাজশাহী প্রদেশ হতে সরবরাহ করা হয়।” অক্টোবর ও নভেম্বর মাসে কার্পাস তুলার বীজ বপন করা হয় এবং এপ্রিল ও মে মাসে এ ফসল উঠে। গাছগুলো ৩ থেকে ৪ ফুট উঁচু হয়ে থাকে। কার্পাস ফসল সংগ্রহের পর এদের চারাগুলো শিকড়সহ উপড়ে ফেলা হয়। অক্টোবর ও নভেম্বর মাসে পরবর্তী বীজ বপনের পূর্বে, একই জমিতে ধারেন চাষ হয়ে থাকে। চতুর্থ বছরে এধরনের অনাবাদী রাখা হয়, অথবা অন্য কোনো ফসলের জন্য ব্যবহার করা হয়।
ইংরেজ রেসিডেন্ট জে. বেব্ব লিখেছেন যে, “বাংলার সুতা বিশেষ করে ঢাকা অঞ্চলের সুতা সমগ্র পৃথিবীর যে কোনো সুতা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ছিল। এবং এ থেকে আশ্চর্য রকমের সূক্ষ্ম বস্ত্র তৈরি হতো।” প্রথমে ব্রিটিশ উৎপাদকরা ভেবেছিলেন যে সুরাটের সুতাই সর্বোৎকৃষ্ট মানের। কার্যত সুরাট ও উত্তরাঞ্চলীয় সুতা সূক্ষ্ম মসলিন বস্ত্র তৈরির জন্য অনুপযোগী ছিল। এই মসলিন বস্ত্র উপরোল্লিখিত অঞ্চলে চাষকৃত ‘ফটি’ নামে অভিহিত একমাত্র বাংলার সুতার সাহায্যেই তৈরি হতো। ‘ফটি’ এপ্রিল ও সেপ্টেম্বরে দু’বার সংগ্রহ করা হতো। সূক্ষ্ম বস্ত্রাদি যেমন মলমল আল্লাবালি, দোরিয়া, তেরিদ্দাম, তানজিব, শরবতি ও নয়নসুখ ইত্যাদি ফটি সুতার সাহায্যে তৈরি হতো। মালদাতে ‘বরাবুঙ্গা’ ‘বিরেটা’ ও ‘নূরমা’ ইত্যাদি তিন প্রকারের সুতার উৎপাদন ছিল। ‘বরাবুঙ্গা’ সুতা ছিল কমনীয় এবং সূক্ষ্ম কিন্তু এর উৎপাদনের পরিমাণ ছিল খুবই সামান্য। সাধারণত অপেক্ষাকৃত মোটা রকমের ‘নূরমা’ ও ‘বিরেটা’ বাইরে রপ্তানি করা হতো। রংপুরে ‘চিস্তিয়া’ নামক এক প্রকার নিম্নমানের সুতা উৎপাদতি হতো। বীরভূমের সুতার উৎপাদন ছিল ব্যাপক, কিন্তু এর দ্বারা কেবলমাত্র মোটাবস্ত্র তৈরি হতো। বর্ধমানে ‘নূরমা’ মুহরী’ ও বোগ্লা এই তিন প্রকারের সুতার অস্তিত্ব ছিল। নয়নসুখ, মলমন্স, শরবতি, দোরিয়া ইত্যাদি বস্ত্র তৈরির জন্য নূরমা সুতা ব্যবহৃত হতো। গোজি ও গুররা বস্ত্রের জন্য ‘মুহরী’ এবং ‘গুররা’ মিশালী কাপড়ের জন্য ‘বোগ্গা’ ব্যবহৃত হতো। রাধানগরে ‘কাউর’ মুহরী ও ‘বোগ্গা’ এ তিন প্রকারের সুতা প্রস্তুত হতো। ‘কাউরে’ চমৎকার সূক্ষ্ম সুতা হতো। মেদিনীপুরে কুরেরারা ও ‘মুহরী’ ও দুপ্রকারের সুতার উৎপাদন ছিল। কুরেরারা ছিল কোমল ও সূক্ষ্ম ধরনের এবং এ সুতা সূক্ষ্ম বস্ত্রাদি যেমন, ‘নয়নসুখ,’ শরবতি ও অন্যান্য প্রকার মসলিন তৈরির জন্যে ব্যবহৃত হতো। ‘মুহরী’ সুতা দিয়ে ‘দিমিতি’ ও অপেক্ষাকৃত মোটা অন্যান্য কাপড়াদি বোনা হতো। উত্তরে ব্রহ্মপুত্র ও দক্ষিণে চলন বিলের মধ্যবর্তী হরিয়াল অঞ্চলে ‘দেশী’ ছিল অপেক্ষাকৃত মোটা শান্তিপুর অঞ্চলের সুতা ছিল উৎকৃষ্ট মানের। এটা উল্লেখযোগ্য যে, বাংলায় উৎপন্ন কাপাস তুলা মসলিন তৈরিতে ব্যবহৃত হতো। ইংরেজরা বাংলাদেশে তাদের কল-কারখানায় সাধারণ কাপড়-চোপড় তৈরির জন্যে সুরাট ও মীর্জাপুর থেকে সুতা আমদানি করত। মসলিম প্রস্তুতের জন্য সুরাটের সুতা উপযোগী ছিল না।
মুসলিম আমলে ভাতের সঙ্গে মাছ ছিল বাংলার মানুষের প্রধান খাদ্য। আবুল ফজল বাংলার মাছের প্রাচুর্যের কথা উল্লেখ করেছেন। এই প্রদেশের নদ, নদী, খাল, বিল ও জলাভূমিসমূহ মাছে ভরা ছিল। বাংলা মুল্লুকে মুগল নৌ-বাহিনীর সেনাপতি মীর্জা নাথন প্রসঙ্গত এ বিষয়ের উল্লেখ করেন। তিনি লিখেছেন যে, মুগল নৌ-বাহিনী যখন করাতোয়া নদী দিয়ে অগ্রসর হচ্ছিল তখন নদীর মাছ পানি থেকে লাভ দিয়ে উঠে এবং সৈন্যদের রণবাদ্য ও কামান-গোলা ইত্যাদির কাছে বহু মাছ নৌকার মধ্যে পড়ে যায়। মীর্জা নাথন সুবাদার ইসলাম খানকে তার তাঁবুতে বড় বড় চল্লিশটি মাছ উপঢৌকন পাঠান। ইসলাম খান তাঁর খাবার জন্য বাবুর্চিকে মাছ রান্না করতে আদেশ দেন। গবাদি ও গৃহপালিত পশু যেমন, গরু উষ্ট্র, ভেড়া, বকরী, অশ্ব ও খচ্চর ইত্যাদি সম্পদে বাংলাদেশ ঐশ্বর্যশালী ছিল। প্রদেশে হাঁস-মুরগি, রাজহাঁস এবং অন্যান্য বহু পাখিও প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যেত।
আবুল ফজল বাংলাদেশে নানা ফুল ও ফলের প্রাচুর্যের উল্লেখ করেছেন। সুপারির প্রাচুর্যের উল্লেখ করে তিনি বলেছেন যে, যারা সুপারি খায় তাদের মুখ লাল রঙে রঞ্জিত হয়। সুপারি ও পান বাংলায় পর্যাপ্ত পরিমাণে জন্মে। অন্যান্য ফল যা’ বাংলায় প্রচুর জন্মাত, তাহলো আম, কাঁঠাল, কলা, ডালিম, খেজুর, কমলা, সানতারাহ ইত্যাদি। সিলেট সরকারে ঘৃত-কুমারী মাঠে সমৃদ্ধ বনভূমি ছিল; এসব কাঠ রপ্তানির জন্য মূল্যবান পণ্য ছিল। লোহা ও হীরক ছিল বাংলার কয়েকটি উল্লেখযোগ্য খনিজ দ্রব্য। সরকার বাজুহাতে লৌহখনি এবং মান্দারন সরকারের হরপাতে হীরক খনি ছিল।
রেশমি বস্ত্র
বাংলার রেশমি বস্ত্রের উৎপাদন সুবাদার, নবাব ও অভিজাত ব্যক্তিদের পৃষ্ঠপোষকতায় সমৃদ্ধি লাভ করে। রেশমি ও মসলিন বস্ত্রের খুব ব্যাপক চাহিদা ছিল। উচ্চ ও অভিজাত শ্রেণির মেয়ে ও পুরুষ সকলে রেশমি ও মসলিন বস্ত্র পরিধান করত। সমসাময়িক, বাংলা সাহিত্যে অভিজাত পরিবারের মহিলাগণ কর্তৃক রেশমি শাড়ি ব্যবহারের উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায়। বাংলায় তুঁত গাছ ও গুটি পোকার চাষ করা হতো। চৈনিক দূতগণ এটা লক্ষ্য করেছেন। হিন্দু আমলে এ উপমহাদেশে গৃহজাত ও বাণিজ্যের জন্য গুটি পোকার চাষ অজ্ঞাত ছিল। মুসলমান আমলেই সর্বপ্রথম খুব সম্ভবত চীন থেকে উহা আমদানি করা হয়। আবুল ফজল ঘোড়াঘাট অঞ্চলে রেশম উৎপাদনের বিষয় উল্লেখ করেছেন। ১৬৬৬ খ্রিষ্টাব্দে টেভর্ণিয়ার কাসিমবাজার পরিদর্শন করেন। তিনি লিখেছেন যে, সে সময় কাসিমবাজার শহরে কাঁচা রেশমের বার্ষিক উৎপাদন ছিল প্রায় আড়াই মিলিয়ন পাউণ্ড (২২,০০০ বেল, প্রতিটি বেলের ওজন ১০০ লিভার); এর মধ্য থেকে ৩/৪ মিলিয়ন গুজরাট ও উপমহাদেশের অন্যান্য অংশে পাঠানো হতো, কিন্তু এর কিছু অংশে তাতার বণিকগণ মধ্য এশিয়ায় নিয়ে যায়। ডাচরাও প্রতিবছর কাসিম বাজারের প্রায় ৩/৪ মিলিয়ন কাঁচা রেশম জাপান ও হল্যান্ডে রপ্তানি করত এবং বাদবাকি এক মিলিয়ন পাউণ্ড বাংলার রেশমি বস্ত্র কারখানাসমূহে ব্যবহৃত হতো। বার্ণিয়ার লিখেছেন, “ডাচরা মাঝে মাঝে কাসিমবাজারে তাদের কারখানায় সাত অথবা আট শত দেশীয় লোকদের নিয়োগ করত; অনুরূপভাবে ইংরেজ’ ও অন্যান্য বণিকরাও অনুরূপ সংখ্যার দেশীয় লোকজন নিয়োগ করেছিল। ডাচরা যে সুতি বস্ত্র বিশাল পরিমাণে রপ্তানি করে তাহা দেখে আমি কখনও বিস্ময়াবিষ্ট হয়ে পড়ি। কাঁচা রেশমের রপ্তানি বাণিজ্য অষ্টাদশ শতকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। এসময়ের কাঁচা রেশমের দেশীয় বাণিজ্যের পরিমাণ সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যেতে পারে এই তথ্য থেকে যে, সুদূর আলিবর্দী খানের আমলে ইউরোপীয়দের বিনিয়োগ ছাড়াই প্রায় ৭০ লক্ষ টাকা মূল্যের কাঁচা রেশম মুর্শিদাবাদের সুষ্ক অফিসের হিসাবে ধরা হয়েছে। ১৬৭৫-৮০ খ্রিষ্টাব্দে বাংলা পরিভ্রমণের সময়ে স্টেশন মাস্টার কাসিমবাজারের চতুঃস্পার্শ্বস্থ গ্রামগুলো তুঁত গাছে পরিপূর্ণ দেখতে পেয়েছেন। বার বার মারাঠা আক্রমণের ফলে পশ্চিম বাংলার রেশম শিল্প ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়ে। কারিগররা গঙ্গার অপর তীরে পালিয়ে যায়। ঈস্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানি পদ্মার পূর্বতীরে তুঁত গাছের চাষ, রেশমের গুটি বর্ধন ও রেশমের সুতা পাকানো উৎসাহিত করার নীতি অনুসরণ করে। ফলে বোয়ালিয়া, জঙ্গীপুর, কুমারখালি, মালদহ, রাধানগর, রংপুর ও রাঙ্গামাটি প্রভৃতি অঞ্চলসমূহ রেশমি উৎপাদন কেন্দ্রে পরিণত হয়। রিয়াজুস সালাতীনে মালদহ এলাকায় উৎকৃষ্ট মানের রেশম উৎপাদনের কথা উল্লেখিত হয়েছে।