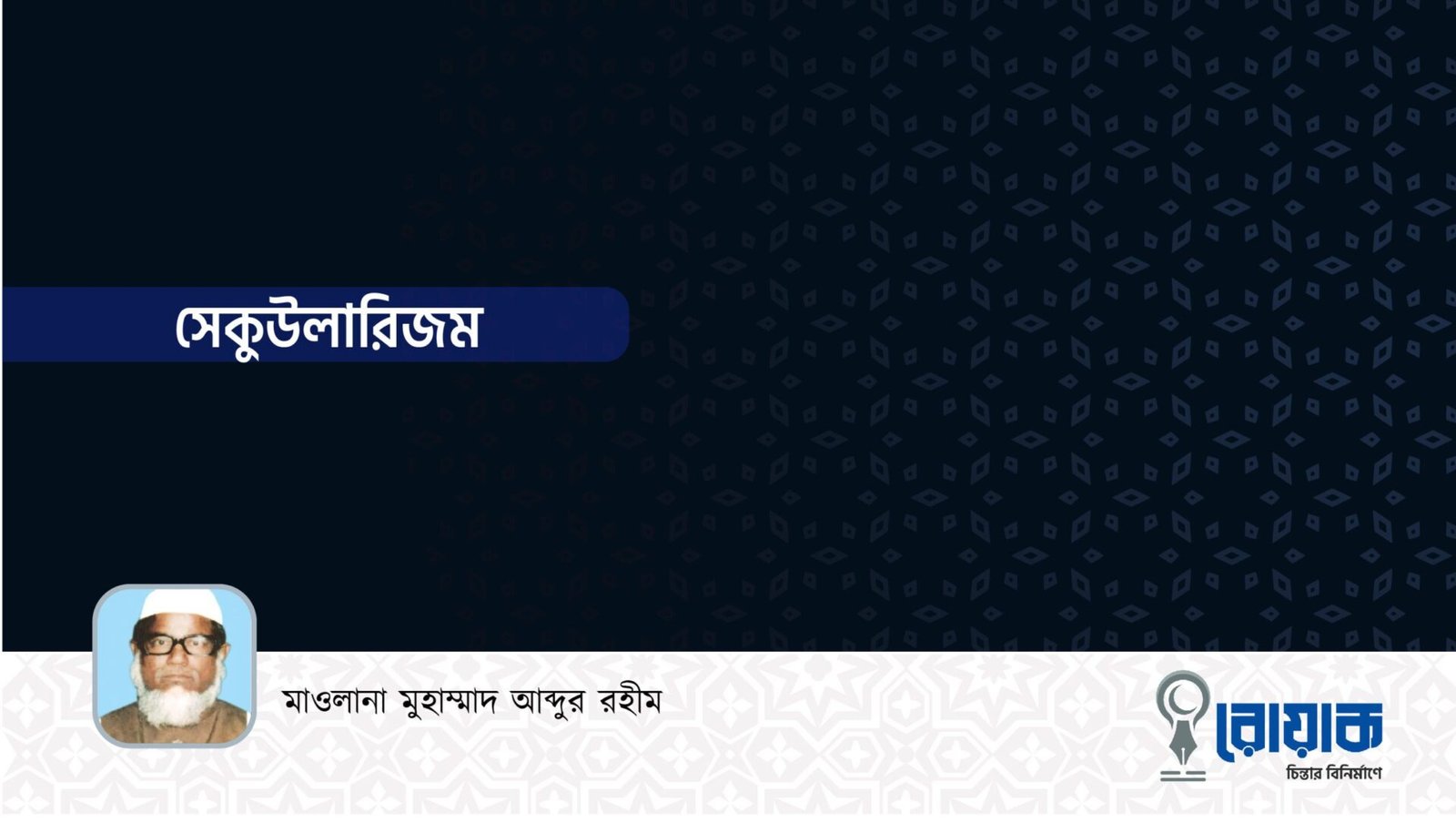‘সেকিউলারিজম’ ল্যাটিন শব্দ Saecularis থেকে উদ্ভূত। তার অর্থ বৈষয়িক (Worldly), অস্থায়ী (Temporal) এবং প্রাচীন (Old Age)। গীর্জার কোনো পাদ্রী যদি বৈরাগ্যবাদী খানকাহী জীবন পরিহার করে বৈষয়িক জীবন যাপনের অনুমতি লাভ করে তাহলে তাকে ‘সেকিউলার’ নামে অভিহিত করা হয়।
পারিভাষিক তাৎপর্যের দিক দিয়ে তা একটি মতাদর্শ, একটি বিশেষ ধরনের কার্যক্রম। তাতে যাবতীয় দ্রব্যাদি, বস্তু নিচয় এবং মানুষকে এই পার্থিব জগত পরিধির মধ্যে সীমাবদ্ধ মনে করা হয়। বাংলাভাষায় ‘সেকিউলারিজম’-এর অনুবাদ করা হয় ‘ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ’ অথবা ‘বৈষয়িকতাবাদ’ কিংবা ‘ধর্মহীনতাবাদ’। ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের ইচ্ছা ও সমর্থনের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধে রাষ্ট্র তার সমস্ত বিষয় সম্পত্তিকে নিতান্ত বৈষয়িক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করার লক্ষ্যে করায়ত্ত করে নেয়ার রক্তাক্ত ইতিহাসই তার উৎপত্তি-উৎস। ইতিহাসে এরূপ ঘটনার দৃষ্টান্ত অগণিত। ‘সেকিউলারিজম’ এর আরও অধিক বিস্তৃত তাৎপর্য বিশ্লেষণ স্বরূপ বলা যায়- মানব জীবনের বিভিন্ন উপাদান ঝোঁক-প্রবণতা, রসম-রেওয়াজ এবং অন্যান্য সামাজিক রূপ তথা স্বয়ং মানুষের জীবনকে কোনো ধর্মবিশ্বাসের ওপর ভিত্তিশীল না করাকেই বলা হয় ‘সেকিউলারিজম’। ধর্ম বিবর্জিত জীবনধারা (Adulthood) অবলম্বনই হচ্ছে ‘সেকিউলারিজম’। এক কথায় তা একটি বিশেষ মতাদর্শ (Ideology) রূপে গড়ে ওঠার জন্য ব্যর্থ চেষ্টায় রত।
‘সেকিউলারিজম’-এর উৎপত্তি ইউরোপে। ঊনবিংশ শতকে একদল ইংরেজ চিন্তাবিদ ‘সেকিউলারিজম’-কে একটা বিশ্বজনীন আন্দোলনে রূপায়িত করার চেষ্টা চালায়। এরা নিজেদের ‘সেকিউলারিস্ট’ ‘বৈষয়িকতাবাদী’ বা ‘ধর্মবিমুক্ত’ চিন্তাবিদ পরিচিয় নিয়ে আত্মপ্রকাশ করে। এদের মধ্যে বিশিষ্ট স্থান দখল করেছিলেন জি. জে হলিউক (১৮৫৪ খ্রিঃ)। তার মতে ‘সেকিউলারিজম’ হচ্ছে জনগণের ‘কর্মদর্শন’। Secularization শব্দটি প্রথমবারে একটি আইনগত পরিভাষারূপে ব্যবহৃত হতে থাকে। যেসব বিশেষ আন্দোলন ১৬৪৬-এর ত্রিশ বর্ষীয় যুদ্ধাবসানকালে সরকারের সাথে আলাপ আলোচনায় আত্মনিয়োগ করেছিল এবং যার ফলে Treaty of west phalia জনগণের সম্মুখে প্রকাশমান হয়েছিল এবং অষ্টদশ শতক থেকে যা Canon-Law রূপে গৃহীত হয়েছিল, তারই ফলে এই পরিভাষাটির উদ্ভব এবং প্রচলন! ঊনবিংশ শতাব্দীতে গীর্জাকে যখন সাংস্কৃতিক কার্যক্রমের ওপর বিশেষ করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ ও বস্তুগত কল্যাণের ব্যাপারাদির ওপর প্রভাব বিস্তার করা থেকে বঞ্চিত করে দেয়া হলো, তখন Secularization-এর তাৎপর্যে ব্যাপকতা ও গভীরতার সৃষ্টি হওয়া ছিল অত্যন্ত স্বাভাবিক ব্যাপার। ফ্রান্সে তখন Secularization-কে একটি পূর্ণাঙ্গ দর্শনরূপে গ্রহণ করা হয়। আর তার নাম দেয়া হয় Laicism তথা ধর্ম থেকে সম্পূর্ণ মুক্তি ও নিষ্কৃতি লাভ। কিন্তু ইংল্যান্ডে এই দর্শনের নাম দেয়া হয় ‘সেকিউলারিজম’ (Secularism)। উভয় পরিভাষাই ধর্মের প্রাধান্য ও সার্বভৌমত্বের সম্পূর্ণ পরিপন্থীরূপ পরিগ্রহ করে। অস্তিত্ববাদী, বস্তুবাদী ও অভিন্ন মৌলবাদী (Monism) বা অদ্বৈতবাদে বিশ্বাসীরাও এই পরিভাষাদ্বয়কে ব্যাপকভাবে ব্যবহার করেছে।
একালের কিছু সংখ্যক চিন্তাবিদ ‘সেকিউলারিজম’ ও ‘সেকিউলারাইজেশন’ এই পরিভাষাদ্বয়ের তাৎপর্যে পার্থক্য সৃষ্টি করতে সচেষ্ট। ‘সেকিউলারিজম’কে একটা মিথ্যা মতাদর্শরূপে উপস্থাপিত করা হয়েছে। আর ইংরেজি ভাষাভাষী দেশসমূহে ‘সেকিউলারাইজেশন’ ষষ্ঠদশ শতকের সেই ঐতিহাসিক স্বৈরতন্ত্র বোঝাবার জন্য ব্যবহৃত হয়েছে, যার অধীন অষ্টম হেনরী সরকার সমস্ত খানকাহ’ বাজেয়াপ্ত করে নিয়েছিল। ইতিহাসের প্রত্যেক অধ্যায়েই কোনো না কোনো ব্যক্তি বা জনগোষ্ঠী কিংবা রাষ্ট্রব্যবস্থা বিজয়ী ধর্মীয় রীতিনীতি ও ঐতিহ্যকে প্রত্যাখ্যান করে ধর্মীয় অনুশাসনকে অগ্রাহ্য করে চলেছে এবং তার প্রভাব থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হতে চেষ্টা চালিয়েছে। এ চেষ্টা মূল ধর্মের মতোই প্রাচীন। এ চেষ্টা-প্রচেষ্টা ও প্রবণতা নিজ নিজ অবস্থা ও পরিবেশ অনুযায়ী বিভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করেছে। খ্রিষ্টপূর্ব চতুর্দশ শতাব্দীতে মিশরীয় ফেরাউন আখ্-ইন-আতুন (Akn-cn-aton) একটি অপেক্ষাকৃত বুদ্ধিবৃত্তিক ব্যবস্থার খাতিরে স্বীয় সাম্রাজ্যের পরিসীমার মধ্য থেকে ঐতিহ্যবাহী উপাস্য দেবদেবীর ও পূজা-উপাসনার নিয়মাদি নির্মূল করে দিয়েছিল। তাছাড়া জীনোফিনিজ ও এন ইজারাস থেকে শুরু করে সক্রেটিস পর্যন্ত গ্রীক দার্শনিকগণ এবং পরে এপিকিউরিন নিজ সময়ের সব দেবদেবী ও দেবমালা পর্যায়ের ধারণাসমূহের যে তীব্র সমালোচনা করেছে তা-ও সর্বজনবিদিত। ধর্মতত্ত্ব সংক্রান্ত বিদ্যার ইতিহাসে লক্ষ্য করা যায়, প্রায় প্রত্যেকটি ধর্মের আকীদা-বিশ্বাস ও আদেশ-উপদেশকে একটি সংকীর্ণ শ্রেণির লোকেরা সবসময়ই সন্দেহ ও সংশয়ের দৃষ্টিতে দেখছে। বাহ্যিকভাবে ও বৈষয়িক সুযোগ-সুবিধার কারণে তারা ধর্মকে হয়ত সম্পূর্ণ অস্বীকার করেনি, কিন্তু একটি প্রশ্নহীন ও সংশয়মুক্ত অন্তর দিয়ে তা তারা কখনোই গ্রহণ করেনি। বাস্তব জীবনের প্রত্যেক পদে তাকে এড়িয়ে চলতেই চেষ্টা করেছে।
মূলত ‘সেকিউলারাইজেশন’ (Secularization) এবং সেকিউলারিজম (Secularism)-এর মধ্যে মৌলিক ও তত্ত্বগত কোনো পার্থক্য নেই। উভয়টিকেই ‘নিতান্ত বৈষয়িক আদর্শ’ বললে কিছুমাত্র ভুল বলা হবেনা, ‘সেকিউলারিজম’ বর্তমান শতাব্দী পর্যন্ত একটি বিরল ও অস্থায়ী মতাদর্শরূপেই বিরাজমান।
যে সময়ে এই মতাদর্শটির উৎপত্তি ঘটে, তখন দুনিয়া ও মানুষের ব্যাখ্যা দেয়া হতো অত্যন্ত স্থবির ধরনের দেবমালা সঙ্গাত ভঙ্গিতে। সমস্ত সামজিক রীতিনীতি ও ব্যবস্থা ধর্মীয় বন্ধনে আবদ্ধ ছিল। এমনকি প্রাকৃতিক শক্তি ও উপাদান ব্যবহারের ক্ষেত্রেও যাদুমন্ত্রের আশ্রয় গ্রহণ করা হতো। তা-ও ছিল ধর্মের একটা বিকৃত রূপ।
সেকিউলারিজম-এর দুটো দিক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দিকটি হচ্ছে, তা জনগণের বৈষয়িক জীবনকে উন্নত বানাতে আগ্রহী। আর এটাই তার নৈতিকতার দিক। কেননা নৈতিকতার সম্পর্ক সমাজের মধ্যকার এমন সব কাজের সাথে, যে সবের সাথে লাভ ও লোকসানের কোনো-না-কোনো সম্পর্ক থাকে। কিন্তু সেকিউলারিজমে এই পর্যায়ের কার্যাবলীর ভিত্তি কোনো ধর্ম বা পরকালে বিশ্বাসের ওপর স্থাপিত নয়। ফলে তা ধর্মকে অস্বীকার করেও ধর্মের লক্ষ্য অর্জনে সচেষ্ট। অন্যকথায়, ইতিবাচকভাবে তা একটি নৈতিক আন্দোলন বিশেষ। কিন্তু নেতিবাচকভাবে তা একটি ‘ধর্মীয় আন্দোলন’-ও বটে। তার উৎপত্তি লাভে বিশেষ ধরনের রাজনৈতিক অবস্থা ও দার্শনিক প্রভাব বিশেষ সাহায্যকারী প্রমাণিত হয়েছে।
সেকিউলারিজমের বিকাশ
রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণে ১৮৩২ খ্রিষ্টাব্দের সংস্কারমূলক বিল-এর পূর্ব ও পরবর্তীকালীন অস্থিরতা, বিপর্যয় ও দাঙ্গা-হাঙ্গামার ফলে এই মতবাদটির উৎপত্তি ঘটে। তার অন্তঃস্থিত বস্তু অনেকটা রবাট ঊন এবং তার অনুসারীদের অবিন্যস্ত ও সম্পর্কহীন সমাজতন্ত্র এবং ভাগ্যাহত চার্চিস্ট আন্দোলনের ফসল। তা চরমপন্থী চার্চিস্ট ও ইউরোপীয় মহাদেশে সৃষ্ট বিভিন্ন বিপ্লবের দরুন জনমনে জেগে ওঠা বিপ্লবাত্মক আশা-আকাঙ্ক্ষার চরম ব্যর্থতার পর ১৮৪৮ খ্রিষ্টাব্দে উদ্ভূত হয়েছিল। সেকিউলারিজম সামাজিক ও রাজনৈতিক বিকাশকে সংগঠন ও প্রশিক্ষণ প্রভৃতি শান্তিপূর্ণ উপায়ের সাহায্যে অগ্রসর করে নেয়ার একটা কার্যক্রম ছিল।
অস্বীকার করার উপায় নেই, অত্যন্ত নিকৃষ্ট ও তীব্র ধরনের সামজিক বিপর্যয়ের পরিণতি স্বরূপ ‘সেকিউলারিজম’-এর উদ্ভব ঘটেছিল। ধনশালী ও প্রভাব প্রতিপত্তি সম্পন্ন লোকদের লালসা, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় স্বাধীনতার পথে অযৌক্তিক ও অসঙ্গত প্রতিবন্ধকতা এবং গীর্জীয় ধর্মতত্ত্বের বন্ধ্যা অহমিকতা প্রভৃতি উপাদান ‘সেকিউলারিজম’ সৃষ্টির নিমিত্ত হয়েছিল। এরই ফলে শ্রমজীবী শ্রেণি যখন অবস্থার চরম অবনতি সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠে, তখন তাদের মধ্যে শুধু যে চরমবাদী রাজনৈতিক মতবাদই মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে তাই নয়, ধর্ম বিদ্বেষ ও ধর্মের প্রতি মারাত্মক প্রতিহিংসামূলক প্রবণতাও জন্মলাভ করে, তা কোনো ক্রমেই অস্বীকার করা যায় না।
‘সেকিউলারিজম’ মূলগতভাবে একটি প্রতিবাদ ও বিক্ষোভ মূলক আন্দোলন ছিল। আর সমস্ত বিক্ষোভমূলক আন্দোলনই ভাবাবেগ সৃষ্টিকারী শক্তির সাহায্য নিয়ে বিশেষ ধরনের উত্তেজনা সৃষ্টি করে থাকে, তা-ই তার প্রকৃতি। এই কারণে তাতে অনিবার্যভাবে বহু প্রকারের দোষত্রুটি ও দুর্বলতা থেকে যায়। তাতে ভারসাম্যহীনতা অনিবার্য হয়ে ওঠে। গঠনমূলক ভাবধারার পরিবর্তে বিপর্যয়কর কার্যক্রমের প্রবণতা প্রবল হয়ে থাকে। দ্বিগুণ অথবা চারগুণ ভাবালুতার বিভ্রান্তিকর প্রয়োগ, দৃষ্টি সংকীর্ণতা ও নেতিবাচক আচরণ প্রভৃতিই এসব আন্দোলনের প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্যে পরিণত হয়। আর প্রচলিত আকীদা-বিশ্বাসের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড প্রতিক্রিয়া হিসেবেই তা আত্মপ্রকাশ করে। ‘সেকিউলারিজম’ যদিও একটি ইতিবাচক নীতি অনুসরণ ও উপস্থাপনের চেষ্টা চালিয়েছিল; কিন্তু এই ‘ইতিবাচক-নীতি-চিন্তা’ একটি বৃত্তের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রয়ে গেছে। ‘সেকিউলারিজম’-এর দৃষ্টি সংকীর্ণতার মূলে বিশেষ কারণ নিহিত। আর তা হচ্ছে, জীবন ও কর্ম পর্যায়ে বেশিরভাগ প্রয়োগ ও বাস্তবায়নের বিরুদ্ধে তা প্রবল ঘৃণা ও বিদ্বেষের অস্ত্র ব্যবহার করেছে। জীবন ও কর্মের গুরুত্ব খুব সামান্যই স্বীকৃত হয়েছে।
‘সেকিউলারিজম’-এর দার্শনিক ভিত্তি জেমস মিল ও জিরামী বেনহাম-এর শরীকানাবাদী চিন্তাপদ্ধতি পর্যন্ত বিস্তীর্ণ। তার একটা নিজস্ব ধর্মবিরোধী দৃষ্টিভঙ্গি ছিল। পাইন ও রিচার্ড কারলাইল তা-ই লাভ করেছিল উত্তরাধিকারসূত্রে। ‘সেকিউলারিজম’-এ ইতিবাচকতার প্রভাব ইংরেজদের প্রতিধ্বনি ছাড়া আর কিছুই নয়। যদিও ‘সেকিউলারিজম’ সে ইতিবাচকতার প্রতি আদৌ কোনো ভ্রূক্ষেপ করেনি, তার প্রতি আরোপ করেনি একবিন্দু গুরুত্ব। মানবতাকে দেবতার আসনে আসীন না করলেও নিজের মধ্যে ইতিবাচক শিক্ষাদর্শনের সংমিশ্রণ করে নিয়েছে। ‘সেকিউলারিজম’-এ এই প্রভাব জি. এইচ. লিউস. এবং জে. এস. মিল থেকেই আমদানী করেছে। ‘সেকিউলারিজম’ যখন মিল্-এর সম্মুখে পেশ করা হলো, তখন সে তাকে সত্যতার সনদ দিয়ে ধন্য করে দিলো। অনুরূপভাবে দার্শনিকতার দিক দিয়ে ‘বৃটেনিয় সুবিধাবাদ’ তার আধ্যাত্মিক গুরু প্রমাণিত হয়েছে। যেসব তিক্ত রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থার কারণে এ আন্দোলনের মূল হোতাগণ সমসাময়িক সার্বজনীন মতবাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিল, তা-ই ছিল এই ‘সেকিউলারিজম’ আন্দোলনেরও মূল কারণ, কিন্তু তার অন্তঃস্থিত প্রভাব ছিল দার্শনিক ধরণের। আর তা হওয়াও ছিল একান্তই অনিবার্য। কেননা ‘সেকিউলারিজম’ যখন প্রকাশ্যভাবে ধর্মের সাথে সকল সম্পর্ক ছিন্ন করে দিলো, তখন তা জীবন ও কর্ম পর্যায়ে একটা নতুন দার্শনিক মতাদর্শ গড়ে তুলেছিল। বিশেষভাবে, নৈতিকতার পর্যায়ে এই দর্শন ছিল অত্যন্ত প্রকট। এই মতাদর্শই ‘সেকিউলারিজম’-কে তার কাঙ্ক্ষিত ভিত্তি সংগ্রহ করে দিয়েছিল।
সেকিউলারিজম-এর উদ্ভাবক
‘সেকিউলারিজম’ তার নামকরণ ও সত্তার দিক দিয়ে অনেকটা জর্জ জ্যাকব হলিউক-এর নিকট অনুগ্রহ এবং ঋণের জালে বন্দী। হলিউক ১৮১৭ খ্রিষ্টাব্দে বার্মিংহামে জন্মগ্রহণ করেছিল। তার পিতা ছিল কঠোর পরিশ্রমী হস্তশিল্পী। গোঁড়া ধর্মীয় পরিবেশে তাঁর লালন-পালন সম্পন্ন হয়েছিল। তার জন্মভূমির পরিবেশ ও বাল্যকালীন পারিপার্শ্বিকতা তার মধ্যে তীব্র ধরণের রাজনৈতিক ও সামাজিক আকীদার জন্ম দেয়। ১৮৩২ খ্রিষ্টাব্দের সংস্কারমূলক বিল পাশকরণ জলন্ত আগুনে তেল ঢালার কাজ করে। তখন হলিউক ছিল পনেরো বছরের এক সংবেদনশীল কিশোর। ফলে তার মন গীর্জার প্রতি অনাস্থাভাজন হয়ে পড়ে। কেননা গীর্জা সাধারণ মানবিক সংবেদনশীলতা ও অনুকম্পাপরায়ণতা থেকে সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত ছিল। সে ‘ঊন’ -এর সমাজ সংস্কারক ও প্রচারক হিসেবে রাজনৈতিক জীবনে সর্বপ্রথম পদার্পণ করেন।
অতঃপর ‘চার্টিজম’ (Chartism) এর সাথে তার সম্পর্ক গড়ে ওঠে। পরবর্তীতে চার্টিজম-এর আন্দোলন ব্যর্থতায় পর্যবসিত হলে হলিউক চরমপন্থী (Radical) মৌলবাদী চিন্তার ধারকের রূপ পরিগ্রহ করে। ১৮৪১ খ্রিস্টাব্দে সে দৃঢ় নিশ্চয়তা সহকারে সৃষ্টিকর্তাকে অস্বীকার করে, পরে ‘চেশটনহাম’ নামক স্থানে তাকে ‘কাফের’ আখ্যায়িত করে গ্রেফতার করা হলে খ্রিষ্টান ধর্মের প্রতি তার ঘৃণা অধিকতর তীব্র, গভীর ও প্রচণ্ড হয়ে ওঠে। কিন্তু হলিউক তার সমসাময়িক বিশ্বাসগত নাস্তিকতাবাদের প্রতিও কোনো সহানুভূতি পোষণ করত না। তার নাস্তিকতা ছিল ‘আমি জানিনা’ পর্যায়ের। সে তার স্বতন্ত্র ধরনের চিন্তাধারার প্রকাশ ও প্রচার করেছিল অসংখ্য পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে। The Reasoner পত্রিকায় সে লিখেছিল: “আমরা কাফের নই যদি এই পরিভাষাটির প্রয়োগ খ্রিষ্টীয় তত্ত্ব অস্বীকৃতির উপর হয়, তাহলে বলব, আমরা সকলে খ্রিষ্টধর্ম সৃষ্ট ভ্রান্তিমূলক রীতিনীতি আদর্শকে প্রত্যাখ্যান করছি।” যেসব খ্রিষ্টান ব্যক্তি রাজনৈতিক ও সামাজিক চিন্তায় তার সাথে একমত ছিল হলিউক তাদের সাথে সম্পর্ক দৃঢ় করে রেখেছিল। মুরাঈম ও কিংয়ের ”ক্রিশ্চিয়ান স্যোশ্যালিজম” -এর দিকে তার ঝোঁক তাদের সাথে একত্মতার নিশ্চয়তা বিধান করছিল।
কিন্তু প্রকৃত সমাজতন্ত্রের মতাদর্শগত বিশেষত্বের দরুন সে তা প্রত্যাখ্যান করেছিল। এই কারণে সমাজতন্ত্রের সঙ্গে খ্রিষ্টবাদের সংমিশ্রণকে সে অত্যন্ত জরুরী বলে মনে করতো। হলিউক কয়েক বছর ধরে জনকল্যাণমূলক ও সমবায়ী আন্দোলনের সাথে অত্যন্ত সম্মানজনকভাবে সংশ্লিষ্ট থাকে। মধ্যম বয়স থেকে একজন পুস্তক ব্যবসায়ী হিসাবে লন্ডনের স্থায়ী অধিবাসী হয়ে থাকতে শুরু করে। এই সময়ে ইটালির স্বাধীনতাই হয়েছিল তার অবসরহীন ব্যস্ততা ও গভীর আন্তরিকতার একমাত্র কেন্দ্রবিন্দু। জীরেমী বাল্ডমি ও মীজেনী উভয়ই ছিল তার ঘনিষ্ঠতম বন্ধু। যে সব হতভাগ্য ইংরেজ সিপাহীকে ইটালির সাহায্যার্থে প্রেরণ করা হয়েছিল, তাদের প্রশিক্ষণদানে সে তখন সর্বান্তঃকরণে ও সার্বক্ষণিকভাবে ব্যতিব্যস্ত হয়ে থাকতো। জীবনের শেষভাগে সে ব্রাইটনে বসবাস শুরু করে এবং ১৯০৫ খ্রিষ্টাব্দে এখানেই তার জীবনের অবসান ঘটে। এই বছরের শুরুতে অনুষ্ঠিতব্য সাধারণ নির্বাচনের সে ছিল সক্রিয় সমর্থক এবং জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত স্বাধীন চিন্তার বিজয়ের সুসংবাদ শ্রবণের জন্য সে হয়েছিল অত্যন্ত ব্যাকুল।
ঊনবিংশ শতাব্দীতে যেসব লোক খ্রিষ্টান বিরোধী প্রচারণাকে প্রচণ্ড ঝটকার ন্যায় পরিচালনা করেছিল, হলিউক তার দীর্ঘ জীবনে তাদের সকলের সাথে গভীর সম্পর্ক রক্ষা করে চলেছে। কিন্তু ঠিক সেই সময়েই সে খ্রিষ্টবাদের প্রখ্যাত প্রচারকবৃন্দের সাথেও সম্পৃক্ত রয়েছে। ডবলিউ. ই. গ্রেডেস্টোন এদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সে হলিউককে একজন স্বতন্ত্র ধরণের বিশ্বস্ত বিরোধী ব্যক্তি বলে মনে করতো।
চার্লস ব্রেডলাফ (Charles Bradiaugh)-এর অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে হলিউকের তুলনায় অধিক মর্যাদাবান ব্যক্তি আর কেউ ছিল না। (তার অর্থে, ধর্মের মৌলিকতার বিরুদ্ধে তার ঘৃণা ছিল না। তার ঘৃণা ছিল ধর্মের বন্ধ্যা গীর্জীয় প্রকাশের বিরুদ্ধে) তার দলের বিপুল সংখ্যক সদস্য তার বিরুদ্ধে যেসব আপত্তি উত্থাপন করেছিল, তা ছিল হলিউকের স্পষ্ট ও দ্বিধামুক্ত ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের জীবন্ত প্রমাণ।
‘সেকিউলারিজম’-কে প্রতিষ্ঠিত করণ প্রচেষ্টায় হলিউকের সহকর্মীদের মধ্যে চার্লস সাউথ ওয়েল, থমাস কুপার (পরে সে খ্রিষ্টান হয়ে গিয়েছিল), থমাস পিটার্সন ও উইলিয়াম বিল্টন প্রমুখ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ১৮৪৯ খ্রিষ্টাব্দে এই আন্দোলনের সূচনা হয়। হলিউক এই আন্দোলনকে নাস্তিকতাবাদের ‘উত্তম বিকল্প’ বলে অভিহিত করেছিল। ১৮৫০ খ্রিষ্টাব্দে ব্রেডলাফ এর সাথে হলিউকের সাক্ষাৎ হয় এবং ১৮৫১ খ্রিষ্টাব্দে সে ‘সেকিউলারিজম’ পরিভাষাটি রচনা করে। সে Netheism Limitatonism -কে সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষা করে চলেছে। অথচ নিজেদের বিশেষত্বের দিক দিয়ে এই দুইজন নাস্তিকতাবাদের ”উত্তম বিকল্প” হওয়ার অধিক অধিকারী ছিল। ‘সেকিউলারিজম’ পর্যায়ে তার বক্তব্য ছিল- ”এটি বর্তমান জীবনের আওতাভুক্ত কর্তব্যসমূহ উত্তমভাবে পালনের মতাদর্শ।” হলিউক ‘সেকিউলারিজম’-এর ধর্মবিরোধী মর্যাদাও ব্রেডলাফ-এর নাস্তিকতাবাদী মতাদর্শসমূহের মধ্যে কিছুটা পার্থক্য প্রকাশ করেছে। যদিও চার্লস ওয়াটস, জি ডাবলিউ ফিট ও অপরাপর ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্য এই ‘সেকিউলার’ আন্দোলনের ফলেই বহাল রয়েছে। কিন্তু হলিউক সবসময়ে চেষ্টা চালিয়েছে এজন্য যে, সামাজিক, রাজনৈতিক ও নৈতিকতার লক্ষ্যে নাস্তিকতাবাদী বিশ্বাসকে জরুরী শতরূপে কখনই যেন গণ্য করা না হয়। তাহলেই স্বাধীন মুক্ত চিন্তার ধারক ব্যক্তিবর্গ নিজেদের নাস্তিকতাবাদের প্রতি কোনরূপ বিদ্বেষী মনোভাব ছাড়াই সে লক্ষ্যসমূহকে সম্মুখের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে তার সাথে ঐকান্তিকভাবে শামিল থাকতে পারবে। এই আবরণের ক্ষেত্রে তার বড় ধরনের সাফল্য লাভ না হলেও সে অত্যন্ত কঠোরতা ও অবিচলতা সহকারে এই নীতিকেই সচল রাখতে বদ্ধপরিকর হয়েছিল।
সেকিউলারিজম-এর মূলনীতি
সেকিউলারিজম-এর মূলনীতি হচ্ছে, মানুষের বৈষয়িক উন্নতির জন্য শুধুমাত্র বৈষয়িক বা পার্থিব উপায় উপকরণের ওপর একান্তভাবে নির্ভর করতে হবে। কেননা বৈষয়িক উপায় উপকরণ মানুষের করায়ত্ত হওয়ার কারণে অন্যান্য সব কিছুর তুলনায় অধিক গুরুত্ব পাওয়ার অধিকারী। তাছাড়া এই উপায় উপকরণসমূহ মানুষের কাঙ্ক্ষিত ও প্রয়োজনীয় সবকিছু অর্জনে অধিক উন্মুক্ততা সহকারে ব্যবহৃত হতে পারে। ‘সেকিউলারিজম’ একটা প্রবল মতাদর্শ হিসেবে মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছিল সেই সময়ে যখন বিজ্ঞান ও ধর্মের বিচ্ছিন্নতা ও সম্পর্কহীনতার দাবি অত্যন্ত প্রবল আকার ধারণ করেছিল।
সেকিউলারিজম-এর মত ছিল এই দাবির সাথে পুরামাত্রায় সংগতিপূর্ণ। সে কারণে ‘সেকিউলার’ তত্ত্বসমূহকে সম্পূর্ণ মুক্ত ও নিরপেক্ষ বলে ঘোষণা করা হয়েছিল। চলমান জীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতার ওপরই রক্ষিত হয়েছিল ‘সেকিউলারিজম’-এর ভিত্তি। সেই সাথে দাবি তোলা হয়েছিল যে, তাকে বিবেক বুদ্ধির সাহায্যে পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে বাস্তব অভিজ্ঞতার আওতায় নিয়ে আসা যায় অতীব সহজভাবে। মনে করা হয়েছে, অংক ও গণিতবিদ্যা এবং রসায়নশাস্ত্র যেভাবে ‘সেকিউলার’ বিদ্যার অন্তর্ভূক্ত, অনুরূপভাবে একটি কল্যাণমূলক জীবন ও মানবীয় কর্মপদ্ধতি সম্পর্কে ‘সেকিউলার’ দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলাও সম্ভব নয়। আর এই পদ্ধতিতেই বৈজ্ঞানিক শিক্ষা-ধারাকেও সচেতন পথ নির্দেশনায় সংযোজিত করা চলে।
এই কারণে ধর্মের সাথে ‘সেকিউলারিজম’-এর সম্পর্ক পারস্পরিক শত্রুতামূলক হওয়ার পরিবর্তে ভিন্নতর ও একক বলে বর্ণনা করা হয়েছে। ধর্মতত্ত্ব অদৃশ্য জগতের ব্যাখ্যা উপস্থাপিত করে আর ‘সেকিউলারিজম’ অদেখা জগত ও তার ব্যাখ্যার সঙ্গে সম্পূর্ণ সম্পর্কহীন। বাস্তব অভিজ্ঞতার আওতাভূক্ত জগতের সঙ্গেই সম্পর্ক সেকিউলারিজমের। পরকালীন জীবন পর্যায়ে তার কিছুই বলবার নেই-না তার পক্ষে ইতিবাচকভাবে, না তার বিপক্ষে নেতিবাচকভবে। এক আল্লাহর প্রতি ঈমান কিংবা নাস্তিকতা-এর কোনটি সেকিউলারিজম-এর অংশ নয়। কেননা বাস্তব পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে এ দুটির প্রমাণ করা যায় না বলে সেকিউলারিজম-এর ধারণা। অবশ্য ধর্মতত্ত্বের নৈতিক শিক্ষার সাথে তার একটা সম্পর্ক রয়েছে, কিন্তু সে জন্য বিশ্বাসের বিষয় উপস্থাপিত করে, তা ধর্মীয় বিশ্বাসের আওতাভূক্ত নয়। যেসব লোক বিভিন্ন কারণে ধর্মতত্ত্বের প্রতি একনিষ্ঠ বিশ্বাস স্থাপনে সক্ষম হচ্ছে না। ‘সেকিউলারিজম’ কেবল তাদেরই মহা আকর্ষণের জিনিস।
‘সেকিউলারিজম’ এর দাবি হচ্ছে পূর্ণাঙ্গ নৈতিকতা কেবলমাত্র সেকিউলার চিন্তা-ভাবনার মাধ্যমেই অর্জন করা যেতে পারে। যেমন- রাজমিস্ত্রী যে সামগ্রী দিয়ে নির্মাণ কাজ করে নির্মাণ কাজের সামগ্রী সে মিস্ত্রী ছাড়াও অর্জন করা সম্ভব। সেকিউলারিজম-এর ঘোষণা হচ্ছে, এই দুনিয়া ছাড়া ‘আলো’ আর কোথাও নেই। আর যদি থেকেও থাকে, তবুও তা মানবীয় লক্ষ্য অর্জনের সহকারী প্রমাণিত হতে পারে না। ধর্মীয় বিশ্বাস যতক্ষণ পর্যন্ত মানবীয় আনন্দ স্ফূর্তির সম্মুখে বাস্তব প্রতিবন্ধকতা দাঁড় না করাচ্ছে ‘সেকিউলারিজম’ ততক্ষণ পর্যন্ত তাকে সে অবস্থায়ই থাকতে দেয়! মরে কিংবা বাঁচে, তা নিয়ে তার কোনো মাথাব্যথা নেই। কিন্তু ঐতিহাসিকভাবে ‘সেকিউলারিজম’ সব সময়ই নাস্তিকতার সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত রয়েছে। যদিও হলিউক সব সময়ই এতদুভয়ের মাঝে পার্থক্য রক্ষার ওপর জোর দিয়েছে। সে ‘সেকিউলারিজম’ নীতিতে ব্রেডলাফ-এর সঙ্গে সানন্দে একাত্মতা ঘোষণা করেছে। সেকিউলার উপায়-উপকরণের সাহায্যে যে লোকই মানবতার পারস্পরিক গঠন ও উন্নয়নমূলক কাজে অংশ গ্রহণে ইচ্ছুক হতো, তার প্রতিই সে সহযোগিতার হস্ত প্রসারিত করতে প্রস্তুত ছিল। ইসলামে তাওহীদী আকীদা ও নাস্তিকতা এই উভয়কেই সে মাত্রাতরিক্ত বিশ্বাসবাদ মনে করত। ব্রেডলাফ-এর মত ছিল এর বিপরীত। সে মনে করত, ধর্মীয় আকীদা-বিশ্বাস প্রতিহত করাই সেকিউলারিজম-এর কর্তব্য। কেননা এই সব কুসংস্কার মূলক ধারণা-বিশ্বাস যতদিন পর্যন্ত পূর্ণ শক্তিতে প্রকাশিত হতে থাকবে, ততদিন পর্যন্ত বস্তুগত উন্নতি লাভ কল্পানাতীত হয়ে থাকবে। সেকিউলারিজম-এর দাবি হচ্ছে, যুক্তি উপস্থাপনের নিয়মে বিবেক-বুদ্ধি ও অনুধাবন দিয়ে তার মূলনীতি সমূহের প্রবর্তন ও পরিচ্ছন্নকরণের মাধ্যমে সেগুলোকে সমস্ত মানবতার ওপর অভিন্ন ভঙ্গিতে প্রয়োগ করা যেতে পারে। সে বলছে, নৈতিকতার ভিত্তি হচ্ছে যুক্তি প্রমাণ উপস্থাপনা। জ্ঞানের ক্ষেত্রে ভুল হতে পারে, ইহাও সংকল্পে তার সম্ভাবনা নেই বললেও অত্যুক্তি হয় না।
হলিউকের মতে, বস্তুগত অবস্থা এমন করা সম্ভব যেখানে দারিদ্র্য ও বঞ্চনার শিকড় হবে উৎপাটিত। উপযোগবাদীদের (Utilitarian) ন্যায় তারও বিশ্বাস ছিল, চরিত্রই হচ্ছে এমন একটি কার্যক্রম যা মানবতার সম্মিলিত কল্যাণ প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম এবং মহাসত্য দিবালোকের মতোই উজ্জ্বল ও অনস্বীকার্য। তার মতে বিজ্ঞান যেমন করে মানুষের সুস্বাস্থ্যের মৌলনীতি নির্দেশ করতে পারে, অনুরূপভাবে মানুষের স্বচ্ছলতার নীতিও উদ্ভাবন করতে সক্ষম। মানবীয় স্বচ্ছলতা অর্জনের জন্য যুক্তি-প্রমাণের সাহায্যে পথ-নির্দেশ লাভ করা আমাদের কর্তব্য। কিন্তু যুক্তি-প্রমাণ উপস্থাপনকালে ব্যক্তিগত কামনা-বাসনার অনুসরণ করা উচিত নয়। কেননা যুক্তি প্রমাণ উপস্থাপনের ব্যক্তিগত কামনা-বাসনা ও ইচ্ছা প্রয়োগ করে আমরা না দৃঢ় প্রত্যয় অর্জন করতে পারি, আর না নিয়ম-শৃঙ্খলা অর্জন করা সম্ভব হতে পারে। কেবলমাত্র নিরপেক্ষ বিবেক-বুদ্ধিই পারে নির্ভুল প্রত্যয় ও নিয়মতন্ত্র সংরক্ষণ করতে। অতএব বিবেক-বুদ্ধিকে অবশ্যই অনাসক্ত ও স্বাধীন- মুক্ত করে রাখা একান্তভাবে জরুরী। নীতি বিজ্ঞান ও ধর্মতত্ত্ব পার্যায়ে চিন্তা-গবেষণা বৈজ্ঞানিক চিন্তা-গবেষণার মতোই স্বাধীনভাবে অনুষ্ঠিত হওয়া উচিত। কোনো প্রকারেরই গবেষণা, সমালোচনা ও প্রচারণা প্রকাশনার কারণে কোনো আইনগত বা আত্মিক শাস্তির ব্যবস্থা হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়। জীবনের এই বাস্তব মতাদর্শ পেশ করে সেকিউলারিজম এমন একটা লক্ষ্য অর্জনে ব্রতী হয়, যা তার কথায় ধর্ম অর্থাবস্থায় ছেড়ে দেয়। তা সত্যকেই সনদরূপে মানে, সনদকে মতরূপে গ্রহণ করে না। তা কর্তব্যবোধের কল্যাণকে কল্যাণের কর্তব্যবোধের ওপর অগ্রাধিকার দেয়। It Topes Truth for Authority, not authorially for truth and substitutes. The piety for usefulness for the usefulness of piety.
মানবতার জন্য যা-ই উত্তম কল্যাণকর, পরীক্ষা-নিরীক্ষার উত্তীর্ণ বিবেক-বুদ্ধির সাহায্যেই তা নির্ধারণ করতে হবে এবং মানবতার স্রষ্টা নিশ্চয়ই তাকে স্বীকৃতি দিবে ও তা নিয়ে গৌরব প্রকাশ করবে। আধুনিক কর্তব্যবোধ স্বশক্তিতেই স্বীয় প্রকাশ ঘটাবে। আর ‘সর্বজ্ঞানী’ রকমারী আবেদন-নিবেদনে ক্ষুণ্ণ হবে না। কার্যত আমরা সাধারণ রীতি-নীতির অধীন। সেই সাধারণ রীতি-নীতির অনুসন্ধান এবং তদনুযায়ী জীবন যাপন করাই মানুষের কর্তব্য।
সেকিউলারিজম -এর উৎকর্ষ ও বিকাশের পরিবেশ
ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে সেকিউলারিজম-এর প্রভাব চতুর্দিকে ব্যাপকভাবে প্রকাশমান হয়ে পড়ে। এই যুগটাই ছিল খ্রিষ্ট ধর্মবিরোধী প্রতিক্রিয়া সেকিউলারিজমের এবং তা তার সহযোগী চিন্তা মতের স্মারক আন্দোলনের রূপ ধারণ করেছিল। উত্তরকালে তা খুব দ্রুততার সঙ্গে বিলীয়মান হয়ে পড়ে এবং সুসংবদ্ধ বুদ্ধিবাদে লীন হয়ে স্বাধীন সত্তা হারিয়ে ফেলে। বর্তমানে বুদ্ধিবাদই সেকিউলার প্রাণ-শক্তির নবতর রূপ উপস্থাপিত করছে। বলা আবশ্যক, সেকিউলারিজম-এর সোনালী যুগ ছিল তখন যখন তা স্বীয় সহযোগীদের ধর্মবিরোধী প্রচারণার সঙ্গে সামগ্রিকভাবে একাত্ম হয়ে গিয়েছিল। ব্রেডলাফ-এর ‘সেকিউলার’ আন্দোলনে যোগদান এই পর্যায়ের একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। অথচ হলিউক নাস্তিকতাকে ‘সেকিউলারিজম’-এর অন্তর্ভূক্ত করাকে কখনই জরুরী মনে করেনি। কিন্তু তা সত্ত্বেও ‘সেকিউলারিজম’-এ নাস্তিকতা ক্রমশ শামিল হয়ে গেলে তখন প্রাচীন দ্বন্দ্ব নিঃশেষ হয়ে গেল। বিজ্ঞান ও ধর্মের বিচ্ছিন্নতার একটা ভারসাম্যপূর্ণ মতাদর্শ বিজয়ী হয়ে দাঁড়ালো। কিন্তু এসব জিনিসের সাহায্যে সেকিউলারিজম-এর আসল বিশেষত্ব নিঃশেষ হয়ে গেল। ফলে তাকে একটি সুসংগঠিত আন্দোলনরূপে বাঁচিয়ে রাখা কঠিন হয়ে দেখা দিল। তা স্বীয় মৌল ভাবধারা ও রীতিনীতিসহ নিজের পুনরুজ্জীবন সুসম্পন্ন করতে পারবে কি? এ ব্যাপারে অধুনা সময়ে কঠিন সন্দেহ দেখা দিয়েছে।
সেকিউলারিজম ভূমণ্ডলে মানবীয় জগত-মানবীয় স্বার্থের সীমাবদ্ধতায় বিশ্বাসী। এ মতবাদ সম্ভব এবং কার্যত নিঃসন্দেহে সত্যভিত্তিক। কিন্তু মতাদৰ্শগত দৃষ্টিকোণে তাকে সত্যভিত্তিক প্রমাণ করা অত্যন্ত কঠিন। তবে, সেকিউলারিজম এই কথা প্রমাণ করার জন্যই ব্যর্থ চেষ্টায় রত রয়েছে। বাস্তব দৃষ্টিতে বিবেচনা করলে লক্ষ্য করা যাবে, অসংখ্য লোকের স্বার্থ ও সম্পর্ক সম্বন্ধ জীবনের বস্তুগত দিকসমূহের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত হয়ে রয়েছে। দুনিয়ায় এই আচরণই কর্মোপযোগী। কেননা অধিকাংশ লোকই জীবন ও কর্ম সম্পর্ক কোনো সচেতন ও সক্রিয় মতাদর্শের ধারক নয়। কোনো মতাদর্শের প্রয়োজনও হয় না তাদের। অন্য কথায়, মতাদর্শের অনুপস্থিতিতেই বাস্তব সেকিউলারিজম-এর কর্মতৎপরতা নিহিত। সেকিউলারিজম কোনো আদর্শ নয়। তা হচ্ছে আদর্শের অস্বীকৃতি (Negation)। তা মানুষকে এইরূপ অপ্রয়োজনীয় ও অসম্পূর্ণ যুক্তি-প্রমাণ দেখায়, যা না চেয়েও সে সেকিউলারিজম-এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য পুরণ করছে, আর এটাই হচ্ছে ‘সেকিউলারিজম’-এর দুর্বলতা। এটা সরল মনের স্বাভাবিক বাস্তববাদী মানুষকে দার্শনিক ভিত্তি সংগ্রহ করে দেয়ার চেষ্টা করার মতোই হাস্যকর ব্যাপার। অথচ এই সরলমনা মানুষ বাহ্যিক সত্যের অস্তিত্বের জন্য তার সাক্ষ্যকেই অকাট্য প্রমাণরূপে গণ্য করে নেয়, এ বাহ্যিক সত্য তেমনই, যেমন আমাদের সম্মুখে তা বর্তমান রয়েছে। বাস্তবতার দৃষ্টিতে তার জন্য কোনো দার্শনিক ভিত্তির আদৌ কোনো প্রয়োজন নেই । মতাদর্শের দৃষ্টিতে এ ভিত্তি সংগ্রহ করা কঠিন, কেননা দর্শন প্রাথমিক পদক্ষেপেই সরল মনের মানুষের প্রতিপাদ্যসমূহকে অসান্ত্বনাদায়ক গণ্য করে। ‘সেকিউলারিজম’-এর অবস্থাও ঠিক তাই। অসংখ্য লোক বাস্তবভাবে সেকিউলার। কিন্তু জীবন ও কর্ম পর্যায়ের সব মতাদর্শই বিবেচনা সাপেক্ষ। কিন্তু সেকিউলারিজম তাকে কোনই গুরুত্ব দেয় না। হলিউক যদিও দাবি করেছিল যে, সেকিউলারিজম জীবন ও কর্মযোগের মতাদর্শ, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা ‘আমি জানিনার’ মতোই নিরপেক্ষ। এ দুয়ের মধ্যে পরম মৈত্রী বন্ধন। তা এ দুটির একটাকে নিঃসন্দেহে অস্বীকার করে। তা যেহেতু কর্মকে অপ্রয়োজনীয় মনে করে, এই কারণে তা সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হয়ে গেছে। উদ্দেশ্য লাভের কোনো অবকাশই এখন তার নেই। বাস্তবতার দৃষ্টিতে যে কোনো ব্যক্তি স্বীয় স্বার্থকে ‘সীমাবদ্ধতার মতাদর্শ’ ছাড়াই সীমাবদ্ধ করতে পারে এবং ‘নেতিবাচক মত’ ব্যতিরেকেই পারে তাকে অস্বীকার (Negation) করতে। এতদসত্ত্বেও আমরা যখন নিজেদের প্রতিই প্রশ্ন তুলি আমাদের নিজেদের জ্ঞানকে কেন সীমাবদ্ধ করে রাখতে হবে? তখন তা গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যানের আচরণ অবলম্বন করা কর্তব্য হয়ে পড়ে। আমরা এ দুটির কোনো একটিও উপেক্ষা করতে পারিনা। পক্ষান্তরে, ধর্ম এমন এক প্রকারের জ্ঞানের সন্ধান দেয়, যা বস্তুগত সম্পর্কের ঊর্ধ্বে অবস্থিত। এই ব্যাপারে ব্রেডলাফ হলিউকের তুলনায় অনেক বেশি দৃঢ়তার পরিচয় দিয়েছে। ধর্মবিরোধী মতাদর্শের সঙ্গে সেকিউলারিজমকে জড়িত করা হলে তা খুবই জীবন্ত ও প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। এই সত্য যখন প্রত্যক্ষ করা যায়, তখন উক্ত সত্য অধিকতর শক্তিশালী হয়ে ওঠে। ধর্মকে অস্বীকার করার পরিবর্তে তাকে উপেক্ষা করে বা এড়িয়ে চলতে চাওয়া অনেকটা অসম্ভব। কেননা ধর্ম বৈষয়িক ও আধ্যাত্মিক উভয় পর্যায়ের সম্পর্ককে পারস্পরিক যুক্ত করে উপস্থাপিত করে। ধর্ম গোটা জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করে। এটা ধর্মের বলিষ্ঠ দাবি। এই দাবি প্রতিরোধ বা খণ্ডন না করা পর্যন্ত সেকিউলার মতাদর্শ প্রতিষ্টা লাভ করতে পারে না। কিন্তু কার্যত তা অসম্ভব। আল্লাহ তো আছেন, কিন্তু তিনি বাস্তবজগতের সঙ্গে সম্পর্ক রাখেন না, এই প্রতিজ্ঞা (Theory) অগ্রহণযোগ্য ও অবাস্তব। যে ব্যক্তিই আল্লাহর প্রতি দৃঢ় প্রত্যয় রাখে, সে সমস্ত মহাসত্যের তুলনায় এই সত্যকে এক উচ্চতর বিশ্বাসরূপে গ্রহণ করে। তবে এটা অসম্ভব নয় যে, একজন তাওহীদবাদী ব্যক্তি স্বীয় কার্যকলাপে আল্লাহর বিধানকে হয়তো বাস্তবভাবে অনুসরণ করে চলছে না বা সেক্ষেত্রে আল্লাহর আইন-কানুনকে কার্যকর করেনি। আর তা না করে সে উল্লেখযোগ্য মাত্রায় নিজের অ-দৃঢ়তারই পরিচয় দিচ্ছে। কিন্তু এই কর্মপদ্ধতিকে যুক্তিযুক্ত প্রমাণ করার জন্য প্রয়োজনীয় শান্তনাদায়ক মতাদর্শ গড়ে তোলা খুবই কঠিন ও দুঃসাধ্য। এই কারণেই ‘সেকিউলারিজম’ যদি পূর্ণমাত্রায় ধর্মবিরোধী দৃষ্টিকোণ অবলম্বন না করে, তা হলে তার ব্যর্থতা অবধারিত হয়ে পড়বে। দার্শনিক দৃষ্টিকোণে-যেমন হলিউক পেশ করেছে সেকিউলারিজম-এর দুর্বলতা অনস্বীকার্য। তা এই সত্যে নিহিত যে, তা সত্য (Reality) মূল্যমান (Value)-এর মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করতে সম্পূর্ণ অক্ষম রয়ে গেছে। এই ব্যর্থতা ধর্মপরায়ণতারও রয়েছে, বলা চলে। ঊনবিংশ শতাব্দীতে তা যখন স্বীয় দাবিসমূহকে বৈজ্ঞানিক রঙ মিশ্রিত করে পেশ করতে চেয়েছিল, তখন তা প্রকট হয়ে উঠেছিল।
সেকিউলারিজম মতাদর্শের আহ্বায়কদের মতে, মহাসত্য বাস্তব পরীক্ষা-নিরীক্ষার আওতা বহির্ভূত। বিজ্ঞানও এই কথা সমর্থন করে। মহাসত্য বিবেক বুদ্ধি পর্যায়ের ব্যাপার বলা চলে। কিন্তু মূল্যমানের গুরুত্ব ও চিরন্তনতা কেবলমাত্র আকীদার কার্যকরতার দরুনই উদ্ভূত হয়। ‘সেকিউলারিজম’ গণিতশাস্ত্র ও রসায়নের ওপর অনুমান করে সত্যসমূহের নৈতিক ব্যবস্থা গড়ে তুলতে চায়। তার সম্পর্ক কেবলমাত্র জ্ঞানের সঙ্গে, আকীদাহ বিশ্বাসের সঙ্গে নয়। এই ধরনের মৌলিক পার্থক্যের কারণে তা নির্বুদ্ধিতারই পরিচায়ক হয়ে দাঁড়ায়। তা সত্যের মানদণ্ডে তুলনামূলক মূল্যমানের পারস্পরিক ব্যাপারে ফয়সালা করে। সত্য (Truth) ও বিবেকবুদ্ধি (Reason) সম্পর্কে তার বক্তব্য আছে; কিন্তু এইসব পরিভাষা নিহিত নিগূঢ় সত্যতার সঙ্গে কি সম্পর্ক রয়েছে, তা না বুঝেই মত প্রকাশ করে। মনে হয়েছে, এই সব পারিভাষিক শব্দ স্বতঃই মূল্যমানসমূহের অস্তিত্বের প্রমাণ দিচ্ছে বলে ধারণা করা হয়েছে। তুলনামূলক মূল্যমানের পারস্পরিক পার্থক্যকে স্পষ্টভাবে বর্ণনা করে। উপযোগবাদ একটা দার্শনিক মতাদর্শ। তা-ই সেকিউলারিজমের চালিকাশক্তি। এখন পর্যন্ত তা-ই ছিল বিজয়ী। সেকিউলার নৈতিকতা অনুযায়ী কাজ করা তার পক্ষে সম্ভব ছিল। কিন্তু উত্তরকালে তারও যখন পরাজয় সূচিত হলো, তখন তা-ই সেকিউলারিজম-এর ভিত্তি ছিল বলে- অনিবার্যভাবে সেকিউলারিজম-এর দার্শনিক ভিত্তিসমূহও ব্যর্থতায় পর্যবসিত হলো। তাই সব কারণে তা জীবন ও কর্মের দর্শন হিসেবে অবশিষ্ট থাকতে পারেনি। তাই বলতে হয়, অবস্থার পরিবর্তনের সাথে সাথে তারও অনিবার্য অবসান সঙ্ঘটিত হয়। তার নৈতিক লক্ষ্য প্রশংসাযোগ্য হলেও তা কোনো উপযুক্ত ভিত্তি থেকে বঞ্চিত। ফলে মানবীয় চিন্তার কোনো শাশ্বত প্রকল্প দাঁড় করা তার পক্ষে সম্ভব হয়নি। ঠিক এই কারণেই দর্শনের কোনো গ্রন্থেই সেকিউলারিজম-এর উল্লেখ পর্যন্ত পাওয়া যায় না! একটি সুস্পষ্ট শিরোনাম দিয়ে এই বিষয়ে কোনো গ্রন্থেই আলোচনা করা হয়নি। কেননা তা মানব জীবনের জন্য কখনই কোনো আদর্শ বা Ideology হতে পারে না। সম্প্রতি ফেডারিক কমপ্লেসটন’ দর্শনের ইতিহাস পর্যায়ে একটি বিরাট গ্রন্থ রচনা ও প্রকাশ করেছেন। তাতে সকল প্রকারের দার্শনিক মতাদর্শের উল্লেখ রয়েছে, কিন্তু তাতে সেকিউলারিজম-এর কোনই উল্লেখ নেই। বার্ট্রান্ড রাসেল রচিত “পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস” গ্রন্থেও এই বিষয়টি অনুল্লেখিত রয়ে গেছে। “দর্শনের বিশ্বকোষ” এ-ও এই বিষয়ের নাম চিহ্ন খুঁজে পাওয়া যায় না। আরও মজার কথা এই যে, বস্তুবাদের লীলাকেন্দ্র মস্কো ‘দর্শনের অভিধান’ প্রকাশ করেছে কিন্তু তাতেও এই বিষয়টি খুঁজে পাওয়া যায়নি।
অ-ধর্মীয় ব্যবস্থা বা Laicism
ফ্রান্সে সেকিউলারিজম-এর পরিবর্তে Laicism পরিভাষাটি সাধারণ্যে প্রচলিত হয়েছে। এটা সেই সময়ের কথা, যখন তৃতীয় রিপাবলিকের অধীনে প্রকৃত মূল্যমানের জন্য গীর্জা ও রাষ্ট্রের মধ্যে দ্বন্দ্ব চলছিল। অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীতে এই পরিভাষাটি গীর্জা ও রাষ্ট্রের সমস্যাদির সমাধানের দিকে অধিকতর লক্ষ্য আরোপ করেছিল।
‘লেইসিজম’ এর আধ্যাত্মিক শিকড় হলো ‘রেনেসাঁ’ মানবতাবাদ এবং সবচাইতে বেশি করে ‘আধুনিকতাবাদ’ পর্যন্ত বিস্তীর্ণ। এই যুগেই দুনিয়ার স্বাধীন ও প্রকৃতিগত মূল্যমান স্বীকৃত হতে শুরু করেছিল জীবনের সকল বিভাগে। রাষ্ট্র, সমাজ, আইন, অর্থব্যবস্থা, সংস্কৃতি ও শিক্ষার কুসংস্কারাচ্ছন্ন ও কাল্পনিক সার্বভৌমত্ব কিংবা গীর্জার সর্বোচ্চ কর্তৃত্ব থেকে নিষ্কৃতি লাভের জন্য এই আন্দোলন পরিচালিত হয়েছিল। এ সময়ে ব্যক্তিকে নিজের ইচ্ছা মতো ধর্ম ও পেশা অবলম্বনের স্বাধীনতা দেয়া হয়েছিল। কিন্তু এ অধিকার কেবলমাত্র ব্যক্তি পর্যন্তই সীমাবদ্ধ ছিল। ধর্মীয় সংগঠনসমূহে এই চিন্তাধারায় প্রচার তখন পর্যন্ত খুব একটা ফলপ্রসূ প্রমাণিত হতে পারেনি। তবুও ধর্মীয় ‘কমিউনিটি’ গুলোকে একান্তভাবে ব্যক্তিগত অধিকারের ভিত্তিতে এক স্বতন্ত্র সংগঠনের মর্যাদা দেয়া হয়েছিল এবং জনগণের প্রতিনিধি বা গণ-জীবনের ওপর প্রভাবশালী হওয়ার অধিকার থেকে তাকে বঞ্চিত করা হয়েছিল। ধর্ম থেকে নিষ্কৃতি লাভের কার্যক্রমকে যখন শাসনতান্ত্রিক আইন বানানো হলো; তখন তার তাৎক্ষণিক পরিণতির রাষ্ট্র ও ধর্মের মধ্যে বিচ্ছিন্নতার সৃষ্টি হতে লাগল। ১৯০৪ মনে পোপের সঙ্গে বিচার বিভাগীয় ব্যবস্থাপনার যাবতীয় সম্পর্ক ছিন্ন করে দেয়া হলো। ১৯০৫ খ্রিষ্টাব্দে তৃতীয় রিপাবলিক-এর আইন প্রণয়নের মাধ্যমে তার সম্পূর্ণতা বিধান করা হলো। ১৮০১ সনের পোপের সঙ্গে কৃত চুক্তি নাকচ করে দেয়া হলো। সাধারণ অর্থভাণ্ডার থেকে গীর্জাকে আর্থিক সাহায্য দান বন্ধ করে দেয়া হলো। গীর্জার সমস্ত দালানকোঠা সরকার বাজেয়াপ্ত করলো ও সরকারী মালিকানাধীন বলে ঘোষণা করা হলো। তবে উপসনা শিক্ষা দানের জন্য নিয়োজিত সরকারী ও সনদধারী জনগোষ্ঠীকে এবং তাদের বাইরের সংগঠনসমূহকে এইসব দালানকোঠা বিনামূল্যে ব্যবহার করার অনুমতি দেয়া হয়েছিল। এসব সরকারী ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনাও সরকার কর্তৃকই নিয়ন্ত্রিত হচ্ছিলো। তৃতীয় রিপাবলিকের শিক্ষা ব্যবস্থা এক ধরনের সরকারী ধর্ম ছিল। যাকে বলা হতো ‘রাষ্ট্রীয় নাস্তিকতা’।
১৭৯৩-১৭৯৫ এর বিপ্লবের ‘খোদা ও মানুষের প্রেম’ (Theophilanthropism)-কে ধর্মের ‘উত্তম বিকল্প’ মনে করে নেয়া হলো। ১৮৮২ সনে যখন সরকার চালিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ থেকে ধর্মীয় পাঠ্য প্রত্যাহার করা হলো ঠিক তখনই এই পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছিল।
তখন ধর্মীয় শিক্ষার পরিবর্তে সরকারীভাবে বিরচিত নৈতিক শিক্ষা প্রচলিত করা হলো। প্রাথমিক পর্যায়ে আল্লাহ বিশ্বাসকে নৈতিক শিক্ষার প্রাথমিক উৎস রূপে অবশিষ্ট রাখা হয়েছিল বটে, কিন্তু ১৮৬৬ খ্রিষ্টাব্দে গঠিত Ligue Delienseignement আল্লাহর সমস্ত বিধান থেকে নৈতিকতাকে সম্পূর্ণরূপে দূর করে রাখার দাবি জানালো। এভাবে রাষ্ট্রীয় গির্জাও ধর্মের বিরুদ্ধে বিদ্রোহীদের পতাকা উন্নত করে ধরলো। ক্রমশ এই মতাদর্শ সার্বজনীন খ্যাতি অর্জন করে বসল। স্বাধীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের পক্ষে ধর্মীয় আইন-কানুন ছিল সবচেয়ে বড় বাধা। এই কারণে আইন প্রণয়নকে তার বিরুদ্ধে সবচেয়ে বেশি ঘুরিয়ে দেয়া হলো। ১৮৮০ খ্রিষ্টাব্দে খ্রিষ্টান ধর্মীয় চিন্তা-পদ্ধতিকে বেআইনী ঘোষণা করা হলো। অন্যান্য গীর্জার জনগোষ্ঠীকে সরকারী সনদ লাভের জন্য সরকারের নিকট দরখাস্ত দেয়ার নির্দেশ দেয়া হলো। ১৯০১ সনের আইন অনুযায়ী প্রত্যেক ধর্মীয় স্থান গ্রহণ ও তথায় নতুন ইমারত নির্মাণের জন্য সরকারের নিকট থেকে লাইসেন্স পাওয়াকে জরুরী করে দেয়া হলো। ১৯০৪ সনে নির্বিশেষে সমস্ত ধর্মীয় স্থানগুলোতে সকল প্রকারের ধর্মীয় প্রচারমূলক তৎপরতা নিষিদ্ধ করে দেয়া হলো। এই বিশেষ সমস্যা ফ্রান্সের ন্যায় ইউরোপের অন্যান্য অংশেও প্রবল হয়ে দেখা দিয়েছিল যে, শিক্ষা ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ ‘সেকিউলার’ রাষ্ট্রের অধীন রাখা হবে, না গীর্জাও কর্তব্যসমূহের অন্তর্ভুক্ত করে দেয়া হবে? রাষ্ট্র যখন ধর্মের বন্ধন থেকে নিষ্কৃতি লাভের জন্য কঠোর নীতি অবলম্বন করল, তখন ক্যাথলিক পন্থীদের পক্ষ থেকে তার বিরুদ্ধে প্রচণ্ড প্রতিরক্ষামূলক চেষ্টা-প্রচেষ্টা শুরু করে দেয়া হয়েছিল। কিন্তু রাষ্ট্রের Credo-কে শোনা ও দেখা ছাড়া তারা আর কিছুই করতে সক্ষম হলো না। রিপাবলিকান রাষ্ট্র এই নির্দেশ কার্যকর করার জন্য। অনুমতিপ্রাপ্ত নয়, একথা তারা বুঝতে পেরেছিল। ফরাসী ক্যাথলিক পন্থীদের অধিকাংশই নিজেদের প্রাধান্য বহাল রাখার কাল্পনিক আকাঙ্ক্ষার ওপর নির্ভর করে বেঁচে ছিল। কেননা ক্যাথলিক গীর্জার বাহ্যিক অবস্থিতির এটাই ছিল একমাত্র নিরাপত্তা ব্যবস্থা। ক্যাথলিকদের এই পদক্ষেপ ছিল একান্তভাবে আত্মরক্ষামূলক। এর দরুন রাষ্ট্র অত্যন্ত শক্ত প্রকৃতির হয়ে গেল। ফরাসী ক্যাথলিকদের অধিকাংশ লোক দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে সর্বাত্মক বিপর্যয়ের পর বিস্তৃত গহ্বর থেকে মুক্তিলাভ করতে সক্ষম হয়েছিল। তারা তাদের ধর্মীয় প্রাধান্য পুনরায় অর্জন করার জন্য চেষ্টানুবর্তী হয়ে উঠলো। পোপের ঘোষণাবলী যদিও ছিল আত্মরক্ষামূলক, তবুও তারা নিজেদের আচরণে ভারসাম্য রক্ষার নীতি অবলম্বন করতে শুরু করেছিল। কার্ডিনাল লাভী-জীবী সমঝোতামূলক সতর্কর্তার বাণী উচ্চারণ করতে শুরু করে দিয়েছিল। ১৯০৬ খ্রিষ্টাব্দে পাইস দশম (PIUS-X) গীর্জার যুক্তিসম্মত ও বৈধ কর্মনীতির ওপর প্রভাব বিস্তার করতে চাওয়ার তীব্র নিন্দা করতে শুরু করল স্বীয় বক্তৃতা ও ভাষণসমূহে। গীর্জা ও রাষ্ট্রের বিচ্ছিন্নতাকেও সে প্রত্যাখ্যান করলো। ১৯২৫ খ্রিষ্টাব্দে পাইস একদশ (PIUS-XI) তার পুস্তিকায় Laicism কে গীর্জার নিজস্ব শব্দ সম্ভারের অন্তভূক্ত করে নিল। গীর্জার বৈরাগ্যবাদী সতর্কতা অবশিষ্ট থাকলো এবং রাষ্ট্রের সঙ্গে নবতর সম্পর্কের কারণে তা আরও পরিপক্কতা লাভ করলো। ওদিকে ‘রাষ্ট্র’ গীর্জা থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া সংক্রান্ত আইনসমূহ খুবই ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা সহকারে কার্যকর করছিল। গীর্জা ও রাষ্ট্রের মধ্যকার ব্যবধান একটি চুক্তির সাহায্যে দূর করে দেয়া হলো। ১৯২১ খ্রিস্টাব্দে HOLYSEE ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত সম্পর্ক পুনর্বহাল করা হলো। ১৯৫৪ খ্রিষ্টাব্দে প্রধান পাদ্রী সংক্রান্ত ফরাসী ঘোষণা প্রচারিত হওয়ার পর গীর্জা চিন্তার আদান-প্রদানের দ্বার উম্মুক্ত রাখার নীতি গ্রহণ করলো। ১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দে Laicism-এর তাৎপর্য প্রকাশ করা হলো এই ভাষায় রাষ্ট্র ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের সেই আইনগত অধিকার ও সর্বোচ্চ ক্ষমতা-যা রাষ্ট্র ও জনগণের সার্বিক কল্যাণের লক্ষ্যে ব্যবহার ও প্রয়োগ করবে, তার ভিত্তিতে বেসরকারী আইনের অধীন ধর্মীয় সংগঠনসমূহের অস্তিত্ব এবং নাগরিকদেরকে ধর্মীয় স্বাধীনতার নিরাপত্তা দেয়া হবে। শিক্ষা ও শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানসমূহ পর্যায়ে CAMBRAI-এর আর্চ বিশপ ই. এম. গৌরী (E.M.GERRY)-র উদ্ধৃতি দেয়া হচ্ছে : ‘রাষ্ট্রীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ কোনো সাম্প্রদায়িকতার অধীন হবে না। সেগুলোর বিশেষ কোনো নামও রাখা হবে না। বরং সেগুলো হবে নিরপেক্ষ। না ধর্মের পক্ষে কোনো কথা বলবে, না তা ধর্মকে প্রত্যাখ্যান করবে।’
আর্চ বিশপের মতে, এটা Laicism-এর বিপরীত দিকে পদক্ষেপ। কেননা এটা একটি দার্শনিক মতাদর্শ। এর ভিত্তি উপযোগবাদ, বস্তুবাদ ও দার্শনিক নাস্তিকতার ওপর রক্ষিত। এরই বলে রাষ্ট্র সমস্ত বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের ওপর তা কার্যকর করে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানও তার অন্তর্ভূক্ত। (১৯৫৯ খ্রিষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসের ৩১ তারিখ) গীর্জার এই আচরণ ভ্যাটিক্যান-২ -এর সেসব ঘোষণা থেকে সমর্থন লাভ করলো, যাতে বৈষয়িক সত্যসমূহের পূর্ণাঙ্গ স্বাধীনতাকে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছিল। তারই ফলে খ্রিষ্ট ধর্মাবলম্বীরা নিজেদের পছন্দসই রাজনৈতিক ব্যবস্থা গ্রহণের পূর্ণ স্বাধীনতা পেয়ে গেল। অন্যকথায় রাষ্ট্রীয় কাঠামোর উভয় প্রান্তের বাইরে থেকে গীর্জা নিজের প্রাধান্যকে বাঁচিয়ে রাখার দাবি জানাচ্ছিল। অথচ একটু সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে বিবেচনা করলেই দেখা যায়, গীর্জা বাস্তবভাবে রাষ্ট্র ও ধর্মের বিচ্ছিন্নতাকে পূর্ণমাত্রার সমর্থন করে নিয়েছিল। আর সরকারেরও একমাত্র কাম্য ছিল তা-ই।
সেকিউলারিজম-এর এ দীর্ঘ বিস্তারিত ইতিহাস অকাট্যভাবে প্রমাণ করছে যে, তা একটি বিশেষ ইউরোপীয় পরিস্থিতির উৎপাদন। খ্রিষ্ট রাষ্ট্র যেমন সেকিউলার, খ্রিষ্ট ধর্মও অনুরূপভাবেই সেকিউলার। সেকিউলারিজম-এর সঙ্গে মুসলিম সমাজ তথা দ্বীন-ইসলামের বিন্দুমাত্রও সম্পর্ক নেই। তার সঙ্গে সামান্যতম সামঞ্জস্য-ও নেই। তাই ইসলামে সেকিউলারিজম সমর্থিত নয় যেমন নয় পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্র। কোনো মুসলমানের পক্ষেই সেকিউলারিজম-এর প্রতি বিশ্বাসী হওয়া কোনক্রমেই সম্ভব নয়। সম্ভব নয় সেকিউলারিজম-এর প্রতি বিশ্বাসী হয়ে দ্বীন-ইসলামের প্রতি একবিন্দু ঈমানদার হওয়া বা থাকা
কিন্তু এই সেকিউলারিজম-ই আমাদের দেশের রাজনীতি ও অর্থনীতিকে মারাত্মকভাবে প্রভাবিত ও কলুষিত করে ফেলেছে। সেকিউলার রাজনীতি মুসলমানদের সার্বিকভাবে ইসলামের বাইরে নিয়ে গেছে এবং পূর্ণাঙ্গরূপে ইসলাম প্রতিষ্ঠার পথে তা-ই হয়ে দাঁড়িয়েছে সর্বাপেক্ষা বড় বাধা। আর অর্থনীতির ক্ষেত্রে মুসলমানদের বাধ্য করেছে সুদ-ঘুষ-দুর্নীতি-শোষণ-প্রভৃতি সম্পূর্ণ ইসলাম পরিপন্থী কার্যক্রমের ধারক ও বাহক হতে। মুসলিম জীবনকে সার্বিকভাবে বিভ্রান্ত ও বিপর্যস্ত করে দেয়ার প্রধান হাতিয়ার হচ্ছে ইউরোপীয় খ্রিষ্টান সমাজ থেকে আগত এই সেকিউলারিজম। সেকিউলারিজম ইসলামী জীবনধারার প্রধান প্রতিবন্ধক। যে কোনো দিকে সেকিউলারিজমকে গ্রহণ করা হলে ইসলামী জীবন সম্ভব নয়। তাই ইসলামী জীবনাদর্শ গ্রহণ ও পূর্ণমাত্রায় প্রতিষ্ঠার জন্য সেকিউলারিজমকে জীবন, সমাজ, রাষ্ট্র ও অর্থনীতি থেকে সম্পূর্ণরূপে উৎখাত করা একান্তই অপরিহার্য।