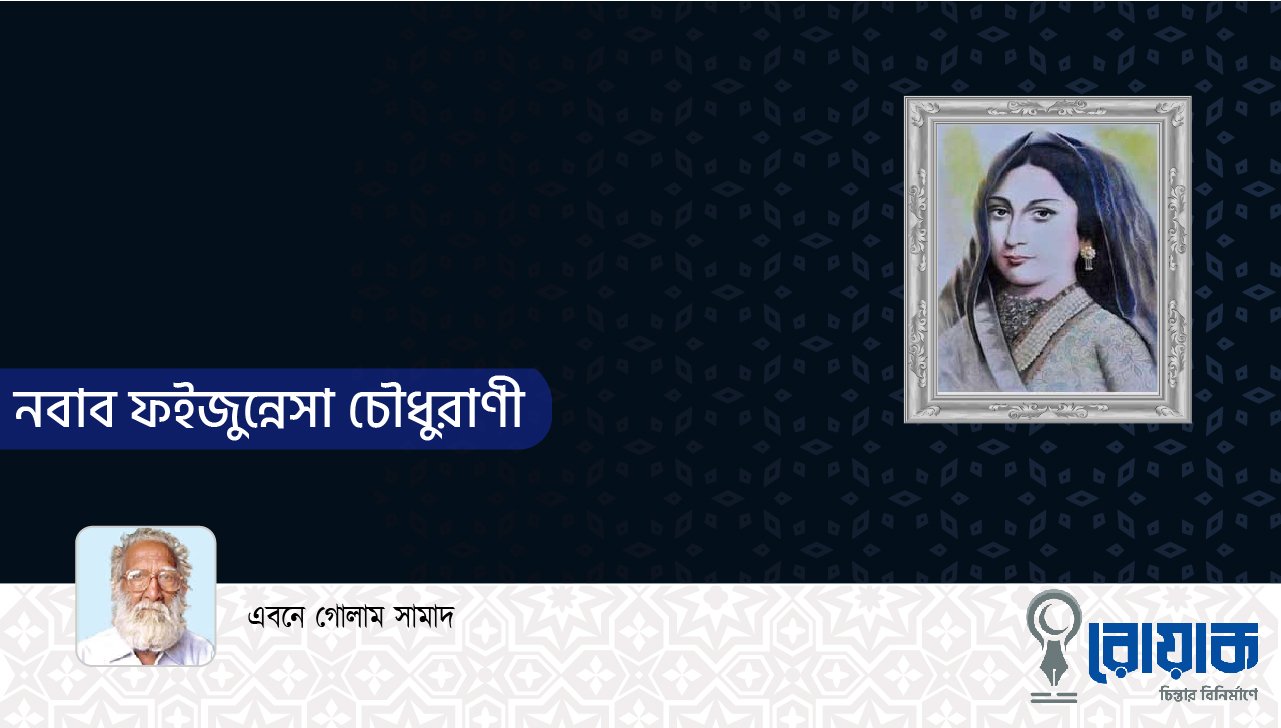নবাব ফইজুন্নেসা চৌধুরাণী (১৮৩৪-১৯০৩) শিক্ষা প্রবর্তক, সমাজ সেবিকা ও সাহিত্যিকা হিসেবে খ্যাত হয়ে আছেন। তিনি জন্মেছিলেন কুমিল্লা জেলার (তখনকার ত্রিপুরা জেলায়) লাকসামের (বর্তমানে উপজেলা) পশ্চিমগাঁও নামক গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম জমিদার পরিবারে। তাঁর পিতা আহমদ আলী চৌধুরী ছিলেন পশ্চিমগাঁওয়ের জমিদার। তাঁরা নিজেদের দাবি করতেন মোগল রাজবংশের সঙ্গে একসময় তাঁদের সংশ্লিষ্টতা ছিলো। ফইজুন্নেসা বাড়িতে একাধিক গৃহশিক্ষকের তত্ত্বাবধানে আরবি, ফারসি, সংস্কৃত ও বাংলা ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। নিজের সম্পর্কে বলতে গিয়ে তিনি বলেছেন,
‘আমি বাল্যাবস্থায় বয়স্যাদিগের সহিত ক্রীড়াকৌতুকে নিমগ্ন থাকিয়াও যথাসময়ে শিক্ষক সান্নিধানে অধ্যয়নাদি সম্পন্ন করিতাম।’
ফইজুন্নেসার বিবাহ হয় তাঁর ফুফাতো ভাই মুহাম্মদ গাজীর সঙ্গে। যিনি ছিলেন কুমিল্লার একজন বড় জমিদার। ফইজুন্নেসা ছিলেন তাঁর দ্বিতীয় স্ত্রী। গাজীর ঔরসে ফইজুন্নেসার দুই কন্যার জন্ম হয়। কিন্তু তিনি বিবাহিত জীবনে সুখী ছিলেন না। তাঁদের মধ্যে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটে। ফইজুন্নেসা ফিরে আসেন তাঁর পিতৃগৃহে। এ সময় তিনি রচনা করেন তাঁর বিখ্যাত সাহিত্যকীর্তি ‘রূপজালাল’ নামক গ্রন্থ। গ্রন্থটি অর্ধেকের বেশি পদ্যে লিখিত। বাদবাকি অংশ লিখিত হয়েছে সাধু বাংলা গদ্যে। বইটির কথা আগে তেমন জানা ছিল না, পরে জানা যায়। রূপজালাল প্রথম প্রকাশিত হয় ১৮৭৬ সালে। বইটি কিছুটা তাঁর আত্মজীবনীমূলক। বইটিতে আছে ফারসি সাহিত্যের প্রভাব। মুসলিম বাংলা সাহিত্য আর হিন্দু বাংলা সাহিত্য ঠিক এক ঐতিহ্যবহ নয়।
এ বিষয়ে বলতে গিয়ে প্রখ্যাত ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার তাঁর সম্পাদিত ‘বাংলা দেশের ইতিহাস’ নামক গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে বলেছেন,
‘বাংলা সাহিত্যে মুসলমান লেখকেরা এমন একটি নতুন বস্তু দিয়াছেন, যাহা হিন্দু লেখকেরা দিতে পারেন নাই। ধর্মনিরপেক্ষ বা লৌকিক কাব্য এবং বিশুদ্ধ প্রণয়মূলক কাব্য প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে তাঁহারাই প্রবর্তন করিয়াছেন। হিন্দুরা প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের যে সমস্ত ধারায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন, তাহাদের প্রায় সবই ধর্মমূলক, কারণ হিন্দুরা সাহিত্যকে ধর্মচর্চার মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার করতেন। কিন্তু মুসলমানরা সাহিত্যচর্চার মধ্য দিয়া ধর্মচর্চার বিশেষ প্রয়োজন অনুভব করেন নাই; এজন্য তাঁহারা ধর্মনিরপেক্ষ বা বিশুদ্ধ প্রণয়মূলক বিষয় অবলম্বনে বহু কাব্য রচনা করিয়াছেন। অবশ্য ধর্মমূলক বিষয় অবলম্বনেও তাঁহারা লিখিয়াছেন।’ (বাংলা দেশের ইতিহাস; দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৩৯২। প্রকাশক : শ্রীসুরজিৎচন্দ্র দাস; জেনারেল প্রিন্টার্স য়্যান্ড পাব্লিসার্শ প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা। ১৩৮০ বঙ্গাব্দ)।
মুসলমান লেখক ও লেখিকারা ফারসি রোমান্টিক কাব্যের অনুসরণ করতে চেয়েছেন। যার মধ্যে পড়ে ‘লাইলী মজনু’ এবং ‘ইউসুফ জুলেখা’র কাহিনী। ইউসুফ জুলেখার কাহিনীতে ইউসুফ নবিকে খুবই সুপুরুষ হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। মেয়েরা তাঁকে দেখে হতেন আকৃষ্ট। চাইতেন তাঁকে বিবাহ করতে। ইউসুফ জুলেখার কাহিনীর সাথে বেশকিছুটা মিল খুঁজে পাওয়া যায় ‘রূপজালাল’এর কাহিনীর। ‘রূপজালাল’ নায়ক জালাল হলেন খুবই সুপুরুষ। তাঁকে দেখে মেয়েরা সহজেই আকৃষ্ট হতে চায়। এতে আছে তাদেরই আকৃষ্ট হবার বিশেষ বর্ণনা। রূপজালাল হলেন রাজপুত্র। তাঁকে দেখে প্রথমে আকৃষ্ট হন দুই নারী, রূপবানু এবং হুরবানু। তিনি এদের বিয়ে করেন। কিন্তু তাঁর জীবনে আরও নারী আসতে চায়। এই নিয়ে হলো রূপজালালের কাহিনী। রূপজালাল ছাড়াও ফইজুন্নেসার আরও দুটি কাব্যগ্রন্থ আছে। একটির নাম হল ‘সঙ্গীতসার’ ও ‘সঙ্গীতলহরী’। কিন্তু ফইজুন্নেসার সাহিত্যিক খ্যাতি লাভ ঘটেছে রূপজালাল গ্রন্থের জন্য। তাঁকে বাংলা একাডেমি ২০০৪ সালে একুশে পদক (মরণোত্তর) প্রদান করে তাঁর এই সাহিত্যকৃতির জন্য। নবাব ফইজুন্নেসা চৌধুরাণী একাধিক বাংলা পত্রিকার পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন। যাদের মধ্যে ‘বান্ধব’, ‘ঢাকা প্রকাশ’, ‘মুসলমান বন্ধু’, ‘সুধাকর’ এবং ‘ইসলাম প্রচারক’ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এসব পত্রিকা সে সময়ে বাংলাভাষী মুসলমান সমাজ জীবনে এনে দিয়েছিল এক বিশেষ জাগরণের জোয়ার। কিন্তু ফইজুন্নেসা কেবল সাহিত্য চর্চা করেননি, তিনি বিশেষভাবে খ্যাত হয়ে আছেন তাঁর বিভিন্ন সমাজসেবা ও জনহিতকর এবং শিক্ষাবিস্তারমূলক কাজকর্মের জন্য।
তিনি কুমিল্লায় মেয়েদের জন্য একটি স্কুল করেন। যা এখন পরিণত হয়েছে নবাব ফইজুন্নেসা সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়। তিনি মেয়েদের জন্যপশ্চিম গাঁওয়ে একটি উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন। যা এখন উন্নীত হয়েছে নবাব ফইজুন্নেসা ডিগ্রি কলেজে। ১৮৯৩ সালে তিনি গরিব অসহায় মেয়েদের জন্য কুমিল্লায় একটি হাসপাতাল স্থাপন করেন। যা পরে খ্যাত হয় ফইজুন্নেসা হাসপাতাল হিসেবে। এছাড়া তিনি পথঘাট নির্মাণ, পানীয় জলের জন্য দিঘি (তালাব) খননে প্রচুর অর্থ ব্যয় করেন। তাঁর এই জনহিতকর কাজের স্বীকৃতি হিসেবে মহারানি ভিক্টোরিয়া ১৮৮৯ সালে তাঁকে নবাব উপাধিতে ভূষিত করেন। মেয়েদের মধ্যে এই উপমহাদেশে তিনিই প্রথম এই সম্মাননা লাভ করেছিলেন।
ফইজুন্নেসা অনেক মসজিদ এবং সেই সঙ্গে মাদ্রাসা স্থাপন করেন। তিনি ১৮৯৪ সালে মক্কায় হজ করতে যান। সেখানেও তিনি একটি মসজিদ ও সেই সঙ্গে মাদ্রাসা স্থাপনের জন্য প্রচুর অর্থ প্রদান করেন। তিনি তাঁর মৃত্যুকালে তাঁর সম্পত্তির অধিকাংশটাই ওয়াকফ করে যান। যা থেকে এখনও গরিব ছাত্ররা বৃত্তি পেতে পারছে। নবাব ফইজুন্নেসা চৌধুরাণী উত্তরাধিকার সূত্রে তাঁর পিতার এবং মাতার কাছ থেকে বিরাট সম্পত্তির উত্তাধিকারী হয়েছিলেন। এর অধিকাংশটাই তিনি দান করে গেছেন জনহিতকর কর্মে। ধনদৌলতের প্রতি তাঁর আকর্ষণ ব্যক্তিগত ছিল না যেমন থেকে থাকে অনেক জমিদারের। তিনি তাঁর জীবদ্দশায় হয়ে ওঠেন কিংবদন্তী নায়িকা।
এ সময় কুমিল্লা শহর ও লাকসাম ছিল দুর্গম অঞ্চল। ১৯০৪ সালের ১৬ ফেব্রুয়ারি আসামের বাংলা রেলপথে ট্রেন চলাচল শুরু হয়। আসাম বাংলা রেল কোম্পানি আসামের লামডিং থেকে চট্টগ্রাম পর্যন্ত রেলপথ খোলে। আসাম থেকে রেলপথে চা চালান যেতে শুরু করে বিলাতে। লাকসাম হয়ে ওঠে খুব বড় রেলওয়ে জংশন শহর। নবাব ফইজুন্নেসা চৌধুরাণীর সময় এই অঞ্চলে কোনো রেলপথ ছিল না। যাতায়াত ব্যবস্থা ছিল খুবই কষ্টকর। কিন্তু সেই অবস্থাতেও নবাব ফইজুন্নেসা অক্লান্ত চেষ্টা করেছেন শিক্ষা বিস্তারের জন্য। অর্থ ব্যয় করেছেন জনকল্যাণে। তিনি সত্যিকার অর্থেই ছিলেন একজন মহিয়সী নারী। যার মধ্যে মানবকল্যাণের অনুপ্রেরণা সৃষ্টি হতে পেরেছিল ভেতর থেকেই; বাইরের কোনো প্রভাবে নয়।
কোনো একজন লেখক তাঁর সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেছেন যে, তিনি উর্দুতে সাহিত্য চর্চা না করে বাংলাতে করেছেন। নবাব ফইজুন্নেসা চৌধুরাণী উর্দু জানতেন বলে আমাদের জানা নেই। তাই উর্দুতে সাহিত্য করার প্রশ্ন ছিল না। বাংলাদেশের বাংলাভাষী মুসলমান নারী ও পুরুষ চিরকাল বাংলা ভাষাতেই সাহিত্য চর্চা করেছেন, উর্দু ভাষায় করেননি। লক্ষ্য করবার বিষয় যে, পূর্ব বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে ছিল বিভিন্ন আঞ্চলিক বাংলা ভাষা। কিন্তু লিখিত ভাষা ছিল সাধু বাংলা। সাধু বাংলাতেই চলেছে লিখিত সাহিত্য চর্চা, এককালের বাংলা ভাষাভাষী অঞ্চলের সর্বত্র। বাংলা গদ্যের ইতিহাস নিয়ে এখনও চলেছে অনেক বিতর্ক। পর্তুগিজ খ্রিস্টান মিশনারিরা পূর্ব বাংলায় খ্রিস্টধর্ম প্রচার করবার জন্য বাংলাগদ্যে বই লিখেছেন। কিন্তু তারা এই লিখবার কাজে ব্যবহার করেছেন রোমান বর্ণমালা, পর্তুগিজ উচ্চারণে। তাদের এই বাংলা যথেষ্ট প্রাঞ্জল। তারা এই বাংলা শিখেছিলেন পূর্ব বাংলা থেকেই। তাই মনে করবার কারণ আছে যে, সপ্তদশ শতকের শেষে ও অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে এবং সম্ভবত এর আগেই একটি প্রাঞ্জল সাধু বাংলা গদ্যের উদ্ভব ঘটেছিল। যা ছিল সাহিত্যের উপযোগী। পর্তুগীজ মিশনারিরা প্রথম বাংলা গদ্যের ব্যাকরণ রচনা করেন এবং সংকলন করেন বাংলা পর্তুগিজ এবং পর্তুগিজ বাংলা অভিধান। কলকাতার ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে প্রথম বাংলা গদ্যের চর্চা শুরু হয়েছিল এই মতকে এখন আর যথেষ্ট আদ্রিত বলে ধরা যায় না। সম্ভবত নবাব ফইজুন্নেসা চৌধুরাণী যে গদ্য লিখেছেন সেটার উৎস ছিল পূর্ব বাংলায় প্রচলিত সাধু বাংলা গদ্যেরই ঐতিহ্যবহ।