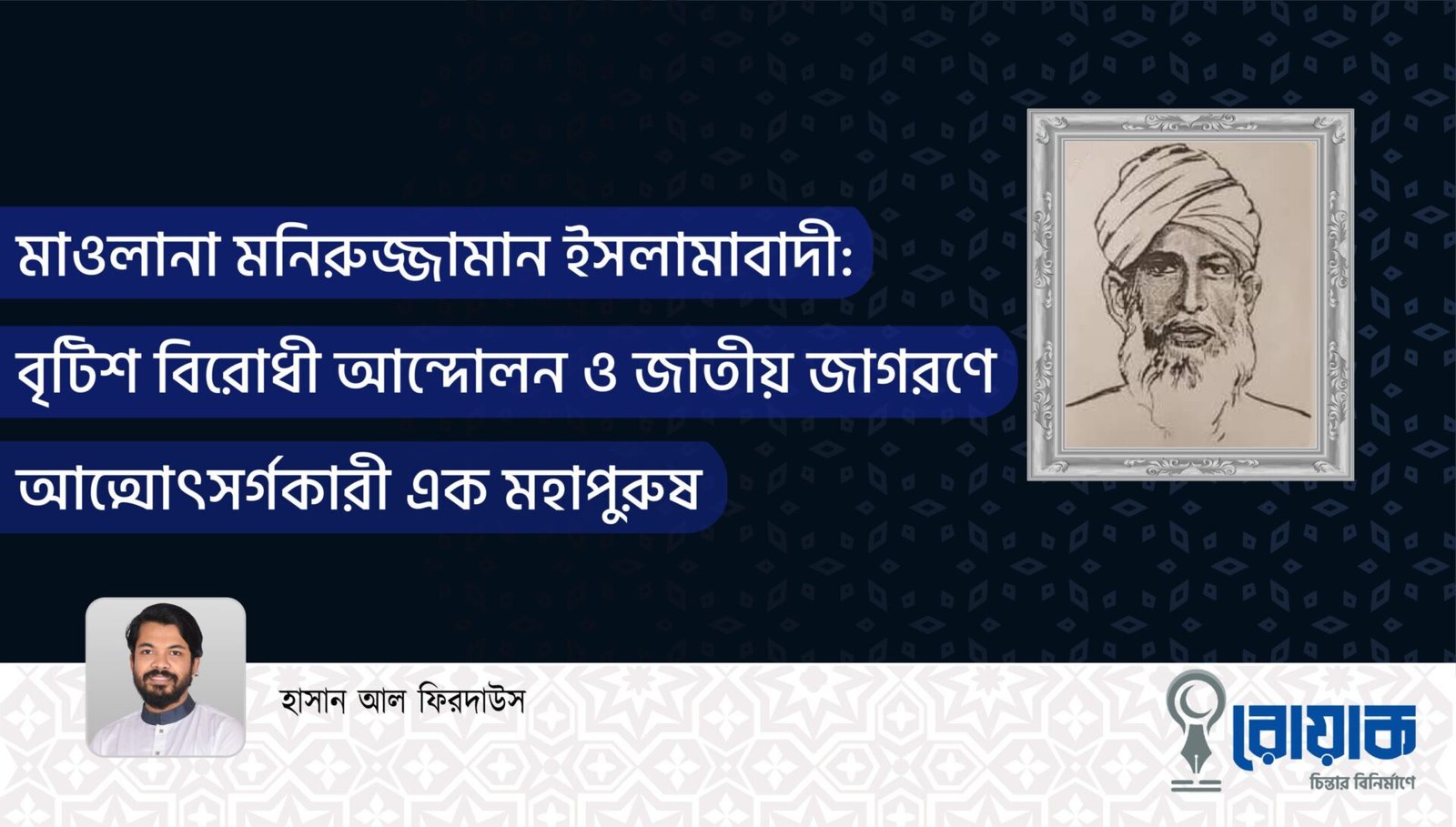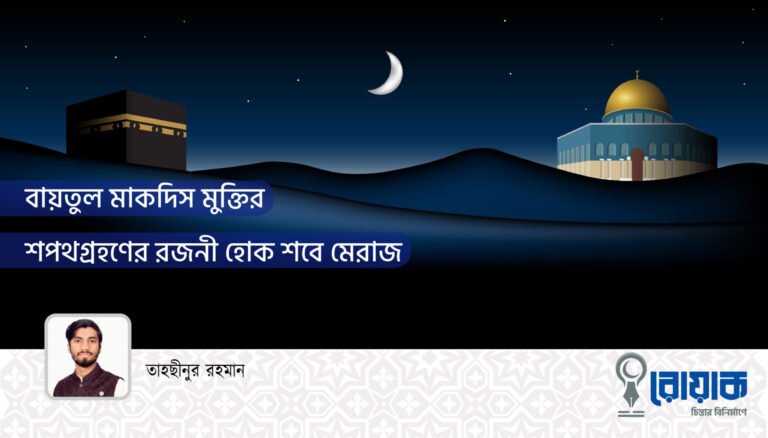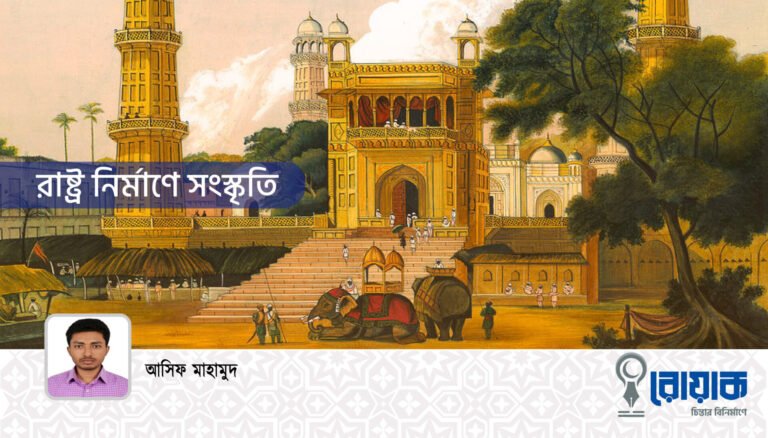ব্রিটিশ শোষণ পরবর্তী সময়ে বাংলা অঞ্চলের প্রতিটি আনাচে কানাচে পরিভ্রমণ করে জাতিকে জাগানোর প্রায় অসম্ভব সাধনায় যারা লিপ্ত হয়েছিলেন- প্রখ্যাত আলেম, রাজনৈতিক, সাহিত্যিক ও বাঙালি মুসলমানদের সাংবাদিকতার অগ্রপথিক মাওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী তাঁদের মধ্যে সর্বাগ্রগণ্য মহাপুরুষ। সাহিত্য, সাংবাদিকতা, শিক্ষকতা, সমাজসংস্কার, ধর্মপ্রচার, রাজনীতি, আইনসভা—সকল দিকেই তিনি তাঁর দূরদর্শী মেধা ও তীক্ষ্মধী চিন্তার প্রমাণ রেখেছেন। সাহিত্যের আসর থেকে রাজনীতির ময়দান; বিচিত্র পথে বিপুল সৃজনপ্রসূ হয়েছিল তাঁর যুগন্ধর প্রতিভা।
মাওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী ১৮৭৫ খ্রিস্টাব্দে চট্টগ্রামের অবিভক্ত পটিয়া থানার আড়ালিয়া (বর্তমান বাইনজুরি) গ্রামে এক ঐতিহ্যবাহী সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর জন্মতারিখ জানা যায়নি। তাঁর পিতার নাম মুন্সি মতিউল্লাহ পণ্ডিত। পিতার প্রচেষ্টায় মনিরুজ্জামান একজন গৃহশিক্ষক মৌলভির তত্ত্বাবধানে স্বগৃহে আরবি শিক্ষা সমাপ্ত করেন। অতঃপর তাঁর পিতা তাঁকে হুগলি পাঠিয়ে দেন। তিনি সেখানে হুগলি মাদ্রাসায় ভর্তি হন এবং ১৮৯৫ খ্রিস্টাব্দে হুগলি মাদ্রাসার সর্বশেষ পরীক্ষায় সর্বোচ্চ স্থান প্রথম শ্রেণিতে প্রথম বিভাগ অধিকার করে জামায়াত-উলা পাস করেন। এসময়ে তাঁর উপর মাওলানা কেরামত আলী জৈনপুরী, স্যার সৈয়দ আহমেদ খান, নওয়াব আব্দুল লতিফ ও জামাল উদ্দীন আফগানী প্রমুখ বিশ্ব মুসলিম মনিষীদের চিন্তা-চেতনা ও কর্মোদ্যেগের ব্যাপক প্রভাব পড়ে। মাওলানা জৈনপুরীর আদর্শে ইসলাম প্রচার, নওয়াব আব্দুল লতিফের আদর্শে শিক্ষা বিস্তার ও জামাল উদ্দিন আফগানীর আদর্শে ইসলামী ভ্রাতৃত্ববোধে অনুপ্রাণিত হন এবং তার আলোকে কর্মতৎপরতা শুরু করেন।
পরবর্তীতে পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখে মনিরুজ্জামানের সাহিত্যিক জীবনের সূত্রপাত হয়। প্রচারক, ইসলাম-প্রচারক, নবনূর, আল-এছলাম প্রভৃতি পত্রিকায় তাঁর ধর্ম, সমাজ, শিক্ষা ও ইতিহাসবিষয়ক প্রবন্ধ মুদ্রিত হয়। তাঁর গদ্যভঙ্গি প্রাঞ্জল অথচ বলিষ্ঠ ছিল। মাওলানা ইসলামাবাদী বেশ কিছু গ্রন্থ রচনা করেন। তিনি বড় ছোট মিলিয়ে ৪২টি গ্রন্থ রচনা করেছেন। উল্লেখযোগ্য হলো, কোরআনে স্বাধীনতার বাণী, ভারতের মুসলমান সভ্যতা, ভারতে ইসলাম প্রচার, সমাজ সংস্কার, মহামান্য উসমানী সুলতানের জীবনী, খাজা নেজামুদ্দীন আউলিয়া, মুসলমানদের সুদ সমস্যা ও অর্থনীতির মৌলিক সমাধান, ভূগোল শাস্ত্রে মুসলমান, কুরআন ও বিজ্ঞান, আরোঙ্গজেব, মোসলেম বীরাঙ্গনা, ইসলামের শিক্ষা, হযরতের জীবনী, ইসলাম ও রাজনীতি, তাপস-কাহিনী, শিল্প ও মুসলমান, সমাজ সংস্কার, রাজনীতির ক্ষেত্রে আলেম সমাজের দান, শুভ সমাচার, স্পেনের ইতিহাস, বঙ্গীয় মুসলমান সমাজের জাতীয় উন্নতির উপায় ইত্যাদি। এছাড়াও লিখেছেন বহু ইংরেজি, উর্দু ও বাংলা প্রবন্ধ।
এরপর মাওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদীর সাংবাদিকতার সূচনা হয় সাপ্তাহিক ‘ছোলতান’-এর মাধ্যমে। সাপ্তাহিক ‘ছোলতান’ পরে ‘দৈনিক ছোলতান’-এ উন্নীত হয়। তিনি ছিলেন এ পত্রিকার সম্পাদক। পরে আঞ্জুমানে ওলামায়ে ইসলাম বাংলা ও আসামের মুখপাত্র ‘আল-ইসলামে’র সম্পাদক হন। এই পত্রিকাগুলোর মাধ্যমে তিনি অবিভক্ত বাংলার মুসলমানদের মাঝে আত্মজাগরণের প্রেরণা ছড়িয়ে দেন। তিনি শিক্ষা-সংস্কৃতিতে পিছিয়ে পড়া মুসলমানদের অগ্রসর করতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। বাঙালী মুসলমানের জাতিগত ইতিহাসে তিনিই প্রথম বাংলায় প্রকাশিত পত্রিকার প্রথম মুসলমান সম্পাদক।
পাশাপাশি তৎকালীন দুনিয়াজোড়া খ্যাতির শীর্ষে ছিল ফারসী ভাষায় প্রকাশিত দৈনিক সংবাদপত্র ‘হাবলুল মতিন’। আল্লামা জামালুদ্দিন আফগানীর শিষ্য ও মজলুম নেতা আগা মঈদুল ইসলামের সম্পাদনায় কলকাতায় ইংরেজীতে ‘মিল্লাত’ ও উর্দু-ফারসীতে, দৈনিক ‘হাবলুল মতিন’ প্রকাশিত হতো। আর ‘হাবলুল মতিনে’র বাংলা সংস্করণের সম্পাদক ছিলেন- মাওলানা ইসলামাবাদী। এর জন্য মাওলানা ইসলামাবাদীকে বলা হয় বাংলায় প্রকাশিত প্রথম দৈনিক পত্রিকার প্রথম মুসলমান সম্পাদক।
সংবাদপত্রের এ জগত ও মুসলিম সাংবাদিকতায় মাওলানা ইসলামাবাদীর অবদানও তাই অপরিসীম। তাই এতিহাসিকগণ বলেন, সাহিত্য, সাংবাদিকতা, শিক্ষকতা, সমাজসংস্কার, ধর্মপ্রচার, রাজনীতি, আইনসভা—যখন যেদিকে তিনি তাঁর প্রতিভা কর্ষণ করেছেন, মুঠো মুঠো ফসলে তাঁর গোলা ভরে উঠেছে। এমনই বিচিত্র পথে বিপুল সৃজনপ্রসূ হয়েছিল তাঁর যুগন্ধর প্রতিভা।
মাওলানা ইসলামাবাদী অবিভক্ত বাংলায় মুসলিম শিক্ষা কনফারেন্স, বঙ্গীয় মুসলিম সাহিত্য সমিতি, প্রাদেশিক মোছলেম শিক্ষা সমিতিসহ বহু কর্ম উদ্যোগের পুরোধা ব্যক্তিত্ব। তাই নানাভাবে তিনি মুক্তি সংগ্রাম করেছেন এবং জাতিকে জাগিয়ে তুলার চেষ্টা করেছেন।
কিন্তু মুসলমানদের সামগ্রিক অবস্থা দেখে তিনি অনুধাবন করেন, বিভিন্ন মতাবলম্বী আলেম সমাজকে একত্রিত না করলে এ প্রয়াস সফল হবেনা। অতঃপর তিনি ফুরফুরার পীর সাহেব মাওলানা আবু বকর ছিদ্দিকী, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের মাওলানা রুহুল আমিন, দৈনিক আজাদের মাওলানা মোহাম্মদ আকরাম খাঁ ও আহলে হাদিসের মাওলানা আবদুল্লাহিল বাকীর সমন্বয়ে গড়ে তোলেন ‘আঞ্জুমানে ওলামায়ে বাংলা’।
১৯৩৯ সালে কলকাতা মুসলিম ইনস্টিটিউট হলে নিখিল বঙ্গ মৌলভী অ্যাসোসিয়েশনের দ্বিতীয় বার্ষিক সম্মেলনে ভাষণ দিতে গিয়ে স্পষ্টভাবে আলিমদের নেতৃত্বের দাবি সম্পর্কে বলেন,
‘‘আলেমশ্রেণী ব্যতীত অন্যশ্রেণীর লোকের নেতৃত্বাধীন ইসলামের তথা মুসলিম জাতির উন্নতির পথ প্রশস্ত হওয়ার উপায় আছে বলে বিশ্বাস করিনা। যে নেতা স্বয়ং শরিয়তের বিধি-বিধানের অধীন থাকবেন না, কুরআন-হাদিস মতে বলবেন না, তার পক্ষে মুসলমানের নেতৃত্ব দেয়ার অধিকার থাকতে পারে না। যদি আমরা মুসলমানদের আত্মপ্রতিষ্ঠা ও আত্মনির্ভরশীল করে তুলতে না পারি বা আলেমদের মধ্যে কোমরে বা বুকে হাত বাঁধা, ‘আমিন’ ছোট করে না উচ্চৈঃস্বরে পড়বে; এই সমস্ত মাসয়ালা নিয়ে তর্ক করতে থাকি, তা হলে ইসলামের ভিত্তি দুর্বল হয়ে যাবে এবং আত্মবিস্মৃত মুসলিম জাতির অস্তিত্ব হুমকির সম্মুখীন হয়ে পড়বে।”
মাওলানা ইসলামাবাদীর গভীর আস্থা ছিলো আলেম সমাজের উপর। এটি তিনি বিশ্বাস করতেন, মুসলিম সমাজের প্রতিদিনকার জীবনাচরণ অর্থাৎ জন্ম-মৃত্যু, বিবাহ ও প্রতিদিনকার অবশ্যপালনীয় ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান যার পরিচালক স্বভাবতই আলেম সমাজ, ধর্মীয় নেতা হিসেবে জনসাধারণের উপর যাদের প্রভাব অপরিসীম। এ আলেম সমাজকে যদি সংঘবদ্ধ করে দেশ সমাজের আশু সমস্যা সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল করে তোলা যায়, তাহলে এদের দিয়ে অসাধ্য সাধন করা যাবে। মুসলমান সমাজ যে বিপর্যয়ের সম্মুখীন আর যেসব অন্তহীন বাধা-বিপত্তি সমাজকে পঙ্গু আর নির্জীব করে রেখেছে ইচ্ছা করলে এরাই তার বন্ধন থেকে সমাজকে মুক্তি দিতে পারে।
আঞ্জুমানে ওলামায়ে বাঙালাহ’ এই পরিকল্পনারই বাস্তব রূপ। সংগঠনটির মুখপত্র আল এসলাম-মাওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী সম্পাদিত প্রথম স্বাধীন পত্রিকা, যা ১৯১৫ সালে কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়।
আলেমদের নিয়ে এসব উদ্যোগ গ্রহণের পর ১৮৯৮ খ্রীস্টাব্দে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে যোগদান করেন।
কেননা মুসলমানদের হাত থেকে ভারতীয় উপমহাদেশের ক্ষমতা জায়নবাদী বৃটিশদের হাতে চলে যাওয়ার পর মুসলমানেরা জায়নবাদী বৃটিশদের চরম দমন ও নির্যাতনের শিকার হয়েছিলো। শিক্ষা-দীক্ষা, জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রভৃতি ক্ষেত্রে মুসলমানদের অভ্যুত্থান স্থবির হয়ে পড়ে। সে সময় মুসলিম সমাজ এক দূর্বিসহ অবস্থায় নিপতিত হয়। জাতির সেই দূর্দিনে মাওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী এগিয়ে আসেন। এজন্য তাঁকে মুসলিম জাতিসত্তার অন্যতম নেতা আখ্যায়িত করা হয়।
নেতা হিসেবেই নয়, শিক্ষা সংগঠন সহ নানাভাবেই তিনি মুসলিম জাতিকে সচেতন করতে থাকেন। এই জাগরনের প্রেরনায় উদ্বুদ্ধ মাওলানার কর্মজীবন ছিলো ঘটনাবহুল ও বৈচিত্রময়। তাই তিনি একাধারে রাজনীতিক, ইসলাম প্রচারক, লেখক, সাংবাদিক ও সমাজ সংস্কারক ছিলেন।
শামসুজ্জমান খান তাঁর রচিত মাওলানা মনিরুজ্জামান এছলামাবাদী গ্রন্থে- তাঁর শিক্ষা, সংগঠন, সাংবাদিকতা ও সংগ্রামের কথা তুলে ধরেছেন। নানা সংগঠনের মধ্যে দিয়ে সাধারণ মানুষের ক্ষুদ্র ও বিক্ষিপ্ত শক্তিকে সঞ্চিত করে মাওলানা তাঁকে সামাজিক অগ্রগতির হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করতে চেয়েছেন। এ লক্ষ্যে তিনি ব্রতী হয়েছিলেন শিক্ষা বিস্তারে, প্রতিষ্ঠা করার উদ্যোগ আয়োজন করেছিলেন একটি জাতীয় আরবি বিশ্ববিদ্যালয়, মোছলেম শিক্ষা সম্মেলন, আঞ্জুমানে ওলামায়ে বাঙ্গালী প্রভৃতি। তাঁর আরবি বিশ্ববিদ্যালয়ের লক্ষ্য ছিল ধর্ম শিক্ষার ছাত্রদের মধ্যে বৈজ্ঞানিক চিন্তা ও যুক্তিবাদের প্রসারের সাথে সাথে তাদের পরিশ্রমী, সংযমী ও স্বাধীনতাকামী করে গড়ে তোলা এবং এভাবে সমাজ ও দেশের বৃহত্তর কর্তব্যের দ্বারে, তাদের পৌছে দেয়া। অন্যদিকে তিনি তাঁর ক্ষুদ্র কিন্তু অসামান্য পুস্তিকা “নিম্নশিক্ষা ও শিক্ষাকর” (১৯৪০) এ বলেছেন-
“পৃথিবীর যত সভ্য দেশ আছে প্রায় সর্বত্রই প্রাথমিক শিক্ষা অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক। জাপান, আমেরিকা ও ইউরোপের জার্মানী ইত্যাদি স্থানে নিম্নশিক্ষা বাধ্যতামূলক; সেখানে শতকরা ১০০জন লোক লিখিতে পড়িতে জানে। ইউরোপের অন্যান্য ক্ষুদ্র, বৃহৎ রাজ্যের শতকরা ৫ জনের অধিক নিরক্ষর লোক নাই। রুশ সাম্রাজ্যেও বর্তমানে শতকরা ৯০ জন পর্যন্ত লোক নূন্যাধিক লেখা পড়া শিখিয়াছে। হতভাগ্য ভারতের অবস্থা স্বতন্ত্র। পরলোকগত দেশপ্রেমিক মি. মেখলে নিম্নশিক্ষা বাধ্যতামূলক করিবার জন্য কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভায় ও মোম্বাই প্রদেশে আজীবন চেষ্টা করিয়াও সফলতা লাভ করিয়া যাইতে পারেন নাই। বাংলায় একদল জাতীয়তাবাদী ও কৃষকপ্রজা বৎসল লোক বহুদিন হইতে নিম্ন শিক্ষা অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক করিবার জন্য আন্দোলন চালাইয়া আসিতেছেন।”
মাওলানার এই আন্দোলন ছিল মৌলিক ও নিম্নতর স্তর থেকে সামাজিক-সাংস্কৃতিক জাগরণের ভিত্তিস্বরূপ। প্রকৃতপক্ষে সংগঠন, শিক্ষা ও সংবাদপত্র একটি সমাজকে গড়ে তোলে। তাঁর জীবন এই লক্ষ্যে স্থিত হয়েই সফলতা পেয়েছিল। মনিরুজ্জামানের কর্ম জীবনের সূচনা কবেই এ ধরণের চিন্তাধারা তাঁর মধ্যে গড়ে উঠতে থাকে। তিনি লিখেছেন,
“১৮৯৮ খ্রিষ্টাব্দে কলকাতায় নিখিল ভারতীয় মোছলেম শিক্ষা সমিতিতে যোগদানের সুযোগ পাইয়াছিলাম। তখন হইতে আমার অন্তর বাঙলাদেশের শিক্ষা বিস্তার ও ইসলাম প্রচারের উপায় সম্বন্ধে নানা বিষয়ও চিন্তাধারা উদ্ধেলিত হইতেছিল। আমার মনে হয়, ১৮৯৮ অব্দে কুমেদপুর হইতে কলিকাতার ইসলাম প্রচারক মাসিক পত্রিকার ইসলাম মিশন সম্বন্ধে একটি বিস্তৃত প্রবন্ধ লিখি। ১৯১৪ খ্রিষ্টাব্দে আঞ্জুমানে উলেমার তত্ত্বাবধানে যখন ‘আল এছলাম’ মাসিক পত্র প্রকাশিত হয় সেই পত্রের দ্বিতীয় বা তৃতীয় বর্ষে আমার ইসলাম প্রচারকে প্রকাশিত প্রবন্ধাবলী পুনমুদ্রিত হইয়া ছিল।”
‘‘প্রত্যেক জেলায় বঙ্গীয় সাহিত্য সমিতির শাখা গঠন, তাতে পুস্তকালয় ও পাঠাগার স্থাপন আবশ্যক। জেলার ইতিহাস, প্রাচীন কীর্তির তত্ত্ব, ওলি ও সাহিত্যিক বর্গের জীবনী সংগ্রহ ফলপ্রদ হইবে। তাঁর দর্শন, মাতৃভাষা চর্চায় অনাগ্রহ মুসলিম সমাজের অনগ্রসরতার মূল কারণ। আপনারা জানেন, মাদ্রাসার কোন উচ্চ লক্ষ্য নাই, তাই সকল মাদ্রাসার ছাত্রদেরকে রাজনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতি, ভূগোল, ইতিহাস, আধুনিক দর্শন, বিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়া আবশ্যক। মাতৃভাষা বাংলার চর্চা করা আবশ্যক। অন্ততঃ একদল ছাত্রকে রাজভাষা ইংরেজি শিক্ষা দিবার বিশেষ প্রয়োজন আছে।’’
প্রায় শতবর্ষ পূর্বে এভাবেই তিনি সাহিত্য, মাদ্রাসা শিক্ষা ও জাতীয় জাগরণে দূরদর্শীতাঁর স্বাক্ষর রেখে গেছেন।
জায়নবাদী বৃটিশদের থেকে মুক্তি লাভের জন্য নারী সমাজ যাতে সম্মান ও মর্যাদার সাথে নিজ পায়ে দাঁড়াতে পারে, মুক্তি সংগ্রামকে এগিয়ে নিতে পারে সেজন্য নারী শিক্ষার প্রসারে ব্যাপক গুরত্বারোপ করেছেন মাওলানা ইসলামাবাদী। উৎপদানশীল কর্মকান্ডে নতুন প্রজন্মকে নিয়োজিত করতে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা কার্যক্রমকে প্রাধান্য দিয়েছেন। তাদের শিক্ষার সম্প্রসারণে তিনি কদম মোবারক এম. ওয়াই উচ্চ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি বাংলার মুসলমান মেয়েদের শিক্ষা ও কল্যাণের পথে আহ্বান জানিয়ে ‘আল এসলাম পত্রিকায় লিখেছিলেন,
‘যখন পুত্র কন্যার মা হইবে, তখন সর্বদা তাহাদিগকে শুধু অলংকার পরাইবার চেষ্টায় লাগিয়ে থাকিও না। যে অলংকার স্থায়ী নহে, তাহাদের শিক্ষার ব্যবস্থা করিও, সভ্যতা শিক্ষা দিও।’
কর্মবীর ও দেশপ্রেমিক এই নেতা মুক্তি সংগ্রামকে এগিয়ে নিতে, সমাজকে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন একেবারে নীচের ধাপ থেকে, যেখানে রয়েছে দেশের ও অর্থনীতির মূল শেকড়। তাই ইসলামাবাদীর একদিকে যেমন কাম্য ছিলো কৃষক শ্রমিকের উন্নতি, তেমনি যেসব অত্যাবশ্যকীয় পেশার প্রতি মুসলিম সমাজের অনীহা ছিলো, তিনি চেয়েছিলেন তার প্রতিও মুসলিম সমাজকে আগ্রহী করে তুলতে। তিনি প্রায় বলতেন, “মুসলমানরা বড় দায়িত্বের পাশাপাশি যদি কর্মকার, শিল্পী, গোয়ালা, নানা হালাল ব্যবসায় অবলম্বন করে তাহাও দেশেরই সেবা। ইহাতে হিন্দুদের অসন্তোষের কোন কারণ নাই।” এভাবে তিনি অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও বহু প্রস্তাবণা দিয়েছেন।
যেহেতু ইসলামাবাদীর মূল লক্ষ্য ছিলো- ব্রিটিশ শাসনে পশ্চাদপদ মুসলমানদের জাতীয় চেতনা সঞ্চার ও নবজাগরণ, এবং সমাজ ও দেশ সেবার মাধ্যমে স্বাধীনতার বাণী প্রচার ও মুক্তি সংগ্রামে সকলের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ। তাই দরিদ্র ও অবহেলিতদের সদা অভিভাবক বা মুখপাত্রও হয়ে উঠেন ইসলামাবাদী।
এভাবেই তিনি রাজনীতির অঙ্গনে অতিরিক্ত দলীয়করণ ও বিদ্বেষমূলক রাজনীতির বিরোধী প্রতীকে পরিণত হন। মানবতাবাদী, জাতীয় ঐক্য, সামপ্রদায়িক সম্প্রতি ও আর্থ সামাজিক উন্নয়ন সহ স্বাধীনতা সংগ্রামের অতন্দ্র প্রহরী হয়ে উঠেন। তিনি ‘‘আল-এসলাম’’ পত্রিকার ১৩২৫-২৬ সংখ্যায় সুস্পষ্ট বর্ণনা করেছেন, ‘‘মাতৃভাষার সাহায্যে দেশের বিভিন্ন সমপ্রদায়ের মধ্যে একতা, সম্প্রীতি ও ভ্রাতৃভাব বর্ধনের চেষ্টা করাই দেশবাসীর নেতা ও সাহিত্য সেবক গণের প্রধান কর্তব্য’’।
স্বাধীনতা ও মুক্তি সংগ্রামের গুরুত্বের পাশাপাশি নিজেদের প্রস্তুতির দিকেও সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেন। তিনি ১৯৩০ সালের যুব সম্মেলনে বলেন,
‘‘মন ও শরীর নিয়ে এই দুই বস্তু লইয়াই মানুষ, শরীরকে সবল ও স্বাস্থ্যবান রাখার জন্য শরীর চর্চা ও ব্যায়াম কৌশলই প্রধান অবলম্বন, যুবকগণের প্রধান কর্তব্য শারীরিক উন্নতির জন্য স্থানে স্থানে আখরা স্থাপন, তাহাতে কুস্তি কছরতের সুব্যবস্থা, লাঠি খেলা, তরবারি ভাজা, ছোরা চালনা ইত্যাদির ব্যবস্থা লাগবে। ধন রক্ষা, ধর্ম রক্ষা, দেশ রক্ষা সমস্তই শারীরিক স্বাস্থ্য ও শক্তির প্রতি নির্ভর করে। আত্মরক্ষা, এছলাম রক্ষা, মোছলেম জাতির স্বার্থ সংরক্ষণকল্পে ব্যায়াম চর্চার জন্য এছলাম ধর্মে কঠোর বিধান আছে। তাই তোমরা মুক্তি সংগ্রামের জন্য নানাভাবেই প্রস্তুত হও।“
এরপরই মাওলানা ইসলামাবাদী বৃটিশ বিরোধী আন্দোলনে প্রত্যক্ষভাবে নেতৃত্ব দিতে শুরু করেন।
আমরা জানি যে, ১৯২০ সাল পরবর্তী সময় ভারতীয় উপমহাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ সময়, এসময়েই অসহযোগ ও খেলাফত আন্দোলনের ডামাডোল উচ্চভাবে বেজে ওঠে। কাজেম আলী মাস্টার, মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী ছিলেন সে আন্দোলনে জে এম সেনগুপ্তের উপদেষ্টা। মহিমচন্দ্র দাশ ও ত্রিপুরা চরণ চৌধুরী ছিলেন প্রধান সহযোগী। ১৯২০ খ্রিষ্টাব্দের ৮ নভেম্বর মুসলিম হাইস্কুলের ছাত্ররা ধর্মঘট করে। জে এম সেন হলে ধর্মঘটি ছাত্র ও জনসাধারণের বিরাট জনসভায় সভাপতিত্ব করেন মাওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী।
তিনি ছিলেন জমিয়তে উলামায়ে হিন্দ-এর বঙ্গীয় শাখার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। ১৯০৩ সালে অবিভক্ত বাংলায় মুসলিম কনফারেন্সের আয়োজন করেন।
মাওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী নিখিল বঙ্গ জমিয়তে ওলামায়ে হিন্দের সভাপতিও ছিলেন।
১৯০৬ সালে ‘মুসলিম সাহিত্য সমিতি’ প্রতিষ্ঠায়ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। মাওলানা প্রথম দিকে কংগ্রেসের সাথে সম্পৃক্ত থাকলেও ১৯২১ সালে খেলাফত আন্দোলনে যোগ দেন। ইসলামাবাদী ১৯২৩ সালের বেঙ্গল প্যাক্টের অন্যতম স্থপতি। ১৯২৯ সালে মাদরাসা ছাত্রদের দাবি আদায়ের লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত আসাম-বেঙ্গল জমিয়তে তালাবায়ে আরাবিয়ার প্রতিষ্ঠাকালীন প্রধান সম্পাদক ছিলেন তিনি। ১৯৩৭ সালে কৃষক-প্রজা পার্টির মনোনয়নে বঙ্গীয় আইন সভার সদস্য নির্বাচিত হন।
খেলাফতের পতনের কারণেই মুসলিম সমাজ আজ হতাশাগ্রস্ত ও নেতৃত্বহারা এবং খেলাফত ব্যবস্থা পুনঃপ্রবর্তনের মাধ্যমে মুসলিম উম্মাহ শান্তি, সমৃদ্ধি ও হারানো ঐতিহ্য ফিরে পেতে পারে। এমন একটি দর্শন তিনি আজীবন লালন করে গেছেন।
১৯২০ সালে কলকাতায় আহূত ভারতীয় কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশন যোগদান করেন ইসলামাবাদী। ১৯৩০ খ্রিষ্টাব্দে তিনি আইন অমান্য আন্দোলনে যোগদান করে কারাবরণ করেন। এরপর ইসলামাবাদী সংসদীয় রাজনীতিতে আকৃষ্ট হন। প্রথমে তিনি জেলা বোর্ডের সদস্য, ১৯৩৭-এর নির্বাচনে চট্টগ্রাম দক্ষিণ (মধ্য) নির্বাচনী এলাকা থেকে বঙ্গীয় আইন পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার অসারতা প্রতিপন্ন করে আনন্দবাজার পত্রিকায় ধারাবাহিক প্রবন্ধ রচনা (১৯৪২-১৯৪৩) করেন। ত্রিশের দশকে তিনি বঙ্গীয় কৃষক-প্রজা দলে যোগদান করেন ও কৃষক প্রজা পার্টির সহসভাপতির পদ অলংকৃত করেন।
মাতৃভূমির স্বাধীনতা অর্জন ছিল তাঁর জীবনের মূল লক্ষ্য। ইসলামাবাদীর রাজনৈতিক জীবনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ‘ভারত ছাড়’ আন্দোলনে যোগদান ও নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর আজাদ হিন্দ ফৌজের সমর্থনে এগিয়ে এসে। ১৯৪২-৪৩ সালে নেতাজির সঙ্গে আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ করে তিনি ইস্টার্ন জোনের (বর্তমান বাংলাদেশ ও আসাম) প্রধান সংগঠক ও সর্বাধিনায়ক নিযুক্ত হন। নেতাজির চট্টগ্রাম সফরকালে কর্ণফুলী নদীর মোহনায় দেয়াং পাহাড়ে মাওলানা ইসলামাবাদীর সঙ্গে তাঁর গোপন বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। ওই সময় ইসলামাবাদী সেখানে ইসলাম মিশন এতিমখানা শাখা, পশুপালন খামার, মত্স্য খামার, কৃষি খামার এবং জাতীয় আরবি বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনা কেন্দ্র স্থাপন করেছিলেন। তার আগে মাওলানা ইসলামাবাদী তাঁর পৈতৃক সম্পত্তি হস্তান্তর করে চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ড এলাকায় ব্রিটিশবিরোধী এবং ব্রিটিশ খেদাও আন্দোলনের গোপন দুর্গ হিসেবে বিপুল জায়গা-জমি নিয়ে এক খামারবাড়ি স্থাপন করেন। বিপ্লবী কর্মকাণ্ডে যুক্ত থাকার দায়ে ১৯৪৪-এর ১৩ অক্টোবর চট্টগ্রামে গ্রেপ্তার হন। এক বছর (১৯৪৪-৪৫) লাহোর সেন্ট্রাল জেলে আটক ছিলেন।
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালে ভারত ছাড় আন্দোলনে যোগদান, আজাদ হিন্দ ফৌজের সাথে সম্পর্ক, ঢাকা ও চট্টগ্রামে বিপ্লবী কেন্দ্র স্থাপন, নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসুর সাথে বার্মায় গিয়ে সাক্ষাৎ ও ব্রিটিশ বিরোধী বিপ্লবী তৎপরতার দায়ে ১৯৪৪ সালের ১৩ অক্টোবর ৭০ বছর বয়সী মওলানা গ্রেফতার হন চট্টগ্রাম থেকে। ব্রিটিশ সরকার তাঁকে মহাত্মা গান্ধী, পণ্ডিত জওহর লাল নেহেরু ও অন্যান্য নেতাদের সাথে দিল্লীর লালকিল্লায় বন্দি করে রাখেন। পরে তাকে স্থানান্তর করা হয় পাঞ্জাবের ময়াওয়ালী জেলে। সেখানকার জেলের ছাদের বিমের সাথে রশি বেঁধে তাঁর উপর অশেষ নির্যাতন চালানো হয়েছিলো গোপন তথ্য জানার জন্য। প্রায় ১১ মাস কারানির্যাতন ভোগ করে মুক্তির পর মওলানা মনিরুজ্জামান কলকাতায় পক্ষাঘাত রোগে আক্রান্ত হন।
কারা নির্যাতনের কারণে তার শরীর ভেঙে পড়ে। আত্মজীবনীতে তিনি লিখেছেন,
‘বৃদ্ধ বয়সে আমার ওপর যেভাবে অত্যাচার ও নির্যাতন ব্রিটিশ সরকার করেছে, পৃথিবীর কোনো সভ্য জাতির ইতিহাসে এরকম ঘটনা ঘটতে পারে না, কিন্তু তারা আমার দেশকে লুটে খাওয়ার জন্য আমাদের দেশে মানুষের ওপর নির্মম অত্যাচার করে চলেছেন, এই অত্যাচারের একদিন শেষ হবে, আমরা স্বাধীন হবো এবং আমাদের পরবর্তী প্রজন্ম সেই স্বাধীনতা ভোগ করবে- এটি আমার বিশ্বাস।’
১৯৫০ সালের ২৪ অক্টোবর জীবনের বহু স্বপ্নসাধ অসম্পূর্ণ রেখে এই অসামান্য কর্মবীর শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।
স্বাধীনতা ও মুক্তি সংগ্রামের পাশাপাশি প্রাজ্ঞ পন্ডিতদের কাছ থেকে সামাজিক, মানবিক দীক্ষার ফসলও ঘরে তুলে ছিলেন ইসলামাবাদী। তাই তাঁর সারাজীবনের সংগ্রামে, শিক্ষকতা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা, সমাজ উন্নয়ন, সংবাদপত্র সেবাই প্রাধান্য পেয়েছিল। তিনি মনে প্রাণে বিশ্বাস করতেন প্রকৃত শিক্ষা ব্যতীত অন্ধকারে ডুবে থাকা সমাজের মানুষকে আলোর পথযাত্রী করার কোনো উপায় নেই। ব্যক্তিগত আর্থিক দৈন্য গোছানো এবং শিক্ষকতা পেশায় দক্ষতা অর্জন ও বিষয় বস্তুর নানান দিক যৌক্তিকভাবে উপলব্ধি করার জন্য রংপুর, কোলকাতা, সীতাকুন্ডসহ নানান প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকতা করেন। বিংশ শতাব্দীর প্রথম ও দ্বিতীয় দশকে মুসলিম সাংবাদিকতার পথিকৃত হিসেবে তিনি তার চিন্তাধারা, অগাধ মনীষা ও বিপ্লবী চেতনা চারদিকে ছড়িয়ে দেন। অনলপ্রবাহের কবি ইসমাইল হোসেন সিরাজীর মতো আত্মসচেতন মনীষীর সাহচর্য ইসলামাবাদীকে সংগ্রামের পথে বজ্রকঠিন শপথে বলীয়ান করে তোলে। গ্রামে গ্রামে তিনি জনসেবা, আলোচনা ও পথসভা করে অধঃপতিত মুসলিম জাতিকে নবীন আলোর বন্দনা করতে শেখান।
সাহিত্য ও সাংবাদিকতাকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে নিজ জাতি ও মুসলিম উম্মাহর জন্য আমৃত্যু সংগ্রাম করে যাওয়া মাওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী তাই আমাদের অনুপ্রেরণার অন্যতম আলোকমশাল। নিজ জাতিসত্তা ও উম্মাহর প্রয়োজনে কিভাবে সাহিত্যের আসর ছেড়ে রাজনীতিতে নামতে হয়, কিংবা রাজনীতির লোভনীয় পদের অফার ফিরিয়ে দিয়ে পত্রিকার দায়িত্ব কাধে তুলে নিতে হয়, কিংবা সবকিছু ছেড়ে মসজিদ-মক্তব প্রতিষ্ঠায় আত্মনিয়োগ করতে হয়, আবার জাতির প্রয়োজনে সবগুলো কাজ নতুন উদ্যমে শুরু করতে হয় তাঁর প্রকৃষ্ট উদাহরণ মাওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী। মুক্তির প্রয়োজনে যেকোন কিছু করার অটল ও অবিচল মানসিকতা, জাতির জন্য আমৃত্যু কাজ করে যাওয়ার আত্মত্যাগী চেতনা ও বহুমুখী ক্ষেত্রে একত্রে সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার সাহসিকতার প্রোজ্জ্বল বাতিঘর ‘মাওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী’। মৃত্যুর পূর্বে মাওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী সমাধিলিপি লিখে গেছেন-
“পথিক : ক্ষণেকের তরে বস মোর শিরেফাতেহা পড়িয়া যাও নিজ নিজ ঘরেযে জন আসিবে মোর সমাধি পাশে।ফাতেহা পড়িয়া যাবে মম মুক্তির আশে।অধম মনিরুজ্জামান নাম আমার।এছলামাবাদী বলে সর্বত্র প্রচার।”