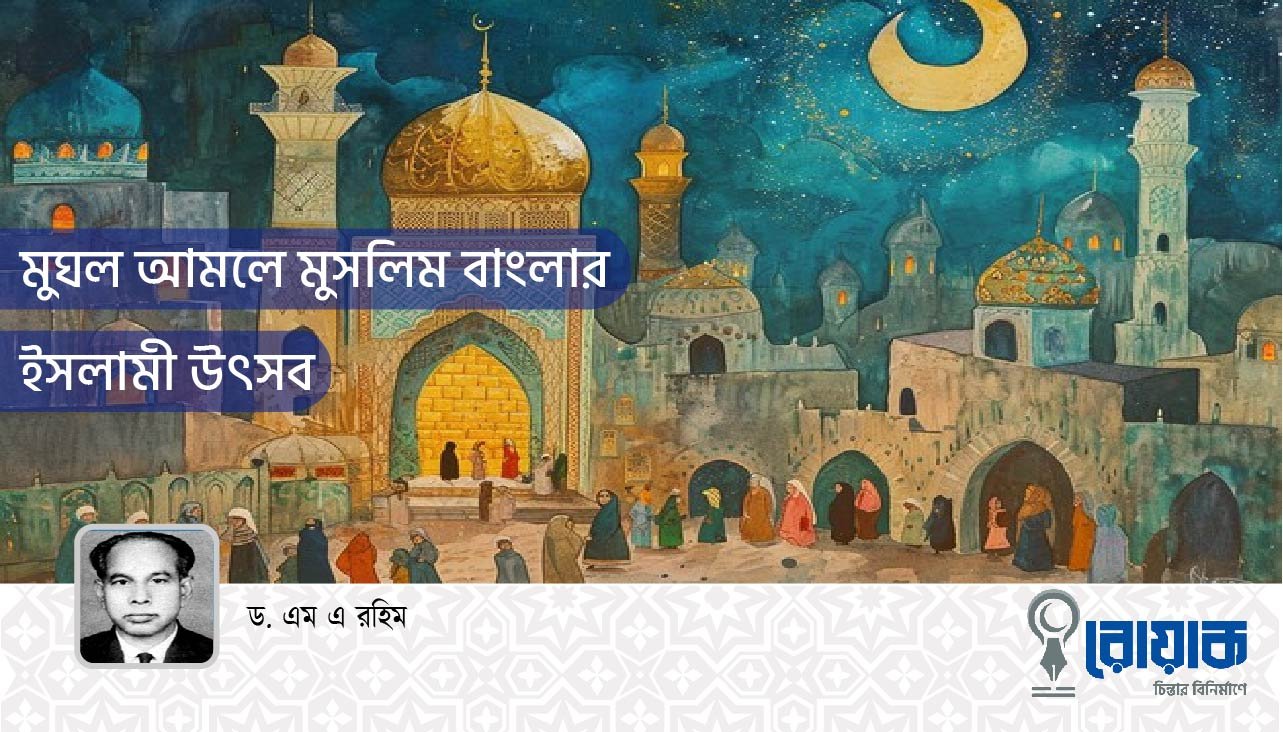মুসলিম শাসনামলে, বাংলার মুসলমানদের ধর্মানুরাগের খ্যাতি ছিল। তারা ঈদ ইত্যাদি ধর্মীয় উৎসবগুলোতে খুব আমোদ-স্ফূর্তি করত। আর্থিক প্রাচুর্য থাকার ফলে তারা তাদের সামাজিক অনুষ্ঠানসমূহ, যেমন বিবাহ ইত্যাদি খুব জাঁকজমকের সঙ্গে সম্পন্ন করত। এটা উল্লেখযোগ্য যে, মুসলমানদের ধর্মীয় উৎসবসমূহ সমগ্র মুসলমান শাসনামলে একই রকম ছিল। তাদের সামাজিক অনুষ্ঠানগুলোও শতাব্দীর পর শতাব্দীব্যাপী অপরিবর্তিত থাকে। মুসলমান সমাজে কিছু সংখ্যক নতুন ধর্মীয় ও সামাজিক উৎসবের আবির্ভাব হয়। মুহররম, বেড়া এবং সব-ই-বরাত ইত্যাদি উৎসবগুলোতে বাংলার হিন্দু উৎসবাদির চাকচিক্য এবং সমারোহের অনেকটা প্রভাব পড়েছিল।
রমজান
উপবাস, সংযম, প্রার্থনা ও সামাজিক সম্মেলনীর সময় হিসেবে সে যুগের মুসলমানগণ ‘রমজান’ পালন করত। তারা রমজানকে পবিত্র ও মঙ্গলজনক মাসরূপে গণ্য করত এবং খুশির সঙ্গে একে স্বাগত জানাত। বাংলায় মুঘল সৈন্যদের রমজান পর্ব পালনের উল্লেখ করে মীর্জা নাথন বলেন, “রমজান মাসের শুরু থেকে এর শেষদিন পর্যন্ত ছোটবড় প্রত্যেকে প্রত্যহ তার বন্ধুর তাঁবুতে মিলিত হতো। এটা একটা স্বাভাবিক রীতিতে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল যে প্রত্যেক দিন সকলে পর্যায়ক্রমে একজন অভিজাত বন্ধুর তাঁবুতে তাদের সময় কাটাত। সেই অনুসারে শেষের দিন রাত্রে মুবারিজ খানের দেওয়া ভোজের পালা ছিল। সকলে সেদিন তার তাঁবুতে সময় কাটায়।”
ঈদ
মীর্জা নাথনের বর্ণনা থেকে সেযুগের ঈদ-উৎসব সম্বন্ধে একটি ধারণা পাওয়া যায়। খুব আমোদ-স্ফূর্তির সঙ্গে ঈদের নতুন চাঁদকে স্বাগত জানানো হয়। মীর্জা নাথনের ভাষায় এটা বর্ণনা করা যেতে পারে; তিনি লিখেছেন, “দিনের শেষে সন্ধ্যা সমাগমে নতুন চাঁদ দেখা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রাজকীয় নাকারা বেজে উঠে এবং গোলন্দাজ সেনাদলের সকল আগ্নেয়াস্ত্র থেকে ক্রমাগত তোপ দাগানো হয়। রাত্রির শেষভাগে, কামানের অগ্নদগীরণ শেষ হয় এবং এর পর শোনা যায় ভারি কামানের আওয়াজ। এটা ছিল দস্তুরমতো একটা ভূমিকম্প। এথেকে বুঝা যায়, ঈদের আগমনে মুসলমানরা কত খুশি হতো। ঈদের দিনে সমস্ত মুসলমান আনন্দস্ফূর্তিতে মসগুল থাকত। স্ত্রী পুরুষ, বালক বালিকা নির্বিশেষে প্রত্যেকে নতুন এবং উৎকৃষ্ট কাপড় পরিধান করত। চমৎকার পোশাক পরিচ্ছদে সজ্জিত হয়ে মুসলমানগণ প্রভাতে ঈদগাহ ময়দান বা ঈদের নামাজের স্থানে শোভাযাত্রা করে গমন করত। অবস্থাপন্ন ব্যক্তিরা পথেপথে টাকা পয়সা ও উপহার দ্রব্য ছড়িয়ে দিত এবং সাধারণ অবস্থার মুসলমানগণ গরিবদেরকে ভিক্ষা দিত। ‘নওবাহার-ই-মুর্শিদকুলী খানী’ গ্রন্থের লেখক আজাদ হোসেন বিলগ্রামীর বর্ণনায় এর উল্লেখ রয়েছে। তিনি বলেন যে, নবাব শুজাউদ্দিনের অধীনে ঢাকার সহকারী শাসনকর্তা ‘ঈদগাহ’ ময়দানের দিকে শোভাযাত্রা করে যাওয়ার সময় দুর্গ থেকে এক ক্রোশপথে প্রচুর পরিমাণে টাকাপয়সা ছড়িয়ে যেতেন। এক বড় জামাতে মুসলমানগণ তাদের নামাজ পড়ত এবং আনন্দ আবেগে একে অন্যকে উৎসাহের সঙ্গে অভিবাদন জানাতো। গোলাম হোসেন তাবাতাবাঈয়ের বর্ণনায় ঈদ উৎসবে মুসলমানদের খুশি ও আনন্দস্ফূর্তির বিষয় প্রকাশ পেয়েছে। তিনি বলেন যে, প্রত্যেকেই এই দিনে উৎকৃষ্ট পোশাকে সজ্জিত হতো। নবাব আলিবর্দীর ভ্রাতুষ্পুত্র ও জামাতা নওয়াজিশ মুহম্মদ খান তার প্রিয়জনের মৃত্যুতে ‘ঈদ-উল-আজহার’ দিনে নিরানন্দভাবে থাকেন। বৃদ্ধ নবাব তাকে নতুন কাপড় চোপড় পরাবার চেষ্টা করে ব্যর্থ হন। অতঃপর তিনি হারেমের বেগম এবং মহিলাদেরকে ঈদের আনন্দ-উৎসব উপযোগী কাপড় চোপড় নিয়ে তাকে উৎফুল্ল করে তুলতে পরামর্শ দেন।
মুসলমানগণ ত্যাগের উৎসরূপে ‘ঈদ-উল-আজহা’ উদ্যাপনের করে। এর উৎপত্তি হয়েছে পয়গম্বর ইব্রাহীমের সময় থেকে। আল্লাহর উদ্দেশ্যে হযরত ইব্রাহীম প্রিয় পুত্র ইসমাইলকে কোরবানির আয়োজন করেছেন। মুসলমানগণ এই মহৎ দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে। তারা প্রভাতে সুন্দর কাপড়-চোপড় পরিধান করে এবং ‘তকবীর’ উচ্চারণ করতে করতে ঈদগাহ ময়দানের দিকে শোভাযাত্রা করে গমন করে। সেখানে জামাতে তারা নামাজ আদায় করে এবং ভ্রাতৃত্বপূর্ণ মনোভাব নিয়ে আনন্দ প্রকাশ করে, পরস্পরকে আলিঙ্গন করে ও সম্ভাষণ জানায়। অতঃপর তারা গৃহে প্রত্যাবর্তন করে এবং তাদের সাধ্যানুসারে তারা কোনো পশু, যেমন, গরু, ছাগল, মহিষ বা উট কোরবানি করে। তারা গরিব-দুঃখী, বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যে মাংস বিতরণ করে এবং গৃহে ভোজের অনুষ্ঠান করে। প্রত্যেক গৃহ ভোজানুষ্ঠান ও আনন্দ স্ফূর্তিতে মুখরিত হয়ে উঠে এবং সকল গৃহে আদর আপ্যায়ন চলতে থাকে। শুভেচ্ছা বিনিময়ের জন্যে তারা বাড়ি বাড়ি ঘুরে বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয় স্বজনদের সঙ্গে মিলিত হয় এবং এই মহান উৎসবে তারা সকলে একত্রে আনন্দ করে। ‘ঈদ-উল-আজহা’ উৎসব উদযাপনের কথা বলতে গিয়ে মীর্জা নাথন লিখেছেন যে, “নামাজান্তে খতিবের খুতবাহ পাঠ শেষ হলে, লোকেরা তাকে কাপড়-চোপড় ও টাকাপয়সা উপহার দেয়। গরিব দুঃখীদের সাহায্যের জন্য তার সম্মুখে টাকাপসয়া ছড়িয়ে দেওয়া হয়। দুঃস্থ লোকদের অনেকে এর দ্বারা তাদের অভাব দূর করে এবং সুখি হয়। পরস্পরের প্রতি সম্ভাষণে আকাশ বাতাস মুখরিত হয়ে উঠে। কোরবানি সম্পন্ন হবার পর বিরাট ভোজের ব্যবস্থা হয়। সুন্দর গায়ক মোহনী নর্তকী এবং নম্র স্বভাবের গল্প কথকদের মধুর আপ্যায়নের সঙ্গে দিনরাত ভোজানুষ্ঠান চলতে থাকে। শিল্প কারখানার বহু শ্রমিককে উপহার সামগ্রী প্রদানে তুষ্ট করা হয়।” মীর্জা নাথন আরো লিখেছেন “উৎসবের দিনে বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়-স্বজন ও রাজকর্মচারীগণ একে অন্যের জায়গায় গমন করেন এবং ঈদের শুভেচ্ছা জানান। সেনাপতি শাজাত খান আনন্দ উৎসবের এই দিনটিতে বন্ধুবান্ধবদের আপ্যায়নের নিমিত্ত একটি সামাজিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন।” দুতিন দিন উৎসবাদি চলতে থাকে। এর সঙ্গে সঙ্গীত ও নৃত্য পরিবেশনের ব্যবস্থা থাকে।
পয়গম্বরের জন্মদিন
মুসলমানগণ একটি বিরাট ধর্মীয় অনুষ্ঠান হিসেবে রসূলের জন্মদিন পালন করে। এবং শানশওকতের সঙ্গে তারা এ অনুষ্ঠান উদ্যাপন করে। মীর্জা নাথন এই উৎসব উদ্যাপনের উল্লেখ করেছেন, কিন্তু তিনি বিস্তারিত বিবরণ দেননি। বাংলার মুসলমানগণ যে খুব আড়ম্বর ও মহা ধুমধামের সঙ্গে রসূলের জন্মদিবস উদ্যাপন করত, নবাব মুর্শিদকুলী খান কর্তৃক এই দিবস উদ্যাপনের নমুনা থেকে সে সম্বন্ধে একটি ধারণা পাওয়া যায়। নবাব এ দিনটি একটি বিরাট উৎসব আনন্দের দিনে পরিণত করেন। তিনি রবিউল আউয়াল মাসের প্রথম বারো দিন লোকদেরকে আদর অভ্যর্থনা করতেন এবং ব্যক্তিগতভাবে আতিথেয়তায় উপস্থিত হতেন। বিশেষ করে তিনি গরিবদেরকে অভ্যর্থনা করতে ভালবাসতেন। এই উপলক্ষে তিনি সমস্ত মুর্শিদাবাদ শহর ভগীরথী নদীর তীর পর্যন্ত আলোকমালায় সজ্জিত করে তুলতেন। বারো দিনব্যাপী এই উৎসব ও আলোকসজ্জা অব্যাহত থাকত। আলোকসজ্জার স্থানগুলোতে কুরআন শরিফের আয়াতসমূহ এবং মসজিদ, বৃক্ষ, লতাপাতা ও ফলসমূহ প্রদর্শিত হতো। সেনাপতি নাজির আহমদের অধীনে এক লক্ষ্য লোক আলোক সজ্জার কাজে নিয়োজিত হতো। কামান গর্জনের সঙ্গে সঙ্গে সড়ক ও নদী তীরের সমস্ত আলোক জ্বলে উঠত এবং সারা শহর ও ভগীরথী এক আনন্দময় রূপ ধারণ করত। মুসলমানদের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ও সবচেয়ে খুশির মুহূর্ত ঘোষণা করে একটি নির্দিষ্ট সময়ে কামানগুলো গর্জন করে উঠত। মুসলমান শাসনকর্তাগণ ও জনসাধারণ উপমহাদেশব্যাপী রসূলের পবিত্র জন্মদিন পালন করত। ‘মী’রাত-ই-সিকান্দরী’ অনুসারে, গুজরাটের সুলতান মুজাফফর (১৫১৫-১৫২৫ খ্রিঃ) উলেমা, সৈয়দ ও বহু শেখদেরকে ভোজে আমন্ত্রণ জানাতেন এবং তাদেরকে সংবৎসরের উপযোগী টাকা পয়সা ও কাপড়-চোপড় উপহার দিতেন। গুজরাট সুলতান দ্বিতীয় মাহমুদ তদীয় রাজপ্রাসাদে রবিউল আউয়াল মাসের প্রথম থেকে বারো তারিখ পর্যন্ত প্রত্যেক দিন উলেমা ও শেখদের সভার আয়োজন করতেন। তারা ভোর থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত হাদিস আলোচনা করতেন এবং অতঃপর তাদেরকে ভোজে আপ্যায়িত করা হতো। ভোজানুষ্ঠানে সুলতান, তদীয় মন্ত্রীবর্গ ও আমিরগণ উলেমা ও শেখদের সেবাযত্ন করতেন। তিনি এসব বিদ্বান ও ধার্মিক মেহমানদেরকে এরূপ পরিমাণ স্বর্ণ ও পোশাক-পরিচ্ছদ দান করতেন যাতে তারা এক বছরকাল চলতে পারেন।
এসব প্রমাণাদি থেকে প্রতীয়মান হয় যে, মহানবীর জন্মদিন উপলক্ষে তার জীবনী আলোচনার জন্য মহফিল অনুষ্ঠানের প্রথা শাসক ও অবস্থাপন্ন মুসলমানদের মধ্যে প্রচলিত ছিল। ধার্মিক ও বিদ্বান ব্যক্তিদেরকে উপহার প্রদান এবং রোজা রাখা ও মুসলমানদের মধ্যে শুভেচ্ছা বিনিময়ের জন্যেও মহানবীর জন্মোৎসব একটা বিশেষ উপলক্ষ ছিল।
শব-ই-বারাত
শাবান মাসের চতুর্দশ দিবসে অনুষ্ঠিত মুসলমানদের একটি বিরাট উৎসব হচ্ছে শব-ই-বরাত। এটা ছিল প্রার্থনা ও ভোজানুষ্ঠানের সময়। উপমহাদেশের মুসলমানগণ এই উপলক্ষে বহু আচার অনুষ্ঠান ও আমোদ স্ফূর্তির ব্যবস্থা করে এবং অসাধারণ আড়ম্বরের সঙ্গে তা উদ্যাপন করে। আলোকসজ্জা ও আতশবাজি পোড়ানো এই উৎসবের একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য অঙ্গ ছিল। শামস সিরাজ আফিফের বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, সুলতান ফিরোজ শাহ তুগলক চারদিনব্যাপী এই উৎসব উদ্যাপন করতেন এবং এতবেশি আতশবাজি পোড়াতেন যে, রাত্রিকালও প্রকাশ্য দিবালোকের রূপ ধারণ করত। সমসাময়িক উৎসগুলো থেকে জানা যয় যে, শের শাহের একজন বিখ্যাত সেনাপতি ও তার জ্যেষ্ঠ পুত্র আদিল খানের সমর্থক খাস খান ফতেহপুর সিকরীর শেখ সলিম চিন্তির সঙ্গে শব-ই-বারাতের দিন সারারাত এবাদত বন্দেগি করেন। ‘বাহারিস্তান-ই-গায়েবীতে, এই উৎসব উদ্যাপনের উল্লেখ পাওয়া যায়। বাংলার নবাবগণ বিরাট জাঁকজমকের সঙ্গে ‘শব-ই-বারাত উদ্যাপন করতেন। বাড়িঘর আলোকমালায় সজ্জিত করা হতো এবং নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলে মসজিদে ও বাড়িতে সারারাত নামাজ অদোয় করতেন। ভোজানুষ্ঠানের ব্যবস্থা হতো দ্রব্যসামগ্রী বিতরণ করা হতো। আতশবাজির প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হতো।
মুসলমানদের মধ্যে এটি একটি প্রচলিত বিশ্বাস যে, ‘শব-ই-বারাত’ রাত্রে আল্লাহ প্রত্যেক নর-নারীর জন্যে বৎসরের জীবিকা বরাদ্দ করেন। বিশ্বাস করা হয় যে, মহানবী মুসলমানদেরকে এই রাত্রে জেগে এবাদত বন্দেগি, কুরআন তেলাওয়াত ও পুণ্যকর্ম করার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন। কোনো কোনো পণ্ডিতের মতে শব-ই-বারাতের উৎসব হিন্দুদের ‘শিবরাত্রি’ উৎসব থেকে নকল করা হয়েছে। শব-ই-বারাতের উৎপত্তি যাই হোক না কেন, সুলতান ফিরোজ শাহ তুগলকের সময় থেকে মুসলমানদেরকে এই ধর্মীয় সামাজিক উৎসব পালন করতে দেখা যায়। বাংলার মুসলমানগণ উপমহাদেশের অন্যান্য অংশে তাদের ভাইদের মতো এই উৎসব প্রার্থনা, ভোজানুষ্ঠান এবং আমোদ প্রমোদের উপলক্ষরূপে পালন করে।
মুহররম
‘মুহররম’ উৎসব শিয়াদের সঙ্গে জড়িত। ইমাম হাসান হোসেনের শাহাদাত বরণের স্মরণার্থে মুহররম মাসের প্রথম দশ দিনে এটা উৎযাপন করা হয়। বাংলা উপমহাদেশের মুসলমানগণ যে মুহররম উৎসব পালন করে তার প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো শোক প্রকাশ এবং তাজিয়া নামে অভিহিত প্রতীক সমাধি নিয়ে শোভাযাত্রা, এবং এর সঙ্গে জড়িত অন্যান্য আনুষঙ্গিক উপকরণ। মুসলমান আমলে সুন্নি মুসলমানরা বর্তমানের মুসলমানদের ন্যায় কারবালায় হোসেনের করুণ মৃত্যুর জন্যে একটি নীরব শোকের উপলক্ষ হিসেবে এই অনুষ্ঠান উদ্যাপন করে। তাজিয়া শোভাযাত্রায় শিয়াদের ভাবাবেগ প্রদর্শনী থেকে তারা দূরে থাকতেন। সুন্নি মুসলমান সম্প্রদায়ের সাধারণ লোকেরা শোভাযাত্রার ক্রিয়াকর্মে অংশগ্রহণ করত। মুসলিম পঞ্জিকা অনুসারে, প্রথম মুহররম হচ্ছে নববর্ষের দিন। ‘বাহারিস্তান-ই গায়েবী’ থেকে জানা যায় যে, মুসলমানগণ আনন্দ উৎসব ও পারস্পরিক শুভেচ্ছা বিনিময়ের মাধ্যমে মুহররমের চাঁদকে স্বাগত জানাত।
এই উপমহাদেশে কখন মুহররমের তাজিয়া শোভাযাত্রা উৎসব শুরু হয় তা জানা যায় না। তাজিয়া প্রথার সূচনা সাধারণত আমির তৈমূরের নামের সঙ্গে বিজড়িত। বাগদাদের বুয়াইদ সুলতানগণ ইমাম হোসেনের শাহাদাত স্মরণে দশই মুহররম জাতীয় শোক দিবস ও সাধারণ ছুটির দিন হিসেবে উদ্যাপনের প্রথা প্রবর্তনের কৃতিত্বের অধিকারী। এটা প্রতীয়মান হয় যে, মুগল সাম্রাজ্যে প্রার্থনা ও শোক দিবসরূপে মুহররম উৎসব শুরু হয় এবং কালক্রমে তাজিয়ার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য উপকরণগুলো যুক্ত হয়ে পড়ে। ফাদার মনসেরাত সম্রাট আকবরের আমলের মুহররম উৎসব উদ্যাপনের বর্ণনা রেখে গেছেন।
তিনি লিখেছেন যে, মুহররমের সময় মূলমানগণ এ মাসের প্রথম দশ দিন রোজা রাখত, শুধু নিরামিশ খেত এবং জনসভায় উচ্চমঞ্চ থেকে ইমাম হাসান ও হোসেনের আদর্শ জীবনে এবং সত্যের জন্যে তাদের ত্যাগের ও দুঃখ কষ্ট সহ্য করার করুণ কাহিনী বর্ণনা করত। এতে সমবেত শ্রোতাদের মধ্যে শোকোচ্ছাস এবং অশ্রুপ্রবাহ বয়ে চলত। শেষের দিন (দশই মুহররম) তারা সামাধি-চিতা তৈরি করত এবং এগুলোকে একটির পর একটি করে পুড়িয়ে ফেলত। লোকেরা জলন্ত আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়ত এবং অতঃপর তারা তাদের পাদিয়ে নিভে যাওয়া ছাইগুলো ছড়িয়ে ফেলত। তারা হাসান হোসেনের নাম করে উচ্চস্বরে চিৎকার করে উঠত। মানডেলসলো আগ্রায় সম্রাট শাহজাহানের আমলের মুহররম শোভাযাত্রার বর্ণনা দিয়েছেন তিনি বলেন, “তীর-ধনুক, পাগড়ি, ভোজালি এবং পশমি পোশাক-পরিচ্ছদে আবৃত শবাধারগুলো শোভাযাত্রা সহকারে শহরের রাস্তায় রাস্তায় বহন করে নিয়ে যাওয়া হয় এবং অশ্রুসিক্ত চোখে বিলাপ করতে করতে লোকেরা তা অনুসরণ করে। তাদের কেউ কেউ এই অনুষ্ঠানে নৃত্য করে। অন্যান্যরা একে অন্যের সঙ্গে তাদের তরবারির আঘাত করে’; শুধু তাই নয়, তাদের অনেকে নিজেদের দেহে এমনভাবে আঘাত করে ও ক্ষত সৃষ্টি করে যে, কয়েক জায়গা থেকে রক্ত বেরিয়ে আসে। সেই রক্ত দিয়ে তারা কাপড় চোপড় রঞ্জিত করে। এভাবে শোভাযাত্রা অদ্ভুত আকার ধারণ করে। রাত্রের দিকে তারা মহান শহীদদের (হাসান হোসেন) হত্যাকারীদেরকে চিহ্নিত করার জন্যে খড়কুটা দিয়ে কয়েকটি মানুষের ছবি তৈরি করে এবং এগুলোর প্রতি অসংখ্য তীর নিক্ষেপ করে পরে তারা সেগুলোতে আগুন ধরিয়ে দেয় ও ভষ্মে পরিণত করে।” ষোড়শ শতকে মুগলদের বাংলা জয়ের সময় থেকে, এই প্রদেশে শিয়া প্রভাব অনুভূত হয়। শাহজাহানের রাজত্বকালে বিশেষত শাহজাদা শুজার সুবাদারির আমলে বাংলায় বহু সংখ্যক শিয়া সম্প্রদায়ের লোক বসতি স্থাপন করে। মুর্শিদাবাদের নবাবদের আমলে শিয়া জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায়; এবং নবাবরা নিজেরা শিয়া বংশোদ্ভূত হওয়ায় রাজধানী শহর, এবং জাহাঙ্গীরনগর ও হুগলী ইত্যাদি স্থানগুলো তাদের সংস্কৃতির গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রে পরিণত হয়। ষোড়শ শতকের বাংলা সাহিত্যে শিয়াদের ইমামবাড়িগুলোর উল্লেখ রয়েছে। কবি মুকুন্দরাম বলেন, শিকারি রাজা (কালকেতু) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত নতুন শহর গুজরাটে মুসলমানগণ তাদের বসতির পশ্চিম প্রান্তে তাদের হাসানহাটি (ইমামবাড়ি অর্থাৎ মুহররম তাজিয়ার স্থান) নির্মাণ করে এবং তারা সকলে তাজিয়ার স্থানে সমবেত হয়। এতে দেখা যায় যে, যোড়শ শতকের বাংলায় মুহররমের শোভাযাত্রার প্রথা প্রচলিত ছিল। নবাবদের সময়ে অষ্টাদশ শতকে মুহররম একটি বিরাট জনপ্রিয় উৎসবে পরিণত হয়। কারবালার হৃদয়-বিদারক ঘটনা জনসাধারণের অন্তরে এক বিশেষ আবেদনের সৃষ্টি করে। মকতুল হোসেন সঙ্গীত ও অন্যান্য মর্সিয়া কবিতাসমূহ এত জনপ্রিয় যে, এগুলো পাঠক ও শ্রোতাদের উভয়কে সমভাবে অশ্রু আপ্লুত করে তোলে।
মুহররম উৎসবের বিস্তারিত বিবরণ কোনো সমসাময়িক গ্রন্থে পাওয়া যায় না। ঢাকা, মুর্শিদাবাদ ও হুগলীতে ইমামবাড়িগুলোর অস্তিত্ব থেকে বুঝা যায় যে, সুবাদার ও নবাবদের আমলে এই শহরগুলাতে মুহররম উৎসব উদ্যাপিত হয়। আলম মুসাওয়ার কর্তৃক অঙ্কিত উনিশ শতকের প্রথম দিকের একটি চিত্রে এবং হাকিম আহসানের একটি বর্ণনায় ঢাকায় মুহররম উৎসব উদ্যাপনের প্রমাণ মেলে। মুহররমের চাঁদ দেখার সঙ্গে সঙ্গে উৎসব শুরু হতো। এবং সেই রাত্রি থেকে ইমামবাড়ির ‘নওবত খানা’য় নওবতের (সঙ্গীত) সুর বাজান হতো। সেই সময় থেকেই মাতমে মজলিশ শুরু হতো। ইমামবাড়ির দেয়ালে দেয়ালে মোমবাতি জ্বালান হতো। চতুর্থ দিবস থেকে মর্সিয়া (শোক সঙ্গীত) শোনার জন্যে ইমামবাড়ির লোকেরা সমাগত হতো। মার্সিয়া-গায়করা দলে দলে তাদের নিজস্ব নিশান নিয়ে আগমন করত। ষষ্ঠ ও সপ্তম দিবসে শহরের বিভিন্ন অঞ্চলের লোকেরা প্রতিযোগিতামূলকভাবে আতশবাজি পোড়াত। পঞ্চম দিনে পানি বাহকরা (মশক) পাজামা আচ্ছাদিত মোটা সবুজ লুঙ্গি ও সবুজ সার্ট বা আচকান, বহু রঙা ঝালরবিশিষ্ট পাগড়ি পরিহিত অবস্থায় শহরে শোভাযাত্রা করে বের হতো। তারা গলায় একখণ্ড কাফনের কাপড় (কাফনি), বুকে একটি ‘বাদ্দী’ (এক সুতার মালা), এবং এরকম অন্যান্য অলংকারাদি ধারণ করত। তারা এক হাতে গ্লাস ও এক পার্শ্বে পানির বোতল এবং অন্যহাতে একটি সুসজ্জিত লাঠি বহন করত এবং খালি পায়ে চলত। ষষ্ঠ দিনে পানি বহনকারীদের লাঠিগুলো ইমামবাড়ির ভূমির উপর আড়াআড়িভাবে রাখা হতো এবং সেখানে সমবেত লোকদের মধ্যে মিষ্টান্ন ও অন্যান্য ‘নিরাজ’ বিতরণ করা হতো এবং অতঃপর তারা পানি বহনকারীদের পোশাকে সজ্জিত হয়ে মিছিল করে তাদের আত্মীয়-স্বজনদের কাছে ভিক্ষার জন্য বের হতো।
‘জুলুসে’র (মিছিলের) সপ্তমদিনে ইমামবাড়া আলোক সজ্জিত করা হতো এবং জনসাধারণ সেখানে শোকোচ্ছ্বাস দেখার জন্য ভিড় জমাত। অষ্টম দিনে মহিলাগণ অপরাহ্নে ইমামবাড়ায় সমবেত হতেন এবং শোকসংগীত পরিবেশন করতেন। এই সময় পুরুষেরা সেখান থেকে সরে যেতেন। রাত্রিতে ‘তুগ গোশত’ (তুর্কী ভাষায় ‘তুগ’ অর্থ পতাকা এবং গোশত্ অর্থ ভ্রাম্যমাণ) নামে অভিহিত মিছিল শুরু হতো এবং শহরের প্রধান প্রধান সড়কগুলো অতিক্রম করা হতো। শোভাযাত্রার পুরাভাগে থাকত দু থেকে চারটি আখড়া (আখড়া ক্লাবের মতো। সেখানে একজন ওস্তাদ যুবকদেরকে লাঠিখেলা শিক্ষা দিতেন।) লোক এবং এদের সঙ্গে থাকত গ্লাসে আলোকবর্তিকা বহনকারিগণ। অতঃপর থাকত একরকম পোশাক পরিহিত একদল লোক, ওরা দু’টা বা তিনটা সারিতে পতাকা বহনকারীদের (আলম-বরদার) অনুগমন করত। অতপর আসত গাঢ় লাল রংয়ের কাপড়ে সজ্জিত হাতি এবং তুগরা পদ্ধতিতে লিখিত ‘ইয়া ফাতাহ’ (হে বিজয়ী) এবং ‘ইয়া আলী’ প্রতীক নিশান। এরপরে অনুগমন করত অভ্রগ্লাসসমূহে আলো বহন করে একসারিতে সুসজ্জিত অশ্বসমূহ। অতঃপর থাকত কাফেলা-মিছিলের প্রতীক ডঙ্কা (বাদ্য), বাদ্যযন্ত্র এবং শোকসঙ্গীত ‘নওবত’ ইত্যাদি বাজিয়ে কয়েকটি সঙ্গীতকারদের দল। এবং এদের অনুগমন করত কাল কাপড়ে আবৃত দুটো পালকি (দোলা) এবং এদের অগ্রভাগে থাকত হাতে আলম (পতাকা) নিয়ে কয়েকজন অশ্বারোহী এবং আলম ও সামরিক বাদ্যযন্ত্র হাতে দুজন পদাতিক। পানিবাহকগণ পালকির উভয়পার্শ্বে শ্লোগান দিতে দিতে অগ্রসর হতো। দোলাগুলো পরে উটের পিঠে বহন করা হতো। পালকির পিছনে থাকত কালো অথবা সবুজ কাপড় পরিহিত ও হস্তে মোমবাতি নিয়ে শোককারিগণ। এই দলে ছিল ‘জুলজানাহ’ (হোসেনের অশ্ব) এবং এর সঙ্গে অনুগমন করত রক্তরঞ্জিত জিন ও জুলফিকার (আলীর তরবারি) বহন করে দুল দুল (আলীর অশ্ব)। সর্বশেষে ছিল দুটো ঢাক নিয়ে একটি হস্তী, ঢাক দুটো মৃদুভাবে বাজান হতো এবং এতে মিছিলের শেষ চিহ্নিত হতো।
নবম দিনে শোভাযাত্রা বের করা হতো রাত্রিবেলা এবং তখন আখড়া-প্রদর্শনীর লাঠি খেলার ব্যবস্থা থাকত। তরবারি, চাকু এবং আগ্নেয়াস্ত্রের খেলারও ব্যবস্থা ছিল। এই ব্যবস্থাপনায় বিগত রাত্রির ‘তুগ গাশত’ এর অনুসরণ করা হতো। ‘জুলজানাহ’র পেছনে আরো কিছু বিষয় সংযোজিত ছিল, যেমন কাঠের তক্তায় বসান একটি পাহাড় এবং উপরে একটি মিহরাব। এগুলোর সবটাই থাকত কাগজে মোড়া ও পার্শ্বগুলো আড়াআড়ি স্থাপিত তরাবারি এবং ঢাল দিয়ে সজ্জিত। ফলে এসব দৃশ্য প্রায় আসলাহ খানার (অস্ত্রাগার) রূপ ধারণ করত। অভ্যন্তর ভাগে থাকত কারবালায় নিহত বীরদের কাগজে তৈরি দ্বিতল বিশিষ্ট একটি প্রতীক সমাধি সৌধ।
দশম দিনকে বলা হতো আশুরা। প্রতীক সমাধি (জরীহমুবারক) ‘সহ তাজিয়া’ শহরের বিভিন্ন এলাকাসমূহে ঘুরান হতো এবং অতঃপর তা পানিতে ফেলে দেওয়া হতো কিন্তু কাল কাপড়ে আবৃত পতাকাগুলো ও প্রতীক সমাধিসমূহ নীরবভাবে ইমামবাড়ায় ফেরৎ আনা হতো। এভাবে শিয়া অনুষ্ঠান সমাপ্ত হতো। অপরাহ্ণে সুন্নিরা তাজিয়া শোভাযাত্রা বের করতেন। এতে হোসেনের প্রতি এজিদের সৈন্যদের সহানুভূতি প্রদর্শিত হতো; এরা হোসেনকে যথারীতি সমাধিস্থ করার জন্য রাত্রে তার পবিত্র দেহ নিয়ে যায়। এই তাজিয়া পানিতে রেখে আসা হতো। এর দ্বারা মুহররম উৎসবের সমাপ্তি করা হতো।
বেড়া উৎসব
বাংলায় মুসলমান শাসনামলে উদ্যাপিত বেড়া অনুষ্ঠান ছিল একটি জনপ্রিয় উৎসব। এই উৎসব উদ্যাপিত হতো খাজা খিজিরের (পয়গম্বর ইলিয়াস) সম্মানে। তিনি হচ্ছেন সমুদয় সমুদ্র, সাগর ও নদনদীর পৃষ্ঠপোষক সাধু দরবেশ। কিংবদন্তি এর উৎপত্তির সঙ্গে সুফিবাদের আদমিয়া সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা ইব্রাহিম-বিন আদমের (মৃত্যু ৭৪৩ খ্রিঃ) নাম যুক্ত করে। ভারতে তার শিষ্য সম্প্রদায় খিজিরিয়া নামে পরিচিত। কেননা, তারা খিজির বা খাওয়াজা খিজিরের অলৌকিক শক্তিতে বিশ্বাসী-যিনি বাংলা মুল্লুকে খিজির পিররূপে জন-সাধারণ্যে পরিচিত। আজও নদীমাতৃক বাংলার লোকেরা বিশ্বাস করে যে, খিজিরপির হচ্ছেন নদনদীতে মাঝি ও নাবিকদের অভিভাবক ও রক্ষাকর্তা এবং তিনি তাদেরকে নদনদী ও সাগরসমূহে সকল বিপদ থেকে রক্ষা করেন। কলিকাতার খিদিরপুর এবং নারায়ণগঞ্জের সন্নিকটস্থ খিদিরপুর খুব সম্ভবত খিজির পিরের নামের স্মৃতি বহন করছে। উনিশ শতকের শেষপাদে ডক্টর ওয়াইজ লিখেছেন যে, বেড়া উৎসব স্থানীয়ভাবে খাজা খিজিরের নামের সঙ্গে বিজড়িত; তিনি “বর্তমানে জাহাজডুবি থেকে রক্ষা করতে ভারতের বহু নদনদী ও সাগরের বসবাস করেন, এবং তিনি কেবল তাদের কাছেই দৃশ্যযোগ্য যারা নদীর তীরে দীর্ঘ চল্লিশ দিনব্যাপী দৃষ্টি রাখেন।” বাংলার জনসাধারণ পৃষ্ঠপোষক দরবেশের প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ হিসেবে আনুষ্ঠানিকভাবে কলাগাছ, বাঁশ ও কাগজের তৈরি ভেলা ভাসিয়ে বেড়া ভাসান উৎসব উদ্যাপন করতেন। মুগল শাসনপর্বে প্রদেশে বেড় উৎসব সরকারিভাবে উদ্যাপিত হতো। এটা সুবিদিত যে, সুবাদার মুকাররম খান (১৬২৬-২৭ খ্রিঃ) ব্যক্তিগতভাবে বুড়ীগঙ্গা নদীতে এই বেড় ভাসান উৎসবের আয়োজন করতেন। মুর্শিদকুলী খান অত্যন্ত একটি বিরাট ভেলা তৈরি করেন এবং এর উপর তিনি কাগজের ঘর ও একটি মসজিদ নির্মাণ করেন। এগুলোকে সুন্দরভাবে সাজানো হয় ও আলোকসজ্জিত করা হয়। ভেলাটি ছিল দৈর্ঘ্যে ৩০০ কিউবিক। জাঁকজমকপূর্ণভাবে সজ্জিত ভেলাটি আতশবাজির প্রদর্শনী ও আমোদ প্রমোদের মধ্য দিয়ে ভাগীরথীর জলে ভাসান হয়েছিল। ভেলাটির আলোকসজ্জা বহু মাইল দূর থেকে দৃষ্টিগোচর হতো। এ উৎসব ভাদ্র মাসের শেষ বৃহস্পতিবারে অনুষ্ঠিত হতো। বহু মুসলমান এই বেড়া উৎসবের আনন্দ স্ফূর্তিতে অংশ নিতেন। ডক্টর ওয়াইজ সিরাজদ্দৌলাহর সময়কার বেড়া উৎসবের বর্ণনা দিয়েছেন। নবাব নিজে ভাগীরথীর জলে শত শত ভেলা ভাসিয়ে এ উৎসব উপভোগ করেন এবং নদীর তীরভূমি জুড়ে মুর্শিদাবাদের অধিবাসীরা বিপুলভাবে জড়ো হয়েছিল। উৎসবের কথা বলতে গিয়ে, ডক্টর ওয়াইজ বলেন, “বেড়া সাধারণত বক্রাকৃতি বিলাস তরণীর অগ্রভাগস্থ আকৃতির অনুকরণে চাকচিক্যপূর্ণভাবে কাগজ দিয়ে তৈরি ছিল এবং পোতাগ্র ভাগ ছিল ময়ূরের ঝুটি ও বক্ষ সম্বলিত স্ত্রী জাতীয় বাজপাখি সদৃশ। কদলীবৃক্ষের গুড়ির একটি ভেলার উপর প্রতিকৃতি স্থাপন করত সূর্যাস্তকালে ভাসিয়ে দেওয়া হতো এবং রাত্রি বেলা অন্ধকারে ভরা নদীজলে আলোকচ্ছটা অপূর্ব চিত্রের মতো মনে হতো।”
নামকরণ
জন মার্শাল ১৬৬৮ খ্রিষ্টাব্দে বাংলা পরিভ্রমণে আসেন এবং শিশুসন্তানের জন্মের সঙ্গে সম্পর্কিত অনুষ্ঠানাদির বর্ণনা রেখে যান। তিনি বলেন, “মুর বা মুসলমানগণ তাদের জন্মের দ্বিতীয় দিনে একটি নাম পায়। নবজাতকের পিতা অথবা নিকট আত্মীয় কোনো মৌলভী বা ধর্মগুরুকে আমন্ত্রণ করেন। তিনি এসে ধর্মীয় পুস্তক (বিশেষত কুরআন) বন্ধ করেন; পিতা কোনো সুচাঁলো কাঠি এই গ্রন্থের পাতার মধ্যে প্রবিষ্ট করেন, অতঃপর সূঁচবিদ্ধ পাতা খোলা হলে মৌলভী সেই পাতার প্রথম অক্ষরটি গ্রহণ করেন। এর অর্থানুসারে শিশুর নামকরণ করা হয়।” জন মার্শালের বর্ণনা থেকে বুঝা যায় যে, বাংলার মুসলমানগণ শিশুর নামকরণে ধর্মীয় গ্রন্থের (কোরআন শরিফ) সাহায্য নিতেন। মুসলমানদের মধ্যে অদ্যাবধি এই রীতি প্রচলিত আছে। বাংলার মুসলমান সমাজে আরবি নামসমূহ প্রচলনের এটি একটি কারণ।
আকিকা
শিশুসন্তানের জন্মের সঙ্গে আকিকা একটি একান্ত প্রয়োজনীয় অনুষ্ঠান। আকিকা শব্দের অর্থ হচ্ছে নবজাতক শিশুর কেশ। কিন্তু এটা সাধারণভাবে ক্ষৌরকর্ম অনুষ্ঠান ও আনুষ্ঠানিকভাবে শিশুর নামকরণ অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এই অনুষ্ঠানে, শিশুর নামকরণের স্মৃতি রক্ষার্থে শিশুপুত্রের ক্ষেত্রে দুটো এবং শিশুকন্যার ক্ষেত্রে একটি মহিষ অথবা ছাগল জবাই করা হতো এবং আত্মীয় স্বজন ও গরিবদের মধ্যে এই মাংস বিতরণ করা হতো। ভোজানুষ্ঠানের আয়োজন করে, অবস্থাপন্ন পিতামাতা জনসাধারণকে আপ্যায়িত করতেন।
বিসমিল্লাহখানি শিশুর সঙ্গে সম্পৃক্ত আর একটি গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠান। শিশুর চার বছর চার মাস চার দিন বয়ঃক্রমকালে এই অনুষ্ঠান উদ্যাপন করা হয়ে থাকে। প্রার্থনা, আর্শীবাদ ও আমোদ-প্রমোদের মধ্যে দিয়ে আল্লাহর নামে পড়াশোনা শুরু করার জন্যে শিশুকে ওস্তাদের নিকট সমর্পণ করা হয়। এভাবে শিশু শিক্ষাজীবনে প্রবেশ করে। লিঙ্গাগ্রের চর্ম কর্তন করাকে বলা হয় খাতনা। এটা সুন্নত নামেও পরিচিত। এটি একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠান। মসলমানরা আনুষ্ঠানিকভাবে এই উৎসব উদ্যাপন করত। সাধারণত শিশুর সাত বছর বয়সের সময় খাতনা করা হতো এবং এই উপলক্ষে আনন্দ উৎসব করা হতো এবং ভোজ ও উপহার দেওয়া হতো।
বিবাহ
বিবাহ একটি গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক অনুষ্ঠান ছিল; ধুমধাম ও ভোজানুষ্ঠানের সঙ্গে এটা সম্পন্ন হতো। বিবাহ উৎসব সম্পর্কে এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।
মৃতের জন্য অনুষ্ঠানাদি
মৃত্যুর সঙ্গে সম্পর্কিত কতকগুলো পবিত্র কৃত্য ছিল। মৃতদেহ একটি শবাধারে (কফিনে) রাখা হতো এবং একটি বড় ধরনের জমায়েতে প্রার্থনাপর্ব অনুষ্ঠিত হতো। অতঃপর শবাধারটি আনুষ্ঠানিকভাবে কবরে রাখা হতো। মৃতের পরিবার পরিজন, আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধুবান্ধবগণ দশদিনব্যাপী শোকপালন করত। বিদেহী আত্মার জন্য মঙ্গল কামনায় তারা প্রার্থনা করত।
পরিবারের শোক-পর্ব ছয়মাসেরও অধিককাল অব্যাহত থাকত। অত্যন্ত ভাবগম্ভীর পরিবেশে ছয়মাস অন্তর মৃতের উদ্দেশ্যে ভোজানুষ্ঠানের ব্যবস্থা হতো। কুরআন শরিফ তেলাওয়াতকারীদের কাপড়-চোপড় ইত্যাদি উপহার প্রদান করা হতো এবং লোকদেরকে সুস্বাদু খাদ্য ও ফলমূল দিয়ে আপ্যায়ন করা হতো। অতঃপর বিরাট ভোজানুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে শোকপর্বের সমাপ্তি ঘটত। এটা আমোদ-প্রমোদের সঙ্গে পালিত হতো। মীর্জা নাথন তদীয় মৃত পিতার জন্য শোকপর্বের সমাপ্তি ঘটান বিরাট ভোজানুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে। নাথন বলেন, “এই উপলক্ষে এরূপ জনসমাগম হয়েছিল যে, এটা পৃথিবীর ইতিহাসে উল্লেখের যোগ্য।”