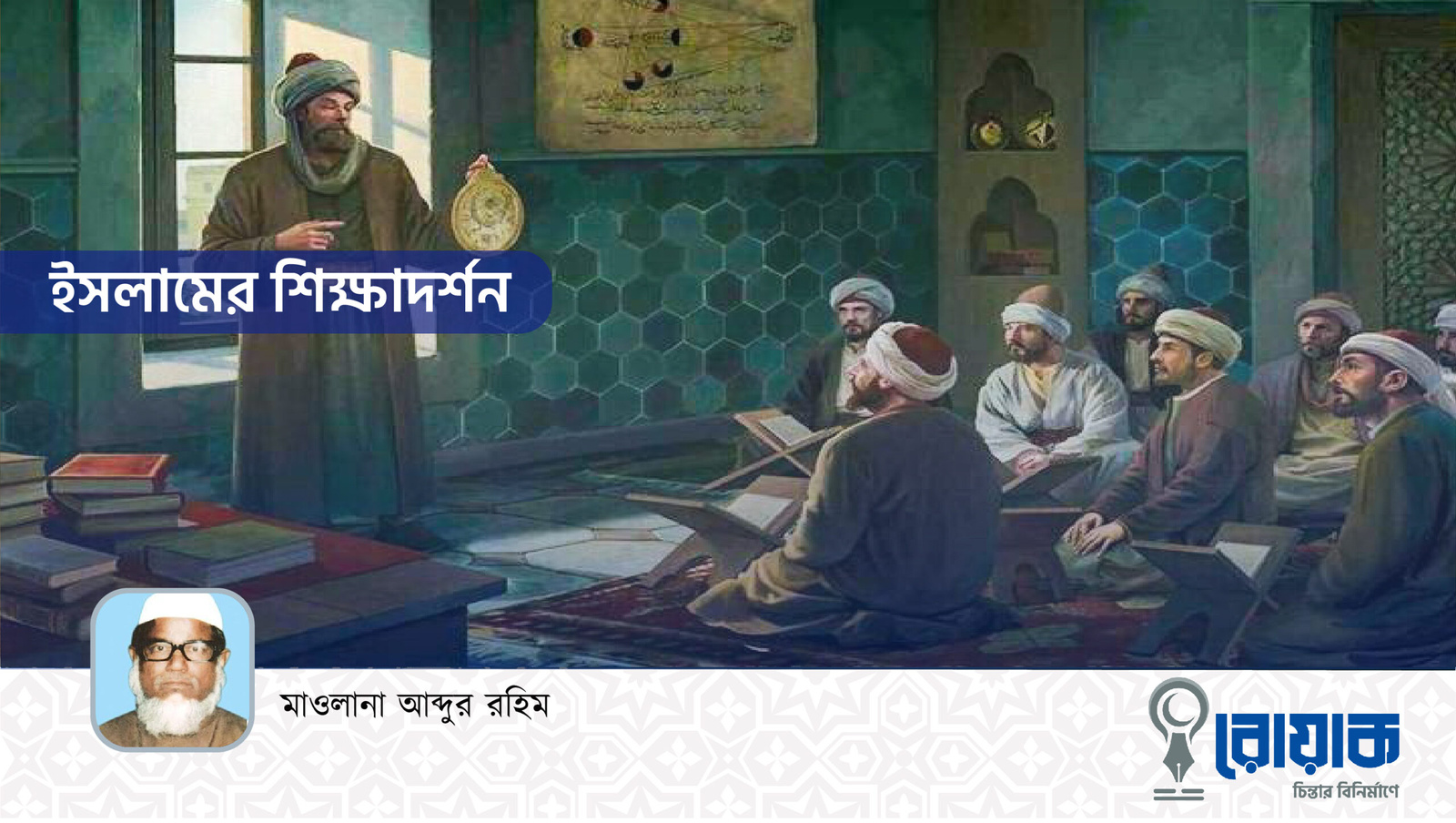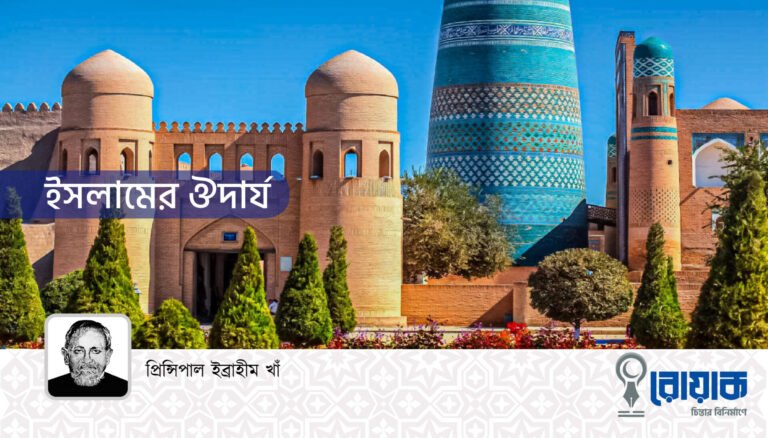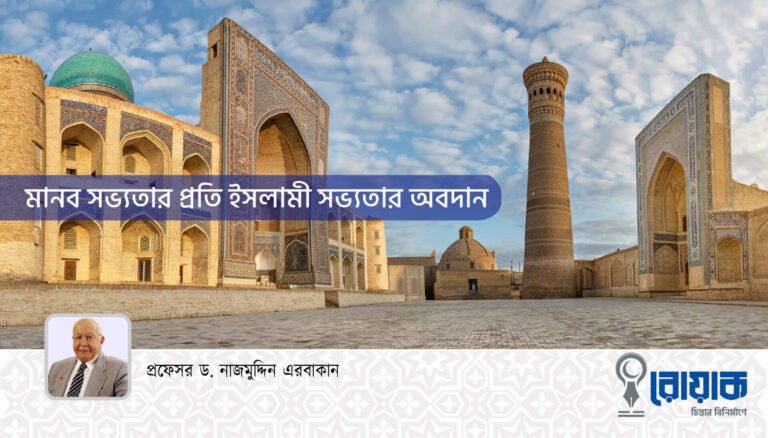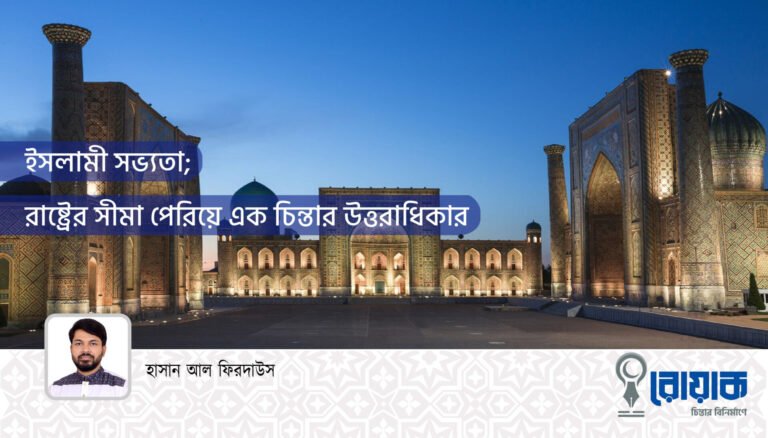ইসলামের শিক্ষা দর্শন বা শিক্ষা সম্পর্কে ইসলামের ধারণা কিংবা দৃষ্টিকোণ কি, তার সংজ্ঞা এবং লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য কি, সে বিষয়ে কোন চূড়ান্ত ও স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছতে হলে প্রথমেই মানুষ সম্পর্কে ইসলামের ধারণা ও দৃষ্টিকোণ বিষয়ে মৌলিকভাবে বিচার বিবেচনা করা হবে।
মানুষ দুনিয়ার অন্যান্য জীবজন্তু ও বস্তুর ন্যায় একটি সৃষ্টি হলেও মানুষ একটা বিশেষ সৃষ্টি। জন্ম, বৃদ্ধি (Growth), খাদ্য ও অন্যান্য প্রাকৃতিক উপাদান গ্রহণ করে জীবনে বেঁচে থাকার দিক দিয়ে মানুষ অন্যান্য জীবের মত হলেও সে সব থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য ও বিশেষত্বের অধিকারী। মানুষ মাটি বা প্রস্তরের ন্যায় নির্জীব, নিষ্প্রাণ বা স্থবির নয়। মানুষ প্রাণসম্পন্ন, সজীব ও চলৎ-শক্তি সম্পন্নও বটে। এখানেই শেষ নয়; সাধারণ জীব-জন্তু ও প্রাণকুল থেকে মানুষ এই দিক দিয়েও ভিন্নতর যে, মানুষের রয়েছে চিন্তাশক্তি, স্মরণশক্তি, বাকশক্তি-আছে মনের কথা প্রকাশ করার ভাষা। সে ভাষা যেমন মুখে ব্যবহৃত হয়, তেমনি হয় কলমের দ্বারা। এই কারণে সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রশ্ন কেবল মানুষের বেলায়, অন্যান্য জীব-জন্তুর ক্ষেত্রে তার কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না। সর্বোপরি মানুষের রয়েছে ন্যায়-অন্যায়, ভাল-মন্দ ও পাপ-পুণ্যবোধ। এই বোধ মানুষের স্বভাবগত, জন্মগত। কিন্তু সাধারণ জন্তু-জানোয়ার এই বোধ থেকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত।
মানুষের চিন্তা-ভাবনা, গবেষণা-বিবেচনার ক্ষমতা রয়েছে। এই কারণেই মনে তীব্র হয়ে জেগে উঠে নিদারুণ জিজ্ঞাসা-নিজের সম্পর্কে, বিশ্বলোক সম্পর্কে।
বিশ্বলোক সম্পর্কিত প্রশ্ন হচ্ছে, এই বিশ্বলোক কি কোন বাস্তব সত্য, না সম্পূর্ণ অলীক, অস্তিত্বহীন? যদি সত্য ও বাস্তব হয়, তাহলে এই বিশ্বলোক কি স্বয়ম্ভু, না এর স্রষ্টা কেউ আছেন? স্রষ্টা থাকলে তিনি কি এক ও অনন্য, না একাধিক বা বহুসংখ্যক? এবং স্রষ্টার সাথে মানুষের সম্পর্কই বা কি?
মানুষের সম্পর্কে যে সব প্রশ্ন জাগে, তা মোটামুটি তিনটি পর্যায়ের। প্রথম পর্যায়ে নিজের অস্তিত্ব সম্পর্কে- সে কে? সে কি দুনিয়ার অন্যান্য জীব-জন্তু-বস্তুর মতই কিছু, না সে সব থেকে তার কোন স্বাতন্ত্র্য আছে? তার নিজের বিবেচনায়ই সে যখন সার্বিকভাবে নিজের স্বাতন্ত্র্য প্রকট দেখতে পায়, তখন তার কারণ ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে তার মনে প্রশ্ন জাগে। দ্বিতীয় পর্যায়ের প্রশ্ন হচ্ছে, এই দুনিয়ায় তাকে যে জীবন দেয়া হয়েছে এই জীবনটাকে সে কোন্ কাজে কোন্ বাস্ততায় এবং কিভাবে ও কি পদ্ধতিতে অতিবাহিত করবে? তার পার্শ্বে অবস্থিত অসীম-অশেষ প্রাকৃতিক শক্তি-সম্পদ ও উপকরণকে নিজের ও অন্যান্য মানুষের কল্যাণে কিভাবে ব্যবহার করবে, কোন্ অধিকারে ও কোন মৌল দৃষ্টিকোণ নিয়ে এবং কোন উদ্দেশ্যে? আর তৃতীয় প্রশ্ন হচ্ছে, তার জীবনে যাবতীয় দায়-দায়িত্ব কি এই দুনিয়ায়ই শেষ ও চূড়ান্ত? না মৃত্যুর পরও তার কোন জের চলবে। যদি চলে, তাহলে তার সাথে এই জীবনের ও জীবনব্যাপী কর্মধারার কি সম্পর্ক?
এসব প্রশ্ন কোন জন্তু জানোয়ারের মনে জাগে না। তাদের পর্যায়ে এসব প্রশ্ন কখন উঠে না। তাই সে ক্ষেত্রে এসব জওয়াব দেওয়ারও কোন প্রয়োজন নেই। এই প্রশ্ন জাগে কেবল মানুষের মনে, মানুষের ক্ষেত্রে। অতএব তাদের জন্য এই প্রশ্নের জবাব একান্তই অপরিহার্য। কেননা এসব প্রশ্নের স্পষ্ট ও অকাট্য জবাব না পেলে এই দুনিয়ার মানুষের পক্ষে সুষ্ঠু জীবন যাপন করা কোন ক্রমেই সম্ভব হতে পারে না।
এসব প্রশ্ন মানুষের মন থেকে কখনই নিঃশেষ ও বিলুপ্ত হয়ে যাবে না। মানুষ যতদিন জন্তু হচ্ছে না (কোন দিনই তা হবার নয়), এই প্রশ্নসমূহ মানব মনে চির জাগরূক হয়েই থাকবে।
কিন্তু এসব প্রশ্নের জবাব মানুষ কোথায় পাবে? এই জবাব তাকে জানতে হয় অর্জিত জ্ঞানের মাধ্যমে। অতএব জ্ঞানার্জন মানুষের জন্য অপরিহার্য। জ্ঞানার্জনের জন্য যে যোগ্যতা থাকা আবশ্যক, তা স্বভাবগতভাবে কেবল মানুষেরই রয়েছে। মানব প্রকৃতি নিহিত সেই শক্তি ও যোগ্যতাকে সম্পূর্ণরূপে ব্যবহার করতে হবে এই জ্ঞান অর্জনের জন্য।
এই বিশ্লেষণের আলোকে বলা যায়, মানুষকে মৌলিকভাবে জানতে হবে-
১. স্রষ্টা ও সৃষ্টিকর্মের নিয়ম ধারা, সৃষ্টি লোকে সদা কার্যকর নিয়মের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশেষত্ব।
২. বিশ্বলোক ও বিশ্বলৌকিক যাবতীয় জিনিষের গুণাগুণ ও বৈশিষ্ট্য, বিশেষত মানুষের কল্যাণ সে সবের প্রয়োগের নির্ভুল পদ্ধতি।
৩. এই দুনিয়ায় মানুষের দায়িত্ব কর্তব্য ও জীবন-যাপন পদ্ধতি এবং পরকালে জবাবদিহির ধারণা ও পরিণাম। এই পরিপ্রেক্ষিতে জ্ঞানের সংজ্ঞায় বলা যায়- স্রষ্টা, তাঁর গুণাবলীর তত্ত্ব ও বাস্তবতা, আল্লাহ্ সৃষ্ট এই বিশ্বলোক, সদা কাল নিয়ম, বস্তুর গুণ ও মানুষের কল্যাণে তার প্রয়োগ পদ্ধতি এবং সর্বোপরি নিজের বিশেষ অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যত, নিজের দায়িত্ব কর্তব্য এবং জবাবদিহি সম্পর্কে এমনভাবে জ্ঞানার্জন যেন তার মন-মগজ ও জীবন স্রষ্টার অনুগত এবং স্রষ্টার সন্তুষ্টি লাভার্থে নিয়োজিত পারে, কেননা, তার শেষ পরিণতি তাতেই।
বস্তুতঃ যে মানুষ স্রষ্টাকে জানে না, জানে না তাঁর মহান গুণাবলী, তাঁর অসীম অসাধারণ দয়া ও অনুগ্রহের অবদান, সে মূলতঃ কিছুই জানে না। সব জ্ঞানের মূল এখানেই নিহিত। যে লোক তার নিজের জীবন যাপন পদ্ধতি ও ভাল-মন্দ জানে না, জানে না তার পরিণতি কি হতে পারে ও শুভ পরিণতি লাভ কিভাবে সম্ভব, সে তো সম্পূর্ণ অন্ধ ও অজ্ঞ। আর অন্ধ ও অজ্ঞ কখনো দর্শনশীলের মত হতে পারে না।
অন্ধত্ব ও অজ্ঞানতার অন্ধকারে মানুষের জীবন কিছুতেই চলতে পারে না। সাধারণভাবে প্রত্যেকটি জীব ও জন্তুর চোখে একটা নিজস্ব আলো আছে। তাই দিয়ে তারা অন্ধকারেও নিজের পথ দেখে চলতে পারে। এজন্য তারা বাইরের আলোর মুখাপেক্ষী নয়। কিন্তু মানুষের চোখের ভিতরে নিজস্ব কোন আলো নেই। এই কারণে দেখার জন্য তারা বাইরের আলো বিচ্ছুরণের মুখাপেক্ষী। কিন্তু বাইরের আলো তার বৈষয়িক জীবনের পথে চলার জন্য যথেষ্ট হলেও মনোপযোগী জীবন যাপনের জন্য তা কিছু মাত্র যথেষ্ট নয়। মানুষের জন্য প্রয়োজন অর্জিত জ্ঞানের স্বচ্ছ আলো। এই আলোই তাকে অর্জন করতে হবে। একমাত্র নির্ভুল ও সর্বপ্রকারের সংশয়মুক্ত সূত্রে অর্জন যোগ্য এই জ্ঞানের কয়েকটি পর্যায় রয়েছে।
মানুষের পক্ষে প্রথম কর্তব্য হচ্ছে, তার স্রষ্টাকে জানা, স্রষ্টা সম্পর্কিত পূর্ণাঙ্গ জ্ঞান অর্জন করা। স্রষ্টাই স্বীয় অনুগ্রহে-স্বীয় ইচ্ছা ও কুদরতে তাকে সৃষ্টি করেছেন। তিনি সৃষ্টি না করলে মানুষের পক্ষে এই জীবন লাভ করা-এই দুনিয়ার সুখ সম্ভোগের কোন সুযোগ পাওয়াই সম্ভবপর হত না। তাই স্রষ্টার গুণ (সিফাত), দয়া অনুগ্রহের কথা তাকে জানতে হবে। জানতে হবে, তিনি কোন মহান উদ্দেশ্যে মানুষকে এই দুনিয়ায় সৃষ্টি করেছেন এবং কিসে তিনি সন্তুষ্ট, কিসে অসন্তুষ্ট? তা জানতে না পারলে মানুষের পক্ষে এই দুনিয়ায় আল্লাহর মর্যী অনুযায়ী জীবন যাপন করা সম্ভব হবে না-সম্ভব হবে না, পরকালে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করাও সম্ভব হবে না। আর তাই যদি না হয়, তাহলে মানুষের এই জীবনটাই যেমন চরমভাবে ব্যর্থ হয়ে গেল মনে করতে হবে, তেমন পরকালীন জীবন তাকে অনন্ত দুঃখ, দুর্দশা ও আযাবে নিক্ষিপ্ত হতে হবে। তা থেকে সে কিছুতেই নিষ্কৃতি লাভ করতে পারবে না। তাই জ্ঞান লাভের একমাত্র সূত্র হচ্ছে আল্লাহর নাযিল করা কিতাব–কুরআন মজীদ, যা তিনি নাযিল করেছেন তাঁর শেষ নবী ও শেষ রাসূল হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর উপর। তিনি আল্লাহর নির্দেশে তাঁর কিতাব দুনিয়ার মানুষের নিকট পৌছিয়েছেন, তার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করে বুঝিয়েছেন এবং নিজে তদনুযায়ী আমল করে তার বাস্তবতা দেখিয়ে দিয়েছেন। পবিত্র কুরআন এবং মহান রাসূলের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ- এই হচ্ছে আল্লাহ্ প্রদত্ত নির্ভুল জ্ঞানের মাধ্যম ও একমাত্র নির্ভরযোগ্য জ্ঞান-উৎস। এই জ্ঞান-মাধ্যম ও জ্ঞান-উৎস থেকেই মানুষ তার মনুষ্যত্বকে জানতে পারে, জানতে পারে কিভাবে তাকে একক ও সামষ্টিক জীবন যাপন করতে হবে। বিশ্ব-প্রকৃতি নিহিত জ্ঞান লাভের মৌল প্রেরণা সে এ থেকেই পেতে পারে। কেননা স্রষ্টা, সৃষ্টিলোক এবং এই মানুষ সম্পর্কে সম্পূর্ণ নির্ভুল জ্ঞান কেবলমাত্র স্বয়ং স্রষ্টারই থাকতে পারে। তাই তাঁর দেয়া জ্ঞানের তুলনায় অপর কোন উৎস থেকে পাওয়া জ্ঞান কখনই অধিক নির্ভুল, যথার্থ ও নির্ভরযোগ্য হতে পারে না। কিন্তু আধুনিক শিক্ষা দর্শনে কেবল মাত্র বিশ্ব-প্রকৃতি ও বস্তুলোক সংক্রান্ত জ্ঞানকেই একমাত্র শিক্ষণীয় বিষয় বলে দাবী করা হয়েছে। কিন্তু তাতে মহান স্রষ্টাকে অস্বীকার করা হয়েছে যেমন, তেমন আল্লাহর দেওয়া নির্ভুল জ্ঞান-উৎসকেও সম্পূর্ণ উপেক্ষা করা হয়েছে।
এই জ্ঞানের প্রথম সূত্র হচ্ছে- মানুষের ইন্দ্রিয়–লব্ধ তথ্য ভিত্তিক চিন্তা গবেষণার ফসল। কিন্তু ইন্দ্রিয়প্রাণী জগত নিতান্তই বাহ্যিক জগত। আসল ও প্রকৃত সত্য নিহিত রয়েছে। এই দৃশ্যমান জগতের অন্তরালে। সেই অন্তরালবর্তী নিগূঢ় সত্য জ্ঞানের ভিত্তিতেই ইন্দ্রিয়-লব্ধ জ্ঞানের সত্য সত্য যাচাই করা সম্ভব। আর সে জ্ঞান মহান সৃষ্টিকর্তা ভিন্ন আর কারোই থাকতে পারে না। ফলে নিছক ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য জ্ঞান-উৎসের উপর নির্ভরশীল মানুষ প্রকৃত জ্ঞান থেকে বঞ্চিত-যা কিছু মানুষ জানে, তা ভুলভাবে জানে। এই কারণেই বিশ্ব প্রকৃতি সম্পর্কিত জ্ঞান মানুষের পক্ষে যতটা কল্যাণকর হতে পারতো, তা হয়নি। সে জ্ঞান মানুষের মনুষ্যত্বও নানাভাবে ক্ষুণ্ণ ও ব্যাহত করেছে। আল্লাহ ছাড়া বস্তু-জ্ঞান মানুষকে বৈষয়িক সুখ শান্তি অনেক দিয়েছে, কিন্তু এই জ্ঞানই একদিকে মানুষকে যেমন ধ্বংস করার সামগ্রী রচনা করেছে, তেমনি মানুষকে নৈতিকতার দিক দিয়ে চরম শূন্যতার মধ্যে ঠেলে দিয়েছে। এই জ্ঞান মানুষকে বুঝিয়েছে যে, মানুষ অন্যান্য জীব-জন্তুর মতই একটা জীব মাত্র। বস্তুগত সুখ শান্তিই তার একমাত্র কাম্য। আর এই বস্তুগত জীবন ভিন্ন আর এমন কোন জীবন নেই মানুষের, যেখানে তার কারো নিকট জবাবদিহি করতে হতে পারে। কিন্তু এই ধারণা যেমন নিছক ইন্দ্রিয়লব্ধ, তেমনি ‘বস্তর’ সর্বাধুনিক বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের দৃষ্টিতে একান্তভাবে ভুল। আধুনিক বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব নাস্তিক্যবাদকে সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন প্রমাণ করে এবং এই সত্য অনস্বীকার্যভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছে যে, বিশ্বলোকের অন্তরালে এর মহত্ত্ব স্রষ্টার অস্তিত্ব অপরিহার্য। তা ব্যতিরেকে যিনি এই বিশ্বলোকের অস্তিত্ব অসম্ভব। সেই সৃষ্টিকর্তা যিনি সব কিছুর নিয়ামক, তেমনি সমস্ত বিষয়ে নির্ভুল জ্ঞানের উৎসও একমাত্র তিনি। মানুষের জীবন এক অবিভাজ্য ইউনিট! জীবনের যত দিক ও যত বিভাগ রয়েছে তা সবই এক অবিভাজ্য এককের অংশ হিসাবে সমান গুরুত্ব সহকারে ও পূর্ণ ভারসাম্য রক্ষা করে যাপন করতে হবে। মানুষ বস্তু ও রূহের সমন্বয়ে গঠিত; অতএব তার যে বস্তুগত চাহিদা আছে, তেমনি আছে রূহ বা আত্মার চাহিদা, যা পূরণ করতে হয় আল্লাহর বিশ্বাস, ধর্ম বিশ্বাস ও পরকাল বিশ্বাস এবং তদনুযায়ী কাজের মাধ্যমে। কিন্তু মানব সংস্থার উপর আসল কর্তৃত্ব হচ্ছে রূহ বা আত্মার। তারই আত্মার দাবী পূরণ এবং এই দাবী পূরণ সাথে সামঞ্জস্য রক্ষা করেই তার দেহের চাহিদা পূরণ করতে হবে। আত্মা ও দেহের চাহিদা পূরণে যেমন সামঞ্জস্য রক্ষা করা প্রয়োজন, তেমনি আবশ্যক ভারসাম্য রক্ষা করাও। দু’য়ের মধ্যে বৈপরীত্য বা দ্বন্দু মানব জীবনের জন্য মারাত্মক। তাই শিক্ষা ব্যবস্থাকে হতে হবে ইহকালীন কল্যাণ ও পরকালীন কল্যাণ সমন্বিত। পরকালের কথা ভুলে গিয়ে তার প্রতি উপেক্ষা দেখিয়ে যে শিক্ষা ব্যবস্থা রচিত, তা মানুষের সার্বিক ও অবিতক জীবনের কল্যাণের নিয়ামক হতে পারে না। কুরআনের শিক্ষা হচ্ছেঃ
رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ .
কেননা দেহ ভিন্ন আত্মা এই জগতে অবাস্তব। আর আত্মাবিহীন দেহ মৃত লাশ ছাড়া আর কিছুই নয়। কাজেই মানুষকে এমন জ্ঞান শিখাতে হবে, যার ফলে সে দেহ এবং আত্মার, অন্য কথায় ইহকালের ও পরকালের দাবী একই সঙ্গে পূর্ণ সামঞ্জস্য ও ভারসাম্য রক্ষা করে পূরণ করতে সক্ষম হবে। অতএব আল্লাহ্, তাঁর দেয়া দ্বীন ও পরকালীন কল্যাণের উপায় যেমন তাকে জানতে হবে, তেমনিভাবে জানতে হবে আল্লাহর দেওয়া দ্রব্য-সামগ্রীর গুণাবলী ও ব্যবহার পদ্ধতি, যেন মানুষের বৈষয়িক জীবন সামগ্রিকভাবে নির্ভুল পথে ও সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের সাথে অতিবাহিত হতে পারে।
মানুষ এই দুনিয়ায় একাকী জন্ম গ্রহণ করতে পারেনি, একাকী বেঁচে থাকাও তার পক্ষে সম্ভবপর নয়। এ কারণেই মানুষকে বলা হয়েছে সামাজিক জীব। মানুষের এই সামাজিক জীবন শুরু হয় তার জন্ম মুহূর্ত থেকেই। কেননা পিতার ঔরসে ও মায়ের গর্ভে তার জন্ম। এই পিতা ও মাতার দাম্পত্য জীবন সূচিত হয় শরীআত সম্মত বিবাহ ও সমাজের সমর্থনের মাধ্যমে। জন্ম লাভের পর তাকে বেঁচে থাকতে, লালিত পালিত ও ক্রমশঃ বড় হয়ে উঠতে হয় পিতার আশ্রয়ে, মায়ের কোলে; ভাই-বোন, চাচা-চাচী, ফুফা-ফুফু ও দাদা-দাদীর পরিবেষ্টনে। এখানেই মানুষের পারিবারিক ও সামষ্টিক জীবন যাপনের প্রশিক্ষণ সূচিত হয়। অতএব একদিকে পিতা-মাতার হক তাকে জানতে হবে, সেই সংগে জানতে হবে অন্যান্য নিকট ও দূরের আত্মীয়-স্বজনের অধিকার এবং তাঁদের প্রতি তার কর্তব্যের কথা।
এ হচ্ছে মানুষের সামাজিক জীবনের প্রথম ধাপ। এরই মধ্যে মানুষের সামাজিকতা সীমাবদ্ধ নয়। তা তার স্থানীয় জনতা ও যে দেশে সে বাস করে, সেই দেশের বিপুল জনতার মধ্যে সম্প্রসারিত। মানুষের জীবনের বহু গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারই এই বিপুল জনতা সমন্বিত, বৃহত্তর সমাজের সাথে গভীরভাবে সম্পৃক্ত। এই সামাজিকতার সাথে জড়িত রয়েছে মানুষের রাজনৈতিক জীবন।
মানুষ যে রাষ্ট্রের প্রশাসনে নিরাপদ জীবন যাপন করে, তা এই সামাজিকতার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্র ব্যবস্থার সাহায্যেই পাওয়া সম্ভবপর। মানুষ যে অর্থনৈতিক পরিমণ্ডলে স্বীয় বৈষয়িক সুখ-সুবিধা, আয়েস-আরাম ও প্রগতি লাভ করে, তা একদিকে যেমন এই বৃহত্তর সামাজিকতার প্রতিষ্ঠিত অর্থ-ব্যবস্থা থেকে পায়, তেমনি সেই অর্থ-ব্যবস্থা এই রাষ্ট্র ব্যবস্থা কর্তৃকই নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত। তাই মানুষকে জানতে হবে বৃহত্তর সমাজের সাথে তার কি সম্পর্ক, তার উপর তার কি অধিকার এবং তার কি কর্তব্য ও দায়িত্ব। অনুরূপভাবে তাকে জানতে হবে, কোন ধরনের রাষ্ট্রনীতি ও অর্থনীতি তাকে ব্যক্তি স্বাধীনতা ও অর্থনৈতিক নিরাপত্তার সুষ্ঠু ও নির্ভরযোগ্য ব্যবস্থা দিতে সক্ষম। কেননা দুনিয়ায় এমন রাষ্ট্র ব্যবস্থা রয়েছে যা ব্যক্তি মানুষ তথা সমষ্টিকে নিতান্ত গোলাম বানিয়ে রেখেছে- পরিণত করেছে কল্যাণহীন পশুতে, কিংবা বাকহীন জন্তুতে। সাধারণ মানুষকে কথা বলার, মত প্রকাশ করার ও ভালমন্দ বিচার করে সরকার কর্তৃপক্ষের সমালোচনা করার কোন অধিকারই দেয় না। এই রাষ্ট্র-ব্যবস্থা মানুষের মনুষ্যত্বের পক্ষে খুবই অপমানকর। দুনিয়ায় এমন অর্থ-ব্যবস্থা রয়েছে যা সম্পদের উপর ব্যক্তির নীতিভিত্তিক অধিকার স্বীকার করে না। সমাজ সমষ্টির দোহাই দিয়ে মানুষের সব কিছু কেড়ে নেয়। তার মানবিক স্বতন্ত্র সত্ত্বাকেও অস্বীকার করে। মানুষ সেখানে নিজের জন্য অর্থোপার্জনের কোন পন্থা নিজেই বাছাই করে অবলম্বন করতে পারে না। অর্থ ও রাষ্ট্র এই উভয় শক্তিরই একচ্ছত্র অধিপতি হয়ে বসে মুষ্টিমেয় ক্ষমতাসীনরা। তারা দেশের সমস্ত মানুষকে এমনভাবে দমিয়ে রাখে এবং নিয়ন্ত্রণ করে, যেন তারা বিরাট একটা যন্ত্রের অংশ মাত্র; কিংবা নির্জীব কাঁচামাল বিশেষ। এরূপ অর্থ ব্যবস্থায় মানুষ মনুষ্যত্ব হারিয়ে ফেলে নিতান্ত জীব ও জন্তুতে পরিণত হয়। কাজেই মানুষকে এই বিশ্বপ্রকৃতির বুকে তার জন্য ঘোষিত মর্যাদার দৃষ্টিতে স্রষ্টা ও সৃষ্টি এবং তার সংগে মানুষের সঠিক সম্পর্ক রক্ষা করে সুষ্ঠু বৈষয়িক জীবন সম্পর্কিত যাবতীয় বিষয়ে সঠিক জ্ঞানার্জন এবং ব্যক্তি ও সামষ্টিক জীবনে সেই জ্ঞানে বাস্তব অনুশীলন সম্পর্কে নির্ভুল জ্ঞান লাভ করতে হবে।
যে শিক্ষাব্যবস্থা এই সব দিক দিয়ে মানুষকে সুশিক্ষিত ও সৎকর্মশীল বানাতে পারে, মানুষের জন্য কেবলমাত্র সে শিক্ষাব্যবস্থাই সর্বাত্মক কল্যাণ বয়ে আনতে পারে। আর এই শিক্ষা ব্যবস্থা হতে পারে কেবলমাত্র তা-ই, যা আল্লাহর অবতীর্ণ কিতাব কুরআন মজীদের সার্বিক দর্শনের ভিত্তিতে রচিত।
বড়ই দুঃখের বিষয়, সাধারণভাবে সারা বিশ্ব সমাজে ও বিশেষভাবে সারা মুসলিম জাহানে এই কুরআন ভিত্তিক সার্বিক শিক্ষা ব্যবস্থা বর্তমানে চালু নেই। সারা দুনিয়ায় বর্তমানে যে শিক্ষা ব্যবস্থা প্রচলিত ও কার্যকর, তা থেকে মানুষ নিজেকে, নিজের স্রষ্টাকে, স্রষ্টার অশেষ অবদানকে এবং তাঁর সাথে মানুষের সম্পর্ককে নির্ভুলভাবে চিনতে পারে না, নিজের উপরোক্ত সার্বিক দায়িত্ব ও কর্তব্যের কথাও জানতে পারে না। সে জানতে পারে শুধু এতটুকু যে, মানুষ সাধারণ জীব জন্তু থেকে ভিন্নতর কিছুই নয়। জানতে পারে, কিভাবে কি উপায়ে ও পদ্ধতিতে এই বিশ্বের পরতে নিহিত উপকরণাদি নিঃশেষে নিংড়িয়ে নিয়ে নিজের জৈব সুখ-সম্ভোগের আয়োজন করা সম্ভব। কিন্তু এই জানা মানুষের উপযোগী জানা নয়। এই জানা কেবলমাত্র জীব-জন্তুর জন্যই শোভন। বর্তমান মুসলিম জাহানের প্রধান কর্তব্য ছিল কেবলমাত্র কুরআন ভিত্তিক সর্বাত্মক শিক্ষা ব্যবস্থা ব্যাপকভাবে ও সর্বস্তরে চালু করা। কিন্তু মুসলমানরাও এই শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পূর্ণতঃ বা অংশতঃ পরিহার করে আল্লাহ্-হীন ব্যক্তিদের রচিত ও তাদের কর্তৃক সারা দুনিয়ায় প্রচলিত শিক্ষা-ব্যবস্থাকেই অনুসরণ করে চলেছে। ফলে তার বংশধররা মুসলিম হিসাবে গড়ে উঠতে পারছে না। মুসলিম পরিবারের ঈমানদার ও চরিত্রবান ছেলে-মেয়েরাও এ শিক্ষা অর্জন করে একই সাথে ঈমান ও চরিত্র উভয়ই হারিয়ে ফেলে। এর ফলে ভবিষ্যতে ‘মুসলিম জাতি’ দুনিয়ায় বেঁচে থাকবে কি না, তার আশংকা এখন তীব্র হয়ে দেখা দিয়েছে। আল্লামা ইকবাল বলেছেন:
به اهل کلیس کا نظام کے نظام ایک سازش هی فقط دین و فطرت کے خلاف
মানুষের মন নিষ্পন্দ বা অনুভূতিহীন দর্পণ নয়। দর্পণে প্রতি মুহূর্তের পরিবর্তনশীল অবস্থা, অনুভূতি ও প্রকৃতির রঙ-বেরঙের বহিঃপ্রকাশ যথাযথভাবে প্রতিবিম্বিত হয়। কিন্তু মানুষের মন সেরূপ নয়। মানব মন কখনই নিষ্ক্রিয় থাকে না। তা সচেতন ও সক্রিয়ভাবে বিভিন্ন ভাবধারা ও উপাদান সংমিশ্রিত অবস্থা ও ঘটনাবলীর একটা বিশেষ প্রতিক্রিয়া গ্রহণ করে।
এখন প্রশ্ন এই যে, আনন্দের চেয়ে এর অবস্থাসমূহের এই প্রতিবিম্ব ও প্রকৃতির চিত্র কি স্বতঃই গড়ে উঠতে থাকে এবং চেতনা নিজ থেকেই কি তাতে যেমন ইচ্ছা রঙ লাগায়, কিংবা চেতনা তার এই সুসজ্জিত ও অলঙ্কৃত হওয়ার জন্যে বাইরের প্রেরণার মুখাপেক্ষী? দুনিয়ার বিশেষজ্ঞদের নিকট একথা স্পষ্ট যে, নিছক চেতনার নিজস্বভাবে এ ধরনের কোন শক্তি বা ক্ষমতা নেই। মানব মন প্রভৃত শক্তি ও প্রতিভার উৎস, সন্দেহ নেই। যাচাই, বাছাই, ছাঁটাই, গ্রহণ ও বর্জন, সুবিন্যস্তকরণ ও রূপায়নের বিপুল শক্তি নিহিত রয়েছে মানুষের মনে। তার হৃদয়ানুভূতিকে যতই objective বলা হোক এবং বিভিন্ন অবস্থা, ঘটনাবলী ও পর্যবেক্ষণ থেকে যে ফল গ্রহণ করেছে, তা তার পটভূমির প্রতিচ্ছায়া থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত ও সুরক্ষিত বলে যত দাবীই করা হোক না কেন, সে দাবী নিরর্থক অহমিকা ও অন্তঃসারশূন্য আত্মম্ভরিতা ছাড়া আর কিছুই না-তা বলাই বাহুল্য।
কোন জীবন্ত সত্ত্বা মহাশূন্যে শ্বাস গ্রহণ করতে পারে না, এ যেমন সত্য, অনুরূপভাবে এ-ও সত্য যে, মানুষের মন আদর্শিক শূন্যতার মধ্যে কাজ করতে পারে না; বিশ্বাস ও প্রত্যয় হচ্ছে তার একমাত্র অবলম্বন। তারই সাহায্যে তাকে অগ্রসর হতে হয় জ্ঞানান্বেষণের বিশাল বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রে। যেসব সুধী নিজেদের চিন্তা-গবেষণার objective-এর উপর গৌরববোধ করেন এবং যাঁরা দাবী করেন যে, তাঁরা আরোহী চিন্তা পদ্ধতি (Deductive)-এর আদিকারের পন্থা পরিত্যাগ করে অবরোহী চিন্তা পদ্ধতির (Inductive) বিজ্ঞান সম্মত পন্থা অবলম্বন করেছেন, তাঁদের জ্ঞান তথ্য ও গবেষণা লব্ধ ফল গভীর সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে অধ্যয়ন ও বিচার-বিশ্লেষণ করা হলে নিঃসন্দেহে জানা যায় যে, তাঁরাও হৃদয়ের মণিকোঠায় প্রচ্ছন্ন বিশ্বাস ও প্রত্যয়ের দীপ জ্বালিয়েই পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণের বিশাল অসীম প্রান্তরে পদক্ষেপ গ্রহণের দুঃসাহস করেছেন- এ এমন এক মহা সত্য, দুনিয়ার বড় বড় চিন্তাবিদরাও তা মেনে নিতে একান্তভাবে বাধ্য। এই পর্যায়ে John Gaird লিখিত ‘An introduction to Philosophy of Religion’ গ্রন্থ থেকে একটি অংশ উদ্ধৃত করা যেতে পারে। তিনি বলেছেন-
‘চিন্তা-গবেষণার প্রতিটি পদক্ষেপে আমাদের মনের নিভৃত গহীনে প্রচ্ছন্ন ধারণাসমূহ থেকেই পথ নির্দেশ লাভ করতে হয়। কেননা আমরা যা কিছুর সন্ধান করি, তার মূল্য ও গুরুত্ব সে সব ধারণা-বিশ্বাসের নিক্তিতে ওযন করেই অনুমান করা যায়। আর সে সব ধারণা রচিত মানদণ্ডে সে সবের সত্যতা যথার্থতা পরীক্ষা ও যাচাই করা সম্ভব হতে পারে। কোন চিন্তা গবেষণাই নিজস্ব ধারণা-বিশ্বাস ও উদ্দেশ্য লক্ষ্য থেকে বিচ্ছিন্ন, নিঃসম্পর্ক ও নিরপেক্ষ হয়ে পরিচালিত করা কারো পক্ষে সম্ভবপর নয়। নিজের ছায়া থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া যেমন কোন মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়, তেমনি চিন্তা–গবেষণার ফল গ্রহণ করাও কারুর সাধ্য নেই।‘
প্রখ্যাত গ্রন্থ প্রণেতা Bevan তাঁর ‘Symbolism of Belief’ গ্রন্থে এ ধরনের মনোভাব প্রকাশ করে লিখেছেন-
‘আমরা শুধুমাত্র বাস্তবতার মধ্যে জড়িয়ে পড়ে থাকতে পারিনি। আমরা যখন কোন বাস্তব জীবনের দিকে পদক্ষেপ গ্রহণ করি, তখন আমরা আমাদের কর্ম ক্ষমতা ও তৎপরতার যাচাই করার জন্য আমাদের নিজস্ব মৌল ধারণাও বিশ্বাসসমূহের দিকে প্রত্যাবর্তন করতে বাধ্য হই।’
বস্তুতঃ এ এমন একটা সত্য, যার স্বপক্ষে বহু প্রখ্যাত চিন্তাবিদের সমর্থন উদ্ধৃত করা যেতে পারে। এ থেকেই এ সত্য অতি সহজেই উপলব্ধি করা যেতে পারে যে, মূলতঃ অবস্থা ও ঘটনাবলীর সুসংবদ্ধ অধ্যয়নই হচ্ছে শিক্ষা এবং তাকে কোন ব্যক্তি ও জাতির মৌল চিন্তা ও মতাদর্শ থেকে কোন অবস্থায়ই বিচ্ছিন্ন করা যেতে পারে না। এই কারণেই মৌল বিশ্বাসের দিক দিয়ে মানুষে মানুষে যে পার্থক্য ধর্মবিশ্বাসের পার্থক্যের দরুন, তাকে স্বীকার করেই বিভিন্ন বিশ্বাস অনুসারীদের শিক্ষাও বিভিন্ন হতে বাধ্য। এ সত্যকে অস্বীকার করা হলে সম্পূর্ণ অবৈজ্ঞানিক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে এবং তার জন্য বিভিন্ন মৌল বিশ্বাস সম্পন্ন মানুষের অপূরণীয় ক্ষতি সাধিত হবে।
জ্ঞান-বিজ্ঞানের জগতে অন্যান্য সব রকমের জ্ঞান শাখাকে বাদ দিয়ে কেবল জীব-বিজ্ঞান, প্রকৃতি বিজ্ঞান, পদার্থ বিজ্ঞান ও ইতিহাস সম্পর্কেই বলা যেতে পারে, এগুলোর objectivity সম্পর্কে অনেক দাবী উত্থাপন করা হয়েছে। উল্লেখ করা যেতে পারে, ডারউইনের ক্রমবিকাশবাদ বিজ্ঞানীদের নিকট সর্ব সমর্থিত মহাসত্য বলে গৃহীত। কিন্তু সকল প্রকার বিদ্বেষ, হৃদয়াবেগ ও আসক্তি আবিলতা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হয়ে অধ্যয়ন করলে নিঃসন্দেহে প্রতীয়মান হবে যে, এই মতটি সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ পর্যবেক্ষণের ফল নয়। এর অনেকগুলো ধারাই ইউরোপীয়দের নিজস্ব অন্ধ বিশ্বাস ও কুসংস্কার প্রসূত। ধর্মবিমুখ ইউরোপীয়রা একবার যখন নিজেদের মনন মগজে এই ধারণা বদ্ধমূল করে নিয়েছে যে, এই বিশ্বলোক স্বয়ম্ভূ, এর স্রষ্টা কেউ নেই; এই জগত একটি ধরাবাঁধা ও শাশ্বত নিয়মের অধীন, স্বতঃই চলমান ও প্রবহমান, তার পরিচালকও কেউ নেই; এই ক্রমবৃদ্ধি, ইচ্ছামূলক গতিশীলতা, অনুভূতি, চেতনা, মনমানসিক উন্মেষ ও স্বজ্ঞা-সব কিছু বস্তুরই উন্নতিলব্ধ বিশেষত্ব, তখন ক্রমবিকাশ সংক্রান্ত ডারউইনী মতবাদ তাদের নিকট হারানো স্বর্গের পুনঃপ্রাপ্তিরূপে বিবেচিত না হওয়ার কোন কারণই থাকতে পারে না। কেননা এই মতবাদেই তারা বিশ্বলোক সম্পর্কিত তাদের বিশেষ ধারণা ও দৃষ্টিকোণের বাস্তব ব্যাখ্যা পেয়ে গেছে। বহু প্রখ্যাত বিজ্ঞানী-ই এই সত্যকে অকপটে স্বীকার করেছেন। এখানে মাত্র একজন বিজ্ঞানীর মত-ই উদ্ধৃতি করা যথেষ্ট হবে।
Arnold luna তাঁর ‘Revolt Against Reason’ গ্রন্থে (১৬৭ পৃ.) উদ্ধৃত করেছেন,
‘ডারউইনবাদ বিজ্ঞান নয়। তা একটি পুরোপুরি ধর্ম-মত, তাতে যুক্তিসংগত সুসংবদ্ধতার দাবী যতই করা হোক না কেন।’
আর মানুষের নিজেদের রচিত এই ধর্মমতে যুক্তি প্রমাণের তুলনায় অন্ধ বিশ্বাস ও ভাবাবেগ অধিক প্রবল হয়ে রয়েছে।
শিক্ষা সম্পর্কে একটি ধারণা হচ্ছে, তা মানুষের অন্তর্নিহিত শক্তিসমূহের বিকাশ সাধন। সূক্ষ্ম, সুকোমল হৃদয়াবেগ পরিমার্জিত করণের উদ্দেশ্যেই তা অর্জন করতে হবে। কিন্তু অধুনা এই ধারণা নিতান্তই পুরাতন এবং অনেক কাল আগের বলে বিবেচিত। আধুনিক কালের প্রবণতা হল, শিক্ষাকে ব্যবহারোপযোগী বানাতে হবে, ব্যবহারিক মূল্যের দৃষ্টিতে যা অধিক মূল্যবান, এমন শিক্ষা অর্জনই হবে লক্ষ্য। শিক্ষার আলোয় হৃদয়লোক উজ্জ্বল-উদ্ভাসিত ও জ্ঞান সমৃদ্ধ করে তোলা আজ আর লক্ষ্য রূপে নির্দিষ্ট থাকেনি। অথচ আজকের দুনিয়ায়ও আমাদের সর্বাধিক প্রয়োজন হচ্ছে এমন শিক্ষা ব্যবস্থার, যা আমাদের মনকে সর্বপ্রকার রোগ থেকে মুক্ত করবে, মানসিক রোগের জীবাণু বিনষ্ট করে দেবে, মানবতার সকল দুঃখ দুর্দশা, বঞ্চনা ও শোষণ-লুণ্ঠন বন্ধ করে দেবে। আর মানবীয় প্রয়োজন পূরণার্থে প্রাকৃতিক উপায়-উপকরণ পূর্ণ মাত্রায় প্রয়োগ; ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার জন্য প্রয়োজনীয় খোরাক পোশাক- বাসস্থানের ও তার ইনসাফপূর্ণ বন্টনের ব্যবস্থা করার প্রাকৃতিক বিপর্যয়-বন্যা প্লাবনের মাত্রা ক্রমাগত হ্রাস ও সীমাবদ্ধ রাখার এবং সকল শ্রেণীর মানুষের জন্য সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও আনন্দ স্ফূর্তি সম্পন্ন অবস্থা সৃষ্টি করার যোগ্য হবে। এগুলো একান্তই জরুরী। যে শিক্ষার মাধ্যমে একাজ সম্ভব, তা যে মানবতার পক্ষে খুবই কল্যাণকর, তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু একটু গভীর চিন্তা বিবেচনা করলে যে কেউই এ সিদ্ধান্তে পৌছতে বাধ্য হবেন যে, মানব প্রকৃতি নিহিত কাম-ক্রোধ-লোভ-মোহ, মাৎসর্য ইত্যাদি স্বভাবজাত প্রবণতা সমূহের কল্যাণময় ও ভারসাম্যপূর্ণ চরিতার্থতাই তা সম্ভব করে দেবে। এর কোন একটিকেও নির্মূল করার প্রবণতা কারুর মধ্যেই জাগবে না। উচ্চতর শিক্ষার চরম লক্ষ্য যদি শুধু এতটুকুই হয়, তাহলে এ উচ্চ শিক্ষা তার আসল তাৎপর্য হারিয়ে ফেলবে। ইতিহাস প্রমাণ করেছে, মানবীয় উন্নতি বিধানে যারা উপস্থিত তাৎক্ষণিক ও দ্রুত সুফল লাভের উদ্দেশ্যে শ্রম করেছে, তাদের তুলনায় যারা জ্ঞানার্জনের জন্য নিজেদের সম্পূর্ণরূপে সমর্পিত করে দিয়েছে, তারা অধিক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনে সক্ষম হয়েছে; এদের সংখ্যা যতই কম হোক না-কেন। কাজেই পূর্বোক্ত ধরনের শিক্ষাই মানুষের কাম্য। আর তা কেবলমাত্র আল্লাহর নিকট থেকে পাওয়া জ্ঞান-উৎস কুরআন ও সুন্নাহ্ থেকেই পাওয়া সম্ভব।
কিন্তু বাস্তব অবস্থা এই যে, মানুষের, জ্ঞান-পরিধি যতই বৃদ্ধি পাচ্ছে, মানুষের সমস্যা ততই জটিল হতে জটিলতর হতে যাচ্ছে। মানুষ বস্তুগত অগ্রগতি যত বেশী লাভ করছে, নিত্য নতুন কামনা-বাসনা, নতুন নতুন সমস্যা অনেক জটিলতা ও অনেক নৈরাশ্য বঞ্চনার হাহাকার নিয়ে মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার ক্ষেত্রে এ উন্নীত ধ্বংস ও বরবাদীর এমন সব হাতিয়ার উদ্ভাবনের দ্বার উন্মুক্ত করে দিয়েছে, যার দরুন মানবতার অস্তিত্বই কঠিন হুমকির সম্মুখীন হয়ে পড়েছে। এটা যে কত বড় বিয়োগান্ত ব্যাপার, তা বলে শেষ করা যায় না। পরন্ত একদিকে মানুষ মানবীয় সুখ-শান্তি ও সমৃদ্ধি বিধানের চেষ্টায় নিয়োজিত, অপরদিকে মানুষ অত্যন্ত তীব্র গতিতে ভিত্তিহীন ধারণা বিশ্বাসে ও কুসংস্কারের সহজ শিকারে পরিণত হচ্ছে। ফলে মানুষ এক স্থায়ী অশান্তি, দুঃখ ও মানসিক যন্ত্রণায় জর্জরিত হয়ে পড়েছে। আমরা যত তীব্রতা ও আন্তরিকতার সাথে বিশ্ব-প্রকৃতিকে জয় করতে শুরু করেছি, তা আমাদের একথা প্রায় ভুলিয়েই দিয়েছে যে, আসলে আমরা কোমল দেহ ও কামনা- বাসনারই অধিকারী নই, ‘আত্মা’ বলতেও একটি জিনিস আমাদের রয়েছে। দেহের জীবন এবং ক্রমবৃদ্ধির জন্যে যেমন খাদ্য অপরিহার্য, মনের পরিশুদ্ধি ও পরিচ্ছন্নতা বিধানের জন্য যেমন প্রয়োজন শিক্ষার, তেমনি আত্মার উন্নতি সাধনের জন্য দরকার ঈমানের। আর ঈমান হচ্ছে কতকগুলো মৌল সত্যের প্রতি স্বতঃস্ফূর্ত প্রত্যয়, যে প্রত্যয় শত প্রতিকূল ঝঞ্ঝা, বাত্যার আঘাতে বিন্দুমাত্র চূর্ণ বা দুর্বল হবে না। এই ঈমান বিনষ্ট হওয়া কঠিনতম দৈহিক রোগ অপেক্ষা অধিক মারাত্মক ও বিপজ্জনক। প্রাচীন মানুষের ইতিহাস বিশেষজ্ঞগণ একথা মেনে নিতে আমাদের বাধ্য করেন যে, বহুসংখ্যক প্রাচীন জাতি ও গোত্র কেবলমাত্র এই জন্যই; ধ্বংস ও পৃথিবীর বুক থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে যে, তারা তাদের নিজস্ব জীবন পদ্ধতির প্রতি ঈমান ও প্রত্যয় হারিয়ে ফেলেছিল। ইতিহাসের এ এমন এক শিক্ষা, যা কোন সময়ই এবং কারোই ভুলে যাওয়া উচিত নয়। এরূপ ঐতিহাসিক ভুলের পুনরাবৃত্তি সংঘটিত হওয়া প্রত্যেকটি জাতির জন্যই অবাঞ্ছনীয়। আমাদের ব্যক্তি ও জাতীয় সত্তার স্থিতি আমাদের কাম্য হলে মূল মানবীয় মূল্যবান ও মূল্যবোধের উপর নিজেদের প্রত্যয়কে পুনরুজ্জীবিত ও দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। যে শিক্ষা শুধু আমাদের দেহ ও বৈষয়িক জীবন রক্ষা ও উন্নতি বিধানের পন্থা প্রদর্শন করে ও উপায়-উপকরণ সংগ্রহের প্রযুক্তি শিখায়, কেবলমাত্র মানসিক উৎকর্ষই যার একমাত্র অবদান, সে শিক্ষা আমাদের জন্য কল্যাণকর হতে পারে না। জাতীয় শিক্ষাকে আমাদের একান্ত নিজস্ব মানবীয় মূল্যমানের প্রতি ঈমানদার বানাতে হবে। কেননা কেবল ঈমানই আমাদের আত্মাকে সুস্থ, সবল, স্বচ্ছ ও সফল করতে সক্ষম।
বর্তমান আমরা এক নবতর সামগ্রিক ব্যবস্থার রূপায়নে ব্যতিব্যস্ত। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, এ সামগ্রিক ব্যবস্থা শেষ পর্যন্ত কি রূপ পরিগ্রহ করবে? এ প্রশ্নের জবাব এই যে, আমরা আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধরদের মধ্যে কোন সব মূল্যমান ও মূল্যবোধের চেতনা জাগাতে চাই, তার-ই উপর আমাদের বর্তমান সামগ্রিক ব্যবস্থার রূপ-ঐশ্বর্য একান্তভাবে নির্ভরশীল। আমরা কি ধরনের মানুষ তৈরী করছি, তার-ই উপর শিক্ষার দিক দিয়ে আমাদের ভবিষ্যৎ জাতীয় লক্ষ্য ও জাতীয় ভবিষ্যত নির্ভর করে। আমাদের সামাজিক সংহতি, সামাজিক সুবিচার ও ন্যায়পরায়ণতা এবং ব্যক্তির পরম সাফল্য ও সার্থকতাই হচ্ছে আমাদের জাতীয় লক্ষ্য। আমরা চাই সকল প্রকার দুর্নীতি, শোষণ ও চরিত্রহীনতা মুক্ত এক আদর্শ সমাজ গড়তে-এমন এক সমাজ গড়তে, যেখানে মানুষে মানুষে হিংসা-বিদ্বেষ, হানাহানি, মারামারি, লুটতরাজ ইত্যাদি অমানবিক ও অসামাজিক আচার-আচরণ থাকবে না; যেখানে মানুষ তার মানবিক মর্যাদা ও অধিকার পেয়ে সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ জীবন যাপন করতে সক্ষম হবে। এ লক্ষ্য অর্জনের পথে অগ্রসর হতে হলে আমাদের প্রাথমিক শিক্ষা থেকে শুরু করে বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ শিক্ষাস্তর পর্যন্ত এমন এক পাঠ্য ও শিক্ষা প্রশিক্ষণ সূচি রচনা করতে হবে, যা শুধু ভাল ভাল জ্ঞান তথ্য দিয়েই শিক্ষার্থীদের মন-মগজ ভরে দেবে না; বরং সেই সংগে আমাদের বালক-বালিকা, তরুণ-তরুণীদের দেবে বিশ্বলোক, জীবন ও সমাজ সম্পর্কে সুস্থ, সঠিক ও নির্ভুল চিন্তা বিশ্বাস ও সুস্পষ্ট স্বচ্ছ দৃষ্টিকোণ, সুদৃঢ় সিদ্ধান্ত গ্রহণ ক্ষমতা, কঠোর শ্রমশীলতা ও সুসংগঠিত বিশ্বস্ততার গুণাবলী। তা এমন সব উচ্চতর মানবীয় মূল্যমানের নির্ভুল চেতনা জাগিয়ে দেবে যা শুধু ব্যক্তির আশা-আকাঙক্ষাই চরিতার্থ করবে না, ব্যাপকভাবে জাতীয় আশা-আকাঙক্ষারও বাস্তব রূপায়নের নিয়ামক হবে।
একমাত্র আল্লাহ্ ও তাঁর সর্বশেষ রাসূল (সা)-এর প্রতি আমাদের যে ঈমান, তাই হচ্ছে আমাদের ব্যক্তি ও জাতীয় উন্নতি বিধানের মৌল কেন্দ্র বিন্দু। এ কথা আজ নতুন করে উপলব্ধি করলেও সিদ্ধান্তরূপে গ্রহণ করতে হবে। এ কেন্দ্রবিন্দুকে উপেক্ষা করে যে শিক্ষা ও সংস্কৃতি রচিত, তা আল্লাহ্, রাসূল তথা ইসলামে বিশ্বাসীদের পক্ষে কোনক্রমেই গ্রহণযোগ্য হতে পারে না এবং তার দ্বারা আদর্শ ও সুনাগরিক গড়ে তোলা সম্ভব হতে পারে না।
ব্যক্তির মন মানসিকতা ও মেধার উৎকর্ষ বিধানের উদ্দেশ্যে শুধু অনুশীলন ও চর্চার নামই শিক্ষা নয়। শিক্ষার উদ্দেশ্যও নয় তা। শিক্ষার উদ্দেশ্য ব্যক্তির নিজ সত্তার সংকীর্ণ পরিধির মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। তার চতুষ্পার্শ্বে বসবাসকারী বিপুল জনতা ও তার পরিবেশ সম্পর্কে নির্ভুল জ্ঞানার্জনও তার একটা দায়িত্ব। ব্যক্তি কোন জনসমষ্টি বা জাতির অংশ হয়েই বাঁচতে পারে। সমাজ ও সমষ্টি থেকে বিচ্ছিন্ন ব্যক্তির অস্তিত্ব কল্পনাতীত। যে শিক্ষা ব্যক্তিকে প্রত্যয় ও আদর্শবাদের দিক দিয়ে তার বংশ, পরিবার ও সমাজ পরিবেশ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়, তা শিক্ষা নামে অভিহিত হওয়ার অযোগ্য। তা নিছক বন্যতা, বর্বরতা ও পশুত্ব মাত্র। প্রতিষ্ঠিত সমাজ-সমষ্টির ভিত্তিমূল চূর্ণ বা শিথিল করে যে শিক্ষা, তাকে শিক্ষা না বলে ‘ডিনামাইট’ বলাই যথার্থ। ব্যক্তিকে সমাজ সমষ্টির একজন উত্তম সদস্যরূপে গড়ে তুলতে হলে জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাকে অবশ্যই জাতীয় মতাদর্শ, ঈমান-বিশ্বাস এবং ঐতিহ্য ও ইতিহাসের প্রতিবিম্ব করে গড়ে তুলতে হবে।
আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থা একটি শিল্পোন্নত সমাজ ও জাতির প্রয়োজন পূরণ উদ্দেশ্যে রচিত। সে শিক্ষায় বৈষয়িক জীবন সত্ত্বার স্থিতি, সুখ-সম্ভোগ ও চাকচিক্যই সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। আর তার মূলে দ্বন্দ্ব, সংগ্রাম ও অপরের উপর প্রাধান্য (Survial of the fittest) লাভের ভাবধারা উৎকন্ঠভাবে নিহিত। কিন্তু এতদঞ্চলের চিন্তাবিদগণ তা কখনও পছন্দ করেননি। ইউরোপ থেকে আমদানী করা জিনিসের প্রতি প্রথম দৃষ্টিতে আকর্ষণ জেগে উঠলেও, তার চাকচিক্য চোখকে ঝলসিয়ে দিলেও এবং প্রথম দিক দিয়ে মানবমনে একটা উৎকট মাদকতার সৃষ্টি করে থাকলেও এতদ্দেশীয় চিন্তাশীলদের ও সমাজদরদীদের ভুল ভাঙতে কিছুমাত্র বিলম্ব হয়নি। ইংরেজদের তৈরী শিক্ষা ব্যবস্থার মারাত্মক বিষক্রিয়া সম্পর্কে সজাগ হতে অন্ততঃ মুসলমানদের খুব বেশী সময় লাগেনি। কবি রবীন্দ্রনাথ পাশ্চাত্য বিজ্ঞান ও সংস্কৃতির সমর্থক হয়েও স্পষ্ট অনুভব করেছিলেন যে, এ শিক্ষা ব্যবস্থা এতদ্দেশীয় পরিবেশের সাথে সম্পর্কহীন। তাই পাশ্চাত্য নিয়ম নীতির প্রতি দাস উপযোগী মনোভাব গ্রহণ যারা আকন্ঠ বিষপান তুল্য মনে করতে হবে। শিক্ষা যাদের জন্য, শিক্ষাকে তাদেরই ঈমান, বিশ্বাস, মন-মানসিকতা, মূল্যমান-মূল্যবোধ, সৌন্দর্যবোধ ও রুচি, সামাজিক ও আধ্যাত্মিক জীবনের সহিত পুরাপুরি সম্পৃক্ত ও সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে। অতএব শিক্ষা তাই গ্রহণযোগ্য, যা নিজেদের দীন ও ঈমান এবং সভ্যতা-সংস্কৃতির সংগে আধুনিক বিজ্ঞানের সর্বশেষ তথ্য ও মূলনীতিসমূহের সমন্বিত ভাবধারার ভিত্তিতে রচিত।
শিক্ষার মৌল লক্ষ্য ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের বিকাশ ও সমৃদ্ধি সাধন। যে ব্যক্তি তার সমাজ সংস্থা থেকে বিচ্ছিন্ন, সে কিছুই নয়। ব্যক্তি কেবল তখনই প্রকৃত অস্তিত্বের অধিকারী হতে পারে, যখন সে সমাজ-সমষ্টির উদ্দেশ্যাবলীকে নিজের মধ্যে রূপায়িত করে তুলবে এবং নিজের সত্তা দিয়ে তার বাস্তব রূপায়ণ ও প্রকাশ ঘটাবে। এইজন্য ব্যক্তির মনমানসিকতাকে সামষ্টিক ও সামগ্রিক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণে সমুদ্ভাসিত করে তুলতে হবে। যে সব মতাদর্শ ও দৃষ্টিকোণ ব্যক্তি ও সমষ্টির দৃষ্টিতে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ, তা শিক্ষার্থীর মনে ও চরিত্র কতটা প্রতিফলিত হয়েছে, তার মূল্যায়ন করে জানা যেতে পারে শিক্ষা ও শিক্ষা ব্যবস্থা তার ক্ষেত্রে কতটা সাফল্য লাভ করেছে। বৈষয়িক জীবনে কে কতটা সাফলতা লাভ করেছে, কিংবা কে কতটা উচ্চতর চাকরি লাভ করতে ও কত বেশী অর্থোপার্জন সক্ষম হয়েছে, তা কোন ব্যবস্থারই সফলতা প্রমাণের মানদণ্ড হতে পারে না। যেমন এরূপ দৃষ্টিভংগি পশুজগতেই সম্ভব-মানব জগতে নয়। অতএব ইসলামী শিক্ষা দর্শনের মূল লক্ষ্য হলো, আধুনিক কালের উপযোগী যাবতীয় জ্ঞান বিজ্ঞান সমৃদ্ধ ও পুরাপুরি ইসলামী আদর্শবাদী নাগরিক, সমাজ ও রাষ্ট্র এবং সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে পূর্ণভাবে গড়ে তোলা। অন্য ভাষায় বলতে গেলে বলা যায়, ইসলামের শিক্ষাদর্শনের দৃষ্টিতে শিক্ষার চরম লক্ষ্য হলো ব্যক্তি ও সমষ্টির মধ্যে আল্লাহর প্রেম ও ভালোবাসা এবং আল্লাহর আনুগত্যের প্রবল ভাবধারা জাগ্রত করে তোলা। এ পর্যায়ে বার্ট্রান্ড রাসেলের কথাটি যথার্থ। তিনি বলেছেন-
“ইসলাম শুরু থেকেই এক রাজনৈতিক ধর্মমত। আমরা বলব, ইসলাম পূর্ণাংগ দ্বীন। জীবনের সমগ্র দিক ও বিভাগের উপর তার প্রভাব বর্তমান থাকা অপরিহার্য। ব্যক্তিগতভাবে তারা হবে উন্নত গুণসম্পন্ন মানুষ, আদর্শবাদী মানুষ, জন দরদী ও সার্বিক কল্যাণকামী মানুষ এবং ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্রের উপযুক্ত নাগরিক।”