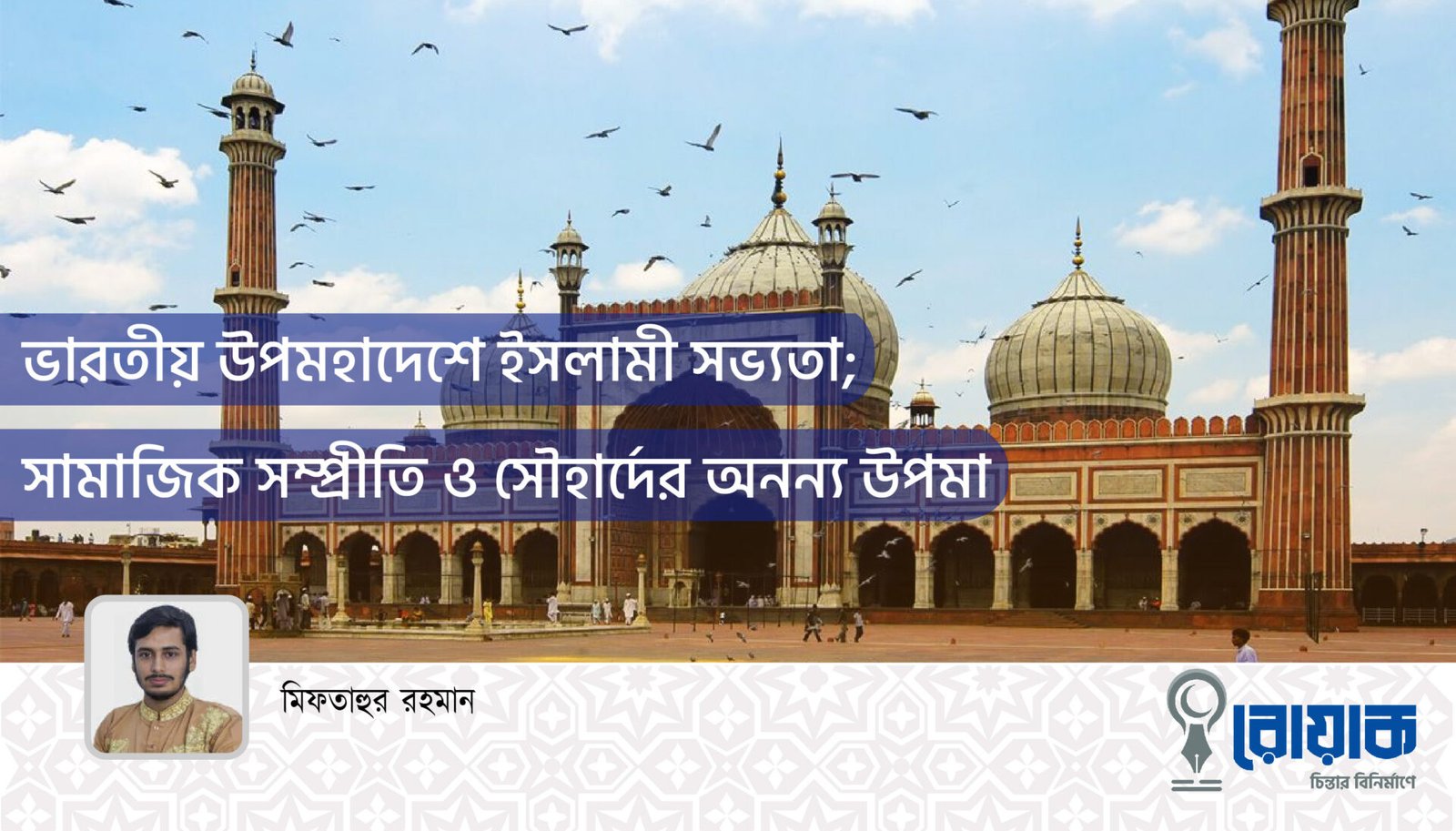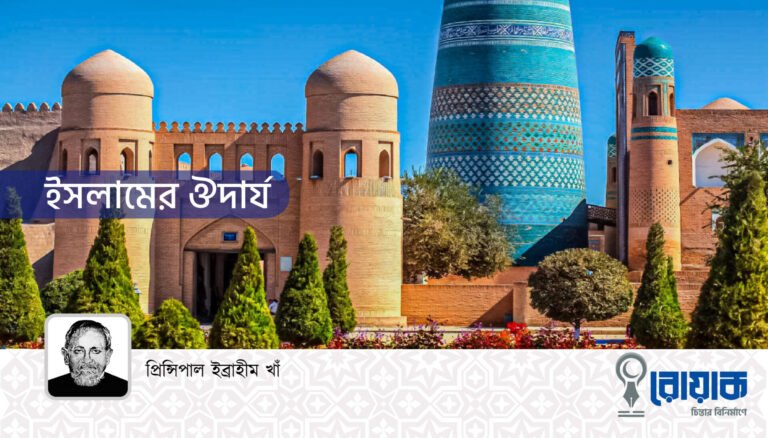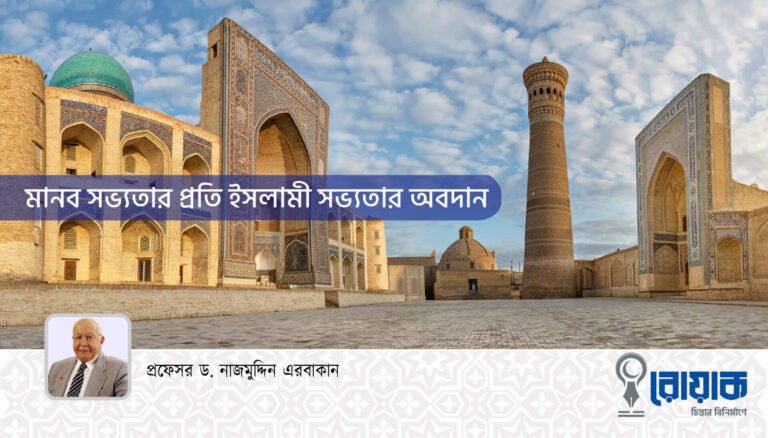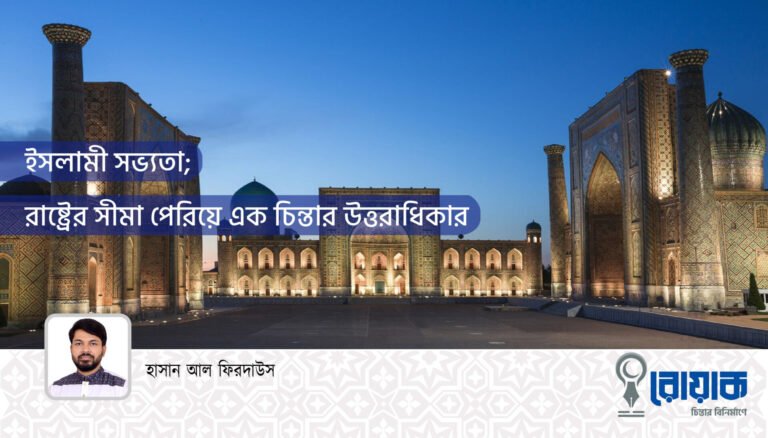এক
ইতিহাস, সমাজ, সভ্যতা, সংস্কৃতি—আমাদের সবচেয়ে সুপরিচিত কয়েকটি পরিভাষা। সমগ্র মানবেতিহাসকে সংজ্ঞায়ন করা পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত এসব শব্দাবলি আজ ভিন্ন অর্থ প্রদানে সিদ্ধহস্ত। কারণ অনুসন্ধানে সর্বাগ্রে যে বিষয়টি আমাদের সামনে লক্ষ্যণীয় হয়ে ওঠে, তা হলো প্যারাডাইম ওয়ার বা পারিভাষিক যুদ্ধ। পৃথিবীর ইতিহাসে একটা সময় যখন এসব শব্দসমূহ সামগ্রিকতাকে পরিমণ্ডল করে ব্যাপৃত হতো, সেসব শব্দগুলোর প্রতিটিই আজ নির্দিষ্ট কিছু শোষকগোষ্ঠীর স্বার্থান্বেষণের প্রধান উপকরণ হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে।
নির্দিষ্ট কিছু শোষকগোষ্ঠী বলতে যে শোষণ ও স্বার্থপরতার বিষবাষ্প নিঃসরণকারী মানবতার এক পরম শত্রু এবং সেকিউলারিজমের নামে রব বা সৃষ্টিকর্তাবিহীন তথাকথিত আধুনিক পরজীবী পাশ্চাত্য সভ্যতা-কে বুঝানো হচ্ছে, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। কোনো সভ্যতায় যদি লিবারেলিজমের জনক জন লক, বিবর্তনবাদের জনক চার্লস ডারউইন, আখলাক বিবর্জিত মনস্তত্ত্বের জনক সিগমুণ্ড ফ্রয়েড-সহ ফ্রান্সিস বেকন, রেনে দেকার্তে, থমাস হবস, ইমানুয়েল কান্ট, বার্ট্রান্ড রাসেল-এর মতো দার্শনিকদের মৌলিক ভিত্তি রোপিত থাকে—যারা দর্শন চর্চার নামে মূলত মানবজাতির রূহ থেকে মানবতা, নৈতিকতা, আখলাক, মারহামাত, আদালত দূরীকরণে সর্বদা ব্যতিব্যস্ত ছিলো—তাহলে বলতে দ্বিধা হওয়া উচিত নয় যে, এমন একটি সভ্যতার নিকট থেকে মানবতা আশা করা সত্যিকারার্থেই অমাবস্যার রজনীতে চন্দ্রালোক খোঁজার মতোই ব্যর্থ প্রচেষ্টার নামান্তর।
উল্লেখ্য, এখানে অনেকে হয়তো আক্ষরিক অর্থের দৃষ্টিকোণে ক্যাপিটালিজম এবং সোশালিজম ও তার আপডেট ভার্সন কমিউনিজম-এর মাঝে মরিচীকা-সদৃশ কিছু তফাত পেয়ে তাদের মধ্যকার বিস্তর ফারাক প্রমাণের প্রচেষ্টায় নত হবেন, তবে বাস্তবিকপক্ষে জায়োনিজম, লেবারেলিজম, ডায়ালেকটিজম, ক্যাপিটালিজম, সোশালিজম ও কমিউনিজম—সহ এমন সকল ইজম (ism) আসলে একই মুদ্রার এপিঠ ওপিঠ। মূলত, মানবজাতিকে নিকৃষ্টতর পদ্ধতিতে শোষণ করার নিমিত্তে সময়ে সময়ে তারা মুদ্রার পৃষ্ঠতল পরিবর্তন করে থাকে, এব্যতীত আর অন্যকিছু নয়।
মানবসভ্যতার শোষক স্বার্থান্বেষী পশ্চিমা দার্শনিকদের অন্যতম একজন হলেন রেনে দেকার্তে। দেকার্তিয়ান/কার্তেসিয়ান ফিলোসফি বা রেনে দেকার্তের দর্শনসমূহের প্রথম রূলস ছিলো, “I think, therefore I am” অর্থাৎ, “আমি চিন্তা করতে পারি, তাই আমার অস্তিত্ব রয়েছে”, যা তিনি ১৬৩৭ সালে তাঁর গ্রন্থ “Discourse on the Method”-এ তুলে ধরেছিলেন। অর্থাৎ, তারা যতটুকু চিন্তা করে বা তারা যেভাবে চিন্তা করে, ততটুকুতেই তাদের অবস্থান সীমাবদ্ধ। পরবর্তীতে এই দর্শনটি পশ্চিমাদের দর্শনে পরিণত হয়। ফলশ্রুতিতে, তারা তাদের মতো করেই ইতিহাসের বলয় তৈরি করে। এই দর্শনটি যেহেতু সমগ্র পশ্চিমের মৌলিক দর্শনে রূপ লাভ করেছিলো, সেহেতু তাদের অতীত ইতিহাস লিপিবদ্ধের ক্ষেত্রে এই বিষয়টি গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিলো। এমনকি, তাদের স্বার্থোদ্ধারের জন্য সম্পূর্ণ বানোয়াট ও বিকৃত ইতিহাস লেখতেও তারা কুণ্ঠাবোধ করেনি।
এসবের উদাহরণ পাওয়া যায় তাদের ইতিহাস চর্চায়। ইতিহাসের পর্যায়ক্রম বা সময়কাল বর্ণনার ক্ষেত্রে তারা তাদের সময়কালকে নিজেদের মতো করে তৈরি করে নিয়েছে। তাদের পর্যায়কালকে যদি সহজভাবে উত্থাপন করা যায়, তাহলে বিষয়টা এমন হয় যে,
- ০১. প্রাগৈতিহাসিক যুগ,
- ০২. ঐতিহাসিক যুগ,
- ০৩. ভবিষ্যৎ যুগ।
এখানে, প্রাগৈতিহাসিক যুগ বলতে সহজ ভাষায় মানবজাতির পূর্ববর্তী যুগ বা ডাইনোসর যুগকে বোঝানো হয়। মানবজাতির ইতিহাস বর্ণনা করতে গিয়ে তারা ঐতিহাসিক যুগকে তিনভাগে আবার ভাগ করে। অর্থাৎ,
- ০১. প্রাচীন যুগ,
- ০২. মধ্য যুগ,
- ০৩. আধুনিক যুগ।
এসবের মধ্যে প্রাচীন যুগকে তারা আবার তিনভাগে ভাগ করেছে। যথা,
- ০১. প্রস্তর যুগ,
- ০২. ব্রোঞ্জ যুগ,
- ০৩. লৌহ যুগ।
এরপর, তাদের ইতিহাস অনুযায়ী মধ্যযুগের সময়সীমা ছিলো তথাকথিত ইউরোপীয় রেনেসাঁ পর্যন্ত। অথচ, তারা কাদের নিকট থেকে কীভাবে সভ্য হতে শুরু করলো, তা তারা বরাবরই লুকিয়ে রাখে। যে মধ্যযুগকে তারা অন্ধকার যুগ বলে অভিহিত করে থাকে, সে অন্ধকার যুগ থেকেই তারা কোন পরশ পাথরের স্পর্শে রেনেসাঁ বা পুনর্জাগরণ ঘটালো, সে বর্ণনার ক্ষেত্রেও তারা ছলচাতুরীর আশ্রয় নিয়ে থাকে। সে যাইহোক, তাদের তথাকথিত রেনেসাঁ-র পর থেকে তারা নিজেদেরকে দুনিয়াব্যাপী সভ্য বলে পরিচিত করতে থাকে। “প্রথমবার কীভাবে সম্পদ অর্জিত হয়, তা ধর্তব্য নয়, বরং সেসব সম্পদকে তখন সংরক্ষণ করা দায়িত্ব ও কর্তব্য হয়ে পড়ে”—দার্শনিক জন লক-এর এমন দর্শন ইউরোপীয়দের আরো স্বেচ্ছাচারী ও নৃশংস বানিয়ে ফেলে। মানবজাতিকে সভ্য বানানোর বুলি আওড়িয়ে সমগ্র বিশ্বব্যাপী তারা সাম্রাজ্যবাদ প্রতিষ্ঠা করে বর্ণনাতীত যে শোষণ ও নিষ্পেষণ চালিয়েছে, তা আজ আর কারও অজানা নয়।
এই হলো তাদের ইতিহাস বর্ণনার পন্থা। কিন্তু, এর বিপরীতে গিয়ে তাদেরই কথিত অন্ধকার মধ্যযুগের সময় ইসলামী সভ্যতা মানবেতিহাসের পাতায় যে ইতিহাস রচনা করেছে; সুদীর্ঘকালব্যাপী আদালত, মারহামাত ও আখলাকের সাথে যে সমগ্র বিশ্ব পরিচালনা করেছে এবং ইসলামী সভ্যতার দর্শনসমূহ যে উপমা উপস্থাপন করেছে, তা পশ্চিমাদের স্বার্থাভিলাষের মূলে কুঠারাঘাত করে। ফলশ্রুতিতে, আমাদের যে সময়কে গোল্ডেন এজ বা স্বর্ণালী সময় বলা হয়, সেসময়কে তারা অন্ধকার যুগ বলে অভিহিত করে থাকে।
শুধু এতোটুকুতেই শেষ নয়, আমরা মুসলিম উম্মাহ যেনো পুনরায় ঘুরে দাড়াতে না পারি, সে লক্ষ্যকে সামনে রেখে তারা “এন্ড অব দ্যা হিস্টোরি” বা “ইতিহাস ও পৃথিবীর শেষ সময়” বিষয়টি নিয়ে পর্যন্ত অসংখ্য পুস্তক রচনা করেছে। অথচ, রাসূল (সা.) এর হাদীস থেকে স্পষ্ট বর্ণনা পাই যে, আমরা যদি জেনেও থাকি, আগামীকাল কেয়ামত সংঘটিত হবে, তবুও যেনো আমরা গাছ রোপণ করতে পিছপা না হই। এখানে, গাছ রোপণের বিষয়টি এসেছে মূলত রূপকার্থে; এর দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে, মানবজাতির জন্য সকল ধরনের কল্যাণকর কাজ জারি রাখা।
মহান রবের একজন খলিফা হিসেবে পৃথিবী বিনির্মাণ মুসলিম উম্মাহর প্রত্যেকের দায়িত্ব ও কর্তব্য; এবং আমরা তা বাস্তবায়ন করে এসেছি সুদীর্ঘ বারোশত বছরেরও বেশি সময় ধরে। মূলত, তাদের শোষণের ধারা বজায় রাখতে এবং আমাদের এই বিশ্বজনীন ও সামগ্রিক চিন্তাধারার বিরোধিতা করতে গিয়েই তারা “এন্ড অব দ্যা হিস্টোরি” বা “ইতিহাস ও পৃথিবীর শেষ সময়” মতবাদের উত্থান করেছে। আবার, এটাও অস্বীকার করার জো নেই যে, এই বিষয়টি থেকেই মূলত আমাদের মুসলিম উম্মাহর ভেতরে “কেয়ামত নিকটবর্তী”-এর মতো অহেতুক, অপ্রয়োজনীয় ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী একটি তত্ত্বের বিকাশ ঘটেছে; যা সরাসরি রাসূল (সা.)-এর হাদীস পরিপন্থী একটা চিন্তাধারা।
অতএব এটা সুস্পষ্ট হয়ে গেলো যে, পশ্চিমাদের দর্শন ও তাদের ইতিহাসের সাথে আমাদের দর্শন ও ইতিহাস চর্চার মাঝে রয়েছে বিস্তর ফারাক। সেহেতু, আমাদেরকে পশুসমতুল্য করা পশ্চিমাদের উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বিদ্বেষপূর্ণ ইতিহাস চর্চা থেকে বিরত থেকে মনোযোগী হতে হবে আমাদেরই রেফারেন্স, তথ্যসূত্র ও পুস্তকাদির দিকে। মোটাদাগে বলে যায়, আমাদের ইতিহাস চর্চার ক্ষেত্রে থাকতে হবে সদা-সতর্ক। আমাদের শাসন ব্যবস্থার ত্রুটিগুলো বিশাল কলেবরে উপস্থাপন করে আদিল ও ন্যয়পরায়ণ শাসকদেরকে তারা যে নিকৃষ্টতর করে উপস্থাপন করে থাকে, সেদিকে আমাদের যথেষ্ট খেয়াল রাখতে হবে। এমনকি, ক্ষেত্রবিশেষে এটাও আমাদের বিশেষ নজরে রাখতে হবে যে, আমাদের ইতিহাস নিয়ে তাদের প্রশংসামূলক পর্যালোচনার পেছনেও থাকতে পারে অন্যকোনো দুরভিসন্ধি; উদাহরণস্বরূপ ওরিয়েন্টালিজম বা প্রাচ্যবাদ-এর কথাও ধর্তব্য হতে পারে।
এই বিষয়টিকে কেন্দ্রে রেখেই এবার একটু ভারতীয় উপমহাদেশের দিকে নজর দেওয়া যাক।
দুই
ভারতীয় উপমহাদেশ। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, ভূতাত্ত্বিক বৈচিত্র এবং সাংস্কৃতিক নান্দনিকতায় পরিপূর্ণ স্রষ্টার বিশেষ মহিমাধন্য অপার এক লীলাভূমি। মহান রব যেনো এই অঞ্চল এবং তার মানুষের উপর নিজ হাতে রহমত প্রেরণ করেছেন; প্রকৃতিগত বিচিত্রতা, উর্বর ভূমি এবং জনসাধারণের কর্মঠ মানসিকতা-র মাধ্যমে এই অঞ্চলকে নেয়ামতে পরিপূর্ণ করেছেন। ফলশ্রুতিতে, সেই প্রাচীন কাল থেকেই এই অঞ্চলের উপর শ্রেষ্ঠ সব বিজেতাদের নজর পড়েছিলো। অতএব, এটাও সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, বিশ্ব মানচিত্র অঙ্কনের সূচনা থেকেই এই অঞ্চলটি তার ব্যতিক্রমী প্রভাব প্রস্ফুটিত করতে থাকে।
ইতিহাস থেকে জানা যায়, প্রস্তর যুগে খ্রিস্টপূর্ব ৭০-৫০ হাজার বছর পূর্বে আফ্রিকা থেকে ভারতে মানবজাতির আগমন ঘটে। এরপর ১২ হাজার বছর পূর্বে ফার্টাইল ক্রিসেন্ট বা সুফলাচন্দ্রিকা নামক একটি অঞ্চলে কৃষির উন্নতির প্রমাণ পাওয়া যায়। এরপর থেকে কৃষি ক্রমান্বয়ে উন্নত হতে থাকে। এই সময়টায় ইরানের ওদিক থেকে বিশাল জনগোষ্ঠী ভারতের এদিকে অভিবাসন করে। ভারতের স্থানীয় অধিবাসী ও অভিবাসন করে আসা জনগোষ্ঠীর মিশ্রণে যে জাতির উদ্ভব হয়, তাদের হাতেই গড়ে ওঠে সুবিশাল হরোপ্পা মহেঞ্জোদারো-র বিখ্যাত সেই সিন্ধু সভ্যতা। সময়টা ছিলো তখন ব্রোঞ্জ যুগ।
সিন্ধু সভ্যতার পরবর্তীতে যে যুগ শুরু হয়, তা হলো বৈদিক যুগ। বৈদিক যুগ মূলত ব্রোঞ্জ যুগকে অতিক্রম করে লৌহ যুগের প্রায় মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত চলমান ছিলো। বৈদিক যুগের পরে যথাক্রমে জনপদ, পুরু জাতি, কুরু সাম্রাজ্য, ষোড়শ মহাজনপদ, নন্দ সাম্রাজ্য ও মৌর্য্য বংশ এই অঞ্চল শাসন করেছিলো। পরবর্তীতে যারা ভারত শাসন করে, তারা হলো যথাক্রমে— শুঙ্গ রাজবংশ, সাতবাহানা সাম্রাজ্য, কুষাণ সাম্রাজ্য, গুপ্ত সাম্রাজ্য, কামরূপ সাম্রাজ্য, পল্লব রাজবংশ, কদম্ব রাজবংশ, চালুক্য রাজবংশ, রাষ্ট্রকূট রাজবংশ এবং পাল সাম্রাজ্য।
এখানে উল্লেখ্য যে, পরবর্তীতে যেসব রাজবংশ বা সাম্রাজ্যের নাম উল্লেখ করা হলো, তারা যে সমগ্র ভারতের মূল শাসক ছিলো, বিষয়টা মোটেও তেমন না। বরং, সমগ্র ভারত তখন বিশাল বিশাল সব বিভিন্ন অঙ্গরাজ্য নিয়ে গঠিত ছিলো, সেহেতু পরবর্তীতে উল্লেখ করা রাজবংশ বা সাম্রাজ্যগুলো বলতে গেলে একই সময়েই তারা তাদের অঞ্চলগুলো শাসন করেছে। আর এসবের সমাপ্তি ঘটতে শুরু করে ত্রয়োদশ শতকের একেবারে উষালগ্নে, অর্থাৎ, মুসলমান কর্তৃক দিল্লি সালতানাত প্রতিষ্ঠার পর থেকে। সূচনা হয় তখন ভারত ইতিহাসে নতুন এক অধ্যায়, ভারতবাসী উপলব্ধি করতে শুরু করে জীবনের প্রকৃত সংজ্ঞা এবং অবলোকন করতে শুরু করে সমগ্র ভারতজুড়ে একই শাসকের শাসন।
ভারতে মুসলিম শাসনকে দুইভাগে বিভক্ত করা যায়। যথা,
- ০১. সুলতানী আমল (১২০৬-১৫২৬),
- ০২. মুঘল আমল (১৫২৬-১৭৫৭)।
সুলতানী আমলকে দিল্লি সালতানাত নামেও ডাকা হয়ে থাকে। এই সময় মুসলিমদের বিপরীতে যে শক্তিশালী সাম্রাজ্য টিকে ছিলো, সেটি হলো দক্ষিণ ভারতের বিজয়নগর সাম্রাজ্য। দিল্লি সালতানাত বা সুলতানী আমলে কয়েকটি রাজবংশ ভারতকে কেন্দ্রীয়ভাবে শাসন করতে শুরু করে। তারা হলো,
- ০১. মামলুক রাজবংশ (১২০৬-১২৯০),
- ০২. খিলজী রাজবংশ (১২৯০-১৩২০),
- ০৩. তুঘলক রাজবংশ (১৩২০-১৪১৪),
- ০৪. সৈয়দ রাজবংশ (১৪১৪-১৪৫১),
- ০৫. লোদী রাজবংশ (১৪৫১-১৫২৬)।
দিল্লি সালতানাত বা সুলতানী আমলের পরে ভারতের কেন্দ্রীয় শাসনভার গ্রহণ করে মুঘলরা। লোদী বংশের শেষ সুলতান ইব্রাহিম লোদীকে পরাজিত করে মুঘল শাসনের সূচনা করেন ভারতের ইতিহাসে সর্বপ্রথম কামান ব্যবহারকারী মুঘল সালতানাতের প্রথম শাসক সম্রাট জহিরুদ্দিন মুহাম্মাদ বাবর। এই সময় মুঘলদের বিপরীতে যে শক্তিশালী সাম্রাজ্য টিকে ছিলো, সেটি হলো মারাঠা সাম্রাজ্য।
এখানে গুরুত্বপূর্ণ যে বিষয়টি আসবে, তা হলো, ১২০৬ সালে যে মুসলিমরা দিল্লি সালতানাতের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় শাসনের পুনঃসূচনা করে বটে, তবে এসবের ভিত্তিপ্রস্তর কিন্তু একদিনে স্থাপিত হয়নি, বরং এর পেছনে রয়েছে প্রায় কয়েকশত বছরের দীর্ঘ ইতিহাস। বিগত পাঁচ শতাব্দী যাবত এই শাসনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়েছিলো। এই সময়ের ইতিহাসকে তিনটি ভাগে বা তিনটি পর্যায়ে বিভক্ত করা হয়। অর্থাৎ, ভারতীয় উপমহাদেশে মুসলিম অভিযানের প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পর্যায়।
প্রথম পর্যায় শুরু হয় ৭১২ সালে তরুণ বিজেতা মুহাম্মাদ বিন কাসেম-এর সিন্ধু ও মুলতান বিজয়ের মাধ্যমে। এই বিজয়ের পর থেকে ভারতবর্ষে মুসলিমরা গ্রামাঞ্চল থেকে শুরু করে রাষ্ট্রীর পর্যায় পর্যন্ত প্রভাব বিস্তার করতে শুরু করে। জনসাধারণও ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হতে থাকে এবং ইসলাম রাষ্ট্রীয়ভাবেই সমগ্র ভারতবর্ষজুড়ে পরিচিত হতে শুরু করে।
এই ধারাবাহিকতায় হাওয়া লাগে দ্বিতীয় পর্যায়ে এসে, অর্থাৎ, দশম শতাব্দীর শেষ এবং একাদশ শতাব্দীর শুরুতে সুলতান মাহমুদ গজনভীর ভারত অভিযানের মাধ্যমে। তিনি একাধারে সতেরোবার ভারত অভিযান পরিচালনা করেছেন। তিনি ছিলেন মূলত ইরানের গজনভী বংশের শাসক। তিনি তাঁর অঞ্চলে যে প্রায় ত্রিশ বছর যাবত শাসন করেছিলেন, তা ছিলো ভারতের তৎকালীন স্বর্ণালী সময়। বিখ্যাত ব্যক্তিত্ব আবু রায়হান আল-বেরুনী ছিলেন সুলতান মাহমুদের দরবারের অন্যতম একজন সদস্য, যিনি সর্বপ্রথম প্রাচ্যের জ্ঞানবিজ্ঞান, বিশেষ করে ভারতের জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতি মুসলিম মনীষীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। এছাড়াও সুলতান মাহমুদের সাথে সখ্যতা ছিলো মহাকবি ফেরদৌসীর, যার শাহনামা এখনও বিশ্বসাহিত্যে অমর হয়ে আছে। উল্লেখ্য যে, শাহনামা নিয়ে সুলতান মাহমুদের বিষয়ে যা ছড়ানো হয়, তার সুস্পষ্ট কোনো দলিল বা ভিত্তি নেই।
এরপর, তৃতীয় পর্যায়ে এসে চিরস্থায়ীভাবে ভারতে মুসলিম শাসনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হয়, যার শুরুটা হয় মুইযুদ্দীন মুহাম্মাদ ঘুরীর ভারত অভিযানের কল্যাণে। ১১৭৫ সালে মুলতান বিজয়, ১১৭৮ সালে আনহিলওয়ারা বিজয়, ১১৮২ সালে সিন্ধু বিজয় এবং ১১৮৬ সালে ত্বরাইনের প্রথম যুদ্ধে পরাজয় বরণ করলেও ১১৯২ সালে ত্বরাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধে বিজয়ার্জনের মাধ্যমে ভারতে ঘুরী রাজবংশ নিজেদের শক্তিমত্তার অস্তিত্বের জানান দেয়। প্রথমবারের মতো ভারতবর্ষে শুরু হয় মুসলিমদের চিরস্থায়ী শাসনের উপমা নিদর্শন। এরপর তিনি মৃত্যুবরণ করলেই তাঁর একজন চৌকস সেনাপতি কুুতুবউদ্দিন আইবেক-এর হাতেই স্থাপিত হয় দিল্লি সালতানাতের ভিত্তিপ্রস্তর। দিল্লি সালতানাতের সময় যে যে রাজবংশ ভারতবর্ষকে কেন্দ্রীয়ভাবে শাসন করতে শুরু করে, তাদের নাম তো পূর্বে উল্লেখিত হয়েছেই।
দিল্লি সালতানাতের পর শুরু হয় মুঘল আমল। মুঘল আমলের ছয়জন শাসক সবচেয়ে পরিচিত। যথাক্রমে তাঁরা হলেন,
- ০১. জহিরুদ্দিন মুহাম্মাদ বাবর (১৫২৬-১৫৩০),
- ০২. নাসিরুদ্দীন মুহাম্মাদ হুমায়ুন ১৫৩০-১৫৪০, ১৫৫৫-৫৬),
- ০৩. জালালুদ্দিন মুহাম্মাদ আকবর (১৫৫৬-১৬০৫),
- ০৪. নূরুদ্দুন মুহাম্মাদ জাহাঙ্গীর (১৬০৫-১৬২৭),
- ০৫. শিহাবুদ্দিন মুহাম্মাদ শাহজাহান (১৬২৭-১৬৫৮),
- ০৬. মুহিউদ্দিন মুহাম্মাদ আওরঙ্গজেব আলমগীর (১৬৫৮-১৭০৭)।
তাঁদের মাঝে সম্রাট আকবর এবং আলমগীর—দু’জন মিলেই শাসন করেছেন শতবছরেরও বেশি সময় ধরে। এরপর, ১৭৫৭ সালে পলাশীর আম্রকাননে শুধু বাংলার নয়, বরং সমগ্র ভারতবর্ষের স্বাধীনতার সূর্য অস্তমিত হয়, যা অদ্যাবধি উদিত হয়নি।
যেকোনো অঞ্চলের ইতিহাসেরই উত্থান-পতন থাকে, থাকে সে সময়ের সফলতা ও উন্নতির সর্বোচ্চ চূড়া। সে হিসেবে মুসলিম শাসনামাল বলা হোক বা ভারতের সমগ্র ইতিহাসই ধরা হোক—উভয়ক্ষেত্রেই মুঘল আমলই ছিলো ভারতবর্ষের সফলতা ও উন্নতির সর্বোচ্চ চূড়া। আখলাক, আদালত ও মারহামাতে পরিপূর্ণ একটি সমাজ তুলে ধরেছিলো সামাজিক সম্প্রীতি ও সৌহার্দ-এর অনন্য উপমা, যা হতভম্ব করে দিয়েছিলো সমগ্র ভারতবাসীকে।
তবে এখানে বলে রাখা ভালো যে, মুসলিম শাসনামল যে একেবারে “ধোয়া তুলসী পাতা” বা শতভাগ নিখুঁত ছিলো, তা কোনো মুসলিম ইতিহাসবেত্তা-ই স্বীকার করেন না। এমনকি, আদালত ও আখলাকবিহীন কাজকর্মের জন্য তারাই সর্বপ্রথম শাসক বা অপরাধীদের সমালোচনা করেছেন। কিন্তু, প্রতিটি রাজবংশ বা শাসকের সময়ের এসব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়গুলোকে উদ্দেশ্যমূলকভাবে ফুলে ফেঁপে তুলে ইতিহাস বর্ণনা করেছে ইংরেজ ইতিহাসবীদ ও তাদের দোসর ব্রাহ্মণ্যবাদীরা। এমনকি, আমরা মুসলিমরাও এখন আমাদেরই ইতিহাস অধ্যয়ন করি ইংরেজ ও ব্রাহ্মণ্যবাদী ইতিহাস লেখকদের তথ্যসূত্রকে কেন্দ্রে রেখে। ফলশ্রুতিতে, বর্তমান ভারতে মুঘল শাসকগণ আজ নেতিবাচকভাবে পরিচিত হয়ে আসছে দীর্ঘ দেড়-দুইশত বছর যাবত। অথচ, প্রকৃত ইতিহাস বলে সম্পূর্ণ ভিন্ন কথা।
এবার তাহলে সে ইতিহাসের দিকেই একটু নজর বুলানো যাক।
তিন
একেবারে শুরুতেই “ইতিহাস, সমাজ, সভ্যতা, সংস্কৃতি”—চারটি পরিভাষার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। ইতিহাস বর্ণনা করা হয় সমাজ, সভ্যতা ও সংস্কৃতি-র। অন্যদিকে, সমাজ ও সংস্কৃতি একে অপরের অবিচ্ছেদ্য একটা অংশ, একটা ব্যতিত আরেকটা অসম্পূর্ণ। আবার এ’দুয়ে মিলে হয় সভ্যতা, আর সর্বশেষে এই সভ্যতারই ইতিহাস বর্ণনা করা হয়। অতএব, এটা অস্বীকার করার জো নেই যে, এসব পরিভাষা একে অপরের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। যেহেতু এসবের মাঝে রয়েছে গভীর সম্পৃক্ততা, সেহেতু সামাজিক সম্প্রীতি ও সৌহার্দের বিষয়টি এলে অবশ্যই অন্য বিষয়গুলোও অবধারিতভাবে চলে আসবে।
ইতোপূর্বে মুসলিম শাসনামলের সময়কালটা সংক্ষেপে তুলে ধরা হয়েছে। সে হিসেবে বলা যায়, সভ্যতার ইতিহাসের কিঞ্চিৎ ফুটে উঠেছে এখানে। কিন্তু, ইতিহাস তো শুধু এভাবে বর্ণনা করলে হয় না, সমাজ ও সংস্কৃতির বিষয়টিও ফুটিয়ে তুলতে হয়। অতএব, সামাজিক সম্প্রীতি ও সৌহার্দের বিষয়টার প্রতিও আমাদের নজর দেওয়া প্রয়োজন।
সহজ ভাষায় বলা হয়, সামাজিক সম্প্রীতি ও সৌহার্দ হলো, সমাজের সকলে মিলে একত্রে শান্তিতে বসবাস বা সহাবস্থান করা; আমাদের পাঠ্যপুস্তকে সামাজিক সম্প্রীতি ও সৌহার্দ-এর সংজ্ঞায়ন এভাবেই করা হয়। অথচ, শুধুমাত্র সমাজের ভেতরে পাশাপাশি শান্তিতে বসবাস করা বা সহাবস্থান করাই সামাজিক সম্প্রীতি ও সৌহার্দ নয়, বরং ধর্ম, রাজনীতি, অর্থনীতি, সংস্কৃতি, শিক্ষা ও সাহিত্য এবং প্রশাসন ও বিচারব্যবস্থা-সহ “সমাজ”-এর সাথে সম্পৃক্ত প্রতিটি বিষয়ই এখানে অন্তর্ভূক্ত হবে। যদি এসবের প্রতিটিতেই আদালত বিরাজমান থাকে, মূলত তখনই একটি সমাজে প্রকৃত সম্প্রীতি ও সৌহার্দ প্রতিষ্ঠিত হবে।
এখানেই শেষ নয়, একটি সমাজ-সভ্যতার প্রকৃত সম্প্রীতি ও সৌহার্দ-এর ইতিহাস তখনই জানতে ও বুঝতে পারা যায়, যখন সে সমাজ-সভ্যতার ইতিহাসের সাথে পূর্বাপর বা সমসাময়িক অন্যান্য সমাজ-সভ্যতার ইতিহাসের সাথে তুলনা করা হয়, চাই সে সমাজ-সভ্যতা স্থানীয় হোক বা পৃথিবীর যেকোনো প্রান্তের সমাজ-সভ্যতা হোক। তবে এটা সত্য যে, স্থানীয় পূর্বাপর সমাজ-সভ্যতার সাথে তুলনা করলেই বরং তখন পার্থক্যটা আরো বেশি সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। অতএব, ভারতবর্ষের মুসলিম শাসনামল বা সমাজ-সভ্যতার সাথে তার পূর্বাপর সমাজ-সভ্যতার তুলনা করলে মুসলিম সমাজ-সভ্যতার প্রকৃত সামাজিক সম্প্রীতি ও সৌহার্দ-এর নমুনা পাওয়া যাবে।
যেহেতু তুলনামূলক আলোচনাকেই কেন্দ্রে রাখা হচ্ছে, সেহেতু গতানুগতিক সম্প্রীতি-সৌহার্দ এবং আদালতের মধ্যকার পার্থক্য জানাটা সকলের জন্য অতীব গুরুত্বপূর্ণ। বুঝার স্বার্থে আদালতকে বলা যেতে পারে ন্যায় অধিকার এবং গতানুগতিক সম্প্রীতি-সৌহার্দ-কে বলা যেতে পারে সমান অধিকার। সকলের নিকট এটা সুস্পষ্ট হতে হবে যে, ন্যায় অধিকার আর সমান অধিকার কখনও এক বিষয় নয়। ন্যায় অধিকার হলো, যার যতটুকু প্রয়োজন তাকে ততটুকু দেওয়া। বিপরীতে, সমান অধিকার হলো, সবার মাঝে সমবণ্টন করা। সমান অধিকারের সবচেয়ে বড় সমস্যা হচ্ছে, কেউ হয়তো প্রয়োজন অনুপাতেও সম্পদ পায় না আবার কেউ প্রয়োজনের চেয়েও অধিক পায়। কিন্তু, ন্যায় অধিকারে কখনও তা হয় না, সবাই সবার প্রাপ্যটুকুই পায়। তবে ক্ষেত্রবিশেষে সমান অধিকারটা ন্যায় অধিকারের অন্তর্ভূক্ত হয়ে যায়। মুসলিম উম্মাহর নিকট এই ন্যায় অধিকারই হলো আদালত। তবে এটা স্মর্তব্য যে, “আদালত” শব্দটি যতোটা সামগ্রিকতা ও বিস্তৃত অর্থ ধারণ করতে পারে, “ন্যায় অধিকার” শব্দটি কখনও তা পারবে না।
সামাজিক সম্প্রীতি ও সৌহার্দপূর্ণ অবস্থান বলতে যে সামাজিক একটা পরিবেশে শুধুমাত্র সহাবস্থান করাকে বুঝানো হচ্ছে না, তা ইতোপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। অতএব, সমাজ বিষয়টির সাথে সম্পৃক্ত সকল দৃষ্টিকোণকে বিবেচনা করেই যেহেতু সামাজিক সম্প্রীতি ও সৌহার্দ-এর বিষয়টি ফুটে ওঠে, সেহেতু সমাজ-এর সাথে সম্পৃক্ত গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি বিষয় থেকে সামাজিক সম্প্রীতি ও সৌহার্দ-এর উদাহরণ দেখা যাক।
💠ধর্মীয় সম্প্রীতি ও সৌহার্দ
মুসলিম পূর্ব ভারত
ভারতবর্ষে ইসলামী সভ্যতার সবচেয়ে বড় অবদান হলো, ধর্মীয় বৈষম্য বিদূরিত করা। কেননা, ইতিহাসই সাক্ষ্য দেয়, মুসলিম বিজয়ের প্রাক্কালে ভারতের ধর্মীয় অবস্থা অত্যন্ত নৈরাশ্যজনক অবস্থায় ছিলো। তখন ভারতে বৌদ্ধ ধর্ম, জৈন ধর্ম ও হিন্দু ধর্ম প্রচলিত ছিলো। মহাবীর নামে এক ক্ষত্রীয় সন্ন্যাসী ভারতে জৈন ধর্ম প্রবর্তন করেন। গৌতম বুদ্ধ বৌদ্ধ ধর্ম প্রবর্তন করেন, তিনি সিদ্ধার্থ নামেও পরিচিত ছিলেন। মৌর্য সম্রাট মহামতি অশোকের সময় বৌদ্ধ ধর্ম ভারতে ব্যাপক বিস্তার লাভ করে। গুপ্ত শাসনামল থেকে বৌদ্ধ ধর্মের পতন শুরু হয়। এ সময় থেকে ভারতে হিন্দু ধর্মের পুনজাগরণ সূচিত হয়।
প্রাক মুসলিম আমলে ভারতে হিন্দু ধর্মই ছিলো প্রধান ধর্ম। ভারতের বেশিরভাগ রাজাই ছিলেন হিন্দু। তারা হিন্দু ধর্মের পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। সমাজের ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়দের প্রভাব ও প্রতিপত্তি ছিলো সবচেয়ে বেশি। বৈশ্য ও শূদ্ররা নির্যাতিত, নিপীড়িত ও নিষ্পেষিত ছিলো। তাদের ধর্মীয় পুস্তক পাঠ করা এমনকি শোনাও নিষিদ্ধ ছিলো। দুর্নীতিপরায়ণ ব্রাহ্মণরা জনসাধারণের দুর্বলতা ভীতির সুযোগ নিয়ে জীবিকা নির্বাহ করতো। ব্রাহ্মণদের আক্রমণাত্মক মনোভাব বৌদ্ধদের মধ্যে শত্রুতার সৃষ্টি করে। ব্রাহ্মণ কর্তৃক নির্যাতিত বৌদ্ধরা ভারতে আক্রমণ করতে মুসলমানদেরকে আমন্ত্রণ জানায় এবং আরবদেরকে স্বাগত জানায়। এ প্রসঙ্গে প্রখ্যাত ঐতিহাসিক অধ্যাপক হাবীব বলেন, ❝ব্রাহ্মণগণ ইচ্ছাপূর্বক জনগণকে অজ্ঞ করে রাখতেন এবং সমাজে এভাবে তারা নিজেদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করতেন।❞
ড. দীনেশ চন্দ্র সেন বলেন, ❝পণ্ডিত ব্রাহ্মণগণ ক্ষমতায় মদমত্ত হয়ে অত্যাচারীর ভূমিকা গ্রহণ করেছিলো।❞
মুসলিম ভারত
প্রাক মুসলিম আমলে এই ছিলো ভারতের ধর্মীয় সহাবস্থানের নমুনা। বিপরীতে দিল্লির সুলতানি আমলে ধর্মীয় ধ্যান-ধারণা ও বিশ্বাসের ক্ষেত্রে ব্যাপক পরিবর্তন আসে। ভারতের মুসলিম শাসকরা উদার ধর্মীয় নীতি গ্রহণ করেন। মুসলিম শাসনামলে ভারতের হিন্দুরা শান্তিপূর্ণভাবে বসবাস করতো। তাদেরকে দেওয়া হয় ধর্মীয় স্বাধীনতা। ভারতের অমুসলিমরা তাদের নিজ নিজ ধর্ম স্বাধীনভাবে পালন করতে পারতো।
ভারতে প্রাথমিক মুসলিম শাসনের সময় ভারতীয়দের কাছে ইসলাম একেবারে অপরিচিত ছিলো না। কারণ, অষ্টম ও নবম শতাব্দীতে সিন্ধু ও তৎসংলগ্ন অঞ্চলে ইসলাম ধর্মের আগমন ঘটে এবং ভারতে বৌদ্ধ রীতি-নীতি ধ্যান-ধারণার প্রভাবে সুফিবাদের উন্মেষ ঘটে। ইসলামের একেশ্বরবাদ ও সুফিদের প্রেম এবং ভক্তির মাধ্যমে ঈশ্বরকে লাভ করার তত্ত্ব ভারতীয় সমাজজীবনকে আলোড়িত করে তোলে। যার ফলে ভারতে হিন্দু-মুসলিম ধর্মের সমন্বয় সাধনের পথ সুগম হয়।
ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, দিল্লির সুলতানরা হিন্দুদের ধর্মীয় উৎসব পালনে কোনোদিন বাধা দেননি। দিল্লির সমগ্র সুলতানি আমলে অমুসলিম নাগরিকদের অর্থাৎ “জিম্মিদের” উপর কোনো ধরনের কঠোর নীতি গ্রহণ করা হয়নি। কোনো কোনো ঐতিহাসিক বলেন যে, “দিল্লির সুলতানি আমলে অমুসলিম প্রজারা ছিলেন দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিক। তাদের মন্দির ধ্বংস করা হয়। তাদেরকে সরকারি চাকরি থেকে বঞ্চিত করা হয়।”
তাদের এ বক্তব্য মোটেও সত্য নয়। কারণ, দিল্লির সুলতানি আমলে কোনো হিন্দু মন্দির ধ্বংস করা হয়নি; যদি ধ্বংস করা হতো, তাহলে প্রাক মুসলিম এবং মুসলিম আমলের মন্দির আজ আর দেখা যেতো না।
এটাও জানা যায় যে, কোনো কোনো সুলতান হিন্দুদের উৎসবেও যোগদান করতেন। যেমন সুলতান মুহম্মদ-বিন-তুঘলক হিন্দুদের “হোলি” উৎসবে যোগদান করতেন। সুলতান আলাউদ্দীন খিলজী জৈন আচার্য মহাসেনকে ধর্ম আলোচনার জন্য কর্নাট থেকে আহ্বান করেন। এছাড়া দিগম্বর জৈন পূর্ণচন্দ্র ও শ্বেতাম্বর জৈন রামচন্দ্র সুরী প্রভৃতি জৈন আচার্যরা সুলতান আলাউদ্দীন খিলজীর আতিথ্য গ্রহণ করেন।
ইবনে বতুতা বলেন যে,
❝মুহম্মাদ-বিন তুঘলকের শাসনামলে অনেক হিন্দু কর্মচারী সুলতানী রাষ্ট্রের উচ্চ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি জনৈক হিন্দু কর্মচারীকে সিন্ধুর শাসনকর্তা পদে নিযুক্ত করেন। সুলতান সতীদাহ প্রথা উচ্ছেদ সাধনে ছিলেন যথেষ্ট তৎপর।❞
অতএব, সতীদাহ প্রথা নিয়ে মাত্র তিনশ বছর আগে নয়, বরং তারও পাঁচশ বছর পূর্বে মুসলিম শাসকরাই সর্বপ্রথম এই প্রথার বিরুদ্ধে আওয়াজ তুলেছিলেন। সেহেতু, সতীদাহ প্রথা বিলুপ্তকরণে রাজা রামমোহন রায় যেভাবে ইতিহাসে মর্যাদাবান হয়ে আছেন, সেটা আদতে মুসলিম শাসকদের অবদান ভুলিয়ে দেবার জন্য ব্রাহ্মণ্যবাদ ও ইংরেজদের উদ্দেশ্যমূলক কর্মকাণ্ড কি-না, তা গভীরভাবে যাচাই করা দরকার।
দিল্লির সুলতানী আমলের ধর্মীয় এই সম্প্রীতি ও সৌহার্দের ধারাবাহিকতা বজায় ছিলো মুঘল আমলেও; এমনকি, ক্ষেত্রবিশেষে তা আরো জোড়ালোভাবে। সম্রাট আকবরের মনসবদারি প্রথা এবং রাজপুতনীতির দিকে তাকালেই বুঝা যায়, তিনি ধর্মীয় দিক থেকে অর্থাৎ হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতিতে কতোটা উদার ছিলেন। সম্রাট জাহাঙ্গীর ও শাহজাহানের ক্ষেত্রে ডক্টর বেনী প্রসাদের মন্তব্য হলো, ❝তাদের ধর্মীয় নীতি ছিলো পরধর্মে সহিষ্ণুতার উপর প্রতিষ্ঠিত।❞
ধর্মীয় সম্প্রীতি ও সৌহার্দের দৃষ্টিকোণে সুলতান আওরঙ্গজেব ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ। অথচ, এই সুলতানকেই ইতিহাসে সবচেয়ে বেশি কলুষিত করা হয়েছে। তাঁর নামেই আজ ভারতে প্রতিষ্ঠিত হয়ে আছে যে, তিনি নির্বিচারে গণহারে হিন্দুবধ করেছেন, অথচ, তার কোনো সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় না।
মহান এই সুলতানের বিরুদ্ধে আনীত ভিত্তিহীন অভিযোগগুলোর মধ্যে অন্যতম ছিলো,
- ০১. হিন্দু মন্দির ও টোল ধ্বংস,
- ০২. হিন্দু কর্মচারীদের পদচ্যুতি,
- ০৩. হিন্দুদের উপর জিজিয়া কর পুনঃপ্রবর্তন।
কিন্তু, সুলতান আওরঙ্গজেব রাজ্যশাসন ব্যবস্থা সুষ্ঠুভাবে পর্যালোচনা করলে স্পষ্ট প্রতীয়মান হবে যে, তিনি কখনই বিধর্মীদের প্রতি অন্যায়, অবিচার এবং জোর জবরদস্তি করেননি। বরং তিনি ভারতের সকল ধর্মের জনগণের প্রতি তার সহিষ্ণুতার মনোভাব প্রদর্শন করেছেন।
প্রথমত, এটা সম্পূর্ণ মিথ্যা ইতিহাস যে, আওরঙ্গজেব হিন্দুবিদ্বেষী ছিলেন এবং হিন্দুমন্দির ও অন্যান্য ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ধ্বংসের আদেশ দিয়েছিলেন। কেননা, তাঁর সময়ে নির্মিত দিল্লি, আগ্রা, বেনারস, মথুরাপুর, গুজরাট প্রভৃতি স্থানে নির্মিত বহু মন্দির আজও বর্তমান রয়েছে। সম্রাট কর্তৃক বেনারসের গভর্নরের নিকট লিখিত ফরমানে জানা যায় যে, তিনি বৈধ উপায়ে নির্মিত মন্দির বিনষ্ট না করার নির্দেশ দেন। প্রধানত যেসব মন্দির রাজদ্রোহ এবং রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রের কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত হতো এবং মসজিদের ধ্বংসস্তূপের ওপর যে সমস্ত মন্দির গড়ে উঠেছিলো, বরং সেগুলো তিনি ধ্বংসের আদেশ দিয়েছিলেন। আওরঙ্গজেবের রাজত্বের শেষভাগে আলেকজান্ডার হ্যামিলটন ভারতবর্ষ পরিভ্রমণে এসে সম্রাটের সহিষ্ণু মনোভাবের পরিচয় পেয়েছিলেন। তিনি মন্তব্য করেন, “Everyone is free to serve and worship God in his own way”.
ঐতিহাসিক শর্মাও স্বীকার করেন যে, আওরঙ্গজেবের রাজত্বকালে হিন্দুগণ ধর্মীয় স্বাধীনতা ভোগ করতো। সবচেয়ে বড় কথা হলো, রাজপুত সেনাপতি ভীমসিংহ আহমেদাবাদে প্রায় ৩০০ মসজিদ ভেঙেছিলেন। কিন্তু, আওরঙ্গজেব তাকে কোনো ধরনের শাস্তি না দিয়ে তাকে মারাঠাদের দমন করতে পাঠান।
দ্বিতীয়ত, আওরঙ্গজেব হিন্দু কর্মচারীদেরকে বরখাস্ত করে সে জায়গায় মুসলমানদেরকে নিযুক্ত করেছিলেন বলে যে অভিযোগ করা হয়, তা সত্য নয়। দুর্নীতির অভিযোগে তিনি কতিপয় হিন্দু কেরানি, দেওয়ান ও রাজস্ব আদায়কারী কর্মচারীকে চাকরিচ্যুত করেছিলেন। এর অর্থ এই নয় যে, তিনি হিন্দুদের প্রতি বৈরী ও রুষ্ট হয়ে তাদেরকে পাইকারি-হারে চাকরি হতে বরখাস্ত করেন। তিনি রাষ্ট্রের সামরিক ও বেসামরিক দফতরে একজন করে হিন্দু-মুসলমান নিয়োগ দেন। কিছু হিন্দু কর্মচারী সম্রাটের বিরুদ্ধাচরণ করলেও তিনি তাদেরকে ক্ষমা প্রদর্শন করে পূর্বপদে বহাল রাখেন। চরম বিরোধিতা করা সত্ত্বেও আওরঙ্গজেব যশোবন্ত সিংহকে শুধু ক্ষমাই করেননি বরং তাকে যথাযচিত সম্মান প্রদর্শন করেন। এ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আওরঙ্গজেব হিন্দুবিদ্বেষী ছিলেন এবং বিনা অপরাধে হিন্দু কর্মচারীদেরকে পদচ্যুত করেছিলেন—এ কথা চিন্তাই করা যায় না।
তৃতীয়ত, অমুসলিমদের জানমালের নিরাপত্তা রক্ষা করার জন্য সামরিক কার্যের পরিবর্তে তাদের উপর আওরঙ্গজেব জিজিয়া কর ধার্য করেন। হিন্দুদের উপর থেকে প্রায় ৮০ প্রকার কর উঠিয়ে নেয়ার ফলে রাষ্ট্রের অর্থভাণ্ডার শূন্য হয়ে পড়ে। তারপরও হিন্দুরা অনুগত না হয়ে আক্রমণ-ভাবাপন্ন হয়ে পড়ে। কাজেই দীর্ঘ ২০ বছর পরে ১৬৭৯ খ্রিস্টাব্দে আর্থিক ক্ষতিপূরণ ও শত্রুভাবাপন্ন হিন্দুদেরকে নিয়ন্ত্রণাধীনে আনার উদ্দেশে সম্রাট হিন্দুদের উপর জিজিয়া কর পুনরায় ধার্য করেন। ভি.ডি. মহাজন স্বীকার করেন যে,
❝এই কর আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার উপর ধার্য হয়নি। বস্তুত, দরিদ্র, স্ত্রীলোক, খোড়া, নাবালক ও উন্মাদগ্রস্ত ব্যক্তিদের অব্যাহতি দেওয়া হয়। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কারণেই তিনি জিজিয়া কর পুনঃপ্রবর্তন করেন।❞
অতএব, হিন্দুদের ক্ষমতা লাভের আকাঙ্ক্ষা থেকে এমন একজন মহান শাসকের উপর এমন সব অভিযোগ পেশ যে সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। সেহেতু বলা যায়, এমন সব মিথ্যা অভিযোগ আনয়ন মূলত ইংরেজ ও ব্রাহ্মণ্যবাদ ইতিহাসবীদদের স্বার্থসিদ্ধি হাসিলের মনোভাবকেই বরং আরো স্পষ্ট করে তোলে।
💠সাংস্কৃতিক সম্প্রীতি ও সৌহার্দ
সাংস্কৃতিক সম্প্রীতি ও সৌহার্দ-এর আলোচনার পূর্বে আমাদেরকে এটা বরং আগে বুঝতে হবে যে, বিনোদন ও সংস্কৃতি এক বিষয় নয়। বিনোদন মূলত সংস্কৃতিরই একটা অংশ। কেননা, আমাদের দৈনন্দিন জীবনের প্রতিটি কাজই কোনো না কোনো সংস্কৃতির আলোকে করে থাকি। অর্থাৎ, ঘুম থেকে জাগ্রত হওয়ার পরের কার্যক্রম থেকে শুরু করে রাতে পুনরায় ঘুমাতে যাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত মানুষ যা করে, তাই সংস্কৃতি। অতএব, সংস্কৃতির আলোচনায় শুধু বিনোদন অন্তর্ভূক্ত হবে না; বরং সমাজের সামগ্রিক বিষয়গুলোই সংস্কৃতিতে আলোচনা হবে।
মুসলিম পূর্ব ভারত
প্রাক মুসলিম ভারতীয় সমাজে জাতিভেদ প্রথা ছিলো খুবই ভয়ংকর। প্রাথমিক অবস্থায় হিন্দু সমাজে উদারতা বিদ্যমান ছিলো। ভারতীয় উপমহাদেশে দ্রাবিড়, আর্য, শক, হুন, কুষাণ প্রভৃতি জাতীয় লোকজন আসে এবং হিন্দু সমাজের উদারতায় মুগ্ধ হয়ে তাদের আলাদা সত্তা হারিয়ে হিন্দু সমাজের সাথে এক হয়ে যায়। কিন্তু, পরবর্তী সময়ে হিন্দু সমাজে জাতিভেদ প্রথা প্রকট আকার ধারণ করে। ৮ম শতাব্দীতে হিন্দু সমাজ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এ চার শ্রেণিতে বিভক্ত হয়ে পড়ে। সমাজে নিম্ন শ্রেণির লোকদের বিশেষ করে শূদ্রদের দুরাবস্থার কোনো সীমা ছিলো না। শূদ্ররা সমাজে অপবিত্র ও অস্পৃশ্য বলে বিবেচিত হতো। এমন কি ধর্ম-কর্ম পর্যন্ত তাদের জন্য নিষিদ্ধ ছিলো।
ঐতিহাসিক আল বেরুনী তার “কিতাব উল-হিন্দ” নামক গ্রন্থে বলেন যে,
❝কোনো বৈশ্য এবং শূদ্র বেদ-গীতা পাঠ করলে, এমনকি বেদবাক্য শুনলেও শাস্তি হিসেবে তার জিহ্বা কেটে দেওয়া হতো। ভিন্ন জাতির লোকদের মধ্যে অন্তবিবাহ ও পানাহার নিষিদ্ধ ছিলো। এমনকি শূদ্রদের স্পর্শও অপবিত্র ছিলো। সমাজে বহু বিবাহ প্রচলিত ছিলো। জাতিচ্যুতদের ভাগ্য আরও খারাপ ছিলো। বেদ শ্রবণ করলে কর্ণে উত্তপ্ত সীসা ঢেলে দেওয়া হতো।❞
মুসলিম বিজয়ের আগে ভারতবর্ষের সমাজে নারীদের অবস্থা ছিলো বড়ই করুণ। নারীদের অধিকার ছিলো খুবই সীমিত। নারীদের সাধারণত ভোগের সামগ্রী হিসেবে ব্যবহার করা হতো। সমাজে পুরুষেরা বহু বিবাহ করতো। কিন্তু, নারীদের দ্বিতীয় বিবাহের কোনো নিয়ম ছিলো না। গ্রিকদের বিবরণ থেকে জানা যায় যে, মৌর্য যুগে সমাজে নারীদের মর্যাদা ছিলো এবং তারা সাহিত্য দর্শনে বিশেষ কৃতিত্বের অধিকারী ছিলো। আল বেরুনী তার “কিতাব-উল-হিন্দ” নামক গ্রন্থে বৈদিক যুগের নারী জাতির উচ্চ মর্যাদার ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। আল-বেরুনী আরও বলেন যে,
❝সে সময় নারীদেরকে শিক্ষা প্রদান করা হতো এবং শাসন-ক্ষেত্রে ও সামাজিক কর্মকাণ্ডে তাদের অংশগ্রহণের সুযোগ ছিলো।❞
তবে এটা যে বৈদিক সমাজের সামগ্রিক চিত্র ছিলো না, তা আর বলার অপেক্ষাও রাখে না। বৈদিক যুগের পরবর্তী সময়ে নারীর অপমানের বিষয়টি উঠে আসে সতীদাহ প্রথা থেকে। ইতিহাস থেকে জানা যায়, মুসলিম বিজয়ের আগে ভারতীয় সমাজে অনেক কু-প্রথা ও কুসংস্কার প্রচলিত ছিলো। অনেক কু-প্রথাকে সমাজে ধর্মের মর্যাদা দেওয়া হতো। কোনো নারীর স্বামী মারা গেলে সহমরণ বা সতীদাহ প্রথা, নরবলি এবং গঙ্গীয় শিশু কন্যা বিসর্জন ইত্যাদি কাজকে হিন্দুরা ধর্মীয় পুণ্যের কাজ বলে মনে করতো। এছাড়াও তখন দেবদাসী প্রথাও প্রচলিত ছিলো।
আবার ভারতের হিন্দু সমাজে দাসপ্রথা প্রচলিত ছিলো। দাস-দাসী কেনা-বেচা হতো এবং প্রাসাদে নিয়োগ দেওয়া হতো। এটি তখন সামাজিক অনুশাসনে পরিণত হয়।
মোদ্দাকথা, মুসলিম বিজয়ের আগে ভারতের সমাজব্যবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় অবস্থায় ছিলো। সমাজে শ্রেণি-বৈষম্য ছিলো। জাতিভেদ প্রথা সমাজকে একেবারে পঙ্গু করে দিয়েছিলো। নারীরা ভোগের সামগ্রী হিসেবে ব্যবহৃত হতো। সমাজে তাদের কোনো মর্যাদাই ছিলো না। এমনকি, ধর্মের দোহাই দিয়ে শাসকরা সমাজের কোনো উন্নয়নে পর্যন্ত এগিয়ে আসেনি।
মুসলিম ভারত
বিপরীতে ভারতের মুসলিম সমাজের অন্য এক চিত্র দেখা যায়।
ভারতীয় উপমহাদেশে মুসলমানদের আসার আগে গ্রিক, শক, হুন, পারসিক প্রভৃতি জাতির লোকজন আসে। তারা তাদের নিজস্ব কোনো সভ্যতা ও ধর্মবিশ্বাস নিয়ে ভারতীয় উপমহাদেশে আসেনি। তারা হিন্দু সমাজের সাথে মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়। এরপর, ৭১২ সালে মুহাম্মাদ বিন কাসিমের সিন্ধু বিজয়ের পর মুসলিম বিজেতারা এদেশে এক উন্নত সভ্যতা, সংস্কৃতি ও ধর্ম নিয়ে আসেন। তারা দীর্ঘদিন ভারতবর্ষে অবস্থান করেন। মুসলমানরা হিন্দুদের সভ্যতা ও সংস্কৃতির সাথে মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়নি এবং মুসলমানরা তাদের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ধরে রাখতে সক্ষম হয়। প্রখ্যাত ঐতিহাসিক এন. সি. মেহতা বলেন,
❝ইসলাম যেখানে এসেছে, সেখানেই মার্জিত রুচি এবং মর্যাদাবোধের প্রকাশ ঘটেছে। এটা স্মরণ রাখা দরকার যে, প্রত্যেক মুসলমান প্রধানত একটি সামাজিক, সহজ ও মুক্ত জীবন-যাপন করে।❞
মুহাম্মাদ বিন কাসিমের সিন্ধু বিজয়ের পর ভারতের সমাজ-কাঠামোর উপর ইসলামের যথেষ্ট প্রভাব পড়ে। ইসলামের উদার, সহনশীল নীতি ও হিন্দু সমাজের কঠোরতা নিম্নবর্ণের হিন্দুদের উপর প্রবল প্রভাব পড়ে। এর ফলে নিম্নবর্ণের হিন্দুরা দলে দলে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে। তাছাড়া ইসলামের প্রভাবে বর্ণভিত্তিক ভারতীয় সমাজে আরও অনেক নতুন নতুন উপবর্ণ ও গোষ্ঠীর উদ্ভব ঘটে।
বিন কাসিমের এই অভিযানের পর ভারতবর্ষের প্রচলিত সামাজিক রীতি-নীতির উপর ইসলামের যথেষ্ট প্রভাব পড়ে। ভারতের হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ই খাদ্য, পোশাক পরিচ্ছেদ ও সামাজিক রীতি-নীতির ক্ষেত্রে একে অন্যের সাথে ভাবের আদান-প্রদান করে। এ প্রসঙ্গে ঐতিহাসিক রোমিলা থাপা বলেন যে,
❝তুর্কিরা বাহ্যত স্থানীয় খাদ্য ও পোশাক গ্রহণ করে। কিন্তু, এর চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হলো, ইসলামের কোনো কোনো সামাজিক চিন্তা ভারতীয় জীবনের অংশ হয়ে যায়। ইসলামের প্রভাবে ভারতের উচ্চবর্ণের হিন্দু মহিলাদের মধ্যে পর্দার প্রচলন ঘটে। প্রাচীন ইরানে (পারস্য) এ প্রথার প্রচলন হলেও ভারতে আরবীয় ও তুর্কিরা এ প্রথা আমদানি করে।❞
এই পর্যায়ে পূর্বের একটি কথা আবারো উল্লেখ করতে হয় যে, মুসলিম শাসনামলে ধর্মীয় ধ্যান-ধারণা ও ধর্মবিশ্বাসের ক্ষেত্রেও পরিবর্তন আসে। ভারতে প্রাথমিক মুসলিম শাসনের সময়ে ভারতীয়দের কাছে ইসলাম একেবারে অপরিচিত ছিোল না। কারণ, অষ্টম ও নবম শতাব্দীতে সিন্ধু ও তৎসংলগ্ন অঞ্চলে ইসলাম ধর্মের আগমন ঘটে। ভারতে বৌদ্ধ রীতি-নীতি ধ্যান-ধারণার প্রভাবে সুফিবাদের উন্মেষ ঘটে। ইসলামের একেশ্বরবাদ ও সুফিদের প্রেম এবং ভক্তির মাধ্যমে ঈশ্বরকে লাভ করার তত্ত্ব ভারতীয় সমাজজীবনকে আলোড়িত করে। যার ফলে ভারতে হিন্দু-মুসলিম ধর্মের সমন্বয় সাধনের পথ সুগম হয়।
হিন্দু ও মুসলিম সম্পর্কের ক্ষেত্রে এস. এ. এ. রিজভী বলেন যে,
❝ভারতে তুর্কি শাসন প্রতিষ্ঠা হিন্দু-মুসলিম সম্পর্ক স্থাপনে অনেক সুযোগ-সুবিধাকে উন্মোচিত করেছিলো।❞
ঐতিহাসিক সতীশ চন্দ্র-এর মতে,
❝ভারতীয়দের সুগভীর ধর্মীয় বিশ্বাস এবং সাহিত্য, শিল্প ও স্থাপত্য সম্পর্কে সমুন্নত ধ্যান-ধারণার সাথে তুর্কি ধ্যান-ধারণার সংমিশ্রণে শেষ পর্যন্ত এক সমৃদ্ধ সংস্কৃতি গড়ে ওঠে।❞
রোমিলা থাপার মতে,
❝ব্রাহ্মণরা তাদের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখার ক্ষেত্রে সচেষ্ট হলেও হিন্দু-মুসলিম মিলনের স্রোত ক্রমশ গতিশীল হয়ে ওঠে।❞
সতীদাহ প্রথা নিয়ে বলতে গেলে ইবনে বতুতার মুহম্মাদ-বিন তুঘলককে নিয়ে একটা মন্তব্য তুলে ধরতে হয়, তিনি বলেন,
❝সুলতান সতীদাহ প্রথা উচ্ছেদ সাধনে সর্বদা ছিলেন তৎপর।❞
শুধু মুহাম্মাদ বিন তুঘলকই না, বরং সম্রাট বাবর, আকবর এবং আওরঙ্গজেবও সতীদাহ প্রথা বিলুপ্তকরণে ভূমিকা পালন করেন। সম্রাট আকবর একবার নিজে গিয়ে এমন হিংস্র কর্মকাণ্ডে বাধা দেন এবং সম্রাট আওরঙ্গজেব সতীদাহ প্রথা বিলুপ্তকরণে আইন পর্যন্ত প্রণয়ন করেন।
অতএব, সতীদাহ প্রথা নিয়ে মাত্র তিনশ বছর আগে নয়, বরং তারও পাঁচশ বছর পূর্বে মুসলিম শাসকরাই সর্বপ্রথম এই প্রথার বিরুদ্ধে আওয়াজ তুলেছিলেন। সেহেতু, সতীদাহ প্রথা বিলুপ্তকরণে রাজা রামমোহন রায় যেভাবে ইতিহাসে মর্যাদাবান হয়ে আছেন, সেটা আদতে মুসলিম শাসকদের অবদান ভুলিয়ে দেবার জন্য ব্রাহ্মণ্যবাদ ও ইংরেজদের উদ্দেশ্যমূলক কর্মকাণ্ড কি-না, তা গভীরভাবে যাচাই করা দরকার।
মোদ্দাকথা, ভারতীয় সংস্কৃতিতে ইসলামের যথেষ্ট প্রভাব পড়ে। মুসলমানরা ভারতে এসে এখানে শ্রেণিহীন সমাজ গঠনে ভারতীয়দেরকে উদ্বুদ্ধ করে। দিল্লির সুলতানি আমলে ভারতে ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার পর, এমনকি মুঘল আমলেও, ইসলামী ভাবধারা ভারতের সমাজ, আচার-আচরণ, ধর্ম, স্থাপত্য, শিল্প, ভাষা-সাহিত্য, সঙ্গীত ও বিজ্ঞানকে প্রভাবান্বিত করে। এভাবেই, ইসলামী ভাবধারা অনেক ক্ষেত্রেই ভারতীয় ঐতিহ্যের সাথে মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়।
💠শিক্ষা, সাহিত্য ও স্থাপত্যে সম্প্রীতি ও সৌহার্দ
মুসলিম পূর্ব ভারত
ধর্ম, সমাজ ও সংস্কৃতির দৃষ্টিকোণ থেকে মুসলিম পূর্ব ভারতের অবস্থা খুবই নাজুক ও হ-য-ব-র-ল হলেও শিক্ষাক্ষেত্রে তারা বেশ এগিয়ে ছিলো। মুসলিম বিজয়ের প্রাক্কালে ভারতের শিক্ষা-দীক্ষা, জ্ঞান-বিজ্ঞান ও কৃষ্টি-সভ্যতার যথেষ্ট উন্নতি সাধন করেছিলো। হিন্দু ও বৌদ্ধ শাসনামলে দেশের সর্বত্র শিক্ষায়তন গড়ে উঠেছিলো। মঠ, টোল, পাঠশালা, কলেজ এমনকি কোথাও কোথাও বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে ওঠে। বিহারে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় ও পশ্চিম ভারতের বালভী বিশ্ববিদ্যালয় ছিল উচ্চশিক্ষার পাদপীঠ। এছাড়াও উদন্তপুর, বারানসী, বিক্রমশীলা প্রভৃতি স্থানে উচ্চশিক্ষার সু-ব্যবস্থা ছিলো। মালব ও আজমীরে সংস্কৃতি কলেজ স্থাপিত হয়। এসব প্রতিষ্ঠানে ধর্মশাস্ত্র ও বেদান্ত ছাড়াও দর্শন, বিজ্ঞান, জ্যোতির্বিদ্যা ও চিকিৎসা বিজ্ঞান সম্পর্কে শিক্ষাদান করা হতো।
প্রাক-মুসলিম আমলে ভারতবর্ষে হিন্দু কাব্য, নাটক, উপন্যাস ও গদ্য সাহিত্যের বিকাশ লাভ করে। সাহিত্যিক হিসেবে ভগবতি, বাহমান, জয়দেব, রাজ শেখর, শ্রীহর্ষ, কালিদাস প্রমুখ খ্যাতি লাভ করেন। আর্যভট্ট, ব্রহ্মগুপ্ত ও নাগার্জুন জ্যোতির্বিদ্যা, গণিত-শাস্ত্র ও চিকিৎসা-বিদ্যায় ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। স্থাপত্য ও ভাস্কর্য শিল্পে ভারতীয়রা অসাধারণ দক্ষতা অর্জন করে। কৈলাশ মন্দির, ভুবনেশ্বর ও কোনারকের মন্দির ছাড়াও ইলোরা, অজন্তা, খাজুরাহ, গান্ধার ও সাঁচির চিত্র ও স্থাপত্য কীর্তি ভারতীয়দের উচ্চমানের শিল্প নৈপুণ্য প্রদর্শন করে। এ সময় ভারতীয়রা সঙ্গীত চর্চায়ও ব্যাপক খ্যাতি লাভ করে।
মুসলিম ভারত
এখন তাহলে প্রশ্ন আসতে পারে, তবে তাহলে শিক্ষাক্ষেত্রে মুসলমানদের অবদান নেই? এক্ষেত্রে উত্তর হলো, শিক্ষা-সাহিত্যে মুসলামদের অবদানের অনস্বীকার্য। পূর্বের এমন একটা ভঙ্গুর সমাজকে যে ইসলামী সভ্যতা উন্নতির সর্বোচ্চ শিখরে পৌঁছে দিতে পারে, তাহলে তারা যে শিক্ষাক্ষেত্রেও এগিয়ে থাকবে, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।
দিল্লির সুলতানি আমলে ভাষা ও সাহিত্যের উপর ইসলামী ভাবধারা যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে। ভারতে তুর্কিদের আগমনের সাথে সাথে এদেশে ফার্সি ভাষার প্রচলন শুরু হয়। ফার্সি ভাষা সরকারি ভাষা হিসেবে ব্যবহৃত হতে থাকে। ফার্সি ভাষায় সাহিত্য চর্চা শুরু হয়। পারস্যের অনুকরণে ভারতেও তখন সাহিত্য চর্চা শুরু হয়। পরবর্তী ফার্সি সাহিত্য ভারতীয় বিষয়বস্তু অবলম্বনে রচিত হতে থাকে। এ’ক্ষেত্রে ভারতের তোতা পাখি হিসেবে খ্যাত আমীর খসরুর ভূমিকা ছিলো সর্বাগ্রে।
ভারতে মুসলিম আগমনের সাথে সাথে বই লেখা ও তাতে চিত্রাঙ্কনে যথেষ্ট প্রভাব পড়ে। ভারতে প্রাচীন যুগে জৈন ধর্মশাস্ত্র সংরক্ষণের জন্য সেগুলোর অনেক অনুলিপি তৈরি করা হতো অথবা পুরনো বইয়ের ভিত্তিতে নতুন বই তৈরি করা হতো। পুথিগুলো ছিলো মূলত তালপাতার। চিকন ও লম্বা তালপাতার উপরে আলঙ্কারিক চিত্রাঙ্কনের কোনো ধরনের সুযোগ ছিলো না। ভারতে মুসলিম শাসনামলে এসব গ্রন্থ রচনা ও চিত্রাঙ্কনের রীতির ব্যাপক পরিবর্তন ঘটে। আরব বণিকরা পশ্চিম ভারতে সর্বপ্রথম কাগজ ব্যবহারের প্রচলন ঘটায়। এর ফলে জৈন ধর্মের পুথিগুলো তখন থেকে কাগজে লেখা শুরু হয় এবং তাতে চিত্রাঙ্কনের ব্যাপক সুযোগ হয়। জ্ঞান-বিজ্ঞান, চিকিৎসা প্রভৃতি থেকে ভারতীয় ও ইসলামের সমন্বয় ঘটে। এই মুসলিমদের মাধ্যমেই আরবীয় ইউনানি (ভেষজ) চিকিৎসা ভারতে আসে। আবার ভারতীয় চিকিৎসা পদ্ধতি পশ্চিম এশিয়ায় সম্প্রসারিত হয়।
শিক্ষাকেন্দ্র
শিক্ষা নিয়ে আলোচনা করতে গেলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বা শিক্ষাকেন্দ্রের বিষয়টি সামনে চলে আসে। সে হিসেবে মুসলিম ভারতের গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম উল্লেখ করা প্রয়োজন। কিন্তু, পুরো ভারতবর্ষের সবগুলো শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান বা শিক্ষাকেন্দ্রের নাম উল্লেখ করার মাধ্যমে প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি না করে আমাদের বুঝার সুবিধার্থে শুধু বাংলার আশেপাশের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য শিক্ষাকেন্দ্রের নাম উল্লেখ করা হলো,
লক্ষ্মণাবতী গৌড় :
বাংলায় মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠার পর থেকে (১২০৪) লক্ষ্মণাবতী (গৌড়) বাংলার শিক্ষা ও সংস্কৃতির এক গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র রূপে আবির্ভূত হয়। সমসাময়িক দিল্লি দরবারের ঐতিহাসিক মিনহাজ-ই-সিরাজ ১২৪৪ সালে বাংলায় আগমন করে বাংলায় অনেক মসজিদ-মাদরাসা দেখতে পান এবং তিনি মন্তব্য করেন যে, বখতিয়ার খিলজীই বাংলায় অসংখ্য মসজিদ-মাদরাসা স্থাপন করেন। বাংলায় মুসলিম অন্যতম শিক্ষা কেন্দ্র ছিলো লক্ষ্মণাবতী (গৌড়)। এখানে সুলতানি যুগের অনেক মসজিদ, মাদরাসা, শিলালিপি আবিষ্কৃত হয়েছে। এর থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় যে, গৌড় ছিল মধ্যযুগে মুসলিম বাংলার অন্যতম শিক্ষা কেন্দ্র। গৌড়ের বিখ্যাত পণ্ডিতদের মধ্যে ছিলেন কাজী রুকনদ্দীন সমরকন্দী। এছাড়াও, ঐতিহাসিক মিনহাজ-ই-সিরাজ দুই বছর গৌড়ে বসবাস করেন। প্রখ্যাত ধর্মতত্ত্ববিদ জালালুদ্দীন গজনবী এ শহরে কয়েক বছর অবস্থান করেন। এছাড়াও তিনি বাংলার সুলতান গিয়াসুদ্দীন ইওয়াজ খলজীর (১২১৩-১২২৭) সভাকক্ষে ভাষণ দেন। বিশিষ্ট কবি ও পণ্ডিত ব্যক্তি শামসুদ্দীন দবীর ও কাজী আসির বাংলার সুলতান নাসিরুদ্দীন বুগরা খানের রাজসভা অলঙ্কৃত করেন।
সোনারগাঁও :
সোনারগাঁও ছিলো বাংলায় ইসলামী শিক্ষার প্রাণকেন্দ্র। আর এ কেন্দ্রের মধ্যবিন্দু ছিলেন বিখ্যাত পীর মাওলানা শরফুদ্দীন আবু তাওয়ামা। তিনি বোখারায় জন্মগ্রহণ করেন, খোরাসানে শিক্ষা লাভ করেন এবং পরবর্তীতে দিল্লিতে আসেন। দিল্লি থেকে সরাসরি সুলতান গিয়াস-উদ্দীন বাংলায় আসেন। সোনারগাঁওয়ে এসে তিনি খানকা স্থাপন করেন। এখান থেকেই তিনি শিক্ষার আলো সারা বাংলায় ছড়িয়ে দিতে সক্ষম হন। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে প্রতিষ্ঠিত এ শিক্ষাকেন্দ্র বাংলাদেশের সর্বশ্রেষ্ঠ গৌরব ছিলো। তাঁর খ্যাতনামা শিষ্য ছিলেন পীর শরফুদ্দীন ইহইয়া মানেরী। বিখ্যাত পীর ও পণ্ডিত শেখ আলাউল হক যখন সোনারগাঁওয়ে নির্বাসনে আসেন, তখন তিনি তাঁর সংস্পর্শে আসেন এবং দু’বছর এখানে কাটান। তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ ছিলো “মাকামাত” ও “নাম-ই-হক”। তিনি ইসলামী শাস্ত্রে অগাধ পাণ্ডিত্যের অধিকারী ছিলেন। এ মহামানব ও মহান শিক্ষক, বাংলা অঞ্চলে শিক্ষার আলোর দিশারী ৭০০ হিজরি মতান্তরে ১৩০০ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন। সোনারগাঁয়ে তাঁকে সমাধিস্থ করা হয়।
সাতগাঁও :
মধ্যযুগে আরেকটি বিখ্যাত শিক্ষাকেন্দ্র ছিলো সাতগাঁও। এখান থেকে বেশ কয়েকটি শিলালিপি আবিষ্কৃত হয়েছে। এতে দেখা গেছে যে, এখানে মাদরাসা তৈরি করা হয়, যার একটি ছিলো বাংলার সুলতান রুকনুদ্দীন কায়কাউসের সময়ে; যেটি ছিলো ১২৯৩ সালে কাজী আল-নাসির মুহাম্মদ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত। শিলালিপিতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, তিনি আল-নাসির মাদরাসা নির্মাণে অনেক অর্থ সাহায্য করেন এবং ইসলামী শিক্ষা কেন্দ্রের শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের ব্যয় নির্বাহের জন্য অনেক অর্থ সাহায্য করেন। আবার বাংলার সুলতান শামসুদ্দীন ফিরোজ শাহের ১৩১৩ সালে আরেকটি মসজিদ নির্মাণের প্রমাণও পাওয়া যায়।
পান্ডুয়া :
পাণ্ডুয়া ছিল বাংলার সর্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষাকেন্দ্র। এটি ছিলো ধর্মীয় আধ্যাত্মিক শিক্ষাকেন্দ্র হিসেবে বিখ্যাত। কারণ, শেখ জালালুদ্দীন তাবরিজী, শেখ আখী সিরাজুদ্দীন উসমান, শেখ আলাউল হক, নূর কুতুব-উল-আলম, শেখ জাহিদসহ অসংখ্য পীর-আউলিয়াদের শিক্ষায় পাণ্ডুয়া ধন্য হয়েছে। মুসলিম শাসকদের রাজধানীও ছিলো পাণ্ডুয়া। বাংলার মুসলিম শাসকরা উদারভাবে তাদের পৃষ্ঠপোষকতা দান করেন। ফলে, পাণ্ডুয়া ইসলামী জ্ঞানকেন্দ্রের পাদপীঠের মর্যাদা লাভ করে। আবার বিখ্যাত পীর হযরত নূর কুতুব-উল-আলম (র.) পাণ্ডুয়ায় একটি বড় মাদরাসা ও চিকিৎসালয় নির্মাণ করেন। পাণ্ডুয়া মূলত বহু বিদ্বান পণ্ডিতদের পদচারণায় ধন্য হয়েছে। ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শতাব্দীতে কয়েকজন বিখ্যাত পণ্ডিতের আবির্ভাব হয়, যারা পান্ডুয়ার বুকে জ্ঞানের আলো জ্বালিয়ে দিতে সক্ষম হন।
এ-তো গেলো শুধু বাংলা ও তার আশপাশের অঞ্চলের গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি শিক্ষাকেন্দ্র। দিল্লি থেকে সুদূর বাংলারই যদি শিক্ষার এই অবস্থা হয়, তাহলে দিল্লি-সহ সমগ্র ভারতের শিক্ষাব্যবস্থা নিয়ে আলোচনা করতে গেলে স্বতন্ত্র একটি প্রবন্ধ রচনার প্রয়োজন পড়বে।
পাঠ্যক্রম
এবার একটু পাঠ্য তালিকার দিকে নজর দেওয়া যাক।
দিল্লি সালতানাত হোক বা মুঘল আমল হোক, মুসলিম ভারতের পাঠ্য তালিকায় অন্তর্ভুক্ত ছিলো কুরআন, হাদিস, ধর্ম ও আইনশাস্ত্র এবং অন্যান্য ইসলামী বিষয়সমূহ। এছাড়াও, যুক্তিবিদ্যা, অঙ্কশাস্ত্র, চিকিৎসাবিদ্যা, রসায়ন, জ্যোতির্বিদ্যা, জ্যামিতি এবং অন্যান্য বিষয়ও মাদরাসায় গুরুত্ব সহকারে পাঠদান করা হতো। এই পাঠ্য তালিকার কথা বলতে গিয়ে মুঘল সম্রাট আকবরের দরবারের সর্বশ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক আবুল ফজল বলেন,
❝প্রত্যেক শিক্ষার্থীরই নীতিশাস্ত্র, গণিত, কৃষি, পরিমাপ-শাস্ত্র, জ্যামিতি, জ্যোতিশাস্ত্র, চরিত্র নির্ণয়বিদ্যা, গার্হস্থ্য বিদ্যা, সরকারি আইন-কানুন, চিকিৎসা বিদ্যা, যুক্তিবিদ্যা, উচ্চতর অংক শাস্ত্র, বিজ্ঞানসমূহ, ইতিহাস ইত্যাদি পাঠ করা উচিত।❞
ভারতীয় উপমহাদেশের মুসলমানরা বাগদাদের আব্বাসীয় আমলের (৭৫০-১২৫৮) প্রচলিত শিক্ষানীতি ও পাঠ্য তালিকা অনুসরণ করেন। পাশাপাশি, বাংলা অঞ্চলেও তা অনুসরণ করা হয়। বাংলায় আগত মুঘল কর্মচারীরা বাংলার অনেক চিকিৎসক ও তাদের উন্নত চিকিৎসা পদ্ধতির কথা বলেছেন। বাংলার নবাবী আমলের দরবারী ঐতিহাসিকরাও তা উল্লেখ করেছেন। যেমন, “বাহারিস্তান-ই-গায়বী”-র লেখক মীর্জা নাথান এবং ”সিয়ার-উল-মুতাখখেরিন”-এর লেখক গোলাম হোসেন খান তবাতবায়ি ছিলেন উল্লেখযোগ্য। তাঁদের মতে, বাংলায় অনেক দক্ষ চিকিৎসক, হাকিম ও কবিরাজ ছিলেন। ফরাসি পর্যটক ও মুঘল সম্রাট আওরঙ্গজেবের ব্যক্তিগত চিকিৎসক বার্নিয়ার বাংলায় এসে বাংলার চিকিৎসক ও তাদের চিকিৎসা পদ্ধতির সম্পর্কে তার ভ্রমণ কাহিনিতে উল্লেখ করেছেন। তিনি এ দেশের মুসলিম চিকিৎসকদের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন। পক্ষান্তরে, শব-ব্যবচ্ছেদ বিদ্যায় হিন্দুদের অজ্ঞতার কথাও তিনি স্পষ্ট করে তার ভ্রমণ কাহিনিতে উল্লেখ করেছেন।
ভাষা সাহিত্য
দিল্লির সুলতানরা ভাষা ও সাহিত্যের পেছনে উদারতার সাথে পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। তাঁরা আরবি ও ফারসি ভাষা ছাড়াও হিন্দি, সংস্কৃত এবং অন্যান্য ভাষারও পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। এ যুগে উল্লিখিত ভাষাগুলো ছাড়াও বাংলা, মারাঠি প্রভৃতি প্রাদেশিক ভাষাসমূহেরও যথেষ্ট বিকাশ লাভ ঘটেছিলো। মুসলিম সুলতানদের জামানায় বাংলা ভাষার বিশেষ বিকাশ ঘটেছিলো। সুলতানদের সাহায্য ছাড়া বাংলা ভাষা আজকে সংস্কৃত ভাষার মতো একটি মৃত ভাষায় পরিণত হতো। বাংলা ভাষার প্রতি মুসলমান সুলতানদের উদার পৃষ্ঠপোষকতার প্রশংসা করতে গিয়ে ড. দীনেশ চন্দ্র সেন বলেন,
❝ব্রাহ্মণগণ প্রথমদিকে বাংলা ভাষা গ্রহণ ও প্রচারের বিরোধী ছিলো। কৃত্তিবাস ও কাশীদাসকে তারা ‘সর্বনেশে’ উপাধি প্রদান করেছিলো। যদি হিন্দু রাজাগণ স্বাধীন থাকতো, তাহলে কদাচিৎ বাংলা ভাষা তাদের দরবারে প্রবেশ করার সুযোগ লাভ করতো। আমাদের বিশ্বাস, মুসলমান কর্তৃক বঙ্গবিজয়ই বঙ্গভাষার এই সৌভাগ্যের কারণ হয়ে দাড়িয়েছিলো। মুসলমানগণ ইরান, তুরান প্রভৃতি যে স্থান হতেই আসুক না কেনো, এ’দেশে এসে তারা সম্পূর্ণরূপে বাঙ্গালি হয়েছেন।❞
আর প্রখ্যাত ঐতিহাসিক স্যার যদুনাথ সরকার বলেন, ❝দিল্লি সাম্রাজ্যের অধীনে শান্তি ও আর্থিক উন্নতির ফলস্বরূপই দেশীয় ভাষা সাহিত্যের সমৃদ্ধি ঘটেছে।❞
ড. লক্ষ্মীধর বলেন, ❝আমাদের এটা ভুললে চলবে না যে, দেশীয় ভাষা হিন্দিকে সর্বপ্রথম মুসলমানগণই সাহিত্য সৃষ্টির উদ্দেশ্যে ব্যবহার করেছেন। অথচ আমরা জানি যে, ব্রাহ্মণগণ ইতর ভাষা বলে এই ভাষাকে অবহেলা করেছেন।❞
বিজয়গুপ্ত, বিপ্রদাশ, মালাধর, পরমেশ্বর কবীন্দ্র, শ্রীকর নন্দীর রচনার দ্বারা ঐ যুগে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রভূত উৎকর্ষ সাধিত হয়েছিলো। সুলতানি আমলে সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যেরও অসামান্য উন্নতি হয়। বাংলার সুলতান আলাউদ্দীন হোসেন শাহের মন্ত্রী রূপগোস্বামী ২৫টি সংস্কৃত গ্রন্থ রচনা করে সংস্কৃত ভাষাকে সমৃদ্ধ করেন।
এই যুগে এদেশের সাধারণ প্রচলিত কথ্য ভাষার সাথে আরবি ও ফারসি শব্দ মিশ্রিত হয়ে উর্দু নামক একটি নতুন ভাষা সৃষ্টি হয়। মুঘল আমলে উর্দু ভাষা যথেষ্ট বিকাশ লাভ করে সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে। উর্দু-সাহিত্য চর্চা প্রথম শুরু করেন আমীর খসরু। সুলতানি আমলে আরেকজন বিখ্যাত কবি-সাহিত্যিক ছিলেন আমীর খসরু। ইতিহাসে তিনি “ভারতবর্ষের তোতাপাখি” নামে আজও অমর হয়ে আছেন। ঐতিহাসিক নোমানী বলেন, ❝বিগত ছয়শত বছরের মধ্যে ভারতবর্ষে তাঁর ন্যায় সর্বতোমুখী প্রতিভার আবির্ভাব ঘটেনি।❞
“খাজায়নুল ফতুহ”, “তারিখ-ই-আলাই”, “তুঘলক নামা” প্রভৃতি তাঁর রচিত বিখ্যাত গ্রন্থ। আমীর হাসান দেহলবী ছিলেন মুহম্মদ-বিন-তুঘলকের সভাকবি ও শিল্পী। তিনি “দিউয়ান” নামক একটি গ্রন্থ রচনা করে খ্যাতি অর্জন করেন। বদরুদ্দীন নামক আরেকজন উঁচুদরের কবি মুহম্মদ-বিন-তুঘলকের দরবার অলঙ্কৃত করেন। এছাড়াও, সাহিত্যিক হিসেবে মালিক মুহাম্মদ যায়সী, দৌলত কাজী প্রমুখের নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। এ’যুগে শিক্ষা-সংস্কৃতির অন্যতম কেন্দ্র হিসেবে জৌনপুর ছিলো বিখ্যাত। সেখানে বহু জ্ঞানী-গুণী, কবি ও সাহিত্যিকের আবির্ভাব ঘটেছিলো।
আবার, সুলতানি আমলে অনেক বিখ্যাত ঐতিহাসিকের আবির্ভাব ঘটেছিলো। তাঁদের মধ্যে মিনহাজ-ই-সিরাজের “তাবাকাত-ই-নাসিরী”, জিয়াউদ্দীন বারানীর “তারিখ-ই-ফিরোজ শাহী”, শামস-ই-সিরাজ আফিফের “তারিখ-ই-ফিরোজ শাহী”, ইয়াহিয়া বিন-আহমদের “তারিখ-ই-মুবারক শাহী”, হাসান নিজামীর “তাজুল মা’সীর” এবং ইসামীর “ফুতুহ-উস-সালাতিন” ছিলো সেই যুগের কয়েকটি বিখ্যাত ইতিহাসগ্রন্থ। এসব ইতিহাস পাঠে সুলতানি আমলের ইতিহাসের একটি ধারাবাহিক বিবরণ সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান লাভ করা যায়।
এছাড়াও, মুঘল আমলের ঐতিহাসিক বাদাউনী, আবুল ফজল, ফিরিস্তা, কাফিখান, আব্দুল হামিদ লাহোরী, নিজামুদ্দীন আহমদ বখশী প্রমুখ ইতিহাস লেখায় শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেন। মুঘল সালতানাতের প্রতিষ্ঠাতা স্বয়ং বাবর ছিলেন একজন পণ্ডিত ও কবি। তিনি “তুযক-ই-বাবুর” লিখে খ্যাতি অর্জন করেন। তাঁর আত্মচরিত ইতিহাস সাহিত্যের অন্যতম সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। সম্রাট জাহাঙ্গীরও তাঁর আত্মচরিত রচনা করে ইতিহাসে বিখ্যাত হয়ে আছেন। হুমায়ুনের ভগ্নি গুলবদন বেগম রচিত “হুমায়ুননামা”, ফিরিস্তার “তারিখ-ই-ফিরিস্তা”, আবুল ফজলের “আকবরনামা” ও “আইন-ই-আকবরী” নিযামুদ্দীনের “তাবাকাত ই-আকবরী”, আব্বাস শিরওয়ানীর “তারিখ-ই-শেরশাহী” প্রভৃতি গ্রন্থের ঐতিহাসিক মান ছিলো অত্যন্ত উঁচুস্তরের। সাহিত্যে জাহানারা ও জেবুন্নেছা সে যুগে সুনাম অর্জন করেন। মুঘল আমলে কবি হিসেবে বিখ্যাত ছিলেন ফৈজী, রামদাস, সুরদাস, তুকারাম ও রামপ্রসাদ।
স্থাপত্য শিল্প
দিল্লির সুলতানরা ভারতীয় উপমহাদেশে বিভিন্ন প্রকার নতুন স্থাপত্য শিল্পের প্রবর্তন করেন। এগুলো সাধারণত মক্কা, দামেস্ক, মিসর, বাইজান্টাইন এবং ইরানের স্থাপত্য রীতির সংমিশ্রণে ও আদর্শে নির্মিত হয়। ঐতিহাসিক ফারগুসন একে “ইন্দো-সারাসিন” বা পাঠান স্থাপত্য বলে উল্লেখ করেছেন। ঐতিহাসিক হ্যাভেল একে ভুল করে অন্তরঙ্গে ও বহিরঙ্গে হিন্দু স্থাপত্য বলে উল্লেখ করেছেন। সুলতানি যুগের স্থাপত্য শিল্পরীতি সম্পর্কে ঐতিহাসিক স্যার জন মার্শাল বলেন,
❝ইন্দো-ইসলামিক স্থাপত্য কেবলমাত্র বৈচিত্র্যময় স্থানীয় (আরবীয়) স্থাপত্য কিংবা শুধুমাত্র হিন্দু স্থাপত্যের সংশোধিত রীতি নয়। বিস্তারিতভাবে বলতে গেলে ইন্দো-ইসলামী স্থাপত্য সমানভাবে না হলেও এটা উভয় উৎসের সংমিশ্রণে উদ্ভূত হয়েছে।❞
প্রাথমিক যুগের সুলতানরা তাঁদের ইমারত নির্মাণে স্থানীয় হিন্দু কারিগরদের নিযুক্ত করতেন। ফলে ভারতীয় মুসলিম স্থাপত্যে হিন্দু প্রভাব দেখা যায়। কাজেই ইন্দো-ইসলামী স্থাপত্য শিল্পে বিশেষ কতকগুলো হিন্দু শিল্পরীতির সংমিশ্রণ দেখা যায়। পরবর্তীকালে এদেশে বিপুলসংখ্যক মুসলিম কারিগর ও শিল্পী আগমন করলে সুলতানি আমলের ইমারতগুলো নির্মাণে স্থাপত্য শিল্পে হিন্দু-প্রভাব লোপ পেতে থাকে।
দিল্লিতে মুসলমানদের প্রথম “কুওয়াতুল ইসলাম” মসজিদটি নির্মাণে কুতুবুদ্দীন আইবেক ২৭টি মন্দিরের উপাদান ব্যবহার করেন বলে জানা যায়। তাঁর নির্মিত “কুতুব মিনারটি” মূলত আজান দেওয়ার জন্য নির্মিত একটি গম্বুজ-বিশেষ। “কুওয়াতুল ইসলাম” মসজিদটির অনুকরণে কুতুবুদ্দীন আইবেক আজমীরে “আড়াই দিনকা ঝোপড়া” নির্মাণ করেন। এ যুগের উল্লেখযোগ্য নিদর্শনের মধ্যে ইলতুৎমিশ কর্তৃক বদাউনে নির্মিত মসজিদ, হাউজে শামশী, শামস-ই-ঈদগাহ প্রভৃতি ছিলো সমধিক প্রসিদ্ধ। এ’আমলে অনেক প্রাদেশিক শাসকও স্থাপত্য শিল্পের পেছনে উদারভাবে পৃষ্ঠপোষকতা করেন। জৌনপুরী শিল্পের শ্রেষ্ঠ নিদর্শনের স্বাক্ষর হিসেবে জৌনপুরের “অটলা মসজিদ”, “জাম-ই-মসজিদ” ও “লাল দরওয়াজা” প্রভৃতি নির্মিত হয়েছিলো।
বাংলার স্বাধীন সুলতানগণের দ্বারা নির্মিত পাণ্ডুয়ার আদিনা মসজিদ, বাগেরহাটের ষাট গম্বুজ মসজিদ, দরবেশ খানজাহান আলীর মাজার, গৌড়ের ছোট সোনা মসজিদ, বড় সোনা মসজিদ, কদম রসুল মসজিদ, হুসেন শাহের সমাধি ইত্যাদি বাংলার স্থাপত্য শিল্পের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। এছাড়াও মালবের রাজধানী মণ্ডুতে নির্মিত জামে মসজিদ, হিন্দু মহল, জাহাজ মহল, হুসাং শাহের সমাধি, বাহাদুর শাহের প্রাসাদ, গুলবর্গার জামে মসজিদ, ফিরোজ শাহ বাহমনীর সমাধি সৌধ, মাহমুদ গাওয়ানের মাদরাসা ভবন, আহমেদাবাদের জামে মসজিদ ইত্যাদি সেই যুগের স্থাপত্য শিল্পের এক অক্ষয় স্বাক্ষর বহন করে আছে।
মুসলিম স্থাপত্য রীতিতে ভারতীয়, মিসরীয়, ইরানি, সিরীয়, বাইজান্টাইন রীতির এক অপূর্ব সংমিশ্রণ ঘটে। এ রীতির চূড়ান্ত বিকাশ ঘটে মুঘল আমলে।
মুঘল আমলের স্থাপত্যশিল্পে ভারত বিশ্ববিখ্যাত ছিলো। উল্লেখযোগ্য স্থাপত্যশিল্পসমূহ হলো, তাজমহল, লালকেল্লা, ফতেপুর সিক্রি, হুমায়ুনের সমাধি ভবন এবং ইতমাদ্দৌলার সমাধি। মুঘলদের এই বিরাট কর্মযজ্ঞে অসংখ্য দক্ষ শ্রমিক আত্মনিয়োগ করেছিলো। তাদের দক্ষতায় ভারতীয় ও পারসিক শিল্পের সমন্বয়ে এক নতুন শিল্পধারা ভারতে প্রবর্তিত হয়েছিলো। এই স্থাপত্যশিল্পের মূল উপাদান ছিলো ইট, পাথর ও চুন। শ্বেতপাথর ও লালপাথরের নিখুঁত ব্যবহারে স্থাপত্য শিল্প এক অভাবনীয় মর্যাদার অধিকারী হয়েছিলো।
এই স্থাপত্য শিল্পের সঙ্গে যেমন মুঘল রাজমিস্ত্রি জড়িত ছিলো, তেমনি এসব উপাদান সরবরাহের কাজে হাজার হাজার মানুষও ছিলো জড়িত। ইট, বালি ও পাথর শিল্প ব্যাপকভাবে সম্প্রসারিত হয়। এ’যুগে সৌধশিল্প উন্নতির চরম শিখরে আরোহণ করে। রাষ্ট্রের পৃষ্ঠপোষকতা ছাড়া এ’ধরনের উৎকর্ষ লাভ কখনই সম্ভব ছিলো না। গ্রামে ও শহরে গৃহনির্মাণকারী, খাল খননকারী, পাথর কাটার কারিগর, ইট প্রস্তুতকারী, রাজমিস্ত্রি, কাঠচেরাইকারী, খোদাইশিল্পী, পালিশের কারিগর, ছাদপেটাই মিস্ত্রি, চুন প্রস্তুতকারক, কুয়োখননকারী ইত্যাদি অসংখ্য কারিগর সহজলভ্য ছিলো। পাশাপাশি, দুর্গ, প্রাসাদ, বাড়ি, মন্দির, সেতু, রাস্তা জাহাজ ইত্যাদি নির্মাণে অনেক শ্রমিক নিয়োজিত ছিলো।
এখানে এটা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, তাজমহল নিয়ে সম্রাট শাহজাহান-এর নামে চরম যে মিথ্যাচার করা হয়, ইতিহাসে আদতে তার কোনো অস্তিত্বই নেই। এমনকি, ভারত সরকার পর্যন্ত এমন মিথ্যাচারিতার বিপরীত মন্তব্য পোষণ করেছে।
সঙ্গীত
ইসলামের প্রভাবে ভারতে সঙ্গীতেও ব্যাপক পরিবর্তন ঘটে। কবি, সঙ্গীতজ্ঞ আমীর খসরু সঙ্গীতের তত্ত্বগত ও ব্যবহারগত দিক দিয়ে বিশেষ দক্ষ ছিলেন। তিনি অনেক পারসিক রাগ যেমন—ইমন, ঘোর, খানম প্রভৃতি ব্যবহার ভারতে করেন। ভারতে তবলা, সেতার প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্রে ইসলামের যথেষ্ট প্রভাব ছিলো। উত্তর ভারতের উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতকে এক বিশিষ্ট উচ্চতায় প্রতিষ্ঠিত করার জন্য মুসলমানদের যথেষ্ট অবদান অনস্বীকার্য। দিল্লির সুলতানি আমলে সঙ্গীতে হিন্দু-মুসলিম সমন্বয় ঘটে। জৌনপুরের সুলতান ইব্রাহীম শাহ শর্কীর পৃষ্ঠপোষকতায় উভয় ধারার সমন্বয় ঘটে। দিল্লির তুঘলক বংশের সুলতান ফিরোজ শাহ তুঘলক সঙ্গীতের সমন্বয় ঘটান। তাঁর সময়ে ভারতীয় ক্লাসিক গ্রন্থ “রাগদর্শন” ফার্সি ভাষায় অনূদিত হয়।
সম্রাট বাবর, হুমায়ুন, আকবর সঙ্গীতে বিশেষজ্ঞ ছিলেন, এমনকি সকলেই সঙ্গীত শাস্ত্রের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। বিলাস খান, লালাখান, তানসেন প্রমুখ গায়ক ছিলেন মুঘল দরবারের অলংকারস্বরূপ। তানসেনের জামাতা লালাখান, জনার্দন ভাট, মহাপট্টক, জগন্নাথ ছিলেন সম্রাট শাহজাহানের দরবারের প্রধান সঙ্গীতজ্ঞ। আবুল ফজলের মতে,
❝আকবরের দরবারে প্রায় ৩৬ জন গায়ক সম্রাটের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করতেন। তানসেন-এর ন্যায় গায়ক গত দু’শ’ বছরেও ভারতবর্ষে দেখতে পাওয়া যায়নি।❞
মালবের বাজ বাহাদুর ছিলেন আরেকজন হিন্দি গায়ক। সঙ্গীত শিল্পী হিসেবে সাধক রামাদাস বিখ্যাত ছিলেন। জৌনপুরের হুসেন শাহ শরকী, বিজাপুরের আদিল শাহ এবং লখনৌর নবাব ওয়াজিদ আলী শাহ মুঘল আমলের শেষের দিকে প্রখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞদের অকাতরে পৃষ্ঠপোষকতা প্রদর্শন করতেন। এসময় কলকাতায় উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের কেন্দ্র গড়ে উঠেছিলো। মুঘল সম্রাট জাহাঙ্গীর ও সম্রাজ্ঞী নূরজাহান সঙ্গীতের উদার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। সম্রাট জাহাঙ্গীরের সময়ে ঐতিহাসিক মোহাম্মদ শালীহ এবং তার ভাইও সঙ্গীতে বিখ্যাত ছিলেন। জাহাঙ্গীর স্বয়ং একজন সুদক্ষ সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন। তিনি অসংখ্য হিন্দি সঙ্গীত রচনা করে খ্যাতি অর্জন করেন। সঙ্গীতানুরাগী বাদশাহ হিসেবে সর্বজনবিদিত শাহজাহান দিল্লির দিওয়ান-ই-খাসে প্রতি সন্ধ্যায় সঙ্গীতের আসর বসাতেন। ঐতিহাসিক জে. এন. সরকার বলেন,
❝শাহজাহানের সুমধুর কণ্ঠস্বর এতই আকর্ষণীয় ছিলো যে, বহু সুফি দুনিয়ার সকল মোহমুক্ত হওয়া সত্ত্বেও তাঁর সান্ধ্য আসরে এসে যোগদান করতেন এবং গান শুনতে শুনতে আবেগে আপ্লুত হয়ে পড়তেন।❞
💠রাজনীতি, প্রশাসন ও বিচারব্যবস্থায় সম্প্রীতি ও সৌহার্দ
মুসলিম পূর্ব ভারত
মুসলিম বিজয়ের প্রাক্কালে ভারতের রাজনৈতিক অবস্থা চরম বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতাপূর্ণ ছিলো। ভারতীয় উপমহাদেশ তখন অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বাধীন রাজ্যে বিভক্ত ছিলো। এ রাজ্যগুলোর মধ্যে ছিলো না কোনো একতা। অধিকন্তু, তাদের মধ্যে বিবাদ-বিসম্বাদ ও যুদ্ধ-বিগ্রহ লেগেই থাকতো। এর ফলে ভারতীয় উপমহাদেশের কোনো রাষ্ট্রীয় স্থায়িত্ব ছিলো না। আর সামাজিক দিক দিয়ে সংকীর্ণতা, শ্রেণিগত বৈষম্য, বর্ণপ্রথা সমাজকে একেবারে কলুষিত করে দিয়েছিলো।
মৌর্য সম্রাট অশোক উত্তরে হিমালয় ও উত্তর-পশ্চিমে হিন্দুকুশ পর্বতমালা হতে দক্ষিণে মহীশূর এবং পশ্চিমে পারস্যের সীমানা ও আরব সাগর হতে পূর্বে ব্রহ্মপুত্র পর্যন্ত এক বিশাল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে ভারতবর্ষে একক রাজনৈতিক প্রভুত্ব কায়েম করতে সক্ষম হন। খ্রিস্টপূর্ব ২৩২ অব্দে তার মৃত্যুর পর হর্ষবর্ধন উত্তর ভারতে এবং চাণক্য সম্রাট পুলকেশিন মোটামুটিভাবে ভারতে রাজনৈতিক ঐক্য প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছিলেন। কিন্তু, তাদের মৃত্যুর পর ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ঐক্য বিনষ্ট হয়। সমগ্র ভারতবর্ষ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রে বিভক্ত হয়ে পড়ে। প্রখ্যাত ঐতিহাসিক V.A. Smith (ভিনসেন্ট স্মিথ) বলেন, ❝ভারতবর্ষের ইতিহাসের আংশিক ঐক্য হর্ষের সঙ্গেই বিলুপ্ত হয়েছিলো।❞
পরবর্তীতে কেন্দ্রীয় শক্তির অভাবে রাজনৈতিক বিচ্ছিন্নতা, প্রজাদের প্রতি অবজ্ঞা-অবহেলা, গোত্রীয় বিরোধ, বিভিন্ন রাজ্যগুলোর মধ্যকার যুদ্ধ-সহ ইত্যকার নানা কারণে মুসলিম বিজয়ের প্রাক্কালে ভারতের রাজনৈতিক অবস্থা একেবারে চরম বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতায় পরিপূর্ণ হয়ে পড়েছিলো। ফলশ্রুতিতে, শাসকদের অত্যাচারে একপ্রকার অতীষ্ঠ হয়ে নির্যাতিত ও নিপীড়িত জনগণ মুসলিম শাসকদের নিকটই সাহায্য প্রার্থনা করে। অতএব, এটা সুস্পষ্ট যে, ভারত বিজয়ের পথ উন্মোচন হয় মূলত স্থানীয়দেরই সাহায্যের মাধ্যমে।
এই যদি হয় মুসলিম পূর্ব ভারতের রাজনৈতিক অবস্থা, তাহলে প্রশাসনিক ও বিচারব্যবস্থার কথা জ্ঞানীমাত্রই উপলব্ধি করতে পারবেন। রাজনৈতিক এমন বিশৃঙ্খলার সময় যে নিরবচ্ছিন্নভাবে প্রশাসনিক কার্যক্রম পরিচালনা করা সম্ভব নয়, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। আর প্রশাসনিক কার্যক্রমই যখন এমন হয়ে পড়ে, তখন সমগ্র বিচারব্যবস্থাই যে ডুমুরের ফুলের মতো অস্পৃশ্য হয়ে পড়বে, সেটাও আর কলমের ডগায় ফুটিয়ে তোলার প্রয়োজন মনে হয় না। অধিকন্তু, ধর্মীয় ও সামাজিক সম্প্রীতির বিষয়টাই যেখানে উপেক্ষিত এবং স্বার্থান্বেষণ ও স্বার্থসিদ্ধিই যেখানে একমাত্র লক্ষ্য হয়ে পড়ে, সেখানে বিচারব্যবস্থা যে চরম স্বেচ্ছাচারিতা আর একনায়কতন্ত্রে রূপ লাভ করবে, এই বিষয়টাও সহসাই উপলব্ধি করা যায়। আবার যেখানে জাতপ্রথার নিরিখেই সমাজের ভালোমন্দের তারতম্য হয়, সেখানে আদতে বিচারব্যবস্থার নাম নেওয়াটাই বিলাসিতা।
মুসলিম ভারত
পক্ষান্তরে, মুসলিম ভারতে এর উল্টোচিত্র দেখা যায়।
এই প্রবন্ধের একেবারে শুরুতেই মুসলিম ভারতের ধারাবাহিক ইতিহাস বর্ণনার মাধ্যমে ভারতে মুসলিম শাসনের রাজনৈতিক ধারার সফলতার বিষয়টি ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। এরপর একাধারে ধর্ম, সমাজ, সংস্কৃতি, শিক্ষা ও সাহিত্যে মুসলিম শাসনামলের এতোসব উৎকর্ষতা, সম্প্রীতি ও সৌহার্দ-এর প্রমাণ দেওয়ার মাধ্যমে প্রশাসনিক কার্যক্রমের শক্তিমত্তা ও সমৃদ্ধশালিতার বিষয়টি সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। তথাপি, আরেকটু আলোচনা করা যাক।
প্রশাসন
মুসলিম শাসনামলে প্রত্যেক শাসকই ভারতের প্রশাসন ব্যবস্থা বা প্রশাসনিক কার্যক্রমকে ক্রমান্বয়ে যুগোপযোগী করে তোলার প্রচেষ্টায় ব্যস্ত থাকতেন। মুসলিম পূর্ব ভারতে যেখানে প্রশাসনিক ব্যবস্থাই ছিলো সম্পূর্ণ বিশৃঙ্খল এবং হ-য-ব-র-ল, সেখানে মুসলিম শাসনামলে সমগ্র অঞ্চল জুড়ে শাসন ব্যবস্থা জারি রাখার জন্য একটি সুনির্দিষ্ট অবকাঠামো দাড় করানো হয়েছিলো। রাষ্ট্রের প্রতিটি সেক্টরকেই স্বতন্ত্র মর্যাদা দেওয়া হয়েছিলো। আইন, শাসন, বিচারবিভাগ-সহ সকল গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ প্রতিনিয়তই শাসক তদারকি করতেন। এমনকি, এগুলোর প্রতিটিরই আবার অসংখ্য সাব-ডিপার্টমেন্ট ছিলো। এছাড়াও, কৃষি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক, অর্থনৈতিক এবং সামরিক ক্ষেত্রেও স্বতন্ত্র বিভাগ বা মন্ত্রণালয় ছিলো।
এর বাইরেও জনসাধারণের সুবিধার্থে স্থানীয় প্রতিনিধিও নিয়োগ করা হতো। প্রতিটি অঙ্গরাজ্যের রাজ্য-প্রধান সে রাজ্যটিকে একজন স্বাধীন শাসকের মতোই শাসন করতো। তবে, তাঁরা শাসক বা উজির/মন্ত্রীর নিকট জবাবদিহিতার ক্ষেত্রে দায়বদ্ধ থাকতো; তাঁদের নিকট নিয়মিত জবাবদিহি করতো হতো।
প্রশাসনিক কার্যক্রমে কখনও স্বজনপ্রীতির আশ্রয় নেওয়া হয়নি ভারতের মুসলিম শাসনামলে। সবসময় যোগ্য ব্যক্তিকেই প্রশাসনিক কার্যক্রমের দায়িত্ব দেওয়া হতো। এক্ষেত্রে হিন্দু-মুসলিম ধর্মীয় বিভাজন কখনই প্রশ্রয় পায়নি। এমনকি এটা পর্যন্ত শোনা যায় যে, দিল্লির সুলতানি আমলে দেশীয় মুসলমানদের বিপরীতে ভিন্নধর্মী স্থানীয়দেরকে প্রশাসনিক কার্যক্রমে সুযোগ দেওয়া হতো। সুলতান কুতুবুদ্দীন আইবেক থেকে শুরু করে ইব্রাহীম লোদী পর্যন্ত এই ৩২০ বছরে দরবারে উজির বা প্রধান সেনাপতির (সিপাহসালার) পদ কোনো ভারতীয় মুসলমান পায়নি। সেসময় অমুসলিম নাগরিকদের প্রতিই উদারতা প্রদর্শন করা হয়।
আবার, মুঘল আমলে সম্রাট আকবরের মনসবদারি প্রথা এবং রাজপুতনীতির দিকে তাকালেই বুঝা যায়, তিনি ধর্মীয় দিক থেকে অর্থাৎ হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতিতে কতোটা উদার ছিলেন। সম্রাট জাহাঙ্গীর ও শাহজাহানের ক্ষেত্রে ডক্টর বেনী প্রসাদের মন্তব্য হলো, ❝তাদের ধর্মীয় নীতি ছিলো পরধর্মে সহিষ্ণুতার উপর প্রতিষ্ঠিত।❞
মুঘল আমলে মনসবদারি পদ্ধতিতে সামরিক বাহিনী গড়ে তোলা হয়। এই মনসবদারি প্রথা মুঘলদের নতুন উদ্ভাবন নয়। মুঘলদের আগে সম্ভবত মধ্য এশিয়ায় এই প্রথা প্রচলিত ছিলো। মোঙ্গল নেতা চেঙ্গিস খান ও তৈমুর লং-এর শাসনামলে মনসবদারি প্রথা প্রাথমিক পর্যায়ে ছিলো। সৈন্যবাহিনীকে বিভিন্ন পদমর্যাদার রীতি সুলতানি আমলেও চলে আসছিলো। শেরশাহ এবং তাঁর পুত্র ইসলাম শাহ সেনাবাহিনীর নতুন সংস্কার সাধন করেন। বাবর ও হুমায়ুন সময় ও সুযোগের অভাবে সেনা বিভাগের তেমন কোনো সংস্কার করে যেতে পারেননি। সিংহাসনে আরোহণ করে আকবর সেনাবাহিনীর শোচনীয় অবস্থা লক্ষ্য করলে তিনি সাম্রাজ্য রক্ষার খাতিরে সেনাবাহিনীকে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে বিন্যস্ত করার সিদ্ধান্ত নেন। তিনি শাহবাজ খানের মাধ্যমে মনসবদারি প্রথার উপর ভিত্তি করে এক অভিনব সামরিক সংগঠন সৃষ্টি করেন। তাঁর এই প্রথার মূল উদ্দেশ্যই ছিলো সেনাবাহিনীর পুনঃগঠন করা। আকবর এই মনসবদারি প্রথা প্রবর্তন করে মুঘলদের সামরিক ইতিহাসে চির স্মরণীয় হয়ে রয়েছেন।
বিচারব্যবস্থা
মুসলিম শাসকগণ আইনের প্রতি ছিলেন শ্রদ্ধাশীল। জাতি, ধর্ম, বর্ণ-নির্বিশেষে সবার জন্য আইন ছিলো সমান। আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় দিল্লির সুলতানরা বদ্ধপরিকর ছিলেন। সমাজে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় দিল্লির সব সুলতান আপ্রাণ চেষ্টা করতেন। সুলতান গিয়াসুদ্দীন বলবন একটি শিকল বাঁধা ঘণ্টা ঝুলিয়ে রাখতেন, যেনো যেকোনো বিচারপ্রার্থী খুব সহজেই সুলতানের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারে। প্রখ্যাত পরিব্রাজক ইবনে বতুতা বলেন,
❝জনসাধারণের অভিযোগ শ্রবণের জন্য তাঁর প্রাসাদে শিকলে বাঁধা একটি ঘণ্টা ঝুলিয়ে দেওয়া হতো এবং অভিযোগকারীরা তা বাজিয়ে সুলতানের দৃষ্টি আকর্ষণ করতো।❞
তাছাড়া, বিচার কার্যের জন্য আইন হিসেবে কুরআন, হাদিস, ইজমা ও কিয়াস ব্যবহার করা হতো। সুলতান গিয়াসুদ্দীন বলবন ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় এতো বেশি কঠোর ছিলেন যে, অপরাধীরা ভয়ে থর থর করে কাঁপতো। এ প্রসঙ্গে প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ঈশ্বরী প্রসাদ বলেন,
❝সুলতানের (বলবন) ন্যায়বিচারের জন্য লোকে এতই ভীতসন্ত্রস্ত থাকতো যে, কেউ কখনো ভৃত্য এবং ক্রীতদাসদের প্রতি অসদাচরণ করতে সাহস পেতো না।”
মুঘল আমলে সাম্রাজ্যের বিচার বিভাগীয় প্রধানকে বলা হতো “কাজী-আল-কুজ্জাত” বা “প্রধান বিচারপতি”। তাঁকে হতে হতো আইনজ্ঞ, ন্যায়পরায়ণ, সুন্দর চরিত্রের অধিকারী ও নিষ্ঠাবান মুসলমান। তিনি হিন্দু-মুসলিম সম্প্রদায়ের দেওয়ানি ও ফৌজদারি বিচার করতেন। তাছাড়া প্রাদেশিক কাজী, সরকার কাজী, পরগণা কাজী ও কাজী-ই-আসকার (সেনাবাহিনীর সঙ্গের কাজী) বিচারকার্য সমাধান করতেন।
বিচারব্যবস্থায় মুফতীদের বিশেষ ভূমিকা ছিলো। তাঁরা বেতনভুক্ত সরকারি কর্মচারী ছিলেন না। তবে প্রয়োজনে কাজী তাঁদের ধর্মীয় বিষয়ে মতামত গ্রহণ করতেন। তারা শরিয়ত অনুযায়ী “ফতোয়া” দিতেন। যখন কাজী কোনো কারণে বিচারকার্য পরিচালনা করতে পারতেন না, তখন “মীর আদিল” তাঁর কার্য-সম্পাদন করতেন। তিনি কাজীর তুলনায় ঊর্ধ্বতন কর্মচারী ছিলেন।
মুঘল আমল ছিলো একনায়কতান্ত্রিক শাসন, রাষ্ট্রের সব ক্ষমতার উৎস ছিলো সম্রাটের হাতে। তারপরও মুঘল সম্রাটরা আইনের ঊর্ধ্বে ছিলেন না। কারণ, তাঁকে যেমন শরিয়ত মোতাবেক চলতে হতো, আবার তেমনি শরিয়তের পাশাপাশি সম্রাটকে রাষ্ট্রের অভিজাত সম্প্রদায়, সেনাবাহিনী, উলামা ও আইন বিশারদদের সমর্থন লাভ করতে হতো। তাঁরা ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় ছিলেন বদ্ধপরিকর। দোষী যেই হোক না কেনো, শাস্তি তাকে পেতেই হতো। সম্রাট জাহাঙ্গীর তাঁর প্রিয়তমা স্ত্রী নূরজাহানের অপরাধের বিরুদ্ধে রায় দেন। সম্রাট আওরঙ্গজেব ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় তাঁর পুত্রের বিরুদ্ধেও শাস্তি দিতে দ্বিধাবোধ করেননি। সম্রাট আকবর বলতেন, ❝আমি স্বয়ং কোনো অপরাধ করলেও নিজের বিরুদ্ধে রায় দিবো।❞
কাজেই বলা যায় যে, মুঘল সম্রাটরা আইনের ঊর্ধ্বে ছিলেন না।
ভারতীয় উপমহাদেশে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় মুঘলদের অবদান ছিলো অপরিসীম। প্রত্যেক মুঘল সম্রাটই সমাজে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করে গিয়েছেন, তা ইতিহাসের পরতে পরতে প্রমাণ বহন করে চলেছে। ইসলামী আইনের চোখে সবাই ছিলো সমান। ইবনে হাসান বলেন, ❝এটা নিশ্চিত যে, মুঘল বিচার পদ্ধতি ছিলো যুগের ও সমাজের জন্য উপযোগী।❞
মুসলিম শাসনামলে বিচারব্যবস্থার নমুনা
মুসলিম শাসনামলে বিচার ব্যবস্থা কেমন ছিলো, তার তিনটি উপমা নিচে উপস্থাপন করা হলো।
প্রথম
সুলতান গিয়াস উদ্দিন আযম শাহ ছিলেন বাংলার শ্রেষ্ঠ সুলতানদের অন্যতম এবং ইলিয়াস শাহী বংশের সর্বশেষ শ্রেষ্ঠ সুলতান। সুলতান গিয়াস উদ্দিন শাহ একজন ন্যায়বিচারক শাসক ছিলেন। রিয়াজ-উস-সালাতিনে সুলতানের ন্যায়বিচারের একটি কাহিনী রয়েছে। তিনি একদা তীর ছুঁড়তে গিয়ে এক বিধবা মহিলার পুত্রকে হত্যা করে ফেলেন। বিধবা মহিলা তৎকালিন প্রধান বিচারপতি কাজী সিরাজ উদ্দিনের কাছে বিচারপ্রার্থী হলেন। প্রধান বিচারপতি নির্ভয়ে সুলতানের নামে সমন জারী করলেন। সুলতান বিচারপতির আদালতে হাজির হলে বিচারপতি কোনো রকম সম্মান প্রদর্শন না করে তাঁর বিরুদ্ধে বিধবার আনীত অভিযোগের কথা উল্লেখ করেন এবং বিধবাকে ক্ষতিপূরণ দানে সন্তুষ্ট করতে না পারলে শরীয়ত মতে সুলতান দণ্ডপ্রাপ্ত হবেন বলে অভিমত প্রকাশ করেন। সুলতান বিধবাকে বিপুল পরিমাণ অর্থ দিয়ে সন্তুষ্ট করেন এবং বিধবা অভিযোগের সন্তোষজনক মিমাংসার কথা বিচারপতিকে অবহিত করেন।
সুলতান তখন শাহী আসন থেকে উঠে এসে বিচারপতিকে সালাম দিয়ে বলেন,
❝আমার রাজ্যে এমন একজন ন্যায় বিচারক আছেন এজন্য দুনিয়া ও আখেরাতের মালিক আল্লাহর দরবারে শুকরিয়া আদায় করছি। বিচারপতি, আপনি আইনের বিধান লঙ্ঘন করলে আমার তরবারি দিয়েই আমি আপনার মস্তক ছেদ করতাম।❞
প্রতি উত্তরে বিচারপতি বলেন,
❝আমার নির্দেশ আপনি অমান্য করলে আমিও আপনাকে বেত্রাঘাত করতাম।❞
পরবর্তীতে, সুলতান বিচারপতিকে ন্যায়বিচারের জন্য পুরষ্কৃত করেন।
দ্বিতীয়
একবার সম্রাট আলমগীরের সৈন্যবাহিনী এক মুসলিম সেনাপতির অধীনে পাঞ্জাবের এক পল্লীর মধ্য দিয়ে যাচ্ছিলো। হঠাৎ পথিমধ্যে জনৈক ব্রাক্ষণের এক অপরূপ সুন্দরী কন্যার প্রস্ফুটিত গোলাপের মত মুখশ্রী দেখে লোভাতুর সেনাপতি তার পিতার নিকট মেয়েটিকে বিবাহের প্রস্তাব দিয়ে বসে এবং সিদ্ধান্ত জারি করে যে, আজ থেকে এক মাস পরেই সে তার বাড়ীতে বর-বেশে উপস্থিত হবে। কন্যার পিতা নিজে সম্রাট আলমগীরের নিকট গিয়ে সমস্ত ঘটনা খুলে বলে বাদশার সাহায্য প্রার্থনা করলেন। সম্রাট তাঁকে আশ্বাস দিয়ে বাড়ি ফিরে যেতে বললেন। সাথে এ-ও জানালেন যে, নিদিষ্ট দিনে তিনি ব্রাহ্মণের বাড়িতে উপস্থিত থাকবে। ব্রাহ্মণ নানা চিন্তার ঝুঁকি নিয়ে বাড়ি ফিরলেন। এরপর, বিবাহের আগের দিন সম্রাট আলমগীর একাই এসে উপস্থিত হলেন ব্রাহ্মণের বাড়িতে। ব্রাহ্মণ হতবাক!
সম্রাট সেই দরিদ্র ব্রাহ্মণের এক পুরাতন জীর্ণ কামরায় সারা রাত এবাদত বন্দেগী ও মোনাজাত-প্রার্থনায় অশ্রুবিসর্জন করে কাটালেন। ব্রাহ্মণের পরিবারবর্গ এ দৃশ্য দেখার পর আবারও অবাক হলেন। পরদিন মুঘল সেনাপতি বর-বেশে ব্রাহ্মণের ঘরে উপস্থিতি হলো। বিবাহের পূর্বে কন্যাকে একবার দেখা উত্তম। সেজন্য, সেনাপতি কন্যাকে দেখতে চাইলো। প্রত্যুত্তরে ব্রাহ্মণ সম্রাটের শেখানো অনুযায়ী সম্রাটের কামরার দিকেই ইশারা করলেন। সেনাপতি ঘরে প্রবেশ করেই দেখলো খোলা তরবারি হাতে সম্রাট আলমগীর বসে রয়েছেন।
যৌবনের বুকভরা আবেগ আর মুখভরা হাসি নিমিষেই সম্রাটকে দেখার পর অদৃশ্য হয়ে গেলো। যে সেনাপতির দাপটে শত্রু সৈন্যরা থরথর করে কাঁপে, যার মাঝে ভয়-ভীতি অথবা দুর্বলতা কখনও স্থান পায় না, আজ সেই মহাবীর কালবৈশাখী ঝড়ের মতো ভীষণ শব্দে যেনো কেঁপে উঠলো। নিজেকে সামলে নিয়ে ক্ষমা চাওয়ার চেষ্টা করলেও দুঃখ, লজ্জা, শাস্তি আর অপমানের আশংকায় সেনাপতি জ্ঞান হারিয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়লো। কন্যার পিতা সম্রাট আলমগীরের সুবিচার, দায়িত্ববোধ আর অসাম্প্রদায়িক ভূমিকা দেখে আনন্দে বললেন,
❝আপনি আমার, বিশেষ করে আমার কন্যার ইজ্জত রক্ষা করেছেন। আপনার এই ঋণ অপরিশোধ্য।❞
সম্রাট আলমগীর ব্রাহ্মণকে বুকে জড়িয়ে আলিঙ্গন করে বললেন,
❝এই মহান দায়িত্ব আমার। আমি যে আমার উপর অর্পিত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করতে পেরেছি এতেই আমি ধন্য।❞
তৃতীয়
মুঘল সম্রাজ্ঞী নূরজাহান ছিলেন আঠারো শতকের ভারতের সবচেয়ে ক্ষমতাশীল নারীদের একজন। জন্মের সময় তার নাম দেয়া হয়েছিলো মিহরুন নিসা। কিন্তু স্বামী মুঘল সম্রাট জাহাঙ্গীর পরে তার নাম পাল্টে রেখেছিলেন নূরজাহান (জগতের আলো)। নূরজাহান কবি, স্থপতি ও দক্ষ শিকারি ছিলেন। তিনি সম্রাট জাহাঙ্গীরের সবচেয়ে প্রিয়তম স্ত্রীতে পরিণত হন। সারাটি দিন তিনি নুরজাহানকে নিয়ে সদা ব্যস্ত থাকতেন। নিজ স্ত্রীর বিচার করার ইতিহাস পৃথিবীতে বিরল হলেও সম্রাট জাহাঙ্গীর ন্যায়বিচার করে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে।
সম্রাট জাহাঙ্গীরের সেই সময়ে সাধারণ প্রজাদের সরাসরি সাক্ষাতের কোনো অনুমতি ছিলো না। তিনি তখন মুজাদ্দিদে আলফেসানীর পরামর্শে দরবারের বাইরের ফটকে একটি শিকল রাখেন, যেটি একেবারে সম্রাট জাহাঙ্গীরের শয়নকক্ষ পর্যন্ত সংযুক্ত ছিলো, যার সঙ্গে একটা ঘণ্টাও বাঁধা ছিলো। যেকোনো অত্যাচারিত, উপবাসী, অবহেলিত কেউ অথবা রাজকর্মচারীদের দ্বারা যার কাজ সমাধান হয়নি, এমন মুসলিম-অমুসলিম প্রজা সেই শিকল টানলেই বাদশাহ জাহাঙ্গীর তাঁকে সঙ্গে সঙ্গে তাকে কক্ষে ডাকতেন এবং তাঁর সন্তোষজনক সমাধান করেই তবে ক্ষান্ত হতেন।
একদিন রূপ লাবণ্যের জীবন্ত প্রতীক নুরজাহান আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে রূপচর্চা করছিলেন। এমন সময় এক বিকৃত মস্তিষ্ক হিন্দু প্রজা বিনা অনুমতিতেই নুরজাহানের কক্ষে উপস্থিত হয়ে পড়েন। নুরজাহান সঙ্গে সঙ্গে হিন্দু প্রজাকে গুলি করে মেরে ফেলেন। নিহত হিন্দু প্রজার আত্মীয় শিকল টানলেন এবং জাহাঙ্গীরের নিকট নুরজাহানের বিরুদ্ধে বিচারপ্রার্থী হলেন। বিচারকের আসনে তখন জাহাঙ্গীর এবং আসামীর কাঠগড়ায় তাঁর প্রিয়তমা স্ত্রী নূরজাহান। কঠিন এই মুর্হুতেও সম্রাট জাহাঙ্গীর ভুললেন না ইসলামের বিধান। জাহাঙ্গীর তাঁর প্রিয়তমা সুন্দরী স্ত্রীর ব্যাপারে রায় ঘোষণা করলেন মৃত্যুদন্ড। রায় ঘোষণার সাথে সাথে সকলেই হতবাক হয়ে গেলেন। স্বয়ং নূরজাহান তখন কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়লেন। এমন সময় সম্রাট জাহাঙ্গীরের মন্তব্য ছিলো,
❝ইসলামের আইনে তুমি তাকে হত্যা করতে পারতে কারোর প্রাণনাশের বা ব্যাভিচারের অপরাধে। কিন্তু সে দোষ তো তার ছিলো না। সে ছিলো বিকৃত মস্তিষ্ক। অতএব, আমি আবার বলছি চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হলো, তোমার মৃত্যুদন্ড।❞
একজন মহান শাসক কর্তৃক ইসলামের এই ইনসাফ-ভিত্তিক ন্যায়বিচার দেখে বিচারপ্রার্থী হিন্দু প্রজারা কান্নাজড়িত কন্ঠে বলেছিলো,
❝হে ন্যায়পরায়ণ বাদশা! আমরা প্রাণদন্ড চাই না। নূরজাহানকে আমরা ক্ষমা করে দিলাম। কারণ, তিনি তো আর ইচ্ছে করে খুন করেননি। তিনি যা করেছেন তা তো নিজের আত্মরক্ষার জন্যই করেছেন।❞
💠অর্থনৈতিক সম্প্রীতি ও সৌহার্দ
মুসলিম পূর্ব ভারত
পূর্বেই বলা হয়েছে, সমগ্র ভারতবর্ষ হলো মহান রবের নেয়ামতধন্য অপার এক লীলাভূমি। কিন্তু, এতো নেয়ামত সত্ত্বেও মুসলিমপূর্ব ভারতের অর্থনৈতিক অবস্থা ছিলো সম্পূর্ণ ভঙ্গুর। দু’বেলা দু’মুঠো আহারের জন্য জনসাধারণের হাড়ভাঙা পরিশ্রম করতে হতো। এসব বিশৃঙ্খলা ও নৈরাজ্যের অন্যতম কারণ ছিলো, অর্থনীতির সুষমবণ্টন না থাকা এবং যোগ্য অর্থনীতিবীদ না থাকা। অবশ্য, যেখানে ধর্মের নামে অধর্ম চর্চা করা হতো, শাসনের নামে জনগণকে শোষণ করা হতো, জাতিভেদ ও জাতপ্রথা যেখানে সমাজকে পুরোপুরি ধ্বংস করে দিয়েছিলো—সর্বোপরি, ভারতের সামগ্রিক অবস্থাই ছিলো যেখানে বিশৃঙ্খল, সেখানে অর্থনৈতিক সুদিনের বিষয় কল্পনা করাটাই ছিলো অতিরঞ্জন। বর্তমান সময়ের মতোই সেসময়েও ধনীরা হয়ে যেতো আরো ধনী এবং দরিদ্ররা হয়ে যেতো একেবারে নিঃশেষ; ভাগ্যের নির্মম পরিহাসে কিছুদিনের মাথায় স্বাধীন ব্যক্তি হয়ে যেতো কোনো একজনের কৃতদাস। কিছুদিন পূর্বে একই ঘরে বসবাস করা একই পরিবারের সদস্যদের ঠিকানা হতো ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে।
ভারতবর্ষ ছিলো একটি কৃষিপ্রধান দেশ। কৃষককে তার উৎপাদিত ফসলের এক ষষ্ঠাংশ (৬ ভাগের ১ ভাগ) রাষ্ট্রকে কর হিসেবে দিতে হতো। এ করকে “ভাগ” বলা হতো। ঐতিহাসিকদের মতে, মৌর্য ও গুপ্ত যুগে ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক অবস্থা ভালো ছিলো। এ সময়ে ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্পের ব্যাপক উন্নতি হয়। খ্রিস্টীয় ৫ম শতাব্দীতে বিখ্যাত চীনা পর্যটক ফা-হিয়েন ভারতে আসেন। তিনি গুপ্ত যুগে ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক বিবরণ দেন। তার মতে মগধের লোক সমৃদ্ধশালী ও ধনী ছিলো এবং তাদের মধ্যে সৎ কাজ করার প্রবণতাও ছিলো। এ সময়ে বাংলার তাম্রলিপ্তি বন্দর একটি প্রসিদ্ধ বাণিজ্য কেন্দ্র ছিলো। এখান থেকে বঙ্গদেশের বণিকরা বড় বড় জাহাজে সিংহল, মালয়, যবদ্বীপ প্রভৃতি অঞ্চলে বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে যাতায়াত করতো। ভারতবর্ষে শিল্পের যথেষ্ট প্রসার ঘটে। কার্পাস বস্ত্র উৎপাদন এবং রপ্তানির জন্য গুজরাট এবং বাংলাদেশ খ্যাতি লাভ করে। ঢাকার মসলিন ছিলো সেসময় পৃথিবী বিখ্যাত।
সে যাইহোক, ভারতবর্ষ অর্থনৈতিক দিক দিয়ে যথেষ্ট সমৃদ্ধশালী থাকলেও সম্পদ বণ্টন ও ভোগের ক্ষেত্রে ছিলো চরম বৈষম্য ও অব্যবস্থা। অভিজাত শ্রেণি ও সাধারণ লোকের জীবনযাত্রার মধ্যে ছিলো ব্যাপক ব্যবধান। সমাজের সাধারণ মানুষ যেমন—কামার, কুমার, ছুতার, স্বর্ণকার এবং কৃষক, শ্রমজীবী মানুষ জীবিকা নির্বাহের জন্য হাড়ভাঙা পরিশ্রম করতো। কিন্তু, সুফল ভোগ করতো অভিজাত শ্রেণির লোকেরা; তারা অত্যন্ত বিলাসবহুল জীবন-যাপনে অভ্যস্ত ছিলো।
মুসলিম ভারত
সমগ্র ভারতের ইতিহাসে চরম অর্থনৈতিক উৎকর্ষতার যুগ হচ্ছে মুসলিম শাসনামল। মুসলিমরা এমন কোনো সেক্টর নেই, যেখানে সফলতা লাভ করেনি। মুঘলামলে এই ভারতবর্ষ সমগ্র পৃথিবীর ২৮-৩০% জিডিপি নিয়ন্ত্রণ করতো। আজকের ইউরোপীয়দেরকে এই ভারতবর্ষ থেকেই স্কলারশিপ বা বৃত্তি প্রদান করা হতো। বার্থেমার মতে কৃষিপণ্যর জন্য বাংলাদেশ পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা ধনী দেশ ছিলো। বাংলার ঐশ্বর্য ছিলো তখন গুজরাট ও বিজয়নগরের মিলিত সম্পদের সমপরিমাণ।
মুসলিম শাসনামলে রাজ্য পরিচালনার জন্য নামেমাত্র কর নেওয়া হতো। কর নেওয়ার ক্ষেত্রে হিন্দু-মুসলিম কোনো বৈষম্য করা হতো না। যার জন্য যেটা ন্যায্য, তার জন্য সেটাই ধার্য করা হতো। মুসলিমদের জন্য যাকাত, ওশর, সদকা ও ফেতরার মতো বিষয়গুলো সেভাবেই ধার্য করা হতো। পাশাপাশি, অন্যদের জন্য অবস্থা অনুযায়ী জিযিয়া ও খারাজ গ্রহণ করা হতো। মুসলিম শাসনামলে অর্থনীতি সচল রাখার জন্য আলাদা দফতর বা মন্ত্রণালয় দক্ষ হাতে পরিচালনা করা হতো। এমনকি, মুসলিম শাসকদের প্রতিটি পণ্যের বাজারমূল্য নির্ধারণ করে দেওয়ার ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করতেন এবং সেসব যথাযথভাবে বাস্তবায়ন হচ্ছে কি-না, তা স্বয়ং শাসক নিয়মিত তদারকি করতেন। পণ্যসমূহের বাজারমূল্য নির্ধারণ করেই শুধু ক্ষান্ত হয়নি শাসকগণ, বরং মুদ্রাব্যবস্থাতেও এনেছিলেন অভূতপূর্ব বিবর্তন; বিবর্তনের পাশাপাশি ব্যবসা বাণিজ্যের সুবিধার্থে নিত্য নতুন মুদ্রার প্রচলনও শুরু করতেন শাসকগণ।
মুসলিম শাসনামলে আমলে বস্ত্রশিল্পে চরম উন্নতি লাভ করে। গুজরাট ও বাংলা ছিলো বস্ত্রশিল্পের প্রধান ঘাটি। এমনকি, এই অঞ্চলে এমনসব পোশাক তৈরি করা হতো, যেসব পোশাক তৈরিতে আবহাওয়াকে পর্যন্ত কাজে লাগানো হতো। সিল্ক, মসলিন, সুসতরি ভিরাইন, কিংখাব ছিলো সে সময়ের জগদ্বিখ্যাত সব পোশাকের নাম। শুধু পোশাকেই নয়; বরং তুলা শিল্প, পশম শিল্প, ধাতু শিল্প, জুয়েলারি শিল্প, পাথর শিল্প, কাঠ শিল্প, কাগজ শিল্প, কাঁচ শিল্প এবং চিনি শিল্পে অভূতপূর্ব উন্নতি সাধন করেছিলো মুসলিম শাসকগণ।
ব্যবসা বাণিজ্য
মুসলমানরা ভারতে আসার পর ব্যবসা-বাণিজ্যে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন আসে। অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক বাণিজ্যে এক নতুন মাত্রা আসে। দিল্লির সুলতানি আমল-সহ মুঘল আমলেও কেন্দ্রীয় শাসন, কৃষি-শিল্পের উন্নতি, যোগাযোগ ব্যবস্থা, নগরায়ন ও মুদ্রা ব্যবস্থার বিকাশের ফলে ব্যবসা-বাণিজ্য সম্প্রসারিত হয়। এ সময় অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক বাণিজ্যে ব্যাপক প্রসার ঘটে। খ্রিস্টীয় দ্বাদশ শতাব্দী থেকে পঞ্চদশ শতাব্দীর সময়ে ভারতে ব্যবসা-বাণিজ্যের ব্যাপক প্রসার ঘটে। এ সময়ের ব্যবসা-বাণিজ্যকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যথা,
- ০১. অভ্যন্তরীণ বা আন্তঃবাণিজ্য,
- ০২. বৈদেশিক বা বহিঃবাণিজ্য।
মুসলিম শাসনামলে ভারতে অভ্যন্তরীণ ব্যবসা-বাণিজ্যে সমৃদ্ধ ছিলো। অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের প্রধান কেন্দ্র ছিলো প্রাদেশিক রাজধানী ও বড় বড় শহরগুলো। যেমন—মুলতান, দিল্লি, আমরোহা, মীরাট, মালবের ধর, অযোধ্যা, দেবগিরি, লক্ষণাবতী, কাশ্মীর, গুজরাট, বিজয়নগর; এসব শহর ও বন্দরগুলো ব্যবসা-বাণিজ্যে বড় ভূমিকা রাখে। সেসময় বিভিন্ন ধরনের পণ্য-দ্রব্য আমদানি-রপ্তানি করা হতো। গ্রাম থেকে খাদ্যশস্য এসব বাণিজ্যকেন্দ্রে আসতো। এসব কেন্দ্র থেকে দেশের বিভিন্ন জায়গায় রপ্তানি করা হতো। গুজরাটের সুরাট ও ম্যাংগ্রল হতে ঘোড়া, গম, চাল, তুলা, কাপড় এবং আরও বহু জিনিসপত্র ভারতের বিভিন্ন বাজারে নিয়ে যাওয়া হতো। আবার এখানে নিয়ে আসা হতো নারকেল, পালিশের শক্ত গুঁড়ো, খনিজ পদার্থ, মোম, এলাচ ও মসলা। ব্যবসায়ীরা উপকূল বাণিজ্যে দিউ, মালাবার, ভাতকল, গোয়া, চাল ও দাভোলের সঙ্গে ভালোই লাভ করতো। বারবোসা বলেছেন যে,
❝মালাবারের জাহাজে করে লোহা, ভাতকলের চিনি, গোলমরিচ, আদা, লবঙ্গ, দারুচিনি, চন্দনকাঠ, সিল্ক ‘দিউ’ বন্দরে যেতো এবং আসার সময় মালাক্কা ও চীন হতে এখানে বিশেষ করে সিল্কের কাপড়, দেশীয় বস্ত্র, ঘোড়া, গম ও আফিম নিয়ে আসতো। আবার বাংলা থেকে বাণিজ্যিক জাহাজে করে চিনি ও কাপড় নিয়ে ক্যাম্বের ও মালাবার যেতো কমোরিন অন্তরীপ হয়ে।❞
ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্য বরাবরই চলতো জলপথে ও স্থলপথে। ইসলামের অভ্যুত্থান ও মূর জাতির আধিপত্য হেতু ইউরোপের সঙ্গে ভারতের প্রত্যক্ষ বাণিজ্যিক যোগাযোগ ছিন্ন হয়ে যায়; কিন্তু তা সত্ত্বেও ভারতের পণ্য যাওয়ার পথে কোনো অসুবিধা হয়নি। কারণ, আরব বণিকরা ভারতীয় পণ্য লোহিত সাগরে বয়ে নিয়ে যেতো; সেখান থেকে যেতো দামাস্কাস ও আলেকজান্দ্রিয়ায়। তারপর, সেখান থেকে ভারতীয় পণ্য বিভিন্ন অঞ্চলে বাগদাদ ও ইউরোপে ছড়িয়ে যেতো। মূর বণিকদের দ্বারাও ভারতীয় পণ্য বিদেশের বাজারে পৌঁছে যেতো। বিশেষ করে আফ্রিকার পূর্ব উপকূল, সুদূর পূর্বাঞ্চলের মালয় দ্বীপপুঞ্জ, চীন ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের বিভিন্ন দেশে পৌঁছে যেতো। স্থলপথে ভারতীয় পণ্য প্রধানত চারটে দেশে যেতো, আফগানিস্তান, মধ্য এশিয়া, পারস্য ও ইরাক। মুলতান-কোয়েটা সড়ক, খাইবার গিরিপথ ও কাশ্মীর যাওয়ার রাস্তাগুলোই ঐসব দেশগুলোর সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করা হতো; এই পথেই আবার বাণিজ্য হতো। বিদেশি বাজার থেকে ভারতে বিলাসদ্রব্য ও অন্যান্য দ্রব্য চলে আসতো এবং সাধারণভাবে সব রকমের প্রয়োজনীয় পণ্যের এদেশে ভালো বাজার ছিলো। আবার পারস্য উপকূলের কোনো কোনো দেশ ভারতের খাদ্যের উপর নির্ভরশীল ছিলো। বারবোসার বক্তব্য অনুসারে বাংলার সাদা চিনি বিদেশে প্রচুর রপ্তানি হতো।
সমুদ্র বাণিজ্যে প্রধানত বাংলা ও গুজরাট বন্দরের মাধ্যমেই এই রপ্তানি বাণিজা চলতো। গুজরাটের প্রধান প্রধান রপ্তানি দ্রব্য ছিলো বহুমূল্য পাথর, নীল, তুলো, পশুর চামড়া এবং আরও বহু জিনিস। সুতি ও অন্যান্য বস্ত্রই ছিলো প্রধান ও গুরুত্বপূর্ণ পণ্য। গৌণ রপ্তানি দ্রব্যের মধ্যে ছিলো বহুমূল্য রক্তিম পাথর, তিল তেল, চন্দন কাঠ, সুবাসিত তেল, দস্তা, আফিম, নীল এবং মালাক্কা ও চীন দেশে থেকে নিয়ে আসা কিছু ঔষধপত্র। কৃষিজাত পণ্যের মধ্যে রপ্তানি হতো গম, জোয়ার, চাল, ডাল, তৈলবীজ, সেন্ট এবং আরও অনেক দ্রব্য। বার্থেমার মতে কৃষিপণ্যর জন্য বাংলাদেশ পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা ধনী দেশ ছিলো। বারবোসার মতে বাংলাদেশের প্রধান রপ্তানি দ্রব্য ছিলো চিনি। বাংলার ঐশ্বর্য ছিলো তখন গুজরাট ও বিজয়নগরের মিলিত সম্পদের সমপরিমাণ।
রাজস্ব ব্যবস্থা
মুঘল শাসনামলে ভারতের রাজস্বব্যবস্থা বেশ শক্তিশালী ছিলো। বাবর ও হুমায়ুনের আমলে সুলতানি আমলের প্রশাসন কাঠামোর উপরই রাজস্ব ব্যবস্থা গড়ে উঠেছিলো। তবে আকবরের রাজত্বকালে মুঘলদের রাজস্ব ব্যবস্থায় যথেষ্ট পরিবর্তন আনয়ন করা হয়। এ আমলে সুষ্ঠু নিয়ম-নীতির মাধ্যমে রাজস্ব আদায় করা হতো। রাজকোষও ছিল যথেষ্ট সমৃদ্ধ। সাম্রাজ্য বিস্তারের প্রয়োজনে বিরাট সেনাবাহিনী রক্ষণাবেক্ষণ, শিল্প-স্থাপত্যের উৎকর্ষ সাধন এবং জনকল্যাণমূলক কাজের জন্য তাদের প্রচুর অর্থেরও প্রয়োজন হতো।
সম্রাট আকবরের শাসনামলে সরকারের আয়ের উৎস ছিলো কয়েকটি। যথা,
- (১) ভূমি রাজস্ব,
- (২) বাণিজ্য শুল্ক,
- (৩) টাকশাল,
- (৪) উত্তরাধিকার স্বত্ব
- (৫) উপঢৌকন,
- (৬) ক্ষতি পূরণের অর্থ।
এগুলোর মধ্যে ভূমি রাজস্ব ছিলো সরকারের আয়ের প্রধান উৎস। সম্রাট আকবরের ভূমি রাজস্ব নীতি সমসাময়িক ও পরবর্তী সময়ের ঐতিহাসিকদের মধ্যে ভূয়সী প্রশংসা অর্জন করে। শের শাহের ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থা, যা পরবর্তী সময়ে লোপ পায়, তা আকবর পুনরায় শুরু করেন। সম্রাট আকবর পর পর একাধিক দেওয়ানের প্রচেষ্টা পর্যবেক্ষণ করে অবশেষে ১৫৮২ খ্রিস্টাব্দে রাজা টোডরমলকে “দিওয়ান-ই-আশরাফ” বা “প্রধান রাজস্ব সচিব” নিযুক্ত করেন এবং রাজস্ব সংস্কারের নির্দেশ দেন। সম্রাট আকবর শেরশাহের রাজস্ব ব্যবস্থার উপর ভিত্তি করে যে অর্থনৈতিক সফলতা অর্জন করেন, তা তাঁর অসামান্য ব্যক্তিত্ব ও মেধার পরিচায়ক।
মুঘল সম্রাট আকবরের রাজস্ব নীতির সুফল সম্পর্কে অনেক ঐতিহাসিক উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন। এসবের ফলে রাজকর সুনির্দিষ্ট হয়। রাজস্ব কর্মচারীদের দুর্নীতি বন্ধ হয়। সম্রাটের আয় বৃদ্ধি পায়। সম্রাট বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক কর্মকাণ্ডে অধিক অর্থ ব্যয় করতে পারেন। এর ফলে কৃষককুল সমৃদ্ধশালী হয়। ১৬০৫ খ্রিস্টাব্দে সম্রাট আকবরের মৃত্যুর আগে বার্ষিক খাজনার পরিমাণ ছিল ১৭, ৪৫,০০,০০০ টাকা। এছাড়াও,
- ক. কৃষকদের আর্থিক উন্নতি হয়।
- খ. অনাবৃষ্টি ও খরাজনিত কারণে কর মওকুফ হয়।
- গ. কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি পায়।
- ঘ. দৈনন্দিন ব্যবহারের দ্রব্যাদির মূল্য হ্রাস,
- ঙ. জনগণের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি পায়,
- চ. গরু, ষাঁড়, লবণ প্রভৃতির উপর নির্ধারিত কর বাতিল।
এসব প্রসঙ্গে প্রখ্যাত ঐতিহাসিক V. A. Smith বলেন,
❝সংক্ষেপে বলতে গেলে, আকবরের রাজস্ব শাসন ছিলো প্রশংসনীয়। নিয়ম-কানুন ছিলো বিজ্ঞচিত এবং কর্মচারীবৃন্দকে জনগণের প্রতি সদয় হতে বাস্তব নির্দেশ দেওয়া হয়েছিলো।❞
কৃষি-ব্যবস্থা
ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক মেরুদণ্ড চিরদিনই ছিলো কৃষিনির্ভর। ভারতের প্রায় শতকরা ৭৫ ভাগ লোকের জীবিকাই ছিলো কৃষি। মুঘল সম্রাটরা কৃষির প্রতি বিশেষ নজর দেন। মুঘল যুগের কৃষি ব্যবস্থা যে খুব খারাপ ছিলো তা বলা যায় না। যান্ত্রিক কৃষি ব্যবস্থা সে যুগে গড়ে ওঠেনি। কিন্তু, তা সত্ত্বেও মুঘল আমলে মুঘল প্রশাসন ও অভিজাতবর্গ ছিলো কৃষিজাত আয়ের উপর নির্ভরশীল। মুঘল আমলের কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থা প্রাক-মুঘল যুগের কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থা অপেক্ষা যথেষ্ট উন্নতি লাভ করে। প্রাক-মুঘল যুগের কৃষি ব্যবস্থার পরিচয় বিখ্যাত আফ্রিকার শাসক ইবন বতুতার বিবরণ থেকে জানা যায়। বারবোসা, মাহুয়ান ও বার্থেমার বিবরণ থেকেও ভারতের কৃষি ও শিল্পের অনেক তথ্য পাওয়া যায়।
পৃথিবীর অন্যান্য দেশের তুলনায় ভারতীয় কৃষকরা অনেক বেশি পণ্য উৎপাদন করতেন। আবুল ফজল তাঁর আইন-ই-আকবরীতে মোট ৪১ রকমের রবি ও খরিপ শস্য উৎপাদনের কথা বলেছেন। তিনি আগ্রা অঞ্চলে ১৬টি রবি শস্য ও ২৫টি খরিপ শস্য উৎপাদনের কথা বলেছেন। শূন্য পুরাণ থেকে জানা যায় যে, ৫০ রকমের চাল বাংলায় উৎপাদন হতো। ভারতীয় কৃষকরা অন্যান্য দেশ থেকে আনা নতুন শস্যও উৎপাদন করতো। অষ্টাদশ শতাব্দীতে আমেরিকার ২টি নতুন পণ্য—তামাক ও ভুট্টা এদেশে উৎপাদিত হতে থাকে। নদীমাতৃক ভারতবর্ষের মাটি পলিমাটি দ্বারা গঠিত হওয়ায় জমি ছিলো খুবই উর্বর। বছরে ২ থেকে ৩ বার ফসল উৎপাদন হতো। সম্রাট বাবরের আত্মজীবনী “বাবরনামা” থেকে জানা যায় যে, বৈচিত্র্যের জন্য উৎপাদন ছিলো ভারতীয় কৃষকদের চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। ১৬০০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে ভারতের পশ্চিম উপকূলে তামাকের চাষ শুরু হয় এবং পরবর্তী ৫০ বছরের মধ্যে সমগ্র মুঘল-ভারতে তামাকের চাষ সম্প্রসারিত হয়। সপ্তদশ শতাব্দীতে রাজস্থান ও মহারাষ্ট্রে ভুট্টা চাষ হতো। মরিচ চাষ মুঘল-ভারতে অষ্টাদশ শতাব্দীতে বৃদ্ধি পায়। আলু ইউরোপীয় বণিকরা আমেরিকা হতে এদেশে আনেন। কফি দক্ষিণ মহারাষ্ট্রে সামান্য উৎপাদিত হতো, কিন্তু তা চাষ ভারতীয় কৃষকদের অজানা ছিলো।
ধান, পাট, গম, কার্পাস, তৈলবীজ, আদা, মরিচ, রেশম এবং বিভিন্ন ধরনের ডাল, বার্লি এবং আরও অসংখ্য রকমের রবিশস্য ও ইক্ষু ভারতের মাটিতে ভালো ফলতো। মুঘল নথিপথে অর্থকরী ফসলকে “জিনিস-এ-কামিল” বলা হয়েছে। কার্পাসের পাশাপাশি ইক্ষু ছিলো এই ধরনের অর্থকরী ফসল। নানাবিধ ফল-মূল ও শাক-সবজির চাষ মুঘল যুগে হতো। বিভিন্ন অঞ্চল বিভিন্ন শস্যের ভিত্তিতে আজকের মতো সেসময়ও শস্য উৎপাদনে খ্যাতি অর্জন করেছিলো।
চার
এখন এতোসব আলোচনার পরিসমাপ্তিতে একটা প্রশ্ন বা মন্তব্য আসতে পারে যে, ভারতের মুসলিম শাসনামলের সাথে পূর্বের শাসনামলের তুলনামূূলক আলোচনার মাধ্যমে সামাজিক সম্প্রীতি ও সৌহার্দ-এর প্রমাণ পাওয়া গেলেও শিক্ষা-ক্ষেত্রে ও অর্থনীতিতে তো হিন্দু-মুসলিম তুলনা করা হয়নি, বরং এই দু’টি সেক্টরে পূর্বের সাথে তুলনা করে উন্নতি ও উৎকর্ষতা দেখানো হয়েছে।
এর উত্তরে এখানে দু’টি বিষয় আসবে। যথা,
প্রথমত,
ইসলামী সভ্যতা সামগ্রিক, ইসলামী সমাজ বিনির্মাণও সেজন্য হয় সামগ্রিক। কখনও এভাবে দু’টি ধর্মের জন্য কাজ করে না ইসলামী সভ্যতা। বরং, মুসলিমদের নিজেদের ভেতরে মারহামাতপূর্ণ একটা সমাজ বিনির্মাণ করে তারপর সমাজের সকলকে একসাথে নিয়ে আদালত ও মারহামাতপূর্ণ সমাজ গড়ে তোলা হয়। ভারতীয় উপমহাদেশের প্রেক্ষাপটে ইসলামী সভ্যতায় হিন্দু-মুসলিম বলে আলাদা কোনোকিছু ছিলো না। কেননা, এখানে হিন্দুদের পাশাপাশি বৌদ্ধদেরও বড় একটা অংশ বসবাস করতো। এমনকি, এই বৌদ্ধ জনসাধারণই মুসলিমদেরকে ভারত অভিযানে আমন্ত্রণ জানায়।
আবার, হিন্দু-মুসলিম সামাজিক সহাবস্থান বজায় রাখা বা রাষ্ট্র থেকে শুরু করে সমাজের প্রতিটি সেক্টরে হিন্দু-মুসলিম একত্রে কাজ করাটাই শুধু সামাজিক সম্প্রীতি ও সৌহার্দের উদাহরণ নয়, বরং মুসলিম সমাজের মাঝেও যদি অভ্যন্তরীণ কোন্দল লেগে থাকে, সে সমাজকেও সামাজিক সম্প্রীতি ও সৌহার্দে পরিপূর্ণ একটা সমাজ বলা যায় না। অতএব, এখানে হিন্দু-মুসলিম সহাবস্থান বলে আদতে কিছুই নেই। যা আছে তা হলো, ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সমাজের প্রত্যেক স্তরের মানুষকে নিয়ে আদালত, আখলাক ও মারহামাতপূর্ণ একটি সমাজ বিনির্মাণ করা; যা ইসলামী সভ্যতা সুদীর্ঘকালব্যাপী ভারতীয় উপমহাদেশে প্রমাণ করে দেখিয়ে এসেছে।
দ্বিতীয়ত,
হ্যাঁ, এটা সত্য যে, ধর্ম, সমাজ, সংস্কৃতি, রাজনীতি, প্রশাসন ও বিচারব্যবস্থায় যেভাবে তুলনামূলক আলোচনার মাধ্যমে সামাজিক সম্প্রীতি ও সৌহার্দ-এর উপমা পেশ করা হয়েছে, সেটার সাথে তুলনা করে অবশ্য শিক্ষা-ক্ষেত্রে ও অর্থনীতিতে সে উপমা পাওয়া যায় না; বরং এখানে উন্নতি ও অগ্রগতির বিষয়টাই তুলনামূলকভাবে প্রাধান্য পেয়েছে। কিন্তু, এখানে আরেকটা বিষয় উঠে আসে যে, প্রাক-মুসলিম ভারতে যেসব সেক্টরে সুস্পষ্টরূপে অসামাজিকতা বা সামাজিক সম্প্রীতি ও সৌহার্দ-এর বিপরীত কার্যক্রম লক্ষ্য করা যেতো, সেসব সেক্টরগুলোকে ধরে ধরে মুসলিম ভারতের সময়কার পার্থক্য সুস্পষ্ট করে তুলে ধরা হয়েছে।
আবার যেখানে রাজনীতি, প্রশাসন ও বিচারব্যবস্থায় তুলনামূলক আলোচনার মাধ্যমে সামাজিক সম্প্রীতি ও সৌহার্দ-বিষয়টা সুস্পষ্ট করে বর্ণনা করা হয়েছে, সেখানে অর্থনীতিতে যে স্বাভাবিকভাবেই সম্প্রীতি ও সৌহার্দ বজায় থাকবে, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। পাশাপাশি, ধর্ম, সমাজ ও সংস্কৃতিতে তখনই সামাজিক সম্প্রীতি ও সৌহার্দ-এর নমুনা পাওয়া যায়, যখন শিক্ষা-সাহিত্যে সম্প্রীতি ও সৌহার্দ বজায় থাকে এবং ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলেই সমানভাবে শিক্ষা অর্জন করতে পারে। কেননা, সঠিক শিক্ষা ব্যতীত কখনই ধর্ম, সমাজ ও সংস্কৃতিতে সামাজিক সম্প্রীতি ও সৌহার্দ-এর নিদর্শন পাওয়া যায় না। সে হিসেবে, যেখানে তুলনামূলক পার্থক্য দেখানোর প্রয়োজন হয়েছে, সেখানে সেটাই করা হয়েছে; এবং যেখানে মুসলিম শাসনামলের উন্নতি ও সমৃদ্ধি উপস্থাপনের প্রয়োজন হয়েছে, সেখানে সেসব বিষয়ই উপস্থাপন করা হয়েছে।
অতএব, পরিসমাপ্তিতে বলা যায় যে,
সার্বিক আলোচনায় এবং সামগ্রিক দৃষ্টিকোণ বিবেচনায় এটাই প্রতীয়মান হয় যে, ভারতীয় উপমহাদেশের সমগ্র ইতিহাসে মুসলিম শাসনামল বা ইসলামী সভ্যতাই একমাত্র সামাজিক সম্প্রীতি ও সৌহার্দ-এর অনন্য উপমা পেশ করেছে। ধর্ম, সংস্কৃতি, নারী, শিক্ষা, রাজনীতি, প্রশাসন, বিচারব্যবস্থা ও অর্থনীতি-সহ সমাজ নামক বিষয়টির সাথে সম্পর্কযুক্ত প্রতিটি বিষয়েই ইসলাম সামাজিক নিরাপত্তা, সম্প্রীতি ও সৌহার্দ নিশ্চিত করেছিলো।
ইসলামী সভ্যতা সুদীর্ঘকালব্যাপী আদালত, আখলাক ও মারহামাতপূ্র্ণ যে সমাজের নিদর্শন উপস্থাপন করেছিলো, তাবত ভারতীয় ইতিহাসের আর কোনো সভ্যতাই সে নিদর্শন পেশ করতে সক্ষম হয়নি। সমগ্র ভারতীয় উপমহাদেশের বাংলাদেশ, পাকিস্তান বা আফগানিস্তানই নয় শুধু, বরং খোদ ভারতের ১০০কোটি মানুষও এখন আবারও ইসলামী সভ্যতার সামাজিক অবকাঠামো অর্থাৎ নিরাপত্তা, সম্প্রীতি ও সৌহার্দে পরিপূর্ণ একটি সমাজের জন্য মুখিয়ে আছে। পলাশীর আম্রকাননে স্বাধীন ভারতের যে সূর্য অস্তমিত হয়েছিলো, আর কোথাও থেকে হোক বা না হোক, যে বাংলার ভূমি থেকেই স্বাধীনতার সূর্য অস্তমিত হয়েছিলো, সেই বাংলার উর্বর জমিন থেকেই আবারো স্বাধীন ভারতের সূর্যোদয় হবে, ইনশাআল্লাহ।
হাওলাঃ
১. ইসলাম ও জ্ঞান, প্রফেসর ড. নাজমুদ্দিন এরবাকান।
২. আন্তর্জাতিক শোষণ ও মুক্তির পন্থা, হাসান আল ফিরদাউস।
৩. সাম্রাজ্যবাদ, ফাহমিদ-উর-রহমান।
৪. দাওয়াম, প্রফেসর ড. নাজমুদ্দিন এরবাকান।
৫. পাশ্চাত্য সভ্যতার দার্শনিক ভিত্তি, মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম।
৬. ভারতে মুসলিম শাসনের ইতিহাস, মুহাম্মদ ইনাম-উল-হক।
৭. আলিম ইসলামের ইতিহাস, লেকচার পাবলিকেশন্স।
৮. মুসলিম ভারতের সামাজিক সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক ইতিহাস, মাহবুবুর রহমান।
৯. ভারতীয় উপমহাদেশের ইতিহাস (মুঘল আমল), মাহবুবুর রহমান।
১০. ভারতীয় উপমহাদেশের ইতিহাস (সুলতানি আমল), মাহবুবুর রহমান।
১১. মুসলিম প্রশাসনব্যবস্থা, ড. সৈয়দ মাহমুদুল হাসান।
১২. মুসলিম প্রশাসন ব্যবস্থার ক্রমবিকাশ, ড. মুহম্মদ আলী আসগর খান, শেখ মুহম্মদ লুৎফর রহমান, মোখলেছুর রহমান।
১৩. সোনারগাঁও: বাংলায় ইলমী সিলসিলার অনন্য মিনার, মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম।
১৪. সুলতানী আমলে বাংলাদেশের মাদ্রাসা শিক্ষার উৎপত্তি ও বিকাশ, ড. আব্দুল করিম।
১৫. মুসলিম শাসনে ন্যায়বিচার, তোফাজ্জল বিন আমীন।
১৬. বাংলা অঞ্চলে কৃষি ও খাদ্যব্যবস্থা; প্রেক্ষিতে ইসলামী সভ্যতা হাসান আল ফিরদাউস (মিহওয়ার ৪র্থ সংখ্যা)
১৭. বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস ডক্টর এম. এ রহিম।
১৮. বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস, আব্বাস আলী খান।
১৯. আমাদের জাতিসত্ত্বার বিকাশধারা, মোহাম্মদ আব্দুল মান্নান।
২০. বাংলার সামাজিক সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক ইতিহাস, মাহবুবুর রহমান।