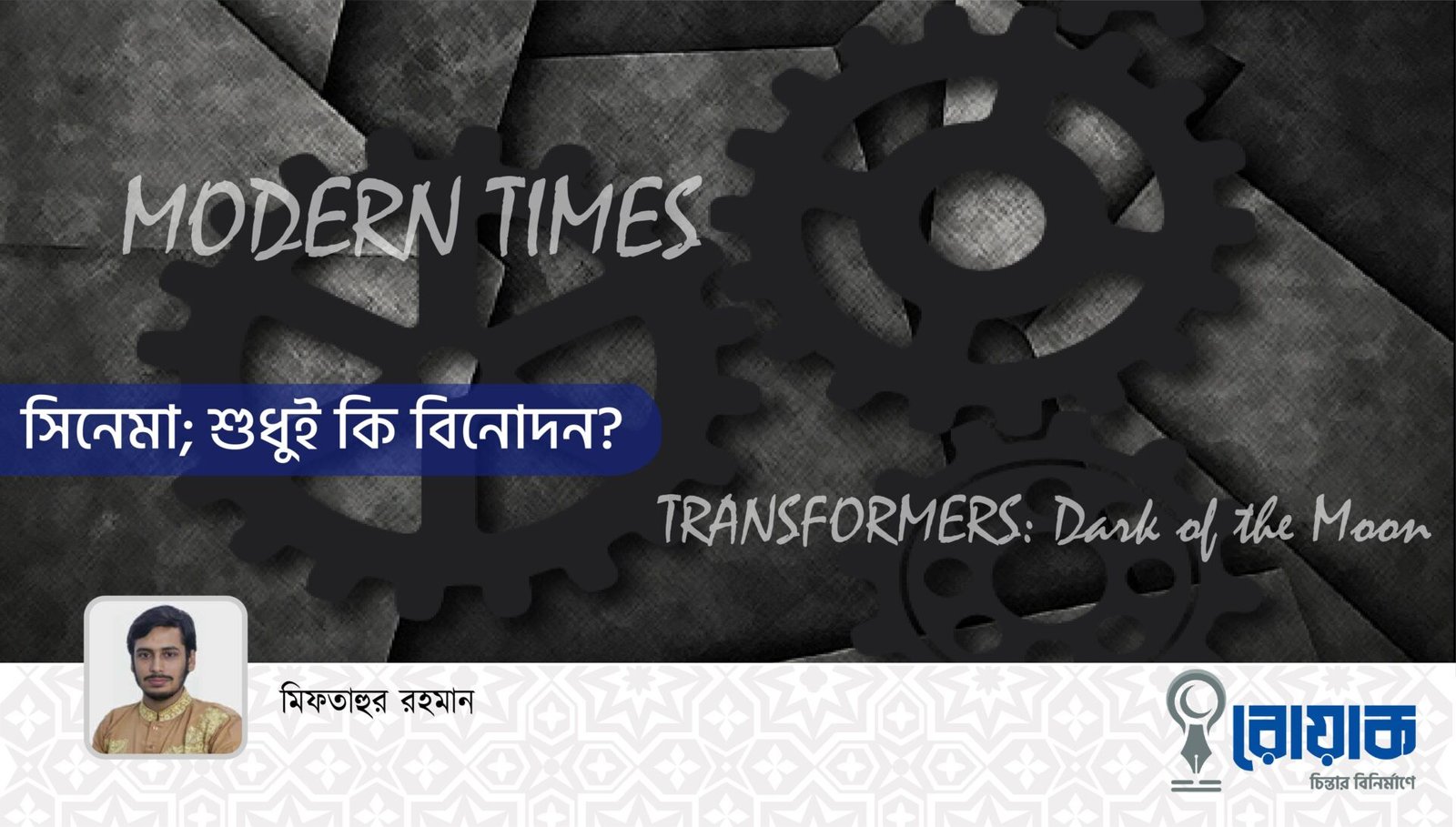আচ্ছা, ধরুন তো, প্রতিদিনের মতোই কাকডাকা ভোরে—শহরে থাকেন হেতু—কিচিরমিচির মধুর তানের পরিবর্তে এলার্মের আওয়াজে ঘুম ভাঙলো আপনার। প্রবল অনিচ্ছা সত্ত্বেও বিছানা ত্যাগ করলেন আপনি। ঘুমজড়ানো চোখে প্রভাতের স্নিগ্ধ কোমল বাতাসে দু’কদম হাঁটলেন কি হাঁটলেন না! প্রাতরাশ সাড়লেন চিরাচরিতভাবে। বিরক্তিভরা মন নিয়ে শরীরে কর্পোরেট পোশাক জড়ালেন। অফিস যাওয়ার পথে টানা দুই ঘণ্টা জ্যামে বসে ধুলাবালির স্বাদ নিলেন। বিরক্তিকর অসহ্য হর্নের কারণে কর্ণকুহরের উপর চললো নিদারুণ অত্যাচার। কর্মস্থলে গিয়ে শুনতে হলো প্রতিষ্ঠান প্রধানের তর্জন গর্জন আর উর্ধ্বতনের হম্বিতম্বি।
কাজের চাপে দুপুর পেরিয়ে দিন গড়িয়ে কখন যে বিকেল হয়ে এলো, তার কোনো হদিস পেলেন না। ঘণ্টা বা বেলের আওয়াজে ঘোর কাটলো আপনার। বুঝলেন, সময় হয়েছে বাড়ি ফেরার। পথিমধ্যে আহারাদির সামগ্রি কেনার জন্য যাত্রাবিরতি করলেন কোনো এক বাজারে। দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতিতে ক্রয়ক্ষমতার গ্রাফচার্টে আপনার রেখা নেমে এসেছে একেবারে তলানিতে। মস্তিষ্কের নিউরনে দুশ্চিন্তার ঝড়ের প্রভাবটা ফুটে উঠলো জুলফি বেয়ে গড়িয়ে পড়া কয়েকফোটা ঘামের মাধ্যমে। দোকানীর সাথে অহেতুক দরাদরি করে কাঁচাবাজারগুলো ব্যাগে পুরে নিয়ে আবারও পথ ধরলেন বাড়ির উদ্দেশে।
বাড়িতে এসে দায়সারাভাবে নিজেকে পরিচ্ছন্ন করে নিলেন। এই দায়সারাভাবে করার কারণও আছে; অফিস বা প্রতিষ্ঠানের একগাদা কাজ বাকী আছে, বাড়িতে বসেই যেগুলো শেষ করতে হবে আপনাকে। দিনভর পরিশ্রমের পর ঘরের মানুষদের সাথে দু’দণ্ড ভালো-মন্দ গল্প করবেন, সৃষ্টিগত এই চাহিদা ও মনের প্রবল এই ইচ্ছাকেও মাটিচাপা দিতে হলো। বাড়ির কর্তা হিসেবে আপনার কাছে থেকে প্রাপ্য সময়টুকুও পেলো না আপনার পরিজনেরা।
যতটুটুই বা একসাথে বসা হয় বা গল্প করা হয়, তাও সেটা হয় রাতের খাবারের টেবিলে। খুবই সামান্য সময়ের জন্য সুযোগ পান একে অপরকে কাছে থেকে দেখার, একে অপরের চাওয়া ও পাওয়া-না পাওয়ার গল্পগুলো শোনার। সবকিছুর পর, কী যেনো একটা না পাওয়ার হতাশা নিয়ে বিছানায় শরীরটা এলিয়ে দিলেন। প্রশান্তিময় সুখনিদ্রা…? কবে যে আপনাকে ত্যাজ্য করে হারিয়ে গিয়েছে অজানা কোথাও, সে হিসেব কষতে বসলে নিজের প্রতিই অভিশাপ দিতে ইচ্ছে করে আপনার।
কোনো পরিবর্তন ছাড়াই এভাবেই বিরক্তিকর এক রুটিনমাফিক যন্ত্রমানব হয়ে আপনাকে অতিবাহিত করতে হয় আপনার প্রতিটা দিন। জীবনের প্রতি আপনার চরম অনীহা; জীবনের প্রতি আপনি মারাত্মক বিরক্ত, মাত্রাতিরিক্ত অতিষ্ঠ। কিন্তু, নিয়ম ও সমাজের বেড়াজালে আবদ্ধ হয়ে পড়েছেন আপনি; চাইলেও পারবেন না এখান থেকে বেরিয়ে আসতে।
এরপর এলো সাপ্তাহিক ছুটির দিন। সবকিছু ফেলে সরিষা-পরিমাণ সামান্য সুখের খোঁজে নেমে পড়লেন। আধুনিকতায় আপনি পরিচিত বলে মনস্থির করলেন মুভি দেখার। অতএব, জীবনের এমন একঘেয়েমি থেকে ক্ষণিকের জন্য মুক্তি পেতে আপনি ঢুঁ মারলেন কোনো এক থিয়েটারে। উদ্দেশ্য, ঘন্টাদুয়েক সময় কাটাবেন সুবিশাল এক স্ক্রিনের দিকে তাকিয়ে, হারিয়ে যাবেন অজানা এক রাজ্যে; যেনো জীবনের সকল কষ্ট, ব্যথা, বেদনাকে ভুলে যেতে পারেন কয়েক মুহুর্তের জন্য, উপভোগ করতে চান অজস্র বন্ধুর পথে প্যাঁচানো দু’দিনের এই জীবনকে। কিন্তু, বিধিবাম! বিপত্তিটা ঘটলো ঠিক এখানেই।
যে মুভিটা দেখতে বসলেন, সেখানে এমন কিছুর চিত্রায়ন হয়েছে, যা আপনার সমগ্র চিন্তাকে ওলট-পালট করে দিলো। বিনোদনের পরিবর্তে আপনার মস্তিষ্ক আপনাকে জীবনের সংজ্ঞাটা নতুন করে ভাবতে বাধ্য করলো। জীবনটাকে সামান্য সময়ের জন্য উপভোগ করতে এসে থিয়েটার থেকে বেরিয়ে পড়লেন সমাজব্যবস্থাকে প্রশ্ন করতে করতে। উত্তর খুঁজে পেলেন নিজের উপর বিরক্ত, জীবনের উপর অতিষ্ঠ এবং প্রশান্তির দূরে চলে যাওয়ার কারণগুলোর।
থিয়েটারের চেয়ারে বসে বিগ-স্ক্রিনের তাকিয়ে সিনেমাটা দেখার সময় আপনার উপলব্ধি হলো, জুলুমপূর্ণ বিশ্বব্যবস্থাপনার যাঁতাকলে পড়ে আপনি হয়েছেন একজন মানসিক দাস, আপনার জীবনটা হয়েছে অত্যাচারিত ও নিপীড়িত একজন গোলামের মতো। যানবহনের তীব্র হর্ন ও ধুলাবালিময় সড়ক মূলত যথোপযুক্ত নগরব্যবস্থাপনার ব্যর্থতার ফলাফল। দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি মূলত উদ্দেশ্যপ্রণোদিত তৈরিকৃত একটা বিষয়, যার পেছনে কলকাঠি নাড়ছে পশ্চিমা অর্থনৈতিক বিশ্বদর্শন। যেখানে ধনীরা হবে আরো ধনী এবং দরিদ্ররা একেবারে নিঃশেষ হয়ে তারা হবে ধনীদের গোলামে পরিণত। অফিস বা প্রতিষ্ঠানে কাজের চাপ মূলত আপনার পরিজন থেকে দূরে রাখার উদ্দেশ্যমূলক হাতিয়ার, যেখানে আপনার মতোই আপনার প্রতিষ্ঠান প্রধান বা উর্ধ্বতনরাও নিজেদের অজান্তেই হয়ে গিয়েছে ঘৃণ্য উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের একেকটা খুঁটি।
ফলশ্রুতিতে, পরিজন থেকে দূরে থাকায় একটা সময় আপনি হয়ে পড়বেন সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন। সবাইকে বাদ রেখে ভাববেন শুধু নিজেকে নিয়ে। আপনার চিন্তা আবর্তিত হবে শুধু আপনাকে কেন্দ্র করেই। পরিবার-পরিজন একসময় বিতৃষ্ণার উপকরণ হয়ে দাড়াবে। আপনার মানসিক প্রশান্তি স্বয়ংক্রিয়ভাবেই আপনার থেকে বহুদূর চলে যাবে। অতঃপর…? আপনার জীবনটা হয়ে যাবে গৎবাঁধা নিয়ম ও রুটিনে আবদ্ধ। থাকবে না কোনো নিজস্ব স্বকীয়তা ও স্বাধীনতা। আপনার অজান্তেই আপনাকে চালিয়ে নেওয়া হবে তাদের স্বার্থ হাসিলের জন্য, আপনি নির্দ্বিধায় হাস্যোজ্জ্বল মুখে পালন করবেন তাদের আদেশ। সর্বোপরি আপনি হবেন, অন্যের চিন্তার উপর ভর করে জীবন ও জীবিকা নির্বাহ করা সুস্থ-মস্তিষ্কহীন বিবেক বিবর্জিত এক যন্ত্রমানব!
এখন একটু ভেবে দেখুন তো, আপনার জীবনের মূল্য ও জীবনবোধটা উপলব্ধি করতে পারলেন থিয়েটারে এসে।
জীবনবোধের সংজ্ঞাটা পরিবর্তন হতে শুরু করলো বিগ-স্ক্রিনের জন্য কৃত্রিমভাবে তৈরিকৃত একটা চিত্রায়ন দেখে। সমাজ ও বিশ্বব্যবস্থাপনাকে জানার শুরুটাও হলো ঠিক এখান থেকেই। আপনার ভেতরে জাগরিত হয়ে গেলো সমাজ পরিবর্তনের একটা সুপ্ত ইচ্ছা।
আপনি কিন্তু বিনোদন নিতে এসে নিজের অজান্তেই এতোকিছুর সাথে পরিচিত হয়ে গেলেন। না চাইলেও আপনি এখন ভাবতে বাধ্য হবেন। কারণ, ভাবার মতো একটা মূল উপাদান আপনার ভেতরে গেঁথে দেওয়া হয়েছে। আপনি ভাবতে বাধ্য হবেন, কারণ, বিগ-স্ক্রিনে চিত্রায়িত সিনেমাটি আপনার জীবনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ, সিনেমাটা যেনো আপনার জীবনেরই প্রতিচ্ছবি। আপনার জীবনের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র ঘটনা থেকে শুরু করে হাসি-কান্না, ব্যথা-বেদনা, দুঃখ-কষ্ট, পাওয়া-না পাওয়া–সবকিছুই ঐ সিনেমায় চিত্রায়িত হয়েছে। আপনার ভেতর থেকে কুড়ে কুড়ে খাওয়া প্রশ্নগুলোর উত্তর আপনি আজ পেয়ে গেলেন।
হ্যাঁ, এখানেই রয়েছে একটা সিনেমার স্বার্থকতা ও সিনেমার মূল দর্শন। অতএব, মোটাদাগে বলা চলে, “সিনেমা” শুধু বিনোদনের উৎকৃষ্ট একটা মাধ্যমই নয়, বরং এটা একটা আর্ট, একটা শিল্প, বিপ্লবের মুখপাত্র এবং সাহিত্যের মতো সামাজিক দর্পণ।
বিশ্বাস হচ্ছে না?
তাহলে এখনই দেখতে বসুন চার্লি চাপলিনের মডার্ন টাইমস মুভিটি।
বিংশ শতাব্দীর চতুর্থ দশকের শুরুতেই ব্ল্যাক মানডে ও ব্ল্যাক থার্সডে-র মাধ্যমে শুরু হওয়া গ্রেট ডিপ্রেশন বা মহানন্দার সেই প্রেক্ষাপটেই পুঁজিবাদি ব্যবস্থাকে প্রশ্নবিদ্ধ করে, অর্থের জন্য মানুষের যন্ত্রমানবে পরিণত হবার স্বরূপ তুলে ধরে এবং বিত্তশালীদের অর্থের লোলুপতার দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করার মাধ্যমে একজন যুবকের দৈনন্দিন স্বাভাবিক জীবনাচরণ এবং অর্থনৈতিকভাবে নিঃস্ব হওয়া একটি পরিবারের খাবারের জন্য নিত্যদিনের খাদ্যযুদ্ধকে অসাধারণভাবে চিত্রায়ন করা হয়েছে ১৯৩৬ সালে নির্মিত চার্লি চ্যাপলিনের এই “মডার্ন টাইমস” মুভিটিতে। তৎকালীন সামাজিক প্রেক্ষাপটকেই উপজীব্য করেই গড়ে তোলা হয়েছে মুভিটির সামগ্রিক কাঠামো।
(আরো বিস্তারিত জানার জন্য পড়তে পারেন ত্রৈমাসিক মিহওয়ার-এর ষষ্ঠ সংখ্যার সিনেমা পর্যালোচনা অংশটুকু)
অতএব, এটা অস্বীকার জো নেই যে, সিনেমার মাধ্যমে কোনো এক সমাজের মানুষ এবং সে সমাজের সংস্কৃতির প্রতিচ্ছবি ফুটে ওঠে। সিনেমার মাধ্যমে খুবই সংক্ষিপ্ত সময়ে আমাদের সমগ্র জীবনের সারাংশ আঁকা সম্ভব। একটা জাতির জাতীয় পরিচয় বহনের একটা মাধ্যমও হলো এই সিনেমা। কারণ, এটি এমন একটি মাধ্যম, যাকে ব্যবহার করে একটা দেশের সংস্কৃতি, জীবনাচরণ, জীবন দর্শনকে পৃথিবীব্যাপি পরিচিত করে দেওয়া যায় অতি সহজেই। কোনো সমাজ এবং সে সমাজের মানুষের জীবনাচরণ অতি দ্রুত ও সংক্ষিপ্ত সময়ে বুঝতে সে সমাজকে নিয়ে নির্মিত মুভি-সিনেমাগুলো দেখাই যথেষ্ট।
সমাজ পরিবর্তন বা সামাজিক বিপ্লবের মুখপাত্র হলো সিনেমা। শুধু জনসাধারণের স্বপ্নের প্রতিফলনই নয়, বরং তাদের চিন্তাকে তৈরি করে দেওয়া, চিন্তার মোড় ঘুরিয়ে দেওয়া বা চিন্তার পরিবর্তনও সম্ভব সিনেমার মাধ্যমে। মানুষের জীবনের দুর্দশা, দুঃখ-কষ্ট ও অসংখ্য সমস্যার সমাধান দেওয়া এবং হাজারো সব প্রশ্নের উত্তর দেবার অন্যতম এক উপাদান হলো সিনেমা।
সিনেমা, রেডিও, টেলিভিশন, ম্যাগাজিন—এসব এমন এক মাধ্যম, যাকে ব্যবহার করে মানুষের ভেতরে থাকা আইডিয়াগুলোকে মানুষের মাঝে অতি সহজেই অতি দ্রুত ছড়িয়ে দেওয়া যায়। উদ্দেশ্যমূলকভাবে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করা যায়। কাজটা সম্ভব হয় জনসাধারণের অজান্তেই; কারণ, তাদের অধিকাংশই থিয়েটারে আসে শুধুমাত্র বিনোদনের খোরাক পেতে।
সর্বোপরি, কেউ যদি ভাবে, স্ক্রিনে চিত্রায়িত বিষয়টার মাঝে ন্যূনতম কোনো দর্শন, সত্য বা কোনো বার্তা নেই, তাহলে সে ব্যক্তিটি কেনো যেনো তার জীবন থেকে ঘন্টাদুয়েক সময় অযথাই নষ্ট করলো।
মূলত, এসবই হলো সিনেমার দর্শন। তবে এখানে একটা প্রশ্ন উঠে আসে, সকল মুভিই কি এমন দর্শনকে সামনে রেখে নির্মিত? উত্তরটা হলো, হ্যাঁ, সব মুভিই এমন দর্শনকে সামনে রেখে নির্মিত বা চিত্রায়িত। তবে মতাদর্শ এবং উদ্দেশ্যগত ভিন্নতা রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ,
আমেরিকান চলচ্চিত্র-হলিউড বা এই মতাদর্শের ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলো বর্তমান সিনেমাপ্রেমী যুবসমাজকে দুই শ্রেণিতে ভাগ করে থাকে। যেমন,
- ০১. অবসর যাপনের জন্য সিনেমাকে যারা বিনোদনের মাধ্যম হিসেবে বিবেচনা করে। এদের ক্ষেত্রে পশ্চিমাদের দর্শন হলো, যুবকরা যেনো সবকিছু ফেলে তাদের তৈরিকৃত জগতের মাঝেই বিচরণ করে।
- ০২. যারা সিনেমাকে একটা আর্ট, বিপ্লব আর সমাজের দর্পণ হিসেবে বিবেচনা করে। এদের ক্ষেত্রে তাদের দর্শন হলো, সিনেমায় ফুটিয়ে তোলা দৃশ্যায়নের মাধ্যমে যুবকদের মাঝে তাদের অজান্তেই নিজেদের দর্শন ও চিন্তা প্রবেশ করিয়ে দেওয়া।
বিষয়টা অনেকটা নির্ভর করে ডিরেক্টর এবং ফিল্ম প্রোডাকশন কোম্পানির নিজস্ব দর্শনের উপর। যে ফিল্ম প্রোডাকশন হাউস যে দর্শনকে ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে, সে কোম্পানি তার সেই দর্শন বা সেই মূল উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে সিনেমা চিত্রায়িত করে। অতএব বলা যায়, তাদের নিজেদের মাঝে মতাদর্শগত ভিন্নতা থাকলেও তাদের উদ্দেশ্য একটাই; যেভাবেই হোক, যুবসমাজকে ফিকশোনাল একটা ওয়ার্ল্ডে বসবাস করানো। নিজেদের দর্শন ও নিজেদের চিন্তা দিয়ে তাদেরকে চিন্তা করানো।
যেহেতু মুভি ফ্র্যাঞ্চাইজি বা ফিল্ম প্রোডাকশন হাউসগুলোর মাঝে মতাদর্শগত ও উদ্দেশ্যমূলক ভিন্নতা রয়েছে, অতএব এটা সুনিশ্চিত যে, সবগুলো মুভি বা সিনেমা কখনও একই ক্যাটাগরির হবে না।
এখানে উল্লেখ্য যে, যে মুভিগুলো সমাজ পরিবর্তনের দর্শনকে সামনে রেখে নির্মিত হয়, কোনো এক চিন্তাকে বিস্তৃত করার লক্ষ্যকে ঘিরে চিত্রায়িত হয়, সামাজিক দুঃখ-দুর্দশার পরিস্ফুটনকে কেন্দ্রে রেখে আবর্তিত হয়, চিন্তার উৎপাদন করতে পারে বা থিংক ট্যাংক হিসেবে কাজ করে, কোনো বিপ্লবের মুখপাত্র হবার যোগ্যতা ও সক্ষমতা রাখে অথবা কোনো বিপ্লবকে প্রশ্নবিদ্ধ করতে পারে, এসব মুভিগুলোকে এই দর্শনের ছাঁচে ফেলা যায়। এই ক্যাটাগরির মুভি-সিনেমাগুলোকে “ক্ল্যাসিক্যাল” এবং “বিয়োন্ড টাইম” মুভি নামেও ডাকা হয়।
সে যাইহোক, এবার কয়েকটা উদাহরণ দেখা যাক।
আমি সকলেই জানি, বর্তমান প্রেক্ষাপটে এটা সত্য যে, অতীতের সোনালী ইতিহাসকে স্ক্রিনে চিত্রায়ন করাও একধরনের পলিটিকাল পলিসি। বর্তমানের বৈশ্বিক এই রাজনীতিতে টিকে থাকতে হলে এটা করা এখন অত্যাবশ্যক হয়ে দাঁড়িয়েছে। পাশাপাশি, অতীতের ইতিহাসকে কাল্পনিক ঘটনার সাথে জুড়ে দিয়ে সিনেমার চিত্রায়নটাও ক্ষেত্রবিশেষে অলিখিত ও অত্যাবশ্যক একটি নিয়ম হয়ে গিয়েছে। কারণ, এতে করে সিনেমাটা দর্শকপ্রিয় ও ব্যবসাসফল হয় এবং একইসাথে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিল ও কূটকৌশল সফল হয়।
হলিউডের হাজারো সিনেমা থেকে মাত্র একটা সিনেমার নাম বলা যায়, যেটাতে শুধু উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে রাজনৈতিক স্বার্থোদ্ধার করেই ক্ষান্ত হয়নি, বরং শত্রু মনোভাবাপন্ন দেশগুলোর বিরুদ্ধে চরম পর্যায়ের মিথ্যাচার করে বিশ্বব্যাপী ঘৃণা, বিদ্বেষ ও জনরোষ সৃষ্টি করার সকল ধরনের প্রচেষ্টা চালানো হয়েছে।
সেই মুভিটা হলো, বিখ্যাত সাইফাই একশন থ্রিলার ফ্র্যাঞ্চাইজি “ট্রান্সফরমার্স”-এর তৃতীয় কিস্তি “ট্রান্সফরমার্স : ডার্ক অব দ্যা মুন”। সিনেমাটি পরিচালনা করেছেন সিনেমাটোগ্রাফিতে “ফাস্ট কাটিং” নামে পরিচিত বিখ্যাত পরিচালক মাইকেল বে। এই ভদ্রব্যক্তি সেই লোক, যিনি ”থারটিন আওয়ার”-এর মতো মুভি পরিচালনা করেছেন। অতএব, এই ব্যক্তির পরিচালিত সিনেমাগুলো কেমন হবে, সেটা আর বলতে হচ্ছে না।
এই সিনেমায় মূলত চন্দ্রাভিযান হওয়ার উদ্দেশ্য দেখানো হয়, চন্দ্রাভিযানের ৬-৭ বছর আগে চাঁদে আননোন একটা স্পেসশিপ ক্র্যাশ করে। সেটার ব্যাপারে এখন রিসার্চ করতে হবে। কিন্তু, রাশিয়ারও এ’ব্যাপারে অবগত থাকার সমূহ সম্ভাবনা থাকায় রিসার্চ করার জন্য এখন চাঁদে যাওয়া প্রয়োজন। এমনকি, সিনেমাটিতে এসব দৃশ্যগুলোয় জন এফ কেনেডি-সহ চন্দ্রাভিযানের সেই সময়ের সাদাকালো রিয়েল ফুটেজ ব্যবহার করা হয়। অর্থাৎ, সত্য ঘটনার সাথে এভাবে ফ্যান্টাসি মিশিয়ে সিনেমাটা ব্যবসাসফল ও দর্শকপ্রিয় হবার সাথে সাথে স্বার্থান্বেষী মনোভাব প্রচার করা।
এরপরের ঘটনাপ্রবাহে মানুষ-রোবটের এলায়েন্স হয়, প্রযুক্তির উন্নয়ন হয়। এমনকি এই আমেরিকাই এখন মানুষ-মানুষে হানাহানি বন্ধ করতে এসব প্রযুক্তির ব্যবহার করে!
মুভির ভাষাতেই বলি। ট্রান্সফরমার্স-এর মূল চরিত্রগুলোর দলনেতা হচ্ছে অপটিমাস প্রাইম। পশ্চিমাদের ভাষ্যানুযায়ী, মধ্যপ্রাচ্যের কল্পিত তাও আবার ‘নিষিদ্ধ’ নিউক্লিয়ার সাইটের উদ্দেশে মুভির প্রেক্ষাপটে ট্রান্সফরমার্স-এর মূল চরিত্রগুলো যাত্রা করে। সে সময় অপটিমাস প্রাইমকে বলতে শোনা যায়,
❝In the years since our arrival, our new home, Earth, has seen much change. Long-range defense systems watch the skies. Energon detectors guard its cities now. So now we assist our allies in solving human conflicts, to prevent mankind from bringing harm to itself.❞
অথচ, এরচেয়ে বড় মিথ্যাচার আর কী হতে পারে, জানা নেই। পৃথিবী বিধ্বংসী শক্তি স্বয়ং বলছে, তারা নাকি মানবহিতৈষী
সিনেমাটিতে মূলত সাই-ফাই একশন থ্রিলার জনর-এর হলেও ফ্র্যাঞ্চাইজির মুভিগুলোতে পলিটিক্স, ডিপ্লোম্যাসি আর সিক্রেট এজেন্সির উপস্থিতি চোখে পড়ার মতো। মুভিগুলোর ব্যপ্তি ছিলো ওয়ার্ল্ডওয়াইড। রাশিয়া থেকে শুরু করে চীন, মধ্যপ্রাচ্য ও ইউরোপ হয়ে ল্যাতিন আমেরিকা পর্যন্ত।
এমনকি, ফ্র্যাঞ্চাইজির মুভিগুলোতে মানুষ-রোবটের এলায়েন্স হওয়ার প্রথম প্রশ্নটাই ছিলো, এই প্রযুক্তি যদি চিন-রাশিয়ার হাতে যায়, তাহলে আমাদের অবস্থা কী হবে?
মানুষ-রোবটের এলায়েন্স না হওয়ার ১০১টা যুক্তি থাকলেও এই প্রশ্নের কাছে গভর্নমেন্ট আর সিক্রেট এজেন্সির মতামত এক। অর্থাৎ, তারা চায় যেকোনো মূল্যে নেতৃত্বের সিংহাসন হাতে রাখতে।
আবার একজন দর্শক যখন অসাধারণ সিনেমাটোগ্রাফি, মনোমুগ্ধকর ব্যাকগ্রাউন্ড স্কোর এবং স্বদেশ বিজয়ী হবার তৃপ্তিদায়ক এক হ্যাপি এন্ডিং দেখে, তখন সিনেমায় দেখানো প্রতিটি দৃশ্যই তার কাছে বাস্তবধর্মী মনে হবে এবং সিনেমায় দেওয়া বার্তাগুলো দর্শকের মগজে গেঁথে যাবে—এটাই স্বাভাবিক। তাই, এসব সিনেমা একটু সতর্ক হয়ে দেখা উচিত!
এখানেই শেষ নয়!
আরো আছে, যেসবে তাদের দ্বিচারিতা ফুটে ওঠে।
কোনো একটা জিনিসের যাচ্ছেতাই ব্যবহারের মাধ্যমে ধ্বংস করে ঐ জিনিসটার প্রতিই আবার দরদ দেখানোটা পশ্চিমাদের অতি পরিচিত একটা স্বভাব।
প্রাণীদেরকে নিয়ে নিষ্ঠুর আর অমানবিক সব এক্সপেরিমেন্ট থেকে শুরু করে মানুষকে পর্যন্ত গিনিপিগ বানিয়েছে তারা। শিল্পায়নের নাম করে নিজেদেরকে শ্রেষ্ঠ প্রমাণ করতে গিয়ে প্রকৃতির অবস্থাটা দুরবস্থা করতে এমন কোনো উপায় বাকী নেই, যেটার ব্যবহার তারা করেনি। প্রতি বছর শয়ে শয়ে পাখি মারা যাচ্ছে শুধুমাত্র বিল্ডিংয়ের থাই গ্লাস বা কাচের জানালার সাথে ধাক্কা খেয়ে। ইনকা, মায়া, এযটেক সভ্যতাকে ধ্বংস করে সেসব জায়গায় ইট-পাথরের বস্তি বানিয়ে রেখেছে এখন তারা
অথচ, নেটফ্লিক্সের বিখ্যাত ডকু সিরিজ Our Planet-এর দ্বিতীয় সিজনের সম্ভবত প্রথম এপিসোডেই বিখ্যাত ন্যারেটর David Attenborough বলেন,
❝Across the island, chicks are dying. There is now so much plastic in our oceans, that it reaches even the most remote islands on Earth, carried here by the currents. And only now are we beginning to understand that all life on Earth depends on the freedom to move.❞
প্রকৃতির ভারসাম্যকে নষ্ট করে প্রাণীদের উদ্বাস্তু করে এখন এসে তারা প্রকৃতির উপর দরদ দেখাচ্ছে। তারা বলছে, মানুষ নাকি কেবল বুঝতে শুরু করেছে প্রাণীদেরকে তাদের মতো করেই রেখে দিতে হয়।
কিন্তু কোথায়? উন্নতির নাম করে শিল্পায়নের আগে তো কখনও প্রাণীরা তাদের জীবন নিয়ে এতোটা বিপাকে পড়েনি! উন্নতি কি আগে হয়নি? উসমানীয়দের সময়ে বরং প্রতিটি দালানেই নির্দিষ্ট একটি স্থান থাকতো, যেখান থেকে পাখিরা বিশ্রাম নিতো আর খাবার খেতো। এমনকি, কোনো অঞ্চলে পাখিদের সুবিধার জন্য উঁচু উঁচু দালান নির্মাণ করা নিষিদ্ধ ছিলো।
দুঃখজনক বিষয় হচ্ছে, পশ্চিমাদের এতোসব কাজ-কারবার যতোটা না আশ্চর্যজনক, তারচেয়েও বেশি আশ্চর্যজনক হলো, মানুষরা এসব আবার বিনা দ্বিধায় বিশ্বাসও করে থাকে।
এবার একটু আমাদের দেশীয় প্রেক্ষাপটের দিকে নজর বুলিয়ে এই আলোচনার সমাপ্তি আঁকা যাক।
আমাদের দেশে সিনেমা হল কেন বিলুপ্ত হলো, এর উত্তর খুঁজতে বসলে অবশ্য অনেকগুলো উত্তরই পাওয়া যাবে। তবে, এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য একটা হলো ঝানু পরিচালক এবং অভিজ্ঞ গল্প-কথকের অভাব।
স্বাধীনতা উত্তর আমাদের সিনেমা অঙ্গন বেশ নামডাক অর্জন করেছিলো। যার উৎকৃষ্ট উদাহরণ হলো ১৯৮৯ এ মুক্তিপ্রাপ্ত “বেদের মেয়ে জোসনা” সিনেমাটি। হাল আমলের হাইপ তোলা কোনো সিনেমাই সেই পুরনো আমলের সিনেমার সফলতার ধারেকাছে পর্যন্ত পৌঁছাতে পারেনি।
এমন উল্লেখযোগ্য আরো কয়েকটি সিনেমার কারণে সিনেমা হলগুলোয় দর্শকের উপচেপড়া ভিড় দেখা যেতো। ছুটির দিনগুলোর বিশেষ আর্কষণই যেনো ছিলো সিনেমা হলগুলো। ইদানীং যেমন বিভিন্ন পার্ক রিসোর্টের প্রতি টান থাকে জনসাধারণের, তেমনি সে আমলে ছুটির দিনগুলোয় সিনেমা হলগুলোয় জায়গা পাওয়াটা কঠিন হয়ে যেতো।
এমন সফলতায় ভাটা পড়তে খুব একটা সময় লাগে না। বিনোদন ক্রমান্বয়ে ব্যবসায় রূপান্তরিত হয়ে যায়। এটা অস্বীকার করার জো নেই যে, ভালো রুচিশীল সিনেমা নির্মাণে সময় ব্যয় হয়। কিন্তু, দর্শকদের এমন সিনেমাপ্রেম আর হলমুখিতা দেখে কয়েকজন পরিচালক ব্যবসায় নেমে পড়ে।
সেক্টরটা বিনোদন থেকে ব্যবসায় রূপান্তর হওয়ায় কমার্শিয়াল মুভির নামে প্রাপ্তবয়স্কদের সিনেমা তৈরির চল শুরু হয়। আর এসবের জন্য তো না লাগে কোনো ঝানু পরিচালক, না লাগে অভিজ্ঞ গল্প-কথক। ফলে, রুচিশীল দর্শক হারাতে শুরু করে সিনেমা হলগুলো। এক এক করে খালি হতে শুরু করে একটা পর্যায়ে এসে দর্শকশূন্য হয়ে পড়ে সিনেমা হলগুলো।
ফলাফল এসে দাঁড়ায়, নব্বইয়ের দশকের শুরুর দিকে সারাদেশে যেখানে প্রায় সাড়ে চোদ্দোশত সিনেমা হল ছিলো, মাত্র এক যুগের ব্যবধানে সেখানে সিনেমা হলের সংখ্যা এসে দাড়ায় সাতশ’তে। কয়েকবছর আগে তা আরো নেমে এসে সংখ্যাটা হয় মাত্র একশোতে।
মূলত, যে বিষয়টার জন্য এতোগুলো কথা নিয়ে আসা, সেটা হলো, হুমায়ূন আহমেদ-এর “যমুনার জল দেখতে কালো” নাটকটা নিয়ে বলা।
সেসময়ের সিনেমা সেক্টরের এমন দুরবস্থাকে ব্যঙ্গ করে হুমায়ূন আহমেদ এই নাটকটা পরিচালনা করেন। যেহেতু তিনি ছিলেন একজন বাম, আবার নামকরা পরিচালক, বিখ্যাত ও ঐতিহাসিক “বাকের ভাই” চরিত্র যেখানে তারই সৃষ্টি, এমনকি অনেকে লেখক হুমায়ূন আহমেদ-এর চেয়ে পরিচালক হুমায়ূন আহমেদ-কেই বেশি পছন্দ করে থাকে, সে হিসেবে দেশের সিনেমাঙ্গনের এমন দুরবস্থাকে কটাক্ষ করতে দেরি ন্যূনতমও কুণ্ঠাবোধ করেননি তিনি।
নাটকটার সময়কাল নিয়ে খুব একটা জানা যায় না। তবে, কলাকুশলীদের বয়স দেখলে টের পাওয়া যায়, সিনেমাঙ্গনে যেসময় এমন দুরবস্থা এবং নাটকের জয়জয়কার চলছিলো, এমন সময়ে পরিচালনা করা হয় নাটকটি।
বাম ঘরানার এই সমালোচক পরিচালকের স্যাটায়ারমূলক নাটকটার কয়েকটা পয়েন্ট উল্লেখ না করলেই না। যেমন,
- ১. অভিনেতাদের নামমাত্র অভিনয়।
- ২. যখন-তখন অভিনেতা পরিবর্তন করা।
- ৩. সিনেমার নামে পয়সার ব্যবসা।
- ৪. কমার্শিয়াল মুভির নামে প্রাপ্তবয়স্কদের সিনেমা তৈরি।
- ৫. পরিচালকদের উপর প্রোটাগোনিস্টদের আধিপত্য।
- ৬. প্রোটাগোনিস্টদের অভ্যন্তরীণ সম্পর্ক এবং সেসব নিয়ে কানাঘুষা।
- ৭. পুরো অভিনয় সেক্টরের উপর সংবাদকর্মীদের আধিপত্য।
- ৮. কমার্শিয়াল মুভির প্রতি নজর দেওয়ায় একই গল্প বারবার নিয়ে আসা।
- ৯. পরিচালকের জ্ঞানের দৈন্যতা এবং কলাকুশলীদের অযোগ্যতা।
এসব দিক-সহ আরো অনেকগুলো দিককে ঝানু এই পরিচালক একেবারে হাস্যরসাত্মকভাবে কটাক্ষ করে উপস্থাপন করেছেন “যমুনার জল দেখতে কালো” নাটকটিতে।
অতএব, পরিশেষে এসে এটা বলতে দ্বিধা হওয়া উচিত নয় যে, সিনেমা যেমন একদিকে একটা আর্ট, একটা শিল্প, বিপ্লবের মুখপাত্র এবং সাহিত্যের মতো সামাজিক দর্পণ; তেমনি অন্যদিকে সিনেমা শুধু সিনেমা না, এটা মানুষের চিন্তাধারা নিয়ন্ত্রণের মাধ্যম এবং পলিটিক্স ও ডিপ্লোমেসির অন্যতম সেরা একটি হাতিয়ার।