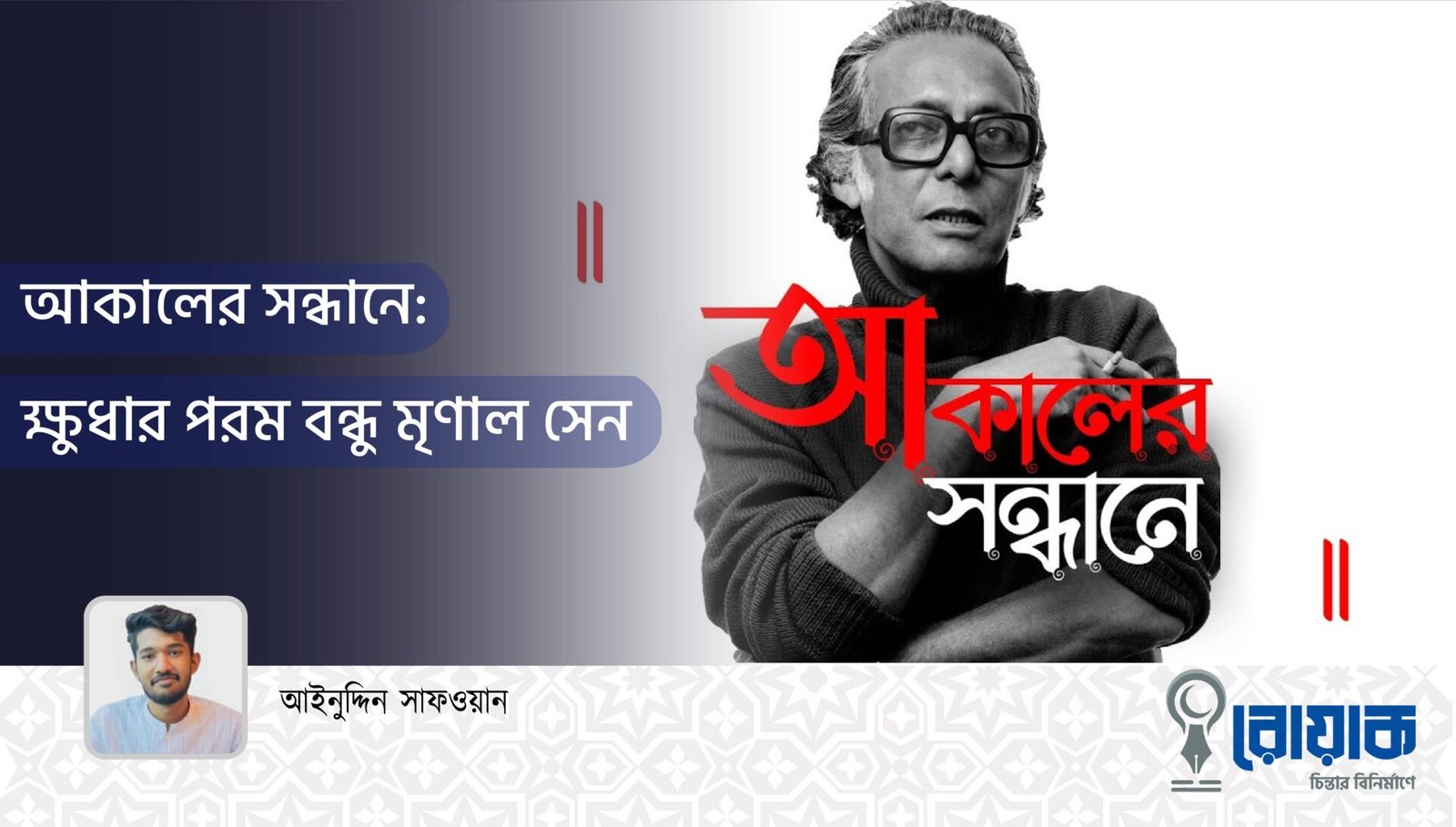“হেই সামালো ধান হো
কাস্তেটা দাও শান হো
জান কবুল আর মান কবুল
আর দেবনা আর দেবনা
রক্তে বোনা ধান মোদের প্রাণ হো।
পঞ্চাশে লাখ প্রাণ দিছি
মা-বোনদের মান দিছি,
কালোবাজার আলো কর তুমি মা।
মোরা তুলবোনা ধান পরের গোলায়
মরবোনা আর ক্ষুধার জ্বালায় মরবোনা,
ধান জমিতে লাঙ্গল চালাই
ঢের সয়েছি আর তো মোরা সইবোনা।
এই লাঙ্গল ধরা কড়া হাতের শপথ ভুলবোনা।”
কিংবদন্তী সংগীত পরিচালক সলীল চৌধুরীর এই গান অবিভক্ত বাংলার তেভাগা আন্দোলন এর সময় কৃষকদের করেছিলো তুমুল উজ্জীবিত। এই গান বাঙালি কৃষকদের শ্রমকে পরিণত করেছিলো শক্তিতে। ‘আকালের সন্ধানে’ সিনেমাটি শুরুই হয় এই গান দিয়ে। পরবর্তীতে পুরো সিনেমা জুড়েই মিশে ছিলো এই গানের সুর।
বাংলা সিনেমার ইতিহাসে কিংবদন্তি ত্রয়ী সত্যজিত রায়, হৃত্তিক কুমার ঘটক এর সাথে আরেকটি নাম অবধারিতভাবে চলে আসে, সেটি হলো ‘মৃণাল সেন‘। যিনি প্রায় ৫ দশক ধরে শুধুমাত্র বাংলা নয়, গোটা উপমহাদেশের চলচ্চিত্র ভাবনাকে সমৃদ্ধ করেছেন। উপমহাদেশের চলচ্চিত্রে রাজনৈতিক সচেতনতার আত্মপ্রকাশ ঘটিয়েছিলেন তিনি। ১৯২৩ সালের ১৪ মে বাংলাদেশের ফরিদপুরে জন্ম মৃণাল সেনের। ফরিদপুরে হাইস্কুল পর্যন্ত পড়ে ৪৩ এ চলে যান কলকাতায়। সেখানেই বামপন্থী আন্দোলনের সাংস্কৃতিক পরিমন্ডলে তিনি সক্রিয় হয়ে উঠেন এবং পরবর্তীতে সেখান থেকেই তার সিনেমার যাত্রা শুরু হয়। ৬৯ সালে ‘ভুবন সোম‘ সিনেমা দিয়ে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে জনপ্রিয় হয়ে উঠেন। এরপর তার ঐতিহাসিক কলকাতা ট্রিলোজির ৩ সিনেমা তাকে নিয়ে যায় সফলতার অনন্য উচ্চতায়। বিভক্ত স্বাধীন ভারতের রাজ্য পশ্চিমবঙ্গের গ্রামীণ জীবন ও অবিভক্ত বাংলায় ১৯৪৩ এর দুর্ভিক্ষ-আকাল-মৃত্যুর তুলনা ও দুই সময়ের পর্যবেক্ষণে ১৯৮০ সালে তৈরি করলেন ‘আকালের সন্ধানে’। ‘আকালের সন্ধানে’ ছবিতে পরিচালক মৃণাল সেন ব্যবহার করেন তৎকালিন জনপ্রিয় অভিনেত্রী স্মিতা পাটিলকে। স্মিতা তখন বম্বে ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির তারকা। কিন্তু চরিত্রটি তার এতই পছন্দ হয় যে তিনি মৃণাল সেনের সঙ্গে কাজ করতে রাজি হন। সাদা-কালো মনোক্রোমে এ ছবি আন্তর্জাতিক সিনেমাতেও অমূল্য। সিনেমায় মানুষকে বাস্তব দেখানো হয়। কিন্তু তার চরিত্রায়ন– আলো নির্মাণ, শব্দ সংযোজন সবই কৃত্রিমভাবে তৈরি যা চলচ্চিত্র সৃষ্টির প্যারাডক্স। এই প্যারাডক্সকে মৃণাল সেন দেখান, ‘ফিল্ম উইদিন ফিল্ম‘ পদ্ধতির মাধ্যমে আকালের সন্ধানে ছবিতে।
এই ছবির পরিচালক হিসেবে মৃণাল সেন ১৯৮১ সালে বার্লিন আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে জুরি বোর্ডের বিশেষ পুরস্কার পান। এ ছাড়া মৃণাল সেন এ ছবির জন্য শ্রেষ্ঠ পরিচালকের জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার ‘স্বর্ণকমল‘ এবং শ্রেষ্ঠ চিত্রনাট্যের জন্য ‘রজতকমল‘ পুরস্কার লাভ করেন। এতে পরিচালকের চরিত্রে অভিনয় করেন ধৃতিমান চট্টোপাধ্যায়। অভিনয় করেছেন স্মিতা পাটিল, দীপংকর দে এবং শ্রীলা মজুমদারসহ আরও অনেকেই। অভিনয় করেছেন মৃণাল সেনের স্ত্রী গীতা সেনও।
সিনেমার শুরুতেই দেখা যায় চিরায়ত গ্রামের ছবি। সবুজ-শ্যামলে ছেয়ে থাকা গ্রাম হাতুই। সেই সবুজের ফাঁক চিড়ে এগিয়ে যেতে থাকে এক ট্রেন। চিরায়ত সবুজের ভাণ্ডার এই হাতুই গ্রামে আবির্ভাব ঘটে এক সিনেমা দলের। তারা এসেছেন ‘৪৩ এর দুর্ভিক্ষের প্রেক্ষাপটে সিনেমা বানাতে। তারা সেলুলয়েডে ফুটিয়ে তুলতে চান সেই মন্বন্তরের কাহিনী, ব্রিটিশের তৈরি ১৯৪৩ সালের যে মন্বন্তরে প্রায় ৫০ লাখ মানুষের মৃত্যু হয়। তাদের প্রবেশের সাথে সাথেই আমরা শুনতে পাই গ্রাম্য ভাষায় এক বৃদ্ধের তিরস্কার, “বাবুরা এয়েছেন আকালের ছবি তুলতে। আকাল তো আমাদিগের সব্বাঙ্গে।”
সিনেমার দলটি তাদের থাকার জায়গা হিসেবে বেছে নেয় এক পুরোনো বনেদি বাড়ি যেখানে আগেকার সময়ের বনেদিয়ানার ছাপ রয়েছে স্পষ্ট। পরিত্যক্ত পাঠাগার আছে। আছে ঐতিহাসিক কিছু বইয়ের কালেকশন। এরপর শুরু হয় শুটিং, গ্রামের মানুষ ভীড় করে শুটিং স্থলে। এটা কোনো নাচ গানের সিনেমা নয় তবুও মানুষের এত উপচে পড়া ভীড়ের কারণ হলো তারা তাদের জীবনকে দেখতে পাচ্ছে চোখের সামনে। আকালে সাথে তারা পরিচিত যুগ যুগ ধরে। শ্যুটিং দেখতে আসা সব শিশু কিশোর এর হাড্ডিসার দেহই বলে দেয় ক্ষুধার সাথে কত পরিচিত তারা।
শ্যুটিং চলাকালীন সময় এক নারী অভিনেত্রী ডিরেক্টরের সঙ্গে গণ্ডগোল করে কাউকে না জানিয়ে কলকাতায় ফিরে যান। সমাধানে এগিয়ে আসেন গ্রামের এক মধ্যবয়স্ক। তিনি নিজে গ্রামে যাত্রাপালা, নাটক করেছেন। তাঁর বিশ্বাস গ্রামের সকলে মন্বন্তরের কাহিনী চলচ্চিত্রায়নের সৎ প্রচেষ্টায় সাহায্য করবে। চরিত্রটি এক তরুণীর, খিদের জ্বালায় সে এখন পতিতা। গ্রামের সেই মধ্যস্থতাকারীর কথায় ঠিক হয় যে স্থানীয় একটি তরুণীকে (ঘটনাচক্রে সে উচ্চবর্ণের) শিখিয়ে কাজ চালানো হবে। সমস্যার শুরু হয় এখান থেকেই। কিন্তু চরিত্রটি একজন পতিতার এটা শোনা মাত্রই গ্রামের মানুষজন প্রচন্ড বিরোধিতা করা শুরু করে। এই গ্রামের নারীদের সম্মানহানীর অভিযোগ তুলেন তারা। পরবর্তীতে পুলিশ এর সাহায্য শুটিং সম্পন্ন করার সিদ্ধান্ত নিলেও সেটি সম্ভব হয়নি। শেষে হাতুই গ্রামে শুটিং অসমাপ্ত রেখেই কলকাতায় ফিরে যেতে হয় সিনেমার দলটির।
ছবিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র ছিলো গ্রামের কৃষক “হরেন”। গ্রাম ঘুরে দেখতে বের হয়ে তার সাথে পরিচয় হয় সিনেমা দল এর পরিচালক এর সাথে। হরেন পরিচালককে বলে সে কলকাতা থেকে কার্ল মার্ক্সের বই এনে সিনেমা করতে চেয়েছিলো। এটি শুনে আশ্চর্য হন পরিচালক। হরেন এর কথায় আরও চমকে যান ডিরেক্টর। কারণ, হরেন বলে তার চেহারা নাকি রুশদের মতো এবং কার্ল মার্ক্সের সেই বইয়ের নাম ভূমিকায় নাকি তার অভিনয় করার কথা ছিলো। তখন পরিচালক গ্রামের মানুষের জানার অক্ষমাতা সম্পর্কে বুঝতে পারলেন এবং তিনি পুরোপুরি নিশ্চিত হন যখন সেখানে বলা হয় বিশ্বের শ্রেষ্ঠ সুন্দরী হচ্ছেন এন্তনিও কুইন। কুইন ছিলেন ‘গান্স অব ন্যাভেরন’ সিনেমার একজন অভিনেতা কিন্তু তাকে বলা হচ্ছে সুন্দরী।
ছবির অন্য আরেকটি চরিত্র হলো ‘দূর্গা’। শ্যুটিং সেটে পরিচারিকার কাজ করে দুর্গা। শ্যুটিংয়ে পারিবারিক কলহের সময় যখন স্বামী রাগে তার বাচ্চাটাকে আছাড় দিয়ে মাটিতে ফেলতে যায়, তখন সেই দুর্গা চিৎকার দিয়ে উঠে। শ্যুটিং সেট পুরোটাই চুপ হয়ে যায়। স্তব্ধ হয়ে যান পরিচালক নিজেই। ধীরে ধীরে শ্যুটিং স্পট থেকে বের হয়ে যায় দূর্গা।
দূর্গা তো তেতাল্লিশের আকাল দেখেনি। তাহলে এই অবস্থা দেখে তার আঁতকে ওঠার কারণ কী হতে পারে? তার একটি বাচ্চা রয়েছে। ঘরে তার স্বামী অসুস্থ হয়ে পড়ে আছে। এ অবস্থায় তার এই প্রতিক্রিয়ার একটাই মানে হতে পারে। বর্তমানে টিকে আছে আকাল। তার মতো অনেকেই সেই আকালের ভুক্তভোগী। পরিবারকে চালাতে হয় কষ্ট করে। হয়তো ঘৃণার পথ বেছে নিতে পারেন না। কিন্তু অন্যের হয়ে গতর খেটে কাজ করে সেই আকালকে সামাল দিচ্ছেন তারা। তবে তাদের মনের ভেতরে টিকে আছে প্রচণ্ড দুঃখবোধ, যা প্রায়ই বেরিয়ে আসতে চায়।
আকালের সন্ধানে‘-র সবচেয়ে শক্তিশালী দিক হলো চিত্রনাট্য, অভিনয় এবং সম্পাদনা। মৃণাল সেন বলতে চেয়েছেন মধ্যবিত্ত মূল্যবোধের অন্তঃসারশূন্যতা। ছবিতে যে গ্রামে শ্যুটিংএর কথা, সে গ্রামও আকালের ভুক্তভোগী- গ্রামের উচ্চবর্ণের তরুণীর বাবা মেয়েকে চটুল বাণিজ্যিক ছবিতে অভিনয় করতে দিতে উৎসাহী, অথচ তিনি ‘ব্রাহ্মণ পরিবারের’ মেয়েকে মন্বন্তরের শিকার এক পতিতার ভূমিকায় অভিনয় করতে দিতে ভীষণ নারাজ। আকালের তাড়নায় পতিতা হওয়া দেখানোটা তাঁর কাছে ভয়ংকর অনৈতিক ও অশ্লীল। তারপর গ্রামের সাধারণ মানুষদের সহজেই ক্ষেপিয়ে তোলা হলো শহর থেকে আসা ছবি-নির্মাতাদের বিরুদ্ধে, অশ্লীলতার দোহাই দিয়ে। আমার মতে এটি মৃণালের মধ্যবিত্ত সমাজের দ্বিচারিতার মুখোশ খুলে দেওয়ার একটি অতি প্রকৃষ্ট উদাহরণ। একটি দৃশ্যে শুটিং সেটের ডিরেক্টর বলতে থাকে, “১৯৪৩। সারা পৃথিবীতে যুদ্ধ। আর আমাদের দেশে? এই বাংলাদেশে? দেশ তখনও ভাগ হয়নি। একটা গুলি চললো না, একটা বোমাও পড়লো না। কিন্তু একটি বছরে মরে গেল ৫০ লক্ষ মানুষ। স্রেফ না খেতে পেয়ে। দে জাস্ট স্টার্ভড অ্যান্ড ড্রপড ডেড।” সিনেমার ইতিহাসে এমন সাহসী যুক্তি সম্পন্ন সংলাপ শুধু মাত্র মৃণাল সেন এর মতো পরিচালকরাই হয়তো ব্যাবহার করেছেন।
মৃণাল সেন পরিচালক হিসেবে কতটা দক্ষ সেটি তিনি প্রমাণ করেছেন বহু আগেই কিন্তু এই সিনেমায় তিনি উদ্ভাবন করেছেন নতুন এক ধারা কিংবা সিস্টেম। আকালের সন্ধানে যেহেতু ‘ফিল্ম উইদিন ফিল্ম’ তাই শট নেওয়ার সেটআপও ছিলো সত্যিকার শ্যুটিং সেটের মতো। আশির দশকের চলচ্চিত্রের ফ্রেমিংয়ে এত ডিটেইলিং ছিলো উল্লেখযোগ্য ব্যপার। প্রতিটা দৃশ্য এবং সাথে চলমান আবহ সংগীত ছিলো যথেষ্ট জীবন্ত।
মৃণাল সেন দেখেছিলেন অমানবিক দেশভাগে বাংলার টুকরো হয়ে যাওয়া। উপনিবেশ শাসনোত্তর এক অপদার্থ রাষ্ট্র রোধ করতে পারেনি বাংলার ভয়াবহ দাঙ্গা, আটকাতে পারেনি ক্রমশ ধ্বসে পড়া অর্থনীতি, বেকারত্ব, উদ্বাস্তু, দারিদ্র্য। এই সমস্যার পরিপ্রেক্ষিতে উঠে এসেছিলো বাম রাজনীতি, তৈরি হয়েছিলো যুক্তিহীন, আবেগতাড়িত ‘আমরা-ওরার’ সাদা-কালো বিভাজন। ‘আমরা’ অর্থাৎ শোষিত শ্রমজীবী এবং ‘ওরা’ অর্থাৎ শোষক–বড়লোক, শিল্পপতি এবং আমলার দল। এই সরলীকরণ অতি সহজপাচ্য, তাই এতেই ভেসে গিয়েছিলো বাংলা, ভেসেছিলেন মৃণাল সেন। ‘বাইশে শ্রাবণ’, ‘কলকাতা ট্রিলজি’, ‘কোরাস’ সৃষ্টির অন্তর্নিহিত আবেগ হয়ত এটাই ছিলো। এ ছবিগুলিতে মৃণাল সরাসরি প্রশ্ন করেছিলেন সামাজিক অদক্ষতা, মানবিক ও নৈতিক মূল্যবোধের অবক্ষয়ের বিরুদ্ধে, আঙুল তুলেছিলেন ‘ওদের’ দিকে। শীঘ্রই মৃণাল সরে আসেন আবেগতাড়িত ভাবনা থেকে। শুরু হয় তাঁর আত্মবীক্ষার পর্ব, নিজেদের দিকে তাকিয়ে দেখা; ‘পদাতিক’ দিয়ে যার শুরু, ‘একদিন প্রতিদিন’, তারপর ‘আকালের সন্ধানে’।
মৃণাল সেন তো কেবল একজন নিছক চলচ্চিত্রকারই ছিলেন না। মৃণাল সেন ছিলেন চলচ্চিত্র আন্দোলন থেকে সাংস্কৃতিক আন্দোলন, সমাজ ও রাজনীতির অন্যতম শ্রেষ্ঠ পুরোধা। যিনি সমাজ, রাজনীতি, সংস্কৃতি, গণ মানুষের ভাষ্য সমস্ত কিছুকে বিবেচনা করতেন চলচ্চিত্রের দলিল হিসেবে। মৃণাল সেনের চলচ্চিত্রের সবচেয়ে শক্তিশালী যে দিক তা হলো গল্পের বাস্তবতা। কাল্পনিক কোনো গল্পের স্থান ছিলো না মৃণাল সেনের চলচ্চিত্রে। অতি সাধারণ মানুষের জীবনের গল্প, পারিপার্শ্বিক অবস্থান, রাজনীতির চিরন্তন বাস্তবতা, অভাব, দৈনন্দিন চিত্র, মানুষের পরিভাষাই ছিলো মৃণাল সেনের চলচ্চিত্রের গল্প। যে গল্পগুলো সচেতনভাবেই বেশিরভাগ চলচ্চিত্রকাররা এড়িয়ে চলেন। তার চলচ্চিত্র নিয়ে তিনি নিজেই বলেন, “আমি অন্যদের মতো কাহিনী নির্ভর ছবি তৈরি করিনি। ডকুমেন্টারি ফিল্মমেকার আমি নই। আমার সিনেমা জ্ঞান ও প্রমাণ দিয়ে বুঝতে হবে।”
“আপনি বিভিন্ন ভাষায় এত ছবি করেন কেনো?” তাঁর কাছে এমন প্রশ্ন এসেছে বারেবারে। একটাই উত্তর ছিলো “আমি দারিদ্র্য নিয়ে ছবি করি। ধেয়ে আফ্রিকাতে গিয়ে সোয়াহিলি ভাষায় ছবি করতেও আমার কোনো অসুবিধে হবে না।” ভাষা তাই তাঁর কাছে বাধা হয়নি কখনও। বরং তিনি ছুটেছেন বিষয়ের কাছে। বারবার বেছে নিয়েছেন গ্রাম্যতাকে, ক্যামেরা তাক করেছেন গরীবগুর্বো মানুষগুলোর চোখে-মুখে। ‘মাটির মনিষা’ করার জন্যে ছুটেছেন উড়িশার গ্রামে, ‘ভুবন সোম’ করতে গুজরাটের প্রত্যন্ত প্রান্তে, ‘ওকা উড়ি কথা’ বা ‘কফন’-এর সময় তেলেঙ্গানার অজপাড়া গ্রামেও পৌঁছেছিলেন মৃণাল সেন।
মৃণাল সেন এমন একজন ব্যক্তিত্ব ইরানের বিখ্যাত নির্মাতা জাফর পানাহি কলকাতায় এসে যাঁর খোঁজ করেন। কিংবদন্তি নির্মাতা মার্টিন স্করসেজির ব্যাক্তিগত আর্কাইভ এ যিনি থাকেন। যার বন্ধু ছিলেন নোবেল বিজয়ী গ্যাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেস, যিনি নিজে মৃণাল সেন কে তার গল্পে সিনেমা বানানোর প্রস্তাব দিয়েছিলেন।
তেতাল্লিশ এর দুর্ভিক্ষ নিয়ে ‘অশনি সংকেত’ বানিয়েছিলেন সত্যজিত রায় কিন্তু মৃণাল সেন এর আকালের সন্ধানের সাথে রয়েছে অনেক পার্থক্য। ‘আকালের সন্ধানে’, ‘অশনি সংকেত’ এর মতো কাব্যিক নয় কিন্তু তার অভিঘাত বড় সাংঘাতিক।
মৃণাল সেন বরাবরের মতই প্রচন্ড স্পষ্টবাদী ছিলেন এই সিনেমায়। আজও বাঙালির কৃষক শ্রমিক এবং সমাজের নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণির মানুষ ক্ষুধা এবং দরিদ্রতার আঁধারে নিমজ্জিত। প্রতিনিয়তই আমরা খবরের কাগজের কোনো ক্ষুদ্র প্যারায় দেখতে পাই, ক্ষুধার যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে আত্মহত্যার পথ বেছে নিচ্ছে সন্তান অথবা বৃদ্ধ মা, বাবা। তার এই সিনেমায় তেতাল্লিশ থেকে আশির দশকের গ্রাম বাংলার মানুষের দুঃখ বেদনা মিলেমিশে একাকার হয়েছে। যে চিত্র আজও প্রতীয়মান রয়েছে স্পষ্টভাবে। এই সিনেমার ডায়ালগ গুলোর মত আজও প্রাসঙ্গিক গ্রাম বাংলার আর্থসামাজিক অবস্থা।
“আকাল এখনও আমাদের সর্বাঙ্গে।“