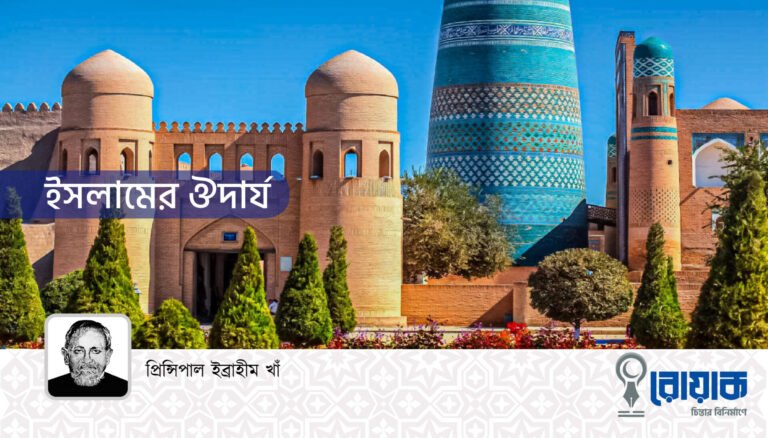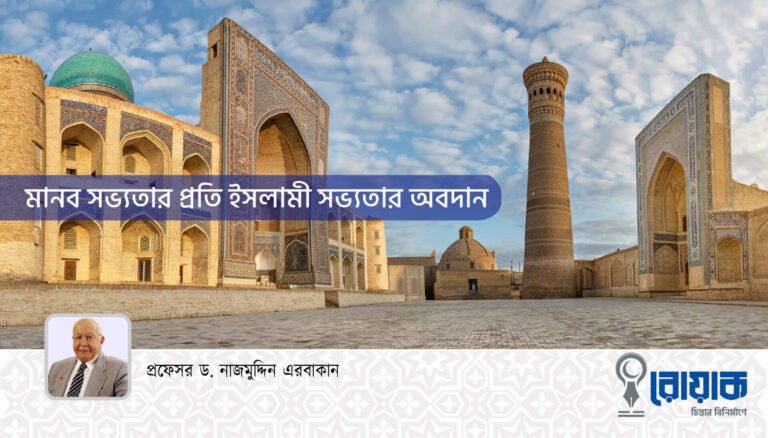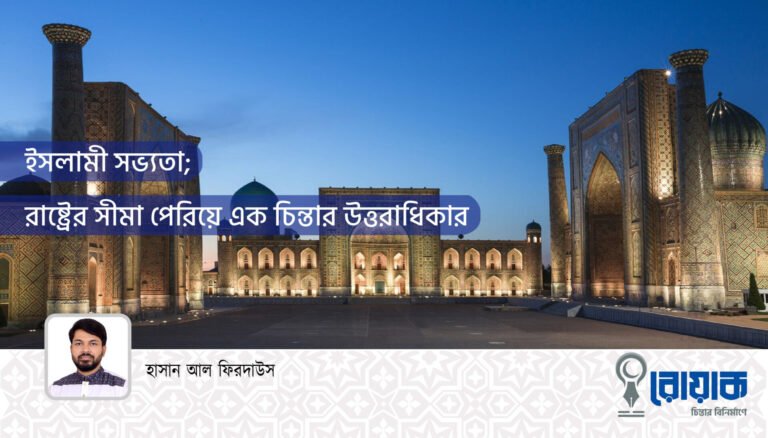প্রায়োগিক অর্থনীতির ক্ষেত্রে প্রাচ্যের প্রাচীন চিন্তাবিদদের ব্যপক ভূমিকা রয়েছে। কিন্তু এক্ষেত্রে পাশ্চাত্যের চিন্তাবিদগণ প্রাচ্যকে একেবারেই আলোচনার বাহিরে রেখে দিয়েছেন। এর কারণ মূলত পাশ্চাত্যে এরকম একটি প্রচারণা রয়েছে যে, ইউরোপীয় রেনেসাঁর পূর্বে অর্থাৎ দ্বাদশ শতাব্দীর আগে অর্থনীতি নিয়ে কোনো ধ্যান ধারণাই দুনিয়াতে ছিল না।১ অন্যদিকে পাশ্চাত্যের চিন্তাবিদগণ যে বিষয়ে আলোচনা করেন না তা অন্য কোথাও আলোচনা হয় না, এই প্রথা ইতোমধ্যেই পাশ্চাত্যের চিন্তাবিদগণ প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছেন।
যদিও এই ধারণাকে প্রত্যাখ্যান করে বর্তমানে অনেক গ্রন্থ রচিত হয়েছে।২ কিন্তু সে সব গ্রন্থ এখনো অর্থনীতিবিদদের মূল্যায়নের অপেক্ষায় স্থবির হয়ে পড়ে আছে। এসকল গ্রন্থে আমাদের জন্য অসংখ্য অর্থনৈতিক চিন্তা উপস্থাপন করা হয়েছে। যেমন সুফি, বিভিন্ন সংস্কারক ও উলামাদের দর্শন, সমাজবিজ্ঞান, আখলাক কিংবা মুঘলদের জীবনী, সমৃদ্ধ ইতিহাস সম্বলিত গ্রন্থাবলি কিংবা আলাউদ্দিন খিলজির অর্থনৈতিক সংস্কার, সুলতান মুহাম্মদ তুঘলকের মুদ্রানীতি, শেরশাহ সুরির ভূমি জরিপ ইত্যাদি প্রত্যেকটি বিষয়ই কোনো না কোনো অর্থনৈতিক চিন্তার উপর গড়ে উঠেছে।
ভারতীয় উপমহাদেশের নেতৃত্ব স্থানীয় চিন্তাবিদ হওয়ায় স্বাভাবিকভাবেই শাহ ওয়ালীউল্লাহ দেহলভীর অর্থনৈতিক চিন্তা বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। তবে শাহ ওয়ালীউল্লাহর অর্থনৈতিক চিন্তার দুই একটি বিষয়ের উপর যে কয়টি প্রবন্ধ ও গ্রন্থ রচিত হয়েছে তা নেহায়েতই হাতেগোনা।৩ কিন্তু অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে তাঁর সকল চিন্তার সমন্বিত পাঠ ও নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে উপস্থাপন করা এখনো অনেক বাকি। তবে এই প্রবন্ধে আমরা কেবল তার ‘আল-ইরতিফাকাত’ তত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করবো। মূলত এই তত্ত্বটি আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের পর্যায়ে পড়ে। আশাকরি এই প্রবন্ধ শাহ ওয়ালীউল্লাহ দেহলভীর অর্থনৈতিক চিন্তা নিয়ে গবেষক ও চিন্তাবিদদের মাঝে নতুন করে চিন্তা করার ক্ষেত্র তৈরি করবে।
শাহ ওয়ালীউল্লাহর অর্থনৈতিক চিন্তার বৃহৎ অংশ মূলত ক্ষয়িষ্ণু মুঘল সালতানাতের চুলচেরা বিশ্লেষণ ও উত্তরণকল্পে প্রদানকৃত অর্থনৈতিক সংস্কারের রূপরেখা এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়নকল্পে তাঁর অভিব্যক্তিমূলক আল-ইরতিফাকাত তত্ত্বের মাঝে লুকায়িত।
শাহ ওয়ালীউল্লাহ এবং তার সময়কাল
২১ সেপ্টেম্বর ১৭০৩ সালে শাহ ওয়ালীউল্লাহ ভারতের মুজাফফরনগরে জন্মগ্রহণ করেন এবং ২০ আগস্ট, ১৭৬২ তে মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর প্রকৃত নাম আহমেদ ইবনে আব্দুর রহিম। তিনি তাঁর জীবদ্দশায় পাঁচ জন মুঘল সুলতানের পতন দেখেছেন। শাহ ওয়ালীউল্লাহ এমন সময় জন্মগ্রহণ করেন যখন মহান সম্রাট জহিরউদ্দীন বাবরের প্রতিষ্ঠিত মুঘল সালতানাত পতনের দ্বার প্রান্তে। একই সময়ে মৌলিক জ্ঞান ও চিন্তার বিকাশ এবং মুসলমানদের রাজনৈতিক অধঃপতনের স্বাক্ষী এই আলেম তৎকালীন সময়ের বিদ্যমান জ্ঞানের সকল শাখায় পারদর্শী ছিলেন। কোরআন ও হাদীসের মূলনীতির ব্যাখ্যা, বিচার ব্যবস্থা, ইলমুল কালাম, দর্শন, ফিকহ, হিকমত ও মাকাসিদ আশ-শরিয়াহর ক্ষেত্রে তাঁর বিশাল অবদান রয়েছে। ১৭৩০ সালে তিনি হিজাজে গমন করেন এবং সেখানে তিনি ২ বছর অবস্থান করে মক্কা এবং মদীনায় অবস্থানরত আলেমদের সান্নিধ্য লাভ করেন। তখন নজদে মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল ওয়াহাবের (১৭০৩-১৭৯২) সংস্কারের যুগ চলছিল। যদিও তাদের দুজনের মাঝে সাক্ষাতের কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না। তবে শাহ ওয়ালীউল্লাহর সংস্কার কেবলমাত্র ধর্মতাত্ত্বিক জায়গায় সীমাবদ্ধ ছিল না, তাঁর সংস্কার আরো অনেক ব্যাপক-বিস্তৃত সামগ্রিক রূপ লাভ করেছিল। তিনি একইসাথে শিক্ষাব্যবস্থা, অর্থনীতি, সমাজ ও রাষ্ট্রের সংস্কারে মনোযোগী ছিলেন।
শাহ ওয়ালীউল্লাহর চিন্তায় অর্থনীতি
শাহ ওয়ালীউল্লাহর অর্থনৈতিক চিন্তাগুলো তাঁর বিভিন্ন গ্রন্থে পাওয়া যায়। যেমন ‘হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ’, ‘আল বুদুর আল বাজিগাহ’, ‘আত-তাফহিমাত আল ইলাহিয়া’র মতো গ্রন্থ ছাড়াও বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন অঞ্চলের শাসক, গভর্নর, বিজ্ঞ আলেমদের নিকট প্রেরিত চিঠিগুলোর মাঝেও তাঁর অর্থনৈতিক চিন্তাগুলো ফোঁটে উঠে। বিশেষত তাঁর লেখা চিঠিগুলোয় তিনি মুঘল সালতানাতের পতনের জন্য অর্থনৈতিক পন্থাকে ব্যাপকভাবে সমালোচনা করেছেন। তাঁর এসকল তীক্ষ্ণ সমালোচনা এখনো অনেককে গভীর চিন্তায় নিমজ্জিত করে।
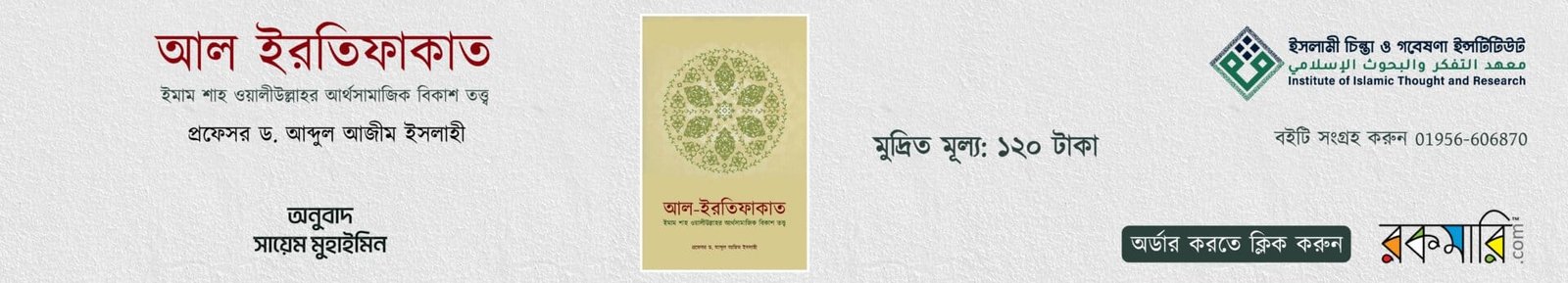
শাহ ওয়ালীউল্লাহর সমসাময়িক একজন আলেম যিনি খুব কাছ থেকে তৎকালীন পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করেছেন এবং একইসাথে শাহ ওয়ালীউল্লাহকেও অধ্যয়ন করেছেন, তাঁর দৃষ্টিকোণ শাহ ওয়ালীউল্লাহর অর্থনৈতিক চিন্তাগুলো পড়ার চেষ্টা করবো। আশাকরি এই সংক্ষিপ্ত আলোচনা আপনাদেরকে শাহ ওয়ালীউল্লাহর চিন্তাকে বুঝতে সহায়তা করবে।
ভারতে মুঘল শাসন অবসানের ক্ষেত্রে দুর্বল অর্থনীতি
শাহ ওয়ালীউল্লাহর সময়কালে মারাঠা, জাঠ, শিখ, রোহিলা ও বিভিন্ন প্রদেশে মুঘল গভর্নরদের দূরভিসন্ধিতে সৃষ্ট নৈরাজ্য ও বিশৃঙ্খলা বিরাজমান ছিল। এসময় মুঘল সম্রাটরা কার্যত লালকেল্লা আর পালামপুর গ্রামের মাঝেই সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে। কৃষক এবং কারিগর সম্প্রদায় খুব খারাপভাবে দরিদ্র হয়ে পড়ে। ঘন ঘন ক্ষমতার রদ বদলের কারণে তাদেরকে বছরে কয়েকবার করে খাজনা প্রদান করতে হতো। সেনাবাহিনী ও আমলারা মাসিক হিসেবে বেতন পেত না।৪ ন্যায়পরায়ণতার মূর্তপ্রতীক মুঘল সম্রাটরা এসময় একেবারেই অসহায় হয়ে পড়ে। শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুঘল সালাতানের পতনের মূল কারণ উল্লেখপূর্বক এ সংকট মোকাবেলায় যে সকল প্রস্তাবনা দেন সেগুলো হলো-
১. রাজস্ব সংকট : রাজস্ব যেকোনো রাষ্ট্রের মূল চালিকাশক্তি। পর্যাপ্ত পরিমাণ রাজস্ব ছাড়া কোনো রাষ্ট্রই সঠিকভাবে তার কার্যক্রম সম্পাদন করতে পারে না। শাহ ওয়ালীউল্লাহর মতে রাজস্ব আট কোটি রুপির মতো হলেও এই পরিমাণ রাজস্ব আয় করা যে সম্ভব তা উপলব্ধি করার মতো শক্তি রাজস্ব কর্তৃপক্ষ ও কেন্দ্রীয় সরকার হারিয়ে ফেলেছিল।৫
২. খালিসা জমির পরিমাণ হ্রাস পাওয়া : খালিসা বলতে সরকারি জমিকে বুঝানো হয়ে থাকে। এই সব ভূমি থেকে প্রাপ্ত রাজস্ব সরাসরি রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা হয়ে থাকে, অন্যদিকে জায়গীরের আওতাধীন জমির রাজস্ব জায়গীরদাররা আদায় করতো। খালিসা জমি ছিল রাজস্ব আয়ের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উৎস। প্রত্যেক শাসক-ই খালিসা আয়তন বৃদ্ধির চেষ্টা করতেন। শাহ ওয়ালীউল্লাহর খালিসা ভূমির বৃদ্ধির প্রতি জোর দেন। বিশেষত দিল্লির আশপাশের অঞ্চল, হিসার ও সিরহিন্দে এই ধরনের ভূমি বৃদ্ধিতে তিনি বিশেষ গুরুত্বারোপ করেন। তিনি রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক দুর্বলতা এবং অপর্যাপ্ত রাজস্ব আয়ের কারণে এই সম্পূর্ণ অঞ্চল অথবা এই অঞ্চলের বেশিরভাগ অংশকে খালিসার আওতাধীন করার প্রস্তাবনা দেন।৬
৩. জায়গীরের সংখ্যা বৃদ্ধি : খালিসা ভূমির সংকোচনের ফলে স্বাভাবিকভাবেই জায়গীরের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে। কিন্তু এসকল ছোট জায়গীরদাররা তাদের আওতাধীন এলাকা নিয়ন্ত্রণে সক্ষম ছিল না। যার ফলে তারা এসব ভূমি ভাড়া দিয়ে দিতে শুরু করে যা অস্থিতিশীল ও নৈরাজ্যকর পরিস্থিতির সৃষ্টি করে। এক্ষেত্রে শাহ ওয়ালীউল্লাহর প্রস্তাবনা ছিল জায়গীরদারী প্রদানের ক্ষমতা কেবলমাত্র রাষ্ট্রপ্রধানের হাতে সীমাবদ্ধ থাকুক। এছাড়া ছোট-খাটো জায়গীরদার থেকে আদায় নগদে হওয়া উচিত, যেমনটা সম্রাট শাহজাহানের আমলে হতো। কেননা এসকল ছোট জায়গীরদাররা তাদের আওতাধীন ভূমি ভাড়ায় প্রদান করতো এবং বেশিরভাগই অর্থকষ্টে ভুগত। ফলে তারা রাষ্ট্র কর্তৃক অর্পিত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করতে পারতো না।৭
৪. সেনাবাহিনী ও আমলাদের অনিয়মিত বেতন প্রদান : মুঘল সালতানাতের পতনের অন্যতম আরেকটি কারণ ছিল সেনাবাহিনী এবং আমলাদের বেতন প্রদানের স্বাভাবিক নিয়মের ব্যত্যয় ঘটা। এই ব্যত্যয় ঘটার কারণ যে রাষ্ট্রীয় সম্পদের অপর্যাপ্ততা তা আগেই বলা হয়েছে। এক্ষেত্রে শাহ ওয়ালীউল্লাহ সেনাবাহিনী ও রাষ্ট্রীয় কাজে নিয়োজিত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বিলম্বে বেতন প্রদানের কঠোর বিরোধিতা করেন। তিনি মনে করেন, সৈন্যদের যদি বেতন পেতে দেরি হয় তবে তারা সুদের উপর ঋণ নিতে বাধ্য হবে। আর সুদের চক্রে আবর্ত হয়ে তারা আরো বেশি দুর্ভোগের শিকার হবে, ফলে তাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করতে পারবে না।৮
৫. করের বোঝা বৃদ্ধি এবং উৎপাদন হ্রাস পাওয়া : রাষ্ট্রের ব্যয় মিটাতে কৃষক ও কারিগর শ্রেণির উপর করের বোঝা চাপিয়ে দেওয়া হয়। ফলে কৃষক ও কারিগরি পেশায় লাভ কমতে থাকে, যা স্বাভাবিকভাবেই উৎপাদন কমিয়ে দেয়। শাহ ওয়ালীউল্লাহ তাঁর হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহতে এ ব্যপারে বলেন,”আরেকটি কারণ হচ্ছে করের বোঝা চাপিয়ে দেওয়া এবং কর আদায়ের নির্মম পন্থা”।৯
৬. উচ্চাভিলাষী জীবনযাত্রা : শাহ ওয়ালীউল্লাহ অর্থনৈতিক সংকটকে মুঘল সালতানাতের পতনের একটি কারণ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন, তবে একমাত্র কারণ হিসেব নয়। তিনি অর্থনৈতিক সংকটের পাশাপাশি উচ্চাভিলাষী জীবনযাত্রা, আখলাকী অধঃপতন, সামাজিক বিশৃঙ্খলা, রাজনৈতিক অস্থিরতাকে মুঘল সালাতানাতের পতনের কারণ হিসেবেও উল্লেখ করেন।১০ এখানে প্রত্যেকটি বিষয়ে আলোচনা করা সম্ভব নয়। শাহ ওয়ালীউল্লাহর মতে, এসকল সংকটের মূলে রয়েছে আল-ইরতিফাকাত আশ-শারিয়াহর লঙ্ঘন করা। অর্থনীতির ক্ষেত্রে শাহ ওয়ালীউল্লাহর প্রস্তাবিত সকল সমাধান মূলত তাঁর আল-ইরতিফাকাত তত্ত্বে চারটি পর্যায়কে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়েছে। এই পর্যায়ে আমরা সংক্ষেপে আল-ইরতিফাকাত তত্ত্বকে বুঝার চেষ্টা করবো।
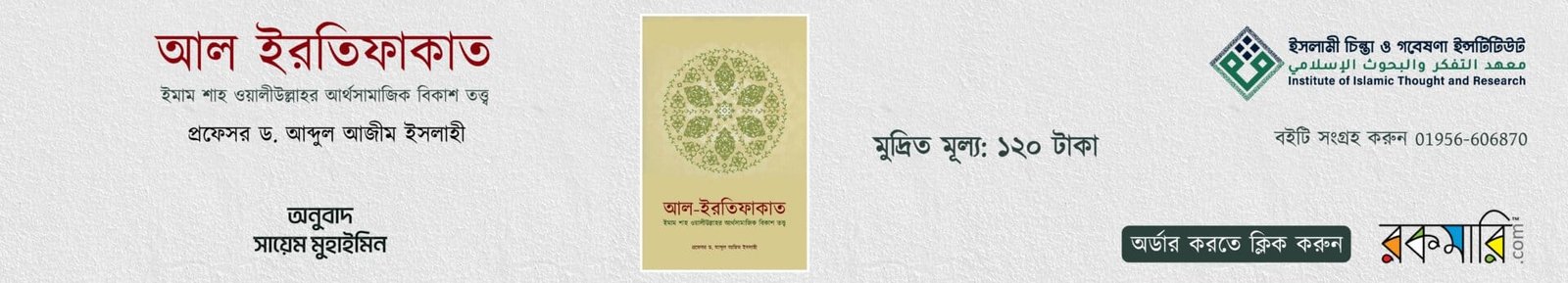
আল-ইতিফাকাত তত্ত্ব
ইরতিফাকাত একটি আরবি শব্দ, এর মূল হচ্ছে (র, ফা, ক্বফ)। যার অর্থ হচ্ছে সহনশীল হওয়া, দয়ালু, পরোপকারী, লাভজনক, সুবিধাজনক ইত্যাদি। ইরতিফাকাত শব্দটি দ্বারা সুবিধাজনক পথ, সাহায্যকারী উপাদান, লাভজনক পন্থা, কার্যকর প্রযুক্তি এবং ব্যক্তি জীবনে আদবের অধিকারী হওয়া বুঝিয়ে থাকে। শাহ ওয়ালীউল্লাহ এই শব্দটিকে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের বিশেষ একটি পন্থা বুঝাতে ব্যবহার করেছেন। তাঁর মতে, গ্রাম্য সমাজ থেকে শুরু করে আন্তর্জাতিক পর্যায় পর্যন্ত মানুষের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নকে চারটি পর্যায়ে বিভক্ত করা যায়। যেখানে প্রথম পর্যায়ে অর্থনৈতিক সংগ্রাম গুরুত্ব পেয়েছে এবং শেষ পর্যায়ে আর্থ-সামাজিক সুরক্ষা নিশ্চিতকল্পে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে শান্তি ও আদালত প্রতিষ্ঠায় যথাযথ রাজনীতির বিকাশ গুরুত্ব পেয়েছে। শাহ ওয়ালীউল্লাহর সকল অর্থনৈতিক চিন্তা মূলত আল-ইরতিফাকাত তথা আর্থ-সামাজিক উন্নয়নকে কেন্দ্র করে বিকশিত হয়েছে।
আল-ইরতিফাকাত এর প্রথম পর্যায়
আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের প্রথম পর্যায়ে আলোচনার বিষয়বস্তু হচ্ছে জীবজন্তু, স্বচ্ছতা, পারস্পরিক যোগাযোগ, সমাজের পরিশুদ্ধি, বুদ্ধিবৃত্তি।১১ আল-ইরতিফাকাতের প্রথম পর্যায় মানুষকে কোনো প্রকার প্রতিবন্ধকতায় নিমজ্জিত না থেকে উন্মুক্তভাবে নিজের মত প্রকাশের সক্ষমতা অর্জন করার দিকনির্দেশনা দেয়। এই পর্যায়ে মানুষ তার শরীর গঠনের জন্য উপযুক্ত খাদ্য-দ্রব্যের সাথে পরিচিত হয় এবং এই সকল খাদ্য-দ্রব্যকে খাবার উপযোগী করার পদ্ধতির সাথে অবগত হয়। এছাড়াও এ জাতীয় ফসলের চাষাবাদ, সেচ, ফসল সংগ্রহ, সংরক্ষণ থেকে শুরু করে এসকল ফসল রান্না করার প্রক্রিয়া সম্পর্কেও পূর্ণাঙ্গ ধারণা লাভ করতে হয়। সেই সাথে পশু-পালন ও গৃহপালিত পশু থেকে চামড়া, দুধ, ঘি ইত্যাদি উৎপাদনের মাধ্যমে উপকৃত হওয়ার পদ্ধতিও শিখতে হয়। কেননা পশুপালন সম্পর্কে যথাযথ জ্ঞানারোহণ ছাড়া ফসল উৎপাদন থেকে শুরু করে মৌলিক জীবনযাত্রার জন্য প্রয়োজনীয় কার্যক্রম পরিচালনা করা কষ্টকর হয়ে পড়ে। শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা থেকে সুরক্ষায় পশুর চামড়া থেকে তৈরি বস্ত্র কিংবা গাছের পাতার ছাউনি থেকে শুরু করে আধুনিক পোশাক ও বাসস্থান প্রণালীও এই পর্যায়ের আলোচনার বিষয়।
এছাড়াও পরিবাবের মৌলিক ধারণা, জৈবিক চাহিদা পূরণ ও প্রজননও এই পর্যায়ের আলোচনার অন্যতম বিষয়বস্তু।১২ এই প্রাথমিক পর্যায়ে মানুষ কৃষি ও বাসস্থানের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি তৈরি করে, পণ্যের আদান-প্রদানের মাধ্যমে নিজেদের মাঝে একটি আন্তঃসম্পর্ক গড়ে তুলে এবং মানুষের দ্বারা সৃষ্ট এই সমাজে মানুষ সামাজিক বিচার ব্যবস্থা ও ক্ষমতার একটি সুবিন্যস্ত কাঠামো গড়ে তুলে। যেখানে তাদের মধ্যকার বিরোধগুলোর নিষ্পত্তি থেকে শুরু করে দুষ্কৃতিকারী-অপরাধীদের উপযুক্ত শাস্তি প্রদান করা হয়। অন্যদিকে বুদ্ধিবৃত্তিক পর্যায়ে একজন বুদ্ধিজীবী ঐ সমাজের বাস্তব পরিস্থিতির আলোকে প্রত্যেকটি বিষয়ের জন্য ইরতিফাকাতের পন্থা খুঁজে বের করেন, যেন সমাজের বাকিরা এই পন্থার আলোকে সমাজকে সাজাতে পারেন।
শাহ ওয়ালীউল্লাহর আল ইরতিফাকাতের প্রথম পর্যায়ের বর্ণনায় আমরা একটি আদর্শ গ্রামীণ সমাজের আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থাপনার উল্লেখ দেখতে পাই। যেখানে একজন মানুষ তার অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান থেকে শুরু করে সকল মৌলিক চাহিদাগুলো প্রকৃতি দেওয়া সুযোগ-সুবিধা থেকে পূরণ করে। এখানে সে সমাজের মাধ্যমে আদালত প্রতিষ্ঠা করে। এই ব্যবস্থাপনায় মানুষ তার অর্থনৈতিক চাহিদাগুলো সামাজিক রীতি-নীতির মাধ্যমে পূরণ করে। কিন্তু এই সামাজিক কাঠামোয় কর্মীয় শ্রেণিবিন্যাস খুব একটা দেখতে পাওয়া যায় না এবং এখানে আধুনিক বাজার ব্যবস্থাও অনুপস্থিত। মূলত আল-ইরতিফাকাতের প্রথম পর্যায় মানুষের সমাজকে পশুদের জীবনপ্রণালী থেকে পার্থক্য করে এবং একইসাথে এটি আল-ইরতিফাকাতের দ্বিতীয় পর্যায়কে বুঝার প্রাথমিক শর্ত।
আল-ইরতিফাকাত এর দ্বিতীয় পর্যায়
মানুষ যখন অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থানের মতো মৌলিক চাহিদাগুলো পূরণ করে তখনই সে আর্থ-সামাজিক উন্নতির স্তরে প্রবেশ করে।১৪ এই পর্যায়ে এসে তার আখলাক ও বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশ প্রথম পর্যায়কে ছাড়িয়ে যায়।১৫ জীবনযাত্রায় জটিলতা বৃদ্ধি পেতে থাকে। ফলে সমাজ পরিচালনায়, নীতি-নির্ধারণে, আদর্শ মানদ- স্থাপনে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিতে থাকে। এই পর্যায়ে এসে তিনি ক্রমান্বয়ে ৫ টি হিকমত আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন-
১. হিকমত আল মাসিয়াহ বা জীবনযাত্রা সম্পর্কিত জ্ঞান। যা একটি নির্দিষ্ট মানদন্ডের আলোকে শিষ্টাচার, খাওয়া-দাওয়া, পোশাক-পরিচ্ছদ থেকে শুরু করে আদব-কায়দা তথা বসবাস সম্পর্কিত সকল বিষয়কে পরিচালনা করে থাকে।
২. হিকমত আল মানজিলিয়াহ বা গার্হস্থ্য জীবন সম্পর্কিত জ্ঞান। যা মূলত বৈবাহিক জীবন, সন্তান লালন-পালন, আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করা, পারস্পরিক সম্পর্ক বজায় রাখার আদব সম্পর্কিত জ্ঞান।
৩. হিকমত আল ইকতিসাবিয়াহ বা জীবিকা উপার্জন সম্পর্কিত জ্ঞান। ব্যক্তিকে তার সামর্থ্যরে জানান দেওয়ার মাধ্যম কামার, ছুতোর থেকে শুরু করে সমাজে বিদ্যমান সকল পেশাই আল হিকমত আল ইকতিসাবিয়াহর আলোচ্য বিষয়।
৪. হিকমত আত-তামুলিয়াহ বা পারস্পরিক বিনিময় সম্পর্কিত জ্ঞান। পণ্যের কেনা-বেচা, উপহার প্রদান, মালিক-ভাড়াটিয়ার সম্পর্ক, ঋণ, সঞ্চয়, বন্ধক, ওয়াকফ ইত্যাদি এখানের আলোচ্য বিষয়।
৫. হিকমত আল-তাউনিয়াহ বা সহযোগিতার প্রজ্ঞা। যা স্থায়ী জামিন, নীরব অংশীদারিত্ব, বাণিজ্যিক উদ্যোগ, পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি এবং ভোগদখলের সাথে সম্পর্কিত।১৬
উপর্যুক্ত ৫টি হিকমতের মাঝে প্রথম দুটি হিকমত সমাজবিজ্ঞান সম্পর্কিত এবং পরবর্তী তিনটি হিকমত অর্থনীতি সম্পর্কিত।১৭ আমরা প্রথমেই উল্লেখ করেছি। ইরতিফাকাতের দ্বিতীয় পর্যায় মূলত প্রথম পর্যায়ের উপর ভিত্তি করে দাঁড় করানো হয়েছে। যার ফলে প্রত্যকটি ধাপ একটি আরেকটির সাথে সংযুক্ত। এজন্য প্রত্যেকটি বিষয় সামনে রেখে সামগ্রিক-সমন্বিত রূপে চিন্তা করতে হবে। যেমন ইরতিফাকাত এর দ্বিতীয় পর্যায়ের প্রথম দুটি বিষয়কে আমরা ইরতিফাকাত এর প্রথম পর্যায়েও খুঁজে পাই। কিন্তু পার্থক্য হচ্ছে ক্রমান্বয়ে পরিমার্জিত-পরিবর্ধিত ক্রমশ বিকশিত রূপের মাঝে। যেমন মানুষের উচিত তার দ্বীন নির্দেশিত পন্থায় খাদ্য, পানীয়, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, সাজসজ্জা, পোশাক, বাসস্থান, কথা বলা, চলাফেরা, ভ্রমণ, বেচাকেনা, সহবাস, চিকিৎসা এবং স্বামী-স্ত্রী-সন্তানের সাথে তাকওয়ায় উন্নত নৈতিক প্রয়োজন অনুযায়ী জীবনযাপন করা।১৮ শাহ ওয়ালীউল্লাহ তাঁর বুদুর আল বাজিগাহতে একজন সাধারণ মানুষের চাওয়া পাওয়ার আলোকে জীবনযাত্রার একটি মডেল দাঁড় করিয়েছেন।১৯ যদিও আপাতত এটা আমাদের আলোচ্য বিষয় নয়। আমরা বরং আল ইরতিফাকাত এর দ্বিতীয় পর্যায়ের শেষ তিনটি হিকমত নিয়ে আলোচনা করবো। যেখানে শাহ ওয়ালীউল্লাহ মানুষের আর্থ-সামাজিক জীবনকে আরো বিকশিত এবং শক্তিশালী করার প্রচেষ্ঠা করেছেন।
হিকমত আল-ইকতিসাবিয়াহ
শাহ ওয়ালীউল্লাহর হিকমত আল-ইকতিসাবিয়াহ দ্বিতীয় ইরতিফাকাতের দিকগুলো হলো শ্রমের বিভাজন, বিশেষীকরণ, পেশাগত বৈচিত্র্য এবং অর্থের ব্যবহার।
শ্রমের বিভাজন
শাহ ওয়ালীউল্লাহর মতে মানুষ যখন আল-ইরতিফাকাত এর প্রথম পর্যায় ছাড়িয়ে আল-ইরতিফাকাত এর দ্বিতীয় পর্যায়ে প্রবেশ করে তখন মানুষের নানাবিধ চাহিদা ও একক ব্যক্তির পক্ষে সে সকল চাহিদার যোগান দেওয়ার সামর্থ্যহীনতার ফলে স্বাভাবিকভাবেই শ্রম বিভাজনের সৃষ্টি হয়।২০ এক্ষেত্রে তিনি কৃষিকে আমাদের সামনে উদাহরণ হিসেবে তুলে ধরে দেখান যে, শুধুমাত্র কৃষি কাজ করতেই প্রশিক্ষিত গবাদি পশু, নানান ধরণের যন্ত্রপাতি থেকে শুরু করে বিভিন্ন ধরণের পেশার মানুষের এখানে প্রয়োজন হয়। অনুরূপভাবে তিনি পোশাক শিল্পের উদাহরণ দিয়ে প্রমাণ করেন যে, যদি একই পরিবারের সবাই এসকল কাজ সম্পাদন করার চেষ্টা করে তবুও তারা আল-ইরতিফাকাতের প্রথম পর্যায়ে যে অবস্থার কথা তুলে ধরা হয়েছে সেই অবস্থাকে উত্তরণ করে আল ইরতিফাকাতের দ্বিতীয় পর্যায়ে প্রবেশ করতে পারবে না।২১ এই আলোচনা থেকে এটা স্পষ্ট যে, যখন কোনো সমাজ আল-ইরতিফাকাতের দ্বিতীয় পর্যায়ে প্রবেশ করে তখন সেখানে বিশেষায়িত কাজের উপর বিশেষভাবে দক্ষ শ্রেণি নানা রকম পেশার সৃষ্টি করে।
শাহ ওয়ালীউল্লাহর মতে, মৌলিক পেশাগুলো হলো কৃষিকাজ, পশুচারণ, সমুদ্র ও ভূমি থেকে প্রকৃতি প্রদত্ত নিয়ামত আহরণ যেমন ধাতু, গাছ, পশু-পাখি এবং এসকল নিয়ামত থেকে দক্ষতার মাধ্যমে শিল্প গড়ে তোলা যেমন ছুতোর, লোহার কাজ, বয়ন ইত্যাদি। দ্বিতীয় ধাপে আসে ব্যবসা-বাণিজ্য, নগর ব্যবস্থাপনা থেকে শুরু করে মানুষের নিত্য প্রয়োজনীয় সেবা ও পণ্যের ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি।২২ তাঁর মতে, একটি নির্দিষ্ট পেশায় একজন ব্যক্তির জন্য বিশেষীকরণের দুটি কারণ রয়েছে-
১. উদাহরণস্বরূপ শারীরিকভাবে সক্ষম একজন শক্তিশালী মানুষ যুদ্ধের জন্য ভালো; অন্যদিকে তীক্ষ্ণ স্মৃতিশক্তি সম্পন্ন একজন বুদ্ধিমান ব্যক্তি গণিতের জন্য উপযুক্ত; আবার একটি শক্তিশালী মানুষ অনেক ভারী জিনিস বহনের কাজের জন্য উপযুক্ত।
২. পরিবেশগত সুবিধা যেমন একজন কামারের ছেলে বা প্রতিবেশী সহজেই লোহার কাজ করতে পারে ঠিক তেমনি সমুদ্রের নিকটে বসবাসকারী ব্যক্তি মাছ ধরার সুবিধা পান যা পাহাড়ে বসবাসকারীরা পায় না।২৩
পেশাগত বৈচিত্র্য একজন মানুষকে তার বিশেষ দক্ষতার জন্য গুরুত্বপূর্ণ করে তুলে এবং এর ফলে ব্যক্তি একইসাথে সমাজের এবং নিজের প্রয়োজন পূরণ করে। শাহ ওয়ালীউল্লাহর মতে, ফরজে কিফায়ার বিধান রাখার অন্যতম একটি কারণ হলো সামাজিক কর্তব্যগুলোকে পেশাগত বৈচিত্র্যের মাধ্যমে আদায় করা এবং বিশেষ দক্ষতার জন্য ব্যক্তিকে সুবিধা দেওয়া। কেননা, সকলে একই কাজের উপযুক্ত নয়। প্রত্যেককে তার দক্ষতা অনুযায়ী কাজে লাগাতে হয়।২৪
শাহ ওয়ালীউল্লাহর মতে, প্রত্যেকের উচিত স্রোতের তালে গা না ভাসিয়ে তার নিজস্ব সক্ষমতার আলোকে পেশা নির্বাচন করা।২৫ এক্ষেত্রে তিনি সংশ্লিষ্টদের উপযুক্ত কাজে যথাযোগ্য ব্যক্তি নির্বাচনে, বেকারত্ব নিরসনে এবং বিলাসিতা পরিহারে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।২৫
সুযোগের সদ্ব্যবহার
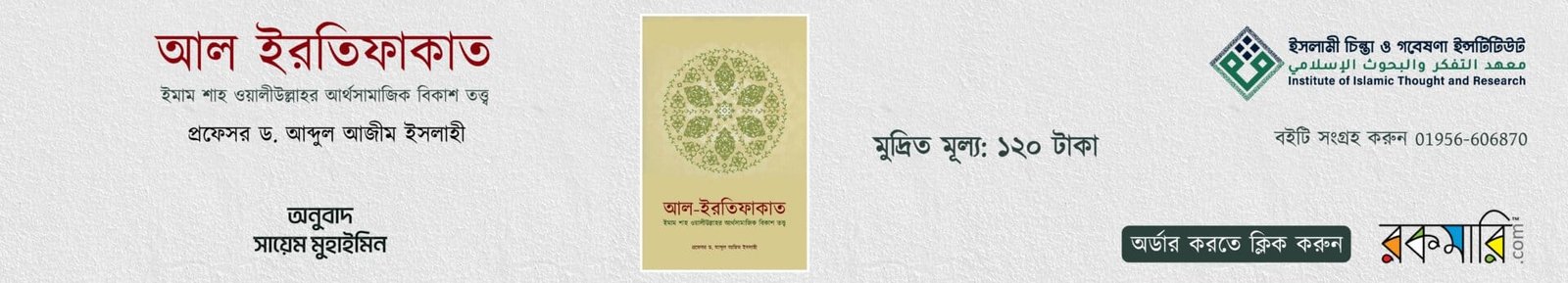
আর্থ-সামাজিক চাহিদার কথা আলোচনা করতে গিয়ে শাহ ওয়ালীউল্লাহ নগরপতিদের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন, “বিভিন্ন সরকারি প্রকল্প গ্রহণ ও সেই সকল প্রকল্পে লোক নিয়োগের ক্ষেত্রে সচেতন থাকতে হবে। যেন প্রয়োজনের অতিরিক্ত লোক নিয়োগ না হয় এবং খেয়াল রাখতে হবে যেন এসকল প্রকল্পের অধীনস্থ কর্মকর্তাদের এমন সুযোগ-সুবিধা যেন প্রদান করা না হয় যাতে লোকেরা শিল্প, কৃষি ও ব্যবসা-বাণিজ্যের মতো মৌলিক উৎপাদনমুখী পেশার প্রতি আকর্ষণ হারিয়ে ফেলে। কেননা এতে একইসাথে নাগরিকদের মধ্যে কিছু অংশ বিলাসিতায় নিমজ্জিত হয়, অন্যদিকে এধরণের পেশার মোহ কৃষি ও বাণিজ্যের প্রতি লোকদের আগ্রহ কমিয়ে দেয়, ফলে উৎপাদন কমে যায়।২৭
মুদ্রার ব্যবহার
শ্রমের বিভাজন এবং দক্ষতা ভিত্তিক পেশার উপস্থিতি নিশ্চিত করতে এমন একটি মাধ্যমের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয় যা দ্বারা সম্পদের বিনিময় সম্ভব। এই প্রয়োজনীয়তা থেকেই মুদ্রার উদ্ভব ঘটে। এভাবে আল ইরতিফাকাতের দ্বিতীয় পর্যায়ে এসে মুদ্রার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। শাহ ওয়ালীউল্লাহর মতে, মুদ্রা অবশ্যই বহনযোগ্য ও সর্বজনগ্রহণীয় বস্তু হওয়া উচিত।২৮ তার আল-বুদুর আল-বাজিগা গ্রন্থে তিনি বলেছেন, মুদ্রার নিজস্ব উপযোগিতা থাকা উচিত নয়; বরং মুদ্রা হওয়ার শর্ত হচ্ছে তা বিনিময়ে গ্রহণযোগ্য হতে হবে।২৯ হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা-তে তিনি উল্লেখ করেছেন, সোনা এবং রুপা মুদ্রা হিসাবে ব্যবহার করার জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত কারণ, এগুলো সহজেই ছোট ছোট টুকরোয় বিভক্ত করা যায় এবং খন্ডগুলোর মাঝে সাদৃশ্য বজায় থাকে। এছাড়াও এসকল ধাতু সকল মানুষের কাছেই গ্রহণযোগ্য। ফলে স্বাভাবিকভাবেই এসকল ধাতু মুদ্রা হিসেবে ব্যবহারের জন্য আদর্শ।৩০ এভাবে মূলত তিনি, যারা বলেন মুদ্রার নিজস্ব মূল্যমান থাকার প্রয়োজন নেই, তাদের বিরোধিতা করেছেন। তিনি মুদ্রা ব্যবস্থাকে ধাতব মুদ্রা এবং টোকেন মুদ্রা (বর্তমানে ব্যবহৃত মুদ্রা) এই দুভাগে বিভক্ত করেন এবং টোকেন মুদ্রার মানের দ্রুত পরিবর্তনশীলতার উপর ভিত্তি করে এ মুদ্রা ব্যবহারের ক্ষেত্রে কিছু ভিন্ন নিয়ম-নীতি দাঁড় করান।
হিকমত আত-তামুলিয়াহ
হিকমত আত-তামুলিয়াহর অধীনে শাহ ওয়ালীউল্লাহ বাণিজ্য, নিয়োগ, দান, ঋণ এবং বন্ধকী নিয়ে আলোচনা করেন। শ্রম বিভাজন এবং দক্ষতার উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত একটি অর্থনীতির জন্য এই ধরনের লেনদেনগুলো অপরিহার্য। কেননা এ ধরনের লেনদেনে জড়ানো ছাড়া কোনো সমাজ আল-ইরতিফাকাতের দ্বিতীয় পর্যায়ে উন্নীত হতে পারে না। এই সকল লেনদেনের পেছনে মূলত পারস্পরিক সহযোগিতা করা, সম্পদ ও শ্রমের বিনিময়ের মাধ্যমে নিজেদের প্রয়োজন পূরণ করাই মূল উদ্দেশ্য। সেই সাথে লেনদেনের মাধ্যমে আমানতদারিতা, বিশ্বস্ততা কামালিয়্যাত লাভ করে। মানুষের সাথে মানুষের এ ধরনের বিনিময়ের মাধ্যমে গড়ে উঠা পারস্পরিক সম্পর্কের উপর ভিত্তি করে বান্দা তার রবের কাছে মূল্যায়িত হবে। দুনিয়ার এসকল লেনদেনের ফলাফল সে আখিরাতে লাভ করে। শাহ ওয়ালীউল্লাহ ফিকহের আদলে এই চুক্তিগুলোকে সংজ্ঞায়িত করেছেন এবং বৈধতা ও ন্যায়পরায়ণতার প্রয়োজনীয়তা পূরণের জন্য শরীয়াহর গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশাবলি আরো বিশদভাবে বর্ণনা করেছেন।৩১ তিনি হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগায় পারস্পরিক লেনদেনের ক্ষেত্রে ইসলামের উপস্থাপিত বিধানগুলোর পেছনের হিকমতগুলো নিয়ে বিশদভাবে আলোচনা করেছেন।৩২ ভিন্ন একটি প্রসঙ্গে তিনি সদকাহ (দাতব্য), ওয়াসিয়্যাহ (ইচ্ছা) এবং ওয়াকফ (ধর্মীয় দান ও ট্রাস্ট) এর মতো পুণ্য ও কল্যাণের উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত পারস্পরিক লেনদেনের আরো কিছু বিধানের হিকমত ব্যাখ্যা করেছেন।৩৩ তাঁর মতে, ওয়াকফের ধারণা ইসলাম আসার পূর্বে মানুষের কাছে অজানা ছিল। এসকল নতুন সামাজিক প্রতিষ্ঠান হযরত মুহাম্মদ (স.) বিভিন্ন কল্যাণের বিবেচনায় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। ওয়াকফের মাধ্যমে দাতার আয়ের উৎস থেকে অভাবী লোকেরা উপকৃত হয়, তবে মালিকানা ওয়াকফকারীর অধীনেই থাকে।৩৪
পারস্পরিক লেনদেনে স্বচ্ছতা লঙ্ঘনের অভ্যাস
বিবাদ এবং শোষণ দূরীভূত করতে শরীয়ত এমন সব চুক্তিকে নিষিদ্ধ করে যার মাধ্যমে অকল্যাণ সংঘটিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে (ফিকহের পরিভাষায় সাদদুয জারিয়াহ বলা হয়ে থাকে -অনুবাদক)। যেমন অনিশ্চয়তার উপর ভিত্তি করে সম্পাদিত চুক্তি, প্রতারণা, দ্বিমুখী লেনদেন ইত্যাদি। এক্ষেত্রে শাহ ওয়ালীউল্লাহ বিশেষভাবে সুদ, ঘুষ এবং জুয়া চর্চার প্রতি লক্ষ্য রাখেন।৩৫ তিনি বলেন, এই সামান্য বিষয়গুলো বড় বড় বিষয়গুলোকে প্রভাবিত করে। এজন্য শরীয়ত এগুলোর সবগুলোকেই নিষিদ্ধ করে।৩৬ তাঁর মতে, যখন সুদ সমাজে বিস্তার লাভ করে তখন তা সরাসরি কৃষি ও শিল্পের উৎপাদনকে বাঁধাগ্রস্ত করে। অথচ কৃষি ও শিল্প সরাসরি মানব সমাজের জীবনধারণ ও আয়ের উৎস। প্রকৃতপক্ষে সুদ এবং জুয়া উভয়ই মদ্যপানের সমতুল্য, কারণ উভয়ই জীবিকা অর্জনের জন্য আল্লাহ যে নীতি নির্ধারণ করেছেন তার স্পষ্ট লঙ্ঘন।৩৭
রিবা আল-ফাদল এবং রিবা আল-নাসিআহ
শাহ ওয়ালীউল্লাহ ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে যে সুদ(লভ্যাংশ) নেওয়া হয় সেটাকেই প্রকৃত সুদ (আর-রিবা আল-হাকীকী) হিসাবে বিবেচনা করেন।৩৮ তিনি শরীয়তে রিবা আল-ফাদল এবং রিবা আল-নাসিয়াহ হিসাবে আখ্যায়িত পরিমাণ বা সময়ের ক্ষেত্রে বৈষম্যপূর্ণ বিনিময়ের বিষয়টিও উল্লেখ করেন। তিনি এসবকে সুদের উপমা হিসেবে গণ্য করেন।৩৯ সুদের উপর এই ধরনের নিষেধাজ্ঞা রাসূলুল্লাহর রেওয়ায়েত থেকে জানা যায়। রাসূল (স.) বলেছেন সোনার বদলে সোনা, রুপার বদলে রুপা, গমের বদলে গম, যবের বদলে যব, খেজুরের বদলে খেজুর এবং লবণের বদলে লবণ একই পরিমাণে বিনিময় করতে হবে।
শাহ ওয়ালীউল্লাহর মতে, এই ধরনের সুদকে নিষিদ্ধ করার কারণ হলো, বিলাসবহুল জীবনযাপন এবং বস্তুবাদের প্রতি মানুষের অত্যধিক ঝোঁককে সংযত করা।৪০ কারণ সমপরিমাণ পণ্যের সাথে সমপরিমাণ পণ্যের আদান-প্রদান কখনোই মানুষের অত্যধিক সম্পদ লাভের বাসনা মেটায় না; বরং সংযত হতে বাধ্য করে। যদিও এই আলাপ অনেকের কাছে যুতসই নাও ঠেকতে পারে, তবুও ন্যায্যতার মানদন্ডে বিচার করলে নিম্নমানের গমের বিনিময় কেউ-ই ভালো মানের গম দিয়ে করবে না, কিন্তু রিবা আল-ফাদল মূলত এই বৈষম্যই তৈরি করে। তবে এক্ষেত্রে পূর্ববর্তী আলেমগণের মাঝে ইমাম ইবনুল কাইয়ূমের (১৩৫২ খ্রি.) মত অনেক বেশি গ্রহণযোগ্য। তাঁর মতে, রিবা আল-ফাদলকে নিষিদ্ধ করার মূল কারণ হচ্ছে, সুদের অবাধ বিস্তারে সহায়ক ভূমিকা পালনে বাধা দান করা।
হিকমত আত-তাউনিয়্যাহ
আল-ইরতিফাকাতের দ্বিতীয় পর্যায়ের পঞ্চম হিকমতটি অর্থনীতির ক্ষেত্রে আর্থ-সামাজিক সহযোগিতার সাথে সম্পর্কিত। শাহ ওয়ালীউল্লাহ এ পর্যায়ে বলেন, “আর্থ-সামাজিক সহযোগিতা প্রয়োজন সমাজের নিজের প্রয়োজনেই। কেননা সমাজের কিছু মানুষ বুদ্ধিমান আবার কিছু মানুষ হয় নির্বোধ, কিছু পুঁজিপতি তো আবার কিছু লোক একেবারে হতঃদরিদ্র কিন্তু কঠোর পরিশ্রমে সক্ষম। কিছু মানুষ ছোটখাটো কাজ করতে অপছন্দ করে আবার কিছু মানুষ স্বাচ্ছন্দেই তা করে যায়। এখান থেকে সহজেই উপলব্ধি করা যায় যে মানুষের জাগতিক জীবন খুব কঠিন হয়ে উঠতো, যদি তারা একে অপরকে সহযোগিতা না করতো। মুজারাহ (শস্য বিনিময়)কে যদি উদাহরণ হিসেবে ধরি তাহলে দেখা যায়, একজন ব্যক্তির জমি আছে কিন্তু বীজ নেই, চাষ দেওয়ার জন্য বলদ নেই ফলে সেই ব্যক্তির পক্ষে কখনোই ফসল ফলানো সম্ভব নয়। অথবা আমরা যদি মুদারাবাহর থেকে উদাহরণ দেই যেমন একজন ব্যক্তির পুঁজি আছে কিন্তু সে ব্যবসা করার মতো পরিস্থিাতিতে নেই, কিন্তু অন্য আরেকজনের ব্যবসা করার মতো সক্ষমতা আছে কিন্তু পুঁজি নেই। এখানে প্রয়োজন উভয়ের পারস্পরিক সহযোগিতা”।৪১
শাহ ওয়ালীউল্লাহ তাঁর হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহতে এরকম বিভিন্ন প্রকারের সম্পর্ক উল্লেখ করেছেন। যা মূলত ফিকহের গ্রন্থগুলোয় বিশদভাবে ঠাঁই পেয়েছে। তিনি বলেন, এসব লেনদেনের পন্থা নবী করিম (স.) এর পূর্বেও প্রচলিত ছিল। এগুলো রাসূল (স.)-এর বিশেষ কোনো কারণবশত নিষেধ ছাড়া সবক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।৪২
আল-ইরতিফাকাতের তৃতীয় পর্যায়
দ্বিতীয় পর্যায়ের ইরতিফাকাত পূর্ণতা পেলে মানব সমাজ নগর রাষ্ট্রে পরিণত হয়। শাহ ওয়ালীউল্লাহ খুব জোর দিয়েই বলেন নগর মানে বড় বড় বাজার, উঁচু উঁচু দালান আর প্রাচীর না। বরং শহর হচ্ছে বিভিন্ন শ্রেণির মানুষের মধ্যকার আন্তঃসম্পর্ক, যেখানে সম্পর্কের ভিত্তি হচ্ছে পারস্পরিক শ্রদ্ধা, সহযোগিতা ও নানা ধরনের লেনদেন।৪৩ মানুষের মধ্যকার এই আন্তঃসম্পর্ক রক্ষা এবং অর্থনীতিকে বিভিন্ন দুষ্ট চক্র থেকে হেফাজত রাখার প্রয়োজনীয়তা সমাজকে আল-ইরতিফাকাতের তৃতীয় পর্যায়ে নিয়ে আসে। শাহ ওয়ালীউল্লাহর মতে, নগর হচ্ছে একটা একক বা বলা যায় একটি শরীরের মতো এবং একটি শরীরের মতো এরও আভ্যন্তরীণ ও বহির্গত অনেক রোগ হতে পারে। এজন্য প্রত্যেকটি শহরের একজন দক্ষ চিকিৎসকের খুব বেশি প্রয়োজন। শহরের ইমাম বা নেতৃত্ব এই পর্যায়ে নগর চিকিৎসকের প্রতিনিধিত্ব করেন।৪৪ ইমাম বা নেতৃত্ব এমন একটি প্রতিষ্ঠান যার মাধ্যমে শহরের অখ-তা, স্বার্থ এবং স্বাধীনতা বজায় থাকে।৪৫ আল-ইরতিফাকাতের তৃতীয় পর্যায়ে নিম্নলিখিত পাঁচটি প্রতিষ্ঠান খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কেননা এর মাধ্যমে নগর-রাষ্ট্রের অগ্রগতি অব্যাহত থাকে এবং দুর্নীতি, অপব্যবহার, বিশৃঙ্খলা ও ক্ষয়-ক্ষতির মতো অসুখগুলোর যথাযথ প্রতিরোধ ও প্রতিকার করা যায়।
১. বিচার বিভাগ : কৃপণতা, হিংসা এবং অন্যের অধিকার হরণ যখন সামাজিক জীবনে প্রবেশ করে, তখন একটি নগর-রাষ্ট্রের মানুষের মধ্যে বিবাদ ও মতানৈক্য তৈরি হতে বাধ্য। তাই একটি স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান থাকতে হবে যার কাছে বিরোধের ন্যায়সঙ্গত নিষ্পত্তির জন্য আসতে পারে।
২. নির্বাহী বিভাগ : যখন বিকৃত স্বভাব ও ক্ষতিকর কর্মকা- মানুষের মাঝে প্রাধান্য পায় এবং মানুষ সেই অনুযায়ী কাজ করে, তখন নগর-রাষ্ট্র অপরাধপ্রবণ ও বিশৃঙ্খল হয়ে পড়ে। তাই এই ধরনের ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধমূলক ও শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য একটি শক্তিশালী সংস্থা থাকা উচিত।
৩. আল-জিহাদ বা পুলিশ ও সামরিক বাহিনী : দুর্নীতিগ্রস্ত প্রকৃতির লোকেরা প্রায়শই হত্যা, ডাকাতি বা বিদ্রোহের মতো হিংসাত্মক কার্যকলাপে লিপ্ত হয় এবং ইচ্ছাকৃতভাবে একটি শহরের শান্তি ও শৃঙ্খলা নষ্ট করার চেষ্টা করে। এই ধরনের সহিংস পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করতে এবং তাদের সৃষ্ট দুর্ভোগ থেকে নগর-রাষ্ট্রকে রক্ষা করার জন্য, সাহসী যোদ্ধাদের সমন্বয়ে গঠিত একটি প্রতিরক্ষা বাহিনী অপরিহার্য।
৪. আত-তাওয়াল্লি ওয়াল-নাকাবা বা কল্যাণ ও জনসাধারণের উপকারে কাজ : শহরে নানা ধরনের প্রতিষ্ঠান ও কর্পোরেট সংস্থা থাকে যা একটি শহরকে নিখুঁত নগর-রাষ্ট্রে পরিণত করে। তবে এখানে যদি জনসাধারণের উপকারে কাজ করবে এমন প্রতিষ্ঠানের অভাব থাকে তাহলে এই নগরকে রক্ষা করা কঠিন। একটি নগর-রাষ্ট্রকে স্থায়িত্ব দিতে হলে জনসাধারণ সম্পর্কিত বিষয়গুলো খেয়াল রাখতে হবে, যেমন সীমান্ত রক্ষা, সুপেয় পানির ব্যবস্থা করা, বাজার নির্মাণ করা, সেতু-খাল নির্মাণ, এতিমদের বিয়ে দেওয়া এবং তাদের সম্পত্তি রক্ষা, অভাবগ্রস্তদের মধ্যে রাষ্ট্রীয় সাহায্য বণ্টন, উত্তরাধিকারীদের মধ্যে উত্তরাধিকার বণ্টন। রাষ্ট্রের নানা বিষয়ের হাল-হাকীকত সম্পর্কে অবগত করা ও বিভিন্ন বিষয়ে সচেতনতা তৈরি এবং আয় ও ব্যয়ের হিসাব রাখা।
৫. আল-মাওইজাহ ওয়াল-তাজকিয়াহ বা ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষা : যেহেতু সত্য ধর্ম কখনোই মানুষকে নৈতিক জ্ঞান প্রদান থেকে বিতাড়িত করে না যদিও বিচক্ষণ মানুষ তার বিচক্ষণতা দিয়েই ধর্মের এসব জ্ঞানকে উপলব্ধিতে নিয়ে আসে কিন্তু সমাজে এমনও অসংখ্য মানুষ রয়েছে যা সত্যকে প্রত্যাখ্যান করেছে এবং নিজের নফসের প্ররোচনায় পরিচালিত হচ্ছে। এ ধরনের মানুষের একজন মহৎ ব্যক্তির সাহচর্য প্রয়োজন হয়। এক্ষেত্রে ধর্মীয় শিক্ষা ও ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব এসব মানুষকে সঠিকভাবে জীবন পরিচালনায় শিক্ষা প্রদান করতে পারেন।৪৬
শাহ ওয়ালীউল্লাহ ইমামদেরকে জনগণ এবং সেনাবাহিনীর সাথে ন্যায়পরায়ণ আচরণ করার এবং সেনাবাহিনী ও সরকারী কর্মকর্তাদের প্রতি যথাযথ মনোযোগ দেওয়ার পরামর্শ দেন।৪৭ এই পর্যায়ে সরকারের দায়িত্ব হবে বিভিন্ন শিল্প ও সেবায় কর্মসংস্থানের যথাযথ ব্যবস্থা করা। ব্যবসায়ী ও কৃষকদের তাদের স্ব স্ব পেশায় উৎসাহিত করা এবং তাদের যথাযথ শিক্ষার ব্যবস্থাও করা। এক্ষেত্রে শাহ ওয়ালীউল্লাহ তাঁর সময়ের খারাপ অবস্থার দিকে ইঙ্গিত করেছেন যেখানে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের তৃতীয় পর্যায়ের প্রয়োজনীয়তা যথাযথভাবে পূরণ হয়নি। শাহ ওয়ালীউল্লাহ বলেন, “আমাদের সময়ে শহরগুলোর পতনের দুটি প্রধান কারণ রয়েছে।
এক. লোকেরা বাইতুল-মালের (রাষ্ট্রীয় কোষাগার) উপর বোঝা চাপিয়ে দেয়। তারা যোদ্ধা, শিক্ষাবিদ, ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব, কবি হওয়ার অজুহাতে এখান থেকে তাদের জীবিকা অর্জনে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে।
দুই. কৃষক, ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিদের উপর ভারী কর আরোপ এবং তাদের প্রতি কঠোরতা, যা অনুগত কর্মকর্তাদের মধ্যেও হতাশা সৃষ্টি করে এবং একইসাথে ভিনদেশীদের কর ফাঁকি ও বিদ্রোহ আমাদের পতনকে ত্বরান্বিত করে।”
শাহ ওয়ালীউল্লাহ আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের তৃতীয় পর্যায়ে পাঁচটি প্রতিষ্ঠানকে কীভাবে পরিচালনা করতে হবে তার উপর বিশদ নীতি প্রণয়ন করেছেন। তিনি একজন সফল নেতার গুণাবলিও বর্ণনা করেছেন।৪৯
রাষ্ট্রীয় অর্থনীতি
আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের চতুর্থ ও শেষ পর্যায় নিয়ে আলোচনা করার আগে, এখানে জাতীয় অর্থনীতি, কর আদায়ে পালনীয় নিয়মাবলি এবং রাজস্ব ব্যয় সম্পর্কে শাহ ওয়ালীউল্লাহর ধারণার সাথে পরিচিত হওয়া দরকার। তাঁর মতে, আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের তৃতীয় ও চতুর্থ পর্যায়ে সফল হতে হলে জাতীয় অর্থনীতির শক্তিশালী অবস্থা আবশ্যক। ভারতে মুঘল শাসনের দুর্বলতা ও পতনের প্রধান কারণ হিসেবে বাইতুল-মালের অস্বচ্ছলতা এবং জনগণের উপর অতি নির্ভরশীলতা কীভাবে চিত্রায়িত করেছেন তা আমরা ইতোমধ্যেই দেখেছি। একই কথা পারস্য এবং বাইজেন্টাইন সাম্রারাজ্যের ক্ষেত্রেও সত্য।৫০
করের নিয়ম সম্পর্কে শাহ ওয়ালীউল্লাহ পরামর্শ দেন যে, কর ধার্য ও আদায়ের একটি ন্যায়সঙ্গত ব্যবস্থা থাকা আবশ্যক যাতে জনগণ ক্ষতিগ্রস্ত না হয় এবং কর থেকে প্রাপ্ত আয় রাষ্ট্রের চাহিদা পূরণের জন্য পর্যাপ্ত হয়।৫১ প্রত্যেক ব্যক্তি এবং প্রতিটি পণ্যের উপর কর আরোপ করা উচিত নয়। এটি এমন লোকদের উপর হওয়া উচিত যাদের ক্রমবর্ধমান সম্পত্তি যেমন গবাদি পশুর প্রজনন, কৃষি খামার, গচ্ছিত সম্পদ এবং ব্যবসা রয়েছে। যদি আরো অর্থের প্রয়োজন হয় তবে শারীরিক শ্রমে উপার্জনকারী জনসংখ্যাকেও অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে।৫২ তবে তাঁর প্রস্তাবনা হচ্ছে, যে রাষ্ট্রের অর্থ আয়ের নিজস্ব কিছু উপায় থাকা উচিত যেমন অনাবাদি জমি লিজ দেওয়া, গবাদি পশুর পালন ইত্যাদি উৎপাদনশীল কর্মকান্ড। এটি রাষ্ট্রকে জনগণের আয় থেকে কর্তন করার নির্ভরশীলতা থেকে স্বাধীন করবে এবং সামগ্রিকভাবে মানুষের জন্য স্বস্তিদায়ক করে তুলবে।৫৩ তবে এখানে লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে, তিনি শরীয়ত নির্ধারিত উৎসগুলো থেকে প্রাপ্ত সম্পদ যেমন গনীমত, ফাই, উশর, খারাজের উপর কর কোন হারে আদায় হবে এ সংক্রান্ত কোনো আলোচনা করেননি। শাহ ওয়ালীউল্লাহ রাষ্ট্রীয় আয়ের উৎসের বর্ণনায় যাকাতকেও উল্লখ করেননি। উল্লেখ না করার কারণ, এসকল বিষয়ে শরীয়তের মানদন্ড পূর্বে নির্ধারিত হয়ে গেছে। তবে এই আলোচনা তাঁর গ্রন্থে ইসলামের অন্যান্য বিষয়ের সাথে এসেছে। আরেকটি কারণ হতে পারে যে, মুঘল আমলে সুদীর্ঘকাল থেকে সরকার কর্তৃক যাকাত আদায় ও বণ্টন বিদ্যমান ছিল। কিন্তু বর্তমানে যাকাতের অর্থ সংগ্রহ এবং বিতরণ শুধুমাত্র একটি ব্যক্তিগত কার্যকলাপে পরিণত হয়েছে। তবে ব্যয়ের বিষয়ে যতদূর আলোচনা হয়েছে তাতে এটি স্পষ্ট যে, আল-ইরতিফাকাতের তৃতীয় পর্যায়ের অধীনে উল্লিখিত সমস্ত প্রয়োজনীয় প্রতিষ্ঠান যথাযথ অংশ পাবে। তহবিল বরাদ্দের ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ খাত, তারপরের গুরুত্বপূর্ণ (আলহাম ফাল-আহাম্ম) এভাবে গুরুত্বের উপর ভিত্তি করে খাত নির্ধারণের নীতিতে বিবেচনা করা হবে।৫৪
যুদ্ধের পর কাফেরদের কাছ থেকে দখলকৃত জমি সম্পর্কে তার অভিমত হলো, হয় এর বণ্টন করে দিতে হবে অথবা বিদ্যমান শাসক পরিস্থিতি অনুযায়ী সিদ্ধান্ত দিবেন।৫৫ তাঁর ইজালাতুল-খাফা গ্রন্থে তিনি দ্বিতীয় খলীফা ওমর (রা.)-এর জমির মালিকানা পূর্ববর্তীদের হাতে সোপর্দ করার অনন্য ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তিনি বলেন, পারস্যের লোকেরা যারা মুসলিম সৈন্যদের সাথে যুদ্ধ করেছিল তারা বিজিত জমির মালিক ছিল না; প্রকৃতপক্ষে মালিক হচ্ছে ঐসকল কৃষক যারা প্রকৃত যুদ্ধ ছাড়াই আত্মসমর্পণ করেছিলেন। শাহ ওয়ালীউল্লাহ এমন কোনো ব্যক্তিকে জমি দেওয়ার বিরোধিতা করেন যাকে ব্যবসা কিংবা কৃষিতে নয় বরং সমাজের এর চেয়েও অধিক গুরুত্বপূর্ণ খাতে প্রয়োজন।৫৭ যাকাত এবং এর বণ্টন সম্পর্কে শাহ ওয়ালীউল্লাহ আলাদাভাবে আলোচনা করেছেন। তার মতে, যাকাত প্রদান শুধুমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য। এটি প্রধানত মূল্যবান ধাতব সম্পদ, পশুসম্পদ, বাণিজ্যিক পণ্য এবং কৃষি পণ্যের উপর ধার্য করা হয়। যাকাত প্রদানকে সহজ করার জন্য একটি উপযুক্ত সময়কাল এবং একটি অব্যহতির সীমা নির্ধারণ করা হয়েছে।৫৮ তিনি যাকাত প্রদানের মাধ্যমে সৃষ্ট আধ্যাত্মিক কল্যাণের কথা উল্লেখ করেছেন এবং যাকাতকে ভিত্তি হিসেবে ধরে বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক কারণ ব্যাখ্যা করেছেন।৫৯ সমুদ্র বা পাহাড়ি দ্রব্য এবং শুকনো ফল যাকাতের অন্তর্ভুক্ত করা যাবে কিনা তা নিয়ে মতপার্থক্য রয়েছে। এ ব্যপারে শাহ ওয়ালীউল্লাহর অভিমত হচ্ছে, শাসক যদি প্রয়োজন মনে করেন, তাহলে তিনি তা করতে পারেন।৬০ তবে ঐতিহাসিক প্রমাণ থেকে দেখা যায় যে, শাহ ওয়ালীউল্লাহর সময়ে যাকাত সরকার কর্তৃক পরিচালিত হতো না, তাই এটিকে শাহ ওয়ালীউল্লাহর কেবলমাত্র একটি একাডেমিক মতামত বা একটি পরামর্শ হিসেবেও নেওয়া যেতে পারে। তবে এর মাধ্যমে একটি বিষয় স্পষ্ট হয় যে, তিনিও মনে করেন যাকাতের ব্যবস্থাপনা রাষ্ট্রীয় দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত।
আল-ইরতিফাকাতের চতুর্থ পর্যায়
এই পর্যায়ে এসে মানব সমাজ ও সরকার আন্তর্জাতিক রূপ লাভ করে এবং ছোট ছোট শাসনের উপর কেন্দ্রীয় শাসনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। যখন ইরতিফাকাতের তৃতীয় পর্যায় সম্পাদিত হয়ে যায় তখন বিভিন্ন স্থানের শাসকদের নিজস্ব আয়ের উৎস সৃষ্টি হয়, তারা সাহসী যোদ্ধাদের সমর্থন লাভ করে কিন্তু তাদের পারস্পরিক সুরক্ষা বিধান ও লোভ তাদের মধ্যে শত্রুতার জন্ম দেয় ফলে এসকল শাসকেরা পরস্পর রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে। এতে জীবন ও জীবিকার ব্যপক প্রাণহানী ঘটে এবং পূর্বের সকল ইরতিফাকাত ধুলোয় মিশে যায়। এসকল সমস্যা একটি কেন্দ্রীয় শাসন বা খিলাফত আল খুলাফাকে প্রতিষ্ঠা করতে বাধ্য করে।৬১ এক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় শাসককে সামরিক এবং বস্তুগত দিক থেকে অন্তত এতটুকু শক্তিশালী হতে হবে যেন অন্য কোনো শক্তি তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে জয়ী হওয়ার দুঃস্বপ্ন না দেখে।৬২ জনসাধারণের জীবনের নিরাপত্তায় প্রয়োজনে খলিফা দুস্কৃতিকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধও করবেন।৬৩
শাহ ওয়ালীউল্লাহ আন্তর্জাতিক চরিত্রের এই কেন্দ্রীয় সরকারকে কোনো অর্থনৈতিক দায়িত্ব অর্পণ করেননি, তবে শান্তিরক্ষা, ন্যায়বিচার প্রদান এবং শোষণ রোধ করার দায়িত্ব পালনের জন্য এই কেন্দ্রীয় শাসকের প্রচুর লোক এবং উপাদানের প্রয়োজন হবে। এসকল খরচ মেটাতে বিভিন্ন কর ধার্য করা এবং এসকল বিষয় পরিচালনা করার অর্থ প্রয়োজন পড়বে। এক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকার বিদ্রোহী ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারীদের আর্থিক শাস্তি দিতে পারেন। কিন্তু এই ধরনের শাস্তির উদ্দেশ্য হওয়া উচিত সংস্কার করা এবং সেগুলোকে শৃঙ্খলায় আনা, তহবিল সংগ্রহ নয়।৬৪ শাহ ওয়ালীউল্লাহ একজন যোগ্য ও সফল খলিফার গুণাবলি বর্ণনা করেছেন এবং দায়িত্ব পালনে তাঁর ভূমিকাকে দৃঢ় ও কার্যকর করার জন্য বিভিন্ন ধরনের পরামর্শ দিয়েছেন।৬৫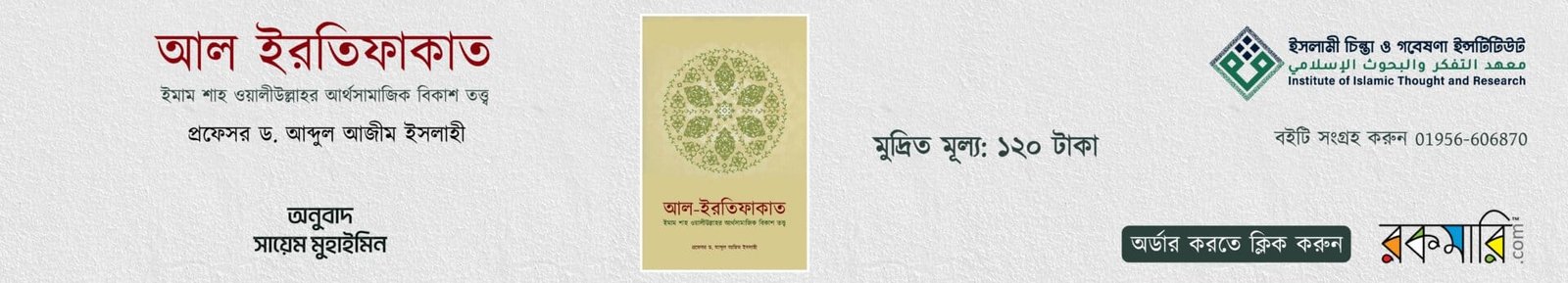
ইরতিফাকাত; একটি স্বাভাবিক বিকাশ পদ্ধতি
শাহ ওয়ালীউল্লাহর মতে, ইরতিফাকাত হচ্ছে একটি স্বাভাবিক বিকাশ পদ্ধতি।৬৬ তবে এক্ষেত্রে কোনো ব্যত্যয় পরিলক্ষিত হলে সেটা মূলত মানুষের খারাপ অভ্যাস ও অসৎ প্রকৃতির কারণে সৃষ্টি হয়। প্রতিষ্ঠান হিসেবে নবুওয়তের উদ্দেশ্যও ছিল মানুষকে ইরতিফাকাতের মাধ্যমে বিকশিত করা এবং এই পথে বিঘ্ন সৃষ্টিকারী সকল বাধাকে দূরীভূত করা। শাহ ওয়ালীউল্লাহর মতে, গার্হস্থ্য ও ব্যবস্থাপনা কোরআনী শরীয়তের দুটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তাঁর মতে, রাসূল (স.)-এর দায়িত্ব ছিল ইরতিফাকাতের দ্বিতীয় পর্যায়কে পরিশুদ্ধ করা এবং তৃতীয় পর্যায়ের ইরতিফাকাত প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে আল্লাহর দ্বীনকে সমগ্র বিশ্বে ছড়িয়ে দেওয়া এবং এই দ্বীনকে চতুর্থ পর্যায়ের ইরতিফাকাতের মাধ্যমে দুনিয়ার কেন্দ্রে প্রতিষ্ঠার পথকে সুগম করা।৬৮ এভাবে তিনি আর্থ-সামাজিক বিকাশ এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনকে একত্রিত করে ‘ইকতিরাবাত’ নামে নতুন একটি পরিভাষার জন্ম দেন। ইকতিরাবাতের মাধ্যমে একজন মানুষ তার আত্মপরিশুদ্ধিকে আরো বিকশিত করে।৬৯ যাহোক এখন আমরা আবার আমাদের পূর্বের আলোচনায় ফিরে আসি।
এখানে একটি বিষয় লক্ষ্য রাখা দরকার, তা হচ্ছে অর্থনীতির ক্ষেত্রে শাহ ওয়ালীউল্লাহর উল্লিখিত শ্রম বিভাজন, মুদ্রার বিনিময়, বাজার, সুদের বিকাশ রোধ, যাকাত, জাতীয় অর্থনীতি ইত্যাদি সম্পর্কে শাহ ওয়ালীউল্লাহর পূর্ববর্তী আলেমগণ যেমন ইমাম আবু ইউসুফ (মৃত্যু : ৭৯৮ খ্রি.), ইমাম গাজ্জালী (মৃত্যু : ১১১১), ইমাম ইবনে তাইমিয়াহ (মৃত্যু : ১৩২৮), ইমাম ইবনুল কাইয়্যুম (মৃত্যু : ১৩৫২), ইবনে খালদুন (মৃত্যু : ১৪০৬) সহ আরো অনেকে আলোচনা করেছেন। কিন্তু শাহ ওয়ালীউল্লাহ কৃতিত্ব হচ্ছে তিনি অর্থনৈতিক কার্যক্রমকে বিভিন্ন পর্যায়ে বিভিক্ত করে ইরতিফাকাতের মূলনীতির মাধ্যমে ব্যাখ্যা করেছেন।
প্রথম পর্যায় একেবারেই নিখাদ ঐতিহ্যবাহী আলোচনা যেখানে মানুষ কেবল খাবার এবং মৌলিক প্রয়োজন পূরণে ব্যস্ত। কিন্তু আস্তে আস্তে শ্রমের বিভাজন, দক্ষতা ভিত্তিক শ্রেণির বিকাশ মুদ্রার বিনিময় ঘটাতে বাধ্য করে এবং নতুন নতুন প্রযুক্তির বিকাশ সাধন ও মানুষের মধ্যকার আন্তঃসম্পর্ককে কিছু মৌলিক চুক্তির উপর নিয়ে আসে। এটা আর্থ-সামাজিক বিকাশের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্তর। এই স্তর থেকেই মৌলিক অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলো বিকশিত হতে শুরু করে এবং ব্যক্তিকে অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল সদস্য হিসেবে পরিণত হওয়া থেকে রক্ষা করে। এই স্তরেই আর্থ-সামাজিক বিকাশের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ানো আর্থ-সামাজিক দুষ্টচক্রের প্রতিকার সাধন করে সমাজের জন্য একটি সুস্থ-স্বাভাবিক পরিবেশ ও অবকাঠামোর সৃষ্টি হয়। অর্থনীতি যখনই দ্বিতীয় স্তর অতিক্রম করে ফেলে তখন রাষ্ট্রের তথা শাসকের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়।
এভাবে মানব সমাজ ইরতিফাকাতের তৃতীয় পর্যায়ে প্রবেশ করে এবং নগর-রাষ্ট্র জাতিরাষ্ট্রে রূপলাভ করে। এই পর্যায়ে ভারসাম্যপূর্ণ অর্থনীতি বজায় রাখার দায়িত্ব রাষ্ট্রের উপর অর্পিত হয়। জাতিরাষ্ট্রের মাঝে দ্বন্দ্ব-সংঘাতের প্রতিকারে জাতিরাষ্ট্রের চেয়েও শক্তিশালী কর্তৃত্বের প্রয়োজনীয়তা আন্তর্জাতিক নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের জন্ম দেয়। আর এভাবে মানব সমাজ ইরতিফাকাতের চতুর্থ পর্যায়ে প্রবেশ করে।
তবে শাহ ওয়ালীউল্লাহ এই কেন্দ্রীয় প্রশাসনকে অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে জড়িয়ে পরেননি। কেন জড়িয়ে পরেননি এর উত্তরে বলা যায়, হয়ত শাহ ওয়ালীউল্লাহর সময়ে তিনি তেমনটা প্রয়োজনবোধ করেননি। তবে বর্তমানে প্রতিষ্ঠিত আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহ দূর্বল রাষ্ট্রগুলোকে সাহায্য করে থাকে যা শাহ ওয়ালীউল্লাহ ছোট ছোট রাষ্ট্রগুলোকে পারস্পরিক বিরোধ থেকে বাঁচানো এবং অর্থনৈতিক ও সামাজিকভাবে দুর্বল রাষ্ট্রগুলোকে সাহায্য করার নীতিরই বাস্তবায়ন।
শাহ ওয়ালীউল্লাহ এমন এক সময়ে আর্থ-সামাজিক বিকাশের এই সিস্টেমটি দুনিয়ার সামনে তুলে ধরেন যখন দুনিয়ায় এই বিষয়টি তখনো একটি সাবজেক্ট হিসেবেই প্রতিষ্ঠিত হয়নি। তাঁর এমন কৃতিত্ব তাঁকে জ্ঞানের এই ক্ষেত্রে প্রধান গোড়াপত্তনকারীদের একজন হিসেবে বিবেচনা করতে বাধ্য করে। তাঁর ইরতিফাকাতের তত্ত্ব এতবেশি সামগ্রিক যে বিংশ শতাব্দীর অসংখ্য মডেল এই তত্ত্বে অনায়াসেই ঠাঁই পেতে পারে।
তথ্যসূত্র :
- 1. Schumpeter, J. A., History of Economic Analysis: London, George Allen and Unwin, 1972, p.73; Mazer, A J., “Economic Thought and Its Application and Methodologz in the Middle East” Middle East Economic Papers, Beirut, vol. 56, pp. 66-74.
- 2. Here are a few of them: Siddiqi, M.N., Recent Works on History of Economic Thought in Islam – A Survey, Jeddah, ICRIE, 1982; Islahi, Abdul Azim, Economic Thought of Ibn al-Qazzim, Jeddah, ICRIE, 1984; Islahi, Abdul Azim, Economic Concepts of Ibn Taimizah, Leicester, The Islamic Foundation, 1988.
- 3. For example, Ahmad, B., Imam Wali-Allah Dehlawi awr unka Falsafah-e- Umraniyat wa Ma`ashizat (Shah Wali-Allah Dehlawi and his Philosophy of Sociology and Economics), Lahore, Bait al-Hikmat, 1945.
- 4. Tadhkirah Adil Khan (Manuscript), p. 34, Quoted by Nizami, K. A., in his edited work: Shah Wali-Allah Ke Siyasi Maktubat (Political Letters of Shah Wali-Allah), Aligarh, 1950, p. 162.
- 5. Dehlawi, Shah Wali-Allah, Shah Wali-Allah Ke Siyasi Maktubat (Political Letters of Shah Wali-Allah), Nizami, K. A. (ed.), op. cit., p. 53.
- Ibid. p. 52.
- Ibid. p. 42.
- Ibid.
- Dehlawi, Shah Wali-Allah, Hujjat-Allah al-Balighah (Henceforth Hujjat), Beirut, Dar
al-Fikr, n.d. vol. 1, p. 45.
- Ibid. p.l06, Siyasi Maktubat, op. cit., pp. 43, 52, 83, 84. Shah Wali-Allah addresses different sections of the society and warns them of bad consequences of their sinful behaviour, cf. Dehlawi, Shah Wali-Allah, al-Tafhimat al-Ilahiyah, Dabhel, al-Majlis al-`Ilmi, n.d.
- Dehlawi, Shah Wali-Allah, al-Budur al-Bazighah (henceforth al-Budur), Dabhel, al-Majlis al-`Ilmi, p. 51.
- Ibid. pp. 53-54, Hujjat, op. cit., vol. 2, pp. 39-40
- Hujjat, op. cit., p. 40.
- al-Budur, p. 50.
- Ibid. p. 52.
- Ibid. p. 50.
- Ibid. p. 51.
- Ibid. p. 55.
- Ibid. pp. 55-60.
- Ibid. p. 60.
- Ibid. pp. 66-67.
- Ibid. p. 67; Hujjat, vol. 1, p. 43.
- Ibid.
- Hujjat, vol. 1, p. 97
- al-Budur, op. cit., p. 68.
- Hujjat, vol. 2, p. 105.
- Ibid. p. 106.
- Ibid. vol. 1, p. 43.
- al-Budur, p. 67.
- Hujjat, vol. 2, p. 43
- al-Budur, pp. 68-69.
- Hujjat, vol. 2, pp. 112-113.
- Ibid. pp. 114-116.
- Ibid. p. 1l6. This view is held by him although some others do not agree that the donor’s right of ownership rests with him.
- al-Budur, 69, 78; Hujjat, vol. 2, p. 106.
- Hujjat, vol. 2, p. 106.
- Hujjat, vol. 2. p. 106.
- Ibid. p. 107.
- Ibid.
- al-Budur, p. 70.
- Hujjat, vol. 2 p. 1l7.
- al-Budur, pp. 50-51.
- Ibid. p. 51.
- Ibid. p. 71.
- Ibid. pp. 71-72.
- Ibid. p. 73.
- Hujjat, vol. 1, pp. 44-45.
- Ibid. pp. 45-47; al-Budur, pp. 73-85.
- Hujjat, vol. 1, p. 105.
- Ibid. p. 46; al-Budur, p. 85.
- Hujjat, vol. 1, p. 46.
- al-Budur, p. 85.
- Hujjat, vol. 2, p. 174.
- Ibid. p. l71.
- Dehlawi, Shah Wali-Allah, Izalat al-Khafa, Bareilz (India), 1286 H., vol. 2, p. 264.
- Hujjat, vol. 2, p. 104.
- al-Budur, pp. 120, 214.
- Ibid. pp. 214-215.
- Izalat al-Khafa, vol. 2, p. ll7.
- al-Budur, p. 51; Hujjat, vol. I, p. 47.
- al-Budur, p. 85.
- Hujjat,vol. 1, p. 47.
- Ibid. p. 48
- Ibid.
- al-Budur, p. 94; Hujjat, vol 2, p. 48.
- Deh1awi, Shah Wali-Allah, al-Khair al-Kathir, Dabhel, al-Majlis al-`Ilmi, 1352 H.,
- 83.
- al-Budur, p. 199; al-Tafhimat al-Ilahizah, op. cit., vol. 1, p. 60.
- al-Budur, p. 266.
- Ibid. pp. 241-42.
অনুবাদঃ সায়েম মুহাইমিন