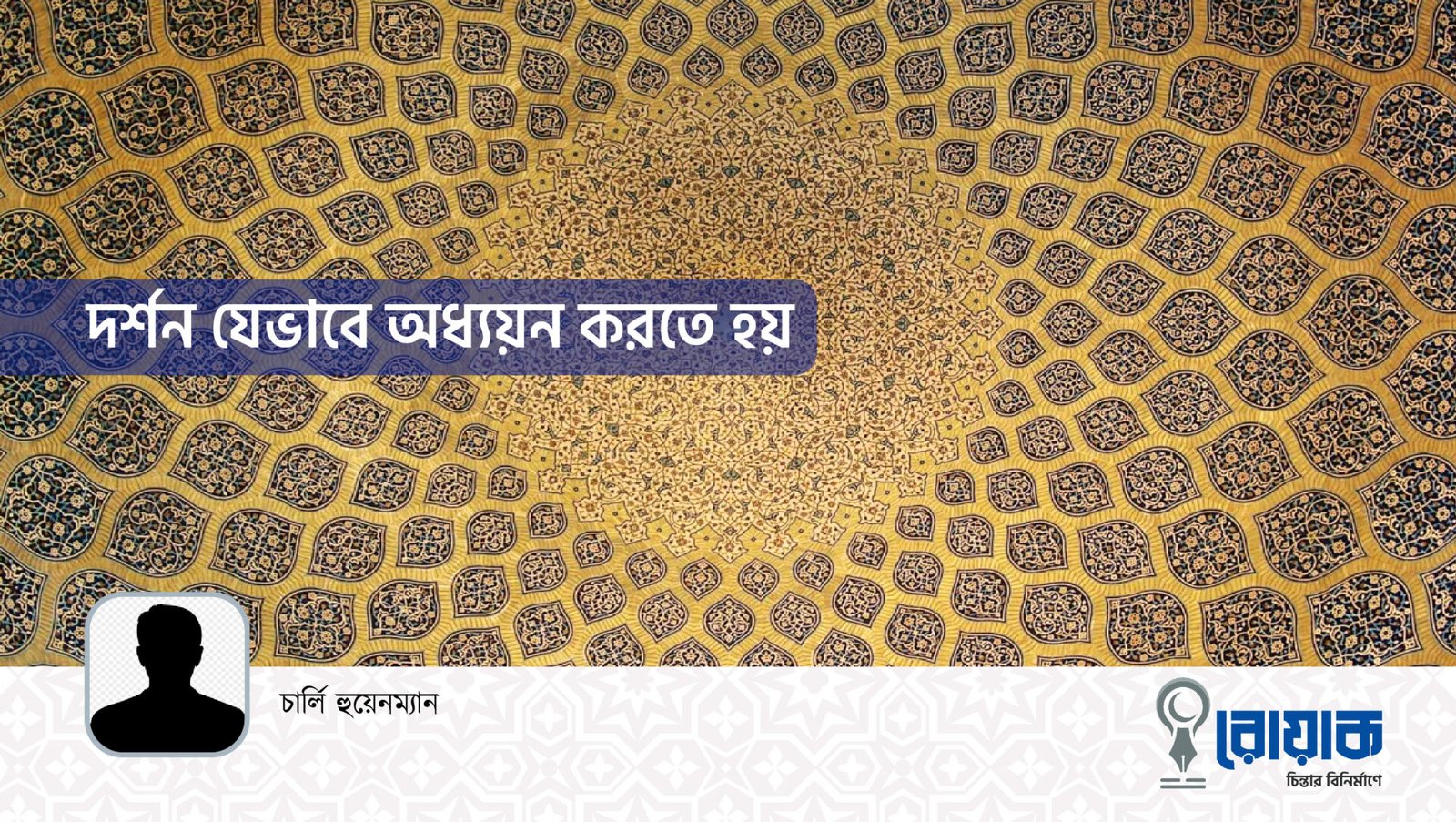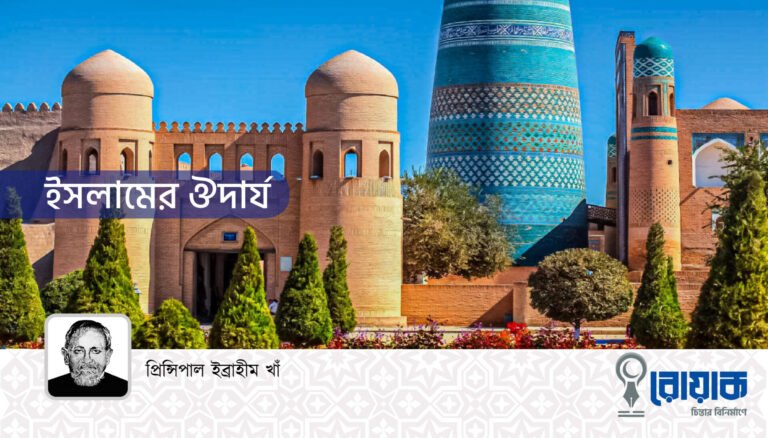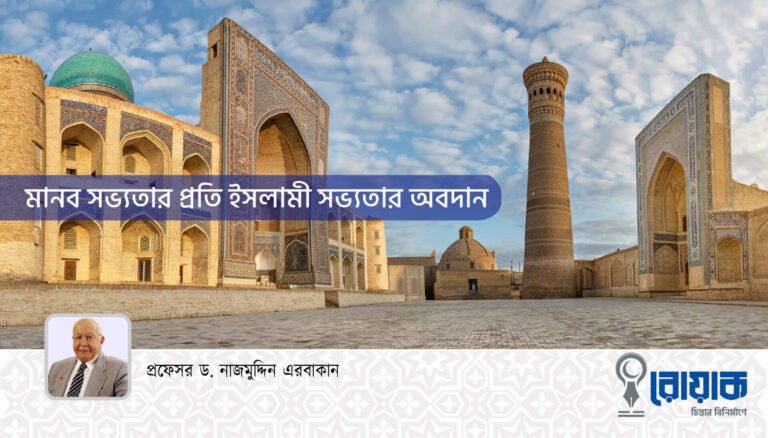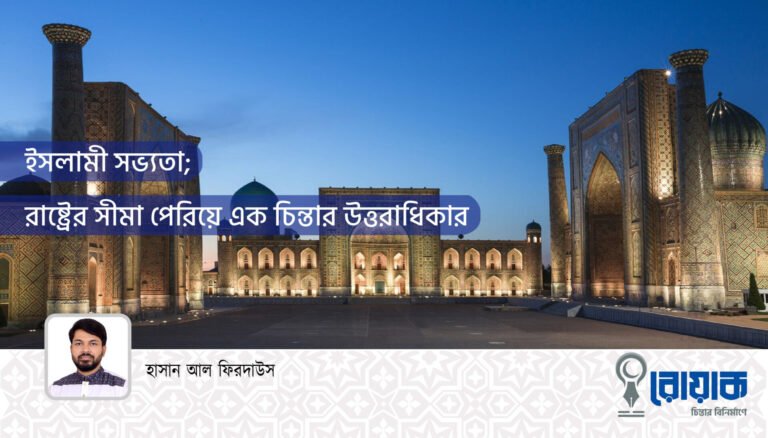প্রথমেই যে জিনিসটা মাথায় আনতে হবে, তা হচ্ছে বিখ্যাত দার্শনিকগণ সবাই কেবলই মানুষ ছিলেন। সুতরাং আপনিও তাদের সাথে দ্বিমত করে শুরুটা করতে পারেন।
যা জানা প্রয়োজন
দর্শনের বিষয়টাকে কঠিন মনে হতে পারে। চিন্তাদানব খ্যাত হেগেল, প্লেটো, মার্ক্স, নীটশে, কিয়ার্কেগার্ড এরা আমাদের উপর কর্তৃত্বমূলক দৃষ্টি দিয়েছেন এই প্রশ্ন করে যে, আমরা যে মূল্যবান, এ ব্যাপারে আমরা নিজেরা নিশ্চিত কিনা। আমরা হয়তো এ ব্যাপারে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠতে পারি যে, তারা যা বলছে তার সবকিছু আমরা বুঝতে পারছি কিনা; এমনকি যদি মনে করি বুঝতেছি, তবুও এই চিন্তাটি ঘুরেফিরে আসবে যে, হয়তো কোনোভাবে আমরা এ ব্যাপারে ভুল বুঝছি এবং বুঝবো।
সুতরাং আমরা যদি দর্শন পড়া শুরু করি, তাহলে এই দানবদেরকে হজম করেই শুরুটা করতে হবে। এই যাত্রায় তাদের প্রত্যেকেই দৌড়িয়েছেন, ঢেকুর তুলেছেন, হাবিজাবি কাজ করেছেন। তাদের কয়েকজন সত্যিকার অর্থেই কাপানো ব্যক্তি ছিলেন। আর্থার শপেনহাওয়ার তার সহকর্মী জার্মান দার্শনিক ফ্রেডরিখ হেগেল এর কাছে ছিলেন একজন “চ্যাপ্টা মাথাওয়ালা, নীরস, বমি বমি ভাব উদ্বেগকারী, নিরক্ষর পণ্ডিত, যিনি একসাথে হিজিবিজি লেখালেখি করতে এবং পাগলাটে রহস্যময় বাজে কথা লেখার ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ সাহসিকতাসম্পন্ন।” তবে শপেনহাওয়ার নাকি হেগেল, কে বেশি কাপানো দার্শনিক ছিলেন, এ ব্যাপারে আমি নিশ্চিত নই।
এখন বিষয়টা হচ্ছে দর্শনের প্রত্যেকটি বিখ্যাত ব্যক্তিই মানুষ ছিলেন। তারা সেসব কাজই করতেন, যা আপনি স্বাভাবিকভাবে করেন। যেমনঃ পড়া, চিন্তা করা, পর্যবেক্ষণ করা, লেখালেখি করা। তাদের বড়বড় কথাবার্তা শুনে আপনি ভয় পাবেন না; আমরা এভাবে বলতে পারি যে, তাদের কথাগুলো গুরুত্বপূর্ণ, বা অন্তত এটা বলতে পারি যে তারা আমাদের চক্রান্ত করছে, অথবা আমরা পেছনে রয়ে গেছি। তাদের অবশ্যই উচিত হবে তাদের মুল্যটা আমাদের কাছে প্রমাণ করা।
কিন্তু সেই মুল্যটা কী হতে পারে?
সেটা হচ্ছে, প্রথমেই কেন দর্শন পড়তে হবে ! এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া। এই উত্তর দেওয়ার উদ্দেশ্য হচ্ছে, আপনার আত্মার উন্নতি সাধন করা। শুধুমাত্র শুনতে ভালো লাগে, অন্যদেরকে ভয় দেখানো যায়, বা বুকসেলফে উঁচুমাপের বই রাখা যায় – এইধরণের খোলা চিন্তায় বুদ হয়ে দর্শন পড়া উচিত নয়। বরং দর্শন পড়া উচিত মানসিক উৎকর্ষতা অর্জনের জন্য, আত্মিক শক্তি পাওয়ার জন্য এবং একটি সুন্দর জীবনের জন্য। (অথবা এসকল বিষয়ের কোনোকিছুই কেন সম্ভব নয় এবং কেন এগুলোর কিছুই আপনার জীবনে তেমন গুরুত্ব বহন করে না এ ব্যাপারে একটি ভালো বুঝাপড়া দাঁড় করানোর জন্য হলেও দর্শন পড়া চাই। কেননা দর্শন কোনো সম্ভাবনাকেই লুকায়িত [Unexplored] রাখে না।) আশার কথা হচ্ছে, এই তথাকথিত চিন্তাদানব খ্যাত ব্যক্তিবর্গ আমাদের জন্য এক্ষেত্রে কিছু সহায়িকা, কিছু প্রস্তাব রেখে গেছেন। আপনি চাইলে এগুলো গ্রহণ করতে পারেন আবার এগুলোকেই চ্যালেঞ্জ করতে পারেন!
এই বিগবসদেরই একজন বার্ট্রান্ড রাসেল তার The Problems of Philosophy (1912) গ্রন্থের শেষ দিকে দর্শন পড়ার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কারণ হিসেবে বলেনঃ
“দর্শন অধ্যয়নের অর্থ এই নয় যে, কোনো প্রশ্নের নির্দিষ্ট উত্তর থাকতেই হবে। আর নিয়মানুসারে, যেহেতু কোনো নির্দিষ্ট উত্তরকেই সত্য হিসেবে জানা যায় না বরং প্রশ্নগুলোর নিজস্ব কারণ নিত্য নতুন প্রশ্ন করতে দার্শনিককে প্রলুব্ধ করে। কেননা এসকল প্রশ্ন ‘কি কি’ সম্ভব, তথা সম্ভাব্যতার ব্যাপারে আমাদের চিন্তাশক্তিকে প্রসারিত করে এবং আমাদের বুদ্ধিবৃত্তিক কল্পনাশক্তিকে উন্নত করে। যার ফলাফল আমাদের কাজে গোঁড়ামির সম্ভাবনাকে দূর করার মধ্য দিয়ে চিত্রায়িত হয় ;যা চোখকে অনুমান নির্ভরতা থেকে হেফাজত করে। এজন্য দর্শন সকল জ্ঞানের উপরে। কারণ, মহাবিশ্বের মহত্বকে উপলব্ধির মধ্য দিয়ে মনও উন্নত হয়, যার ব্যাপারে দর্শন চিন্তা করে এবং যখন তা মহাবিশ্বের সাথে মিলিত হতে সক্ষম হয় তখন এ ব্যাপারে সর্বোত্তম বিষয়টি উপহার দেয়।”
দর্শন অধ্যয়ন আমাদের উন্নত উপায়ে ভাবতে পারার সম্ভাবনাকে উন্মুক্ত করে, গভীর বিস্ময়ে ফেলে দেয় এবং একজন মানুষের কলবে উদয় হতে পারে এমন সকল প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর দিতে সাহায্য করে। এটা হচ্ছে দর্শনের একটি দিক এবং এমন একটি দিক যা কেবল কাজের মধ্যে ডুব দিয়েই সম্পন্ন করা যেতে পারে।
তাহলে, মানুষ দর্শন পড়ে কিভাবে? এর ভেতর দিয়ে ভাবুন ! দর্শনের ব্যাপারে আপনার প্রত্যাশার পুনর্বিবেচনা করুন!
লাইব্রেরী বা বুকস্টোরগুলোতে “দর্শন” নামে একটা ক্যাটাগরি থাকে। সেখানে এরকম কিছু বই থাকেঃ The Seven Secrets to a Happier Life অথবা Get Your Sh*t Together অথবা Living With Your Heart Wide Open. এই বইগুলো কেবল নিজের উন্নতি কেন্দ্রিক, এগুলোর কিছু বই জীবনের বিভিন্ন সমস্যার সমাধানের ক্ষেত্রে একটি সুন্দর দৃষ্টিভঙ্গি দিবে অথবা সমস্যাগুলো মোকাবেলা করার বিভিন্ন রাস্তা দেখাবে। আপনি হয়তো প্রতিদিন সকালে আপনার বিছানা গুছাতে পারেন, অথবা রান্নার ক্লাস করতে পারেন, অথবা প্রতিটি মানুষকে বিশুদ্ধ মানুষ ভাবতে পারেন। সেটা চমৎকার। তবে প্রতিটি মানুষের প্রতি মুহুর্তেই একটা গতি প্রয়োজন, একটি সাহায্যকারী হাত থাকা প্রয়োজন এবং নিজের উন্নতি কেন্দ্রিক প্রতিটি সাহায্যকারী বই অনেককেই অনেকভাবে সাহায্য করেছে।
কিন্তু আত্মকেন্দ্রিক বইগুলো সাহায্যকারী হলেও দর্শনের বই নয়। দর্শন সাধারণত ব্যক্তিগত বিষয়ে অল্পই ভাবে, যেমন সময় বাস্তব কিনা, মানুষ প্রকৃতির আইন থেকে নিজেদেরকে মুক্ত করতে পারে কিনা, মানুষের মস্তিষ্ক যা বলে মানুষ সেটাই কিনা, অদ্ভুত মানুষের ক্ষেত্রে আমাদের নৈতিক বাধ্যবাধকতা আছে কিনা ইত্যাদি এবং দর্শন এই প্রশ্নগুলোর সুস্পষ্ট জবাব চায় না, তবে যা চায় তা হচ্ছে, কেন কিছু জবাবে এত সুন্দর আর কেনইবা কেন কিছু জবাব এত গোঁজামিলে ভরপুর।
হ্যা, ভুল। দর্শন এটা বলতে ভয় পায় না।
খুবই সাধারণ পর্যায়ে আত্মকেন্দ্রিক বইগুলো আপনার যেসব সমস্যা থাকা উচিত নয়, সেসবের সমাধান দিবে; আর দর্শন আপনার যেসব সমস্যা থাকা উচিত, সেসবের ব্যাপারে সাহায্য করবে। (অবশ্য কিছু বিষয় আছে যেমনঃ দর্শনের কিছু বই আপনাকে যেগুলোকে আপনার সমস্যা মনে করা উচিত নয়, সেগুলো সমাধানের ক্ষেত্রে সাহায্য করবে এবং কিছু আত্মকেন্দ্রিক বই আপনার জীবনে যেগুলোকে সমস্যা মনে করা উচিত, সেগুলোর ব্যাপারে মনোযোগ আকর্ষণ করবে।) কিন্তু আরো সাধারণভাবে বললে, দার্শনিক সমস্যা হচ্ছে সেইগুলো, যা সচেতনভাবে আসে এবং এড়িয়ে যাওয়া যায় না। যদি আপনি মনে করেন, তাহলে আপনার সমস্যা আছে, আর এজন্যেই দর্শন।
হাইডেগার এরিস্টটলের ব্যাপারে বলেন, তার শুধু জীবনীকেন্দ্রিক বিভিন্ন বিষয় জানা প্রয়োজন ছিল, যে তিনি ছিলেন একজন মানুষ যিনি জন্মগ্রহণ করেন, কাজ করেন এবং মারা যান। অন্য যত বিষয় আছে জীবনের, তার সবই দুর্ঘটনা। তাই দর্শনের বই থেকে ভুলেও কারো কোনো কাউন্সিলিং অথবা উপদেশ প্রত্যাশা করা উচিত নয়, যা গড়পড়তা যেকোনো মানুষের উপর প্রয়োগ করা যাবে না।
কিন্তু তাহলে শুরুটা করবে কিভাবে? কোন বই দিয়ে শুরু করলে ভালো হবে? দর্শন গণিতের মতো নয়, যেখানে মানুষ রাজী হবে যে, আপনাকে একটা জায়গা থেকে শুরু করতে হবে এবং কিছু ধাপ অতিক্রম করতে হবে, যেগুলো একটা আরেকটার উপর দৃঢ়ভাবে স্থাপিত। দর্শনকে চিত্রায়িত করলে দেখা যাবে একটা রুমে অনেকগুলো সংলাপ চলছে এর চাইতেও বেশি কিছু না। একজন নবীন এক্ষেত্রে সূচনা করার জন্য সেই রুমে যাওয়ার ম্যাপটা বুঝার জন্য এবং কথা বলার জন্য সাধারণ ভূমিকামূলক বিষয়গুলোকে উপকারী হিসেবে পেতে পারে। এ ব্যাপারে কিছু নির্দিষ্ট রেফারেন্স দেওয়া আছে লেখাটার শেষ দিকে, কিন্তু সম্ভবত সবচাইতে বড় যে বিষয়টি মাথায় আনতে হবে, তা হচ্ছে শুরু করার সুনির্দষ্ট কিংবা সর্বোত্তম কোনো পন্থা নেই। যেকোনো জায়গা থেকে শুরু করতে পারেন এবং সাধারণ ভাবে বললে আপনার আগ্রহের জায়গাগুলোকে অনুসরণ করুন যেদিক মন চায় সেদিক থেকে শুরু করুন।
দর্শনের জন্য প্রয়োজন সক্রিয়, বিপরীতমুখী অধ্যয়ন
আমাদের অবশ্যই মাথায় রাখা উচিত যে, আমরা যখনই কোনো বই পড়ি তখন সেটাতে মোহাবিষ্ট হয়ে পড়ি, কারণ পড়ার সময় আমরা ততটা নড়াচড়া করি না। শুধু আমাদের চোখগুলো নড়ে, বাম থেকে ডানে। কখনো পৃষ্ঠা উল্টাই বা নিচের দিকে যাই (স্ক্রলডাউন) সফটকপিতে পড়লে। যখন কোনো শব্দ আমাদের ভেতরে যায় তখন কোথাও থেমে থাকি এবং সেগুলোকে ধারণায় (Idea) রুপ দিই। মূলত, আমরা ভালো লেখা মনে করি সেগুলোকে, যা বুঝতে আমাদের ততবেশি পরিশ্রম করতে হয় না। কিন্তু যেগুলো পড়তে গেলে আমাদের ভ্রু কুচকে যায়, পেছনের পৃষ্ঠায় ফিরে যেতে হয়, অস্থির নিঃশ্বাস ফেলি, চাঁদের দিকে তাকিয়ে থাকি, সেগুলোকে বাজে লেখা বলি।
এই দৃষ্টিকোণ থেকে দর্শনের লেখাগুলোকে খুবই বাজে লেখা বলা যায়। কারণ, এই ধাচের বিষয়গুলোই এখানে দাবীদার হয়ে ওঠে। দর্শনের কোনো বইয়ে কোনো শব্দকে আইডিয়ায় পরিণত করা কঠিন কাজ। আপনাকে অব্যবহারিক পরিভাষা, স্পষ্ট পার্থক্য, মূল উদাহরণ এবং সাধারণ মূলনীতিগুলোর দিকে মনোযোগ ধরে রাখতে হবে। আপনি যদি এটা ঠিকঠাকভাবে করেন, তাহলে আপনি গুরুত্বপূর্ণ বা বিভ্রান্তিকর অনুচ্ছেদগুলো দাগিয়ে নিতে, গুরুত্বপূর্ণ দাবীগুলো আন্ডারলাইন করতে এবং বিভ্রান্তিকর বিষয়গুলির পাশে “???” বা “?” এরকম লিখে রাখতে একটা কলম, পেন্সিল ব্যবহার করবেন, দার্শনিকগণ এরকম বলতে চায় না। (বরং মোহাবিষ্ট না হয়ে আপনার এরকম চিন্তা করা উচিত যে, আপনি আপনার বইয়ের সাথে যুদ্ধরত আছেন)।
দর্শনের বইগুলো বারবার অধ্যয়ন করা উচিত। আপনি প্রথমবার দ্রুত পড়ে যেতে পারেন, যাতে ভাসা-ভাসা একটা ধারণা পান। তারপর আবার পূর্ণ মনোযোগ দিয়ে বিস্তারিত পড়বেন, তখন দাঁগিয়ে পড়বেন, নোট নিবেন, যাতে আরো ভালোভাবে বুঝতে পারেন লেখক কী বলেছে, কেন বলেছে। কিছু বইয়ের ক্ষেত্রে আপনি হয়তো আগ্রহ হারিয়ে ফেলতে পারেন। অন্যগুলোর ক্ষেত্রে আপনি এই প্রক্রিয়াটা অব্যাহত রাখবেন; দ্রুত পড়া, তারপর ধীরে ধীরে পড়া, তারপর আবার পড়া।
বলা হয়ে থাকে যে, যেকোনো দার্শনিক অভিযোগের ক্ষেত্রে দুই ধরণের জবাব দেওয়া হয়ঃ “ও হ্যাঁ?” এবং “তাহলে কী!” সেটা ঠিক। আপনি যখন দর্শন পড়তে শুরু করবেন তখন থেকে সর্বদাই আপনার মাথায় এই দুটি জবাব থাকতে হবে। সাধারণ অভিযোগগুলোর ক্ষেত্রে আপনার বিপরীতমুখী উদাহরণ দেওয়ার চিন্তা থাকতে হবে, অথবা অন্যান্য সম্ভাব্য ব্যাখ্যা, অথবা জিজ্ঞাসা করা যে দার্শনিকরা একইরকম বিষয়গুলো ধারাবাহিকভাবে হ্যান্ডেল করছে কিনা। আপনার এই প্রশ্নও করা উচিত যে, সেই অভিযোগগুলোর গুরুত্বপূর্ণ কোনো প্রভাব আছে কিনা, অথবা আপনি কোনো বিষয়ে সম্মতি দিলে আপনার জীবন সম্পূর্ণ বদলে যেতো কিনা। এক্ষেত্রে দার্শনিকরা আপনার মনোযোগ আকর্ষণের জন্য বাধ্যতামূলক কোনো বিষয় তৈরি করেন।
এর মানে হচ্ছে দার্শনিক লেখালেখি পাঠের ক্ষেত্রে মানসিকভাবে একটি বিপরীতমুখী অবস্থান নেওয়া জরুরি। অনেকটা এমন যেন কোনো বিতর্কিত বিষয়ে যাকে কিছু অসহায় আইনজীবী যুক্তি দিচ্ছেন তার সামনে আপনি কঠিন মনের অধিকারী হতে চান, সন্দেহমুক্ত বিচার করতে চান। তবে এটাও সত্যি যে, এই কঠিন মনের অধিকারী হওয়াটা অবশ্যই ব্যাখ্যামূলক কিছু পর্যায়ের সাথে মিল থাকতে হবে। সকল সম্ভাবনার ক্ষেত্রে আপনি যে দার্শনিককে পড়ছেন, তিনি বোকা নন; সুতরাং যদি আপনার অধ্যয়ন এরকম বুঝায় যে, দার্শনিক একটি বোকাসোকা যুক্তি দিচ্ছেন, তাহলে সমস্যাটা আপনার অধ্যয়নের হতে পারে। যুক্তি ও অভিযোগগুলোকে সুন্দর উপায়ে ব্যাখ্যা করুন। এরপরও যদি সমস্যা থেকেই যায়, তাহলে আপনি বিচার পেতে পারেন।
খেয়াল করুন অন্যান্য অনেক অধ্যয়ন থেকে এটা কিভাবে ভিন্ন। কোনো উপন্যাস পড়তে গিয়ে মার্জিনে “ও হ্যা?” এবং “তাহলে কী?!” দেখলে সেটাকে বিকৃত মনে হবে। অনেক ননফিকশন বই আপনাকে ইতিহাস, বিজ্ঞান, রাজনীতি, বা অন্যান্য বিষয়ে অনেক কিছু বলবে, কিন্তু সেগুলো আপনাকে ‘সত্য মানে কী’, সে ব্যাপারে কোনো কিছুই বলবে না। অবশ্য আপনি কখনো এই বইগুলোর সন্দেহজনক কোনো দাবীর ব্যাপারে “ও হ্যা?” এরকম প্রশ্ন করবেন। কিন্তু দর্শনের বই পড়ার সময় এই প্রশ্নগুলো মাথায় রাখতে হবে, কারণ স্বাভাবিকভাবেই আপনি সেগুলোকে বুঝবেন না, যতক্ষণ না আপনি এদেরকে সক্রিয় ও বিপরীতমুখী দৃষ্টিতে না দেখবেন। আপনি শক্তিশালী ও মোটা মানুষের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে কখনোই শক্তিশালী হতে পারবেন না। যদি শক্তিশালী হতে চান তবে আপনাকে তাদের মতো প্রশিক্ষণ নিতে হবে। দর্শনের ক্ষেত্রেও বিষয়টা অনেকটা এমনই।
পাশাপাশি এ ধরণের সক্রিয় অধ্যয়ন আপনি যা পড়ছেন তা উপলদ্ধির চাইতে বেশি ধারণ করতে সাহায্য করবে। অন্যদিকে নিষ্ক্রিয় অধ্যয়নে পাঠ করা বইগুলো মানুষ ক্রমেই ভুলে যায়।
দর্শন হচ্ছে ডায়লগ
কিছু দার্শনিক বই হচ্ছে একে অপরের সাথে সংলাপের মতো। তারা নাটকের মতো পড়ে, যদি আপনার স্থানীয় উচ্চ বিদ্যালয় প্লেটোর থিয়েটাস (জ্ঞান ও বিচার নিয়ে একটি লম্বা আলোচনা) নিয়ে কাজ করে, তাহলে আমি বিদ্যালয়ে না গিয়ে বাড়িতে থাকার পরামর্শ দেব। অন্যান্য বইগুলো সহজবোধ্য, যা সম্পূর্ণ একক কথকের (Monologue) মাধ্যমে কিছু বিষয় কভার করে। কিন্তু সকল প্রকার দার্শনিক কাজ এমনকি মনোলগ-ও (মনোলগ হচ্ছে যে নাটকীয় রচনায় একটি মাত্র লোক কথা বলে) সংলাপ নির্ভর। এই সংলাপগুলো হচ্ছে এমন যে, কেউ একজন দাবী তুলছে, আরেকজন গিয়ে সেটার ব্যাপারে অভিযোগ দিচ্ছে বা গভীর কোনো প্রশ্ন তৈরী উত্থাপন করছে। অবশ্য দার্শনিক বইগুলো খুবই জটিল সংলাপপূর্ণ হতে পারে। কারণ, সেখানে শুধুমাত্র অনেকগুলো কন্ঠস্বরই উপস্থিত হচ্ছে না, আপনিও সেখানে যুক্ত হচ্ছেন, সেই কন্ঠগুলোর সাথে কথা বলছেন। আপনি এবং সেই বই মিলে এখন একটা পার্টিতে পরিণত হয়েছে।
অনেক দর্শনের বইতে বিভিন্ন দার্শনিকদের পারস্পরিক আলোচনা পাওয়া যায়। উদাহরণস্বরুপ, ফরাসি দার্শনিক রেনে দেকার্তে তার Meditations (1641) গ্রন্থে প্যারাগ্রাফের পর প্যারাগ্রাফ ধারাবাহিকভাবে যুক্তি দিয়ে যান- “আমি অল্প অল্প করে আমার নিজের সম্পর্কে আরো কিছু ঘনিষ্ঠ বিষয় জানার চেষ্টা করবো। আচ্ছা তাহলে আমিও কি জানিনা কোনো বিষয়ে নিশ্চিত হওয়ার জন্য আমার কি কি প্রয়োজন? তবুও আমি অনেককিছুকে নিশ্চিত এবং প্রমাণরুপে গ্রহণ করেছি, যা পরবর্তীতে বুঝতে পারি বিষয়গুলো সন্দেহজনক ছিল। কিন্তু যে বিষয়গুলোকে খুবই সাদাসিদে মনে হয়েছিল, সেগুলোর কী হবে?’’
দেকার্তে নিজের ক্ষেত্রে “ও হ্যা?” কে সমাধান হিসেবে দেখছেন। এক অর্থে, এটি একটি অলংকারমূলক চক্রান্ত, যেহেতু তিনি এরকম মনে করার চেষ্টা করছেন যেন কেউ (যিনি স্বচ্ছ মানসিকতাসম্পন্ন এবং নিজেদের ব্যাপারে সৎ) কার্তেসিয়ান ম্যাটাফিজিক্সের বৃত্তে অনির্দিষ্টভাবে গমন করবে। তবে এটা মনে করবেন না যে, এটা ডায়ালেকটিক্যাল প্রভাবসম্পন্ন গুরুত্বপূর্ণ কোনো কাজ।
দেকার্তে যে অভিযোগ করেছেন এবং তার জবাব দেওয়ার চেষ্টা করেছেন, সেই অভিযোগের কথা চিন্তা করে পাঠককে এই সংলাপে নিয়ে আসতে হবে। কিন্তু একজন চালাক পাঠক সম্ভবত এমন কিছু প্রশ্ন করবেন যেগুলো দেকার্তে করেন নাই, অথবা আপনি এমন কিছু জবাব দেবেন যেগুলো দেকার্তে চিন্তা করেন নাই। সুতরাং সংলাপে আপনারও একটা অবস্থান আছে। তাই এসবের সব ব্যাপারেই নোট নিন।
দর্শনে ডায়লগ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সম্ভবত সকল চিন্তার ক্ষেত্রেই এটা গুরুত্বপূর্ণ। আমরা আইডিয়া দাঁড় করাই, প্রশ্ন করি, সমস্যা দেখাই, সেই আইডিয়াগুলোকে পুনরায় কাটাছেড়া করি, নতুন চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করি, নতুন আইডিয়া সামনে আনি এবং যতক্ষণ না নতুন কিছু বলার থাকে বা নতুন কিছু সামনে আসে, ততক্ষণ আইডিয়াগুলোকে প্রশ্ন-উত্তর এভাবে পারস্পরিকভাবে মোকাবেলা করতে থাকি। কিন্তু দর্শন টা বাস করে আইডিয়াগুলোকে আগ-পিছ করার মধ্যে, হারিয়ে ফেলা সম্ভাবনাগুলোকে তুলে আনার মধ্যে, নতুন প্রশ্ন উত্থাপনের মধ্যে, অথবা ভয়ংকর বা ক্ষতিকর সিদ্ধান্তে আসার আগে কিছু বিভাজন সৃষ্টির মধ্যে। সংলাপকে এগিয়ে নেওয়া, পরিবর্তন পরিবর্ধন করা–এটাই হচ্ছে দার্শনিক পদ্ধতি।
যেমন আমি সংজ্ঞায়িত করবো এভাবে, দর্শন হচ্ছে আইডিয়াগুলো নিয়ে বোধগম্যতার সীমান্তে ঝাপিয়ে পড়া। যত দ্রুত প্রশ্নগুলো বোধগম্য হয়ে ওঠে, ততই নতুন কোনো ডিসিপ্লিন বের হয়। যেমন ফিজিক্স, বায়োলজি, সাইকোলজি। কিন্তু এখনো যখন আমরা সামনে পেছনে যুদ্ধ করছি কোনটা সত্য মনে হয়, কোনটা অসম্ভব মনে হয় (যা আমরা দেখতে পারিনা) এসব নিয়ে, তখন আমরা দর্শন চর্চা করছি। সেখানে সংলাপের মধ্যে আসলে সামনে-পেছনে পদ্ধতি ছাড়া আর কোনো পথ নেই।
দর্শন অধ্যয়নে, আপনি ডায়লগকে এগিয়ে নেওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করতে চান। সেই পর্যায়ে, দর্শনের কোনো বইতে কী লেখা আছে, তার ব্যাপারে আপনার চিন্তাগুলো বুঝার জন্য একটি ম্যাগাজিনে আপনার লেখালেখি করা উচিত, যেখান থেকে আপনার চিন্তাগুলো বুঝা যাবে, আপনি সেই লেখককে কী জিগ্যেস করতে চান এবং আপনি তাকে কী বলতে চান (সেটা ভদ্রোজনিত না হলেও।) যেহেতু আপনি আপনার চিন্তাগুলোকে উন্মুক্ত করছেন, সেহেতু আপনি আপনার নিজের সম্পর্কে আরো বেশি জানবেন। মাঝেমাঝে আমরা নিজেরাও বুঝিনা আমরা কি চিন্তা করি, যতক্ষণ না নিজেরা সেগুলো বলি বা শেয়ার করি। দার্শনিক সংলাপগুলো পড়ার সময় নোট নেওয়ার মাধ্যমে নতুন কিছু জানা এবং নতুন অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হওয়া যায়। তারপর যখন আপনি সেই কাটাছেড়া করা বইটি ৩য় বা ৪র্থ বারের মতো পড়বেন, তখন আপনার মনে নতুন প্রশ্ন, নতুন দৃষ্টিভঙ্গি উদয় হবে। এর দ্বারা আপনি নতুন এক বইকে আবিষ্কার করবেন।
বলা হয়ে থাকে যে, কোনো বিখ্যাত বইকে কখনোই সম্পূর্নরুপে পড়ে ফেলা যায় না। কারণ, যতবারই আপনি এটা পড়বেন, আপনি তখন ভিন্ন একজন পাঠক হয়ে যান। এটাকে অতিরঞ্জিত মনে হলেও এর মাঝে কিছু একটা আছে। মাঝেমাঝে এটাও বলা হয়ে থাকে যে, আপনি যখন বিখ্যাত কোনো বই পড়েন, তখন বইটিও আপনাকে পড়ে। সেটাই হচ্ছে, বইয়ের আইডিয়াগুলোর মাধ্যমে আপনি আপনার জীবনকে নতুনভাবে জানতে শুরু করবেন। এটাই হচ্ছে কোনো খাটি সংলাপের অনিবার্য ফলাফল। তখনই কেবল দর্শন তার সর্বোচ্চ রুপ দেখাতে পারে।
আপনাকে ঘিরেই দর্শন
দর্শন আপনার কর্মস্থলের সমস্যাগুলো নিয়ে নয়, অথবা আপনার ফোনের কন্টাক্ট কিভাবে নিয়ন্ত্রণ করবেন সেগুলো নিয়ে নয়, অথবা সকল সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম স্থগিত করে দিবেন কিনা এগুলো নিয়ে নয়, যদিও সেগুলো দর্শনের মাধ্যমে বিশেষায়িত করা যেতে পারে। বরং এটা হচ্ছে মানুষ হিসেবে আপনার জীবনকে নিয়ে।
কল্পনা করুন, অনেক যুগ আগে একটা সময়ের ঘুর্ণাবর্তে পড়ে গেলেন এবং কিছু মানুষের মধ্যে হারিয়ে গেলেন। তখন একবার যদি কোনো একটা ভাষায় তাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন, তাহলে কি তাদের বন্ধু হতে পারবেন? আপনি কি তাদের সাথে আপনার দুঃখ, আশা, ধারণা, বিশ্বাসকে শেয়ার করতে পারবেন? অবশ্যই পারবেন। তবে আপনার যোগাযোগ বা সংলাপটা অবশ্যই মানুষের সাথে মানুষের হতে হবে, শিল্পবিপ্লব পরবর্তী প্রযুক্তিবিদের সাথে গুহাবাসীর সংলাপ হলে হবে না। আপনি কেবল আপনার শেয়ার করা মানবিক মুল্যবোধের উপর বন্ধুত্ব স্থাপন করতে পারবেন। অবশ্যই এটা হবে আপনার সকল সম্পর্কের চাইতে সেরা বন্ধুত্বের সম্পর্ক। কারণ, তখন এই খাটি বন্ধুত্বের মধ্যে কোনো বাজে কথাবার্তা থাকবে না।
সবাই যেভাবে আপনাকে ব্যাখ্যা করেছে তার বিপরীতে গিয়ে (আগে উল্লেখ করা) অনেক বই আপনি আসলে কে, সেটা খুজে বের করার উপর ফোকাস করে। কেউ এটা করতে পারে অভ্যন্তরীন দৃষ্টিভঙ্গির মাধ্যমে অথবা ভিন্ন জীবনধারা সৃষ্টি করে। দর্শন ভিন্নকিছু করতে বলে। “আমরা কে হতে পারি” এই বিষয়ে সংলাপের মাধ্যমে “আমরা আসলে কারা” এটা খুজে পেতে পারি। প্লেটো, এরিস্টটল, ইবনে সিনা সবারই এ ব্যাপারে মতামত ছিল, তেমনি ছিল জিইএম অ্যান্সকোম্ভ, কার্ল মার্ক্স, ফ্রেডরিখ নীটশে; নগরজুনা, লাও জু এবং কোয়াসি ভীরেদু। অবশেষে, যদি আমরা কারো মতো হতে চাই, তাহলে কোথাও থেকে আসা কিছু ব্যাখ্যার মাধ্যমে আমরা সমৃদ্ধ হতে পারি। দর্শন বিভিন্ন রকমের ব্যাখ্যা উদ্ভাবন করার সুযোগ দেয় এবং সেগুলোর মধ্যে আপনাকে খুজে পাওয়ার চেষ্টা করে। এটাই হচ্ছে সকল দার্শনিক পড়াশোনার সমন্বিত কার্যক্রম।
বিভিন্ন উৎসের ব্যবহারঃ
বিষয়টির বাস্তবতা হচ্ছে আমরা দর্শনের সাথে পরিচিত হতে পারার মতো একটি চমৎকার সময়ে বসবাস করছি। ইউটিউবে অসংখ্য দার্শনিক এবং তাদের আইডিয়াগুলো পাওয়া যায় এবং যদিও প্রতিটি ভিডিওতে সন্দেহের অবকাশ থাকতে পারে, তবুও এক্ষেত্রে অনেকে আমাদের প্রসিদ্ধির পথে নিয়ে যাওয়ার পথে বিরাট ভূমিকা রাখছে।
ইউটিউবের দর্শনের ভিডিওগুলো আমাদেরকে রসাত্মক ও উত্তেজনাপূর্ণ আবিস্কারের দিকে আহবান করে। অনেক পডকাস্টে উপকারী জিনিস পাওয়া যায়। যেমনঃ The Partially Examined Life, Very Bad Wizards, Philosophy Bites (এটা Aeon+Psyche এর সমন্বয়ে পরিচালিত হয় যেখানে সম্পাদনায় থাকেন Nigel Warburton) এবং Peter Adamson এর সাহসী ও উজ্জ্বল History of Philosophy, যাতে কোনো গ্যাপ ছিলো না। এরকম আরো অনেকেই দর্শনের পথে আকস্মিক প্রবেশ ঘটিয়ে থাকেন।
আসুন বই পাগল না হই। কারণ, প্লেটো নিজেই মনে করতেন যে, প্রকৃত দর্শন কেবল সরাসরি সংলাপের মধ্যেই হয়ে থাকে, আর লিখিত বিষয়টি প্রকৃত বিষয়ের প্রতিফলন মাত্র। (ও হ্যা, এটা তিনি একটি পাণ্ডুলিপিতে লিখেছিলেন।)
বিখ্যাত দার্শনিক লেখাগুলোর জটিলতাগুলোকে ফুঁসিয়ে তুলতে আপনার কাছে যে গৌণ উৎসগুলোর (Secondary Sources) একটি বিস্তৃত জগত রয়েছে, সেগুলোকে নির্দ্বিধায় ব্যবহার করুন। দর্শন পুরনো হলেও এর অন্যতম সুন্দর একটি দিক হলো এটা কখনো পুরনো হয় না এবং কখনো ১৯৭০ সাল থেকে পুরনো ভূমিকামূলক কিছু বই সুন্দর কিছু প্রশ্নের জবাব দিতে পারে।
আপনি বারবার অধ্যয়ন করতে গিয়ে পুরনো অন্যান্য বইপত্রগুলোর ত্রুটিবিচ্যুতি খুজে পাবেন। কিন্তু আপনার এটিকে একটি বিজয় মনে করা উচিত। কারণ এর মাধ্যমে আপনি নিজেকে দর্শনের উন্নত স্তরে নিয়ে যাচ্ছেন।
অবশেষে বলা যায়, অন্যান্য উৎস হিসেবে (কিংবা প্রধান উৎস হিসেবে) কারোরই বন্ধুত্বের মুল্যকে অবমূল্যায়ন করা উচিত নয়। যদি আপনি একটি পাঠক শ্রেণী তৈরি করতে পারেন এবং আপনার অনুভূতিগুলো তাদেরকে শেয়ার করতে পারেন, তাহলে আপনি শিখবেন কিভাবে ব্যাখ্যা করতে হয়, যুক্তি উপস্থাপন করতে হয় এবং আপনার মনকে চ্যালেঞ্জ করতে হয় বা কোনো দার্শনিকের সকল প্রয়োজনীয় উপাদানগুলোকে (এমনকি যেকোনো মানুষের) কিভাবে চ্যালেঞ্জ করতে হয়।
মূলকথা – দর্শনকে যেভাবে পড়তে হবে
১। দর্শনের ব্যাপারে আপনার প্রত্যাশার পুনর্বিবেচনা করুন। আপনার ভেতর একটি নিশ্চিত মানসিকতা আছে, যা দর্শন বুঝতে গেলে আপনাকে সাহায্য করবে। এছাড়া এটা উত্তরবিহীন প্রশ্ন এবং সমাধানহীন সমস্যার মোকাবেলা করার জন্য প্রস্তুতি নিতে সাহায্য করবে।
২। দর্শনের জন্য প্রয়োজন এক্টিভ ও বিপরীতমুখী অধ্যয়ন। অধ্যয়নের সময় সেখান থেকে সর্বোচ্চটা পেতে হাতে একটি পেন্সিল নিন, জরুরী জায়গাগুলো চিহ্নিত করুন এবং সুযোগ পেলেই লেখককে চ্যালেঞ্জ করার সাহস করুন। (এভাবে যে, আপনি লিখলে বিষয়টা কিভাবে লিখতেন।)
৩। দর্শন হচ্ছে ডায়লগঃ যে বিষয়গুলো চমৎকার সেগুলো প্রয়োজনে যোজন বিয়োজন করুন, এর সামনে পেছনে চিন্তা করুন। আপনি যখন পড়বেন, তখন দর্শনের জায়গাগুলোতে মনোযোগ দিন। এবং সেগুলো ধরতে পারছেন কিনা, নিশ্চিত হউন।
৪। দর্শন মূলত আপনাকে ঘিরেই। দার্শনিক কথাবার্তা (কোনো বই বা বন্ধুদের আড্ডালাপ) সর্বদাই আপনাকে আপনার নিজের ব্যাপারে আরো নতুন কিছু বলবে। কে আপনি, পৃথিবী নিয়ে আপনি কী ভাবেন; এসব। দর্শন হচ্ছে নিজেকে বিভিন্ন উপায়ে জানার একটা প্রক্রিয়া।
৫। অন্যান্য উৎস ব্যবহার করুন। দর্শন বুঝতে শুরু করার এটাই উপযুক্ত সময়। কারণ, অসংখ্য উৎস আছে যেগুলোর মাধ্যমে আপনি নতুন জগতে প্রবেশ করতে পারেন।
কেন এটা গুরুত্বপূর্ণ
আমি এই বিষয়ে আপনাকে এতকিছু বলার জন্য দুঃখিত, কিন্তু আপনি মরণশীল। যদিও আপনার মৃত্যুর আগে উচিত ঠিকঠাকভাবে খাওয়া দাওয়া করা, প্রতিনিয়ত ব্যায়াম করা, বন্ধু তৈরি করা, সহায়হীনদের সাহায্য করা। আপনি একটু সময় নিয়ে ভাবতে পারেন অস্তিত্ব মানে কী, বাস্তবতা আসলে কী, স্রষ্টা বলতে কেউ আছে কিনা, বা এই মানব জীবনের কোনো উদ্দেশ্য আছে কিনা। জবাবগুলো নিশ্চিত না, তবে সেগুলোর খোঁজ করা আপনাকে সাহায্য করবে এটা ভাবতে যেন, আপনি এই বিষয়গুলো বুঝতে একটা সুযোগও হাতছাড়া করেন নাই।
এই বড় প্রশ্নগুলো মোকাবেলা করার সবচাইতে সেরা পদ্ধতি হচ্ছে দর্শন পাঠ। আবার, কোনো জবাবই নিশ্চিত নয়, অথবা অনেকগুলো জবাবই নিশ্চিত! কিন্তু বিখ্যাত দার্শনিকদের সাথে করা সংলাপটি আপনাকে সাহায্য করবে এটা আবিষ্কার করতে যে, সেই বড় প্রশ্নগুলো দিয়ে আসলে কী বুঝায়। আপনার যা দরকার তা হচ্ছে সময়, কিছু কৌতুহল এবং একটা লাইব্রেরী কার্ড।
প্লেটো বলেন যে, দর্শন শুরু হয় বিস্ময় থেকে। সে বিস্ময় কিসের? এটা হতে পারে আপনার নিজের সচেতনতাবোধের; বা আপনার কোনো অঙ্গ আপনার মৃত্যুর পর টিকে থাকবে কিনা; সৌন্দর্য বা প্রেমের প্রকৃতি; মানুষ সবসময় একে অপরের সাথে বাজে আচরণ করতে বাধ্য কিনা অথবা আমাদের আচরণ উন্নত করা যায় কিনা; হতে পারে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান সম্পর্কে, অথবা সবকিছু বুঝতে পারা সম্ভব কিনা। মানবিক অভিজ্ঞতার মাধ্যমে এরকম বিস্মিত হওয়ার অনেকরকম উপায় দেখে থাকি। যেমনঃ (https://tinyurl.com/mrxxrhe4)
কিন্তু প্রতিদিনকার জীবনে এই ধরণের বিস্ময়কে প্রায়ই নিরুৎসাহিত করা হয়। কারণ, এটা অপ্রায়োগিক হিসেবে দেখা যায়। আমরা মনে করি “এই ধাচের প্রশ্নের কোনো জবাব নেই।” “শুধু জল্পনা; প্রত্যেকেই তাদের নিজস্ব রুপে।”
তাই আমাদের কি আশ্চর্য হওয়া উচিত নয়? আমাদের কি এই অভিনয় করা উচিত যে, এগুলো কোনো প্রশ্নই না, তার একমাত্র কারণ তার মুল্য অনেক বেশি? অথবা দোলনা থেকে কবরে যাওয়ার পথে বিস্মিত হওয়ার জন্য গভীর যে প্রশ্নগুলো করতে পারি, সেখানে কি আমাদের এই সুযোগটি ব্যবহার করা উচিত?
লিংক ও বইঃ
মানুষ বিভিন্ন কারণে দর্শন পড়তে আগ্রহী হয়। কেউ পছন্দ করে দ্রুত ও রসালো ধাধা, যেমন ট্রলি সমস্যা (https://tinyurl.com/y4xm8vn4) বা পরিবহনকারীদের (https://tinyurl.com/53hf9f3s) ব্যাপারে প্রশ্ন। David Chalmers এর সাম্পতিক বই Reality+ (2022)। এটা ভার্চুয়াল বাস্তবতার বাস্তবতা সম্পর্কে উত্তেজনাপূর্ণ প্রশ্ন ও দৃষ্টিভঙ্গি উত্থাপন করে দুর্দান্ত ধাধার দিকে আহবান করে।
অন্যান্য লোকেরা আইডিয়ার বৃহৎ ইতিহাসে তাদের জ্ঞানের কিছু ফাক ফোকর পূরণ করতে পছন্দ করে। Durant এর ক্লাসিক গ্রন্থ The Story of Knowledge (1926) যা কতিপয় যাজক শ্রেণির দার্শনিকদের দৃষ্টিভঙ্গি উপস্থাপন করে। এই বইটা আমি সাজেস্ট করি তাদেরকে যারা দর্শন পড়া শুরু করবে এবং একটা রোডম্যাপ পেতে চায়।
Bryan Magee তার The Story of Philosophy: A Concise Introduction to the World’s Greatest Thinkers and Their Ideas (2nd ed, 2016) বইতে Durant এর বইয়ের আপডেট ব্যাখ্যা দিয়েছেন। কেউ চাইলে সহজেই ডুরান্ট বা ম্যাগির দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ক্লাসিক দর্শনের ধারণা পেতে পারে এবং নিজেকে এগিয়ে নিতে পারে যেমনটা Steven M Cahn এর Classics of Western Philosophy (8th ed, 2011) বইতে পাওয়া যায়।
যদি কেউ সমসাময়িক দার্শনিকেরা কি নিয়ে ভাবে, তা জানার ব্যাপারে আগ্রহী হয়ে থাকে, তাহলে এর সরাসরি ধাচের সাক্ষাৎকারটা শুনতে পারেন তার ওয়েবসাইট 3:16 (https://tinyurl.com/3yxdync5) এ।
আরেকটু জেনারেল লেভেলে একটি ক্লাসিক বই হচ্ছে Mortimer Adler এবং Charles Van Doren এর How to Read a Book (1940)। এর ধাচটা প্রাচীন স্কুল লেভেলের, কিন্তু এ জাতীয় স্পষ্ট ও স্বাস্থ্যকর লেখাগুলোতে নস্টালজিক একটা আনন্দ পাওয়া যায়। আর এটা দর্শনের বইপত্র পড়ার জন্য খুবই কার্যকর।
দর্শন পড়ার ক্ষেত্রে কিছু গুরুত্বপূর্ণ উপদেশ পাওয়া যায় এডিনবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের এই ব্লগে (https://tinyurl.com/yc8feyec)। আবার যদি কেউ ভিডিও দেখে শিখতে চায়, তিনি Christopher Anadale এর How to Read Philosophy in 6 Steps’ (2016) ভিডিওগুলো দেখতে পারেন। লিংকঃ (https://tinyurl.com/2p8va9p6)
অবশেষে, Justin E H Smith এর The Philosopher: A History in Six Types (2016) বইটি দর্শন বলতে কী বুঝায় সেই বুঝাপড়া এবং দর্শন রপ্ত করতে গিয়ে কোন দিকটির প্রতি আগ্রহী হয়ে উঠতে পারি, সেই ব্যাপারগুলো প্রশস্ত করবে। এটা হচ্ছে যে কারো জন্য একটি উপকারী আত্মসংশোধনমূলক বই তার জন্য, যিনি জ্ঞানের প্রতি আগ্রহটা ধরে রাখতে চান।
অনুবাদক: রিয়াজ আহমেদ