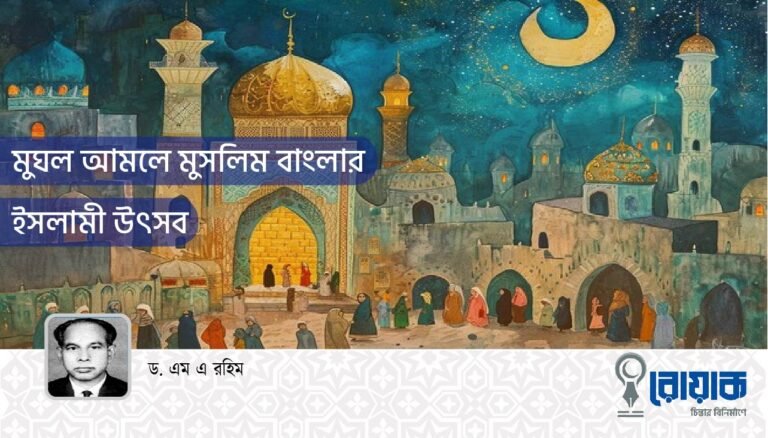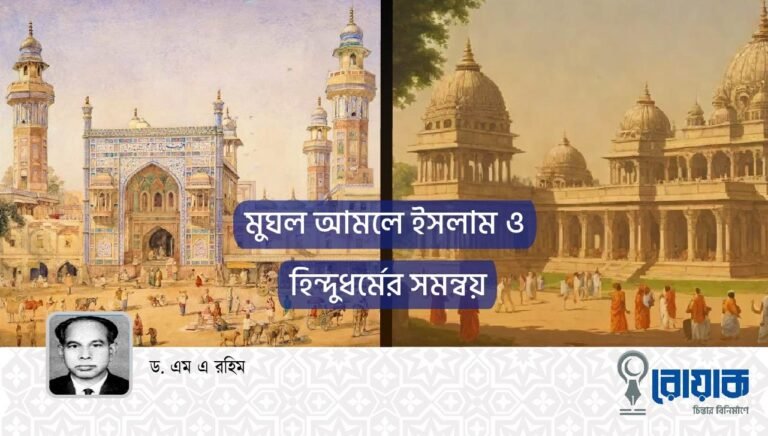(১)
মহাকালকে আত্মিক বা তাত্ত্বিক সত্তা যেভাবেই ভাবা যাক না কেনো, তার প্রবহমানতা বা গতিকে কিছুতেই অস্বীকার করা যায় না। সে-কালের গতি অবিচ্ছিন্ন, তার আদি অন্ত আজ মানুষের জ্ঞানের বহির্ভূত। তবু আমাদের সুবিধার জন্য আমরা তাতে রেখা টেনে ভাগ করি এবং পুরাতন, মধ্য ও আধুনিক যুগ বলে তাতে তিনটে পর্যায়ের সৃষ্টি করি। আধুনিক যুগের বর্ণনা প্রসঙ্গে দর্শনের ইতিহাসবিদ মিলি বলেন,
“বর্তমান কালের ইতিহাসের মধ্যে লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে চিন্তার পুনর্জাগরণ, সমালোচনা করার মনোবৃত্তির জন্মলাভ, গুরুবাদের ও ঐতিহ্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ, নির্বিশেষবাদ (Absolution) ও সংঘবাদের (Collectivum) বিরুদ্ধে প্রতিবাদ এবং চিন্তায়, অনুভূতিতে ও কার্যে স্বাধীনতার দাবী। রেনেসাঁ ও রিফরমেশনের ক্রান্তিকাল থেকে যে প্রভাব কার্যকরী ছিল, তাই পরবর্তী শতাব্দীতে রয়েছে ক্রিয়াশীল এবং এখন পর্যন্ত তা শান্ত হয়নি।”
এ মতবাদের পোষকতায় ঐতিহাসিক দৃষ্টান্তের উল্লেখ করে বলা হয়, দার্শনিক চিন্তার ক্ষেত্রে প্রাচীনকালের গ্রীক মনীষার সঙ্গে বর্তমানকালের সাদৃশ্য রয়েছে। অপরদিকে মধ্যযুগ ছিল বর্তমান কালের সম্পূর্ণ বিপরীত—ধর্মী। গ্রীকদের চিন্তারাজ্যে কোন আপ্তবাক্য (Authority) বা কোন সংঘবদ্ধ চিন্তার শাসন ছিল না। ছোট ছোট নগরকেন্দ্রিক রাষ্ট্রে প্রত্যেক মনীষীরই আপনার স্বাধীন মতামত ব্যক্ত করার অধিকার ছিল। এ জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে তাদের ধারণার ফল কোনো ধর্ম সংক্রান্ত প্রত্যয় দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়নি। সক্রেটিস, প্লেটো বা এরিস্টটলের চিন্তাধারায় তাই স্বাধীন মানসের পরিচয় পাওয়া যায়। তেমনি কাব্যে ও নাটকে সেই সাশ্রয়ী মানসের স্বাক্ষর রয়েছে। হোমার, সকোক্লিস, এসকাইলাস প্রভৃতি মহাকবি ও নাট্যকারগণের অমর অবদানে এ সত্যই বার বার প্রমাণিত হচ্ছে।
মতামত ব্যক্ত করার প্রবৃত্তি প্রাচীনকালে ছিল—এ থিওরী সত্য হলেও প্রচলিত প্রত্যয় বা রীতি-নীতির বিরুদ্ধে প্রচারণা সে-যুগেও বিস্তৃতি লাভ করেছে। সক্রেটিসের জীবন তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। আবার মধ্যযুগেও স্বাধীনভাবে চিন্তা করার উদাহরণ রয়েছে। সেলজুক বাদশাহ মালিক শাহের আমলে, তাঁর উজির নিজাম-উল-মূলক প্রতিষ্ঠিত নিশাপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের জ্যোতির্বিজ্ঞানের অধ্যাপক ওমর খৈয়াম তার ‘রুবাই’তে যে-সব আদিম ও সার্বজনীন প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন, তার সঙ্গে তুলনা করলে অতি আধুনিক তত্ত্ব-জিজ্ঞাসাও ম্লান হয়ে পড়ে। আবার এ বিংশ শতাব্দীতেই টি.এস. এলিয়ট তাঁর কাব্যে ধর্মাশ্রিত দর্শনকে প্রতিষ্ঠা করবার প্রয়াস পেয়েছেন।
এ বিভাজনকে তাই সাধারণ নীতি হিসাবে গ্রহণ করলেও তার মধ্যে ব্যতিক্রমের অবকাশ রয়েছে বলে স্বীকার করতেই হবে, এ বিভাজন করার মূলে রয়েছে যে মানদণ্ড, তাকে স্বাধীন বা ধর্মসংক্রান্ত প্রত্যয়শীলতা বলেও গ্রহণ করা যায় না। স্বাধীন চিন্তার মূলেও রয়েছে জীবন-দর্শনসম্ভূত প্রত্যয়শীলতা। আর ধর্মকেন্দ্রিক প্রত্যয়শীলতায় যে এক প্রচন্ড জীবনবোধ রয়েছে তা অনস্বীকার্য। কোনো জীবন-বেদ ব্যতীত যে সত্যিকার কাব্য-সৃষ্টি সম্ভব নয়, তা যে কোনো মহাকাব্যের বিশ্লেষণেই প্রমাণিত হয়। হোমার বা বাল্মীকির কাব্যে আমরা সে প্রত্যয়শীলতারই নিদর্শন পাই—ইলিয়ড ওডিসির যে প্রত্যয়শীলতা—‘সত্যের জয় এবং অসত্যের ক্ষয়’ নামক নীতির স্বীকৃতিতে তা প্রমাণিত হয়। রামায়ণেও সে নীতিরই সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। তবে পার্থক্য এই যে, রামায়নের সর্বত্রই প্রকৃতির মধ্যেও নীতির কার্যকারিতা দেখা যায়। সক্রেটিসের নাটকাদিতে নিয়তির অমোঘ বিধানের উপর নাট্যকারের অগাধ বিশ্বাসের পরিচর পাওয়া যায়।
মধ্যযুগের বিশেষত্ব হচ্ছে ধর্মীয় প্রত্যয়শীলতার পটভূমিতে জীবনের সমালোচনা করার প্রবৃত্তি। এজন্যই সে যুগের কাব্যকে ধর্মীয় বাণী থেকে পৃথক করা কষ্টসাধ্য। জালাল-উদ্দীন রুমীর মসনভীতে একাধারে ধর্মতত্ত্ব ও কাব্য-রসের সন্ধান পাওয়া যায়। মরমী তত্ত্ববাণী যেমন এ কাব্য থেকে তাঁর সাধনার অনুকূল প্রেরণার উৎসের সন্ধান পান, তেমনি কাব্যরস পিপাসু রসিকজন তাতে উৎকৃষ্ট কাব্যের লক্ষণ আবিষ্কার করে অভিভূত হন।
এ ধারা মধ্যযুগে ব্যাপকভাবে প্রচলিত হলেও এখনও তার ইতি হয়নি। বাঙলা কাব্যের বৈষ্ণব পদাবলীতে সে ধারারই অনুসরণ দেখা যায়। মৈথিলী কবি বিদ্যাপতির কাব্যের পটভূমিকায় এবং মীরার ভজনে সে মানসিকতাই বর্তমান। উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর বাউলদের গানে সে ধারার অনুবর্তন লক্ষিত হয়।
এভাবে কাব্যের মধ্যে ধর্মীয় প্রত্যয়ও ও ব্যক্তিগত জীবনের অভিজ্ঞতা ওতপ্রোতভাবে বিজড়িত থাকায় তাকে দু’দিক থেকেও বিচার করার সম্ভাবনা রয়েছে। তার কারণস্বরূপ বলা যায়‚ বর্তমান কালের সূচনায় জ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রকে যেভাবে পৃথক করা হয়েছে— মধ্যযুগে সে পার্থক্য এত উৎকট হয়ে দেখা দেয়নি বলে একই মানসে তা’ কোথাও ধর্মের আবেগরূপে আবার কোথাও কাব্যের অনুরাগরূপে অপরূপ ভঙ্গিমায় প্রকাশ লাভ করেছে। সম্ভবতঃ এজন্যই মধ্যযুগীয় কাব্যসাধনা তথা ধর্মীয় প্রত্যয়শীলতার ফল Cult-এ পরিণত হয়েছে।
ইকবাল আমার সঙ্গে কথা বললেন একজন পরামর্শদাতার মতো করে। তাঁর কবিতার মধ্যে বিপুল চিন্তাশক্তি আর ভাবপ্রবণতার আভাষে আমি স্তম্ভিত হলাম। কখনও তিনি বিশ্বস্ত সংলাপী, কখনও আবার অগ্নিময়ী বিচারকের মতো ‘মানুষের’ জয়গান গেয়েছেন।
‘তুমি গড়িয়াছ রাত্রি,
আমি এনেছি আলোর দিশা,
তুমি আমারে দিয়েছ মৃত্তিকা
আমি গড়িয়া তুলেছি পাত্র।
মরু প্রান্তর, পর্বত
সবি তোমারি দান,
উদ্যান প্রভু রচেছি যে আমি—
বিরাম স্থান।
বালুকার রাশি রূপ পেয়ে
হোলো স্বচ্ছ কাঁচ
বিষ নাশি বিষে মধু আনি দিনু
নতুন ধাঁচ।”
(‘মানুষে ও স্রষ্টার মধ্যে কথোপকথন’)
একথা বলেছেন তিনি সৃষ্টিকর্তাকে উদ্দেশ্য করে। এখানে তাঁর সতর্কীস্বর মানুষের ক্ষমতাবোধকে জাগিয়ে তুলেছে।
“…..দিনভর শুধু ঘুমায় যে জন
প্রকৃতি চাহেনা তারে
যে মানুষ খাটে দিনটি ভরিয়া
সব প্রেম তার ভরে।”
(‘দুর্দশার দৃশ্য’ কবিতা থেকে)
ইকবাল ডাক দিয়েছেন তাঁর দেশবাসীকে ঘুমভেঙে জেগে উঠতে, স্বাধীনতা আর ন্যায়-বিচারের জন্যে সংগ্রামে আগুয়ান হতে। অন্যায়, নিষ্ঠুরতা আর দমনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে তিনি তাঁর দেশের মানুষদের উপনিবেশ স্থাপনকারীদের অত্যাচার থেকে দেশকে মুক্ত করতে আহ্বান জানিয়েছেন।
যতই আমি ইকবালের কবিতা পড়ি, তাঁর দেশের মানুষের জীবনধারাকে আরো পরিষ্কাররূপে দেখতে পাই, অনুধাবন করি তার মাতৃভূমির মহিমান্বিত রূপ আর সেই দেশের জন্যে কবির অপরিসীম ভালবাসা।
তার বইগুলো আমার চোখের সামনে প্রাচ্যের মানুষদের মহিমাভরা অপূর্ব জীবনধারা আর সে জীবনের দুঃখভরা দৃশ্যাবলী রূপায়িত করে।
ইকবালের কাব্যধারা সোভিয়েত পাঠকদেরও বিশেষ করে কাযাখরা, যারা কাস্পিয়ান সাগর আর উরাল পর্বতমালা থেকে অন্যদিকে আলতাই পর্বতমালা আর জুনগর দরওয়াজা পর্যন্ত এশিয়ার এক সুবিশাল বৃক্ষপত্রহীন প্রান্তরে বসবাস করে, তাদের কাছে উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া সম্পত্তির মতো হয়ে দাঁড়িয়েছে। কাযাখদের যুগযুগের পুরাতন একটা ইতিহাস রয়েছে; ওদের সমৃদ্ধ কৃষ্টিধারা আছে তাই ওরা কাব্যজগতের মূল্য উপলব্ধি করে। কাযাখদের নিজেদের আছে মহাকাব্যের ধনাগার। আমি নিশ্চিতভাবে বিশ্বাস করি যে, আমাদের প্রখ্যাত কবি যোদ্ধা কবি মঘোম্বেত (১৮০৪-১৮৪৬), নীতিগর্ভ উপদেশ আর প্রবাদবাক্যে ভরা কাব্যের বিখ্যাত দার্শনিক কবি আবাই (১৮৪৫-১৯০৪), এবং নামকরা মানবতার কবি মুখতার অডিএজোভের (১৮৯৭-১৯৮১) বইগুলো যদি উর্দুতে অনুদিত হতো তাহলে সেগুলো ইকবালের কাযাখ ভাষায় অনুবাদ করা কবিতাগুলির মতোই হৃদয়গ্রাহী হতো। ইকবালের মতো এদের কাব্যলিতেও আছে গভীর একটি ভাবাবেগ; মানুষের প্রতি ভালবাসা, মহৎ একটি আকাঙ্ক্ষা, মানুষের স্বাধীনতা, বিচারশক্তি এবং আলোর পথে ডাক দেওয়া।
আমাদের আধুনিক মানস স্বভাবতঃই স্বাশ্রয়ী ও স্বাতন্ত্র্যবাদী। সেজন্য ধর্মাশ্রিত কাব্যকে সত্যিকার কবিমনের প্রকাশ বলে গ্রহণ করতে দ্বিধাগ্রস্ত। কাব্যের বয়েছে এ সার্বজনীন আবেগ। এ দুনিয়ার এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে যেখানেই মানুষ থাক না কেন—সেখানেই কাব্যের আদর হয় বলে তাকে সাম্প্রদায়িকতার স্পর্শ থেকে দূরে রাখা বাঞ্ছনীয় মনে করা হয়। ধর্মের বিষয়বস্তুর মধ্যে পার্থক্য ও বিভিন্নতা থাকা এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে বিপরীতমুখী ভাবধারা থাকায় কোনো বিশিষ্ট ধর্মের অনুসারীর মর্মবাণী অপর ধর্মের মানুষের মনে আবেগের সৃষ্টিতে সক্ষম কি না—সে সম্বন্ধে তর্কের অবকাশ রয়েছে। আবেগের বিষয়বস্তুর উপর গুরুত্ব আরোপ করলে এবং বিধ সিদ্ধান্ত অপরিহার্য বলে প্রতিভাত হয়।
তবে মানব-মানসের দিক থেকে (From the subjective standpoint) বিচার করলে বুঝতে পারা যায়, ধর্মের মধ্যে বিভিন্নতা থাকলেও ধর্মের মধ্যে রয়েছে এক মহান ঐক্য। মানবমন স্বভাবতই বহির্মুখীন এবং তার স্বাভাবিক প্রবণতার দরুনই এ বিশ্বের পশ্চাদপটে বিরাজমান আদিসত্তাকে সে জানতে চায়। জ্ঞানের এ প্রেরণাই তাকে তার সীমাবদ্ধ জীবনের পরিস্থিতি থেকে সীমাহীন সত্তার অন্বেষণে ধাবিত করে। জীবনের এ জোরালো চাহিদার তৃপ্তি সাধনে তৎপর রয়েছে বলেই মানব-মানস ধর্মমুখী। সে তৃপ্তির জন্য যে-সব পদ্ধতি গ্রহণ করা হয় অথবা যে-সব ধারণার আশ্রয় লওয়া হয়, সেগুলো ধর্মের রাজ্যে মুখ্য বিষয় নয়; মুখ্য বিষয় হচ্ছে, মনের যে আদিম চাহিদা এবং তার তৃপ্তির জন্য মানব-মানসের বহির্গমন। ধর্মীয় আবেগের পরিতৃপ্তির জন্য যে সব ধারণা গ্রহণ করা হয়, সেগুলো মানব-জীবনেরই সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ। কোথাও আদর্শকে প্রেমিক হিসাবে, কোথাও পিতারূণে কোথাও বা প্রেমিকারূপে গ্রহণ করে ধর্মীয় মানস স্বস্তি পায়। এসব আদর্শে উপলব্ধির পথ বিভিন্ন হতে পারে, তবে মানব-জীবনে যে আবেগের ফলে তাদের উৎপত্তি, তা’ এক ও অবিভাজ্য।
তবে আদর্শের সংঘর্ষের ফল এবং সে-সব আদর্শের রূপায়ণের মাধ্যমের বিভিন্নতার দরুণ অনেক সময় ধর্মীয় অনুষঙ্গ সার্বজনীনতা লাভ করতে পারে না। এজন্যই বোধ হয় কোনো কোনো মধ্যযুগীয় কবি তাদের ধর্মীয় আবেগকে মানবিকরূপ দান করেছেন, ইরানি কবি হাফিজের কাব্য-প্রতিভার বৈশিষ্ট্য এই খানেই। তিনি অতি গুঢ় আধ্যাত্মিক ভাবধারাকে অতি সহজভাবে মানব-প্রেমের প্রকাশ ভঙ্গিমায় মাধ্যমে ব্যক্ত করেছেন। তার ‘দিওয়ানের’ সর্বত্রই আপাতঃদৃষ্টিতে মানব-প্রেমেরই এক লালসাপূর্ণ অধ্যায়ের প্রকাশ পাওয়া যায়,
“প্রিয়ারে ছাড়িয়া থেকো না হাফিজ, ছেড়ো না পেয়েলা লাল এ যে গোলাপের চামেলীর দিন, এ যে উৎসব কাল…”
(তরজমাঃ সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত)
এবংবিধ উক্তির মর্মমূলে আধ্যাত্মিক সাধনার গূঢ় অর্থ থাকলেও আপাতঃশ্রুতিতে তাতে কামনাময় শারীরিক সম্বন্ধজাত আবেগের সন্ধান পাওয়া যায়। এ ধরনের সৃষ্টির উদাহরণ রয়েছে মৈথিলী কবি বিদ্যাপতির কাব্যে। তাঁর ধারণাতে শ্রীকৃষ্ণ তাঁর ঐশ্বরিকরূপ পরিত্যাগ করে কবি-জীবনের চরম সখারূপে দেখা দিয়েছেন,
“তিমির দিক ভরি ঘোর যামিনী অথির বিজুরিত পাতিয়া বিদ্যাপতি কহে ক্যায়সে গোয়াইব হরি বিনে দিন রাতিয়া।“
তবে কাব্যের বিষয়বস্তু ধর্মীয় রূপ গ্রহণ করুক অথবা মানবীয় রূপেই তা প্রকাশিত হোক, তার পশ্চাদপটে বিশিষ্ট জীবন-দর্শন থাকা অবশ্যম্ভাবী। সে জীবন-দর্শনেও পার্থক্য থাকা স্বাভাবিক। নানাবিধ পার্থক্য ও বৈশিষ্ট্য থাকা সত্ত্বেও মহাকাব্যে কতকগুলো লক্ষণ ফুটে ওঠে। তন্মধ্যে শ্রেষ্ঠ লক্ষণ হচ্ছে তার অন্তর্গত নানাবিধ ভাবধারার সমাবেশ। তাতে এমন কতকগুলো ভাবধারা বর্তমান থাকে যার ফলে তার জাতি নির্ণয় করা কঠিন হয়ে পড়ে। মানব-জীবনকে সামগ্রিকভাবে দেখার ফলে তার মধ্যে নানাবিধ ভাবধারা থাকে বর্তমান, যার ফলে তত্ত্বানুসন্ধানী দার্শনিক তার মধ্যে খুজে পান দর্শনের জটিল তত্ত্বের সমাধানের প্রয়াস, মানব-প্রেমিক তার মধ্যে আবিষ্কার করেন মানব-প্রেমের বা মানবতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।
রামায়ণে বর্ণিত রাজা রামচন্দ্রের চরিত্রে যেমন আদর্শ নরপতির উদাহরণ পাওয়া যায়, তেমনি প্রজাগণের মনোরঞ্জনার্থে সীতাকে বনবাসে প্রেরণের মধ্যে প্রজাতন্ত্রের (Democracy) আদি বীজেরও সন্ধান পাওয়া যায়। এ ক্ষেত্রে ধর্মের সঙ্গে রয়েছে মহাকাব্যের সাদৃশ্য। ধর্মের মধ্যে যেমন মানব-জীবনের নানাবিধ দিকের সন্তোষ বিধানের রয়েছে উপাদান। এ দুনিয়ার সকল ধর্মের মধ্যে সমাজ-নীতি ও রাজনীতির মৌলিকসূত্র বর্তমান। এ সব নীতিকে ধর্ম- প্রবর্তকগণ কেবল প্রচার করেই ক্ষান্ত হননি, বাস্তব জীবনেও তার রূপায়ণের জন্যও চেষ্টা করেছেন।
বৌদ্ধ ধর্মকে সাধারণতঃ অহিংসার ধর্ম বলেই গ্রহণ করা হয়, অথচ বুদ্ধদেব স্বম্বন্ধে কাহিনী প্রচলিত রয়েছে যে, তিনি ব্রাহ্মণ বৈশ্যদের ষড়ন্ত্রের ফলে ব্যবসায় ও বাণিজ্যে যে কর্ডনিং প্রথার সৃষ্টি হয়েছিল এবং যে জঘন্য প্রথার ফলে সর্বসাধারণের মানুষের জীবনে সংকট দেখা দিয়েছিল তার বিরুদ্ধে তিনি দলবলসহ যুদ্ধ করেছেন। যীশুখৃষ্ট দাসের দল নিয়ে ইহুদিদের সুদ লেনদেনের প্রতিষ্ঠান আক্রমণ করেছেন এবং হযরত মুহাম্মদ (দঃ) দাসকে মুক্ত করা তাঁর জীবনের ব্রত হিসাবেই গ্রহণ করেছিলেন। কাজেই এ সব ধর্মে জনগণের কল্যাণকে শ্রেষ্ঠ সম্মান দেওয়া হয়েছে বলে অম্লান বদনে স্বীকার করা যায়। তাই দেখা যায় পারলৌকিক মুক্তির সঙ্গে সঙ্গে ইহলোকিক কল্যাণও এ-সব ধর্মের লক্ষ্যের বিষয়।
এখানেই মহাকাব্যের স্রষ্টাগণ অপরাপর সৃষ্টিধর্মী মানুষ থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। বহুধা বিস্তৃত জীবনের নানাবিধ ভূয়োদর্শনের ফলে এদের মানস এত গভীর ও সমৃদ্ধ হয় যে, মহাসমুদ্রের মত তাতে হাঙ্গর, কুমীর, তিমি থেকে শুরু করে অতি নিরীহ ঝিনুকানিও স্থান পায়। বিচিত্র জীবনের বৈচিত্র্য প্রকাশে কৃতী বলেই তারা এ জগতে অমর হয়ে বিরাজমান।
তবে এ ক্ষেত্রে আমাদের পক্ষে স্মরণ করা কর্তব্য যে, মহাকাব্য রচনায় সফল হওয়ার পূর্বে এসব অপূর্ব প্রতিভা ও মণীষার অধিকারী শিল্পীগণ নানা স্তর পার হয়ে সেই চরমস্তরে উপনীত হন। স্বজন ধর্ম স্বভাবজাত হলেও তাকে সার্থক করে তুলতে হলে সাধনার সোপান উত্তীর্ণ হতে হয়। ইকবালকে মহাকবি বলার অর্থ এই যে, তাঁর মধ্যেও মানব-জীবনের নানাদিকের নানা প্রশ্নের সমাধানের চেষ্টা রয়েছে। সাধনার সর্বশেষ স্তরে উপনীত হওয়ার আগে তাঁকে নানা স্তর পার হতে হয়েছে।
(২)
মহাকবি ইকবালে কাব্য-পাঠে সর্বপ্রথমেই ভেসে উঠে তার প্রতি জোরালো প্রত্যয়শীলতা। সে প্রত্যয়শীলতা প্রথমদিকে আধুনিক ভাবধারা দ্বারা বিকশিত হয়েছে এবং বিকাশের ধারায় পরবর্তীকালে ধর্মীয় ধারণার দ্বারা পুষ্ট হয়ে পরিণতির দিকে অগ্রসর হয়েছে। প্রথমদিকে তাঁর ভাব প্রকাশের বাহন হিসাবে তিনি বিজাতীয় ধারণা বা সংস্কৃতিকে গ্রহণ করলেও পরবর্তীকাল তিনি সম্পূর্ণ ইসলামী সংস্কৃতির ধারণার মাধ্যমে তাঁর পরিণত বয়সের চিন্তার ফল প্রকাশ করেছেন। অবশ্য উভয় পর্যায়েই তিনি আধুনিক চিন্তাধারার সমালোচনা করে তাঁর জীবনদর্শন প্রকাশ করার চেষ্টা করেছেন। তাঁর মহাকাব্যের উপজীব্য বিষয়গুলোর মধ্যে সর্বপ্রধান বিষয়গুলো ছিলো, সৃষ্টিশীল আল্লাহ সম্বন্ধে তাঁর ধারণা, মানব জীবনের গতিশীলতা, খুদী, তকদীর ও অমরতা। এসব ধারণায় তিনি অকস্মাৎ এসে উপনীত হননি। ক্রমবিকাশের ধারায় সর্বশেষ স্তরে তাঁর মানস এ-সব ধারণার মর্ম গ্রহণে সমর্থ হয়েছে।
তাঁর মহাকাব্যের বিকাশের ধারার অনুসরণ করলে আমরা দেখতে পাই, প্রথমে তিনি জীর্ণ-শীর্ণ এ ঘুনে ধরা সমাজের নানাবিধ গ্লানিতে অতিষ্ঠ হয়ে তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছেন। হিন্দু ও মুসলিম সংস্কৃতি অধ্যুষিত এই বিশাল দেশে কোথাও প্রাণের স্পন্দন তিনি পাননি। গতানুগতিক আচার পদ্ধতির মাধ্যমে মানুষ সেই পুরাতনেরই আরাধনা করছে। তাতে বাইরের খোলাটাই বড় হয়ে দেখা দিয়েছে, অন্তরের কোনো সাড়া তাতে প্রকাশ পাচ্ছে না। সে যুগের ইকবাল মানসের পরিচয় হিসাবে নিম্নে উদ্ধৃত কবিতাকে শ্রেষ্ঠ নিদর্শন বলা যায়,
শূন্য পড়িয়া আছে বহু যুগ হতে হৃদয়ের লোকালয়
এসো এক নূতন শিবালয় এই দেশে বসাইয়া দেই,
পৃথিবীর তীর্থ হইতে উচ্চ হউক আপন তীর্থ
আকাশের বস্ত্রাঞ্চলের সঙ্গে তাহার চূড়ায় কলস মিলাইয়া দেই।
(অনুবাদ: ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ)
এ যুগেরই অপর এক কবিতায় তাঁর এ মনোভাবের আরও স্পষ্ট হয়ে প্রকাশিত হয়েছে—
ওগো ব্রাহ্মণ!
মন্দিরের দেবতা তোর পুরানো হয়ে গেছে
নিজেদের মধ্যে ভেদাভেদ—
এতো তুই তার কাছেই শিখেছিস
খোদাই শিখিয়েছেন ওয়াইজকে ঝগড়া বিবাদ করতে—
মসজিদ মন্দির কোনটাতেই আমার ভক্তি নেই—
ব্রাহ্মণ মোল্লা দুই-ই ছেড়েছি আমি
তুই ভেবেছিস পাথরের মন্দিরে দেবতা আছে
জন্মভূমির প্রতি ধূলিকণা কিন্তু আমার দেবতা—
নুতন শিবালয় তৈরি করব প্রাণের বশত ভূমিতে
উদার আকাশে মেলে দেবে এ চূড়ার পাখা
সকল তীর্থের সেরা তীর্ঘ হবে এই—
মানুষের মুক্তি আনবে প্রেমের ভিতর দিয়ে—
(নয়া শিবালয়, অনুবাদ- ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ)
এক্ষেত্রে স্পষ্টই বুঝতে পারা যায় তথাকথিত হিন্দু বা মুসলিম কোনো সংস্কৃতিতেই তাঁর আস্থা ছিল না। তিনি ছিলেন জীবনের অন্বেষণে ধাবমান। সত্যিকার জীবন কোথায়—কিভাবে তাকে আবার ফিরে পাওয়া যায়—এ-ই ছিল তাঁর গবেষণার বিষয়বস্তু। এ যুগের অপর একটি কবিতায় এ ভাবটি সুপরিস্ফুট। ‘চাঁদ’ নামক কবিতায় তাঁর জীবনের সেই অধ্যায়ের স্পষ্ট চিত্র পাওয়া যায়—
কাহারে খুঁজিছ তুমি, কোন সে সুন্দর
ফিরিছ তালাশ করি আমারি মতন?
অনন্ত আলোকে যার মানব-অন্তর
আলোকিত প্রভাসিত প্রদীপ যেমন।’
(ইকবাল চয়নিকা— বাঙ-ই-দারা; তরজমা- মীজানুর রহমান)
এ পর্যায়েই তাঁর মানসে স্বদেশ-প্রেম ছিল অগ্নি-শিখার মত জ্বলন্ত। অতি আধুনিক যুগে স্বদেশ-প্রেমকে অনেক মনীষীই মানব জীবনের ঐক্য প্রতিষ্ঠার মহা প্রতিবন্ধকরূপে গণ্য করছেন। বার্ট্রান্ড রাসেল স্বদেশ-প্রেমের জন্ম ইতিহাস বিশ্লেষণ করে প্রমাণ করেছেন যে, তার বয়স খুব বেশী নয়। জোয়ান-অব-আর্ক কর্তৃক তা সর্বপ্রথমে ফ্রান্সে প্রতিষ্ঠিত হয়। নেপোলিয়ন তা জার্মানীতে আমদানী করেন। মেটারনিক তাঁর বীজ ইটালীতে বপন করেন এবং শেক্সপীয়রের মতল এমন মধুর ভাষায় আর কেউই এ বিষ পরিবেশন করেননি। স্বদেশ-প্রেমের প্রথমদিকে থাকে আত্মরক্ষামূলক মনোবৃত্তি এবং পরিশেষে তাতে দেখা দেয় আত্ম-প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে শোষণের প্রবৃত্তি।
ভৌগলিক পরিবেশ, রক্ত, ভাষা, অর্থনৈতিক সংস্থা প্রভৃতি থেকে মানুষের মনে জাতীয়তাবোধের প্রতিষ্ঠা হয়। এ জাতীয়তার সর্বপ্রধান লক্ষ্য অপর জাতির অধিকার থেকে আপনাকে বাঁচিয়ে রাখা। আবার এভাবে জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় সক্ষম হলে পরবর্তীকালে তাকে মানুষের শ্রেষ্ঠ সমাজ মনে করে এবং অপরাপর জাতির রক্ত মোক্ষণ করে আনন্দ পাওয়াটা তাদের স্বভাবে পরিণত হয়। এঙ্গেলস সেকসনস, ব্রিটন প্রভতি জাতির সমবায়ে যে বিটিশ জাতি বা ন্যাশন গড়ে ওঠে, তার মূল কারণ ছিলো নরম্যানসদের সাগরের অপরপারের অপরাপর জাতি থেকে নিরাপদ হওয়ার জন্য সংঘবদ্ধ হওয়ার প্রয়োজন বোধ। আবার সংঘবদ্ধ হয়ে আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করার পর এ ব্রিটিশ জাতিই এ দুনিয়ার সুদূর প্রান্তে কত শত জাতিকে অধীনতা স্বীকারে বাধ্য করে শতাব্দীর পর শতাব্দী শোষণ করে নিঃশেষিত করে ফেলেছে, তার ইয়ত্তা নেই।
ইকবালের জন্ম ইংরেজ শাসনের চূড়ান্ত পর্যায়ে। এদেশবাসীকে ইংরেজরা কি অমানুষিকভাবে শাসন ও শোষণ করতো, তা তিনি মর্মে মর্মে অনুভব করেছিলেন। কাজেই স্বদেশ-প্রেমের প্রাথমিক পর্যায়ের অনুপ্রেরণা তিনি লাভ করেছিলেন। বর্তমানকালের স্বদেশ-প্রেমের যে বিষময় ফল এ দুনিয়ার সর্বত্র দেখা দিচ্ছে তা’ও তিনি পরিণত বয়সে উপলব্ধি করেছিলেন এবং সে পর্যায়ে তাঁর কাব্যে যে বিদ্রোহ ঘোষিত হয়েছে, এবং তা বিশ্ব-সাহিত্যের ইতিহাসে অনন্য। আলোচিত পর্যায়ে তাঁর মনে স্বদেশ তথা ভারতীয় প্রেম তাঁকে কীভাবে উজ্জীবিত করছে তার প্রমাণ পাওয়া যায় তারানায়ে হিন্দ, মেরা ওয়তান ওহি হ্যায়, হিন্দুস্থান হামারা প্রভৃতি কবিতায়। তারানায়ে হিন্দতে তিনি গেয়েছেন—
ধর্ম কখনও শিখায় না শত্রুতা করিতে
হিন্দি আমি, হিন্দুস্তান স্বদেশ আমার—
(তরজমা: ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ)
অথবা হিন্দুস্তান হামারাতে গর্ব করেছেন—
সারা জাহাঁসে আচ্ছা হিন্দুস্তান হামারা
তবে স্বদেশ-প্রেম ইকবাল কাব্যের চূড়ান্ত নয়। এ স্তর তিনি অনায়াসে পার হয়েছেন তার অন্তর্নিহিত আশাবাদের উজ্জ্বল আলোকে। যে চিরন্তন সত্যের জন্য তাঁর এ যাত্রা এবং যে সন্ধানের আভাস আমরা পূর্বে পেয়েছি তাতে সফলতার আশাবাদ তিনি সর্বদাই পোষণ করতেন—
কিন্তু তবু, ভ্রাম্যমাণ চিরকাল জীবনের জাহাজ
মানবের দৃষ্টির আড়ালে—
কখনো হারিয়ে যায়, হয়ত বা যেতে পারে তবু
ধ্বংস তার নেই কোনো কালে—
(ইকবাল চয়নিকা—রাভীতীরে; তরজমা— মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ)
পরবর্তীকালে যে অমরতার বাণী তিনি মানবকে শুনিয়েছেন তার সূত্রও এখানে পাওয়া যায়—
জীবন জাহাজ চিরকাল ভ্রাম্যমাণ। সে কখনও বা হারিয়ে যায়, কখনও বা দৃষ্টির বাইরে চলে যায়, তবে তার ধ্বংস নেই কোনোকালে।
দ্বিতীয় পর্যায়ের কবিতার মধ্যে বিশেষভাবে তাঁর তত্ত্বজ্ঞানের প্রবণতার নিদর্শন পাওয়া যায়। অবিনশ্বর জীবনের যে ধারণা পূর্বতন পর্যায়ে পাওয়া যায়, তাই আরও পাকা দানা বেঁধেছে তার মানসে। এ পর্যায়েই বিশেষভাবে স্থিতির নিন্দা ও গতির উচ্চ প্রশংসা তাঁর কাব্যে পরিলক্ষিত হয়–
গতি হইতে জগতের জীবন
ইহাই ইহার প্রাচীন রীতি
এই পথে অবস্থিতি লুক্কায়িত
চলনশীল নিষ্কৃতি পাইয়াছে,
যে একটু থামিয়াছে বিধ্বস্ত হইয়াছে।
এ গতিবাদ বা DYNAMISM জগতের চিন্তাধারার ইতিহাসে নতুন নয়। গ্রীক দর্শনে হিরাক্লাইটাস এ-গতিবাদ প্রথমে প্রচার করেন। তাঁর চিন্তাধারাকে ইলিয়াটিক (ELEATIC) চিন্তাধারার ব্যত্যয় বলা যায়। ইলিয়াটিক চিন্তার মর্ম কথা হচ্ছে, গতিকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করে এ দুনিয়ায় অপরিবর্তনশীল সত্তাকে প্রতিষ্ঠা করা। মননশীলতার দিক থেকে বিচার করলে গতিশীলতাকে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জ্ঞানের ভ্রান্তি বলেই ধরে নিতে হয়। এ চিন্তাধারার প্রতিনিধি পারমিনাইডিসের (Parmenides) প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল—চিন্তা ও স্থিতির ঐক্য। জিনো (Zeno) গতির অবাস্তবতা প্রমাণ করতে গিয়ে দেখিয়েছেন যে, কোনো গতিশীল তীরকে এক বিন্দু থেকে অন্য বিন্দুতে যেতে হলে তার মধ্যবর্তী অনন্ত বিন্দুর ভিতর দিয়েই যেতে হবে। অনন্ত বিন্দুর মধ্যে দিয়ে তার পক্ষে যাওয়া সম্ভবপর নয়। হিরাক্লাইটাস এ চিন্তার প্রতিপক্ষীয় মতবাদ প্রচার করেন। পরস্পর বিরোধী বস্তুর দ্বন্দ্বই সকল বস্তুর প্রকৃত সত্তা এবং তার প্রকৃত স্বরূপ প্রকাশ পাচ্ছে অগ্নিতে। তবে এ গতির কোনো লক্ষ্য নেই।
অতি আধুনিক দর্শনে এ গতিবাদ প্রচার করেছেন ফরাসী দার্শনিক বের্গসোঁ (Bergsou)। ডারউইন বা লেমার্ক বর্ণিত জীব-জগতের বিবর্তনের ব্যাখ্যার সমালোচনা প্রসঙ্গে বের্গসোঁ মন্তব্য করেন, ওঁরা বাইরের দিক থেকে ক্রমবিকাশের ধারাকে বর্ণনা করেছেন। ওঁরা দেখিয়েছেন কিভাবে জীব-জগতে বিবর্তন হচ্ছে—তবে কেন এ বিবর্তন হচ্ছে এ প্রশ্নটা ওঁরা তোলেননি। তাঁর মতে, এ বিবর্তনের কারণ হচ্ছে তার পশ্চাতে রয়েছে এমন একটি শক্তি যা নিত্যনূতন নব নব সৃষ্টি করেই চলে। এ শক্তির ধাতুই হচ্ছে নব নব সৃষ্টিতে পর্যবসিত হওয়া। এজন্যই কালকে বের্গসোঁ বলেছেন বিশ্বসত্তা। কালে যেভাবে কোন স্থিতি নেই—গতিই একমাত্র সত্য—তেমনি এ বিশ্বে স্থিতিশীল বলে কোনো কিছুই নেই। কালের বা বিশ্বসত্তার স্বাভাবিক ধর্ম গতিশীলতা হলেও—তাতে কোন লক্ষ্য নেই। অর্থাৎ কোনো আদর্শের বাস্তবায়নে বা কোনো লক্ষ্যের পানে পৌঁছার জন্য সে গতিরও কেউ নিয়ন্ত্রণ করেনি। গতির ফলেই ক্রমবিকাশের ধারায় নিত্য নতুন নানা মূল্যমানের সৃষ্টি হচ্ছে।
ইকবাল গতিবাদকে স্বীকার করে তাকে সংশোধিত আকারে প্রকাশ করেছেন। তাঁর মতবাদ অনুসারে ক্রমবিকাশের ধারার লক্ষ্য হচ্ছে মানুষের সৃষ্টি এবং তার মাধ্যমে প্রকৃত জীবনের সন্ধান। বিশ্ব প্রকৃতিতে মানুষের উৎপত্তি এক মহান ব্যাপার। মানুষকে হাদিসে কুদসিতে বলা হয়েছে আল্লার প্রতিনিধি বা খলিফা। সে খলিফার প্রকৃত কর্তব্য হচ্ছে এ দুনিয়ায় আল্লার রাজত্বের প্রতিষ্ঠা করা। কাজেই সেই আল্লার রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাকল্পেই বিবর্তনের ধারা ছুটে চলেছে এবং মানুষের মাধ্যমেই তা এ দুনিয়ার বুকে বাস্তবায়িত হবে। এই ভাবধারাকেই ইকবাল প্রকাশ করেছেন তাঁর অনবদ্য ভাষায়—
ঝরণা চায় নদীতে মিশতে
নদী চায় সমুদ্রে মিশে যেতে
সমুদ্রের ঢেউ কামনা করে চাঁদের জ্যোৎস্নাকে
জীবন রহস্যের সন্ধান নাও খিজিরের কাছে থেকে
দুনিয়ায় কারোর আশাই তো পূর্ণ হলো না।
(কোশেশ-ই-না তামাম; অনুবাদঃ ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ)
এখানে লক্ষ্যণীয় বিষয় এই যে, যদিও ইসলামী ভাবধারায় খিজির আলায়-হিস-সাল্লাম এখনও জীবিত এবং তাঁর কাছে থেকেই জীবন-রহস্যের সন্ধানের ইকবাল তাগিদ করছেন, তবু শেষ পংক্তিতে তিনি স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করেছেন যে কারোর আশাই তো পূর্ণ হলো না। এখানে স্পষ্টই বুঝতে পারা যায় খিজিরের কাছে জীবনরহস্যের সন্ধান পেলেও কারো আশাই পূর্ণ হবে না। সারাটা জীবনব্যাপী তাকে উপলব্ধি করার জন্য অন্বেষণ করতে হবে।
তৃতীয় পর্যায়ে কবি-মানস আরও সমৃদ্ধতর হয়ে দেখা দিয়েছে। এ পর্যায়ে তিনি তার বিখ্যাত অভিযোগমূলক কাব্য শেকোয়া ও তার জওয়াব প্রকাশ করে। মানবাত্মা সম্বন্ধে তাঁর ধারণাও আসরারে খুদীর মধ্যে ব্যক্ত রয়েছে। শেকোয়া বা অভিযোগমূলক কাব্যের প্রবর্তন এ-দুনিয়ার ইতিহাসে নতুন নয়। ইকবালের বহু পূর্বে ওমর খৈয়াম তার অপূর্ব বচনভঙ্গিমায় মানুষের পক্ষ থেকে অভিযোগ করেছেন। সাধারণভাবে মানুষকে তাঁর পাপের জন্য দায়ী করা হয়, কিন্তু পাপের সৃষ্টি তো খোদা আল্লাহর দ্বারাই হয়েছে। কাজেই মানুষ সর্বতোভাবে ক্ষমার যোগ্য—
পাপের কালো মূর্তি নিয়ে জীব জগতে ঘুরছ হায়,
মানুষ তোমায় করছে ক্ষমা তুমিও দেব ক্ষমিয় তার।
(রুবাইয়াতে ওমর খৈয়াম, তরজমা: কান্তি চন্দ্র ঘোষ)
অপরদিকে রবীন্দ্রনাথ অভিযোগ করেছেন-
এ দুনিয়ার সৃষ্টির উপাদান শুধু মৃত্তিকা। একে নন্দনকানন করে গড়ে তোলেননি ভগবান। সে গড়ার সম্পূর্ণ ভার দেওয়া হয়েছে মানুষকে, অথচ মানুষের হাতে স্বাভাবিক কোনো যন্ত্র নেই যে, তার মাধ্যমে সে এ মাটির পৃথিবীকে সুন্দর ও শোভন করে তুলে। তবু সে ভার মানুষের উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে—
তুমি তো গড়েছো শুধু এ মাটির ধরণী
তোমার মিলাইয়া আলোকে আঁধার
শুন্য হাতে সেখা মোরে রেখে
হাসিছ আপনি সেই শুন্যের আড়ালে
গুপ্ত থেকে দিয়াছ আমার পরে ভার
তোমার স্বর্গটা রচিবার।
এ-সব অভিযোগকে সার্বজনীন অভিযোগ বলা হয়। এ দুনিয়ার সকল মানুষের প্রতিনিধি হয়েই ওমর খৈয়াম বা রবীন্দ্রনাথ এ-সব অভিযোগ করেছেন। ইকবাল অভিযোগ করেছেন এ দুনিয়ার এ বিশিষ্ট মতবাদে বিশ্বাসী এক মানব গোষ্ঠীর পক্ষ থেকে। তবে এ ক্ষেত্রে ভাববার বিষয় এই, মুসলিমদেরকে একটি আদর্শবাদে প্রত্যয়শীল দল বলেই তিনি গ্রহণ করেছেন। ইসলামের ঐতিহ্যের আলোচনা প্রসঙ্গে দেখা যায়, আদি যুগ থেকেই মুসলিমেরা এ দুনিয়ায় আল্লার ওহদানীয়ত বা ঐক্য এবং সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য বিরুদ্ধমতবাদী লোকের সঙ্গে সংগ্রাম করেছে। বাইবেলের ওল্ড টেস্টামেন্টে ও আল কুরআনে সে সংগ্রামের কাহিনী লিপিবদ্ধ রয়েছে। হযরত ইব্রাহিম খলিল থেকে এ দুনিয়ায় আল্লাহর ওহদানীয়ত ও সার্বভৌমত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার সূচনায় কাফের বাদশা নমরুদের শত্রুতা থেকে যে সংগ্রামের সূচনা হয়েছিলো এবং যে সংগ্রাম এখনও চলেছে অত্যাচারী রাজা বাদশাহ বা তথাকথিত জননেতার বিরুদ্ধে, সে সংগ্রামে অংশগ্রহণকারী একটি বিশিষ্ট মানব গোষ্ঠীর প্রতিনিধি হয়েই তিনি এ অভিযোগ করেছেন।
এ মানবগোষ্ঠীর জীবনে কোনো বংশের বা গোত্রের প্রতিষ্ঠা বা স্বার্থ আদায় করার প্রবৃত্তি ছিলো না। এরা ছিলো এক বলিষ্ঠ জীবন-বোধে অনুপ্রাণিত। এ দুনিয়ায় কোনো বক্তির নয়, কোনো জাতির নয়, কোনো অধিপতির নয়— খোদ আল্লাহর সার্বভৌমত্ব ও মানুষের প্রতিনিধিত্ব প্রতিষ্ঠায় এরা ছিল উন্মুখ। ওরা চেয়েছিল আল্লার সার্বভৌমত্বের প্রতিষ্ঠা করে এ দুনিয়ার সম্পদ সমানভাবে ভোগ করার নীতি প্রতিষ্ঠা করতে। এজন্যেই পরবর্তী-কালে ওরা কেবল বিধর্মীর সঙ্গেই যুদ্ধে লিপ্ত হয়নি, বরং তথাকথিত মুসলিম নামধারী শাসক ও শোসকদের বিরুদ্ধেও সংগ্রামে জান কোরবান করেছে। কারবালা প্রান্তরে ইয়াজিদের বিরুদ্ধে ইমাম হোসেনের (রাঃ) জেহাদ বা জাহাঙ্গীরের ইসলাম-বিরোধী কার্যকলাপের প্রতিরোধকল্পে মুজাদ্দিদে আলফে সানী শেখ আহমদ সিরহিন্দের বিদ্রোহও সেই মানসিকতার পরিচায়ক। কাজেই এ স্থলে মুসলিম শব্দ ব্যাপক বা সাধারণ অর্থে ইকবাল ব্যবহার করেননি। এক বিশিষ্ট জীবনদর্শনে প্রত্যয়শীল আদর্শবাদী এক মানুষ গোষ্ঠী সম্বন্ধে তিনি এ শব্দ প্রয়োগ করেছেন। তার ব্যাখ্যার কারণ স্বরূপ বলা যায়, যে জাতি সারাজীবন ভরে আল্লার আধিপত্য ও সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠাকল্পে অবিরাম বিরুদ্ধবাদী প্রতিপক্ষীয় শক্তির সঙ্গে যুদ্ধ করেই গেলো, তার পতন বাস্তবিকই ইনসাফের দিক থেকে সহনীয় নয়—
কেহ কি তোমার মহিমার লাগি করেছিল তেগ উত্তোলন
বিকল তোমার সৃষ্টি যন্ত্রে বাঁধিল নিয়মে কোন সে জন?
তব নাম লয়ে বুজিয়াছি একা আমি মুসলিম অমিত বল
কখানা ভুলতে মেতেছি সমরে, আলোড়িয়া কভু সিন্ধু জল।
(মোহাম্মদ সুলতান; শোকোয়ার তরজমা থেকে)
তার প্রতিদানে আল্লাহ মুসলিমদের কি দান করেছেন? আপাতদৃষ্টিতে কিছু নয়। বরং যারা তাঁর নামও শ্রদ্ধার সঙ্গে উচ্চারণ করে না তাদের তরেই বর্ধিত আল্লার যত নিয়ামত কণা—
নহে অভিযোগ দিয়াছ বলিয়া ধনাগার করি পূর্ণ তার
তব সনে যার কহিতেও কথা নাহিক চিহ্ন ভদ্রতার
আফসোস হায় হুরীসহ তারা করিছে রম্য হর্ম্যে বাস
মুসলিম তরে রাখিয়াহ বাকী কেবল হুরীর প্রাপ্তি আশ।
(তরজমাঃ মোহাম্মদ সুলতান)
মুসলিম জীবনের এতো সব দৈন্যের মধ্যেও কবি তাঁর আশ্যবাদ বর্জন করেননি। জওয়াবে শেকোয়াতে মুসলিম জীবনের এ অধঃপতনের জন্য আল্লাহ খোদ মুসলিমদেরই দায়ী করেছেন এবং কোন পদ্ধতিতে তারা আবার তাদের লুপ্ত গৌরব ফিরে পেতে পারে তার পথও দেখিয়েছেন—
ধর্মযাজক বিশ্বাসহীন ধর্মে নাহিক আস্থা হায়
বিদ্যুৎ সম নাহি সে স্বভাব নাহি উষ্ণতা বক্তৃতায়,
বেঁচে আছে শুধু আজানের প্রথা কোথা সে বেলাল ভক্তিমান
দর্শন আজি পুঁথির বিধান গাজ্জালীর নাই শিক্ষাদান। (পূর্বোক্ত)
তব মুসলিম জীবনে নিরাশাবাদের কোন স্থান নাই—
জ্ঞানের বর্মে শোভিত অঙ্গ প্রেম-তরবারি হস্তে ঝলে
হে মোর বিরাগী তব খেলাফত রহিবে অটুট বিশ্বতলে
বহ্নিতুল্য তকবীর উজলিবে সারা সৃষ্টি খান
তদবীর হতে তকদীর তব হওগো সাচ্চা মুসলমান। (পূর্বোক্ত)
এখানেও লক্ষণীয় বিষয়, এই পরবর্তীকালে তকদীর সম্বন্ধে যে মতবাদ তিনি প্রকাশ করেছেন তার ইঙ্গিত এ কবিতায় রয়েছে। মানুষ নিয়তির হাতের ক্রীড়নক নয়—সে তার ভাগ্য আপনি সৃষ্টি করে। বিকাশের ধারায় তার চেষ্টাই তাকে সফল করে। এ পর্যায়েই কবি-জীবনে খুদি তত্ত্ব পূর্ণ বিকাশ লাভ করে। খুদি তত্ত্বের একটি বিশিষ্ট পংক্তি এখন পাকিস্তানের সর্বত্রই উচ্চরিত হয়—
“খুদি কো কর বুলন্দ কে হর তকদীর সে পহেলে খুদ খোদা বান্দা সে পুছে কে বাতা তেরি রিজা কিয়া হ্যায়…”
এ কোন জাতীয় খুদি?
সাধারণতঃ ইউরোপী ধারণায় Indivdualism বা ব্যাষ্টিবাদ বলে যে মতবাদ প্রচলিত রয়েছে, এ খুদিকে তারই অপর এক নাম বলে ভুল ধারণার সৃষ্টি হতে পারে। ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদ নামেও এ মতবাদ পরিচিত। ফরাসী দার্শনিক রুশো ও ইংরেজ দার্শনিক জন লক এ-মতবাদকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য আজীবন চেষ্টা করেছেন। এ মতবাদকে সমষ্টিবাদ বা Collectivism-এর বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ বলা যায়। পূর্বেই বলা হয়েছে, আধুনিক যুগের বিশেষত্ব হচ্ছে নির্বিশেষবাদ (Absolution) ও সংঘবাদের (Collectivism) বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণাতে। পূর্বেই বলা হয়েছে, প্রাচীনকালে গ্রীকদের ছোটো ছোটো রাষ্ট্রে সংঘবদ্ধ বলে বিশেষ কিছুই ছিলো না। ব্যাষ্টিকে স্বাধীনভাবে তার মতামত প্রকাশ করার অধিকার দেওয়া হতো। যদিও কোনো কোনো ক্ষেত্রে নির্যাতনেরও নজির পাওয়া যায়, তবু মোটামুটিভাবে মানুষের চিন্তার ও বাক্যের স্বাধীনতা ছিল বলতেই হবে।
রেনেসাঁর পর থেকেই ব্যক্তিস্বাধীনতার নীতি স্বীকৃতি লাভ করে এবং মধ্যযুগীয় ধর্ম রাজ্যের পোপের আধিপত্য বা চার্চের শাসন থেকে মানুষ মুক্তি লাভ করে, আপনাদের স্বাধীন চিন্তাপ্রসূত মতামত প্রকাশ করার বাসনা পোষণ করে। এ মতবাদের পোষকতায় বলা হয় মানুষ তার স্বকীয় ভুয়োদর্শনের ফলে যে-মতবাদ গঠন করতে সমর্থ হয় তাই তাকে প্রকাশ করার স্বাধীনতা দিতে হবে। ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানের উপাদান বাইরের পৃথিবী থেকে আহরিত হয় এবং সে-সব উপকরণের ভিত্তির উপর আমাদের মানস একটা সৌধ গঠন করে। সে সৌধের মধ্যে গুরু বাক্য বা আপ্তবাক্যের (Authority) কোন স্থান নাই। প্রাকৃতিক রাজনীতিকে স্বীকার করতে বাধ্য হলেও মানুষ অপর মানুষের দ্বারা প্রতারিত হতে বা প্রচলিত কোনো নীতি মানতে বাধ্য নয়। সে তার নিজের সুখ- সুবিধার প্রতি লক্ষ্য রেখে আপন মতবাদ গঠন করতে পারে।
প্রকৃতপক্ষে, ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানকে মানব-জ্ঞানের মূল উপকরণ বলে স্বীকার করলে মানুষের পক্ষে আপনার সুখ-শান্তির আকাঙ্খা ছাড়া আর কোনো কিছুই কাম্য হতে পারে না। কাজেই ব্যাষ্টিবাদ তার পরিণতিতে সুখবাদ বা Hedonism-এ পরিণত হয়। জন লক যে ধারণা প্রচার করেছিলেন, তার পরিণতিতেই ইংল্যান্ডে সুখবাদ ব্যাপকভাবে প্রচারিত হয় এবং জন স্টুয়ার্ট মিল ও বেনথাম তাকে একটু পরিবর্তিত আকারে প্রচার করে তাঁদের দেশের তথা তৎকালীন সভ্যজগতের প্রশংসা লাভ করেন। প্রাচীন কালে গ্রীকদের মধ্যে যে সুখবাদ প্রচলিত ছিলো, তাতে ব্যাষ্টির পক্ষে সর্বতোভাবে তার নিজের সুখস্বাচ্ছন্দ্যই কামনা করার নীতি গৃহিত হয়েছিলো। মিল ব্যাষ্টির নিজস্ব সুখের স্থলে নীতি হিসাবে প্রচুরতম লোকের প্রভুততম উপকার (Greatest good of the greatest number)-কে মানব জীবনের লক্ষ্য হিসাবে গ্রহণ করেন। এতে ন্যায়শাস্ত্রের সুস্পষ্ট নীতি লঙ্ঘিত হয়েছে। তা দর্শনের ছাত্র মাত্রই অবগত আছেন। প্রত্যেকে তার সুখ চায়, কাজেই সকলেই সকলের সুখ চায়, একটা মস্ত বড় তর্ক শাস্ত্রীয় ফাটলের উপর প্রতিষ্ঠিত।
জন লকের ধারণা ছিলো মানুষ একক হিসাবেই জন্মগ্রহণ করে। একা তার পক্ষে এ জীবনে টিকে থাকা সম্ভবপর নয়, তাকে বাধ্য হয়ে অপরের সঙ্গে যুক্ত হয়ে সমাজ গঠন করতে হয়। এক্ষেত্রে তার মননশীলতার দ্বারা চালিত হয়েই সে সমাজ গঠনে অগ্রসর হয়। রুশো তার বিখ্যাত বাণীতে বলেছিলেন- Man is born free but everywhere he is in chains. মানুষ স্বাধীন হয়েই জন্মগ্রহণ করে তবে সবখানেই সে বন্দী। তার ধারণা ছিলো লকের ধারণারই অনুরূপ। মানুষ এক জন্মায় এবং ব্যাষ্টি সমাজের আদি সংখ্যা, তবে তার নানাবিধ প্রক্ষোভ (emotion) অপরের সঙ্গে যুক্ত হতে বাধ্য করে। বাধ্য হয়েই সে তার পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র প্রভৃতি গঠন করে বটে, তবে যতই সে এসব সংস্থা গঠনে অগ্রসর হয়, ততোই সে তার জন্মগত স্বাধীনতা বিসর্জন দিতে বাধ্য হয়। জন লক ও রুশোর মতবাদের মধ্যে পার্থক্য শুধু এইখানেই। লক মানুষকে বৃদ্ধি-প্রধান আর রুশো প্রক্ষোভ-প্রাণ বলেছেন। মানুষ স্বভাবতই আত্মকেন্দ্রিক হলে তার পক্ষে নিজের সুখ-সুবিধার আদায় করা বা সে-সবের জন্য প্রাণপণ করেও চেষ্টা করা মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক বৃত্তি ছাড়া কিছুই নয়।
বাক্তি স্বাতন্ত্রবাদের অপর এক উদাহরণ পাওয়া যায় জার্মান মনীষী নীটশের চিন্তাধারায়। তার ধারণা ছিলো জ্ঞান অর্জন মানুষের জীবনের লক্ষ্য নয়, উপমা মাত্র। জ্ঞানের মাধ্যমে মানুষ জীবন-আহবে (Struggle for existence) টিকে থাকরে পারে। জ্ঞান মানুষের পক্ষে জীবন-যুদ্ধে টিকে থাকার অস্ত্রবিশেষ। এজগতে কেবল শক্তিশালীই টিকে থাকে। যারা পঙ্গু, যারা বিকলাঙ্গ তারা অচিরেই ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। কাজেই, মানুষের শক্তি আহরণ করা উচিত এবং এমন সব গুণের অধিকার হওয়া উচিত যাতে সে মহামানবে পরিণত হতে পারে। শক্তির অধিকারী হতে হলে আমাদের নৈতিক ধারণার পরিবর্তন করতে হবে। ঐতিহ্যের দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করে খৃষ্টান-জগৎ প্রেম, দয়া, মমতা প্রভৃতিকে শ্রেষ্ঠ গুণাবলী বলে স্বীকার করেছে। প্রকৃতপক্ষে এগুলো দাস জাতির গুণাবলী। বীরের গুণাবলী হচ্ছে সাধারণ মানুষ থেকে উর্ধ্বে আরোহণ করার শক্তিমত্তা। সর্বসাধারণ মানুষ অতি মানুষের কাছে যন্ত্র সদৃশ। ক্রমবিকাশের ধারায় অনিবার্যভাবে অতিমানুষের সৃষ্টি হচ্ছে।
নীটশের ভাষ্য থকে বুঝা যায়, তিনি হিটলার বা মুসোলিনীর মত নাৎসী ধারাকেই অতিমানব বলে ধারণা করেছিলেন এবং ক্রমবিকাশের গতি যে ঐরূপ মানুষের সৃষ্টিতে তা তিনি তাঁর দিব্যচক্ষুতে দেখেছিলেন। ইকবাল খুদির বিকাশ বলতে লকের ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদকে বা রুশোর ব্যাষ্টিবাদকে ধারণা করেননি। নীটশের মত অতি পাষণ্ড অতি মানুষ তৈরির কোন পরিকল্পনাও করেননি। তাঁর খুদির অর্থ ছিল মানব-জীবনে আল্লাহর যে-সব গুণাবলী রয়েছে সে-সব রহমানী গুণাবলীর বিকাশ শয়তানী গুণাবলীর বিকাশ নয়।
এ সম্বন্ধে তাঁর চিন্তার অনুসরণ করতে হলে তাঁর পূর্ববর্তী চিন্তানায়ক অপর মহাকবি জালালউদ্দিনের অহমবাদের আলোচনা করতে হয়। জালালউদ্দিনের চিন্তাকে গ্রীক বা ভারতীয় চিন্তার তীব্র প্রতিবাদ বলা হয়। থেলিস (Thales) থেকে গ্রিক চিন্তাধারার সূচনা হয় এবং তার পূর্ণ পরিণাম প্লেটোর দর্শন। এরিস্টটল প্লেটোর নানাবিধ ভাবধারার সামঞ্জস্য বিধান করেছেন। এ চিন্তায় নির্বিশেষই চূড়ান্ত স্থান লাভ করেছে প্লেটোর কাছে।
এরিস্টটল নির্বিশেষকে বিশেষের মধ্যে রূপায়িত করার চেষ্টা করেছেন, তবু মর্যাদার দিক থেকে নির্বিশেষই উচ্চ স্থানের অধিকারী বলে পরিগণিত হয়েছে। প্লেটো মানবাত্মার অমরত্ব স্বীকার করেছেন এবং নির্বিশেষের সঙ্গে তার যোগসূত্রের জন্য এ জীবনে কীভাবে মানবাত্মা অধীর আগ্রহ প্রকাশ করে তাও চমৎকার ভাষায় বর্ণনা করেছেন। তবে এক্ষেত্রে গরজটা মানবাত্মার দিক থেকেই প্রকাশ পায়, নির্বিশেষ এসে স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে মানবাত্মার সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হয় না। ভারতীয় দর্শনেও তেমনি দেখা যায়, শংকরাচার্য-কৃত বেদান্ত ভাষ্যে ব্রহ্মকেই চরম স্থিতি বলে গণ্য করা হয়েছে। জ্ঞানের মাধ্যমে মানবাত্মা সে ব্রহ্মেই আপনার চরম স্থিতি খুঁজে পায় এবং এতে তার মোক্ষ লাভ হয়। কাজেই গ্রীক দর্শনের মত ভারতীয় দর্শনেও ঐক্য চেতনা মানব-আত্মা থেকেই আসে এবং ব্রহ্ম-জীবনে স্থান লাভ মানব-জীবনের চরম ও পরম কার্য। এ সব চিন্তার প্রতিবাদ হিসাবে রুমী ঘোষণা করেন মানবাত্মা এক ও অবিভাজ্য। এ সৃষ্টির বিভিন্ন স্তর মানব জীবনেরই বিভিন্ন পর্যায়ের প্রকাশ। তার এ অহমবোধকে তাই দার্শনিক জগতের এক অভিনব অবদান বলা যায়। কি উদাত্ত স্বরে রুমী তা এ আত্মচেতনা প্রকাশ করেছেন—
মৃত্তিকার অন্ধকার তলে
আমার সত্তা ছিল মিশে
প্রস্তর আর লৌহ পিণ্ড সাথে
স্তব্ধবাক বর্ণ, গন্ধ হীন,
তার পর একদা প্রভাতে
প্রাণের স্পন্দন এলো
মাটির আধারে
আমার সত্তা পেল রূপ রস প্রাণ
বিচিত্র রঙের ফুলে হেসে উঠিলাম
প্রাণ পেল গতি আর
মাটির বাঁধন গেল টুটে
শুরু হল ভ্রাম্যমান জীবনের
পথ পরিক্রমা
সন্তরণ, উড্ডয়ন
হামাগুড়ি আর পায়ে চলা
শেষ হলো
শুরু হলো আরেক জীবন
আমার সত্তা পেল নবতর রূপ
দৃষ্টি পেল—যে দৃষ্টিতে এসে
বিশ্বের রহস্য দিল ধরা;
এই দৃষ্টি মানুষের
…..এই দূর আকাশের পারে মৃত্যুহীন
ফেরেশতার লোকে আরো দূরে রাত্রিদিন
জন্ম আর মরণের বাহিরে
দৃশ্য অদৃশ্য আর সকল অস্তিত্ব যেখানে
একাকার লীন হয়ে গেছে
আমার গন্তব্য সেই মৃত্যুহীন অমৃতের পানে।
এই দর্শনের ভিত্তিতেই ইকবাল তার খুদি-তত্ত্ব প্রচার করেছিলেন। যে সত্তার সর্ব প্রথম প্রকাশ মৃত্তিকার অন্ধকার তলে এবং বিবর্তনের ধারায় যে সত্তার কাছে বিশ্বের রহস্য ধরা দিয়েছে- সে সত্তার অধিকারেই সব। রুমীর অনুসরণ করে ইকবাল সে সত্তাকে মানব জীবন থেকে পৃথক কোনো সত্তা বলে স্বীকার করেননি। সেই সত্তাকে উপলব্ধি করার জন্য সাধনা করবার জন্যও তিনি কাউকে উপদেশ দেননি। তার বিকাশের জন্য ইসলামের বিধানকেই তিনি চরম পন্থা বলে জ্ঞান করেছেন।
এ চিন্তাকে অহমবাদী চিন্তা বললেও একে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ মূলক চিন্তাধারা বা অতিমানব সম্বন্ধীয় চিন্তাধারা থেকে সম্পূর্ণ পৃথকরূপে পরিচয় করা যায়। কারণ এখানে ব্যাক্তি তার স্বীয় বৈশিষ্ট্য প্রমাণ করতে বা তার আনুষঙ্গিক সুখ-সুবিধা ভোগ করতে লালায়িত নয়, তেমনই অতিমানব রূপে বিকশিত হয়ে সে অপরাপর মানুষের উপর আধিপত্য বিস্তার করতে চায় না। এ অহমবাদের মর্ম কথা হচ্ছে আত্মপরিচয় লাভ এবং তারই মাধ্যমে এ বিশ্ব-চৈতন্যে আপনার প্রকৃত স্বরূপের উপলব্ধি। এ অহমবাদের পরিচয় পাওয়া যায় আসরারই খুদির ছত্রে ছত্রে। এ ধারণা ছিল এ পাক-ভারত মানুষকে নির্জীব-করণে ক্রিয়াশীল, মানুষের জানকে যেখানে মনে করা হতো মায়াময় মরীচিকা ভ্রম বৈ আর কিছুই নয়, ব্রহ্মজ্ঞান লাভে যে জানের ভ্রান্তি সহজেই ধরা পড়ে, জীবাত্মাকে অসহায় ও ভাগ্যের ক্রীড়নক হিসাবে যেখানে করা হয়েছে অথর্ব ও পঙ্গু; ইকবাল তারই প্রতিবাদ করে জ্বালাময়ী ভাষায় ঘোষণা করেছেন-
পানি আর কাদা বলে
নিজেকে ভাবছো কেন
কেন ছোট করে ফেল মন?
এই হীনমন্যতায় কতকাল কাটাবে জীবন;
তোমার কর্দম হতে সৃষ্টি কর জ্বালাময় নতুন সিনাই।
(ইকবাল চয়নিকা- আসরার-ই-খুদী); তরজমা, আ.ক.শ. নূর মোহাম্মদ)
সক্রিয়, জীবন্ত, চঞ্চল ও গতিশীল আভার উদ্বোধনের জন্য তিনি আবেগময়ী ভাষায় ‘রমুজে বেখুদী’তেও মানব সমাজকে আহ্বান জানিয়েছেন। এক্ষেত্রে তাঁর চোখে আমাদের সমাজের সুফীদের ধারণা অত্যন্ত গর্হিত বলে প্রতিভাত হয়েছিলো। তারা মানবাত্মার অসহায় অবস্থা ও তার পরিণতি সাহিত্যে ও কাব্যে প্রচার করেছিলেন। তাতে রুজ-ই-আলন্তে মানুষের ভাগ্যলিপির নির্ণয় ও তার ফলে পুতুলের মতো জীবন-নদের স্রোতে তাদের ভাসমান অবস্থার জন্য বিলাপ করেছিলেন। মহাকবি হাফিজ তাঁর অনবদ্য ভাষায় মানুষের এ করুণ চিত্র এঁকেছিলেন। ইকবাল তার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ ঘোষণা করে বলেছিলেন ফার্সি ভাষায়-
মানবগণ যাহারা আফিমের নেশায়
বিভোর হয়ে এ জগৎকে নীচ বলে ঘৃণা করছ
উঠো জাগো, চোখ খোলো, এ জগতের দুঃখ দর্দশার
নিন্দা করো না-
এ দুঃখ-দর্দশা মুসলিমদের সমাজ জীবনকে
গঠন করার জন্য ও
তাদের অন্তর্নিহিত শক্তির
স্ফুরণের জন্য নির্দিষ্ট হয়েছে।
রমুজ-ই-বেখুদীর অন্যত্রও তিনি বলেছেন-
বিচিত্র ছন্দে ও তালে সঙ্গীত তাহার
মৃত পৃথিবীতে করে প্রাণের সঞ্চার
তাহার নিকট থেকে আলোর আস্বাদ
পৃথিবী ভ্রমণ করে নূতনের সাধ।
এই তো সে আদর্শ, যার প্রতীক্ষায় আকাশ বাতাস জল স্থল অন্তরীক্ষ সবই অপেক্ষা করছে। সবল সরল মেরুদণ্ডের অধিকারী উন্নত শীর্ষ মহামানবের অপেক্ষায় সতত সৃষ্টিশীল কর্মচঞ্চল বিশ্বসত্তা আজও অপেক্ষা করছে। তার এ উন্নত অবস্থার পটভূমিতে রয়েছে তাওহীদে তার শিক্ষা। তাওহীদের মূলমন্ত্রে দীক্ষিত হয়েই সে উন্নত শীর্ষ মহামানব এ জগতের বুকে করে আদর্শ পূণ্য ভূমির প্রতিষ্ঠা-
তওহীদের মূল-সূত্র তাহার শিক্ষায়
তাহার নিয়ম পূর্ণ শৃঙ্খলা প্রথায়-
অমিতাচারী উচ্ছৃঙ্খল মানুষ সে নয়-
তার প্রত্যেক কথায় ও কাজে রয়েছে শৃঙ্খলা ও নিয়মানুবর্তিতা।
পরবর্তী বা শেষ স্তরে ইকবাল-মানস তত্ত্বজ্ঞানের দিকে বিশেষ করে ঝুঁকে পড়ে। ‘পয়ামে মশরিক’ বা প্রাচ্যের বাণী ১৯২৩ সালে প্রকাশিত হয়। তথসীয়ে ফিত্রৎ বা সৃষ্টির অধিকার নামক খণ্ডকাব্য এর অন্তর্ভুক্ত। এ কাব্য জার্মান দেশীয় দার্শনিক কবি গ্যেটের DEST WESTERLICHE DIWAN-এর উত্তরে রচিত।
কড়া যাহার খাদ্য যোগায় ভাই,
জানি একদিন উঠবে আকাশ-পথে
হয়া-আবর্ষ ছেড়ে পাবে রোশনাই।
কেন জিজ্ঞাসা করছো আমার কথা?
মানুষের কথা ভাবো, আর দেখো চেয়ে।
এ হৃদয় আরো উন্নীত,
হলে পর হবে যে মহান স্বর্ণ-ধারায় নেয়ে।
সময় মতন মামুলি চিন্তাধারা
যদি বিকাশের মহান সুযোগ পায়
তবে তার স্থান আনন্দ উচ্ছাসে হবে
নিশ্চয় খোদার মনের ছায়।
(ইকবাল চয়নিকা, তরজমা: আবদুর-রশীদ খান)
মানুষের সকল আশা ও আকাঙ্খা, প্রেম-ভালবাসা সব কিছুরই মূল্য রয়েছে বিশ্বে। এর কণামাত্রও নিরর্থক নয়, বিকশিত হলে এ সবের প্রত্যেকটিরই রয়েছে স্বতন্ত্র ভাব। মানবতার বিকাশের পথে কিন্তু চাই সত্যিকার ঈমান। মাটির খুলির গড়া ও কায়াকে স্বর্গীয়ভাবে দীপ্তিমান করে তুলতে হলে তাকে ঈমানের রশ্মিতেই উজ্জ্বল করতে হবে-
জীবন্ত এই আত্মাখানির
ঈমানটুকু বাজে স্বপ্ন নয়-
ছড়ানো এ ধুলো দিয়েই
নকসা গড়া অধিক শক্তিময়-
(ইকবাল চয়নিকা, তরজমা: আবদূর-রশীদ খান)
ঈমানের রোশনীতে উদ্দীপিত আত্মার পক্ষে তাই এগিয়ে চলাই হচ্ছে সারতত্ত্ব। ধূলিময় এ পৃথিবীতে অতীতকে আঁকড়ে ধরে বসে থাকা তার পক্ষে উচিত নয়। মানুষকে কান পেতে শুনতে হবে পৃথিবীর অদম্য চলার গান। মানুষকে ভাবতে হবে অতীতের কথা— শুধুমাত্র নিজেদের ঐতিহ্যের সঙ্গে যোগসূত্র রাখার জন্য। তাকে প্রস্তুত হতে হবে ভবিষ্যতের জন্য, আগ্রহভরে অপেক্ষা করতে হবে অনাগত দিনগুলোর জন্য, তাই তিনি পরিষ্কার ভাষায় বলছেন-
পৃথিবীর জনপদে আমিও তো
ধুলির মতন কাহার কোমল গান
তারপর শুনেছি এ বুকে:
সময় নদীর উৎস খুঁজে পাবে আমার ঝর্ণায়
অতীত কেবল মোর শৌর্যবীর্য হারানো দিনের
এখন আগ্রহভরে ভবিষ্যতের প্রতীক্ষা আমার।
(ইকবাল চয়নিকা, তরজমাঃ আবদুর-রশীদ খান)
মানুষের ধুলি তার কর্ম-জীবনের দ্বারাই উজ্জ্বল হয়ে লোক থেকে লোকান্তরে নিম্নতর পর্যায় থেকে অধিষ্ঠিত হয়, যাতে ফেরেশতারাও ঈর্ষান্বিত হয়ে পড়ে—
সবচেয়ে উঁচু মণ্ডল পরে
এমনি গতি যে মোর ফেরেশতাগণ
তা দেখে আমায় ধরিতে লাগায় সোর
মানুষের ধুলি নিত্য নূতন কর্মে উজ্জ্বল হয়
পুরানো দিনের মত চাঁদ তার, এখনো আলোকময়
(ইকবাল চয়নিকা, তরজমাঃ আবদুর-রশীদ খান)
মানুষ তার তেজদীপ্ত বাহুকে বাজুবন্ধ পরে শক্তিহীন করেছে, তাই তাকে আবার প্রাণময় করার জন্য খুদির প্রদীপ জেলে আপনার প্রকৃত সত্তার পরিচয় লাভ করতে হবে। এ ক্ষেত্রে খুদির বিকাশের পথে তাকে রসুল নির্দেশিত পথেই হতে হবে অগ্রসর-
বাজুবন্ধের আড়ালে যেহেতু মানুষ লুকালো
আনি মুসার হাতকে, তাই জ্বালি মোর প্রদীপখানি
এসো গো নামাজে, শাহজাদা দ্বারা দিও না ধর্না
আর তাই ছিল মোর পূর্ব পুরুষ পুরাকালে এ-ধারার
(ইকবাল চয়নিকা, তরজমাঃ আবদুর-রশীদ খান)
(৩)
প্রকৃতপক্ষে ইকবালের কায়া সত্তাকে আর তুলনা করা যায় না। নিছক সৌন্দর্য সৃষ্টি বা সৌন্দর্য পুজার সাধনা তিনি করেননি। শিল্পের জন্যই শিল্পের সৃষ্টি (Art for at sake) করার চেষ্টা তিনি কোনোকালেই করেননি। অস্কার ওয়াইলডের এবং বিশ্ব ভাবধারা দ্বারা তিনি কোনোকালেই প্রভাবান্বিত At in Calydon-এ নিসর্গ পূজার যে অতি স্পন্দনয়ায় নিদর্শন পাওয়া যায়, তার কোনো প্রভাবই ইকবালের কাব্যে পড়েনি।
বাঙলা কাব্যে রবীন্দ্রনাথ বা বিশেষ করে সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের নানাবিধ কবিতায় নিসর্গবাদের যে চমৎকার নিদর্শনের সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎলাভ হয়, ইকবালের কাব্যে তার কোন উদাহরণই নেই। তার ভাষা ও ছন্দের একত্র সমাবেশে বাঙলা কাব্যে উর্বশী যে অপূর্ব স্থানের অধিকারী, সেরূপ প্রতিমধুর বা মায়াময় রূপ সৃষ্টিধর্মী কবিতাও ইকবাল সাহিত্যে বিরল। মহাকাব্যের বিরাট পটভূমিতে যেভাবে নানা মানুষ ও নানা চরিত্রের সমাবেশ রয়েছে ইকবাল কাব্যে, তার কোনো আভাষই নেই; খণ্ড কবিতার স্বল্পপরিসর আলোর মাঝে জীবনের কোনোমবিশিষ্ট দিক বা ভাবও তাতে মূর্ত হয়ে উঠেনি।
কাব্যের গোড়াতেই রয়েছে এক তীব্র প্রতিবাদ। সে প্রতিবাদ সবপ্রথমে দেখা দিয়েছে প্রচলিত সংস্কারের বিরদ্ধেএবং ক্রমবিকাশের ধারায় তা পূর্ণ পরিণতি লাভ করেছে মানব-জীবন সম্বন্ধে দীর্ঘকাল শোষিত নিরাশাবাদের বিরুদ্ধে। এ প্রতিবাদ বজ্রগম্ভীর কণ্ঠে তিনি উচ্চারণ করেছেন তাঁর নিজস্ব অভিমত প্রচার করার উদ্দেশ্যে এবং তাতে তিনি সফল হয়েছেন অপ্রত্যাশিতভাবে।
যদিও নজরুল ইসলামের মত তিনি মানবিকত্বকে সার্বিক ও পরম শান্তিময় রূপদানে কুন্ঠিত ছিলেন; জগদীশ্বর, ঈদ, পুরষোত্তর সত্য বলে তিনি দাবি করেননি, তবু তাঁর সীমিত ভাষায় মানব-জীবনের পূর্ণ পরিণতির যে আশ্বাস দিয়েছেন, বিশ্ব-সাহিত্যে তা অনবদ্য। তার দার্শনিক মতবাদের বৈশিষ্ট্য হিসাবে বলা যায় ব্রহ্ম-কেন্দ্রিক বা পরমাত্মা কেন্দ্রিক; মানব-সৃষ্টির স্থলে তিনি মানব-কেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিষ্ঠায় ছিলেন দৃঢ়-সংকল্প।
এজন্যই এই মাটির মানুষকে তিনি জ্যোতির্ময় ফেরেশতাদের উপরেও স্থান দিতে একটু ইতঃস্তত করেননি। এ ক্ষেত্রে তাঁর এ বৈপ্লবিক পদক্ষেপ রবীন্দ্রনাথের পদক্ষেপের পরিপূরক বলা যায়। ব্রহ্মবাদের অতল তলায় তলিয়ে যাওয়া মাটির পৃথিবীতেই রবীন্দ্রনাথ পেয়েছিলেন ব্রহ্মাস্থান—’এ মাটির বেড়ার প্রান্ত হতে অমূর্তের পেয়েছি সন্ধান’—খেয়ালী কবির কল্পনা-বিলাস নয়। এ বক্তব্য মহাধ্যানীর জীবন-সাধনার সিদ্ধিজাত ফল।
মাটির পৃথিবীতে স্বর্গের সব উপাদান বিরাজমান বলে ধারণা করা রবীন্দ্র-দর্শনের পরিণত ফল। সেই মাটির মানুষের ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখ ও হাসি-কান্নার বিভিন্ন রূপ তিনি সাধ্যমত তুলিকা-স্পর্শে অমর করে তুলেছেন। শ্রেণী-সংগ্রামের পর্যুদস্ত অসহায় নির্বিত্তের করুণ চিত্রও তিনি দূর থেকে দেখেছেন। আফসোসও করেছেন। তবে মানুষকে এ-সমাজ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করতে কোনো অনুপ্রেরণা দান করেননি। ইকবাল এক্ষেত্রে আরও অগ্রসর হয়েছেন এবং মাটির ধারার অধিবাসী আপাতঃদৃষ্টিতে নানাবিধ দুর্যোগে সম্পূর্ণ অসহায় পঙ্গু ও অশক্ত মানব নামধারী একদল জীবকে তাদের ‘খুদী’ তার প্রকৃত সত্তার পরিচয় লাভ করার জন্য উদাত্ত স্বরে আহ্বান জানিয়েছেন। এখানেই তাঁর কাব্যের বিশেষত্ব।
শুধু মাত্র আনন্দ পরিবেশনই তাঁর কাব্যের লক্ষ্য নয়, মানুষকে এক বিশিষ্ট জীবনাদর্শে উদ্বোধিত করে তোলা এবং তার মধ্যে আত্মপ্রত্যয়ের প্রতিষ্ঠা করাই ছিল তাঁর জীবনের মূল আদর্শ। তাকে মহাকবি এজন্যই বলা যায়। নতুনভাবে জগৎ ও জীবনকে দেখার প্রেরণা ও পদ্ধতি উভয়ই তার কাব্যে পাওয়া যায়। মুসলিম জীবনের প্রতি অতিরিক্ত অনুরাগের জন্য নিকলসন (Nickolson) প্রমুখ সমঝদারেরা তাঁকে মুসলিমদের কবি বলে একটি বিশিষ্ট জাতির মধ্যে সীমাবদ্ধ করার চেষ্টা করেছেন।
ওঁরা ভুলে গেছেন ইসলাম ও মুসলিম জাতি এক নয়। ইকবাল বার বার বলেছেন এ দুনিয়ার নানাবিধ সংকটের সময় মুসলিমরা ইসলামকে রক্ষা করেনি বরং ঠিক উল্টোভাবে ইসলামই মুসলিমদের রক্ষা করেছে। ইকবাল ইসলামকে শুধুমাত্র প্রত্যয় হিসাবে গ্রহণ করেননি বরং এক অভিনব পূর্ণাঙ্গ জীবন-দর্শন ও জীবন-পদ্ধতি হিসাবে গ্রহণ করেছেন। সে পূর্ণাঙ্গ জীবন-দর্শনের অনুশীলনের ফলে মানুষ ‘ইনসানে কামিল’ বা পূর্ণ বিকশিত মানুষে পরিণত হতে পারে। সে জীবন-দর্শনে প্রত্যয়শীল মানুষ গোষ্ঠীকেই তিনি সত্যিকার মুসলিম বলে ধরে নিয়েছিলেন এবং শেকোয়াতে সেই আদর্শবাদী মানুষ গোষ্ঠীর তরফ থেকেই তিনি আল্লার দরবারে অভিযোগ পেশ করেছেন। বর্তমানকালের নাম-সর্বস্ব মুসলিমদের জন্য তিনি আল্লার কাছে আহাজারি করেননি।
-ঋণ স্বীকার: মাহে নও, এপ্রিল ১৯৬৯।