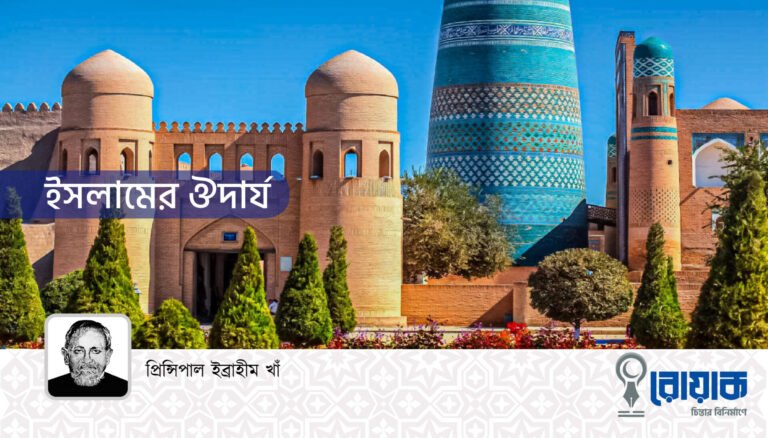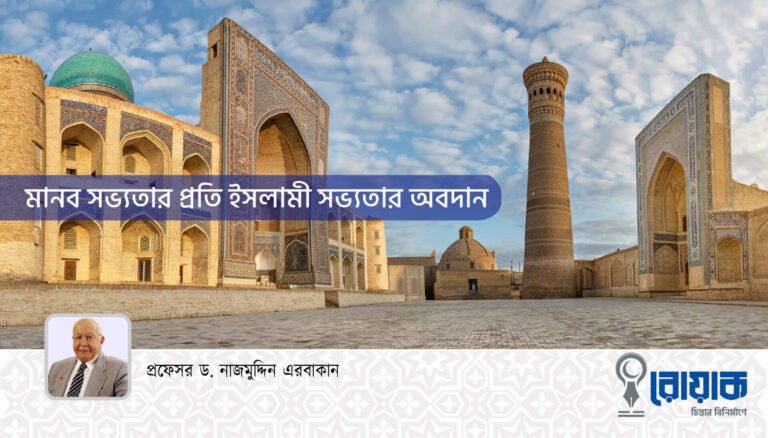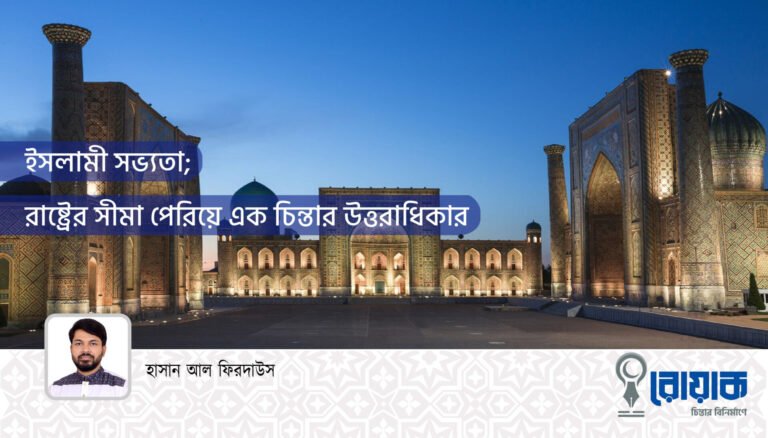আধুনিক যুগে ক্রমবিকাশবাদ (Evolution Theory) একটি বৈজ্ঞানিক মহাসত্যরূপে বিদ্বজ্জনের সমাজে স্বীকৃত। Science of Life গ্রন্থ প্রণেতাগণ লিখেছেন : আঙ্গিক ক্রমবিকাশকে একটি মহাসত্যরূপে মেনে নিতে এখন কারোরই আপত্তি থাকতে পারে না। কেবল সে সব লোক ছাড়া, যারা মূর্খ বা বিদ্বেষী, কিংবা কুসংস্কারে নিমজ্জিত। Modern Packet Library- New York Man and the Universe নামে বইয়ের একটি সিরিজ প্রকাশ করেছে। এই পর্যায়ের পঞ্চম গ্রন্থটিতে ডারউইনের Origin of Speices বই খানিকে ইতিহাস স্রষ্টা আখ্যায়িত করে বলা হয়েছে: “মানুষ স্বীয় বংশ তালিকা জানবার জন্য দীর্ঘকাল ধরে যে চেষ্টা চালিয়ে আসছে, এপর্যায়ে কোনো মতবাদকে এতটা তীব্র ধর্মীয় বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হয়নি, যতটা হতে হয়েছে ডারউইনের লিখিত Natural Selection গ্রন্থটিকে এবং অপর কোনো মতবাদ এতটা বৈজ্ঞানিক সমর্থন (Scientific Affirmation) পায়নি, যতটা এই মতবাদটি পেয়েছে। ১
আমেরিকার প্রখ্যাত ক্রমবিকাশবাদী বিজ্ঞানী G.G. Simpson লিখেছেন :
“ডারউইন ছিলেন ইতিহাসের উচ্চতর লোকদের অন্যতম। তিনি মানবীয় জ্ঞানের বিকাশ ও উৎকর্ষ সাধনে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছেন। এই উচ্চতর মর্যাদা তিনি অর্জন করতে সক্ষম হয়েছেন এ কারণে যে, তিনি ‘ক্রমবিকাশ’ মতবাদ (Theory of Evolution)-কে চূড়ান্ত ও পূর্ণাঙ্গভাবে একটি মহাসত্যরূপে প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছেন, একটা নিছক অনুমান বা বিকল্প প্রকল্পরূপে নয়, যা বৈজ্ঞানিক তত্ত্বানুসন্ধানের জন্য তৈরি করা হয়েছিল। ২
এ.ঈ. মেন্ডর লিখেছেন : “মানুষ ও অন্যান্য প্রাণসম্পন্ন জিনিসসমূহের বর্তমান আকার-আকৃতি পর্যন্ত পৌঁছতে ক্রমবিকাশ প্রক্রিয়া অবলম্বন করতে হয়েছে এই মতটি এত অকাট্য দলীল দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে যে, মতটিকে এখন প্রায় নিশ্চিত ও বাস্তব (Approximate Certainity) বলা যেতে পারে।”৩
লাল (RS. Lull) লিখেছেন : “ডারউইনের পর ক্রমবিকাশ মতবাদটি অধিকতর জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। এমনকি চিন্তাশীল গবেষকদের নিকট এ ব্যাপারে কোনো সংশয় নেই যে, এটাই একক যৌক্তিক পদ্ধতি, যার ভিত্তিতে সৃষ্টিকর্মের ব্যাখ্যা দেয়া এবং তা অনুধাবন করা সম্ভব। তিনি আরও লিখেছেন : “সমগ্র বিজ্ঞানী ও অন্যান্য অভিজ্ঞ অধিকাংশ লোকই ক্রমবিকাশতত্ত্বে সত্যতায় (Truthness) সম্পূর্ণ নিশ্চিত, তা প্রস্তর পর্যায়ের হোক কিংবা জীবজন্তু পর্যায়ের। অন্য কথায়, পৃথিবী যখন জীবনের বাসোপযোগী হলো তখন দীর্ঘকালীন কার্যক্রমের ফলে প্রাথমিক পর্যায়ের কিছু জীবনের উন্মেষ হলো। অতঃপর দীর্ঘতম কালের ক্রমাগত কার্যক্রমের ফলে উদ্ভিদ ও জীব-জন্তুর সেসব বিস্ময়কর প্রজাতিসমূহ অস্তিত্ব লাভ করল যা আজ আমরা প্রত্যক্ষভাবে দেখতে পাচ্ছি।”৪
এই মতবাদটির জনপ্রিয়তা সম্পর্কে এটা দেখেও অনুমান করা চলে যে, লাল-এর সাতশ পৃষ্ঠার গ্রন্থে জীবনের সৃষ্টিমূলক ধারণা (Special Creation) পর্যায়ের আলোচনা শুধু একপৃষ্ঠা ও কয়েকটি ছত্রে সন্নিবেশিত হয়েছে। ‘ইনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা’- (১৯৫৮) গ্রন্থে সৃষ্টি সংক্রান্ত (Creationism) মতবাদের আলোচনার জন্য মাত্র এক চতুর্থাংশ পৃষ্ঠারও কম স্থান বরাদ্দ করা হয়েছে। কিন্তু তার বিপরীত ‘আঙ্গিক অভিব্যক্তি’ (Organic Evolution) শীর্ষক যে রচনাটি সন্নিবেশিত হয়েছে, তা ক্ষুদ্র টাইপে পূর্ণ চৌদ্দটি পৃষ্ঠায় বিস্তৃত হয়ে আছে। এই প্রবন্ধটিতেও জীব-জন্তুর ক্রমবিকাশকে একটি চূড়ান্ত সত্য ঘটনা (Fact) হিসেবে সমর্থন করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে, ডারউনের পর এই মতবাদটি বিজ্ঞানী ও জনগণকর্তৃক সাধারণভাবে স্বীকৃত (General acceptance) হয়েছে। এখানে প্রশ্ন ওঠে, বিজ্ঞানীরা আংশিক ক্রমবিকাশ মতবাদটিকে সাধারণ সত্যরূপে নিরূপণ করলেন কিভাবে? তাঁরা কি অতীতের অন্ধকারাচ্ছন্ন গহ্বরে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে জীবজন্তু ও মানুষকে আংশিকভাবে ক্রম বিবর্তন লাভ করতে দেখতে পেয়েছেন, যদ্দ্বারা সমগ্র জীবজন্তু ও মানুষ এক সহজ সরল পর্যায়ের প্রাথমিক জীব থেকে আঙ্গিক বিবর্তনের মাধ্যমে ক্রমবিকাশ লাভের পদ্ধতিতে অস্তিত্ব লাভ করেছে বলে সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে?
এই প্রশ্নের জবাবে বিজ্ঞানবিদেরা বলেছেন, তাদের নিকট নাকি এরূপ দলীল রয়েছে এবং পর্যবেক্ষণ পরীক্ষণের অকাট্য পদ্ধতিতে তাঁরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, আঙ্গিক ক্রমবিকাশ লাভের এই মতটি সম্পূর্ণ নির্ভুল ও সর্বতোভাবে সত্য।
বিজ্ঞানীদের এই জবাব বিশেষভাবে একটি ভিত্তির ওপর নির্ভরশীল আর তা হচ্ছে, জীবজন্তু বা প্রাণীর অস্বাভাবিকভাবে দৈহিক ও আঙ্গিক সাদৃশ্য থাকা উচ্চতর ও নিম্নতর বহু প্রকারে (Kind) বিভক্ত। এগুলোর পারস্পরিক সাদৃশ্য করে যে, এগুলো সব একই বংশজাত, আর সেগুলোর উচ্চতর ও নিম্নতর প্রকারভেদ থেকে প্রমাণিত হয় যে, এগুলো ক্রমবিকাশ পদ্ধতিতে বিভিন্ন প্রজাতিতে পরিণতি লাভ করেছে।
জীব ও প্রাণীকূলের মধ্যে সর্বপ্রথম যে সব প্রাণী আসে, তারা ‘এ্যামীরা’ (Amoeba) নামে পরিচিত। এগুলো অত্যন্ত ক্ষুদ্রকায়। এগুলোর গোটা দেহ এককোষ সম্পন্ন মাত্র। খাদ্যগ্রহণ, খাদ্য হজমকরণ, হজম হয়ে যাওয়া খাদ্যের দেহাংশে পরিণতি হওয়া এবং আবর্জনা নিষ্কাশন, শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ এবং প্রজনন ও বংশ সংরক্ষণের ধারাবাহিকতা প্রভৃতি জীবনের অপরিহার্য কার্যাবলী এই এককোষ সম্পন্ন দেহ দিয়েই সুসম্পন্ন করে থাকে। অতঃপর যা লক্ষ্য করা যায়, তা হইড্রা (Hydra) নামে খ্যাত। এর রয়েছে কয়েক সহস্র কোষ। পোকার (Worm)-ও থাকে কয়েক লক্ষ কোষ। আর একটি মানবদেহ
কয়েক হাজার কোটি কোষের সমন্বয়ে গড়ে ওঠে। অপরাপর জীব-জন্তু অপেক্ষা মানবদেহের কোষের প্রকারও হয়ে থাকে অনেক বেশি। এ থেকে জানা গেল যে, বিভিন্ন জীব ও প্রাণী স্বীয় দৈহিকতা ও জটিলতায় পরস্পর থেকে যথেষ্ট মাত্রায় ভিন্ন।
যোগ্যতা ও কর্মক্ষমতার দিক দিয়েও এগুলোর মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য বিদ্যমান। ‘এ্যামীবা’ ও ‘হাইড্ৰা’ প্লাবন, স্রোত ও শুষ্কতার দয়ার ওপর নির্ভরশীল। একটি পোকা মাটির খুব ক্ষুদ্র স্থানের সাথে সম্পর্কিত। মাছের পরিধি অধিক বিস্তীর্ণ। প্রতিকূল অবস্থায় স্বীয় অবস্থিতির পরিবর্তন তার সাধ্যায়ত্ব। কিন্তু তা সত্ত্বেও মাছ পানিতেই থাকে। পানির অভ্যন্তর ছাড়া মাছের অস্তিত্ব অকল্পনীয়। কুকুর পানিতে সাঁতার কাটে; আর স্থলভাগে দৌড়ায়। কিন্তু মানুষ জল ও স্থলভাগ ছাড়াও শূন্যলোকের উপরও কর্তৃত্ব করে।
পরিবেশের যে অবস্থা এই সবের ওপর প্রভাব বিস্তার করে, তাও বিস্ময়করভাবে বিভিন্ন। এ্যামীবা’র প্রভাবিত হওয়ার ঘটনাবলী এক মিটারের কয়েক হাজার ভাগের একভাগের মধ্যে সঙ্ঘটিত হয়, যখন আলো ও কম্পন তাকে প্রভাবিত করে। কিন্তু এই আলো ও কম্পনের উৎস কোথায় এবং তার দূরত্ব কতটা, তা জানবার কোনো উপায় তার আয়ত্তে নেই। তা খুবই সাদাসিধাভাবে আলো ও কম্পনের প্রভাব গ্রহণ করে থাকে। হাইড্রা সাপের মতো এক প্রকারের সামুদ্রিক পোকা কয়েক শত মিটার দূরত্বের পরিবেশ থেকে প্রভাব গ্রহণ করে। পোকা আকারে কিছুটা বড় হয়। তা কোনো অতিরিক্ত অনুভূতিশীল অঙ্গ ব্যতিরেকেই আলো ও অন্ধকার অনুভব করতে পারে। কিন্তু তা কোনো জিনিসের সংগঠন, তার বর্ণ বা দূরত্ব দেখতে পারে না। সে জানতে পারে কেবল তখন, যখন পৃথিবীতে কম্পন শুরু হয়ে যায়। কিন্তু তা শুনতে পায় না। কেননা বিভিন্ন ধ্বনি ও শব্দের মধ্যে পার্থক্য করার কোনো সাধ্য তার নাই। মানুষের ন্যায় পরিবেশকে আয়ত্তাধীন ও নিয়ন্ত্রণ করার জন্য কোনো চেষ্টা করা তার পক্ষে সম্ভব নয়। কেননা পরিবেশের সঙ্গে তার কোনো সংশ্লিষ্টতা নেই। তা বাইরের সব কিছু থেকে সম্পূর্ণ নিঃসম্পর্ক হয়ে একটা বন্ধ জগতে জীবন যাপন করে। আমাদের অনুভূতি-যন্ত্রপাতি থাকা সত্ত্বেও তা প্রায় দুর্বোধ্য।
মাছ প্রতিবিম্ব দেখতে পারে। কিন্তু পানির বাইরের কোনো জিনিস দেখা তার পক্ষে কঠিন। পানির মধ্যেই তার সবকিছু প্রায় সীমাবদ্ধ। কয়েক ফুটের একটি গর্তই তার জগত । কুকুর দেখে ও শুনে, আর ঘ্রাণের শক্তিও তীব্র। পৃথিবীর বুকে দৌড়ানোও তার পক্ষে সম্ভব। ইন্দ্রিয় নিচয় দ্বারা তার অনুভবকৃত পরিবেশ মানুষের পরিবেশের মতোই বিস্তীর্ণ। কিন্তু পরিবেশকে অনুধাবন করা মানুষের পক্ষে যতটা সম্ভব তার পক্ষে ততটা নয়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায়, মেঘ, চন্দ্র, সূর্য বা তারকা-নক্ষত্রসমূহের মধ্যকার দূরত্ব অনুধাবন করা কুকুরের পক্ষে কখনই সম্ভব নয়, যা মানুষের পক্ষে সহজ। অনুরূপভাবে কুকুরের মন ইন্দ্রিয়ানুভূত জিনিসসমূহের মধ্যে বুদ্ধিগত সম্পর্ক স্থাপন করতে সক্ষম নয়, যা মানুষ পারে। কুকুরও জানতে পারে; কিন্তু সে জানাটা অ-বুদ্ধি বিবেকসঞ্জাত।
সাপ তার ডিমসমূহ মাটির উপর ছেড়ে দেয়। তা থেকে আপনা আপনি বাচ্চা বের হয়ে আসে। পাখি ডিম পেড়ে দীর্ঘ সময় পর্যন্ত ‘তা’ দিতে থাকে। এই সময়ে পুরুষ পাখি তার অন্ন জোগায়। অনেক সময় পুরুষ পাখি ও স্ত্রী পাখি উভয়ই পর পর ডিমে তা দেয়। দুগ্ধ দানকারী জন্তুগুলোর অবস্থা এদের থেকে উন্নত ও অগ্রসর। স্ত্রী-পশু বাচ্চা প্রসব করে স্বীয় দেহের ‘রক্ত’ সৃষ্ট দুগ্ধ পান করিয়ে করিয়ে বাচ্চাকে পালে ও বড় করে।
এভাবেই বিভিন্ন জীব ও জন্তুর মধ্যে স্তর ভেদ বিদ্যমান। স্তর ভেদের এই রূপ অকাট্যভাবে প্রমাণ করে যে, এগুলোর মধ্যে একটা বিকাশমান বিন্যাস পরম্পরা রয়েছে। নিম্নতার পর্যায়ের জীব জৈবিক ক্রমবিকাশের অতীত স্তরসমূহের প্রতি ইঙ্গিত করে। আর উচ্চতর বা উন্নততর জীব জৈবিক ক্রমবিকাশের পরবর্তী স্তরসমূহ তুলে ধরে। বিজ্ঞানীদের মতে এ নিছক অনুমান বা কল্পনা নয়। এ হচ্ছে জীবনের সেই অকথিত কাহিনী, যা মাটির স্তরসমূহে লিপিবদ্ধ রয়েছে। আর তা এই মতবাদটিকে পর্যবেক্ষণিক যুক্তি পর্যায়ে সর্বতোভাবে সঠিক ও নির্ভুল প্রমাণ করে।
ভারতের শিমলা ও চণ্ডীগড়ের মাঝখানে সিওয়ালিক (Siwalik) নামে পরিচিত একটি পর্বতমালা অবস্থিত। এখানকার ভূপৃষ্ঠের উপর নানাস্থানে দাঁত, মাথার খুলি ও অস্থিখণ্ড প্রস্তর খন্ডের ন্যায় যত্রতত্র পড়ে থাকতে দেখা যায়। কেবল এখানেই নয়, দুনিয়ার বিভিন্ন স্থানে এ রকম পাওয়া গেছে। আসলে এগুলো কোটি কোটি বছর পূর্বে দুনিয়ায় বসবাসকারী জন্তু-জানোয়ারের দেহ কাঠামোর ধ্বংসাবশিষ্ট মাত্র। তা মাটির তলায় পড়ে গেছে এবং দীর্ঘদিনের কার্যক্রমের ফলে তা প্রস্তরে রূপান্তরিত হয়েছে। উদ্ভিদ ও জীব-জন্তুর এই প্রস্তরায়িত রূপকে ফসিল (Fossile) বলা হয়। ভূমিকম্প ইত্যাদির ফলে এগুলো মাটির তলদেশ থেকে উপরে উঠে এসেছে। অথবা মাটি খোদাই কাজের দরুনও এগুলো আবিষ্কৃত হয়ে থাকবে। বর্তমানে এই ফসিল বিপুল পরিমাণে পাওয়া গেছে এবং বড় বড় যাদুঘরে প্রদর্শনীর জন্য সংরক্ষিত হয়েছে। এই প্রস্তরায়িত দেহাবয়বের পূর্ণাঙ্গ কাঠামো কোথাও পাওয়া যায় না, পাওয়া যায় খণ্ড খণ্ড টুকরা টুকরা রূপে। অবশ্য বিশেষজ্ঞগণ এই খণ্ড টুকরাসমূহ একত্রিত সংযোজিত করে প্রাচীন জীব-জন্তুর আকৃতি বানিয়ে নিতে চেষ্টা করেছেন।
এইসব প্রস্তর খণ্ড ভূ-তাত্ত্বিক দৃষ্টিতে মিলিত ও পরস্পর সংযোজিত করার ফলে এক মহাসত্যের উদ্ঘাটন সম্ভবপর হয়েছে বলে দাবি করা হয়েছে। বিজ্ঞানের উৎকর্ষের ফলে যে কোনো প্রস্তর খণ্ডকে দেখে তার বয়স এবং কতকাল ধরে তা পৃথিবী পৃষ্টে অবস্থান করছে তা অতি সহজেই বলে দেয়া যেতে পারে। প্রস্তরসমূহের স্তর দেখে পৃথিবীর বিভিন্ন স্তরের বয়স জানতে পারা আজকের দিনে কঠিন কিছু নয়। এই বিজ্ঞানের আলোকে প্রস্তবায়িত খণ্ডসমূহকে দেখে জানা গেছে যে, সকল প্রকার জীব-জন্তুই প্রথম দিন থেকেই আর পৃথিবীতে অবস্থান করছে না। এগুলোর মধ্যে কালের একটি স্তর বিন্যাস রয়েছে। পৃথিবীর প্রাচীনতম স্তরগুলো হালকা ও প্রাথমিক পর্যায়ের জীবগুলোর সন্ধান দেয়। অতঃপর পাওয়া যায় পর্যায়ক্রমিক জটিল ও উন্নত মানের জীবের সন্ধান। আর সর্বোচ্চ স্তরে অবস্থিত এই মানুষ। এই উদ্ভাবনের ভিত্তিতে বিবর্তন তত্ত্বের সমর্থনে অসংখ্য গ্রন্থাবলী রচিত হয়েছে। আধুনিক বিজ্ঞানীদের বিশ্বাস, অতঃপর ক্রমবিকাশবাদ একটা পর্যবেক্ষিত পর্যায়ে প্রমাণিত তত্ত্বে পরিণত হয়েছে।
প্রখ্যাত প্রাণীবিদ জুলিয়াস হাক্সলি ও জে বি এম হাল্ডেস-এর যৌথভাবে লিখিত Animal Biology গ্রন্থে লিখেছেন: “প্রাণী প্রজাতিসমূহের সাধারণ ও উচ্চ বিন্যাস থেকে একথা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, উচ্চতর জীবসমূহ বিবর্তিত হয়ে পরে অস্তিত্ব লাভ করেছে। এইগুলোকে আমরা যেন ঠিক অস্তিত্ব লাভ করতে দেখতে পাচ্ছি, যখন আমরা পিছনের দিকে ফিরে ফসিলের সাহায্যে ইতিহাস অধ্যয়ন করি। এটা অনুমান বা ধারণা পর্যায়ের হলেও দৃঢ় প্রত্যয়ের সব বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হয়ে আছে। পৃথিবীর যে প্রাথমিক ইতিহাস প্রস্তর খণ্ড ও প্রস্তরায়িত কাঠামোসমূহে অঙ্কিত হয়ে আছে, তা এখন পর্যন্ত পূর্ণমাত্রায় লিপিবদ্ধ হয়নি। তা সত্ত্বেও এ এক প্রমাণিত সত্য যে, জীবন সাধারণ ও নিম্ন পর্যায়ের প্রাণীকূলের রূপে উন্মেষ লাভ করেছিল।”৫
এই ঘটনার সঙ্গে জৈব-জীবনের অপরাপর ঘটনাবলী মিলিয়ে নিলে অনুমান পূর্ণাঙ্গ রূপ লাভ করে। আর তা হচ্ছে, জীবগুলো পারস্পরিক বহু বৈষম্য ও পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও অসাধারণভাবে পরস্পর সাদৃশ্য সম্পন্ন। মানবীয় কাঠামোর এক একটি ‘অস্থির’ সঙ্গে ঘোড়া, বানর বা চামচিকার ‘অস্থি’র তুলনা করা চলে। জীব-জন্তুসমূহের দৈহিক গঠন এবং এগুলোর হাড়, রগ ও স্নায়ুগুলো সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে বিবেচনা করা হলে স্পষ্টভবে জানা যাবে যে, সব জীবই পারস্পরিক আত্মীয়তার বন্ধনে আবদ্ধ। আর এগুলো গোড়ায় ছিল একটি জীব। সহস্র কোটি বছরের বিবর্তন প্রক্রিয়ার পরিণতিতে এগুলো বর্তমান রূপ পরিগ্রহ করেছে।
বিভিন্ন প্রাণীর ভ্রূণ প্রাথমিক পর্যায়ে পরস্পর সদৃশ। আমাদের প্রত্যেকটি ব্যক্তিসত্তাই এককোষ নিয়ে জীবনের সূচনা করেছে। অন্যান্য দুগ্ধপায়ী জীবকূলের প্রাথমিক কোষের তুলনায় শুধু পরিমাণ ও গঠন প্রকৃতির কতিপয় সূক্ষ্ম দিকে (Fine details) বিভিন্ন হয়ে থাকে। এই কোষ একটি থেকে দুটি ও দুটি থেকে চারটিতে পরিণত হয়ে সংখ্যা বৃদ্ধি করে। জন্মের পূর্বে মানব শিশু মাছ, ব্যাঙ, সাপ ও প্রাথমিক পর্যায়ে দুগ্ধদায়ী প্রাণীকূল এবং বন মানুষ সদৃশ আকৃতি অবলম্বন করে।
এক পর্যায়ে তার পাখা গজায় এবং পরবর্তী এক পর্যায়ে তার লেজ বের হয়। জন্মের তিন মাস পূর্বে তার সমগ্র দেহ কালো মসৃণ পশমে আচ্ছাদিত হয়ে যায়। ক্রম বৃদ্ধির পর্যায়ে বানর ও মানবশিশু পরস্পর সাদৃশ্যপূর্ণ থাকে। কেবল মাত্র শেষ পর্যায়ে এই দুয়ের মাঝে পার্থক্য করা সম্ভবপর হয়। ভূমিষ্ঠ হওয়ার পরও মানব শিশু ঠিক তেমনি লালন-পালন পায়, জীব বিজ্ঞানীদের মতে ঠিক যেভাবে মানব বংশের ক্রমবিকাশ সম্ভব হয়েছিল। তা যখনই স্বীয় হাত-পা ব্যবহার করার যোগ্য হয়ে যায়, তখনই হাটুর উপর ভর করে হামাগুড়ি দিয়ে চলতে শুরু করে। অর্থাৎ ঠিক চতুষ্পদ জন্তুর মতোই শুরু হয় তাঁর জৈবজীবন। কেবল মাত্র একটি ক্ষেত্রেই নয়, অসংখ্য প্রকারের সাদৃশ্য রয়েছে জীবগুলোর পরস্পরের মধ্যে। এর ভিত্তিতে জীব-বিজ্ঞানীরা এই মতবাদ রচনা করেছে যে, প্রত্যেকটি প্রাণীই তার জীবনের সামান্য সময়ের মধ্যে সেই সমস্ত পরিবর্তনগুলোরই পুনরাবৃত্তি করে, যা এর পূর্বে তার পূর্ববংশের লক্ষ কোটি বছরের পরিসরে সঙ্ঘটিত হয়েছে। মানুষ ও জীবের ভ্রূণ ও তার ক্রমবৃদ্ধির ক্ষেত্রের সাদৃশ্যের উল্লেখ করার পর বিজ্ঞানী লাল লিখেছেন : “গর্ভের অন্ধ প্রকোষ্ঠ উপরোক্তভাবে যে বিস্ময়কর পরিবর্তনসমূহ সঙ্ঘটিত হয়, তা খুবই সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যে সেই সমস্ত পরিবর্তনেরই পুনরাবৃত্তি, যা পৃথিবীর উপরিভাগে দীর্ঘকাল ধরে ইতিপূর্বে সঙ্ঘটিত হয়েছে।”৬
অন্যান্য জীব-জন্তু অপেক্ষা মানুষ ও বনমানুষের মধ্যকার সাদৃশ্য অধিকতর ঘনিষ্ঠ। এই কারণে মনে করা হয়েছে যে, মানুষ সম্ভবত বন মানুষেরই পরবর্তী ক্রমবিকাশপ্রাপ্ত বংশ। এই দুই শ্রেণির জীবের আকৃতির মধ্যে বর্তমান সাদৃশ্যসমূহ স্যার আর্থার কিইথের (Keith) গণনানুযায়ী এটি ধরা পড়েছে, যা অপরাপর লেজুড় সম্পন্ন বানরের মধ্যে পাওয়া যায় না। ডারউইন তার গ্রন্থে মানুষের বংশধারার প্রথম অধ্যায়ে মানুষ ও অন্যান্য জীব-জন্তুর মধ্যে বহু সংখ্যক সাদৃশ্যের উল্লেখ করে শেষে লিখেছেন : “আমাদের বিদ্বেষ ও অহংকারই আমাদের পিতৃ-পুরুষদের মুখে একথা বলিয়েছে যে, তারা দেবতার সন্তান। আর এই অনুভূতিই মানুষকে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে দেয়নি যে, (তারা স্বতন্ত্র কোনো সৃষ্টি নয়, আসলে তারা অন্যান্য জীব-জন্তুর ক্রমবিকাশ প্রাপ্ত বংশধর মাত্র)। কিন্তু সে সময় অবশ্যই আসবে, যখন বিশ্বকরভাবে তারা জানবে। প্রকৃতি-বিজ্ঞানীরা এটা ভালভাবেই জানতেন যে, মানুষ ও অন্যান্য স্তন্যপায়ী জীব-জন্তুর দেহ কাঠামোতে যথেষ্ট সাদৃশ্য রয়েছে। তাদের দৃঢ় প্রত্যয় ছিল যে, তাদের প্রত্যেককে আলাদা আলাদাভাবে সৃষ্টি করা হয়নি।”৭
মিষ্ট পানিতে সতেরো প্রকারের শামুক পাওয়া গেছে। এগুলোর মধ্যে পর্যায় বিন্যাস পরম্পরা নির্ধারণ করে প্রাণীবিদরা দাবি করেছেন যে, এগুলো আসলে একই শামুকের আগের পরের অভিব্যক্তি পর্যায় সমূহ মাত্র। এখানে তিনটি শামুকের ছবি দেয়া হয়েছে। অভিব্যক্তিবাদী বিজ্ঞানীদের দাবি অনুযায়ী তাদের মতবাদের দুটি ভিত্তি এগুলোর মধ্যে প্রকটভাবে বিদ্যমান তার একটি হচ্ছে এগুলোর পারস্পরিক সাদৃশ্য আর দ্বিতীয়, এগুলোর মধ্যকার ক্রমিক নিয়মের অভিব্যক্তি।
এছাড়াও বহু সাক্ষ্য প্রমাণ রয়েছে, সেগুলো বিজ্ঞানীদের এই মতবাদ রচনায় বাধ্য করেছে পথ দেখিয়েছে। যেমন-উচ্চতর জীব জন্তুর দেহে অনেক অপ্রয়োজনীয় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ রয়েছে, অথচ, এগুলোই নিম্নস্তরের প্রাণীকূলের জন্য খুবই প্রয়োজনীয়। মানব দেহে প্রায় দুশো তন্ত্র ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ রয়েছে, যা বর্তমান অবস্থায় আমাদের কোনো কাজে আসে না। অথচ নিম্নস্তরের প্রাণীকূলের জন্য সেগুলো অনেক জরুরী কাজ সুসম্পন্ন করে। কান দোলানো ও লোম খাড়া করার তন্ত্রগুলো এ পর্যায়ে গণ্য। এগুলো মানব দেহে রয়েছে, কিন্তু বাস্তবে এগুলোর তেমন কোনো কাজ নেই। Vermiform appendix ঘাষাশী জন্তুগুলোর জন্য অত্যন্ত জরুরী অঙ্গ; মানুষের জন্য তা অপ্রয়োজনীয়ই শুধু নয়, অনেক ক্ষেত্রে অত্যন্ত মারাত্মক হয়েও দেখা দেয়। এজন্য অনেকে আগভাগেই তার অপারেশন করিয়ে নেয়। জীব বিজ্ঞানীদের মতে, এই কাঁটাকার অন্ত্র সেই সময়কার স্মারক, যখন মানুষের পূর্ববংশ ঘাষ খেত। কেননা এই অন্ত্র ঘাষ চিবানোর জন্য খুবই জরুরী। এমনকি মানুষের ঝরে যাওয়া লেজের চিহ্ন স্বরূপ মেদণ্ডের নিম্নাগ্রে কয়েকটি অস্থি বর্তমান রয়েছে, যা বুঝাতে চায় যে, মানুষ এক সময় লেজযুক্ত জীব ছিল। মানুষ এককালে যেসব পর্যায়ে ছিল, সেসব পর্যায়ের মধ্য দিয়েই বর্তমানে অন্যান্য জীব-জন্তু অগ্রসর হচ্ছে এবং এগুলোই তা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে বাস্তব প্রমাণ সহকারে। মানবদেহের এসব অপ্রয়োজনীয় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের উল্লেখ করে লাল তার গ্রন্থের ৩৯ তম অধ্যায় লিখেছেন : “আসলে এক ঐতিহাসিক প্রমাণ হিসেবেই এগুলোর প্রত্যেকটিকে মানুষের দেহে যুক্ত করে দেয়া হয়েছে। এগুলো তার দীর্ঘ অতীতকে প্রকট ও প্রকাশ করে। এদের এ ছাড়া অন্য কোনো তাৎপর্য থাকতে পারে বলে মনে করা যায় না।”৮
ডারউইন লিখেছেন : “সমগ্র উচ্চতর গুণপনা ও যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও মানুষ এখন পর্যন্ত নিজের দেহের মধ্যে সেকালের অমোচনীয় চিহ্নসমূহ বহন করে চলছে; যখন সে নিম্নমানের জীবের আকৃতিতে ছিল।”৯
এই মতবাদটি সম্পর্কে একটা প্রশ্ন ওঠে। তাহলো ক্রমবিবর্তনের এই কার্যটি কিভাবে সাধিত হয়েছে? এর কার্যকলাপ ও অনুপ্রেরক কি ছিল? এই প্রশ্নের জবাবে অনেকগুলো মতবাদ উপস্থাপন করা হয়েছে। লাল তাঁর লিখিত Organic Evolution গ্রন্থে ছয়টি কারণ উল্লেখ করেছেন। যার সারনির্যাস হলো, প্রত্যেকটি প্রজাতির কতিপয় ব্যক্তিসত্তার মধ্যে কিছু পার্থক্যকারী বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি হয়ে যায়। যেমন-কিছু সংখ্যক অন্যান্যদের অপেক্ষা অনেক বড় হয়ে যায়। কতকগুলো অধিকতর তীক্ষ্ণ ও শক্তিশালী হয়। এগুলোর এ পার্থক্যধর্মী বিশেষত্ব প্রজনন ও বংশানুক্রমিকতার মাধ্যমে পরবর্তী বংশধরদের মধ্যে সংক্রমিত হয়। আর পারস্পরিক প্রতিযোগিতায় এবং নৈসর্গিক ঘটনা-দুর্ঘটনাসমূহে পার্থক্যকারী বিশেষত্ব সম্পন্ন এই স্বতন্ত্র ব্যক্তিসত্তাগুলোই রক্ষা পায় এবং বেঁচে যায়। এই কার্যক্রম অব্যাহতভাবে চলতে থাকে এবং প্রত্যেক পরবর্তী বংশে পূর্ববর্তী বংশের পার্থক্যধর্মী বিশেষত্বসমূহ বারবার সংরক্ষিত হতে থাকে এবং এভাবেই সম্মুখের দিকে অগ্রসর হতে থাকে। শেষ পর্যন্ত দীর্ঘকাল পরে সে বিশেষত্বগুলো এত বিপুল পরিমাণে সঞ্চিত হয়ে যায় যে, পূর্ববর্তী প্রজাতির ব্যক্তিসত্তা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ও ভিন্নতর প্রজাতীয় রূপ পরিগ্রহ করে নেয়।
এই পার্থক্যধর্মী বিশেষত্বসমূহ কেমন করে উন্মোচিত হয়। এ পর্যায়ে প্রথমে এই ধারণা উপস্থাপিত করা হয়েছিল যে, অঙ্গ-প্রতঙ্গের ব্যবহার ও অপব্যবহার কিংবা বাহ্যিক পারিপার্শ্বিকতাই এগুলোর স্রষ্টা। পরে অপর একটি মতবাদ দাঁড় করানো হয়েছে, তা হচ্ছে, এই পার্থক্যটা ক্রমাগতভাবে কোনো প্রজাতির কতিপয় ব্যক্তিসত্তা লাভ করে বসে। কিন্তু আধুনিকতম মতবাদ এই দুটিকে একত্রিত করে দিয়েছে। সিম্পসন তাঁর Meaning of Evolution গ্রন্থে লিখেছেন : “বিবর্তন সংক্রান্ত মতবাদ পর্যায়ে দীর্ঘ বৈজ্ঞানিক পর্যালোচনার পর কথাবার্তা এখানে এসে ঠেকেছে যে, ক্রমবিকাশমূলক পরিবর্তনসমূহ জন্মগতভাবে স্বতঃই প্রকাশমান হয়ে পড়ে। অথবা পারিপার্শ্বিকতার প্রভাবে কোনো বংশের কতিপয় ব্যক্তিসত্তা তা লাভ করে বসে। অর্থাৎ জীবনের অভিব্যক্তিমূলক ইতিহাসে যে সব চূড়ান্ত সিদ্ধান্তকারী কার্যকারণ সক্রিয় হয়ে রয়েছে তা অভ্যন্তরীণ ছিল, অথবা ছিল বাহ্যিক। এক্ষণে একথা অধিকতর স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, এই বিরোধের আলোচনা সম্পূর্ণ অর্থহীন। এ দুটি দৃষ্টিকোণের কোনো একটিতেও প্রকৃত সত্য নিহিত নেই। বরং তা তৃতীয় দৃষ্টিকোণে নিহিত রয়েছে। আর তা হচ্ছে, অভিব্যক্তির কার্যক্রমে উভয় ধরণের প্রভাব কার্যকর রয়েছে।”১০
পর্যালোচনা
উপরোক্ত আলোচনার মাধ্যমে খুবই সংক্ষিপ্তভাবে অত্যন্ত সহজ সরল ও সাধাসিধা ভঙ্গিতে বিবর্তন বা অভিব্যক্তিবাদ পর্যায়ে বিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ উপস্থাপন করতে চেষ্টা করেছি। বিস্তারিত ও পুঙ্খানুপুঙ্খ পর্যালোচনা বা সমালোচনা এখানে সম্ভব নয় বলে মাত্র কয়েকটি মৌলিক বিষয়ের পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ করতে চেষ্টা করছি।
১. বিভিন্ন প্রাণীর উচ্চ নিম্নস্তরের বিন্যাস সর্বপ্রথম আলোচ্য, এই ধরনের বিন্যাস ও পরম্পরা দাঁড় করানো সামষ্টিক অর্থে ঠিক কিনা, সে প্রশ্ন না তুলে আমরা এই প্রশ্ন তুলতে চাই যে, নিছক এই বিন্যাস বা পরম্পরা এ কথা কি করে প্রমাণিত করতে পারে যে, প্রত্যেকটি পরবর্তী প্রজাতি পূর্ববর্তী প্রজাতি থেকে নির্গত হয়েছে? এই মতবাদকে বাদ দিয়ে যদি দাবি করা হয় যে, প্রত্যেকটি প্রজাতি কালগত বিন্যাস বা পরম্পরা অনুযায়ী আলাদা আলাদাভাবে অস্তিত্ব লাভ করেছে, তাহলে পূর্বোক্ত প্রকল্পটির অগ্রাধিকার পাওয়ার এবং একটির তুলনায় সেটিকেই সত্য ও সঠিক মেনে নেয়ার কি কারণ থাকতে পারে? এই শেষোক্ত প্রকল্পটিকে ভুলই বা বলা হবে কোন যুক্তিতে? এহেন অবস্থার একটা ব্যাখ্যা এরূপও তো দেয়া যেতে পারে যে, নিম্নতর ও উচ্চতর সৃষ্টির মধ্যকার পার্থক্যটা আসলে প্রজাতীয় পার্থক্য, কলগত বিন্যাস ও পরম্পরাই এগুলোর সৃষ্টিগত পরম্পরা প্রকাশ করেছে।
জীবনের সূচনাকালীন প্রাণী যদি সর্বপ্রথম অস্তিত্ব লাভ করতে পারে, তাহলে জীবনের অন্যান্য প্রকার ও প্রজাতিসমূহ প্রথমবারেই অস্তিত্ব লাভ করতে পারেনি কেন? সেরূপ অস্তিত্ব লাভ করা যে অসম্ভব বা অবৈজ্ঞানিক, তা মনে করা হবে কোন যুক্তির বলে?
মাটির স্তর সংক্রান্ত তত্ত্ব ও তথ্যাদি থেকে জানা যায়, ভূপৃষ্ঠে সর্বপ্রথম নিম্ন শ্রেণির জীবের অস্তিত্ব ছিল। উচ্চশ্রেণি জীবের আগমন ঘটেছে তৎপরবর্তীকালে। কিন্তু এ থেকে একথা কি করে প্রমাণিত হয় যে, শেষের দিকে আগত প্রাণী প্রথমে আগত প্রাণীকূল থেকে বংশানুক্রমিক ভাবে অস্তিত্ব লাভ করেছে? এ থেকে পর্যায়ক্রমিক আগমন বা অস্তিত্ব লাভের কথা তো প্রমাণিত হয়, কিন্তু তা অভিব্যক্তিমূলক জন্মলাভের প্রমাণ হয় কিভাবে? সামুদ্রিক ভ্রমণের ইতিহাস বলে, প্রথম দিকে হালবৈঠাধারী নৌকা চালানো হয়েছে, পরে পালতোলা নৌকা ব্যবহৃত হয়েছে। এরপরে পাম্প শক্তির বলে বড় বড় জাহাজ চালিয়েছে। এক্ষণে কি করে বলা যেতে পারে যে, এসব নৌকা জাহাজের প্রতি পরবর্তী বাহনটি পূর্ববর্তী বাহনটির গর্ভজাত? তা কিছুতেই বলা যায় না। বরং সত্যি কথা হচ্ছে, প্রত্যেকটি বাহনই স্বতন্ত্রভাবে নির্মিত ও ব্যবহৃত হয়েছে, পার্থক্য হচ্ছে আগে ও পরের মাত্র।
জীবাশ্ম (Fossile) অধ্যয়ন থেকে জানা গেছে, প্রাচীনতম কালে ভূপৃষ্ঠে এমন এমন অসংখ্য প্রজাতি বসবাস করত, যার অস্তিত্ব বর্তমানে কোথায়ও খুঁজে পাওয়া যাবে না। সে সব সম্পর্কে এক্ষণে মনে করা হয় যে, তা বর্তমানের জীব-প্রাণীসমূহের অভিব্যক্তি পূর্ব আকৃতি ছিল। একটি যাদুঘরে হরিণ প্রজাতির জন্তুর তিনটি প্রস্তরায়িত মাথার খুলি পড়ে ছিল। তিনটি খুলিই সুবিন্যস্তভাবে একটির পর অন্যটি একই কাতারে সাজিয়ে রাখা হয়েছিল। এই খুলিগুলো বাহ্যত একই ধরনের ছিল। অবশ্য এই তিনটি খুলির মধ্যে
একটা বিশেষ পার্থক্য ছিল। প্রথম খুলিটির শিং ও পার্শ কপালের মধ্যকার দূরত্ব দুই ইঞ্চি পরিমাণ ছিল, দ্বিতীয়টিতে এই দূরত্ব দেড় ইঞ্চি পরিমাণ এবং তৃতীয়টিতে ছিল এক ইঞ্চি পরিমাণে। প্রাণী বিজ্ঞানীদের দৃষ্টিতে এটাই অভিব্যক্তির অকাট্য প্রমাণ, একটি বংশজাত কিভাবে অভিব্যক্তির ধারা অবলম্বন করে সম্মুখে অগ্রসর হয়েছে, তা এ থেকেই জানা যায় বলে তাদের দাবি। কয়েক টুকরা অস্থি বিভিন্ন স্থান থেকে কুড়িয়ে এনে একত্রিত করে মনে মনে সেগুলোর পরস্পরিক বিন্যাস ও পরম্পরা সাজানো সহজ হলেও বাস্তবতার সাথে তার দূরতম সম্পর্কও খুঁজে পাওয়া যাবে না। এগুলো ভিন্ন ভিন্ন ও স্বতন্ত্র প্রজাতি নয়, তার কি কোনো প্রমাণ আছে? এগুলোকে ক্রমবিবর্তনমুখী একটি প্রজাতির আগের পরের ব্যক্তি সত্তা ধরে নেয়ার পক্ষে কোন অকাট্য যুক্তিটি পেশ করা যেতে পারে? আসলে এই অস্থিগুলোকে মিলিয়ে একটা মানসিক ‘প্রকল্প’-কে মনে করানোর চেষ্টা করা হয়েছে মাত্র। অথচ এর অপর একটি ব্যাখ্যাও দেয়া হয়েছে তদ্দ্বারা প্রকৃত সত্য অনুধাবন অধিকতর সহজসাধ্য।
২. জীব ও প্রাণীসমূহের দৈহিক যোগ্যতা ক্ষমতা পর্যায়ের পারস্পরিক সাদৃশ্যকে অভিব্যক্তিবাদের প্রমাণ স্বরূপ পেশ করা হয়েছে। আমেরিকার যাদুঘরে প্রাকৃতিক ইতিহাস পর্যায়ের যেসব জিনিস সংগ্রহ করে রাখা হয়েছে তন্মধ্যে মানুষ ও ঘোড়ার দুটি কংকালও রয়েছে। একটা বিশেষ ভঙ্গিতে পরস্পর মিলিয়ে ও সাজিয়ে দুটিকে রাখা হয়েছে। দেখা যায়, ঘোড়াটি তার সম্মুখ ভাগের পা দুটিকে ঊর্ধ্বে তুলে পিছন দিকের দুটি পায়ের ওপর ভর করে দাঁড়িয়ে রয়েছে। আর মানুষটির হাত দুখানি যথারীতি ঝুলিয়ে দেয়ার পরিবর্তে ঊর্ধ্বে তুলে ধরা হয়েছে। এরূপ কংকাল বাহ্যত পরস্পর সৌসাদৃশ্যপূর্ণ মনে হয়। এতদ্বারা মানুষকে অন্যান্য স্তন্যপায়ী জন্তুর বংশধর বুঝানোই এর আসল উদ্দেশ্য। মানুষ দাঁড়াবার চেষ্টা করতে গিয়ে সোজা খাড়া হয়ে গেছে বলে মনে হচ্ছে। উভয়ই একই বংশজাত না হলে এতটা সৌসাদৃশ্যপূর্ণ হলো কি করে, তা বোঝানোই এর মূলে নিহিত একমাত্র ইচ্ছা।
কিন্তু মানুষ ও জন্তুর মধ্যে নিছক দৈহিক ও আকৃতিক সৌসাদৃশ্য উভয়ের অভিন্ন বংশজাত হওয়ার কথা প্রমাণ করতে পারে না। কেননা মানুষ বুদ্ধিবৃত্তিক বিশেষত্বে অন্যান্য সমস্ত প্রকারের জীব-জন্তুর ওপর এতটা প্রাধান্য ও বৈশিষ্ট্যের অধিকারী যে, এদুটিকে কোনো প্রকারে ও কোনো উপায়েই পরস্পরের বংশধর প্রমাণ করা সম্ভবপর নয়। প্লাস্টিক নির্মিত একটা মানবদেহ বাহ্যিক আকৃতির দিক দিয়ে প্রকৃত মানব দেহের সঙ্গে শতকরা একশ ভাগ সাদৃশ্যপূর্ণ হলেও প্রথমটিকে একটা প্রকৃত মানব দেহ প্রমাণ করার কি কোনো উপায় থাকতে পারে? উপরন্তু মানুষ ও জীব-জন্তুর দেহ পরস্পর সাদৃশ্যপূর্ণ হলে; কিংবা বিশেষত্বের দিক দিয়ে উভয়ের মধ্যে কোনরূপ নৈকট্য পাওয়া গেলেও মানুষ অন্যান্য জীব-জন্তুর ঔরসজাত সন্তান, তা প্রমাণিত হয়েছে বলে কি করে দাবি করা যেতে পারে? লক্ষ লক্ষ কাঁচা ইট স্তুপীকৃত করে আগুন দিয়ে পোড়ানো হয়। ইটগুলো দেখতে প্রায় একই রকম মনে হয়। তাই বলে এই ইটগুলোর প্রত্যেকটি অপরগুলোর গর্ভজাত-তা মনে করা যেতে পারে কি? এগুলোর মধ্যে বংশানুক্রমিকতা ও প্রজনন প্রক্রিয়া কার্যকর রয়েছে বলে আজ পর্যন্ত কি কোনো প্রমাণ পাওয়া গেছে? সৌসাদৃশ্যের এরূপ অর্থ গ্রহণ বিজ্ঞানের কোনো প্রতিষ্ঠিত সত্যের ওপর ভিত্তিশীল বলে দাবি করা যেতে পারে?
এরূপ অবস্থায় একটা ব্যাখ্যা এতদপেক্ষাও সুন্দর ও অধিকতর যুক্তিসঙ্গতভাবে দেয়া যেতে পারে। তা হচ্ছে, জীব-জন্তুর স্রষ্টা ভালো করেই জানতেন যে, মানুষ ও জীব-জন্তুকে একই প্রকারের পরিবেশগত অবস্থার মধ্যে জীবন-যাপন করতে হবে, এই কারণে তিনি অতি স্বাভাবিকভাবেই এসবের দেহ কাঠামোর মধ্যে বহুদিকের এককতা, অভিন্নতা, সৌসাদৃশ্য রেখে দিয়েছেন। জীবনের যদি বিভিন্ন ধরনের পার্থক্যপূর্ণ পরিবেশ পারিপার্শ্বিকতার মধ্যে জীবন-যাপন করতে হতো, তা হলে নিশ্চিয়ই এই সৌসাদৃশ্য রক্ষা করা হতো না, প্রত্যেকটির কাঠামোগত বিশেষত্ব সম্পূর্ণরূপে বিভিন্ন হতো। কিন্তু সত্য কথা হচ্ছে, তাদের সবাইকে একই ধরনের ভৌগোলিক ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে দিনাতিপাত করতে হচ্ছে বংশানুক্রমে যুগের পর যুগ ধরে। এটাই তাদের নিয়তি, প্রাকৃতিক বিধান। এই কারণেই তাদের সকলের দেহ কাঠামোকে অভিন্ন মৌলিকতার অধিকারী বানিয়ে দেয়া হয়েছে। অনুরূপভাবে মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীর ভ্রূণের সৌসাদৃশ্য আছে বলে তার ভিত্তিতে এসবের একই বংশজাত হওয়ার কথা প্রমাণ করতে যাওয়া কোনক্রমেই যুক্তিসঙ্গত বলে মেনে নেয়া যায় না। তা থেকে বড় জোর শুধু এতটুকুই প্রমাণিত হতে পারে যে, বিভিন্ন প্রজাতি ক্রমবৃদ্ধি লাভের একেবারে প্রাথমিক পর্যায়ে পারস্পরিক অভিন্ন আকৃতির হয়ে থাকে। (অথবা বলা যায়, ভ্রূণের এই অভিন্নতা চোখে দেখা গেলেও তা প্রকৃতপক্ষে সত্য নয়)। পরে ক্রমবৃদ্ধি লাভের শেষ পর্যায়ে তাদের মধ্যকার পার্থক্য ভিন্নতা স্পষ্ট ও প্রকট হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু তাতে তারা সব একই বংশজাত এমন কথা তো কিছুতেই প্রমাণিত হতে পারে না। আসলে এই যুক্তি দেখিয়ে একটা প্রকৃত ব্যাপারকে ভিত্তি করে একটা সম্পূর্ণ ভুল ও অসত্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে।
৩. বিবর্তন বা অভিব্যক্তি কার্যকারণ অনুপ্রেরক পর্যায়ে যা কিছু বলা হয়েছে, তা এর চেয়েও অধিকতর হাস্যকর। এ দর্শনের প্রাণ হচ্ছে বিবর্তন ও পরিবর্তনের পার্থক্যধর্মী বিশেষত্বসমূহ। এ পর্যায়ে লাল লিখেছেন, কতিপয় ব্যক্তিসত্তার মধ্যে পরিবর্তন সূচিত হওয়াই বিবর্তন অভিব্যক্তির প্রথম ও সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ কারণ তার বক্তব্য এই : ‘পরিবর্তন (Variation) স্বতঃই বিবর্তন কার্যক্রমের কারণ হতে পারে।’ ১১
‘Animal Biolgy’ গ্রন্থের লেখক হল্ডেন ও হাক্সালির ভাষায় ‘প্রাকৃতিক নির্বাচন’ আসলে ‘পরিবর্তনসমূহের নির্বাচন (Selection of Mutations) এর নাম১২ তারা আরও লিখেছেন, যন্ত্র নির্মাণের ইতিহাসে আমরা যেমন একটি বিকাশ মাত্র ও ক্রমউৎকর্ষমূলক কার্যক্রম লক্ষ্য করছি, মানুষ ও জীব-জন্তুর ক্ষেত্রেও অনুরূপভাবে বিবর্তন সঙ্ঘটিত হয়েছে। অতঃপর লিখেছেন: “জীব-জন্তু ও যন্ত্রের মধ্যে একটা বড় পার্থক্য রয়েছে। যন্ত্রের নীল নকশা সরাসরি মানুষ নিজে তৈরি করে। অথচ জৈবিক বিবর্তনের ক্ষেত্রে নকশা প্রস্তুতকারীর (Designer) স্থান নিয়েছে পরিবর্তন (Variation) যা প্রাণীলের মধ্যে সামগ্রিকভাবে কার্যকর। এই পরিবর্তনই প্রাথমিক পার্থক্য সৃষ্টি করে, প্রাকৃতিক নির্বাচনের চালুনি তার ওপরই কাজ করে।”১৩ এখানে একটা সত্য তত্ত্বকে ভিত্তি করে একটা ভুল যুক্তি অবতারণ করা হয়েছে। একই দম্পতির চারটি সন্তান সর্বদিক দিয়ে এক ও অভিন্ন হয়না, একথা সত্য। এদের মধ্যে কিছু না কিছু বৈসাদৃশ্য অবশ্যই থেকে যায়। এই কথাটি যতখানি সত্য, তার চাইতে অনেক বেশি ভুল হচ্ছে এই কথা যে, ছাগলের দেহকাঠামো বৃদ্ধি পেতে পেতে জিরাফের কাঠামো হয়ে যেতে পারে। উপরের প্রত্যেকটি কথা স্বীয় পরিমন্ডলে সত্য। কিন্তু তার পরিধির বাইরে সেই সত্যই সুস্পষ্ট মিথ্যা ও অসত্যে পরিণত হয়।
এছাড়া যে সব পরিবর্তন উপার্জিত হয় বলে ধরে নেয়া হয়েছে তারও কোনো তাৎপর্য খুঁজে পাওয়া যায়না। মনস্তাত্ত্বিক অধ্যয়ন বিশ্লেষণ থেকে জানা যায়, ব্যক্তিসত্তার মধ্যে জন্মগতভাবে পূর্ব থেকেই যেসব বিশেষত্ব বর্তমান নেই তা কেউই পরবর্তীকালে নিজের মধ্যে অর্জন করতে পারেনা। তাহলে প্রাচীন জীবসত্তাসূহ একটি প্রজাতি থেকে অন্য প্রজাতিতে রূপান্তরিত হওয়ার অভিনব ও বিস্ময়কর বিশেষত্বসমূহ নিজেদের মধ্যে কি করে সৃষ্টি করে নিতে সক্ষম হতে পারলো? প্রকৃতির অধ্যয়ন যে সম্ভাব্যতাকে আজ প্রমাণ করতে পারেনা, অতীতে সেই সম্ভাব্যতা বাস্তবায়িত হয়েছিল বলে আজ কোন দলিলের ভিত্তিতে দাবি করা যেতে পারে?
প্রখ্যাত দার্শনিক হার্বার্ট স্পেন্সার অঙ্গ প্রত্যঙ্গের ব্যবহার অব্যবহারের বংশানুক্রমিক স্থানান্তরে বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি বলতেন, ‘আমার হাত এতোটা খাটো এই কারণে যে, আমার পিতা-মাতা তাদের হাত দ্বারা কোনরূপ শ্রমের কাজ করতেন না।’ বস্তুত পাশ্চাত্য বিজ্ঞানীরা অভিব্যক্তিকে বাস্তব সত্য প্রমাণ করার জন্য কত যে হাস্যকর কথাবর্তা বলতে পারেন, তা উপরোক্ত উক্তি থেকে নিঃসন্দেহে বোঝা যায়। স্পেন্সারের খাটো হাত যদি তাঁর পিতা মাতা থেকে সত্যই উত্তরাধিকার সূত্রে হয়ে থাকে, তাহলে এই উত্তরাধিকার তার নিজের বংশধরদের মধ্যেও সংক্রমিত ও স্থানান্তরিত হওয়া অবধারিত ছিল। শুধু তা-ই নয়, প্রত্যেকটি বংশেই এই ঘটনা সঙ্ঘটিত হওয়া উচিৎ ছিল। এমনকি, যাদের কোনো অঙ্গ কোনো দুর্ঘটনায় পড়ে বিনষ্ট হয়ে গেছে, তাদের বংশ অনুরূপ অঙ্গহীন মানুষের নতুন একটা প্রজাতি গড়ে ওঠা বাঞ্ছনীয় ছিল। কিন্তু তা যখন হয়নি, তখন এই প্রকল্পও ভিত্তিহীন হয়ে গেছে।**
বিবর্তনবাদীদের বক্তব্য হচ্ছে, একটি প্রজাতির অস্তিত্ব লাভের জন্য একটা ‘কারণ’ থাকা অবশ্যক। বিবর্তনবাদ এমনিই একটি ‘কারণ’ চিহ্নিত করছে, কিন্তু স্বতন্ত্রভাবে প্রজাতি সৃষ্টির মতবাদ কোনো অনুভবযোগ্য ও জ্ঞানগত কারণ নির্ধারণ করছে না।
এর জবাবে বলতে চাই, এটাই যদি বিবর্তনবাদের বিশেষত্ব হয়ে থাকে, তাহলে কথাটি ঠিক এই পর্যায়ের মনে হবে, যেমন- কেউ জীব সত্তার ব্যাখ্যায় বলে দিলো, সমস্ত জিনিসই স্বীয় মাতৃগর্ভে জন্ম গ্রহণ করেছে। আর এই কথা বলে যেমন-মনে অহংকার বোধ করবে যে, সেতো জীবত্বের ব্যাখ্যা দিয়েই ফেলেছে। আসলে এই ব্যাখ্যাটি যেমন—একটা মধ্যবর্তী কথা, পূর্বোক্তটিও তেমনি মধ্যবর্তী অবস্থার বিশ্লেষণ মাত্র। কিন্তু মধ্যবর্তী ব্যাখ্যা কখনোই কোনো প্রশ্নের চূড়ান্ত জবাব হতে পারেনা। বিবর্তনবাদীরা তাদের এই কথাকে আসল প্রশ্নের জবাব বলে অভিহিত করতে পারেন, যদি প্রথম জীবের অস্তিত্ব লাভের কারণসমূহ তাদের করায়ত্ত হয়ে থাকে। জিরাফ অন্যান্য ক্ষুরধারী চতুষ্পদ জন্তু থেকে বিবর্তনের মাধ্যমে অস্তিত্ব লাভ করেছে। আর ক্ষুরধারী চতুষ্পদ জন্তুগুলি হামাগুড়ি দিয়ে চলা জীবগুলো থেকে বের হয়ে এসেছে। এভাবে প্রতিটি প্রাণীর পশ্চাতে অপর একটি প্রাণী রয়েছে, তা-ই এর স্রষ্টা। বিবর্তনবাদীদের এই তত্ত্ব বিশ্লেষণে প্রশ্ন জাগে, এই ধারাবাহিকতার পিছনের দিক এসে যে প্রাণীটি পর্যন্ত গিয়ে ঠেকেছে তার স্রষ্টা কে?
Pasteur একথা পূর্ণমাত্রায় প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছেন, যে কোনো প্রাণী-ই- এমনকি অনুবীক্ষণী পোকাও শুধুমাত্র জীবনের সাহায্যেই জন্ম লাভ করতে পারে। তাহলে যে প্রাথমিক রূপ থেকে জীবনের সূচনা হয়েছে বলে ধরে নেয়া হয়েছে তাঁকে অস্তিত্বদান করলো কে? বিবর্তনবাদের দাবি অনুযায়ী জীবনের সমস্ত অতীত স্তর বর্তমান সময় পর্যন্ত পৃথিবীর বুকে বিরাজমান রয়েছে। তাহলে জড় যে জীবনটার সহসা আত্মপ্রকাশ ঘটিয়েছিল, এক্ষণে সেটি আমরা দেখতে পাচ্ছিনা কেন?
বিজ্ঞানের নিকট এই প্রশ্নের কোনো জবাব নাই। সিম্পসন যেমন- বলেছেন, সর্বশেষ ও চূড়ান্ত মহাসত্য সম্পর্কে কিছু জানতে পারা বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও তত্ত্বানুসন্ধানের আওতার বাইরে অবস্থিত। বরং সম্ভবত মানুষের কল্পনা শক্তিও সে পর্যন্ত পৌঁছতে পারে না। ১৪
তিনি লিখেছেন : “জীবন কী করে সৃষ্টি হলো? এই প্রশ্নের সততানিষ্ঠ জবাব হচ্ছে, এই প্রশ্নের জবাব আমাদের জানা নেই। অবশ্য তার কিছু লক্ষণ প্রতীকের কথা আমরা বলতে পারি।” ১৫
‘লক্ষণ আর প্রতীক’ বলে তিনি কি বোঝাতে চেয়েছেন? সম্ভবত তা এই যে, পানির মধ্যে দীর্ঘকাল ধরে বিশেষ কার্যক্রম চলার ফলে এই ঘটনাটি স্বতঃই সঙ্ঘটিত হয়েছে। সিম্পসন লিখেছেন: ‘জীবনের একেবারে সেই প্রাথমিক রূপ যে কি ছিল বিজ্ঞান এখন পর্যন্ত তা জানতে পারেনি। বর্তমান অবস্থায় তা কখনও জানা যাবে, তারও কোনো আশা নেই। তবে আমাদের অধ্যয়ন এই সম্ভাব্যতার সাক্ষ্য দেয়-বরং এই শক্ত অনুমান পর্যন্ত পৌঁছে দেয় যে, জীবন অবৃদ্ধি প্রবণ উপাদান থেকে স্বতঃই (Spontaneously) অস্তিত্ব লাভ করেছিল। আর কোনরূপ অতি প্রাকৃতিক শক্তির হস্তক্ষেপ ছাড়াই নিছক বস্তুগত কার্যক্রমের সাহায্যে এই ঘটনা সঙ্ঘটিত হয়েছিল। এই অজানা সূচনা থেকে রূপান্তরিত হয়ে অন্যান্য সমস্ত জীব প্রজাতি অস্তিত্ব লাভ করেছে।” ১৬
(**বিবর্তনবাদ জীবন ও তার বাহ্য প্রকাশসমূহের যে ব্যখ্যা ও বিশ্লেষণ উপস্থাপিত করেছে, তাতে সুস্পষ্টরূপে দুটি শূণ্যতা বিরাজ করে। একটি এই যে, এই ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ আদিম নয়, বরং মধ্যবর্তী ব্যাখ্যা। আর দ্বিতীয় হচ্ছে, স্বরূপের বিচারের এই ব্যাখ্যা ধর্মীয় ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ থেকে ভিন্নতর কিছু নয়।)
বস্তুবাদী বিজ্ঞানীদের এরূপ কথা নিঃসন্দেহে বিস্ময়কর। ধর্ম যদি বলে যে, জীবন কোনরূপ পূর্ববর্তী অস্তিত্ব ছাড়াই একটা বিশেষ সময়ে প্রথমবারের মতো অস্তিত্বলাভ করেছিল, তাহলে বিজ্ঞানীরা তা শুনে নাক সিটকাতে শুরু করেন। কিন্তু বিজ্ঞানী বলে পরিচিত ও খ্যাতিপ্রাপ্ত লোকদের উত্তরূপ কথা সহজেই বোধগম্য হয়ে যায় এবং তারা ‘মহাবিজ্ঞানী’ বলে অভিনন্দিত হন। বস্তুত সিম্পসনের উপরোক্ত স্বীকারোক্তি এবং ধর্মের বক্তব্যে মৌলিক কোনো পার্থক্য নেই। আসল কথা হচ্ছে ব্যাপারটিকে মাঝখান থেকে না দেখে সামগ্রিকভাবে বিচার বিবেচনা করা হলে স্পষ্ট ও অকাট্যভাবে জানা যাবে যে, ধর্ম ও বিজ্ঞান উভয়ই ‘বিশেষ সৃষ্টিকর্ম’ (Special creation) স্বীকার করে। তবে পার্থক্য শুধু এটুকুই হয় যে, বিজ্ঞান শুধু প্রথম প্রাণী সম্পর্কে এই কথা স্বীকার করে, আর ধর্ম এই আকীদা বিশ্বাস করে জীব-জন্তুর সময় প্রজাতি সম্পর্কে। প্রশ্ন হচ্ছে, বিজ্ঞান জীবের প্রথম উন্মেষ বা প্রকাশের বিশ্লেষণ যে ভিত্তিটিকে মেনে নিচ্ছে, জীবনের বাড়তি প্রকাশের বিশ্লেষণেও সেই ভিত্তিটিকে মেনে নিচ্ছে না কেন? এ পর্যায়ে সময়ের প্রশ্নটি সম্পূর্ণ অবান্তর ব্যাপার। আমরা বিশ্বাস করি, প্রতিটি প্রজাতি স্বতন্ত্রভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে। তাদের সৃষ্টি কর্মে কতটা সময় লেগেছে, তা এক আপেক্ষিক প্রশ্ন। মূল বিষয়ের ওপর তার কোনই প্রভাব নেই বা তার সাথে এর কোনো সম্পর্কও নেই।
প্রজাতিসমূহের অস্তিত্বের যে ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে তাও স্বীয় স্বরূপে ধর্মে দেয়া ব্যাখ্যা থেকে ভিন্নতর কিছু নয়। বিবেচনা করা যেতে পারে, ‘প্রজাতি’ কাকে বলে? ভূপৃষ্ঠে প্রায় পাঁচ লক্ষ প্রকারের জীব পাওয়া যায়। এই সংখ্যার প্রত্যেকটি প্রাণী অন্যান্য প্রাণী থেকে কি সম্পূর্ণ ভাবে ভিন্নতর?…… না নিশ্চয়ই নয়। এগুলো অসংখ্য দিক দিয়ে পারস্পরিক সৌসাদৃশ্য সম্পন্ন। মাত্র কতিপয় দিকের পার্থক্যই তাদের আলাদা প্রজাতি বানিয়ে দিয়েছে। এই প্রজাতীর পার্থক্য কি করে হলো? আমরা বলব, প্রত্যেকটি প্রজাতি স্বীয় বর্তমান পার্থক্যপূর্ণ বিশেষত্বসহ প্রথম দিনই সৃষ্টি করা হয়েছে। বিজ্ঞানের দাবি হচ্ছে, শুরুতে একই প্রকারের জীবন ছিল, তার বংশধরদের মধ্যে কোনো কোনো কার্যকারণ হেতু পূর্ব পুরুষদের থেকে সামান্য সামান্য পার্থক্য’ হতে থাকে। এই পার্থক্যই সুদীর্ঘকালের পরিক্রমায় কোনো কোনো ব্যক্তিসত্তায় প্রকট মাত্রায় একীভূত হয়ে গেল। আর তখনই তা স্বতন্ত্র একটা প্রজাতিরূপ পেয়ে গেল।
এ দুটি ব্যাখ্যার মাঝে পরিমাণগত পার্থক্য অবশ্য আছে, কিন্তু স্বরূপতার দিক দিয়েও কি কোনো পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়? কোনো বংশের কতিপয় ব্যক্তিসত্তায় স্বীয় অপরাপর স্বজাতীয়দের তুলনায় যে পরিবর্তনটার কথা স্বীকার করে নেয়া হয়েছে যে কারণে তা সে বংশের অপরাপর ব্যক্তিসত্তা’ থেকে স্বতন্ত্র বিশিষ্ট হয়ে দাঁড়ায়, সে স্থলে যদি প্রজাতি শব্দটি বসিয়ে দেয়া যায়, তাহলে সহজেই জানা যাবে যে, প্রকৃত ব্যপারের দিক দিয়ে ধর্ম ও বিজ্ঞানের বক্তব্য কোনো পার্থক্য নেই। ধর্ম ‘প্রজাতি সৃষ্ট’ বলে যে জিনিসটিকে বোঝাচ্ছে – ভিন্নতর শব্দের আবরণে।
নিষ্প্রাণ জগতে জীবনের প্রথম সৃষ্টি সাধনের কার্যকারণ যদি পৃথিবী ও আকাশ মণ্ডলে কার্যকর থাকে, তা হলে সেই কার্যকারণ অন্যান্য প্রকারের জীবন সৃষ্টিকর্মে অক্ষম প্রমাণিত হবে কেন? অনুরূপভাবে এ বিশ্বলোককে যখন সৃষ্টি করা হয়েছিল, নির্মাণ সামগ্রীসমূহ কোথেকে সংগৃহীত হয়েছিল, প্রস্তরখণ্ডসমূহ একটির ওপর অপরটি এমন সুন্দরভাবে রক্ষিত হলো কিভাবে, ঠিক প্রয়োজন ও পরিমাণ অনুযায়ী কিভাবে তৈরি হয়ে গেল? তাহলে এ রকম আরও অসংখ্য ইমারত নির্মিত হতে থাকল না কেন এ যাবৎ পর্যন্ত? ……. ইত্যাদি ইত্যাদি। তিনি যদি এইসব এবং এ ধরনের অন্যান্য প্রশ্নাবলীর সান্ত্বনাদায়ক জবাব দিতে সক্ষম হন তাহলে তাজমহলের নির্মিত হওয়ার দাবি মেনে নেয়া হবে। কিন্তু এসব প্রশ্নের জবাব দেয়া যদি তার পক্ষে সম্ভব না হয় – সম্ভব যে নয় তো সুস্পষ্ট – তাহলে উক্ত কথাটি একটি মিথ্যা ও ভিত্তিহীন উক্তি হয়েই থাকবে, তার যথার্থতা কেউ মেনে নেবে না। উল্লেখিত প্রশ্নগুলো নিছক ব্যাখ্যামূলক নয়, এ হচ্ছে প্রদত্ত ব্যাখ্যার জবাবে দলীল প্রমাণের দাবি।
বিবর্তনবাদ সংক্রান্ত বিজ্ঞানীদের ব্যাখ্যার জবাবেও বহু সংখ্যক প্রশ্ন মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। প্রশ্ন ওঠে, তা কি করে ঘটলো, কল্পিত পরিবর্তনসমূহের মূলে কার্যকরণ ও অনুপ্রেরক কি ছিল? অতীতে ঘটেছে বলে যে বিবর্তনমূলক কার্যক্রমকে মেনে নেয়া হচ্ছে, তাকে আজও এক্ষণে আমরা দেখতে পাচ্ছিনা কেন? এ প্রশ্নগুলোর কোনো যথার্থ জবাব দেয়া বিবর্তনবাদী বিজ্ঞানীদের পক্ষে সম্ভবপর নয়, জবাব দিতে তারা সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হয়েছেন। এ কথার সত্যতায় একবিন্দু সন্দেহের অবকাশ নেই। এ পর্যায়ে যতগুলো ব্যাখ্যা ও কারণ উপস্থাপিত করা হয়েছে সে সম্পর্কে স্বয়ং বিজ্ঞানীদের পক্ষ থেকে প্রচন্ড সমালোচনার ঝড় উঠেছে। কোনো একটি ব্যাখ্যায়ও সম্পূর্ণ একমত হওয়া তাঁদের পক্ষে সম্ভবপর হয়নি। তার অর্থ হচ্ছে, বিবর্তনবাদী মতবাদ যুক্তির কষ্টিপাথরে সম্পূর্ণ কৃত্রিম ও ভেজাল প্রমাণিত হয়েছে। কিন্তু বস্তুবাদী বিজ্ঞানীদের নিকট এই মতবাদটি এতই প্রিয় যে, তাদের কামনা হচ্ছে, কোনো যুক্তি বা প্রমাণ ছাড়াই তাকে সত্য বলে মেনে নেয়া হোক। এই উদ্দেশ্যে একটি চাকচিক্যপূর্ণ ও প্রতারণামূলক ধারণাও রচনা করা হয়েছে। এই পর্যায়ে এ. ঈ. মেন্ডারের বক্তব্য তুলে ধরছি। তিনি লিখেছেন : ‘আঙ্গিক বিবর্তন’ বাদের দুটি দিক। একটি হচ্ছে-সমগ্র জীবন্ত সত্তা বিবর্তিত হয়ে বর্তমান আকার-আকৃতি ধারণ করেছে। বিবর্তনের দ্বিতীয় ব্যাখ্যাটি হচ্ছে, বিবর্তন কি করে সঙ্ঘটিত হলো, তার কার্যকারণ ও অবস্থা কি ছিল? জীবন্ত সত্তাসমূহের মধ্যে বিবর্তন কার্যক্রম চলেছে, এটা কোনো নতুন প্রকল্প নয়। দুই হাজার বছর পূর্বে কোনো কোনো গ্রীক চিন্তাবিদ এই মতবাদ পেশ করেছিলেন। অতীতের দুই তিনটি বংশধরের জীবন কালে নবতর ঘটনা ও বাস্তবতা বিপুল পরিমাণ ধরা পড়েছে। সেই অনুযায়ী পরীক্ষণ কার্যক্রম চালানও হয়েছে। এক্ষণে এই মতবাদটি সর্বতোভাবে সত্যায়িত ও যথার্থ মতবাদ হয়ে দাঁড়িয়েছে। তার সমর্থনে লক্ষ লক্ষ ঘটনার (Facts) সমাবেশ হয়েছে। বিভিন্ন বিভাগের হাজার হাজার বিশেষজ্ঞের অভিমত-ও এর পক্ষে পাওয়া গেছে। এহেন ‘আঙ্গিক বিবর্তন’ মতবাদটির বক্তব্য হচ্ছে, সমস্ত জীবন্ত প্রজাতি উদ্ভিদ ও জীবজন্তু-উভয়ই আজকের দৃশ্যমান আকার-আকৃতিতে চিরকাল বর্তমান ছিল না। বরং দীর্ঘ পরিক্রমায় ওরা অসংখ্য পরিবর্তনের মাধ্যমে সাদাসিধা ও নিম্নমানের প্রাণী থেকে ধীরে ধীরে অস্তিত্ব লাভ করে এসেছে। বিবর্তনের অপর অংশ ডারউইনবাদ বা ‘নিউ ডারউইনিজম’ প্রভৃতি নামে পরিচিত। বিবর্তন সংক্রান্ত এই দ্বিতীয় ধরনের মতবাদসমূহ জীবজন্তুর ক্ষেত্রে বিবর্তন কার্যক্রম চলেছে একথা বলার জন্য আসেনি, বরং এগুলো এই মতবাদের ব্যাখ্যা করে মাত্র যে, পরিবর্তনসমূহ এভাবে সাধিত হয়েছে। এই দ্বিতীয় দিকটির কোনো কিছুই চূড়ান্ত ও অকাট্য বলে দাবি করার কোনো জিনিস আমাদের হাতে নেই। আসলে এ ধরনের সব মতবাদ পরীক্ষাধীন রয়েছে, তাতে অনেক পরিবর্তনও সাধিত হয়েছে। সর্বশেষ চূড়ান্ত ও পূর্ণাঙ্গ মতবাদ পর্যন্ত পৌঁছবার জন্য চেষ্টা অব্যাহতভাবে চলছে।১৭
এখানে ‘বিবর্তন’ ও ‘বিবর্তনের কারণ প্রদর্শন’ এই দুটি শব্দে যে বিভক্তি করা হয়েছে, তা বিভ্রান্তিকর। তার পরিবর্তে ‘বিবর্তন’ ও ‘বিবর্তনের প্রমাণ’ এরূপ বলা হলে বিভক্তিটা উত্তমভাবে করা যায়। এক ব্যক্তি যখন বলে, জীবনের সমস্ত বহিঃপ্রকাশ (Phenomenon) বিবর্তনের ফসল, তখন সাথে সাথেই প্রশ্ন ওঠে, এই বিবর্তনটা কী এবং তা কীভাবে প্রাণীকূলের ওপর কল্পিত কার্যক্রম পরিচালিত করে? এসব প্রশ্নের সান্ত্বনাদায়ক জবাব দিয়ে দিলে কথাটি মেনে নেয়া হবে। কিন্তু এসব প্রশ্নের যথার্থ জবাব দিতে না পারলে কার্যত আপনি এটাই প্রদর্শন করেন যে, আপনার দাবির স্বপক্ষে পেশ করার মতো কোনো দলীলই আপনার নিকট নেই।
বস্তুত বিবর্তনের কার্যকারণ সুপরিজ্ঞাত ও সুনির্দিষ্ট না হলে স্বতঃই প্রকাশ হয়ে পড়ে যে, বিবর্তনবাদ এখন পর্যন্ত প্রমাণের মুখাপেক্ষী। মনে হয়, বিবর্তনের এমন কোনো রূপ এখন পর্যন্ত ধরা পড়েনি যা প্রকৃতপক্ষে এসব ঘটনা সঙ্ঘটিত করাতে সক্ষম, যা এই মতবাদটিতে দাবি করা হয়েছে। এরূপ অবস্থায় বিবর্তনবাদকে একটা প্রমাণিত সত্য বলে দাবি করা এবং বিবর্তনের কার্যকারণসমূহ এখন পর্যন্ত বিবেচনাধীন বলা মূলত একটা প্রমাণহীন দাবি মেনে নেয়ার জন্য চাপ প্রয়োগ করা ছাড়া আর কিছুই নয়। কেউ যদি বলে, এই যে লক্ষ লক্ষ রেল ইঞ্জিন দুনিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে চলছে, আসলে এগুলো বড় বড় লৌহপিন্ড অবস্থায় পড়ে ছিল। পরে তা স্বতঃই সক্রিয় ও গতিশীল হয়ে তীব্রগতিতে দৌড়াতে শুরু করে দিল। পূর্বোদ্ধৃত কথাটি ঠিক এই শেষোক্ত কথাটির মতোই। এই বিস্ময়কর ব্যাপারটি কী করে ঘটল, লোকটিকে এই প্রশ্ন করা হলে সে বলে, ‘আমি এই ‘কী করে’র ব্যাখ্যা দিতে পারব না। তবে এ রকমটা যে হয়েছে, তা আমি নিঃসন্দেহে বিশ্বাস করি।” এইরূপ কথা বিজ্ঞানীদের নিকট কি মর্যাদা পেতে পারে?**
সত্যকথা এই যে, এরূপ অবস্থায় বিবর্তনবাদকে জীবনের প্রকাশমানতার একটা দিক ‘মনে করে নেয়া’ বিশ্লেষণই বলা যেতে পারে, ‘চূড়ান্তভাবে’ প্রমাণিত ও স্বীকৃত সত্য রূপে মেনে নেয়া কোনক্রমেই সম্ভব নয়। তার অর্থ এই দাঁড়ায় যে, বিজ্ঞানীরা উপরোক্ত ধরনের বিভক্তি সৃষ্টি করে যেন একথাই বলেছেন যে, ‘বিবর্তন মতবাদের পক্ষে আমাদের নিকট অকাট্য কোনো প্রমাণ না থাকলেও আমরা বিশ্বাস করি যে, সমস্ত জীবজন্তু বিবর্তনেরই উৎপাদন।’ জীবন সংক্রান্ত বিষয়াদিতে এ-ই যদি হয় বিজ্ঞানের ভূমিকা, তাহলে শেষ পর্যন্ত ধর্মীয় বিশ্বাস ও বৈজ্ঞানিক সত্যে – ধর্ম ও বিজ্ঞানের পার্থক্যটা কী থাকলো? বিজ্ঞানও তো সৃষ্টিলোকের ব্যাখ্যাদানের জন্য একটা ‘বিশ্বাস’ কেই দাঁড় করিয়েছে, যার স্বপক্ষে কোন প্রমাণ উপস্থাপনই তাদের পক্ষে সম্ভব হয়নি। অথচ এরূপ অভিযোগ আজ পর্যন্ত কেবল ধর্মের বিরুদ্ধেই তোলা হতো যে, “ধর্ম কেবল বিশ্বাস করতে বলে, বিশ্বাসের স্বপক্ষে কোন অকাট্য প্রমাণ উপস্থাপিত করে না।” এই অবস্থা বলতে বাধ্য হচ্ছি সমগ্র সৃষ্টি লোকের স্রষ্টার অস্তিত্ব ও একত্বকে মানুষ এই কারণেই হয়ত কোনরূপ প্রমাণ ছাড়াই মেনে নিতে বাধ্য হচ্ছে, কেননা, ‘বিশ্বাস’ সাধারণত এভাবেই দানা বেঁধে ওঠে। যদিও ইসলাম উপস্থাপিত বিশ্বাসসমূহ সম্পর্কে সেকথা আদৌ প্রযোজ্য নয়।
(**এই ধরনের কথাদ্বারা কোন ‘বৈজ্ঞানিক সত্য প্রমাণ করতে চাইলে তা যে কতটা হাস্যকর হয়ে দাঁড়ায় তা বলে শেষ করা যায় না। ঠিক এই হাস্যকর অবস্থার মধ্যেই পড়ে আছে বিবর্তনবাদ যা চূড়ান্ত বৈজ্ঞানিক সত্য বলে একালের একশ্রেণীর বিদগ্ধ লোকেরা স্বীকার করে গিয়েছেন। কিন্তু বৈজ্ঞানিক স্যার আর্থার কিইথ এ সম্পর্কে বলেছেন: Evolution is unproved and unprovable. We belive it because the only altemative is special creation and that unthinkable. অর্থাৎ বিবর্তন ধারায় গোটা সৃষ্টিলোক স্বতঃই গড়ে উঠেছে, একথা প্রমাণিত নয়, প্রমাণিত হতেও পারে না, এর পক্ষে কোন প্রমাণ দেয়াই যেতে পারে না। তা সত্ত্বেও আমরা তা মেনে নিয়েছি এজন্য যে, তা যদি মেনে না নেই তা হলে কেউ বিশেষ ক্ষমতায় সৃষ্টি করেছে বলে মানতে হয়। কিন্তু আল্লাহকে তো এর মানতে প্রস্তুতই নয়, সেই কারণেই না এই চরম অসত্য কথাটিকে পরম বৈজ্ঞানিক সত্য বলে মেনে নিতে হচ্ছে নিরূপায়ের উপায় হিসেবে।….. চমৎকার বিজ্ঞান বটে।)
তথ্যসূত্রঃ
- Philosophers of Science, p-244
- Meaning of Evolution-G.G. Simpson (H.Xi 951) P-127
- Organic Evolution-R.S. Lull, p-15
- Ibid, p-83
- Modern Scientific Thought, p-293
- Organic Evolution-R.S. Lull, p-666
- Descent of Man-Charles Darwin (London-1946) p-26
- Organic Evolution-R.S. Lull, P-663
- Decent of Man-Charles Darwin, P-244
- Meaning of Evolution-G.G. Simpson, p-87
- Organic Evolution-R.S. Lull, P-85
- Modern Scientific Thought, P-26
- Ibid, P-130
- Meaning of Evolution-G.G. Simpson, p.134-35
- Ibid, P-13
- Ibid, P-176
- Clear Thinking-A. E. Mendor, P.112-13