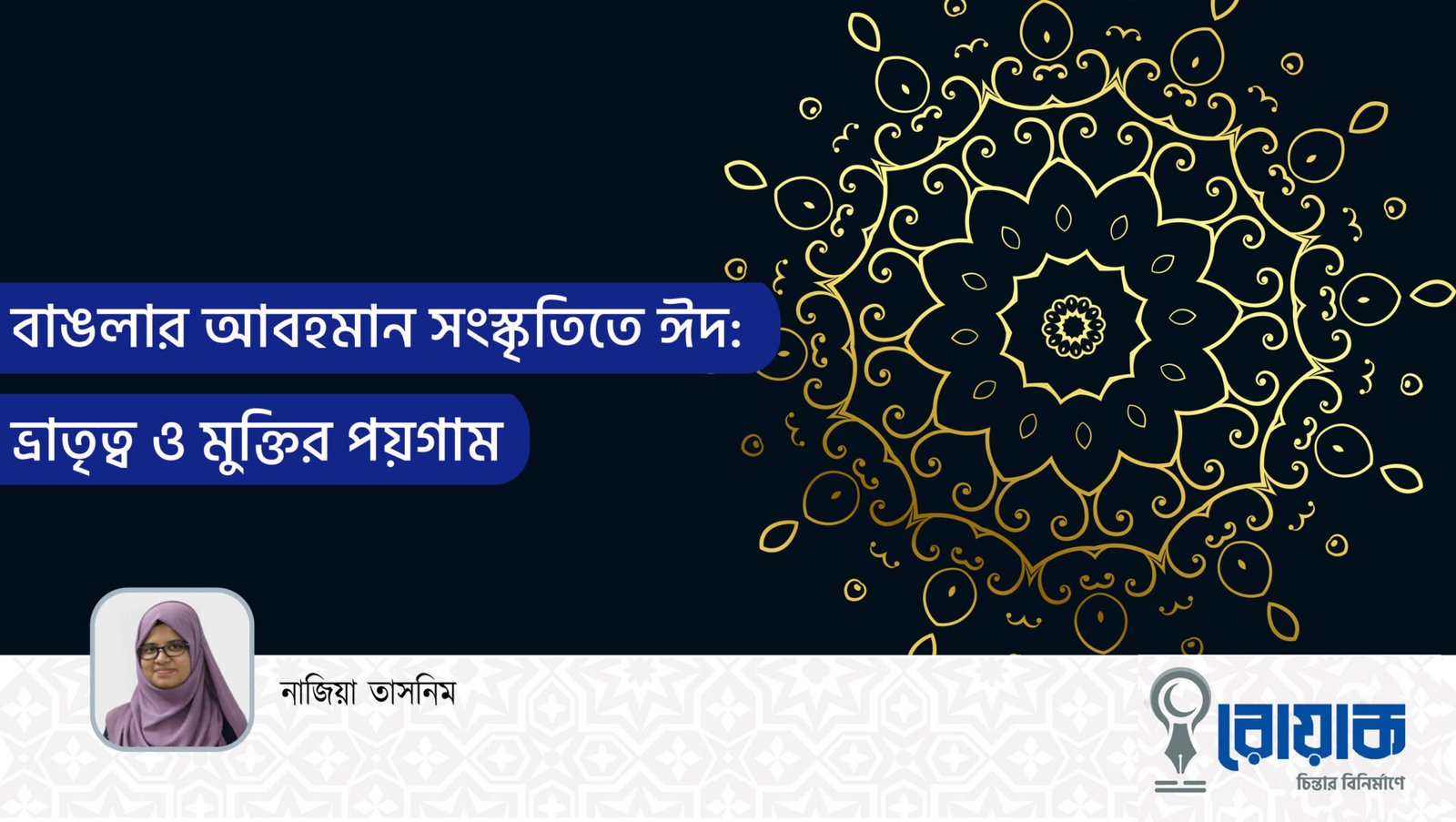মানুষ রক্ত-মাংসে গড়া একটি শরীর মাত্র নয়। তাই শুধু খেয়ে-পরে বাঁচলেই তার চলেনা। তার আবেগ-অনুভূতি আছে, আকল আছে, রুহ আছে। এগুলোরও চাহিদা আছে। সব মিলিয়েই মানুষ। মানুষের জীবনে তাই আনন্দ-বিনোদনের প্রয়োজন হয়। সৌন্দর্য ও রুচিশীলতার প্রয়োজন হয়। আধ্যাত্মিক প্রশান্তির প্রয়োজন হয়।
রমজান মাস মানুষের জীবনে আসে আধ্যাত্মিক প্রশান্তির পরশ নিয়ে। দীর্ঘ একমাস রোজায় মানুষ এই প্রশান্তির পাশাপাশি সংযমের সাধনা করে। ক্ষুধার কষ্টকে অনুভব করে। তাকওয়ার চর্চা করে। তারপর আসে ঈদ। মুমিন জীবনের একমাসের সংযম, আর রুহানী শান্তিকে পূর্ণতা দেয় ঈদ। রমজানের একমাস ধরে যে উৎসবের আবহ সৃষ্টি হয়, তা পূর্ণতা পায় ঈদের মাধ্যমে।
মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,
‘‘যখন ঈদুল ফিতরের দিন আসে, তখন আল্লাহ রাব্বুল আলামীন যারা রোজা পালন করেছে; তাদের সম্পর্কে ফিরিশতাদের নিকট গৌরব করে বলেন- ‘হে আমার ফিরিশতাগণ, তোমরা বলতো! যে শ্রমিক তার কাজ পুরোপুরি সম্পাদন করে তার প্রাপ্য কি হওয়া উচিত? উত্তরে ফিরিশতাগণ বললেন, হে মাবুদ! পুরোপুরি পারিশ্রমিকই তার প্রাপ্য। ফিরিশতাগণ, আমার বান্দা-বান্দীগণ তাদের প্রতি নির্দেশিত ফরজ আদায় করেছে, এমনকি দোয়া করতে করতে ঈদের (ওয়াজিব) নামাজের জন্য বের হয়ে গেছে। এমতাবস্থায় আমার মহিমা, গরিমা, উচ্চ মর্যাদা ও উচ্চাসনের শপথ, আমি অবশ্যই তাদের প্রার্থনায় সাড়া দেব। এরপর নিজ বান্দাগণকে লক্ষ্য করে আল্লাহ পাক ঘোষণা দেন; তোমরা ফিরে যাও, ‘‘আমি তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিলাম এবং তোমাদের সাধারণ পাপরাশিকে পুণ্যে পরিণত করে দিলাম।”
তবে আজকে আমরা ঈদের ধর্মীয় তাৎপর্য নয়, বরং সাংস্কৃতিক তাৎপর্য নিয়ে আলোচনা করার চেষ্টা করবো। জ্ঞানসম্রাট আলিয়া ইজ্জতবেগভিচ এর ভাষায়, “সংস্কৃতি ধর্মের চেয়ে শক্তিশালী।“
এখন প্রশ্ন আসতে পারে, সংস্কৃতি কি ধর্মের সাথে সাংঘর্ষিক? এর জবাবে বাংলাদেশের প্রখ্যাত স্কলার প্রিন্সিপাল ইব্রাহিম খাঁ তার ইসলাম ও সংস্কৃতি প্রবন্ধে স্পষ্টভাষায় বলেন, “ইসলামের সাথে সংস্কৃতির বিরোধ নাই, বন্ধুত্ব আছে।” মুসলিম উম্মাহর সাংস্কৃতিক জীবনে ঈদের তাৎপর্য অপরিসীম।
ঈদ শব্দের আভিধানিক অর্থ ‘আনন্দ’, ‘উৎসব’, ‘প্রত্যাবর্তন’। এটি মুসলমানদের জন্য স্বয়ং আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের পক্ষ থেকে নির্ধারণ করে দেয়া উৎসব। আসমান-জমিনের রব যে দিনটিকে আনন্দ-উৎসবের দিন হিসেবে নির্ধারণ করেছেন, নিঃসন্দেহে এ দিনটি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ উৎসবের দিন। তবে ঈদ কেবল উৎসবমাত্র নয়। এটি একই সাথে আমাদের আধ্যাত্মিক অনুভূতিকে জাগরণকারী, উম্মাহর চেতনাকে জাগ্রতকারী একটি দিন। সারা বিশ্বের মানুষ একইসাথে ছয় তাকবীরের নামায আদায়ের মাধ্যমে এই দিনটি শুরু করে, যা আমাদেরকে স্মরণ করিয়ে দেয় আমরা এক উম্মাহ। আমরা সবাই একই আল্লাহর দরবারে সিজদা করি। এটি আমাদের ভ্রাতৃত্ববোধকে মজবুত করার দেয়। আমাদের পুরনো দিনের সব হিংসা-দ্বেষ, মনোমালিন্যকে পেছনে ফেলে কাঁধে -কাঁধ মিলিয়ে, বুকে -বুক মিলিয়ে আমরা নতুন করে ভ্রাতৃত্বের মজবুত বন্ধনে আবদ্ধ হই ৷ এই ঈদ আমাদেরকে পৃথিবীর প্রতি মানুষ হিসেবে, আমাদের কর্তব্যগুলোকে স্মরণ করিয়ে দেয়। ফিতরা-যাকাত আদায়ের মাধ্যমে আমরা একে অন্যের পাশে দাঁড়াই। আল্লাহ চাননা তার কোন বান্দাহ ঈদের আনন্দ থেকে বঞ্চিত হোক। তাই তিনি ঈদের জামায়াতের আগেই ফিতরা যাকাত আদায় করার জন্য বারবার তাগিদ দিয়েছেন। এছাড়াও রমজান মাসে বেশি বেশি দান-সাদকাহ করার জন্য উৎসাহিত করেছেন। ফলে ঈদের আনন্দ ধনী-দরিদ্র সবাই মিলেমিশে ভাগাভাগি করার সুযোগ পায়। আমাদের হৃদয়গুলো কাছাকাছি আসার সুযোগ পায়। এজন্য ঈদ আমাদের সংস্কৃতির সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ অধ্যায়।
পৃথিবীর ইতিহাসে প্রথম ঈদ কবে পালিত হয়েছিলো সে সম্পর্কে সঠিক তথ্য আমি খুঁজে পাওয়া যায়নি। তবে এতটুকু জানা যায় যে, পূর্ববর্তী নবীদের যুগেও ঈদ মুসলমানদের জন্য উৎসবের দিন হিসেবে নির্ধারিত ছিলো। নবী মুহাম্মদ (স.) এর সময়ে হিজরতের পরের বছর থেকে মদীনায় ঈদ পালন শুরু হয়। আর মক্কায় শুরু হয় মক্কা বিজয়ের পর।
বাংলা অঞ্চলে প্রথম ঈদ পালনের ইতিহাস ও বেশ পুরনো। ইসলামের প্রাথমিক যুগেই ইসলামের আলো এ উপমহাদেশের ভূমিকে স্পর্শ করেছে। ঐতিহাসিক বর্ণনামতে, ৬৪০ খ্রিস্টাব্দ অর্থাৎ মক্কা বিজয়ের দশ বছর পরে উপমহাদেশে ইসলামের আগমন ঘটে। পীর, আলেম, ব্যবসায়ীদের মাধ্যমেই মূলত এখানে ইসলামের অমীয় বাণী পৌঁছেছিলো। যেহেতু মুসলমানরা এখানে ছিলো, তাই স্বাভাবিকভাবেই নামাজ-রোজার মতো ঈদ ও তখন থেকেই এখানে পালিত হয়ে আসছিলো। তবে রাষ্ট্রীয়ভাবে ঈদ উদযাপন শুরু হয়, মুসলমান শাসকরা এখানে আসার পর। সে হিসেবে ১২০৪ খ্রিস্টাব্দে বখতিয়ার খিলজির বাংলা বিজয়ের পর থেকেই বাংলা অঞ্চলে রাষ্ট্রীয়ভাবে ঈদ উদযাপন শুরু হয়। মোঘল এবং সুলতানী আমলে বাংলা অঞ্চলে বিশেষ করে ঢাকায় রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে বেশ আড়ম্বরপূর্ণ ভাবে ঈদ উদযাপিত হতো।
মুঘল আমলে ভারতে ঈদের দিনের ইতিহাস সম্পর্কে লেখা পাওয়া গেছে বিভিন্ন বইপত্রে। সেসময় সরকারি ভাবে ঈদ ও ঈদের অনুষ্ঠানকে বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হতো। মুঘল সালতানাতে যেসব অনুষ্ঠান হতো সেসব অনুষ্ঠানের আবার চিত্রাঙ্কনও করা হতো। সে আমলের বিভিন্ন চিত্রে ফুটে ওঠে সে সময়ের উৎসবের আড়ম্বরতা। এমনই একটি চিত্রে প্রথম মুঘল সম্রাট বাবরকে ঈদুল ফিতর উপলক্ষে তারা রাজ দরবারের সভাসদকে ঈদের শুভেচ্ছা জানাতে দেখা যায়। প্রায় সব মুঘল সম্রাটকেই ঈদের নানা উৎসব পালন করতে দেখা গেছে। এসব তথ্য ইতিহাসে যেমন আছে, তেমনি আছে শিল্পীদের আঁকা চিত্রেও। ঈদের দিন নানা আয়োজনের মধ্যে মেলামেশা, ঘুড়ি উড়ানো, পায়রার খেলা, মোরগ লড়াই, মেলার কথা জানা যায় মুঘল ঢাকার ইতিহাসে। বাংলাদেশে ঈদের সবচেয়ে পুরনো বর্ণনা পাওয়া যায় মির্জা নাথানের লেখায়। ঈদুল ফিতরের সময় তিনি ছিলেন বোকাই নগরে। তার লেখার ভিত্তিতে জানা যায়, শাওয়ালের চাঁদ দেখা গেলে মোমবাতির আলোয় সারা শহর আলোকিত হয়ে উঠতো। যখন নতুন চাঁদ দেখা যেত, তখন শিবিরে বেজে উঠত শাহী তুর্য অর্থাৎ রণশিঙ্গা এবং একের পর এক গোলন্দাজ বাহিনী আতশবাজির মতো গুলি ছুড়তে থাকতো। সন্ধ্যা থেকে মাঝরাত পর্যন্ত চলত এ আতশবাজি। শেষ রাতের দিকে বড় কামান দাগানো হতো। কামানের তীব্র শব্দে ভূকম্প অনুভূত হতো।
অধ্যাপক আবদুর রহিম বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসে মুসলমান ঐতিহাসিকদের লেখা থেকে সেসময়ের ঈদ উৎসবের বিবরণ দিয়েছেন। তিনি যা লিখেছেন তা অনুযায়ী বলা যায় বাংলাদেশে মুঘল সৈন্যদের ছাউনি থেকে ঈদের আনন্দবার্তা ঘোষণা করা হতো। এতে প্রকাশ পায় কীভাবে মুসলমানরা ঈদ উৎসবকে স্বাগত জানাতো এবং এই আনন্দ-উৎসবে আমোদ-প্রমোদ করত এবং এর জন্য শুকরিয়া আদায় করত। ঈদের দিন মুসলমানরা সব বয়সের নারী-পুরুষ ও ছেলে-মেয়েরা সুন্দর নতুন কাপড় পরিধান করতো, আতর ব্যবহার করতো। বাহারী খাবার-দাবারের আয়োজন হতো সবার বাড়িতে। মুসলমানরা সুন্দর পোশাক-পরিচ্ছদে সজ্জিত হয়ে শোভাযাত্রা করে ঈদগাহে যেত। অবস্থাপন্ন ব্যক্তিরা উৎসবের সময়ে মুক্তহস্তে অর্থ ও উপহারাদি পথে ছড়িয়ে দিতেন।
তাই তখন মুঘলরা রমজানের প্রথম থেকেই চেষ্টায় থাকত ঈদের খুশিকে আয়ত্ত করে নিতে। কিন্তু এসব আনন্দ শুধু উচ্চবিত্তদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিলোনা। নিম্নবিত্ত মুসলমানদের জন্যও আনন্দ-উৎসবের সুব্যবস্থা করেছিলেন তখনকার মুঘল অধিপতিরা।
মুঘল আমলে ঈদ উদযাপন হতো দু-তিন দিন ধরে। চলতো সংগীত ও নৃত্য পরিবেশন। আত্মীয়-স্বজন, পরিবার-পরিজন নিয়ে একরকম মেলাই বসে যেত। তখনকার ঈদ উদযাপনের চিত্র পাওয়া যায় সুবেদার ইসলাম খানের সেনাপতি মির্জা নাথানের বর্ণনা অনুযায়ী, সুবেদার ইসলাম খান ঢাকার ইসলামপুরে বুড়িগঙ্গা নদীতে নৌকাবাইচের ব্যবস্থা করতেন। এ সময় স্বয়ং সুবেদার ইসলাম খান উপস্থিত থাকতেন।
বাদশাহ শাহজানের পুত্র শাহ সুজা এখানে এলে তার পৃষ্ঠপোষকতায় সাংস্কৃতিকভাবে ঢাকা আরো মার্জিত হয়ে ওঠে। একই সঙ্গে ধরে নেওয়া যায় ঈদ উদযাপনেও আরো চাকচিক্যের সংযোজন ঘটে। সব উৎসবে ঢাকার স্থানীয় বাসিন্দাদের উপস্থিতি না থাকলেও, সবাই নিজ নিজ জায়গা থকে উৎসবমুখর পরিবেশেই ঈদ উদযাপন করতো।
মুঘল আমলের সবচেয়ে বড় ঈদগাহের নিদর্শন এখনো দৃশ্যমান। ১৬৪০ খ্রিস্টাব্দে সম্রাট শাহজাহানের পুত্র শাহ সুজার প্রধান অমাত্য মীর আবুল কাসেম ধানমন্ডির শাহী ঈদগাহ প্রতিষ্ঠা করেন। ঢাকায় অবস্থিত মুঘল স্থাপত্য নিদর্শনগুলোর অন্যতম এই ঈদগাহ। ৪ ফুট উঁচু করে ভূমির ওপরে এটি নির্মিত হয়, যাতে বন্যা থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। ঈদগাহের উত্তর পাশে রয়েছে, তিন ধাপের মিম্বার। এখানে দাঁড়িয়ে ইমামরা নামাজ পড়ান। ঈদগাহটি চারদিকে ১৫ ফুট উঁচু প্রাচীর দিয়ে ঘেরা। প্রথমদিকে এখানে শুধু সুবেদার, নায়েবে নাজিম ও অভিজাত মুঘল কর্মকর্তা এবং তাদের স্বজন-বান্ধবরাই নামাজ পড়তে পারতেন, সাধারণ নগরবাসীরা এতে প্রবেশ করার তেমন একটা সুযোগ পেতেন না। পরে ঈদগাহটি সবার জন্য উন্মুক্ত করা হয় এবং তাতে ঢাকাসহ আশপাশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে মুসল্লিরা আসতেন। ঈদগাহটি বর্তমানেও ঈদের নামাজের জন্য ব্যবহৃত হয়।
এছাড়াও দিকে দেশের বিভিন্ন জায়গায় ঈদের জামায়াত অনুষ্ঠিত হতো। ঈদের নামাজ পড়ানোর জন্য সুলতানরা ইমাম নিয়োগ করতেন। শহরের বাইরের বিরাট উন্মুক্ত জায়গায় অথবা গ্রামে ঈদের নামাজ অনুষ্ঠিত হতো এবং এসব স্থানকে ঈদগাহ বলা হতো।
স্যার টমাস মেটকাফে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সিভিল সার্ভেন্ট ছিলেন। সম্রাট বাহাদুর শাহ জাফরের কোর্টে কাজ করার কারণে মেটকাফে সম্রাটের প্রিয়ভাজন হওয়ার সুযোগ লাভ করেন। বাহাদুর শাহ জাফর স্যার টমাস মেটকাফেকে দিয়ে ভারতের শিল্প-সংস্কৃতির ওপর জরিপ করান এবং সেগুলোর ওপর চিত্রাঙ্কন করার দায়িত্ব দেন। চমৎকার এই দায়িত্ব পেয়ে মেটকাফে অতি উৎসাহের সঙ্গে কাজ শুরু করেন। তিনি ভারতের শিল্পীদের সহযোগিতায় মুসলিম আর্কিটেকচারের ওপর গবেষণা ও চিত্রাঙ্কনের কাজ শুরু করেন। একে একে গুরুত্বপূর্ণ ইমারতগুলোর চিত্র অঙ্কন করেন। এরপর মুঘল আমলে ঈদকে কেন্দ্র করে যেসব অনুষ্ঠান হতো সেই অনুষ্ঠানেরও চিত্র অঙ্কনে অসাধারণ কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন। এমনই একটি চিত্রের নাম ‘ঈদের শোভাযাত্রা’। কাগজে আঁকা এই চিত্রটির মাধ্যম ছিল কালি, তুলি এবং রঙ। ১২ ফোল্ডের দীর্ঘ এই স্ক্রল চিত্রে বাদশাহ বাহাদুর শাহ জাফর, তার ছেলে এবং আত্মীয়-স্বজন উপস্থিত রয়েছেন। উপস্থিত রয়েছেন স্যার টমাস মেটকাফে ও অন্য সভাসদরা। ঈদ শোভাযাত্রার চিত্রের সর্বত্র রয়েছে সর্বস্তরের সাধারণ মানুষ। সম্রাট, উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা, সম্রাটের ছেলে ও আত্মীয়-স্বজনরা সুসজ্জিত হাতির পিঠে অবস্থান করছেন। ঘোড়ার পিঠেও রয়েছেন কেউ কেউ। যার সরাসরি উদ্যোগে এ চিত্র সৃষ্টি হয়েছে, সেই টমাস মেটকাফে অবস্থান করছেন সুসজ্জিত হাতির পিঠে। যেসব শিল্পী চিত্রাঙ্কনের ক্ষেত্রে মেটকাফেকে সাহায্য করেছেন, তাদের মধ্যে দিল্লির চিত্রশিল্পী মাজহার আলী খানের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তার অঙ্কিত চিত্রটি কাল্পনিক নয়। বাস্তব দৃশ্য অবলম্বনেই ঈদুল ফিতরের এ চিত্র অঙ্কন করা হয়েছে। শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণকারী সাধারণ মানুষ যাতে মুঘল সম্রাট, সভাসদ ও উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সান্নিধ্যলাভে উৎসাহ বোধ করেন সে জন্য শোভাযাত্রার সর্বপরিকল্পিতভাবে তাদের অবস্থানকে নিশ্চিত করেছে। এটাই এ চিত্রের বিশেষত্ব।
মুঘল আমলে ঢাকায় ঈদ মিছিল বলে একটা কথা ছিল। সে মিছিলে শামিল হতেন রাজধানীর অভিজাত থেকে শুরু করে সর্বস্তরের মানুষ। উনিশ শতকের প্রথমদিকে আলম মুসাওয়ার নামে এক শিল্পী ঢাকার ঈদ ও মহরমের মিছিলের ছবি এঁকেছিলেন। মোট ৩৯টি ছবি আঁকেন তিনি। চিত্রগুলোতে দেখা যায় ঈদের মিছিলগুলো নায়েব-নাযিমদের নিমতলী প্রাসাদ, চকবাজার, হোসেনি দালান প্রভৃতি স্থাপনার সামনে দিয়ে যাচ্ছে। ঈদের দিন নায়েব-নাযিমদের বাসস্থান নিমতলী প্রাসাদের ফটক থেকে বিভিন্ন পথ ঘুরে, চকবাজার, হোসেনি দালান হয়ে মিছিল আবার শেষ হতো মূল জায়গায় এসে। মিছিলে থাকত জমকালো হাওদায় সজ্জিত হাতি, উট, পালকি। সামনের হাতিতে থাকতেন নায়েব-নাযিম। কিংখাবের ছাতি হাতে ছাতি বরদার, বাদ্যযন্ত্র হিসেবে ছিল কাড়া-নাকাড়া শিঙা। রঙ-বেরঙের নিশান দিয়ে মিছিলকে আরো জাঁকজমকপূর্ণ করা হতো। দর্শকরা সারি বেঁধে থাকতেন রাস্তার দু’পাশে। সুবেদারেরা ‘ঝরোকা’ মঞ্চে প্রজাদের দর্শন দিতেন। বিকেলে কাঞ্চনিদের নৃত্য ছিল রাজদরবারে। মুঘল আমলে গ্রামীণ মানুষের ঈদ উৎসবের ধারা একই ছিল।
অনুমান করে নেয়া হয় মুঘল আমলে বাদশাহী বাজারে অর্থাৎ বর্তমান চকবাজারে ঈদ মেলার আয়োজন হতো। বিশেষ করে তখনকার প্রশাসনিক সদর দফতর ঢাকা কেল্লার আশপাশের এলাকা ঈদের সময়টায় থাকতো জমজমাট। চকবাজার এবং রমনা ময়দানের সেই ঈদ মেলায় বিভিন্ন রকমের বাঁশের তৈরি খঞ্চা ডালা আসতো। বিভিন্ন কাঠের খেলনা, ময়দা এবং ছানার খাবারের দোকান বসতো সুন্দর করে সাজিয়ে আর বিকেল বেলা হতো কাবলির নাচ। চকবাজার, কমলাপুরে এখনো সেই মেলার রেশ ধরে মেলা বসে। তাছাড়া দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ঈদের দিন ছোট-বড় মেলা বসে। মেলায় এখনো অনেকেই গিয়ে থাকে ঈদের আনন্দ উপভোগ করতে। বিশেষ করে গ্রামের ছেলে-মেয়েরা ঈদের দিন মেলায় যায় আনন্দ উপভোগ করতে। ঈদ মেলায় বিভিন্ন খেলা, পুতুল নাচ আরো অনেক বিনোদনের ব্যবস্থা করা হতো। হরেকরকম মিষ্টান্ন বানিয়ে বিক্রি করতো ব্যবসায়ীরা এই ঈদ মেলায়।
ঈদের খুশি যেন পরিপূর্ণ হয় না ঘরে শাহী খাবারের আয়োজন না হলে। মুঘল আমল থেকে শুরু করে আজ অবধি ঈদের দিন সব মুসলমানদের ঘরে ঘরেই রান্না হয় মুখরোচক সব শাহী রান্না। মুঘলদের রাজত্বকালে ঈদের দিন তৈরি হতো বিভিন্ন ধরনের শাহী খাবার। সকালের নাশতায় খাওয়া হতো বাকরখানি, পরোটা, মাংস আর কয়েক পদে রান্না করা সেমাই। দুপুরের খাবারে থাকত মোরগ পোলাও, কোরমা, পরোটা, কালিয়া, জর্দা। রাতেও এমন সব খাবারের আয়োজন করা হতো। মুঘলদের ঈদের সব রান্নায় মালাই ব্যবহার করা হতো। এসব খাবার-দাবার মুঘল যুগে অভিজাত পরিবারদের মধ্যে ব্যাপক প্রচলিত ছিল। এছাড়া সেই আমলে মুসাফিরদের জন্য ঈদের খাবার-দাবারের বন্দোবস্ত করা হতো।
এইযে, বাঙালির আবহমান উৎসবের দিন ঈদ, কবে কখন কীভাবে উৎসবহীন হয়ে গেলো?
কারা আমাদের সংস্কৃতিকে আমাদের কাছ থেকে কেড়ে নিলো? উত্তরে বলতে হয় সাম্রাজ্যবাদীদের রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক-বুদ্ধিবৃত্তিক ও অর্থনৈতিক আগ্রাসনের কথা। তারা এখানে এসে রাষ্ট্রীয়ভাবে ঈদ উদযাপন বন্ধ করে দেয়। ঈদের ছুটি কমিয়ে আনে। তারপর আসে অর্থনৈতিক দুর্দশা। তাদের শোষণের ফলে এখানকার মুসলমানরা অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়ে। ফলে, জাঁকজমপূর্ণ আয়োজনে ঈদ উদযাপনের সামর্থ খুব কম মুসলমান পরিবারেরই ছিলো। তাই ধীরে ধীরে ঈদের জৌলুশ কমে আসতে থাকে। ফিকে হয়ে আসতে থাকে এর বর্ণিল উৎসবমুখরতা।
এখানে আরেকটি বিষয় উল্লেখযোগ্য, ব্রিটিশরা এখানে এসে হাজার হাজার মক্তব-মাদরাসা ধ্বংস করে। আলেমদের হত্যা করে, নির্বাসন দেয়। হঠাৎ করে ইংরেজি শিক্ষা চালু করে। এভাবে মুসলমানদের অজ্ঞানতার অন্ধকারে আবৃত করে ফেলে। ইসলাম সম্পর্কেও তারা ধীরে ধীরে অজ্ঞ হতে থাকে। এজন্য রমজান-ঈদ এর শান-মান সম্পর্কে অজ্ঞতা থেকেও এগুলো উদযাপনে উদাসীনতার শুরু হয়।
ঔপনেবশিক সময়ে বিংশ শতাব্দীর দিকে এসে মুসলমানদের স্বতন্ত্র রাজনৈতিক চেতনা জোরদার হতে থাকে। এসময় মুসলমানদের জ্ঞান এবং সংস্কৃতির পুনর্জাগরণের জন্য ঢাকার নবাব পরিবার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। তারা আবারও ঢাকায় জমকালো ঈদের আয়োজন করার চেষ্টা করেন। আহসান মঞ্জিল থেকে তখন কামান দেগে শহরবাসীকে ঈদের চাঁদের আগমনী জানান দেয়া হতো। ঢাকায় আবার ঈদ মিছিলও শুরু হয়। নবাব পরিবার অর্থ ও সাহস দিয়ে ঈদ মিছিলে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেন। নবাব বাড়ির খাজা শাহাবুদ্দীন ও খাজা ইসমাইল মিছিলে পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। কাদের সরদার, আব্দুল আজিজ, জুম্মন ব্যাপারী কোনো কোনো বছর মিছিলে অগ্রভাগে থাকতেন। মিছিলে থাকতো কাসিদার দল। ঈদ মিছিলে তখনকার দিনের বড় আকর্ষণ মোটরগাড়ি, মোটর বাস ও ট্রাকগুলোকে ময়ূর, প্লেন, নৌকা, জাহাজ, বিভিন্নভাবে সাজিয়ে বের করা হতো। এই মিছিল চকবাজার থেকে শুরু হয়ে ইসলামপুর, পাটুয়াটুলি, নবাবপুর, বংশাল হয়ে পুনরায় চকে এসে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেত। তবে কোনো কোনো বছর এর ব্যতিক্রম হতো। এখান থেকেই পুরস্কার বিতরণের কাজ সমাধা করা হতো।
এই মিছিলে উর্দু গান ও কাওয়ালী গাওয়া হতো এবং সকল মুসলমানরাই এতে অংশ নিত। ঢাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ ও সরদাররা চারটি স্পটে যেমন দাঁড়িয়ে মিছিলকারীদের উৎসাহিত করে চা নাস্তা দিয়ে আপ্যায়ন করতেন। আহসান মঞ্জিলের প্রধান ফটকের উপর নবাব পরিবারের মহিলারা দাঁড়িয়ে পর্দার আড়াল থেকে মিছিল দেখতেন। শুধু নবাব বাড়ির মহিলা নয়, বিভিন্ন মহল্লা থেকে মহিলারা আসতেন মিছিল দেখার জন্য। ছাদের উপর কাপড় দিয়ে পর্দা ঘেরাও করে দেয়া হতো, যাতে বেপর্দা না হয়।
বিভিন্ন এলাকার যুব সম্প্রদায় শরবতের গাড়ি নিয়ে মিছিলে অংশগ্রহণ করতেন। মিছিলে শরবত পান করানো নিয়ে ছিল প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা। মানে ভালো শরবত পানাহারকারীকে পুরস্কৃত করা হতো। এ মিছিলে সৌন্দর্য্য জৌলুস বৃদ্ধি করতে একাধিক হাতি সুন্দর সাজে সাজিয়ে রাজপথে সারি বেঁধে নিয়ে যাওয়া হতো। হাতির সংখ্যা যে বছর কম দেখা যেতো, সে বছর ট্রাক দেখা যেতো বেশি। উন্নতমানের রেসের ঘোড়া সুন্দর সাজে সাজিয়ে মিছিলে আনা হতো। মিছিল চলাকালীন সময়ে ঘোড়াগুলো বাদ্যের তালে ছন্দে ছন্দে এগিয়ে যেতো এবং বিভিন্ন ভঙ্গিমার নাচ দেখিয়ে দর্শকদের মুগ্ধ করতো। রহমতগঞ্জ এলাকার যুবক সম্প্রদায় একবার বখতিয়ার খিলজি ও তার সপ্তদশ অশ্বারোহীর বিজয়ের চমৎকার চিত্র মিছিলে প্রদর্শন করেছিলো। এছাড়াও ঘোড়ার গাড়ি ও গরুর গাড়ির বহর ও মিছিলে দেখা যেতো। পরবর্তীতে বিভিন্ন দাঙ্গা-হাঙ্গামায় দেশে রাজনৈতিক অস্থিতিশীল পরিস্থিতির সৃষ্টি হলে এ মিছিল আবারও বন্ধ হয়ে যায়। এরপর ঈদ ধীরে ধীরে বর্তমানের রূপ লাভ করে।
অপসংস্কৃতির এ জামানায় এসে সাংস্কৃতিক জাগরণের আলাপ আজকে খুব বেশি প্রাসঙ্গিক মনে হয়। কেননা সংস্কৃতি সমুদ্রের জোয়ারের মতো। এর প্রবল বেগের সামনে যুক্তি-তর্ক-বয়ান সবকিছু ভেসে যায়। এটিকে মোকাবেলা করতে পারে কেবল এর চেয়েও প্রবল বেগের কোন স্রোত। তাই একটি প্রবল বেগে বেগমান সাংস্কৃতিক জোয়ার সৃষ্টি করা আজ সময়ের দাবী। আমাদের মনে রাখতে হবে আমরা এক গৌরবময় সভ্যতার সন্তান। আমাদের আছে শক্তিশালী সাংস্কৃতিক পাটাতন। সে পাটাতনের উপর আজকের সময়ের বাস্তবতার আলোকে আমাদেরকে নতুন এক সাংস্কৃতিক জোয়ার সৃষ্টি করতে হবে। সে ধারাবাহিকতায় আমাদের সংস্কৃতির সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ অধ্যায় ঈদের জৌলুশ ফিরিয়ে আনতে হবে। আমাদের সামনে এখনও বিপুল সম্ভাবনা বিদ্যমান।
দুইশ বছরের শোষণ আমাদের ছয় তাকবীরের ঈদের জামায়াত কোনদিন বন্ধ হয়নি। বন্ধ হয়নি আমাদের সেহরি-ইফতার আর তারাবীর সংস্কৃতি। হয়তো তার জৌলুশ কমেছে, কিন্তু হারিয়ে যায়নি। আমাদের মিনারগুলো আজও আমাদের এক কাতারে দাঁড়াবার আহবান জানায়। এক দস্তরে বসবার আহবান জানায়। আমরা এখনো সে আহবানে সাড়া দিয়ে আমাদের ঈদের রুহকে ফিরিয়ে আনতে পারি। যেন ঈদ হয়ে ওঠে আমাদের আধ্যাত্মিক বলয় ও উম্মাহর চেতনাকে জাগ্রতকারী একটি দিন। ঈদ যেন হয়ে ওঠে আমাদের ভ্রাতৃত্বের বন্ধনকে মজবুত করে নেয়ার দিন। ঈদ যেন হয়ে ওঠে পড়শির খবর নেয়ার দিন, আত্মীয়তার বন্ধনগুলোকে দৃঢ় করার দিন। ঈদ যেন হয়ে ওঠে মজলুমের মুখে হাসি-ফোটাবার দিন, আমাদের শপথগুলোকে ঝালাই করে নেয়ার দিন, আমাদের স্বপ্নগুলোতে আরেকটু রঙ ছোঁয়াবার দিন। ঈদ যেন হয় কাশ্মীরের সংগ্রামী ভাই-বোনদের জন্য দোয়া করার, কুদসের মায়েদের জন্য সালাম পাঠাবার দিন, রোহিঙ্গা ক্যাম্পে অমানুষিক জীবন কাটানো পরিবারগুলোর জন্য দোয়া করার দিন। সর্বোপরি মেহেদীর রঙে, সেমাই-পায়েশের স্বাদে, আতরের গন্ধে ঈদ হয়ে উঠুক আমাদের জন্য একটি সত্যিকারের উৎসবের দিন।
তথ্যসূত্র:
উৎসবের ঢাকা- সাদ উর রহমান।
বাংলাদেশ জার্নাল/এনকে
বাংলাদেশের কালচার-আবুল মনসুর আহমদ
‘ঈদ উৎসবের ইতিহাস ও ঐতিহ্য’-অনুপম হায়াৎ।