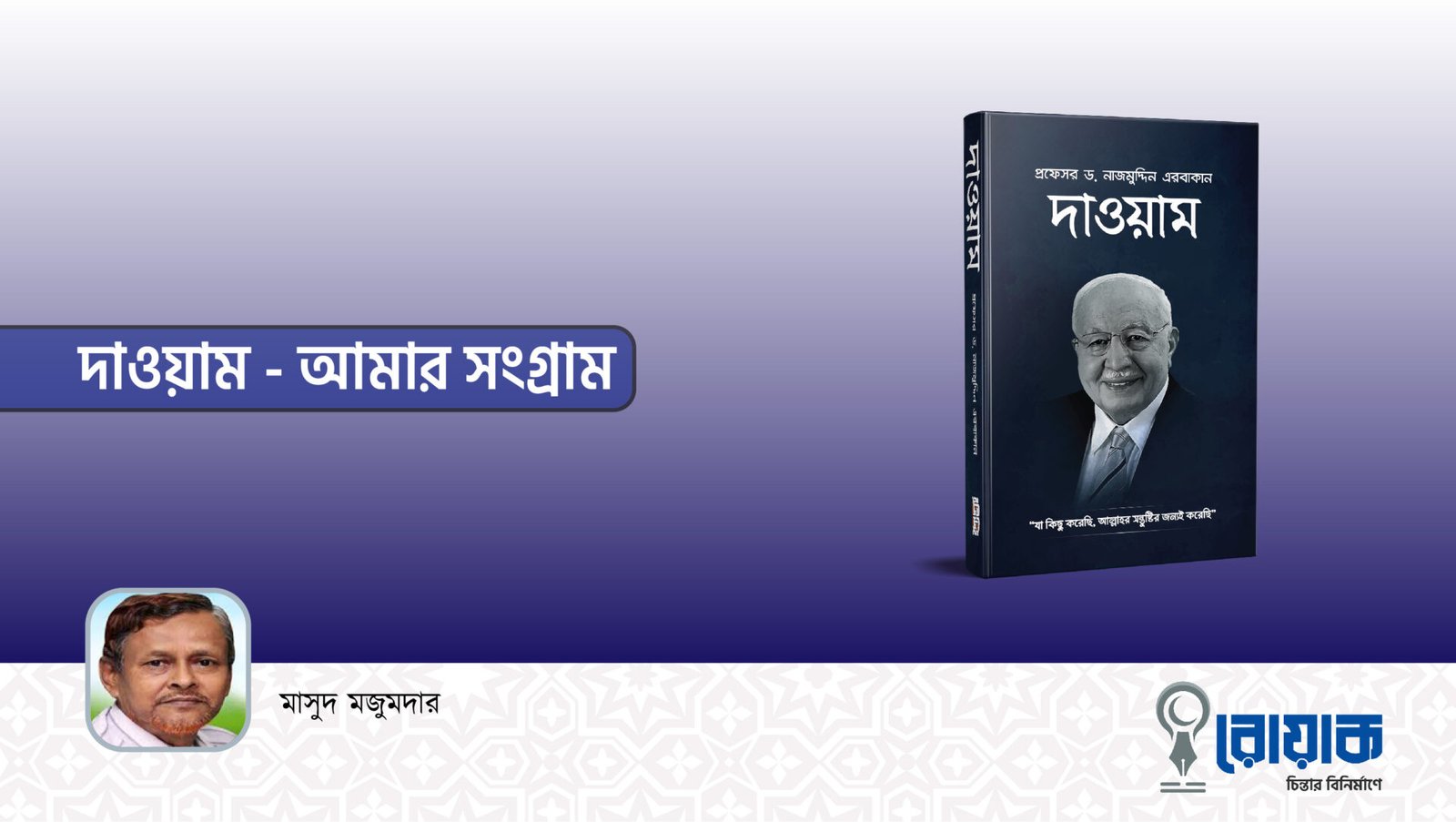২০১১ সালের ঘটনা। তারিখ ২৭ ফেব্রুয়ারি। কেউ একজন জানালেন তুরস্কের বর্ণাঢ্য ব্যক্তিত্ব প্রফেসর ড. নাজমুদ্দিন এরবাকান আর নেই। তার সম্পর্কে বাড়তি আগ্রহের কারণ, তিনি নিজেকে নিয়ে তো বটেই, তুরস্কের রাজনীতি সম্পর্কেও অনেক এক্সপেরিমেন্ট চালিয়েছেন। কামালবাদের বিরুদ্ধে কোনো প্রকাশ্য চ্যালেঞ্জ করেননি; কিন্তু তুরস্ককে গণ-ইচ্ছার কাছাকাছি নিয়ে গেছেন। কারো বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে অবস্থান না নিয়েও ইতিবাচক ভূমিকা পালনের মাধ্যমে সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থায় পরিবর্তন আনা যায়,- এটি প্রফেসর ড. নাজমুদ্দিন এরবাকান-ই প্রমাণ করলেন। তার প্রতি তুরস্কের জনগণের ভক্তি শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার কোনো পরিমাপ হয় না। ৮৫ বছর বয়সে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে মৃত্যুর পর তার জানাজায় লাখো লাখো লোকের সমাগম হয়েছিল। মিডিয়া সেই উপস্থিতির পরিমাপ করতে গিয়ে ধারণা দিয়েছিল, কনস্টান্টিনোপল ও পরিবর্তিত নাম ইস্তাম্বুল হওয়া পর্যন্ত দীর্ঘ তিন হাজার বছরের ইতিহাসে প্রায় চল্লিশ লাখ মানুষের উপস্থিতি এর আগে কেউ দেখেনি। এরবাকানের জানাজায় উপস্থিতির পরিমাপ মিডিয়া এভাবেই করেছিল। লাখো লাখো লোকের জানাজা শেষে মরহুমের যোগ্য দু’জন উত্তরসূরি ও ছাত্র রজব তাইয়্যেব এরদোগান ও আবদুল্লাহ গুল লাশ বহন করেছিলেন। দু’জনের একজন সাবেক প্রেসিডেন্ট, অন্যজন বর্তমান প্রেসিডেন্ট।
এরবাকানের অনুরোধ ছিল তার দাফন যেন রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় না হয়। তার এই অনুরোধ রক্ষা করার দায়বোধ করেননি তার স্নেহ ও প্রীতিভাজনেরা। একই সাথে কৃতজ্ঞ শত শত ঊর্ধ্বতন সামরিক-বেসামরিক সরকারি কর্মকর্তাও জানাজায় শরিক থেকে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে কার্পণ্য করেননি। এটি ছিল তার প্রতি রাজনৈতিক প্রবঞ্চনার প্রতিবাদ। এ প্রসঙ্গে একটি কথা বলে রাখা ভালো, কামাল পাশা আরবি ভাষা ও ইসলামি ঐতিহ্য মুছে ফেলে জাতিকে আধুনিক বানাতে চেয়েছিলেন, তখন থেকে তুর্কি ভাষা লেখা হয় ইংরেজি অক্ষরে। তাই ধ্বনিতত্ত্ব উচ্চারণ বিভ্রাট সৃষ্টি করে। যেমন, তাদের নামগুলো। কেউ মনে করেন এরবাকান, কারো উচ্চারণ আরবাকান; সব নামের ক্ষেত্রে এটি দেখা যায়।
এরবাকানের যখন মৃত্যু হয় তখনো তিনি ছিলেন সক্রিয় এবং দায়িত্ব পালন করছিলেন। তিনি জন্মেছিলেন তুরস্কের সিপন শহরে। পিতা মাহমুদ সাবরি এরবাকান ছিলেন সরকারি কর্মকর্তা। প্রায়ই তার কর্মস্থল বদল হতো। এরবাকানও পরিবারের সাথে বসবাস করতেন। তাই বিভিন্ন শহর সম্পর্কে তার ধারণা জন্মেছিল শৈশবেই। প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর সময়কালে ১৯২৬ সালের ২৯ অক্টোবর তার জন্ম। প্রাথমিক শিক্ষা পান স্থানীয় সরকারি প্রাথমিক স্কুলে। বাবার আগ্রহে গৃহশিক্ষকের কাছে পেয়েছেন ইসলামি শিক্ষার প্রাথমিক পাঠ। মেধা, মনন ও প্রতিভাগুণে তিনি সব শিক্ষকের নজরে পড়ে যেতেন। অনেক শিক্ষক তাকে ডাকতেন ‘দরিয়া নাজমুদ্দিন’। এর অর্থ ‘জ্ঞানের সাগর’। আক্ষরিক অর্থেই তিনি প্রমাণ করেছিলেন, আসলেই তিনি ছিলেন বহুমুখী জ্ঞানের সাগর। সব পরীক্ষায় তিনি ভালো ফলাফল করতেন। সেই ভালো ফলাফল হতো অন্যদের তুলনায় অনেক বেশি উঁচুমানের। সব সময় তিনি প্রথম হতেন। তার সাথে যারা দ্বিতীয় হতেন তাদের সাথে নাম্বারের দূরত্ব থাকত ব্যতিক্রমধর্মী বেশি। তুরস্কের নিয়ম অনুযায়ী উচ্চশিক্ষায় ভালো শিক্ষার্থীদের ভর্তি পরীক্ষায় অংশ নিতে হতো না। কিন্তু এরবাকান নিজের মান যাচাই করতে ভর্তি পরীক্ষায় অংশ নিলেন। সেবার বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি পরীক্ষায় তিনি পুরো তুরস্কের মধ্যে প্রথম হয়েছিলেন। ভর্তি হলেন ইস্তাম্বুলের বিখ্যাত প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে। তবে প্রথম বর্ষে নয়, দ্বিতীয় বর্ষ থেকে তার বিশ্ববিদ্যালয় জীবন শুরু হয়। গড়ার কারিগর এই মেধাবী তরুণ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়েছিলেন মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং। রেকর্ডসংখ্যক নাম্বার নিয়ে তিনি প্রথম হয়ে সবাইকে তাক লাগিয়েছিলেন।
আত্মবিশ্বাস ও পরীক্ষার ভালো ফলাফল তাকে শিক্ষকতা পেশায় বেশি আকৃষ্ট করত। কিন্তু নিয়ম অনুযায়ী তুরস্কের প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচডি ছাড়া শিক্ষকতা শুরুর কোনো সুযোগ ছিল না। তারপরও সহকারী হিসেবে বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দিলেন। সব নিয়মের ব্যতিক্রম হলেন তিনি। নাজমুদ্দিনকে প্রথম দিন থেকেই ক্লাস নেয়ার সুযোগ করে দেওয়া হয়। ১৯৪৮ সালে পাস করার পর তিন বছরের মধ্যে তিনি পিএইচডির থিসিস প্রস্তুত করে ফেলেন। তারপর জার্মানিতে গবেষণার জন্য পাড়ি জমান। একজন খ্যাতিমান জার্মান বিজ্ঞানীর তত্ত্বাবধানে তিনি দুই বছরেই তিনটি থিসিস জমা দেন। এরপর গবেষণায় ব্যাপৃত হন। তার বিষয় ছিল, এমন ইঞ্জিন তৈরি করতে হবে যাতে জ্বালানি খরচ হবে কম। দ্রুত সাফল্য তাকে চুম্বন করে। আত্মপ্রত্যয়ী নাজমুদ্দিন পিএইচডি নিয়ে ইস্তাম্বুলে ফিরে আসেন। সহকারী অধ্যাপক হিসেবে যোগ দেন ইস্তাম্বুলেরই টেকনিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে। তার আগে মাত্র ২৭ বছর বয়সে আর কোনো ভাগ্যবানের কপালে এমন কৃতিত্ব জোটেনি।
তুরস্কে উচ্চশিক্ষা শেষে এক বছর সামরিক শিক্ষা গ্রহণ করা বাধ্যতামূলক। নাজমুদ্দিন সেকেন্ড লেফটেন্যান্ট হিসেবে যোগ দিয়ে মাত্র ছয় মাসের মাথায় লেফটেন্যান্ট হিসেবে কাজ করার কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন। তার প্রশিক্ষক আমেরিকান ক্যাপ্টেন বিস্মিত হন এই তরুণের ইচ্ছাশক্তি এবং সুবিন্যস্ত চিন্তার সাথে পরিচিত হয়ে। সেনাপ্রশিক্ষণের সময় তিনি একটি নিয়মিত বাহিনীর অস্ত্রের আয়োজন প্রয়োজন বুঝে নিয়েছিলেন। তার পরিকল্পনা দেখে ক্যাপ্টেন জানতে চাইলেন, তার ভাবনার পরিধি এতটা উচ্চাভিলাষী কেন? তুরস্কের প্রয়োজনীয় অস্ত্রের জোগান তো চুক্তি অনুযায়ী আমেরিকা দিচ্ছে। এরবাকান প্রত্যয়দীপ্ত হয়ে জবাব দিয়েছিলেন, আমেরিকা যা পারে আমরাও তা পারব।
পারিবারিক জীবনেই এরবাকান বিশ্বাসের খোরাক পেয়েছিলেন, একই সাথে জীবনজিজ্ঞাসার জবাবও পেয়েছিলেন। তারপরও ইস্তাম্বুলে এসে তার জীবনের মোড় ঘুরে যায়। সান্নিধ্য পান প্রখ্যাত আলেম মেহমেদ যাহিদ কতকুর। তার সান্নিধ্য এরবাকানকে উম্মাহর সোনালি অতীত, জ্ঞানভাণ্ডারের মৌলিক বিষয়, উন্নত বিশ্বাসী জীবনবোধ, ইনসাফ ও ন্যায় প্রতিষ্ঠার সূত্র ধরিয়ে দেয়। সম্ভবত সে সময় তিনি সাঈদ নুরসির রেসালায়ে নূর সম্পর্কেও সুস্পষ্ট ধারণা পেয়ে থাকবেন।
প্রফেসর ড. নাজমুদ্দিন এরবাকান
কর্মবীর এরবাকান কর্মজীবন শুরু করেন বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদানের মাধ্যমে। সামরিক প্রশিক্ষণ শেষে ফিরে যান বিশ্ববিদ্যালয়ে। একই সাথে স্বয়ম্ভর তুরস্কের স্বপ্নদ্রষ্টা, দক্ষ মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার এরবাকান ‘গুমুশ মোটর’ নামে একটি ইঞ্জিন কোম্পানি প্রতিষ্ঠার দিকে মনোযোগ দেন। যারা তুরস্কের অস্ত্র, ইঞ্জিন ও উন্নত প্রযুক্তির জোগানদার তারা এরবাকানের পথ রোধ করে দাঁড়াল। দমলেন না তিনি। একটি সফল কোম্পানি প্রতিষ্ঠা করে ষড়যন্ত্রকারীদের জবাব দিলেন। তত দিনে এরবাকানের সাথে পরিচয় হয় তৎকালীন তুরস্কের প্রধানমন্ত্রী আদনান মেন্দারেসের সাথে। আদনান ছিলেন জহুরি, খাঁটি সোনা চিনতেন, তিনি এরবাকানের চ্যালেঞ্জ গ্রহণের ক্ষমতা ও দৃঢ়তা দেখে আবেগাপ্লুত হন। এরবাকানের জন্য কিছু করার আগেই সামরিক জান্তা আদনানকে ক্ষমতাচ্যুত করে প্রহসনের বিচারে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে হত্যা করে। এই ফাঁসির ঘটনা তার চোখ খুলে দেয়। তত দিনে তিনি জেনে যান দেশী-বিদেশী শিল্পোদ্যোক্তারা কাদের ইশারায় চলেন। তিনি পথ চিনলেন কিন্তু রাজনীতির পঙ্কিল ও পিচ্ছিল পথ তাকে বারকয়েক তার অঙ্গীকারের পথ থেকে ছিটকে ফেলে দেয়। এর পরই চেম্বার রাজনীতিতে প্রবেশের লক্ষ্যে কাজ শুরু করে দেন। অল্প সময়ের মধ্যেই সভাপতি হয়ে তার যোগ্যতার স্বাক্ষর রাখতে শুরু করেন। আবারো সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্ত এবং রাজনৈতিক বাধা তাকে ছিটকে পড়তে বাধ্য করে। এরপরই প্রত্যক্ষ রাজনীতির মাঠে নামার ঘোষণা দেন তিনি।
এক দিকে সততা, অন্য দিকে দৃঢ়তা তাকে রাজনৈতিক চ্যালেঞ্জ গ্রহণের পথ বাতলে দেয়। এই অনলবর্ষী বক্তার জাদুময়ী ভাষা ব্যবহার, যুক্তির অবতারণা ও স্বপ্ন দেখানোর যোগ্যতা জনগণের মনে জায়গা করে দিলো তাকে। কুনিয়া থেকে স্বতন্ত্র প্রার্থী হয়ে সংসদ সদস্য হয়ে গেলেন। তারপর তুরস্কজুড়ে উন্নয়ন, ইনসাফ ও বিজ্ঞানচর্চার ওপর সভা-সমাবেশ করতে শুরু করলেন। তুরস্কের সংবিধানে ধর্মভিত্তিক দল নিষিদ্ধ রয়েছে কামালবাদের জন্ম থেকে। ইসলাম-মুসলমান, আরবি ভাষা, আলেম-ওলামা, মাদরাসা প্রভৃতি শাসকদের মধ্যে এক ধরনের এলার্জি সৃষ্টি করত। সামরিক বাহিনী নিয়ন্ত্রিত শাসকেরা চাইত পশ্চিমা ধাঁচে তুর্কিরা দাঁড়াক। জনগণ চাইত, বিশ্বাসও টিকে থাকুক। জনগণ ও শাসকদের মধ্যকার এ তফাৎ এরবাকান প্রত্যক্ষ করেছেন। প্রফেসর এরবাকান ধর্ম ও বিজ্ঞান, বিজ্ঞান ও ইসলাম, ইনসাফ ও ন্যায়নীতি নিয়ে তুরস্কজুড়ে সভা-সেমিনার ও বিষয়ভিত্তিক কনফারেন্স করতে শুরু করলেন। বিজ্ঞান ও ঐতিহ্যের মেলবন্ধনে জাতিকে জাগৃতির স্বপ্ন দেখাতে শুরু করলেন। আলেমদের সান্নিধ্য ও প্রেরণা এরবাকানকে ‘মিল্লি গরুশ’ নামে একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠার দিকে ঝুঁকে পড়তে উদ্বুদ্ধ করল। অনেকের ধারণা, এটাই ছিল সেই দিনকার প্রেক্ষাপটে তার লক্ষ্যভেদী আন্দোলনের প্রথম পদক্ষেপ এবং এটিই ছিল বাঁক ঘুরে দাঁড়ানোর জন্য একটি অনন্যসাধারণ থিংক-ট্যাংক।
তিনি যে দুর্দান্ত সংগঠক ছিলেন সেটির প্রমাণ দিয়েছিলেন ছাত্র হিসেবে বিশ্ববিদ্যালয় জীবনেই। বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে নামাজ পড়ার ব্যবস্থা ছিল না। ছাত্রদের নিয়ে রাতারাতি প্রতিষ্ঠা করলেন একটি ঘরোয়া মসজিদ। ‘মিল্লি গরুশ’ তুর্কি ভাষার দু’টি প্রতীকী শব্দ। এর অর্থ ‘জাতীয় ভিশন’। ‘জাতি’ বুঝাতে তিনি তুরস্ক ও মুসলিম উম্মাহর মিশন-ভিশনকে এক করে দেখেছেন। লক্ষ্য ছিল, তারুণ্যের ভেতর জাগৃতির মন্ত্র ছড়িয়ে দেয়া, আধ্যাত্মিকভাবে সমৃদ্ধ হওয়া, জাতিকে অর্থনৈতিকভাবে স্বয়ংসম্পন্ন করা, উম্মাহর ঐক্য চেতনায় ভর করে সাম্রাজ্যবাদ ঠেকানো।
একাধিক নিবন্ধে উল্লেখ করেছি, তুরস্কের রাজনীতি নিয়ন্ত্রণ করত সেনাবাহিনী। এখনো সেই ধারা চলছে। সামরিকভাবে এরদোগানকে উৎখাতের একটা চেষ্টা গত বছর ১৫ জুলাই জনগণ প্রতিহত করে দেয়। নির্বাচিত সরকার এবং সংসদের পক্ষেই জনগণ সাহসী ভূমিকা পালন করেছে। আগে সামরিক নেতারাই আমলাতন্ত্রের ওপর ভর করে নেপথ্যে থেকে দেশ চালাতেন। প্রফেসর এরবাকান এবং তার মিশন ভিশন তাদের অজানা ছিল না। এটা এরবাকানও জানতেন। তাই চেতনার উৎস হিসেবে মিল্লি গুরুশকে রেখে ‘মিল্লি নিজাম পার্টির’ মাধ্যমে রাজনৈতিক তৎপরতা চালানোর সিদ্ধান্ত নিলেন। মাত্র এক বছরের মাথায় এই দলটিকে নিষিদ্ধ করে দেয়া হলো। এরপরও এরবাকান থেমে গেলেন না। গঠন করলেন ‘মিল্লি সালামত পার্টি’। এই দলটি নির্বাচনে অংশ নেয়ার সুযোগ পেল। আসনও পেল ৪৮টি। কিছু শর্তের ভিত্তিতে কোয়ালিশন সরকারে যোগ দিলেন। এরবাকান হলেন উপপ্রধানমন্ত্রী। তার দায়িত্বে ছিল অর্থ বিভাগ। তার দল থেকে শিল্প, শিক্ষা ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর দায়িত্ব পেয়েছিলেন তিনজন যোগ্য ব্যক্তি।
এরবাকানের তৎপরতা ছিল এতটাই দৃষ্টিগ্রাহ্য, মনে হচ্ছিল দেশটা যেন তিনিই পরিচালনা করছেন। উপপ্রধানমন্ত্রী হয়েও তিনিই যেন সরকারে নেতৃত্ব দিচ্ছেন। সময় মেপে কাজ করতে অভ্যস্ত এরবাকান সাম্রাজ্যবাদ ও ইহুদি লবির শ্যেনদৃষ্টিতে পড়েন। মাত্র ক’টা বছরের মধ্যেই তিনি বিমান তৈরির কারখানাসহ ২৭০টি ভারী শিল্পকারখানা প্রতিষ্ঠা করে সবাইকে তাক লাগিয়ে দেন। এই সময় কোয়ালিশন সরকারকে দিয়ে তিনি ছয় হাজার গ্রেফতারকৃত মুসলিমকে মুক্তি দেয়ার ব্যবস্থা করেন। সাইপ্রাসকে গ্রিস থেকে মুক্ত করে ‘তুর্কি সাইপ্রাস’ গঠন করেন। সাইপ্রাসের নিপীড়িত মুসলিমরা জুলুমের নিগড় থেকে মুক্তি পায়। তিনিই স্ব-উদ্যোগে মাদরাসা নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিষ্ঠার দ্বার উন্মুুক্ত করে দেন। দেশজুড়ে কুরআন চর্চার অসংখ্য কেন্দ্র গড়ে তোলেন। মাদরাসাছাত্রদের উচ্চশিক্ষার বন্ধ সুযোগ অবারিত করে দিলেন। সাঈদ নুরসির রেসালায়ে নুরের ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের ব্যবস্থা করেন। সবধরনের অফিস-আদালতে, এমনকি সেনাছাউনিতেও মসজিদের ব্যবস্থা করে দিলেন। ধর্মীয় বই প্রকাশের বিরোধী সব কালাকানুন বাতিল করে দিলেন। নৈতিকতা ধ্বংস এবং তরুণদের বস্তুবাদী ও অনৈতিক কাজে প্রলুব্ধ করে, এমন কিছু আচরণ নিষিদ্ধ করে আইন তৈরি করা হয়।
তদানীন্তন কোয়ালিশন সরকারকে উৎখাতের জন্য সেনাবাহিনী সুযোগ খুঁজতে থাকে। ১৯৮০ সালের ৬ সেপ্টেম্বর তুরস্কের কুনিয়াতে কুদস দিবস পালনের অভিযোগে ১২ সেপ্টেম্বর সামরিক অভ্যুত্থান ঘটিয়ে এরবাকানের দলটিকে নিষিদ্ধ করা হলো। একই সাথে অন্যান্য দলও নিষিদ্ধ হলো। বিশেষভাবে এরবাকানকে রাজনীতি থেকেও নিষিদ্ধ করে দেয়া হয়। তাকে গ্রেফতার করে জেলে পাঠানো হলো। অবশ্য সামরিক অভ্যুত্থানের আগেই পরিকল্পিতভাবে কোয়ালিশন থেকে মিল্লি সালামত পার্টিকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়া হয়েছিল।
এরবাকান এ সময় রাষ্ট্রশক্তির বেপরোয়া জুলুম নির্যাতন এড়াতে পারেননি। তাকে রাজনীতিতে নিষিদ্ধ করার জন্য সাজানো হয় মিথ্যা মামলা। রাজনীতিতে নিষিদ্ধ করে, ১৯৮৩ সালে তাকে জেল থেকে মুক্তি দেয়া হয়। মুক্তি পেয়েই তিনি নতুন পথে হাঁটার পথ খুঁজলেন। দলের নেতৃবৃন্দকে নিয়ে নিজে নেপথ্যে থেকে রেফাহ পার্টি গঠন করলেন। প্রতিষ্ঠার অল্প ক’দিন পরই রেফাহ পার্টি তুরস্কের জনপ্রিয় দলে পরিণত হয়। ১৯৮৭ সালের গণভোটের মাধ্যমে নাজমুদ্দিনের ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নেয়া হলো। আবার তিনি রাজনীতিতে সক্রিয় হলেন। সভাপতি হলেন রেফাহ পার্টির। তিনি সভাপতি হওয়ার পর দলটির জনপ্রিয়তা হাজার গুণ বেড়ে যায়। ১৯৯৪ সালের স্থানীয় নির্বাচনে দলটি বিপুল সাফল্য পায়। ইস্তাম্বুল, আঙ্কারাসহ অনেকগুলো সিটিতে বিজয় পেলেন তারা।
এবার তিনি আবার কৌশল পাল্টিয়ে ন্যায়ভিত্তিক ইনসাফের সমাজ প্রতিষ্ঠার আওয়াজ তুললেন। ১৯৯৬ সালের জাতীয় নির্বাচনে জয় পেয়ে সরকার গঠন করলেন। মাত্র ১১ মাসের মাথায় আরেক পরিকল্পিত সামরিক অভ্যুত্থান ঘটিয়ে তাকে ক্ষমতাচ্যুত করা হয়।
কিন্তু ১১ মাসে তিনি দেশকে এগিয়ে নিলেন এক অভাবনীয় স্তরে। তিনিই ছিলেন ‘ডি-৮’ নামে আটটি মুসলিম দেশের সমন্বিত ফোরামের উদ্যোক্তা। সদস্যরাষ্ট্রগুলো হচ্ছে- তুরস্ক, ইরান, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, মিসর, বাংলাদেশ, পাকিস্তান ও নাইজেরিয়া। এর বাইরে সুদের হার কমানো, লোকসান ঠেকানো, বেতন বৃদ্ধি, শিল্পকারখানায় উৎপাদনের চাকা সচল করাসহ অর্থনৈতিকভাবে শক্তিশালী তুরস্ক গড়ার ভিত্তিটায় স্থিতি এনে দিলেন। তার উদ্যোগেই মুসলিম দেশগুলোর কমন মার্কেট ধারণা কার্যকর হয়। তার ঘোষণা ছিল, পূর্ণমেয়াদ ক্ষমতাচর্চার সুযোগ পেলে তিনি তুরস্ককে জাপান-জার্মানদের চেয়েও বড় আকারে শিল্পায়নের মহাসড়কে তুলে দেবেন।
তার এই সাফল্য ও স্বয়ম্ভরতার স্বপ্ন ভেঙে চুরমার করে দিতে উদ্যত হলো ইহুদি লবি এবং সাম্রাজ্যবাদী শক্তি। এবার তার বিরুদ্ধে অভিযোগ তোলা হলো, তিনি শরিয়তভিত্তিক সরকার কাঠামো গঠন করবেন এবং সেভাবেই দেশ চালাবেন। তাকে অপসারণের জন্য বরাবরের মতো সেনাবাহিনীর সাহায্য চাওয়া হলো। এরবাকান এবারো কৌশল পাল্টালেন। শর্তসাপেক্ষে তিনি সরে দাঁড়াবেন এবং প্রধানমন্ত্রীর আসনও ছেড়ে দেবেন, কিন্তু তার কোয়ালিশন সরকারের অন্যতম নেত্রী তানসি সুলারকে প্রধানমন্ত্রী করতে হবে। প্রেসিডেন্ট সোলেমান ড্যামিরেল সেই প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেননি। বরং রেফাহ পার্টিকে নিষিদ্ধ করে দেন এবং এরবাকানকে আবার রাজনীতি থেকে নিষিদ্ধ করার ঘোষণা দেন। এ সবই করা হয় সাংবিধানিক আদালতের দোহাই দিয়ে। এরপরও এরবাকান থামলেন না। তার মিল্লি গুরুশের অন্যতম শীর্ষ সংগঠক রেজাই কুতানের মাধ্যমে ফজিলত পার্টি গঠন করেন, যা প্রতিষ্ঠার অল্প ক’দিন পরই নিষেধাজ্ঞার কবলে পড়ে। ২০০১ সালে এসে ক্যাটালিস্ট ফোরাম এবং থিংকট্যাংক মিল্লি গুরুশের মধ্যে চিন্তার বিস্তৃতি ঘটে। একদল তরুণ তুরস্কের রাজনৈতিক বাস্তবতার কথা বলে লিবারেল গণতন্ত্রের পথে চলার উদ্যোগ নিয়ে একে পার্টি গঠন করেন। এর আগে সা’দাত পার্টির যাত্রা শুরু হয়। বিরোধটি আদর্শ ও চিন্তাগত ছিল না। ছিল কৌশলগত। একে পার্টি সময়ের সাথে লাগসই হয়ে চলার কথা বলেছে। বারবার সাংবিধানিক আদালতের কোপানলে পড়ার বিষয়টি এড়াতে চেয়েছে। অন্য দিকে, সা’দাত পার্টি মিল্লি গুরুশের মূল স্পিরিট ধরে রাখার পক্ষে অবস্থান নেয়। সা’দাত পার্টি নেতৃত্ব সঙ্কটে পড়লে ২০১০ সালে ৮৪ বছর বয়সে প্রফেসর ড. নাজমুদ্দিন এরবাকান পুনরায় দলের সভাপতির দায়িত্ব গ্রহণে বাধ্য হন। একে পার্টি রাজনৈতিক দৌড়ে এগিয়ে থাকলেও সা’দাত পার্টিও তুরস্কের মাটিতে চতুর্থ বৃহত্তম রাজনৈতিক দল হিসেবে টিকে আছে। এক বছর পর এরবাকানের মৃত্যু মিল্লি গুরুশের সব পক্ষকে চিন্তাগতভাবে একই সমতলে নিয়ে আসে। এখন এরবাকান ব্যক্তি নন, একটি প্রেরণাদায়ক প্রতিষ্ঠান। তিনি তুরস্কের জনগণকে বিশ্বাসভিত্তিক ইনসাফ, ন্যায়নীতি ও উন্নয়নের পথে এগোনোর প্রেরণা হয়ে আছেন। মুসলিম উম্মাহও তাকে একটি সঙ্কটকালীন সময়ের বরপুত্র ও বিপরীত স্রোতের মুখে দাঁড়ানোর কালপুরুষ ভেবে নতুন চিন্তার পথিকৃতের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করে রেখেছে।
এরবাকানের চিন্তা-দর্শন এবং প্রায়োগিক রাজনীতির চর্চা সবাইকে প্রেরণা জোগাবে। তার কাছে লক্ষ্যভেদী উদ্দেশ্যের গুরুত্ব ছিল বেশি। দলীয় চিন্তা এবং ক্ষুদ্র ভাবনা তাকে কখনো কক্ষচ্যুত করেনি; লক্ষ্যভ্রষ্ট করেনি। তিনি চেয়েছিলেন সমৃদ্ধ তুরস্ক ও ঐক্যবদ্ধ উম্মাহ। পেশায় ইঞ্জিনিয়ার হলেও তিনি ছিলেন বাস্তবে কিংমেকার, অসাধারণ সংগঠক ও সময়ের এক সাহসী সন্তান।
যারা ভাবেন ইনসাফের সমাজ নিয়ে, প্রায়োগিক রাজনীতির কর্মকৌশল ও ধরন নিয়ে, তাদের জন্য প্রফেসর ড. নাজমুদ্দিন এরবাকান এ সময়ের একজন আদর্শ পথপ্রদর্শক ও মডেল হতে পারেন। তার জীবনভিত্তিক লেখা ‘দাওয়াম’ বা ‘আমার সংগ্রাম’ প্রেরণা হয়ে উঠতে পারে।