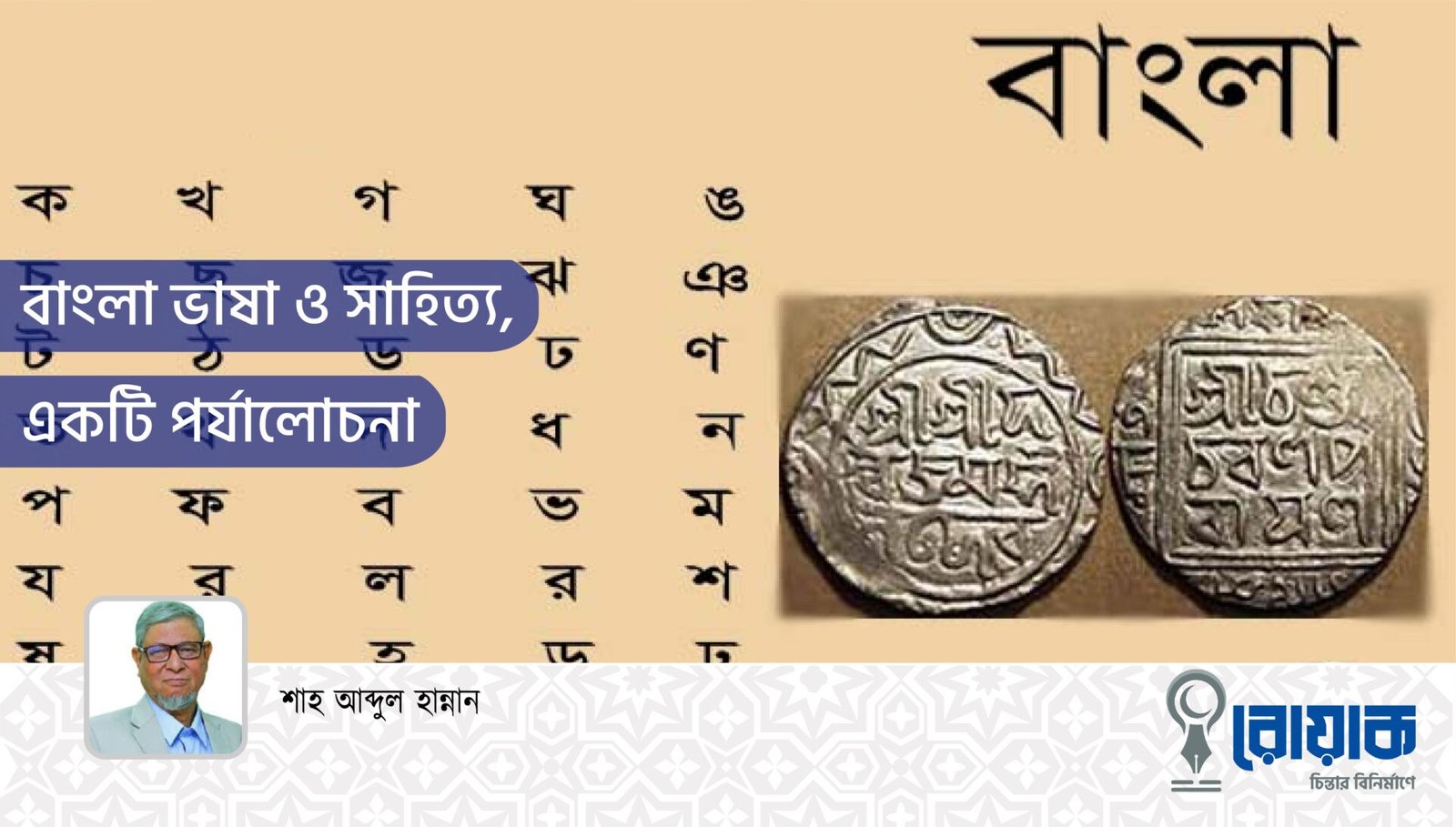আমাদের ভাষা আন্দোলনের পঞ্চাশ বছর পূর্তি হলো। ভাষা ও সাহিত্যে আমাদের অর্জনকে মূল্যায়ন করা প্রয়োজন। আমার যতটুকু পড়াশুনা তার আলোকে আমি দেখতে পাই বাংলাভাষা একটি অত্যন্ত শক্তিশালী ভাষায় পরিণত হয়েছে। এটা এমনি করে হয়নি। রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, ফররুখ এবং এর পরে অন্যান্য কবি সাহিত্যিক যারা এসেছেন, তাদের চেষ্টা ও সাধনার ফলেই এই ভাষা একটি শক্তিশালী রূপ গ্রহণ করে। এই ভাষার একটি বড় সুবিধা হলো বিদেশী শব্দ ভাণ্ডার থেকে অবলীলায় শব্দ গ্রহণ করা। একদিকে সংস্কৃত, অন্যদিকে আরবী এবং ফার্সী থেকে ব্যাপকভাবে শব্দ গ্রহণ এবং পরবর্তীকালে যেহেতু ইংরেজরা দু’শো বছর এদেশ শাসন করে সেখান থেকে বাংলা ভাষায় ইংরেজী শব্দও ব্যাপক ভাবে প্রবেশ করে। ফলে দেখা যায় বিশ্বের যে কয়টি ভাষার শব্দ ভাণ্ডার বেশ সমৃদ্ধ তার মধ্যে বাংলা একটি। যদিও এই বিষয়টি অবশ্যই গবেষণার দাবীদার।
যদি একটি ভাষার শব্দভাণ্ডার খুব ব্যাপক হয় তাহলে সে ভাষা যেকোনো বিষয় প্রকাশ (Express) করতে পারে। যেকোনো বিষয় সে ভাষার মাধ্যমে প্রকাশ করা যায়। আমি মনে করি বাংলা ভাষার মাধ্যমে বর্তমানে যেকোনো বিষয়, যেকোনো কিছু প্রকাশ করা সম্ভব—তার শব্দভাণ্ডারের ব্যাপকতার কারণে। তুলনামূলকভাবে শব্দভাণ্ডার অতি অল্প হলে সে ভাষার মাধ্যমে কখনো ব্যাপক চিন্তাধারা তুলে ধরা সম্ভব হয় না। বাংলা ভাষার মাধ্যমে বর্তমানে যেকোনো দর্শন, অর্থনীতি, রাষ্ট্রনীতি বা সমাজবিজ্ঞান, বিজ্ঞান কিংবা সকল কিছু প্রকাশ করা সম্ভব। তবে বিজ্ঞানকে প্রকাশ করতে গেলে আন্তর্জাতিক বৈজ্ঞানিক যে শব্দমালা সেগুলোকে গ্রহণ করতে হবে। ইতোমধ্যে যেগুলো গ্রহণ করা হয়েছে তার ফলে যেহেতু কোনো সমস্যা হয়নি, তাই প্রয়োজনে আরো গ্রহণ করলেও কোনো সমস্যা হবে না বলেই আমার বিশ্বাস।
কাজেই আমি বলব, খুবই শক্তিশালী একটি ভাষা আমরা পেয়েছি, যেটা গত এক দেড়শ বছরে অভাবনীয় উন্নতি করেছে। বিশেষ করে গত পঞ্চাশ বছরে এই ভাষা আরো ব্যাপকতর সমৃদ্ধ হয়েছে। ইংরেজি শব্দের প্রবেশ এই সময় ব্যাপকতর হয়েছে। বিজ্ঞানের প্রয়োজনে এবং অন্যান্য কারণে বিশ্বের অগ্রযাত্রার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে অগ্রসর হয়েছে এই ভাষা।
এখানে আরেকটি বিষয় উল্লেখ করতে হয়, সেটা হলো, আমরা একই সঙ্গে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা এবং শিক্ষার মাধ্যম করেছি। যদিও বাংলাকে শিক্ষার মাধ্যম করা ঠিক হয়েছে কিনা – এই নিয়ে কেউ কেউ মতভেদ করেন, তবে আমি মনে করি ঠিকই হয়েছে। ইংরেজি শিখবো, বিশ্বের ভাষা ঠিক আছে। ইংরেজির মাধ্যমে আন্তর্জাতিক যোগাযোগ করতে হবে, তাও ঠিক আছে। কিন্তু এর মানে এই নয় যে, এতবড় একটি শক্তিশালী ভাষা হওয়া সত্ত্বও আমাদের অফিসিয়াল ভাষা ইংরেজি হবে, এই কথা মনে করা একেবারেই অসঙ্গত।
যে কথা বলছিলাম, বাংলা ভাষা যে শিক্ষার মাধ্যম হয়ে গেল প্রাথমিক থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায় পর্যন্ত – তার ফলে আরো অসংখ্য ইংরেজি শব্দ বিজ্ঞানের প্রয়োজনে আমরা গ্রহণ করে ফেললাম। এই ডেভেলপমেন্টটা হলো গত বিশ-ত্রিশ বছরে।
এখন সাহিত্য প্রসঙ্গে আসি। ভাষার মাধ্যমে আমরা সবই প্রকাশ করতে সক্ষম এরকম একটা অস্ত্র আমাদের হাতে থাকা সত্ত্বেও সে তুলনায় আমাদের সাহিত্যের অর্জন ব্যাপক -এটা বলতে আমার দ্বিধা আছে। আজ আমাদের নিজেদেরকে প্রশ্ন করতে হবে, চিন্তার ক্ষেত্রে আমরা কতটুকু লিখেছি, রাষ্ট্রবিজ্ঞান কিংবা অর্থনীতির উপর কতটুকু লিখেছি, দর্শন বা অন্যান্য বিজ্ঞানে এবং সমাজ বিজ্ঞানের ওপর কতটুকু লিখেছি? বাস্তবে দেখা যাবে খুব কমই লিখেছি। কিছু টেক্সট বইয়ের অনুবাদ ছাড়া সত্যিকার অর্থে মূল কাজ আমরা যাকে বলি, তা বাংলা সাহিত্যে করিনি।
তেমনিভাবে উপন্যাস, গল্পের কথা বললেও বলব আমাদের অর্জন খুব বেশি নয়। নিশ্চয় বাংলায় অনেক জনপ্রিয় উপন্যাস লেখা হয়েছে। যেমন ছোট ছোট উপন্যাস যাকে নভেল বলা যায়- যখন একজন লেখক লেখেন – তখন হাজার হাজার কপি বিক্রি হয়ে যায়। কিন্তু সাহিত্যের বিচার এটুকুতেই সীমাবদ্ধ নয়। ভাষার সমৃদ্ধির তুলনায় সাহিত্যের দরবারে আমাদের অর্জন এখনো সেই পরিমাণ নয়। এরপর যদি কবিতা প্রসঙ্গে বলি তাহলে একথা ঠিক যে, আমাদের কবির সংখ্যা অনেক। অসংখ্য কবি আছেন, তার মধ্যে কেউ কেউ উল্লেখযোগ্য কবি হিসেবেও খ্যাতি অর্জন করেছেন।
কিন্তু তবু বলা যায় বাংলা ভাষা একটি শক্তিশালী ভাষায় পরিণত হলেও আমরা সামগ্রিকভাবে একটি শক্তিশালী সাহিত্য তৈরি করতে পেরেছি এমন কথা বলতে পারি না। তবে আমাদের সুযোগ রয়েছে। এই ভাষাকে ব্যবহার করে আমরা একটা শক্তিশালী সাহিত্য তৈরি করতে পারি। উপন্যাসের ক্ষেত্রে, গল্পের ক্ষেত্রে, আর কবিতার ক্ষেত্রে তো পারিই। সর্বোপরি একটা জাতিকে প্রতিনিধিত্ব (Represent) করার জন্য মূল যে চিন্তা (Thought) তার ক্ষেত্রেও। এর জন্যে যেটা প্রয়োজন সেটা হচ্ছে, বিশ্ব সাহিত্যকে জানা (বিশ্বের যে দর্শন-সেটা রাজনৈতিক হোক বা অর্থনৈতিক হোক কিংবা সমাজ বা সভ্যতা সংক্রান্ত থিওরিই হোক) সে সম্পর্কে গভীর পড়াশুনা করা। তাহলেই আমাদের সাহিত্য শক্তিশালী হবে।
বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অগ্রগতিতে অনুবাদ সাহিত্য একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছে। অনুবাদ ক্ষেত্রে যে কাজ হয়েছে, বিশেষ করে বেশকিছু বিশ্বখ্যাত তাফসীর এরই মধ্যে অনূদিত হয়েছে। মাওলানা মওদূদীর তাফসীর তাফহীমুল কোরআন অনুবাদ হয়েছে। সাইয়েদ কুতুবের তাফসীর ‘ফি যিলালিল কুরআন’ অনুবাদ হয়েছে। তাফসীরে ইবনে কাসীর ও মুফতী শফীর তাফসীর মা’রেফুল কোরআন সহ অন্যান্য আরো কিছু উল্লেখযোগ্য তাফসীর অনুবাদ হয়েছে। অনুবাদ বাদে এই সময় বাংলায় মূল তাফসীরও লেখা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে মাওলানা আকরাম খাঁর তাফসীর সহ আরো বেশ কিছু তাফসীরের কথা বলা যায়। প্রসঙ্গত এক্ষেত্রে গিরীশচন্দ্র সেনের নামও এসে যায়। তাফসীরের পর ছিহাহ-ছিত্তা সহ উল্লেখযোগ্য হাদীস গ্রন্থের অনুবাদের কথা উল্লেখ করা যায়। এছাড়া বেশ কিছু ইসলামী বইয়ের অনুবাদও হয়েছে। তবে হাদীস গ্রন্থগুলোর অনুবাদ হলেও হাদীস গ্রন্থের টিকাসমূহের (Commentry) পূর্ণাঙ্গ অনুবাদ হয়নি। এখন পর্যন্ত বোখারী, মুসলিমের যে সমস্ত কমেন্টারি ব্যাখ্যগ্রন্থ রয়েছে, তার পুরোপুরি অনুবাদ হয়নি । এ কথা অবশ্য বলা ভালো যে, আজকে কমেন্টারী অনুবাদ করতে গেলে নতুন করে টীকা যোগ করার (Annotation) প্রয়োজন হবে। কেননা তৎকালীন প্রেক্ষাপট আলাদা ছিল, পরিস্থিতি আলাদা ছিল, যেটা তাদের টিকা বা মতামতে প্রবেশ করেছে। সেদিক থেকে আজকে তার অনুবাদ করতে গেলে তার এনোটেশন লাগবে। তার নতুন করে নোট দিতে হবে।
ইসলামী চিন্তাবিদদের মধ্যে ইমাম গাজ্জালীর কিছু অনুবাদ হলেও ইবনে খালদুন, আল কিন্দি, আল ফারাবী, ইবনুল আরাবী এঁদের বইয়ের তেমন অনুবাদ হয়নি। আধুনিক লেখকদের মধ্যে ড. ইউসুফ আল কারদাভীর কিছু বইয়ের অনুবাদ হয়েছে। অনুবাদ হয়েছে মাও: মওদূদী, ড. মরিস বুকাইলি, আল্লামা আসাদ, সাইয়দ কুতুব, মোহাম্মদ কুতুবের বইয়ের। অনুবাদ সাহিত্যের ক্ষেত্রে ড. ত্বহা হোসাইন, ড. নাজীব কিলানী, নসীম হিজাযীর বইয়ের অনুবাদ হয়েছে। অন্যদিকে ইসলামের উপর বাংলা ভাষায় কয়েক হাজার বই লেখা হয়েছে। এর মধ্যে মাওলানা আকরম খাঁ, গোলাম মোস্তফা, মাওলানা আবদুর রহীম সাহেবের মত চিন্তাবিদদের লেখাগুলোও মান সম্পন্ন হলেও অন্যান্য অধিকাংশ লেখাই নিম্নমানের। এই গুলোকে নোটবুক বলে গণ্য করতে হবে। সংখ্যার দিক থেকে বাংলাদেশ বিশ্বের তৃতীয় মুসলিম দেশ। প্রথম ইন্দোনেশিয়া, দ্বিতীয় পাকিস্তান, তৃতীয় বাংলাদেশ, বর্তমানে। একসময় বাংলাদেশ দ্বিতীয় ছিল। আজ সেই দেশের ইসলামী সাহিত্য লেখার এবং অনুবাদের এই অবস্থা। ড. কারদাভী, ড. আব্দুল হামিদ আবু সলেমান, ড. ত্বহা জাবির আল আলিওয়ালি, মোহাম্মদ আল গাজ্জালী, ড. খুরশীদ আহমদ, ড. ওমর চাপরার লেখার সাথে তুলনামূলক বিচার করলে আমাদের অবস্থান বুঝা যাবে। তখনই আমরা আমাদের ভাষার মাধ্যমে আমাদের সাহিত্যকে আন্তর্জাতিকভাবে গ্রহণীয় ও প্রসারিত করতে ভূমিকা রাখতে পারবো।
একটি ভাষাকে আন্তর্জাতিকভাবে পরিচিতি করার দু’টি পদ্ধতি থাকে। একটি ভাষা যদি নিজেই আরেকটি দেশের ভাষায় পরিণত হয়, একেবারে স্থানীয় ভাষা হয়ে যায়। আর একটি হলো, কোনো ভাষা যদি রাষ্ট্র ভাষা করা হয়। যেমন আরবীর ক্ষেত্রে কোরাইশদের ভাষা মধ্যপ্রাচ্যের পুরা অঞ্চলের ভাষা হয়ে গেছে। সেটা একটা পথ। অথবা আমরা যেমন দেখি ইংরেজি বিশ্বের প্রায় একশটি দেশের রাষ্ট্র ভাষা হয়েছে। আমরা এখনো দেখি ভারত ও পাকিস্তানের অফিসের ভাষা ইংরেজি। কিন্তু আমরা বাংলা ভাষাকে আমাদের অফিসিয়াল ভাষা করতে পেরেছি। যাইহোক, এই ক্ষেত্রে বাংলা ভাষা অন্য একটি এলাকা দখল করে ফেলবে সে সম্ভাবনা নেই। কাজেই, বাংলা ভাষাকে আন্তর্জাতিক ভাবে পরিচিতি করার পদ্ধতি একটাই, সেটা হলো অনুবাদ আমাদের যা কিছু ভালো কাজ হয়েছে সেগুলো অনুবাদ হওয়া দরকার। বিশেষ করে গল্প, কবিতা, ও উপন্যাস, তথা সৃজনশীল সাহিত্য গল্প উপন্যাস, কবিতা মানুষের হৃদয়কে নাড়া দেয়, আবেগকে উদ্বোধিত করে। সুতরাং আমাদের ভালো গল্প গুলোর অনুবাদ হওয়া দরকার। গল্পের সাথে সাথে শক্তিশালী উপন্যাস গুলো অনুবাদ হওয়া দরকার, শক্তিশালী কবিতাগুলো অনুবাদ হওয়া দরকার।
সেই সাথে যদি জ্ঞানের ক্ষেত্রে আমরা কোনো মৌলিক কাজ করে থাকি, যদিও আমি দেখছি না সেগুলো অনুবাদ হওয়া দরকার – এর জন্য রাষ্ট্রের এবং সরকারের একটা দায়িত্ব আছে। সাহিত্যিকদেরও একটা দায়িত্ব আছে, এই জন্যে সংগঠন থাকা দরকার। বাংলা একাডেমি, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ও ভূমিকা পালন করতে পারে। এ ক্ষেত্রে মার্কেটিং (Marketing), অনুবাদ (Translation), প্রচার (Campaign) ছাড়া কোনো বিকল্প নেই। আর অনুবাদ শুধু ইংরেজিতে নয়, অন্য ভাষাতেও হতে হবে। ইংরেজিতে করলে সুবিধা হলো অন্য ভাষায় রূপান্তর করা সহজ হয়। আমাদের দেশে ইংরেজি জানা লোক অনেক আছে। কিন্তু জার্মান জানা লোক অত নেই। অন্যান্য ভাষা জানা লোক ধরতে গেলে নেই-ই। সুতরাং অনুবাদ ইংরেজিতে করলে এবং মার্কেট হয়ে গেলে সেখান থেকে অটোমেটিক অন্যান্য ভাষায় অনুবাদ হয়ে যাবে। আর একটা পদ্ধতি হতে পারে, কয়েকটি বিশেষ ভাষায়, যে গুলোতে বিশ্বের বিরাট এক অংশ কথা বলে, যেমন চাইনিজ । কিছু চাইনিজ জানা লোক আমাদের আছে অথবা রাশিয়ায় পড়াশুনা করা রুশ জানা লোক আমাদের কিছু আছে। তাদের মাধ্যমে যদি আমরা অনুবাদ করি তাহলে সেটা একটা পদ্ধতি হতে পারে। সেটা করা উচিতও বলে আমি মনে করি। তেমনি ফ্রেঞ্চ জানা কিছু লোক আমাদের থাকতে পারে। তাদের মাধ্যমেও সেই ভাষায় আমরা সরাসরি অনুবাদ করতে পারি। তবে ইংরেজি করলে ইংরেজি থেকে অন্যান্য ভাষায় আবার পূনরায় অনুবাদের সম্ভাবনা থাকে। বর্তমানে আমাদের দেশে বিশ্বের বেশ কয়েকটি দেশের ভাষাও শিক্ষা দেয়া হয় ।
সবচেয়ে ভালো হবে, যদি সরকার বাংলা একাডেমি ও ইসলামিক ফাউন্ডেশনের ভিতর একটা করে অনুবাদ ব্যুরো খুলে ফেলেন। আলাদা নতুন কোনো সংগঠন করতে গেলে নানান ধরনের সমস্যা চলে আসে। তাদের একটা উইং (Wing) খুলে ফেলা বর্তমান কাঠামোর (Existing structure) মধ্যে সহজ হবে।
মনে রাখা দরকার, আরোপিত কিছুই মঙ্গলজনক হয় না। কিন্তু আমাদের ভাষার ক্ষেত্রে এ ধরনের প্রচেষ্টা চালানো হয়েছে। এটা আরোপ করা হয়েছে দুই ভাবে। মুসলিম লেখকদের মধ্যে ইসলাম সম্পর্কে নানা ভুল বোঝাবুঝির কারণে এবং ব্যক্তিগত জীবনে কিছু তিক্ততার কারণে। কিংবা নিজেদের পড়াশুনার কারণে ইসলাম সম্পর্কে ভালো ধারণা রাখেন না-এই ধরনের লেখকরা ইসলাম বিরোধী, তৌহিদ বিরোধী শব্দ ঢুকিয়ে দিয়েছে। এইটুকু হলো আরোপিত ব্যাপার। আবার পশ্চিমবঙ্গের বাংলা ভাষার সাথে আমাদের বাংলা ভাষার পার্থক্যের কারণেও এমন কিছু শব্দ এসেছে, এ অঞ্চলের জন্য যা আরোপিত। কেউ যদি এই দুই এলাকার ভাষা গভীর ভাবে পর্যালোচনা করেন তিনি এই পার্থক্য ধরতে পারবেন। ভাষা আন্দোলনের ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে-এ সব বিষয়গুলোতে আমাদের বিশেষভাবে নজর দেয়া দরকার।