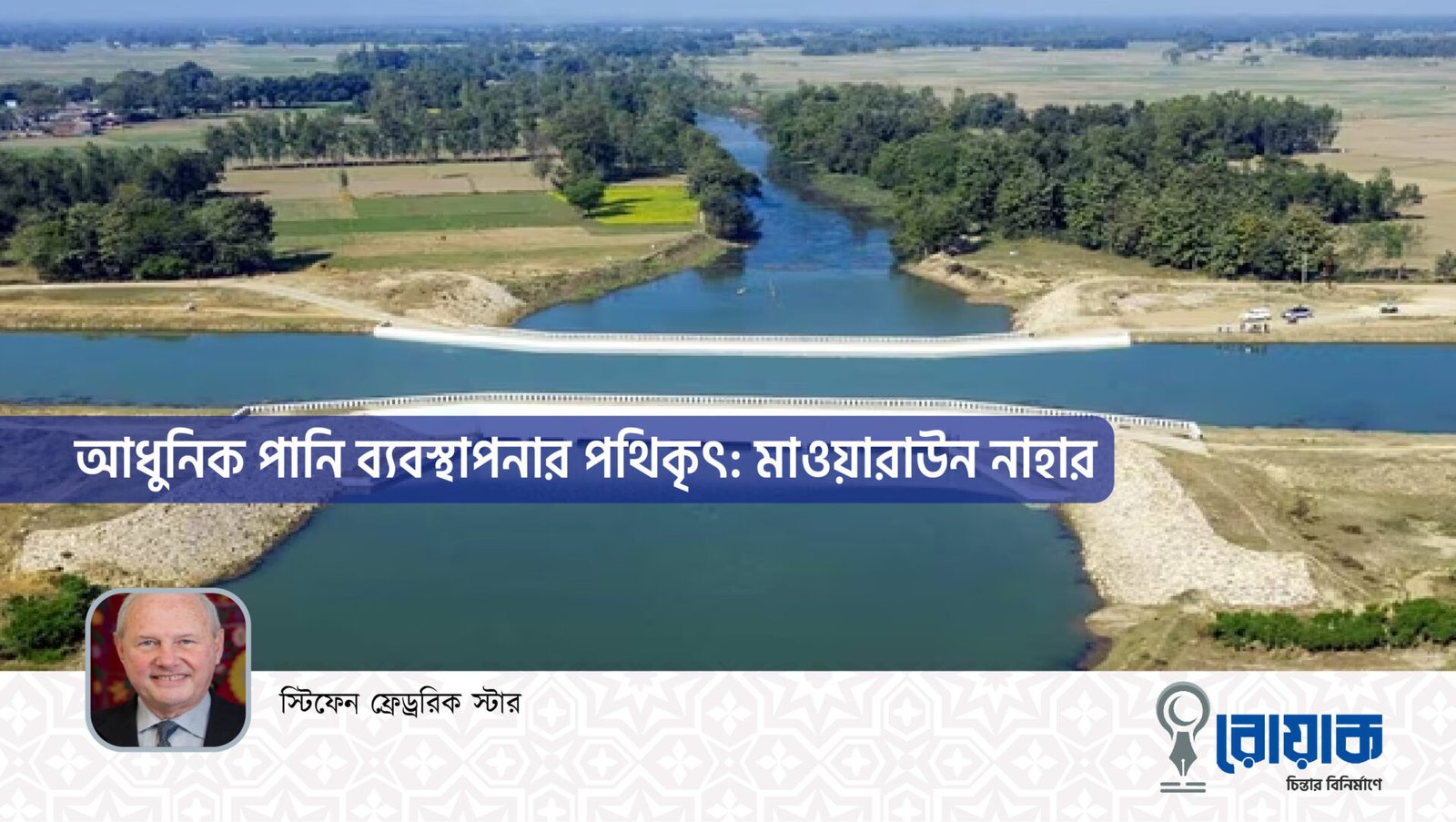মাওয়ারাউন নাহারে সভ্যতার বিকাশ কোন প্রাকৃতিক ঘটনা নয়; বরং এর পিছনে রয়েছে মাওয়ারাউন নাহারে বিকশিত অসাধারণ বুদ্ধিবৃত্তি। যার ফলে মধ্য এশিয়ার অনুর্ভর ভূমিগুলোও ফুলে ফলে ভরে উঠেছিল। শুধুমাত্র পানির যথাযথ ব্যবস্থাপনা মরুদ্যানে একটি কৃষিভিত্তিক সভ্যতার জন্ম দিয়েছিল। আর এধরণের অসাধ্য সাধন হয়ে অসাধারণ সেচ ব্যবস্থাপনা মাধ্যমে। এ দৃষ্টিকোণ থেকে মাওয়ারাউন নাহারকে সেচ ভিত্তিক সভ্যতা বললেও ভুল হবে না। মাওয়ারাউন নাহারের সমাজ ব্যবস্থায় পানির সংরক্ষণ, বণ্টনের জটিল ব্যবস্থাপনা খুবই দক্ষতার সাথে করা হয়েছিল, কেননা পানির যথাযথ ব্যবস্থাপনা তাদের সমাজের অন্যতম চালিকা শক্তি হিসেবে আবির্ভূত হয়েছিল। (৩৭) “সেচ নির্ভর সভ্যতা” এই পরিভাষাটি সর্বপ্রথম জার্মান-আমেরিকান গবেষক কার্ল উইটফোগেল Karl Wittfogel তার বিতর্কিত গ্রন্থ Oriental Despotism(1957) এ ব্যবহার করেছিলেন । যদিও তিনি এই পরিভাষাটি মূলত চীন, ভারত থেকে শুরু করে মেক্সিকো ,মেসপটোমিয়ার মতো সভ্যতাগুলোর জন্য ব্যবহার করেছিলেন , তবে এক্ষেত্রে তার এই পরিভাষাটি মধ্যে এশিয়ার ক্ষেত্রেও খাটে। সেচের উপর অধিক নির্ভরশীলতা সমাজিক ভাবে অত্যন্ত সুশৃঙ্খল এবং হায়ারারকিক্যাল রাজনৈতিক সংস্কৃতির জন্ম দেয় যাকে উইটফোগেল despotism বলে আখ্যায়িত করেছেন। এ ধরণের ব্যবস্থায় রাষ্ট্রই সেচ ব্যবস্থার জন্য প্রয়োজনীয় শ্রমিক ও আনুষাঙ্গিক জটিল ব্যবস্থাপনা কেন্দ্রীয়ভাবে নিয়ন্ত্রণ করে থাকে।
মূলত চীন এবং মেসো আমেরিকাকে বিবেচনায় রেখে প্রণীত উইটফিগেলের এই মডেলটি মাওয়ারাউন নাহারের জন্য এই আপাতদৃষ্টিতে কার্যকর হলেও এখানে ব্যবস্থাপনাগত দিক থেকে একটা বড় পার্থক্য আছে । চীনে সেচ ব্যবস্থা যেরকম সরকার কর্তৃক কেন্দ্রীয়ভাবে নিয়ন্ত্রিত ছিল মাওয়ারাউন নাহারের ক্ষেত্রে তেমনটা ঘটেনি। মাওয়ারাউন নাহারে সরকারিকরণ ব্যাপক ভাবে বিস্তৃত ছিল না। আর সীমিত সেনা শক্তির অধিকারী এসকল সরকারের পক্ষে ব্যক্তি পর্যায়েও সেচ ব্যবস্থার কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপনা করা সম্ভবপর ছিল না। যেহেতু কারো পক্ষেই পুরো অঞ্চলের কৃষিকে এককভাবে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব ছিল না; ফলশ্রুতিতে এই অঞ্চলের ইতিহাসে অনেকগুলো সালতানাতের জন্ম হতে দেখা যায়। মাওয়ারাউন নাহারের এ সকল বড় বড় সেচ ব্যবস্থাগুলো মঙ্গল আক্রমণের আগ পর্যন্ত টিকে ছিল।(৩৮) যেসকল প্রকৌশলীরা এ ধরণের সেচ ব্যবস্থা প্রণয়ন করেছিলেন তারা একেকজন নিশ্চিত অনেক বড় মাপের সেচবিদ ছিলেন। এখানে আমরা দুইধরণের সেচ ব্যবস্থার উপস্থিতি দেখতে পাই।
প্রথমত এক ধরণের সেচ ব্যবস্থার উপস্থিতি দেখা যায় যেগুলো তৈরি করা হতো পাহাড়ের ঐ সকল চূড়ায় যার পাশ দিয়ে নদী প্রবাহিত হয়েছে এমন স্থানে তারা বাঁধ (Dam) দিয়ে কৃত্রিম হ্রদের তৈরি করতেন যার পানি সমতলে সুনির্দিষ্ট পথে সুচারু ভাবে প্রবাহিত করা সম্ভব হতো। এসকল হ্রদ বিশাল, মাঝারি এবং ক্ষুদ্র আকারের হতো । এগুলোকে কাদামাটি দিয়ে খুব সুন্দর আকৃতি দেওয়া হতো। এরকম কিছু হ্রদ হচ্ছে বালখ নদীর সংলগ্ন বালখ, বুখারার জারুয়্যিদ, মার্ভের মুরগাব, আফ্রিসিয়াবের জাফারসান, গুরগঞ্জের আমু দরিয়া। এই হ্রদগুলোয় সুইচ গেটের ব্যবস্থাপনা ছিল। এর মাধ্যমে লোকালয়ে সারা বছর সকল মৌসুমে চাহিদা মতো পানির সরবারাহ নিশ্চিত করা সম্ভব হতো। মাঝে মাঝে এই হ্রদগুলো শত্রুপক্ষের প্রধান হাতিয়ারেও পরিণত হতো। ইতিহাসে বালখ এবং গুরগঞ্জকে হ্রদের পানিতে ভাসিয়ে দেওয়ার নজিরও আমরা দেখতে পাই।(৪০) এসকল হ্রদের পানি শহরে এবং কৃষি জমিতে প্রবাহিত করার জন্য প্রতিটি শহরের চারপাশে অনেকগুলো খাল খনন করা হয়েছিল। বালখে আমরা এরকম ২০ টি খালের উপস্থিতি দেখতে পাই। সাধারণত এসকল খালগুলো একেকটি ৬০ মাইল পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল এবং খুব স্বাভাবিক ভাবেই বলা যায় এ ধরনের পানির ব্যবস্থাপনা খুবই উঁচ্চ মানের ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের নিদর্শন।
এ সকল জলাধারের পানি যাতে দ্রুত বাষ্পে পরিণত না হয় এর জন্য বিকল্প ব্যবস্থা হিসেবে তারা খালগুলোকে গভীর থেকে গভীরত করেছিল ফলে পানির খুব কম অংশই সূর্যের তাপ পেত। কিন্তু তাদের এসকল টেকনিককে সোভিয়েত ইঞ্জিনিয়াররা উপেক্ষা করে গেছে যার ফলাফল এখন সকলের কাছেই দৃশ্যমান। শুধু খালের মাধ্যমেই পানির ব্যবস্থাপনা ছিল না এর সাথে মাটির নিচ দিয়ে পোঁড়া মাটির পাইপের মধ্য দিয়েও পানির সরবারাহ করা হতো এবং এ সকল পাইপ থেকে শাখা প্রশাখাও বের হতো এগুলো একটা আরেকটার সাথে খুব ভালোভাবেই খাপ খেত। আফ্রিসিয়াবের ক্ষেত্রে এ ধরণের পানির কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপনা দেখে একজন পর্যটক তো একে অষ্টম আশ্চার্য হিসেবে আখ্যায়িত করেন।
এবার দ্বিতীয় প্রকারের ব্যবস্থাপনার দিকে আলোকপাত করা যাক। এ ধরণের ব্যবস্থাপনায় সাধারণত শহরের নিকটবর্তী উঁচু স্থানে পানি সংরক্ষণ করে সেখান থেকে শহুরে বসতি এবং আশপাশের কৃষি জমিতে মাটির নিচে খুবই যত্নসহকারে খননকৃত নালার মাধ্যমে পানি সরবরাহ করা হতো। এ সকল নালাকে তারা “কেরেজ” বলতো। এই কেরেজগুলো অনেক দূর পর্যন্ত বিস্তৃত হতো এবং এসকল কেরেজে একটা নির্দিষ্ট দূরত্ব পরপর গভীরতা বৃদ্ধি পেত যাতে পানির গতি ঠিক থাকে। কয়েক মাইল বিস্তৃত এসকল কেরেজ পুরো শহরে জালের মতো ছড়িয়ে থাকত এবং এগুলোর গভীরতা তিনশত ফিট পর্যন্ত ছিল। সত্যি এ ধরণের পানি ব্যবস্থাপনা প্রকৌশল জগতের অনন্য নির্দশন।
উভয় ধরণের পানির ব্যবস্থাপনায় উঁচ্চতা ব্যবহার খুবই সূক্ষভাবে করা হয়েছে। নগর ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে তাদের পানির ব্যবস্থাপনা ছিল আরো জটিল এবং অত্যন্ত নিখুঁত। মাওয়ারাউন নাহারের প্রকৌশলীগণ শহরের মাটির তলদেশে পোঁড়ামাটির নল দিয়ে পানি বাসা বাড়ির টয়লেট ,বাথরুম, পাকঘর পর্যন্ত পৌঁছে দিয়েছিল। শুধু তাই নয় এসকল বাসা বাড়ির থেকে সৃষ্ট বর্জ্য নির্গমনের জন্য আলাদা বর্জ্য ব্যবস্থাপনাও তারা করতে সক্ষম হয়েছিলেন (৪২)। আপনার মনে প্রশ্ন জাগতেই পারে এ ধরণের কাজের জন্য যেরকম দক্ষ লোকবলের দরকার তা কি তাদের ছিল ? হুম ছিল! শুধু ছিলই না প্রচুর পরিমাণে ছিল । এক বালখেই দ্বাদশ শতাব্দীতেই পানি ব্যবস্থাপনার জন্য ১২০০ এর অধিক লোকবল নিয়োগ দেওয়া হয়েছিল। এর মাঝে শুধু ৩০০ জন প্রকৌশলী-ই ছিলেন ! (৪৩) বলা হয়ে থাকে এ সময় মার্ভ ছিল পৃথিবীর সবচেয়ে বড় শহর এমনকি তৎকালীন চীনের হাংজু থেকেও বড় শহর (৪৪)।
মরুদ্যানে বিকশিত হওয়া এই সভ্যতার কৃষিতে স্বয়ংসম্পূর্ণ ছিল। এর উৎপাদন এবং সম্পদের প্রাচুর্য ছিল চোখে পড়ার মতো। কিন্তু এসকল উৎকর্ষতার মূলে থাকা পানির ব্যবস্থাপনা করা মোটেই সহজ ছিল না। মরুদ্যানে পানির সংরক্ষণ, সরবহরাহ, খাল খনন, নাব্যতা নিয়ন্ত্রণ সত্যি-ই তাদের জন্য বেশ চ্যালেঞ্জিং ছিল। কিন্তু তারা তাদের চিন্তাগত বিকাশ এতদূর ঘটাতে পেরেছিল যা তাদেরকে এ সকল চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে স্বল্প উপায় উপাদান দিয়ে এরূপ নগরায়ন করতে সক্ষম করে তোলে। বিশেষত তাদের মাটির তলদেশে পাইপের মাধ্যমে পানির ব্যবস্থাপনা করার মতো ইঞ্জিনিয়ারিং সত্যি অসাধারণ। এ ধরণের সভ্যতা যা ব্যাপকভাবে বিকাশের ক্ষেত্রে বহির্গত সম্পদের পরিবর্তে নিজস্ব উপায় উপাদানের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠে যাকে আমরা “Intensive Civilization”(স্বয়ংসম্পূর্ণ সভ্যতা) বলি। জাপান এ ধরণের সভ্যতার অন্যতম উদারহরণ। এ ধরণের সভ্যতা নিজেদের সম্পদের যথাযথ ব্যবহারের মাধ্যমে গড়ে উঠে অন্যদিকে আরেক প্রকার সভ্যতা আছে যেগুলো সোভিয়েত ইউনিয়নের “Extensive Civilization” (লুটেরা সভ্যতা) মত অন্যদের সম্পদ লুট করে বেড়ে উঠে। এ ধরণের সভ্যতা কেবল রাজ্যের পর রাজ্য দখল করে সম্পদ আহরণ করে কেন্দ্রীভূত করতে থাকে।(যেমন হাল আমলের বৃটিশ জায়নবাদী সভ্যতা)
একথা বলতে কোন দ্বিধা নেই যে সেচ ব্যবস্থার অভূতপূর্ব ব্যবহার মাওয়ারাউন নাহারের বুদ্ধিবৃত্তিক ও সাংস্কৃতিক বসন্তেরই ফল যা এই বসন্তকে কয়েক শতাব্দী কাল পর্যন্ত দীর্ঘায়িত করেছিল।