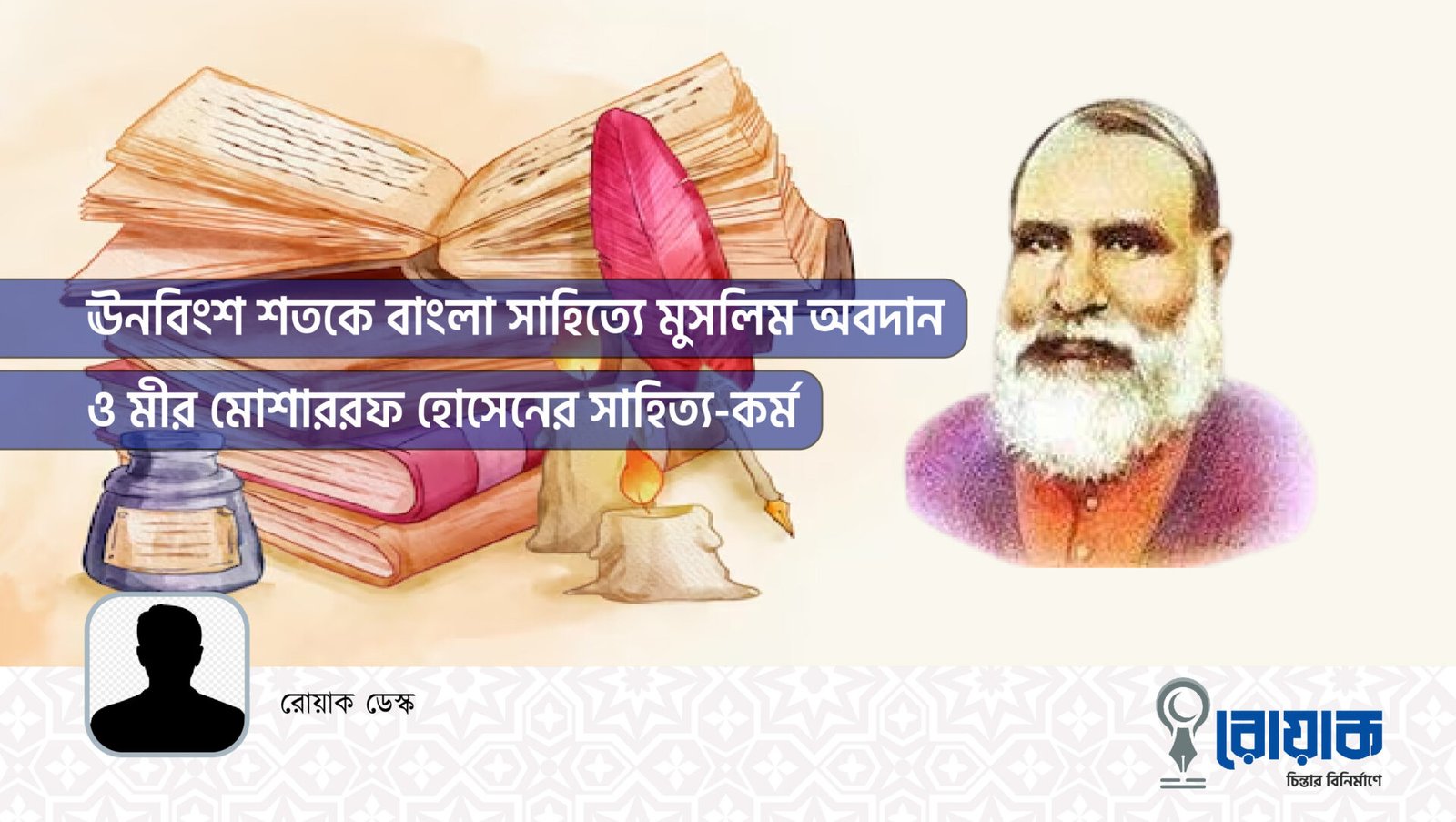১৭৫৭ খ্রীস্টাব্দে পলাশীর যুদ্ধের ফলে বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে যে বিপর্যয় সৃষ্টি হয়েছিল, তা বোধ করি অন্য কোন বড় রকম ক্ষতির চেয়ে কোন অংশে কম নয়। এতদিন পর্যন্ত নবাব-জমিদার ও বিভিন্ন ধনিক-বণিক শ্রেণীর লোকদের আশ্রয়ে ও পৃষ্ঠপোষকতায় কবি-সাহিত্যিকগণ কাব্য ও সাহিত্যের চর্চায় নিয়োজিত ছিলেন। কিন্তু পলাশীর রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের পর রাজনৈতিক বিপর্যয়ের সঙ্গে সঙ্গে স্বাভাবিকভাবেই সামাজিক, সাহিত্যিক ও তামাদ্দুনিক ক্ষেত্রেও সমূহ বিপর্যয়ের সৃষ্টি হয়। কবি ও বিদগ্ধ সংস্কৃতিসেবিগণ পৃষ্ঠপোষকহীন, অসহায় ছিন্নমূল মানুষে পরিণত হলেন। রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিবর্তন ও অনিশ্চয়তার কারণে মানুষের মনে সদা সশংয় ভাব বিরাজ করছিল। এই পরিবর্তমান অবস্থায় মানুষের মানস-রাজ্য নিতান্তই অভিব্যক্তিহীন, ফ্যাকাশে এবং সংক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিল। জনগণ সর্বদা ইংরেজ সৈন্যদের নানারূপ অত্যাচার, অর্থনৈতিক শোষণ প্রভৃতি বালা-মুসীবতের দুর্ভাবনায় চিন্তাকুল থাকতো। এরূপ পরিবেশ কখনো সাহিত্য-সাংস্কৃতিক বিকাশের উপযোগী নয়।
কিন্তু অর্থ-লিপ্সা ক্রমে রাজনৈতিক আধিপত্য লাভের আকাঙক্ষায় রূপান্তরিত হয়। এই বেনিয়া শ্রেণীর ইংরেজগণ যখন ছলে-বলে-কৌশলে রাজনৈতিক আধিপত্য লাভে সক্ষম হলো, তখন তাদের কাছ থেকে কল্যাণ-বুদ্ধিসম্পন্ন কোন সুশাসন প্রত্যাশা করা ছিল অবান্তর মাত্র। ব্যবসায়-বুদ্ধিসম্পন্ন ইংরেজগণ রাজনৈতিক হাতিয়ারকে অর্থনৈতিক শোষণের যন্ত্রে পরিণত করেছিল। সামাজিক উন্নয়ন ও শিক্ষা-সাংস্কৃতিক বিকাশের কোন কর্মসূচীই তাদের ছিল না। এরূপ পরিবেশে জনগণের চিন্তা বৃত্তি কোন বিকাশ ঘটা সম্ভব ছিল না। পরবর্তীকালে অবশ্য তারা উপলব্ধি করেছিল যে, রাজনৈতিক আধিপত্য স্থায়ী করতে হলে এ দেশের মানুষকে মানসিক দিক দিয়ে গোলামে পরিণত করা প্রয়োজন। ফলে, তারা এ দেশে বিশেষ এক জাতীয় ইউরোপীয় সভ্যতা-সংস্কৃতি আমদানি করার প্রয়াস পেল। এদেশের মানুষকে তাদের দেশের মানুষের মত জ্ঞানী, গুণী ও বিদ্বান করে তোলার উদ্দেশ্যে এ জাতীয় সভ্যতা-সংস্কৃতি আমদানি করা হয়নি; রবং দেশীয় জনগণের মধ্যে থেকে এক শ্রেণীর মানুষকে ট্রেনিং দিয়ে তাদেরকে এজেন্টে পরিণত করে তাদের মাধ্যমে এদেশে বেনিয়া শাসন শোষণের হাতিয়ারকে মযবুত করা এবং রাজনৈতিক গোলামির সাথে সাথে চিন্তা ও মননের ক্ষেত্রে হীনম্মন্যতা ও দাসত্ব সৃষ্টিই তাদের প্রধান লক্ষ্য ছিল। এই নব শিক্ষা সভ্যতা আমদানির ফলে একশ্রেণীর মানুষের মধ্যে যথেষ্ট উৎসাহ-উদ্দীপনা লক্ষ্য করা গেলেও দেশীয় শিক্ষা-সংস্কৃতির বিকাশ চরমভাবে বাধাগ্রস্ত হলো। পরবর্তীকালে অবশ্য এই আঘাতের বেদনা কাটিয়ে ইংরেজদের শিক্ষা-সভ্যতার প্রত্যক্ষ প্রভাবে আমাদের সাহিত্য-সাংস্কৃতিক বিকাশের প্রয়াস চলেছে, কিন্তু তাতে সময় লেগেছে কমপক্ষে এক শতাব্দীকাল। ইউরোপীয় শিক্ষা-সভ্যতা আমদানির সাথে সাথে রাজা ভাষণ এবং শিক্ষার মাধ্যম হিসেবেও ইংরেজী ভাষার প্রচলন করা হয়। এতদিন পর্যন্ত রাজ-ভাষা ছিল ফারসী এবং সাহিত্যের ভাষা ছিল বাংলা বা ফারসী প্রভাবিত বাংলা। হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সকলেই এই ভাষায় সাহিত্য চর্চা করতেন।
তুলনামূলকভাবে মুসলমানদের ব্যবহৃত ভাষায় যদিও আরবী-উর্দু-ফারসীর ব্যাপক প্রাধান্য ছিল; তবু হিন্দুদের ব্যবহৃত ভাষায়ও এর কোন কমতি ছিল না। সে আমলের শ্রেষ্ঠ বাঙালী কবি ভারতচন্দ্রের সুবিখ্যাত “অন্নদা মঙ্গল” কাব্যই তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। সুতরাং রাজ-কার্য ও শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে ভাষার এই পরিবর্তনের দ্বারা নির্বিশেষে বাঙালী সাধারণেরই সমূহ ক্ষতি সাধিত হয়। ফলে সাহিত্য-সৃষ্টির ক্ষেত্রে চরম বন্ধ্যাত্ব দেখা দেয়। অবশ্য হিন্দুসমাজে এই বন্ধ্যাত্ব দীর্ঘস্থায়ী না হলেও মুসলমান সমাজে নানা কারণে এই বন্ধ্যাত্ব দীর্ঘদিন পর্যন্ত বহাল থাকে। ইংরেজদের আগমনের পূর্বে রাজনৈতিক ক্ষমতা ও সামাজিক আধিপত্য ছিল মুসলমানদেরই হাতে। আকস্মিকভাবে এই আধিপত্য হারানোর বেদনা তাদেরকে হতাশ ও বিক্ষুব্ধ করে তুলেছিল। উপরন্তু রাজকার্য ও শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে ইংরেজী ভাষা চালু করার কারণে মুসলমানদের মনে অধিকতর ঘৃণা ও বিদ্বেষের সৃষ্টি হয়। গৌরবময় ঐতিহ্য ও বিগত দিনের দীর্ঘস্থায়ী ক্রুসেডের (মুসলমান ও খ্রিস্টানদের মধ্যে কয়েক শতাব্দী স্থায়ী ধর্মযুদ্ধ) তিক্ততার কারণে ফিরিঙ্গি সভ্যতা, সংস্কৃতি ও ভাষাকে মুসলমানগণ কিছুতেই সহজভাবে গ্রহণ করতে পারেনি। এদিক থেকে হিন্দুদের সাথে তাদের পার্থক্য ছিল সুস্পষ্ট। ইংরেজদের আগমনের ফলে হিন্দুদেরকে কিছু হারাতে হয়নি। শাসন-ক্ষমতা মুসলমানদের হাত থেকে ইংরেজদের হাতে চলে যাওয়ায় প্রত্যক্ষভাবে তাদের কোন ক্ষতি হয়নি। বরং মুসলমানদের তুলনায় তারা সহজে ইংরেজদের আধিপত্য স্বীকার করে নেয়ায় অল্প সময়ের মধ্যেই তারা ইংরেজদের আস্থা অর্জনে সক্ষম হয় এবং ব্যবসা-বাণিজ্য ও সামাজিক ক্ষেত্রে দ্রুত প্রতিষ্ঠা লাভে সমর্থ হয়। রাজশক্তির আস্থা অর্জনের সঙ্গে সঙ্গে চাকরি-বাকরি ও শিক্ষা-দীক্ষার ক্ষেত্রেও তারা অনেক অগ্রসর হয়। অন্যদিকে মুসলমানগণ মানসিক দিক দিয়ে সহজে ইংরেজদের আধিপত্য স্বীকার করে নিতে না পারায় এবং দীর্ঘকাল পর্যন্ত হারানো রাজশক্তি ফিরে পাবার আকাঙক্ষা মনে মনে পোষণ করায় তারা কেবল সামাজিক সুযোগ-সুবিধা ও আধিপত্য হারিয়েছে তাই নয়; শিক্ষা-দীক্ষার ক্ষেত্রেও অনেক পেছনে পড়ে গেছে। মূলত ১৮৫৭ খ্রীস্টাব্দে সিপাহী বিদ্রোহের পূর্ব পর্যন্ত এই অবস্থার কোন পরিবর্তন হয়নি। সিপাহী বিদ্রোহ ব্যর্থতা বরণ করায় মুসলমানদের রাজনৈতিক আধিপত্য লাভের আকাঙক্ষা সাময়িকভাবে নস্যাৎ হয়ে যায় এবং এর পর থেকে গত্যন্তর না দেখে তারা কেউ কেউ ইংরেজদের প্রবর্তিত শিক্ষা-দীক্ষা অনুসরণে উদ্যোগী হয়। এ সময় কতিপয় মুসলিম মনীষী ও সমাজসেবী ব্যক্তিও এগিয়ে আসেন। মুসলমান সমাজের অধঃপতন ও দুরবস্থা অবলোকন করে তাঁরা অতিশয় ব্যথিত হন এবং শিক্ষা-দীক্ষার ক্ষেত্রে মুসলমানগণ যাতে দ্রুত এগিয়ে আসে, সে ব্যাপারে তারা সর্বতোভাবে প্রচেষ্টা চালান। কিন্তু ইতিমধ্যে পুরো এক শতাব্দীকাল অতিবাহিত হয়েছে এবং ততদিনে শিক্ষাগত, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক প্রভৃতি সকল দিক দিয়ে মুসলমানদের অবস্থা শোচনীয় হয়ে পড়েছে। কিন্তু তবু এই সামাজিক শোচনীয় অবস্থা ও সিপাহী বিদ্রোহ ব্যর্থতা বরণের পটভূমিতেই মুসলমানগণ সর্বপ্রথম ব্যাপক ও কিছুটা সচেতনভাবে ইংরেজী শিক্ষা-দীক্ষার প্রতি আগ্রহ প্রকাশ করে। কিন্তু ইংরেজী শিক্ষা-দীক্ষার প্রতি এসময় মুসলমানদের আগ্রহ দেখা দিলেও বাস্তব ক্ষেত্রে তারা কতিপয় অসুবিধারও সম্মুখীন হয়। প্রথমত ইংরেজদের প্রবর্তিত শিক্ষা ব্যবস্থা মুসলমানদের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক জীবনধারা বিকাশের উপযোগী ছিল না। দ্বিতীয়ত ইংরেজী শিক্ষা-সভ্যতার নামে তখন যে শোষণ ও সামাজিক অনাচার আমদানি করা হয়েছিল, তা গ্রহণে মুসলমানগণ স্বাভাবিকভাবেই দ্বিধাগ্রস্ত ছিল। এ কারণেই পরবর্তীকালে মুসলমানদের জন্য মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থার নামে আর এক জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার প্রবর্তন করা হয়েছে। কিন্তু এটা সমস্যার কোন সঠিক সমাধান ছিল না। মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থায় সীমিত অর্থে ধর্মীয় শিক্ষার ব্যবস্থা থাকলেও উক্ত শিক্ষা ব্যবস্থায় উচ্চতম ডিগ্রী হাসিলের পরেও যথাযথ সামাজিক স্বীকৃতি লাভ করা সম্ভব ছিল না; অর্থাৎ চাকরি-বাকরি লাভ বা সামাজিক কোন দায়িত্ব পালনের বা কোনরূপ উৎপাদনমুখী ভূমিকা পালনের যোগ্যতা সৃষ্টি হতো না। মসজিদ-মক্তবে বিনা বেতনের মুনশী মোল্লাগিরি বা অনুগ্রহের দান হিসেবে সামান্য কিছু দাক্ষিণ্য লাভই তাঁদের বিধিলিপিতে পরিণত হয়েছিল। তাই চাকরি-বাকরি লাভের উদ্দেশ্যে মুসলমানদের মধ্যে অনেকে ইংরেজী শিক্ষার দিকে ঝুঁকে পড়তে বাধ্য হয়। এভাবে মুসলমান সমাজ মূলত ত্রিধা বিভক্ত হয়ে পড়ে। একদিকে ইংরেজী শিক্ষিত আধুনিক সমাজ, আরেকদিকে আরবী-ফারসী শিক্ষিত ধর্মীয় আলেমশ্রেণী এবং এ দু’য়ের মাঝখানে সংখ্যাগরিষ্ঠ অশিক্ষিত সমাজ। এরূপ ত্রিধা বিভক্ত সমাজে ভারসাম্যমূলক সুষ্ঠু সাংস্কৃতিক চেতনার বিকাশ অতিশয় দুরূহ। বাংলাদেশে মুসলমানদের জন্য এটা এক অপ্রত্যাশিত ও চরম বিপর্যয়কর অবস্থা। এ প্রসঙ্গে ইতিহাসের পটভূমিতে মুসলমানদের অবস্থা সম্পর্কে কিঞ্চিৎ আলোকপাত করা যেতে পারে।
বাঙালী মুসলমানদের মধ্যে অধিকাংশই নিম্নবর্ণ হিন্দু ও নির্যাতিত বৌদ্ধদের থেকে ধর্মান্তরিত হয়। বিদেশাগত মুসলমানদের মধ্যে দুটো শ্রেণী। প্রথমত ধর্ম-প্রচারক। তাঁরা খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতক থেকে বিভিন্ন সময়ে বাংলাদেশে আগমন করেন। বাংলাদেশের অসংখ্য মাজার ও বিভিন্ন প্রাচীন মসজিদ আজো তাঁদের পবিত্র স্মৃতি বহন করে চলেছে। দ্বিতীয় শ্রেণীর বিদেশাগত মুসলমান হলেন শাসক সম্প্রদায়। ত্রয়োদশ শতকের গোড়ার দিকে ইখতিয়ার উদ্দিন মুহাম্মদ বখতিয়ার খিলজির নেতৃত্বে তাঁরা এদেশে বিজয়াভিযান পরিচালনা করে গৌড়ের সেন রাজাদের বিতাড়িত করে মুসলিম রাজত্ব কায়েম করেন। এঁরা ছিলেন মূলত তুরস্কের অধিবাসী। এই দুই শ্রেণীর বিদেশাগত মুসলমানদের মধ্যে দৃষ্টিভঙ্গি ও উদ্দেশ্যগত পার্থক্য ছিল। ধর্মপ্রচারক মুসলমানদের উদ্দেশ্য ছিল ইসলামের মাহাত্ম্য প্রচার এবং তাওহীদের মন্ত্রে সকলকে দীক্ষিত করা। ধর্ম-প্রচারক ও তাঁদের অনুসারী শিষ্যদের চরিত্র ছিল ত্যাগ-তিতিক্ষায় পরিপূর্ণ পূত-পবিত্র ও অনুসরণযোগ্য। ইসলামের সর্বজনীন মানবতাবাদ, সাম্য, মৈত্রী ও ভ্রাতৃত্ব শতধাবিভক্ত পৌত্তলিক বাঙালী সমাজে এক বিশ্বয়কর বিপ্লব সৃষ্টি করে। পুণ্যাত্মা ধর্ম-প্রচারকদের উদ্দীপনাময় চরিত্র-মাহাত্ম্যও ছিল এক অবিস্মরণীয় মহৎ আকর্ষণ। ফলে এদেশে মুসলমানদের শাসন কায়েম হওয়ার পূর্ব থেকেই বহু লোক ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়। ত্রয়োদশ শতকের গোড়ার দিকে মুসলমান রাজত্ব কায়েম হওয়ার পরে ইসলাম ধর্ম এক অপ্রতিহত শক্তিতে পরিণত হয়। রাজশক্তির যদিও এ ব্যাপারে প্রত্যক্ষ কোন ভূমিকা ছিলা না, কিন্তু ইসলাম শাসক শ্রেণীর ধর্ম হওয়ার কারণে ইসলাম প্রচারে এটা একটা স্বাভাবিক অনুকূল প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছে। তাই দেখা গেল, মাত্র অল্প কিছুদিনের মধ্যেই বাংলাদেশের প্রায় অর্ধেক বা তারও অধিক সংখ্যক অধিবাসী ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়েছে। বাংলাদেশের ইতিহাসে বহিরাগত কোন ধর্ম বা আদর্শ এত অত্যল্প কালের মধ্যে এত অধিক সংখ্যক মানুষের নিকট গ্রহণীয় হয়েছে বলে জানা যায় না। বাংলাদেশের মাটিতে ইসলামের এই অভূতপূর্ব সাফল্যের কারণ প্রধানত দু’টি। প্রথমটি হলো, ইসলামের বিশ্বজনীন মানবিক আবেদন; সাম্য, ভ্রাতৃত্ব ও ইনসাফপূর্ণ উদার আদর্শবাদ এবং দ্বিতীয়টি হলো, তৎকালীন বিপর্যস্ত অবস্থা। বাংলার মাটি থেকে জৈন ধর্মের অস্তিত্ব তখন স্বাভাবিকভাবেই বিলুপ্ত হয়ে গেছে। বৌদ্ধ ধর্মের মধ্যে যেটুকু মানবতাবাদের অস্তিত্ব ছিল, তা নিয়ে বাংলার মাটিতে হয়তো তা মোটামুটি স্থায়ী আসন প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হতো; কিন্তু অসহিষ্ণু ব্রাহ্মণ্যবাদের রোষানলে বাংলার সমতলভূমি থেকে তা অনেক আগেই বিদায় নিয়েছে। পাহাড়ী প্রত্যন্ত ও দুর্ভেদ্য বনাঞ্চলে এবং প্রচ্ছন্নভাবে লোকজ ধর্মের মধ্যে যদিও তার অস্তিত্ব কিছুটা বজায় ছিল, কিন্তু বাঙালী সমাজে তার প্রকাশ্য সদর্প আবির্ভাব ছিল একান্ত অসম্ভব। বাঙালী সমাজে তখন একমাত্র হিন্দুধর্মেরই প্রচন্ড দাপট। কিন্তু সে হিন্দু ধর্ম বেদ-উপনিষদের হিন্দুধর্ম নয়; হিন্দুধর্মের নামে ব্রাহ্মণ্যবাদের সংকীর্ণ, বিভেদাত্মক, অনুদার আদর্শই প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল। তার ফলে হিন্দুসমাজ শতধা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল এবং উচ-নিচের ব্যবধান এত প্রকট ছিল যে, সাম্য ও মানবতার আদর্শ সেখানে অবাস্তব কল্পনার বিষয়ে পরিণত হয়ে পড়েছিল। তেত্রিশ কোটি দেবতার উপস্থিতি, চুতমার্গ, অবাঞ্ছিত অগণিত অমানবিক সংস্কার, ধর্মীয় নেতা ও সামাজপতিদের হৃদয়হীন শোষণ এবং নৈতিকতাহীন সমাজগ্রন্থি তখন নিতান্তই শিথিল হয়ে পড়েছিল। ইসলামের আগমনের সাথে সাথে তাই এই সমাজের ভিত সহজেই ধসে পড়ে। ইসলামের প্রগতিশীল মানবিক আদর্শ তখন বাংলার সমাজ-ব্যবস্থায় এক অভূতপূর্ব বিপ্লব সৃষ্টি করে। মুসলিম রাজশক্তি তখন ইসলাম প্রচারে প্রত্যক্ষ সহযোগিতা প্রদান করলে এবং শ্রীচৈতন্য প্রমুখ হিন্দু সমাজপতিগণ হিন্দুধর্মের সংস্কার সাধন ও পুনরুজ্জীবনের প্রয়াসে গভীরভাবে আত্মনিয়োগ না করলে হয়ত সমগ্র বাঙালী সমাজই তখন ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়ে পড়তো।
কিন্তু ইসলামের এই অপ্রতিরোধ্য প্রসারের যুগেও সর্বাধিক অনুধাবনযোগ্য বিষয় হলো এই যে, মুসলিম রাজশক্তি কিংবা মুসলিম ধর্মপ্রচারকগণের মধ্যে কখনো অসহিষ্ণুতার পরিচয় পাওয়া যায়নি। শাসক শ্রেণী প্রতিরোধহীন রাজকীয় আধিপত্য লাভেই সন্তুষ্ট ছিলেন আর স্বীয় ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব ও মাহাত্ম্যই ছিল ধর্ম-প্রচারকগণের প্রধান হাতিয়ার। অবশ্য বিরুদ্ধ-শক্তির মোকাবিলায় কখনো কখনো সংঘর্ষের সৃষ্টি হয়নি এমন নয়; কিন্তু ইতিহাসের সামগ্রিক পটভূমিতে তা ব্যাপক গুরুত্বের অধিকারী নয়। বাংলাদেশে ব্রাহ্মণ্য রাজশক্তির আধিপত্য প্রতিষ্ঠার সাথে তাই এর পার্থক্য অতি সুস্পষ্ট। এক ব্যাপক সামাজিক প্রলয় ও নৃশংস ধ্বংসযজ্ঞের মধ্য দিয়ে বৌদ্ধ-যুগের অবসান ঘটিয়ে ব্রাহ্মণ্য সেন রাজাদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা হয়। কিন্তু মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠা ও ইসলামের প্রসারের সাথে সাথে বাঙালী সমাজে আদর্শ ও মূল্যবোধগত তাৎপর্যময় ব্যাপক পুনর্বিন্যাস সংঘটিত হলেও তা সামাজিক অগ্রগতির পথে কোনরূপ প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করেনি; নতুন ও প্রাণময় গতিসঞ্চার করেছে মাত্র। তাই দেখা যায়, মুসলিম শাসনামলে বাংলা ভাষার কদরদানি বেড়েছে; বাংলা-সাহিত্যের চরম উৎকর্ষ সাধিত হয়েছে। ইসলামের উদারনৈতিক আদর্শ এবং মুসলিম শাসক-সম্প্রদায়ের ঔদার্য ও পৃষ্ঠপোষকতায় ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে হিন্দু-মুসলমান সকলেই সাহিত্য চর্চার যথাযোগ্য অধিকার লাভ করেছে। অবশ্য সাংস্কৃতিক চেতনা ও ঐতিহ্যগত স্বাতন্ত্র্যের জন্যে উভয়ের সাহিত্য স্ব স্ব বৈশিষ্ট্যে সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে।
ইংরেজ আগমনের সাথে সাথে সাহিত্য-সংস্কৃতির চর্চায় বিঘ্ন সৃষ্টি হয়। চরম হতাশাগ্রস্ত সামাজিক পরিবর্তনের পটভূমিতে শিল্প-সাহিত্যের বিকাশ সম্ভব ছিল না। ফলে পলাশী যুদ্ধের পর প্রায় এক শতাব্দী কাল পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে কোন উল্লেখযোগ্য অবদান চোখে পড়ে না। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে এটাকে ‘তমসা – যুগ’ বলে চিহ্নিত করা চলে। উক্ত এক শতাব্দী কালের মধ্যে একমাত্র ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ছাড়া অন্য কোন উল্লেখযোগ্য কবিরই সন্ধান পাওয়া যায় না বলা চলে। এ সময়ে সামাজিক পরিবেশ ও মানুষের মানস-রাজ্য কতখানি ভাবলেশশূন্য ফ্যাকাসে হয়ে পড়েছিল কবি ঈশ্বর গুপ্তের কবিতায়ও তার প্রমাণ মেলে। বস্তুত বৈষ্ণব-কাব্যের মত গভীর ভাবসম্পন্ন কাব্য ও আলাওলের ‘পদ্মাবতী’র মত নিখুঁত শিল্প সৃষ্টির মত ধৈর্য ও সাধনা এ যুগের কবি-সাহিত্যিকদের মধ্যে ছিল না বললেই চলে। তবে এ সময় অধুনা প্রায় লুপ্ত এক শ্রেণীর সাহিত্য সৃষ্টি হচ্ছিল বটে, যেগুলোকে কবিয়ালদের গান, কীর্তন, গ্রাম্য ছড়া, আউল-বাউল এবং হেঁয়ালি জাতীয় বিভিন্ন নিম্নস্তরের সাহিত্য বলে আখ্যায়িত করা চলে। এ শ্রেণীর সাহিত্যের মধ্যে এক ধরনের মানসিক দৈন্য, হতাশা- নৈরাশ্য, বৈরাগ্য ও হৃদয়বৃত্তির রুচিগর্হিত উৎকট প্রকাশ ঘটেছে মাত্র।
ঊনবিংশ শতকের শুরুতেই সামাজিক অস্থিরতা ও মানসিক দৈন্যভাব বিদূরিত হওয়ার লক্ষণ সূচিত হয়, কিন্তু সে লক্ষণ কেবলমাত্র বাঙালী হিন্দুসমাজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। কলকাতায় ১৮০০ খ্রীস্টাব্দে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ ও ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে হিন্দু কলেজ স্থাপিত হওয়ার ফলে বাঙালী হিন্দু সমাজে নবজাগরণের সূচনা হয়। এ সময় পন্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রাজা রামমোহন রায়, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্যারীচাঁদ মিত্র প্রমুখ সমাজ-সংস্কারক ও বিদ্বজ্জন ব্যক্তির আবির্ভাবের ফলেও হিন্দুসমাজে নবজাগরণের এক অভূতপূর্ব সাড়া পড়ে যায়। কিন্তু মুসলমান সমাজে তখনো এমন কোন পরিবর্তনের সূচনা হয়নি। বরং ইংরেজদের বিরূপতা এবং রাজশক্তির অসহযোগিতার ফলে বাঙালী মুসলমান সমাজ তখনো চরম হতাশা ও দৈন্যদশার মধ্যে জীবন-যাপন করছিল। সামাজিক কর্মযোগ ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনা থেকে তাদের জীবন ছিল সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন। এ সময় তাদের মধ্যে বৈরাগ্যভাব ও আউল বাউলের জন্ম তাই এ দিক থেকে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। রাষ্ট্রীয় তথা বাস্তব দিক থেকে সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত ও নিরাসক্ত হয়ে পড়ার ফলে আধ্যাত্মিক ও বৈরাগ্যভাবই তাদের মধ্যে প্রাধান্য লাভ করে। ১৮৫৭ খ্রীস্টাব্দে ‘সিপাহী বিদ্রোহে’র পরে অর্থাৎ উনবিংশ শতকের শেষার্ধে চরম বাস্তবতার নিদারুণ আঘাতে তাদের এই বৈরাগ্য ও নিরাসক্তভাবের অবসান ঘটতে থাকে। এ সময় মুসলমান সমাজে কিছুটা স্থিতিশীলতার ভাব লক্ষ্য করা যায় এবং তার ফলে কিছু কিছু সাহিত্য সৃষ্টির সম্ভাবনাও পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু এ সময় রচিত সাহিত্যে ভাবাবেগের আধিক্য এবং সব হারানোর এক অস্বস্তিকর মনোবেদনার প্রকাশ চোখে পড়ে।
ঊনবিংশ শতাব্দীকে মুসলমানদের জন্য আত্মগ্লানি অপনোদন ও আত্ম-চেতনার বিকাশ সাধনের প্রচেষ্টার যুগ বলে অভিহিত করা যেতে পারে। দীর্ঘ-সুপ্তির অবসান ঘটিয়ে নব-অভ্যুত্থানের প্রথম লগ্নে তাদের মধ্যে এক বৈশিষ্ট্যপূর্ণ স্বাতন্ত্র্য পরিলক্ষিত হয়। এই স্বাতন্ত্র্য যেমন ভাষার ক্ষেত্রে, তেমনি ভাব, উপজীব্য, ঐতিহ্য-চেতনা ও জীবন-অনুভবের ক্ষেত্রেও।
ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে মুসলমানগণ যখন সাহিত্য চর্চা শুরু করেন, তখন বাংলাদেশের সামাজিক পরিবেশটাও বিশেষভাবে বিচার্য। উনবিংশ শতকের শুরুতেই এক শ্রেণীর হিন্দু সংস্কৃত পন্ডিতদের প্রচেষ্টায় বাংলাভাষার রূপ-পরিবর্তনের প্রয়াস চলে। আরবী-উর্দু-ফারসী ভাষার অসংখ্য শব্দরাজি যা স্বাভাবিকভাবে বাঙালা ভাষার শব্দ-ভান্ডারের সাথে মিশে গিয়েছিল, সেগুলোকে ‘মুসলমানী জবান’ রূপে আখ্যায়িত করে বাংলাভাষা থেকে ঝেটিয়ে তাড়িয়ে তার পরিবর্তে খাঁটি দুর্বোধ্য ও অপ্রচলিত সংস্কৃত শব্দাবলীতে বাংলা ভাষার নব-রূপায়ণের সযত্ন প্রয়াস চলে। দ্বিতীয়ত, ইংরেজী শিক্ষা-সভ্যতার প্রভাবে উনবিংশ শতকের শুরুতেই বাঙালী হিন্দু ধর্ম ও সমাজে নতুন পরিবর্তন ও নবজন্মের আভাস পরিলক্ষিত হয়। ধর্মীয়-চিন্তার ক্ষেত্রে এই বিবর্তন ব্রাহ্মণ সমাজের জন্ম দেয়। অনেকে হিন্দু ধর্ম পরিত্যাগ করে খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ করে এবং সনাতন হিন্দুধর্মের যারা অনুসারী তাদের মধ্যেও ব্যাপকভাবে ধর্মীয় সংস্কার সাধনের প্রয়াস চলে। এই ধর্মীয় সংস্কার সাধনের প্রয়াসে অনেকে হিন্দু ধর্মের মাহাত্ম্য ও প্রাধান্য প্রমাণার্থে অন্য ধর্ম এবং বিশেষতঃ ইসলাম ধর্ম তথা মুসলমানদেরকে হেয় প্রতিপন্ন করার প্রয়াসে লিপ্ত হয়। বঙ্কিম চন্দ্র ছিলেন এই গোষ্ঠীর সর্বাধিক সোচ্চার ও উচ্চকন্ঠ বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্ব। ঊনবিংশ শতকে মুসলমানদের নবজাগরণ ও সাহিত্য চর্চার প্রয়াস প্রধানত এই সনাতনপন্থী হিন্দুদের মুসলিম বিদ্বেষী প্রচারণা ও বিদ্বিষ্ট আঘাতেরই প্রত্যক্ষ প্রতিক্রিয়া-কেন্দ্রিক। তাই এ যুগের সাহিত্যে আবেগ-উত্তেজনা এবং আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যমূলক প্রচারণা যতটা রয়েছে, শিল্প-কলার উচ্চাঙ্গ প্রকাশ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ততটা ঘটেনি। উক্ত একই কারণে সাহিত্য-সাধনার ক্ষেত্রে মুসলমানগণ স্বকীয় ঐতিহ্য ও স্বতন্ত্র জীবন-দৃষ্টি নিয়ে আবির্ভূত হন। স্বভাবতই এ সময় তাদের সাহিত্যে ধর্মভাবের প্রাধান্যও অনিবার্য হয়ে পড়ে।
ঊনবিংশ শতকের মধ্যভাগ থেকে বাংলা সাহিত্যে আধুনিকতার সূত্রপাত। কালগত বিচারে নয়; বরং উপজীব্য ও শিল্পগত বৈশিষ্ট্যের দ্বারাই আধুনিকতার বিচার হয়ে থাকে। মাইকেল মধুসূদন দত্তকেই আধুনিক বাংলা সাহিত্যের প্রথম, উল্লেখযোগ্য ও অবিস্মরণীয় প্রতিভা বলে চিহ্নিত করা হয়। মধুসূদনের শিক্ষা, জীবন-পরিবেশ, অভিজ্ঞতা ও দৃষ্টিভঙ্গি বহুল পরিমাণে আধুনিক বাংলা সাহিত্যকে প্রভাবিত করেছে। মূলত মধুসূদনই বাংলা সাহিত্যে আধুনিকতার প্রবর্তক। ইউরোপীয় শিক্ষা, সভ্যতা ও সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য আত্মস্থ করে মধুসূদন বাংলা সাহিত্যে এক যুগান্তকারী সাহিত্য সৃষ্টির প্রয়াস পান। সাহিত্যের উপজীব্য যেমন পরিবর্তিত হয়, শিল্পগত বৈশিষ্ট্য ও আঙ্গিকের ক্ষেত্রেও তেমনি নতুনত্ব আসে। মধুসূদনের পরে যাঁরা সাহিত্য রচনা করেছেন, প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে তাঁরা অনেকেই তাঁর দ্বারা ব্যাপকভাবে প্রভাবান্বিত হয়েছেন। সমকালীন মুসলিম কবি-সাহিত্যিকগণও এর ব্যতিক্রম নন। কিন্তু মধুসূদনের প্রবর্তিত সাহিত্যের আঙ্গিক ও শিল্পগত বৈশিষ্ট্য তাঁরা যতটা অনুসরণ করেছেন উপজীব্য ও অনুপ্রেরণার দিক থেকে তেমনি তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য স্বাতন্ত্র্য বর্তমান। স্বতন্ত্র ঐতিহ্য-চেতনা, স্বকীয় জীবন-দৃষ্টি ও নব-জাগরণের উদ্দীপনা এ সময় তাঁদের সাহিত্যসৃষ্টির প্রধান উপজীব্য। ‘ইয়ং বেঙ্গল’দের আবির্ভাব এ যুগে যেমন বাঙালী হিন্দুসমাজকে ব্যাপকভাবে আলোড়িত করেছিল, ইসলামী ভাব-দর্শন ও ঐতিহ্য চেতনাও তেমনি মুসলিম সমাজে নব উদ্দীপনা সৃষ্টি করেছিল। এই ভাব-চেতনাকে উপজীব্য করেই এ যুগে মুসলিম কবি-সাহিত্যিকদের সাহিত্য-সাধনার যাত্রা শুরু।
এবারে উনবিংশ শতকের কতিপয় বিশিষ্ট কবি-সাহিত্যিক ও তাঁদের অবদানের বিশিষ্ট স্বরূপ-বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনার প্রয়াস পাবো।
মীর মোশাররফ হোসেন
মীর মোশাররফ হোসেন ঊনবিংশ শতকের একজন বিশিষ্ট সাহিত্যিক। এ শতকের মুসলিম কবি-সাহিত্যিকদের মধ্যে তিনি সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য ও জনপ্রিয়। ১৮৪৮ খ্রীস্টাব্দে কুষ্টিয়া জেলার লোহানীপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন জমিদারের অধীনে চাকরি করেন। গভীর নিষ্ঠা ও অধ্যবসায়ের সাথে তিনি দীর্ঘকাল সাহিত্য সাধনায় আত্মনিবেদিত ছিলেন। বিভিন্ন সূত্র থেকে তাঁর রচিত গ্রন্থের সংখ্যা সর্বমোট পঁয়ত্রিশ খানা বলে জানা যায়। এর মধ্যে ‘বিষাদ সিন্ধু” তাঁর সর্বাধিক পরিচিত ও জনপ্রিয় রচনা। তাঁর অন্যান্য রচনাবলী যদিও উপেক্ষণীয় নয়; তবু বিষাদ সিন্ধুর জনপ্রিয়তা এত অসাধারণ যে, বাংলা সাহিত্যে তিনি একমাত্র বিষাদ সিন্ধুর রচয়িতা হিসাবেই সমধিক খ্যাতিমান; বিশেষত বাঙালী মুসলমানের কাছে তিনি সবিশেষ মর্যাদার অধিকারী।
রচনার আকারের দিক থেকে যেমন, বৈচিত্র্যের দিক থেকেও। মোশাররফ হোসেন ঊনবিংশ শতকের এক অবিস্মরণীয় প্রতিভা। তাঁর সমকালের তেমনি মীর সর্বশ্রেষ্ঠ কবি-প্রতিভা এবং বাংলা সাহিত্যে আধুনিকতার প্রতিভূ মাইকেল মধুসূদন দত্তের অবদান কাব্য –মহাকাব্য, সনেট, নাটক ও প্রহসনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। মধুসূদনের পর বাংলা সাহিত্যের সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য সাহিত্য প্রতিভা বঙ্কিম চন্দ্রের অবদানও কেবলমাত্র উপন্যাস, প্রবন্ধ ও রম্য জাতীয় রচনার মধ্যেই সীমিত। অবশ্য প্রাথমিক যুগে তিনি কবিতা জাতীয় রচনার চেষ্টা করেছিলেন বটে, কিন্তু পরিণত বয়সে সেদিকে তিনি আর কখনো মনোযোগ দেননি। সেদিক থেকে মীর মোশাররফ হোসেনের বৈচিত্র্যপূর্ণ সাহিত্যপ্রয়াস সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।
তাঁর সমগ্র সাহিত্য-কর্মকে মোটামুটি ছয় ভাগে বিভক্ত করা চলে। (১) উপন্যাস জাতীয় রচনা, (২) আত্ম চরিতমূলক রচনা, (৩) নাটক, (৪) প্রহসন, (৫) কবিতা ও গান এবং (৬) প্রবন্ধ। ‘বিষাদ-সিন্ধু’, ‘রত্নাবতী’ ও ‘উদাসীন পথিকের মনের কথা’ প্রথম শ্রেণীভূক্ত রচনা। ‘গাজী মিয়ার বস্তানী’,দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত, ‘বসন্ত কুমারী’ ও ‘জমিদার দর্পণ’ তৃতীয় শ্রেণীভুক্ত, ‘এর উপায় কি’ চতুর্থ শ্রেণীভুক্ত, ‘গোরাই ব্রীজ’, ‘ সঙ্গীত লহরী’, পঞ্চম এবং ‘গো-জীবন’ প্রভৃতি ষষ্ঠ শ্রেণীর অন্তর্গত রচনা। তাঁর কিছু কিছু রচনা অবশ্য উনবিংশ শতকের মধ্যে পড়ে না, তবু উনবিংশ শতকের ভাব-চিন্তা ও সামাজিক পরিবেশই মূলত তাঁর সমগ্র রচনাবলীকে প্রভাবিত করেছে।
মীর মোশাররফ হোসেনের রচনায় মোটামুটি তিনটি ভাব পরিলক্ষিত হয়। (১) ইসলামী ভাব ও মুসলিম-ঐতিহ্য চেতনা, (২) সমাজ-সচেতনতা মানবিক মূল্যবোধ এবং (৩) মানবিক প্রেম ও মরমী সংবেদনশীলতা।
ঊনবিংশ শতকে ইসলামী ভাব ও মুসলিম পুনর্জাগরণের যে উদ্দীপনাপূর্ণ প্রয়াস সমকালীন মুসলিম কবি-সাহিত্যিকদের মধ্যে লক্ষ্য করা গিয়েছিল, মীর সাহেবের রচনায়ও তার সুস্পষ্ট প্রকাশ ঘটেছে। বিষাদ সিন্ধু এর সর্বোৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। বিষাদ সিন্ধুকে যেমন উপন্যাস বলা মুশকিল, তেমনি ইতিহাসও বলা চলে না। কারণ এতে মাঝে মাঝে ঐতিহাসিক সত্যতার অপলাপ ঘটেছে, আবার আধুনিক উপন্যাসের শিল্পগত বাঁধন রীতিও নিষ্ঠার সাথে অনুসরণ করা হয়নি। তবে এটাকে মোটামুটি মধ্যযুগীয় কাহিনীর ঢং-এ ইতিহাস-আশ্রয়ী উপন্যাস জাতীয় রচনা বলে অভিহিত করা চলে। ইসলামের ইতিহাসের এক বিষাদ করুণ ঘটনাকে মানবিক সংবেদনা ও আর্তিতে পূর্ণ করে এমন এক অপরূপ মাহাত্ম্যে ফুটিয়ে তুলেছেন যে, তা এক অবিস্মরণীয় গ্রন্থ হিসেবে পরিগণিত হয়ে এসেছে। বিষাদ সিন্ধুর আর একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হলো এর অপরূপ বাক-বিন্যাস। বাক-বিন্যাসের বিরল নৈপুণ্য, আবেগ ও উচ্ছ্বাসপূর্ণ সুরময় প্রকাশ একে অনেকটা কাব্যের মহিমা দান করেছে। ঘটনা ও কাহিনীর দিক থেকে আবার এটাকে অনেকটা মহাকাব্যধর্মী বলে আখ্যায়িত করা চলে।
বিষাদ-সিন্ধুর মত রত্নাবতী ও উদাসীন পথিকের মনের কথায়ও উপন্যাসের বাঁধা রীতি সংযম ও নিষ্ঠার সাথে অনুসৃত হয়নি। এ জাতীয় রচনায় ঘটনা ও কাহিনীকে যথাযথ আকর্ষণীয় রূপে ফুটিয়ে তোলার দিকে লেখকের যতটা আন্তরিক প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়, উপন্যাসের প্রকৃতি ও শিল্প-রীতির প্রতি লেখকের ততটা সজাগতা লক্ষ্য করা যায় না।
ইংরেজদের রাজ্য-বিস্তারের সাথে সাথে যেমন রাজনৈতিক-সামাজিক পীড়ন ও অর্থনৈতিক শোষণ চলছিল, তেমনি ইউরোপীয় সভ্যতার প্রভাবে উনবিংশ শতকে আমাদের সমাজে এক নব-মানবতাবাদের অভ্যুদয় ঘটে। মূলত মাইকেল মধুসূদনের সাহিত্যেই এই মানবতাবাদের প্রথম সুস্পষ্ট প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। মধুসূদনের ‘মেঘনাদ বধ’ কাব্যে পৌরাণিক দশানন রাক্ষস রাবণের চরিত্রে যেমন মানবিক মূল্যবোধের জীবন্ত প্রকাশ ঘটেছে, তেমনি স্বদেশ-প্রীতির চেতনা প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। তাঁর রচিত সনেটসমূহের মধ্যে স্বদেশপ্রেমের পরিচয় পাওয়া যায়। হিন্দু মুসলিম নির্বিশেষে ঊনবিংশ শতকের সকল কবি-সাহিত্যিকের রচনাতেই এই অনুভূতির প্রকাশ কম-বেশী পরিলক্ষিত হয়। মীর মোশাররফ হোসেনের রচনাতেও মানবিক মূল্যবোধ ও স্বদেশ-প্রীতির আত্যন্তিক প্রকাশ ঘটেছে। এদিক থেকে তিনি ছিলেন প্রকৃত সমাজ-সচেতন সাহিত্যিক। তাঁর বিভিন্ন রচনায় তিনি মানবিক সংবেদনা ও সহানুভূতির সাথে লাঞ্ছিত ও দুর্দশাগ্রস্ত সমাজের করুণ চিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন। মোশাররফ হোসেনের সমকালে একদিকে বিদেশী শাসকের শোষণ, নীলক সাহেবদের হৃদয়হীন পীড়ন এবং অন্যদিকে ঔপনিবেশিক শক্তির দেশীয় প্রতিত্ত্ব নব্য জমিদার ও সামন্ত প্রভুদের অমানুষিক অত্যাচারে সমাজের সাধারণ মানুষের জীবন অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল। মোশাররফ হোসেনের দরদী মন জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে এই নিগৃহীত মানবতার সকরুণ চিত্র অংকন করেছেন। তাঁর রচিত ‘উদাসীন পথিকের মনের কথা’ উপন্যাস এবং ‘জমিদার দর্পণ’ নাটকে যথাক্রমে ইংরেজ নীল – কুঠিয়ালদের নিপীড়ন ও দেশীয় সামন্ত-প্রভুদের অত্যাচারের মর্মন্তুদ কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। ‘জমিদার-দর্পণ’ নাটকে যদিও দীনবন্ধু মিত্রের রচিত ‘নীলদর্পণ’ নাটকের কিছুটা প্রভাব লক্ষ্য করা যায় বলে অনেকের ধারণা, তবু মানবিক সংবেদনার স্বতস্ফূর্ত প্রকাশে এবং ঊনবিংশ শতকের ঐতিহাসিক ও সামাজিক অবস্থার প্রেক্ষিতে এ দুটি গ্রন্থের মর্যাদা অপরিসীম। সমাজের বিভিন্ন দুর্বলতা ও অন্যায়-অবিচারের কথা রস-সৃষ্টির মাধ্যমে নিখুঁতভাবে ফুটিয়ে তোলার ক্ষেত্রে মোশাররফ হোসেন বিশেষ কুশলতার পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর রচিত প্রহসন ‘এর উপায় কি’ এবং আত্ম-কথা জাতীয় রচনা ‘গাজী মিয়ার বস্তানী’ এ ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য। রস-সৃষ্টি হিসাবে ‘গাজী মিঞার বস্তানী’ অত্যন্ত সার্থক সৃষ্টি। এতে নাই এমন রস পৃথিবীতে দুর্লভ। রস-সৃষ্টির মাধ্যমে এতে সামাজিক অনাচার ও ইংরেজদের নানাবিধ দৌরাত্ম্যের পরিচয় পেশ করা হয়েছে। ফলে চার-শ পৃষ্ঠার এ বিরাট গ্রন্থখানি বাজেয়াপ্ত করা হয়। সাহিত্য-সৃষ্টি হিসেবে অনেকে গ্রন্থখানিকে মীর মোশাররফ হোসেনের সর্বাধিক সার্থক ও অনন্য গ্রন্থ হিসেবে বিবেচনা করে থাকেন। তাঁর এ-জাতীয় রচনাবলীতে তীক্ষ্ণ সমাজ-সচেতনতা মানবতাবোধের গভীর প্রকাশ পরিলক্ষিত হয়।
মীর মোশাররফ হোসেনের ‘গোরাই ব্রীজ’, ‘সঙ্গীত লহরী’, ‘বেহুলা’ প্রভৃতি কাব্য, সঙ্গীত ও গীতি-নাটকের মধ্যে একাধারে তাঁর প্রতিভার বহুমুখিতা এবং প্রেম ও মরমী ভাবের প্রকাশ ঘটেছে।
মোটামুটিভাবে এ কথা বলা যেতে পারে যে, মীর মোশাররফ হোসেন উনবিংশ শতকের এক স্মরণীয় প্রতিভা। তাঁর বিচিত্র অবদান বাংলা সাহিত্যের এক মূল্যবান সম্পদ। ভাষা ও শিল্প-সৌকুমার্যের ক্ষেত্রে তিনি যে উন্নত মানের পরিচয় দিয়েছেন, পরবর্তীকালের কবি-সাহিত্যিকদের তা বহুলভাবে প্রভাবিত করেছে। এদিকে থেকে তাঁর কৃতিত্বকে কেবলমাত্র বঙ্কিম চন্দ্রের সাথেই তুলনা করা যেতে পারে।
_________________
বাংলা সাহিত্যের ধারা
রোয়াক ডেস্ক