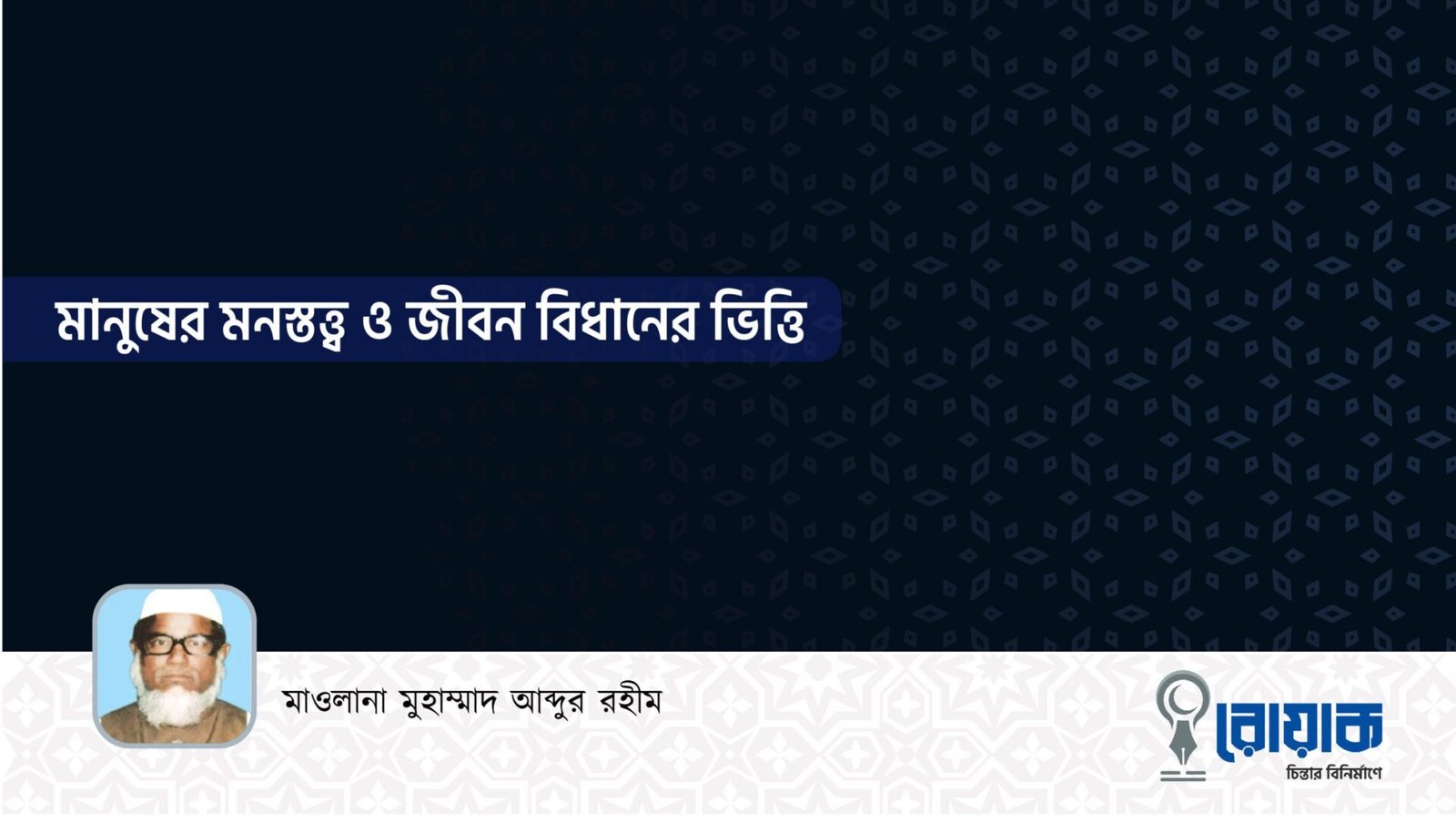মনস্তত্ত্ব ও মতাদর্শের সম্পর্ক:
বিজ্ঞানে আমরা যে প্রাকৃতিক বাহ্য প্রকাশেরই (natural phenomenon ) অধ্যয়ন করি, তা তার প্রকৃত বিশেষত্বসমূহ এবং আমাদের মনস্তাত্ত্বিক অবস্থা সমূহের সমষ্টি। এই পর্যবেক্ষণ ও অধ্যয়নের উপরই আমাদের পরীক্ষণ নিরীক্ষণ ও অভিজ্ঞতা অর্জন ভিত্তিশীল। এ সব পরীক্ষণ-নিরীক্ষণ ও অভিজ্ঞতা অর্জনের মাধ্যমেই আমরা মতাদর্শ গ্রহণ ও রচনা করি। তার অর্থ এই যে, বিশ্বলোক অধ্যয়ন করে আমরা যে মতবাদ – মতাদর্শ রচনা করি, আসলে তা আমাদের মনস্তত্ত্ব ও বিশ্বলোকের বিভিন্ন অংশের পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতি ক্রিয়ার ফল। অর্থাৎ বিশ্বলোকের বিভিন্ন অংশ আমাদের পঞ্চেন্দ্রিয়ের সাহায্যে আমাদের মনস্তত্ত্বের উপর একটা প্রভাব বিস্তার করে একটা ক্রিয়া করে। আর আমাদের মনস্তত্ত্বের দিক থেকেও তার একটা প্রতিক্রিয়া ঘটে। এই ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়ার সংমিশ্রণে একটা ফল দেখা দেয়। আমরা তাকে বলি আমাদের গৃহীত প্রতিক্রিয়া। এই প্রতিক্রিয়ার ভিত্তিতেই অবলম্বিত হয় আমাদের বাস্তব আচরণ। এই কারণে বলা যায়, আমাদের গৃহীত প্রতিক্রিয়ার পরিবর্তনে আমাদের বাস্তব আচরণেও পরিবর্তন আসে।
এ প্রেক্ষিতে বলা যায়, একই ধরনের বিভিন্ন বাহ্য প্রকাশ (phenomenon) বিভিন্ন সময় ও বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের প্রতিক্রিয়ার উদ্ভব করে, তখন তাতে যে কেন্দ্রীয় ও সম্মিলিত প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়, তা-ই এই ধরনের সমস্ত প্রাকৃতিক বাহ্য প্রকাশ সম্পর্কে একটা পরিপক্ক প্রতিক্রিয়া হয়ে থাকে–সে বাহ্য প্রকাশ যা এ পর্যন্ত পর্যবেক্ষণে এসেছে কিংবা ভবিষ্যতে কখনও পর্যবেক্ষণে আসবে, সব সম্পর্কেই এই পরিপন্ধ প্রতিক্রিয়ার ভিত্তিতে আমরা এ ধরনের সংঘটিতব্য প্রাকৃতিক বাহ্য প্রকাশ সম্পর্কে তার সংঘটিত হওয়ার পূর্বেই লক্ষণ ও নিদর্শনসমূহ নির্দেশ করতে পারি, সংঘটিত হওয়ার পর তার ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণও করতে পারি। এই পরিপক্ক প্রতিক্রিয়াই মূলত আমাদের বৈজ্ঞানিক মতাদর্শ। ইতিপূর্বে এ পর্যায়ের বহু কয়টি দৃষ্টান্ত পেশ করা হয়েছে।
আমাদের প্রকৃতি নিহিত ও স্বজ্ঞাজনিত অবস্থাসমূহই আমাদের মনস্তত্ত্ব গঠনের গুরুত্বপূর্ণ যৌগিক অংশ। আমাদের ঝোঁক-প্রবণতা, আমাদের মনের কামনা-বাসনা-লালসা, অনুসন্ধানপ্রিয়তা ও আত্মনিবেদন দাসত্ব গ্রহণ ভাব ধারাও এই পর্যায়েরই মনস্তত্ত্বের যৌগিক অংশ। এ পর্যায়ে আমাদের আকীদা-বিশ্বাস-ই হচ্ছে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তার ভূমিকা মনস্তত্ত্ব গঠনে সমধিক তীব্র ও প্রচন্ড প্রভাবের অধিকারী। কেননা মনস্তত্ত্বের যতগুলি যৌগিক অংশ রয়েছে, তার সবকিছুর উপর আকীদা-বিশ্বাসের আধিপত্য ও প্রাধান্য অবশ্য স্বীকৃতিব্য। অন্যান্য সব অংশ-ই তার অধীনে থেকে (নিজের কাজ করে)। এমন কি, আমাদের স্বভাব-নিহিত ও স্বভাবজনিত অবস্থাসমূহও তারই প্রভাবাধীন হয়ে থাকে। তার বিরুদ্ধে কখনই মাথা তুলে দাঁড়াতে পারে না। আমাদের আকীদা-বিশ্বাসে যখন কোন পরিবর্তন সূচিত হয়, তখন তার প্রভাবে সমগ্ৰ মনস্তত্ত্বও পরিবর্তিত হয়ে যায়। আর আমাদের মনস্তত্ত্বে পরিবর্তন সূচিত হলে বিশ্বলোকের অংশসমূহ ও প্রাকৃতিক বাহ্য প্রকাশ সম্পর্কে আমাদের যে প্রতিক্রিয়া ও মতাদর্শ বা দৃষ্টিভঙ্গি, তা সবই আমূল পরিবর্তিত হয়ে যাবে।
এখানে একটি প্রশ্ন মাথাচাড়া দিয়ে উঠে। কোন ধারণা বা কোন জিনিস কিংবা কোন ব্যক্তিসত্তার প্রতি আমাদের মনে বিশ্বাস জন্মে কিভাবে ? কোন সব কারণে এই আকীদা দৃঢ়মূল কিংবা দুর্বল হয় ? সে কারণগুলি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা দরকার। কেননা সেগুলো যথাযথভাবে নির্ধারিত করা হলেই আমরা নিজেদের আকীদা-বিশ্বাসকে সঠিকরূপে গড়ে তুলতে পারি। যেহেতু আমাদের আকীদা যথার্থ না হলে উপরের ব্যাখ্যা থেকে প্রকট হয়ে উঠেছে যে, আমাদের কোন কাজই যথার্থ হবে না। বিজ্ঞানে আমরা যতই উন্নতি ও উৎকর্ষ লাভ করি না কেন, আমাদের আকীদা বিশ্বাস যথার্থ না হলে একটি সুষ্ঠু আদর্শ ও সৎ সমাজ গঠনের স্বপ্ন আমাদের দ্বারা কখনই সফল ও বাস্তবায়িত হতে পারে না।
সন্ধান প্রবণতা:
আমাদের মনস্তত্ত্বে সন্ধান প্রবণতার তীব্র ভাবধারা বর্তমান। আসলে তা একটা অনিশ্চয়তা ও অস্থিরতামূলক অবস্থা। আর সে অবস্থার উত্তর হয় বিশ্বলোক ও বিশ্বলোকের অংশসমূহের প্রকৃত অবস্থা ও রূপ সঠিক ও নির্ভুল ভাবে না জানার কারণে। মানুষের মনস্তত্ত্ব নিহিত সন্ধান প্রবণতাই মানুষকে জ্ঞানার্জনে উদ্বুদ্ধ করে। জানার্জন পথে অগ্রগতি লাভ হয়, জ্ঞানের পিপাসা ততই তীব্র হয়ে উঠে, অনুসন্ধান প্রবণতা বৃদ্ধি পেয়ে যায়। আর তা থামে না- তৃপ্ত হয় না যতক্ষণ না বিশ্বলোকের অধিবিদ্যা সংক্রান্ত জটিল প্রশ্নাবলীর কোন চূড়ান্ত, অকাট্য ও প্রত্যয়পূর্ণ জবাব লাভ করা যাবে। বস্তুত প্রকৃতি-ঊর্ধ্ব অধিবিদ্যা সংক্রান্ত (metaphysical) সমস্যা ও প্রশ্নাবলী সম্পর্কেই মানব মনে সব সময়ই অসংখ্য জিজ্ঞাসা প্রবল দেখা দেয়। এ বিষয়ে কোন চূড়ান্ত ও অকাট্য স্পষ্ট প্রত্যয়মূলক সমাধান না পেলে বিভিন্ন অনুসন্ধানী নিজ নিজ ধারণা অনুমানের ভিত্তিতে বিভিন্ন সিদ্ধান্তে উপনীত হয়ে থাকে এবং এ ভাবেই অনুসন্ধান প্রবণতা চরিতার্থ করতে চেষ্টা করে। কিন্তু অমূলক ধারণা অনুমানের ভিত্তিতে যে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়, তা কখনও নির্ভুল হতে পারে না। তা ছাড়া সে সিদ্ধান্ত বিভিন্ন লোকের বিভিন্ন রকম হতেও বাধ্য। এই কারণে অনুসন্ধান প্রবণতারও পূর্ণ তৃপ্তি ও চরিতার্থতা কখনই লাভ হতে পারে না।
কোন জিনিস বা ঘটনা সম্পর্কে অনুসন্ধান প্রবণতা চরিতার্থ করার দু’টি মাত্র উপায়ই হতে পারে। প্রথম ব্যক্তি নিজেই সেই জিনিস বা ঘটনা সম্পর্কে পরীক্ষা-নিরীক্ষণ চালাবে এবং নিজেই তার বিশেষত্ব ও গুণাগুণের সরাসরি পর্যবেক্ষণ করবে। আর দ্বিতীয় হচ্ছে, সেই বিষয়ে অন্যদের নিকট থেকে শুনবে ও জানবে। কিন্তু শোনা কথা দেখার মত হয় না কখনও। শোনা কথার ব্যাপারে সন্ধান প্রবণতা চরিতার্থ হতে পারে কেবল তখন, যখন এ কথা নিশ্চিতরূপে জানা যাবে যে, বর্ণনাকারী একান্তই সত্যবাদী ও নিঃস্বার্থ এবং জনদরদী—তার এ গুণের কথা ও তার ত্যাগ ও তিতিক্ষা থেকে অকাট্যভাবে জানা যাবে। সেই সঙ্গেই একথাও নিশ্চিতভাবে জানা যাবে যে, যে বিষয়ে সে সংবাদ দিচ্ছে, তার সহিত তার নিজের ব্যক্তিগত কোন স্বার্থ জড়িত নেই। আরও এই যে, একই ঘটনা বা বিষয়ে যত সংবাদদাতাই সংবাদ দিয়েছে, তাদের সকলের দেয়া সংবাদে পূর্ণ ঐক্য ও সামঞ্জস্য থাকতে হবে। এ কথাও জানতে হবে যে, সংবাদদাতারা যে খবর দিচ্ছে, তার প্রতি তাদের নিজেদেরও পূর্ণ প্রত্যয় রয়েছে। তার প্রমাণ কেবল তাদের মুখের কথায়-ই পাওয়া গেলে চলবে না, তাদের বাস্তব অবস্থা থেকেও তার প্রমাণ প্রকটিত হতে হবে।
কোন ঘটনা বা বিষয়ে পরিপূর্ণ প্রত্যয় উদ্রেককারী এ দু’টি উপায়ই হতে পারে। এ দুটি উপায়েই অনুসন্ধান প্রবণতা পূর্ণরূপে চরিতার্থ হতে পারে এবং এমন দৃঢ় প্রত্যয় ও মানসিক প্রশান্তি অর্জিত হতে পারে যে, বিপরীত কথা যত বলিষ্ঠ ভঙ্গিতেই বলা হোক, তা তার প্রত্যয়ের ভিত্তিমূল নাড়াতে পারবে না, এই বিপরীত কথা বিশ্বাস করতে সে কখনই প্রস্তুত হবে না।
অধিবিদ্যা সংক্রান্ত সমস্যা ও বিষয়াদি:
বিশ্বলোকের প্রকৃতি-ঊর্ধস্থ অধিবিদ্যা পর্যায়ের বিষয়াদি সহজে মানুষের আয়ত্তাধীন হয় না। কিন্তু সে বিষয়গুলো স্বভাবতই এমন যে, সে সম্পর্কে প্রত্যেকটি মানুষের মন ভাবতে বাধ্য এবং মানব প্রকৃতি সে বিষয়ে পূর্ণ প্রত্যয়যোগ্য সমাধান ও নিশ্চিত জ্ঞান লাভের জন্য সদা উন্মুখ, আকুল। সে বিষয়গুলো এই
১. বিশ্বলোকের অস্তিত্ব কি করে হলো? তা কি কোন অতি-প্রাকৃতিক সত্তা নিজ শক্তিবলে সৃষ্টি করেছে, না ‘বস্তু’ বা জড়ের’ বিচিত্র ধরনের স্বতঃস্ফুর্ত কার্যাবলীর ক্রমবিকাশের ফল ?
২. বিশ্বলোক কি কোন আইন-বিধান ও নিয়ম-নীতি অনুসরণ করে চলছে? না, এখানে নিয়ম-শৃঙ্খলাহীন একটা খেলা ও তামাশা চলছে? বিশ্বলোক যদি কোন নিয়ম-শৃঙ্খলা অনুসরণ করে চলে থাকে, যা লঙ্ঘন করার কোন শক্তি-ই তার নেই, তাহলে প্রশ্ন জাগে, সে নিয়ম-শৃঙ্খলা রচনা কারী-ই বা কে এবং এই বিশ্বলোককে সে নিয়ম-শৃঙ্খলা অনুসরন করে চলতে বাধ্যই বা কে করেছে ?
৩. এই বিশ্বলোক স্বীয় বস্তুগত রূপ লয়ে চিরকাল থেকেই আছে এবং তা চিরকাল-ই কি অক্ষয় হয়ে থাকবে ?
৪. এই পৃথিবীতে মানুষের অস্তিত্ব কি করে সম্ভব হলো? এই বিশ্বলোকে তার ‘পজিশন’ বা মর্যাদা কি ? বিশ্বলোক ও তার অন্যান্য অংশের সাথে মানুষের কি সম্পর্ক হওয়া উচিত?
৫. মানুষের এ পার্থিব জীবন ও সত্তা নিঃশেষ হয়ে যাওয়ার পর কি হবে? এইগুলি এবং এই ধরনের আরও অনেক প্রশ্ন এমন রয়েছে, যা চিন্তাশীল মানুষকে সব সময়ই এবং চিরকালই এ সবের জবাব পাওয়ার, জন্যে উদ্বেগ-আকুল করে রেখেছে। ফলে তারা এসব প্রশ্নের জবাব লাভ করার জন্যে—এসব সমস্যার সমাধান করার জন্যে বিভিন্ন মতবাদ ও মতাদর্শ রচনা করেছে এবং সেসব মতবাদ-মতাদর্শের ভিত্তিতে বিভিন্ন পদ্ধতিতে এগুলোর ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করেছে। তাদেরই উন্নতমানের চিন্তার ফসল হিসাবে বিদ্যার এক নবতর শাখার ভিত্তি রচিত হয়েছে।
বিদ্যার এই নবতর শাখার-ই নাম হলো দর্শন। আর পূর্বোদ্ধৃত প্রশ্ন গুলি-ই হচ্ছে দর্শনের মৌলিক জিজ্ঞাসা ও বুনিয়াদী আলোচ্য বিষয়।
মানুষের ইতিহাসে এমন কোন যুগ আসেনি, যখন তার মনে বিশ্বলোক সম্পর্কিত এসব প্রশ্নের কোন না কোন জবার বর্তমান ছিল না। এসব প্রশ্নের একটা জবাব-সমষ্টি প্রত্যেকটি মানুষের মনেই বর্তমান ছিল—চিরকাল। আর এই জবাব সমষ্টি-ই ছিল তার দর্শন— জীবন দর্শন। দর্শন পর্যায়ে চিন্তা গবেষণা চৰ্চা উৎকর্ষ সাধন ও গ্রন্থ প্রণয়নের পূর্বে এ প্রশ্নগুলির জবাব মানুষের প্রকৃতির পক্ষ থেকে দেওয়া হয়েছে। সে জবাবের সারকথা ছিল, বিশ্বলোক স্বতঃই অস্তিত্ব লাভ করেনি, তা সৃষ্টি করা হয়েছে। সৃষ্টি করেছেন বিশ্ব লোক-বহির্ভূত কোন মহাশক্তিমান সত্তা। আর সেই মহান সত্তা-ই এই বিশাল বিশ্বলোকের প্রতিটি অণু-কণার উপর প্রভুত্ব ও কর্তৃত্ব চালাচ্ছেন, তাঁরই রচিত ও জারিকৃত নিয়ম-বিধান মেনে চলতে বাধ্য হচ্ছে বিশ্বপ্রকৃতির প্রতিটি অণু-পরমাণু তাঁর ভয় ও তাঁর অনুগ্রহের স্বীকৃতিমূলক ভাবধারা মানুষের প্রকৃতি নিহিত। এই দর্শন-ই আধ্যাত্মিক দর্শন বা metaphysics নামে অভিহিত এবং তা বস্তুজগত সংক্রান্ত দর্শন থেকে ভিন্নতর। কিন্তু উত্তরকালে কিছু সংখ্যক চিন্তাবিদ প্রাকৃতিক বাহ্য প্রকাশের দিকে মনোনিবেশ করে এবং সে গুলোর ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ পর্যায়ে গভীর চিন্তা ও গবেষণা শুরু করে দেয়। তারা এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে, ‘বস্তু’ বা ‘জড়’ ও বস্তুগত শক্তি (material energies) সমূহ-ই বিশ্বলোক ও তার বাহ্য প্রকাশসমূহের আসল উদগাতা। বিশ্বলোকের অন্তরালে কোন সত্ত্বা বা শক্তির অস্তিত্ব নেই, বিশ্বলোকের উপর তার কোন কর্তৃত্ব বা প্রভুত্ব চলে বলে স্বীকার করার কোন প্রয়োজনই নেই। প্রাকৃতিক বাহ্য প্রকাশের জড়বাদী ব্যাখ্যার ফলে যে ‘দর্শন’ গড়ে উঠল, তা হচ্ছে নাস্তিক্যবাদী দর্শন (philosophy of atheism ) । বস্তুবাদী দর্শন কিংবা জড়বাদ এই দর্শনেরই একটি সংকীর্ণ রূপ। এ অবস্থায়ই দার্শনিক চিন্তা ভাবনা-চর্চা অব্যাহতভাবে চলতে থাকে। উত্তরকালে এমন কিছু লোক আত্মপ্রকাশ করে, যারা স্বীয় প্রকৃতি-নিহিত সাক্ষ্যকেও গুরুত্ব দিতে প্রস্তুত এবং তারা সে সাক্ষ্যের বুদ্ধিসম্মত ব্যাখ্যাদানেরও প্রয়োজন বোধ করে। নাস্তিক্যবাদী দর্শনের বুদ্ধিসম্মত দলীল-প্রমাণের জবাব দেওয়াই ছিল তাদের লক্ষ্য। এসব লোকের চেষ্টার ফলে ধারণাবাদী দর্শনের উদ্ভব হয়। এ দর্শনের ভিত্তি ছিল এ সত্যের উপর স্থাপিত যে, বিশ্বলোকের এক-একটি অণু কণার যা কিছু বিশেষত্ব ও গুণাবলী, তা আসলে মানুষের ইন্দ্রিয়ানুভূতি ও তদজনিত ধারণাবলী মাত্র। মানুষ যদি তা অনুভব না করে, তাহলে সেগুলোর অস্তিত্ব প্রমাণ করা সম্ভবপর নয়। সারকথা হলো, মানুষের ধারণা শক্তিই এসবের অস্তিত্বের উদ্ভাবক। কিন্তু মানুষ নিজে কার ধারণার ফল ? সে হচ্ছে সেই বিশ্ব প্রকৃতি অন্তরালবর্তী সত্তার ধারণা কার্যক্রমের ফল। ফলে এই গোটা বিশ্বলোক এমন এক সত্তার ধারণার ফলে অস্তিত্ব লাভ করেছে, যিনি এই বিশ্বলোক থেকে স্বতন্ত্র ও সম্পূর্ণ বিভিন্ন সত্তা।
জ্ঞান-চর্চা ও চিন্তা-গবেষণার ক্ষেত্রে নাস্তিক্যবাদ ও আদর্শ বাদ ( idealism) নামের এই দুইটি দর্শনেরই চর্চা চলতে থাকল। এ দু’টিরই গর্ভ থেকে জন্ম নিতে থাকল অন্যান্য বহু প্রকারের দর্শন। এর ফলে চিন্তার ক্ষেত্রে একটা দ্বন্দ্ব ও সংগ্রামের ধারাবাহিকতা চলতে থাকল। প্রত্যেক মতের অনুসারী স্বগৃহীত দর্শনের অনুকূলে ও বিপরীত দর্শনের বিরুদ্ধতার যুক্তি প্রমাণ সংগ্রহ করার কাজে ব্যতিব্যস্ত ও বিশেষ কর্মতৎপর হয়ে থাকল। বৈজ্ঞানিক চিন্তা-গবেষণার যুগ সূচিত হওয়ার সময় পর্যন্ত সমগ্র জ্ঞানজগতে এই অবস্থাই অব্যাহত থাকে।
যে সময় থেকে প্রাকৃতিক বাহ্য প্রকাশ নিয়ে বাস্তব পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণ ধারা শুরু হলো এবং তৎলব্ধ ফলাফলকে ভিত্তি করে প্রকল্প ও মতবাদ পর পর সাজানো ও পরম্পরাবিধান শুরু হলো, সে সময় থেকেই নাস্তিক্যবাদী দার্শনিকরা বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব ও মতাদর্শের উপর ভিত্তি করে আলোচনা-পর্যালোচনা ও যুক্তি-প্রমাণ উপস্থাপন শুরু করে দিল। এভাবে বিজ্ঞানের যতই উন্নতি উৎকর্ষ ও অগ্রগতি হতে থাকল, নিত্য নতুন তত্ত্ব ও মত উদঘাটিত হতে থাকল, নাস্তিক্যবাদের এই দর্শন ততটাই বলিষ্ঠ হতে লাগল। বিজ্ঞানের সাথে সম্পর্ক রেখেই তারা তাদের বিশেষ দর্শনের চর্চা করত। ফলে তাদের মনে এই অহমিকতা বোধ জাগল যে, মানুষের ব্যক্তিগত ও সামাজিক-সামষ্টিক জীবনের যাবতীয় সমস্যার প্রকৃত ও বিবেকসম্মত সমাধান কেবল তারাই পেশ করতে সক্ষম। কেবল তারাই পারে এমন একটা জীবন ব্যবস্থা রচনা করতে, যা মানবতা ও মনুষ্যত্বের উন্নতি সাধনের জন্যে অপরিহার্য। ধর্মের দিক থেকে যা কিছু বলা হচ্ছে, তার সাথে বিবেক-বুদ্ধি যুক্তি-বিজ্ঞানের কোন সম্পর্ক নেই। সে সব কথা অনেক পুরাতন এবং সেই কালের উদ্ভাবিত, যখন মানবীয় বিবেক-বৃদ্ধি ছিল নিতান্তই কাঁচা, অপরিপকক্ক ও বাকসুলভ। বিজ্ঞানের নাম-চিহ্নও তখন ছিল না।
নাস্তিক ও জড়বাদীদের এ অহমিকতা একান্তই বাস্তবতা বঞ্চিত, ভিত্তিহীন। তাদের এ অহমিকতা চূর্ণ করার জন্যে একটা কথা-ই যথেষ্ট। মানব জীবনের যে পথ স্বয়ং মানুষের মনস্তত্ত্ব ও স্বভাব-প্রকৃতির সহিত সঙ্গতিপূর্ণ (consistant ) নয়, সে পথ মানবতার ধ্বংস ও বিলুপ্তির দিকে চলে যাবে নিঃসন্দেহে, মানবতার কল্যাণ ও উৎকর্ষ বিধানের দিকে কখন-ই এবং এক -দমও যেতে পারে না। এ এক চূড়ান্ত সত্য কথা। তার কারণ, বিশ্বলোকের metaphysics ( প্রকৃতি-বহির্ভূত) সংক্রান্ত জিজ্ঞাসাসমূহের সঠিক ও নির্ভুল সমাধান বের করার উপরই জীবনের পথ নির্ধারণ একান্তভাবে নির্ভরশীল। আর একথায়ও কোন সন্দেহ নেই যে, এ প্রশ্ন ও জিজ্ঞাসাসমূহ মানুষের বাস্তব পরীক্ষণ-নিরীক্ষণ ও পর্যবেক্ষণের আওতা-বহির্ভূত ব্যাপার। এগুলো কখন-ই মানুষের বাস্তব অনুভূতির মধ্যে আসে না, আসতে পারে না। এই কারণে নাস্তিক্যবাদী দর্শনের ভিত্তি স্থাপিত যে বিজ্ঞানের উপর, তা এ সব সম্পর্কে কোন চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত দিতে পারে না। এর ফল এই দাঁড়ায় যে, নাস্তিকদের দিক থেকে এসব প্রশ্ন ও সমস্যার যে সমাধান পেশ করা হয়, তা পুরাপুরি ধারণা অনুমানমূলক হতে বাধ্য হয়, আর ধারণা অনু মানের কোন স্থিতি নেই বলেই এসব আনুমানিক ও ধারণাগত সমাধানের উপর ভিত্তিশীল জীবন ব্যবস্থাও কোন স্থায়িত্বই লাভ করতে পারে না।
এই সমস্ত দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব ও মতাদর্শ অধ্যয়ন করে মানুষ একটা বিশ্রী ধরনের মানসিক দ্বন্দ্বে নিমজ্জিত হয়ে পড়ে। কোনটা প্রকৃত সত্য— আদর্শবাদী দর্শন যা বলে তা, না নাস্তিক্যবাদী দর্শন যা বলে, তার কোন কিছুই তার বোধগম্য হয় না। সে অনেকটা দিশেহারা হয়ে যায়। প্রত্যেক দর্শন-ই নির্ভুল ও পরম সত্য হওয়ার দাবি করে। অথচ সে সবের বক্তব্য পরস্পর বিরোধী। তার মধ্যে কোন একটিও জীবন ব্যবস্থার ভিত্তি হওয়ার -যোগ্য বিবেচিত হতে পারে না। কেননা তার কোনটি বিশ্ব-প্রকৃতি নিহিত ধ্বনির সহিত সঙ্গতিসম্পন্ন নয়। উভয় দর্শন-ই দুর্বোধ্য ও দুঃসাধ্য সমস্যাবলী রচনা করে তার সমাধান বের করার উদ্দেশ্যে এমন সব জটিল যুক্তি জালের প্রবর্তন করেছে যে, মানুষের বিবেক-বুদ্ধি সে জালে ফেঁসে গিয়ে শুধু ছট ফট করে নিস্তেজ ও স্তব্ধ হয়ে যেতে বাধ্য হয়।
তবে উপরে যে আধ্যাত্মবাদী দর্শনের কথা বলা হয়েছে, তা মানব-প্রকৃতির সহিত অনেকটা সঙ্গতিসম্পন্ন। কিন্তু তবুও এ কথায় সন্দেহ নেই যে, তা-ও মানুষকে নানা ভিত্তিহীন কুসংস্কারের অন্ধত্বে নিমজ্জিত করতে পারে। পারে, যদি মানুষ বিশ্বলোকের বিভিন্ন অংশ সম্পর্কে নির্ভুল জ্ঞানের অধিকারী না হয়। মানব-প্রকৃতিতেও যে দুর্বলতা রয়েছে তা অস্বীকার করার উপায় নেই। কেননা যে সত্তা বা বস্তুতে কোন রাগ কি শক্তি মানুষ দেখতে পায় বা আছে বলে ধারণা হয় এবং সে সত্তা বা বস্তুর আসল পরিচয় তার অবিদিত থাকে, তাহলে মানুষ তাই বিনয় ও আনুগত্যের মস্তক অবনমিত করে দেয়। তার প্রতি ঠিক সেই রূপ আচরণ অবলম্বন করতে শুরু করে দেয়, যেমন আচরণ আল্লাহর সহিত করা বাঞ্ছনীয়। মানব প্রকৃতির এই অন্তর্নিহিত দুর্বরতার কথা স্মরণ রাখা আবশ্যক। বিশ্বলোকের বিভিন্ন অংশকে আল্লাহ্ রূপে গ্রহণ করা মানবেতিহাসে কোন বিরল বা অঘটিত কাহিনী নয়। আজও-বিশ শতকের এই বিজ্ঞানের চরমন্নোতির যুগেও চন্দ্র ও সূর্যকে দুনিয়ার কোন কোন জাতি খোদা বা দেবতা বানিয়ে রেখেছে ও পূজা করছে। ফেরেশতা, নবী-রাসূল, অগ্নী-দরবেশ-পীর প্রভৃতিকে খোদায়ী গুনে উপান্বিত আজও ধারণা করা হচ্ছে। আজও তাদেরকে খোদায়ী ব্যবস্থায় হস্তক্ষেপ করতে সক্ষম বলে বিশ্বাস করা হচ্ছে। আধ্যাত্মিক দর্শন অনুসরণের ফলে অন্ধ কুসংস্কারে নিমজ্জিত হওয়ার এই বিপদ থেকে রক্ষা পাওয়ার একটি মাত্র উপায়ই রয়েছে। আর তা হলো এ আধ্যাত্মবাদী দর্শনের শিক্ষা দান করা হবে কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে এবং সেই সঙ্গে বিজ্ঞানের শিক্ষাও দেওয়া হবে। মানুষ যেসব কারণে বিশ্বলোকের বিভিন্ন অংশের পূজা-উপাসনা শুরু করে দেয়, বিজ্ঞানের নির্ভুল জ্ঞান শিক্ষা দানের ফলে মানব মন থেকে সে সব কারণ নির্মূল হয়ে যাবে এবং মনে-মনস্তত্ত্বে এমন তওহীদী ভাবধারা জাগ্রত হবে, যার ফলে সে কোন দিন-ই কোন অ-খোদার আরাধনা ও উপাসনায় লিপ্ত হতে প্রস্তুত হবে না।