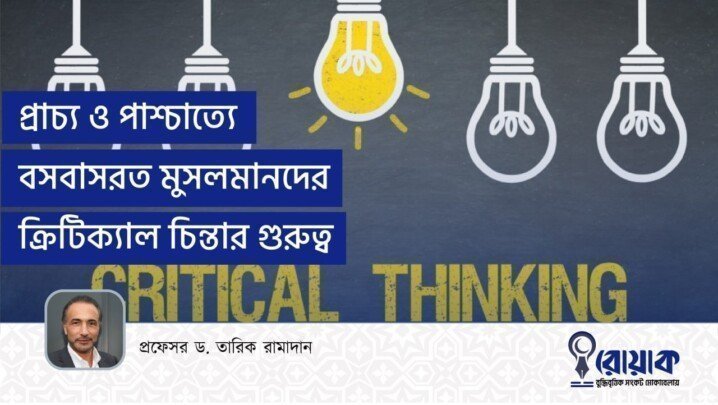আমরা যখন কোনো বিষয়ে ক্রিটিক্যাল চিন্তার কথা বলি, তখন শুধু মানব বিজ্ঞান নিয়ে আলোচনার কথাই বুঝাই না। ক্রিটিক্যাল চিন্তা বলতে বুঝায়, বিশ্বকে পর্যবেক্ষণের ব্যাপারে আমাদের নিজস্ব বোধ, নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি। আমি এখানে ক্রিটিক্যাল চিন্তা বলতে আমরা মুসলিম হিসেবে আমাদের ইসলামিক ট্রাডিশানে কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে কীভাবে আমাদের রেফারেন্সগুলো ব্যবহার করবো সে বিষয়ে কথা বলতে চাই। আমি এখানে পুরো চিত্রটা তুলে ধরে আলোচনার উদ্দেশ্য ও প্রেক্ষাপট বিশ্লেষণ করতে চাই। একজন মুসলিম হিসেবেই শুধু নয়, একজন চিন্তক বা একজন নাগরিক হিসেবে বা আজকের বিশ্বের একজন মানুষ হিসেবে জ্ঞানের অন্যান্য শাখার সাথেও কিভাবে বোঝাপড়া করব সেই বিষয়ে কথা বলতে চাই। শুরুতেই ‘ক্রিটিক্যাল চিন্তা’ বা ‘বিশ্লেষণী চিন্তা’ বলতে আমি কী বুঝাচ্ছি সেটি স্পষ্ট করতে চাই। আমাদের ইসলামী ঐতিহ্যেও এমন অনেক বিষয় আছে, যেগুলোকে প্রশ্ন করা জরুরী। কিন্তু আমরা কি এখানে ‘পিওর রেশনালিজম’ বা ‘নিখাঁদ যুক্তিবাদিতা’র কথা বলছি ? যেখানে সবকিছুই প্রশ্নবিদ্ধ করার যোগ্য ? যারা এ ধরণের ‘নিখাঁদ যুক্তিবাদিতা’র কথা বলেন, তারা এটাকে এমনভাবে উপস্থাপন করার চেষ্টা করেন, যাতে মনে হয় যেন এটা কোনো আদর্শবাদী অবস্থান নয়। কিন্তু আদতে যেখানে কোনো আদর্শ স্থাপিত নেই, সেখানেও একটা আদর্শ থাকে। এখানে প্রশ্নটা হচ্ছে আমি কি এমন কোনো ক্রিটিক্যাল চিন্তার কথা বলছি, যেখানে ‘যুক্তিবাদিতা’ই একমাত্র মাপকাঠি ? নাকি এখানে অন্য কিছু আছে, যার দিকে আমি ইঙ্গিত করছি ? সুতরাং এই বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে, আমরা যা চিন্তা করছি তার ব্যাপারে আমাদের স্বচ্ছ ধারণা আছে কি না ?
যদি আমরা সত্যিকার অর্থেই ইসলাম নিয়ে চিন্তা করি, তাহলে প্রথমেই দুটি বিষয়ে আমাদের বোঝাপড়া থাকতে হবে। একটা হলো বিশ্বাস, অন্যটা হলো রিজন (আক্বল/বুদ্ধি/যুক্তি)। আমরা আমাদের ঐতিহ্যের আলোকে বলে থাকি যে, বিশ্বাস ও যুক্তির মধ্যে কোনো বৈপরীত্য নেই। কিন্তু কিছু বিষয় আছে যেগুলো আমরা বিশ্বাস করি, সেটা যুক্তি দিয়ে প্রমাণিত হোক বা না হোক। কেননা অনেক কিছুই যুক্তি দিয়ে প্রমাণ করা যায় না কিন্তু আমরা এই বিষয়গুলোতে বিশ্বাস করি আমাদের ‘স্টার্টিং পয়েন্ট’ হিসেবে।
যেহেতু আমরা ক্রিটিক্যাল চিন্তা নিয়ে আলোচনা করছি, সেহেতু প্রথমেই কিছু বিষয় ক্লিয়ার করে নেওয়া দরকার যে, এই চিন্তার কোনো সীমা আছে কি না, বা সবকিছুই যুক্তি বা আক্বল নির্ভর কিংবা বিশ্লেষণধর্মী কি না। ইসলামিক ট্রাডিশনে ‘রিজন’ (আক্বল/যুক্তি) এবং ‘বিশ্বাস’ এর সম্পর্কটা কী, সেটাও বোঝা জরুরী।
বদর যুদ্ধের সময় একদা হুবাব ইবনে মুনযির রাসূল (সা.) এর কাছে আসলেন। তিনি তাঁর প্রশ্নের ব্যাপারে ক্লিয়ার ছিলেন আর তা ছিলো যুদ্ধের কৌশল প্রসঙ্গে। তিনি রাসূল (সা.)-কে বললেন, আমরা এখন যে জায়গায় আছি, সেটা কি আপনি নির্ধারণ করেছেন নাকি আল্লাহর পক্ষ থেকে আগত ? যদি এটা (পাহাড় ঘেঁষে অবস্থান করার কৌশল) আল্লাহর পক্ষ থেকে আদেশ হয়ে থাকে, তাহলে সেটা নিয়ে কথা বলবো না। তবে যদি আপনার নিজের কৌশল হয়ে থাকে, তাহলে আমার কিছু বলার আছে। রাসূল (সা.) বললেন, এটা আমার ব্যক্তিগত মতামত। সাহাবী বলেন, হে আল্লাহর রাসূল, এটা কার্যকরী কৌশল নয়, বরং আমরা আমাদের কৌশলকে আরো সুন্দরভাবে সাজাতে পারি।
শুরুতেই তাঁর কাছে মূল বিষয় ছিল তিনটি।
প্রথমত : প্রথম হলো উৎস। এই সিদ্ধান্তটি আপনার পক্ষ থেকে নাকি আল্লাহর পক্ষ থেকে। এটা কি ঐহিক নাকি মানবিক ? যদি ঐহিক হয়, তাহলে আমরা শুনলাম এবং মেনে নিলাম। যদি আপনার পক্ষ থেকে আসে, তাহলে আপনি যেই হোন, এমনকি আল্লাহর রাসূল (সা.) হলেও এটা প্রশ্নাতীত নয়। যে কোনো মানবিক বিষয়ই চূড়ান্ত বা প্রশ্নাতীত নয়।
দ্বিতীয়ত : দ্বিতীয় হলো বুদ্ধিবৃত্তিক মনোভাব; আপনি কি করেন, তা আমার বোঝা দরকার। এটা কি সঠিক বা যৌক্তিক ? তিনি কিছু বিষয় ভালোভাবে বুঝার জন্য এসেছিলেন। সুতরাং বোঝাপড়া হলো দ্বিতীয় বিষয়।
তৃতীয়ত : প্রশ্ন করা। যদি কোথাও প্রশ্ন করার সুযোগই না থাকে, তাহলে সেটা বুঝার জন্য মানুষ প্রশ্ন করতে পারে না। তাই তিনি রাসূল (সা.)-কে প্রশ্ন করেছিলেন। রাসূল হিসেবে নয়, বরং যুদ্ধকালীন সেনাপতি হিসেবে।
প্রথমত উৎস, দ্বিতীয়ত বোঝাপড়া, তৃতীয়ত প্রশ্ন করা। ইসলামিক দৃষ্টিকোণ থেকে এখানে উৎসগুলো স্পষ্ট। যদি আমি বলি আমি আল্লাহকে বিশ্বাস করি তাহলে এখানে একটি ফ্রেম তৈরি হয়, যেটা দিয়ে আপনি বিশ্বকে বোঝাপড়ার চেষ্টা চালাচ্ছেন। আর এটা আমাদের পক্ষ থেকে প্রশ্ন করার বিষয় নয়। কিন্তু একজন বিশ্বাসী হিসেবে আমি বলতে চাই, মানুষের কাছ থেকে যাই আসবে, তার সবই আলোচনা সাপেক্ষ ব্যাপার। সুতরাং মুসলিম হিসেবে আমাদের যাচাই করা দরকার, কোনটা আল্লাহর পক্ষ থেকে আসছে, আর কোনটা মানুষের দ্বারা পুনর্গঠিত হয়েছে।
- কেন এটা যাচাই করা দরকার ?
কারণ, আমরা কখনো কখনো আমাদের ইতিহাসের মানবিক বিষয়গুলোকেও ‘আইডিয়ালাইজ’ (আদর্শায়িত) করে ও পবিত্র মনে করে প্রশ্নাতীতভাবে মেনে নিতে চাই। তারা যেভাবে ধর্মশাস্ত্রগুলো বোঝাপড়া করেছে, যেভাবে সময়ের বাস্তবতাকে বিবেচনায় নিয়েছে বা ইতিহাসকে বোঝাপড়া করেছে; এসব ক্ষেত্রে তাদের নিজস্ব মতামত ও উদ্দেশ্য ছিলো। ফলে আমরা এখন যেরকম আমাদের বর্তমান সময়কে মোকাবেলা করছি, তারাও একইভাবে তাদের সময়কে মোকাবেলা করেছে। এজন্যই এরকম অনেক মানবিক মতামত ও ইতিহাসকে ‘আদর্শায়িত’ কিংবা ‘পবিত্রায়িত’ করে প্রশ্নহীনভাবে গ্রহণ করা আমাদের উচিৎ নয়।
প্রায় সকল বিখ্যাত স্কলারই, শিয়া কি সুন্নী, স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন, আমার মতামত যদি কুরআন হাদীসের সাথে মিলে, তাহলে গ্রহণ করো। যদি না মিলে, বর্জন করো। এর মানে দাঁড়ায়, আমি সাধারণ একজন মানুষ। এর বেশি কিছু না। সুতরাং আমরা যে ক্রিটিক্যাল চিন্তা করতে যাচ্ছি, তা হচ্ছে মানব ইতিহাসকেও ক্রিটিক্যালি বোঝার চেষ্টা করা।
কারণ, আমাদের চিন্তায় যা কিছুই মানবিক বা মানুষের কাছ থেকে এসেছে, সেটা প্রশ্নাতীত নয়, বরং যে কোনো ধরণের আলোচনার জন্য উন্মুক্ত। এজন্যই আমি এই তিনটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সামনে আনছি। প্রথমেই আমাদেরকে কোনো বিষয়ের উৎস কী সেটা বুঝতে হবে। আল্লাহর কাছ থেকে আসলে আমরা প্রশ্নাতীতভাবেই মেনে নেব, আর যদি মানুষের কাছ থেকে আসে তাহলে দ্বিতীয়ত আমরা বিষয়টি ভালোভাবে বোঝাপড়া করার চেষ্টা করবো এবং তৃতীয়ত কোনো ধরণের প্রশ্ন বা জিজ্ঞাসা থাকলে তা উপস্থাপন করবো। প্রশ্ন করা, বিতর্ক করা এগুলোকে আমাদের অবশ্যই ইতিবাচকভাবে নিতে হবে। বিশেষত; একাডেমিয়ায় এই প্রশ্ন করার সুযোগ ও স্বাধীনতাকে আরো সম্প্রসারিত করতে হবে। আমি প্রশ্ন করছি, এর মানে এই নয় যে ইসলামের প্রতি আমার বিশ্বাস আপনার তুলনায় কম। আপনার বিশ্বাসের মানে ‘আপনি প্রশ্ন করা ছাড়াই গ্রহণ করছেন’ এর উপর নির্ভর করে না। বরং গভীর প্রশ্ন আমাদেরকে গভীর বিশ্বাস অর্জনে সাহায্য করে। প্রশ্ন করা আর বিশ্বাস করা, এই দুইয়ের মধ্যে কোনো সংঘাত তো নেই-ই বরং আপনি যদি ইসলামী ঐতিহ্যের দিকে তাকান তাহলে এর বিপরীতটাই দেখতে পাবেন।
আরো কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় রয়েছে। যেমন-প্রথম ইসলামিক সায়েন্স হলো ফিকহ। তখনকার যুগে মানুষের কোনো বিষয় জানার ক্ষেত্রে ধরণটা কেমন ছিল ? বিশেষ করে কোনো আইনি বিষয়ে ফতোয়ার ক্ষেত্রে তারা আলেমদের কাছে যেতো। আর যদি সাহাবীদের সময়ের কথা চিন্তা করেন, আপনি দেখবেন যে, তারা সাধারণত ফতোয়া দিতে চাইতেন না। কারণ, তারা ভুল করার ব্যাপারে খুবই সতর্ক ছিলেন। কিন্তু আপনি যখন কোনো আলেমেট কাছে যাবেন কোনো নির্দিষ্ট বিষয়ে ফতোয়া জানার জন্য, তখন আপনি উত্তর পেয়ে যাবেন। কিন্তু আপনার দায়িত্ব হচ্ছে, এর যৌক্তিকতা খুঁজে নেওয়া। কীভাবে তিনি এই সিদ্ধান্তে আসলেন ? আর আপনি যদি এটা না করেন, সেক্ষেত্রে আপনি যেহেতু মুকাল্লিদ, (মুকাল্লিদ মানে হচ্ছে, আরেকজনের মতামতের অনুসরণ করা) তাই আপনি জবাব তো পেলেন, কিন্তু বিষয়টি আপনার বোঝা হলো না। এ পদ্ধতি সঠিক নয়। ফিকহী বিষয়গুলোতে আমাদের বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে প্রতিশ্রুতিশীল হতে হবে।
সিদ্ধান্তটি কিভাবে কোথা থেকে এসেছে, সেটা বুঝতে হবে। কোনো আলেম যদি কোনো কিছুকে হারাম বলে, তাহলে কেনো হারাম প্রথমেই তার উৎস, দ্বিতীয়ত যৌক্তিকতা বুঝতে হবে এবং তৃতীয়ত কোনো বিষয় অস্পষ্ট থাকলে প্রশ্ন করতে হবে। আর সেটাই বদর যুদ্ধের সময় হুবাব ইবনে মুনযির (রা.) করেছিলেন। আরেকটা হাদীসের কথা আমরা সকলেই জানি। একদা রাসূল (সা.) মুয়ায ইবনে জাবাল (রা.)-কে ইয়েমেনে পাঠানোর চিন্তা করলেন। পাঠানোর সময় জিজ্ঞেস করলেন,
– তুমি সেখানে গিয়ে কোনো বিষয়ের সমাধান কিভাবে করবে?
– কুরআন দিয়ে।
– যদি কুরআনে না পাও ?
– তাহলে সুন্নাহ দিয়ে।
– যদি সুন্নাহর মধ্যেও না পাও ?
– সুন্নাহের মধ্যে না পেলে তখন ইজতিহাদ করবো। নিজস্ব চিন্তা-ভাবনা প্রয়োগে সিদ্ধান্ত দিবো।
এর মানে হচ্ছে, যখন সরাসরি ওহী না থাকে এবং আমাদের সুন্নাহও আমাদের কোনো নির্দেশনা না দেয়, তখন বিষয়টি বুঝার জন্য আমরা আমাদের বুদ্ধিবৃত্তিকে ব্যবহার করবো। দ্বিতীয়ত ইয়েমেনের অবস্থা সম্পর্কে জানবো। তৃতীয়ত একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হবো। বুদ্ধিবৃত্তি হচ্ছে একমাত্র বিষয় যার দ্বারা সমকালীন অবস্থা বুঝা যায়। সুতরাং এটাই হচ্ছে ক্রিটিক্যাল চিন্তা।
আমাদের ইসলামী জীবনধারায় কাঙ্খিত মানের মুসলিম হওয়ার কোনো সুযোগ নাই; যদি আমাদের বুদ্ধির ব্যবহার উৎস, বোঝাপড়া ও প্রশ্ন করা এই তিনটি মৌলিক বিষয়ের উপর ভিত্তি করে না হয়।
এখানে আরো একটি বিষয় আমাদের বোঝা দরকার যে, কখনো কখনো ‘তাকলিদি মুসলিম’ ধারণাটি একটি পরস্পর বিরোধপূর্ণ ধারণা। কারণ, একজন মুসলিম কখনো আরেকজন মানুষের চিন্তার উপর ভর করে চলতে পারেনা। আপনি কী পালন করছেন, সেটা যদি আপনি না-ই বুঝতে পারেন, তাহলে কিভাবে হবে ? কেউ কেউ বলে “সাধারণ মুসলিমরা যদি কারো অনুসরণ করে, তাহলে কী সমস্যা?” আমি মনে করি এটা একটা বিপজ্জনক ধারণা। মানুষের বুদ্ধিবৃত্তিক সত্ত্বাকে এভাবে ছোট করা আসলেই সমস্যাজনক। ইসলাম সবসময়েই বলে নেতাদের দিকে তাকানোর চেয়ে বরং অনুসারীদের দিকে তাকাও। নেতারা কী করে সেটা অনুসারীদের বোঝার প্রয়োজন আছে। ইসলামে যে ‘জামাআহ’র ধারণা, সেটা সামগ্রিকভাবে উম্মতের সকলকে উদ্দেশ্য করেই ব্যবহৃত হয়। এজন্যই সাধারণ মানুষকে শিক্ষিত-সচেতন করে গড়ে তোলা খুবই জরুরী।
একই সাথে, সবকিছুই কুরআনে আছে এটা সঠিক নয়। কেবল মূলনীতিগুলো কুরআনে আছে কিন্তু এর তাৎপর্য ও বাস্তবায়ন পদ্ধতি উল্লেখ নেই। কুরআনে চিকিৎসা বিজ্ঞান কিংবা মানব শরীরতত্ত্ব নেই তবে এগুলোর গুরুত্ব ও মূলনীতি বলা আছে। সমাধান নেই। গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো রাসূল (সা.) বলেছেন, “আল্লাহ তায়ালা কিছু বিষয়ে নীরব থেকেছেন, এর মানে এই নয় যে তিনি ভুলে গেছেন বলে, বরং সেখানে এক ধরনের কল্যাণ বিদ্যমান।” আল্লাহর নীরবতাই হচ্ছে আমাদের ক্রিটিক্যাল চিন্তার প্রথম ধাপ। এরকম অনেক বিষয়ে তিনি চুপ থেকেছেন, এর মধ্য দিয়ে তিনি আমাদের বুদ্ধিবৃত্তিকে গঠন করতে বলেছেন। চিন্তা করুন, প্রশ্ন করুন, সিদ্ধান্তে আসুন। এই হচ্ছে আমাদের জীবনধারা। সুতরাং নীরবতা আমাদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কুরআনে আছে-
يا أيها الذين آمنوا لا تسئلوا عن الأشياء إن تبد لكم تسؤكم-
“তোমরা কিছু বিষয়ে প্রশ্ন করো না। যদি সেগুলো তোমাদের উপর নাযিল হতো, তাহলে তা নেতিবাচক হতো।”
আল্লাহ বুঝাচ্ছেন, আমার নীরবতা তোমাদের জন্য কল্যাণকর। তাই কুরআন অবতীর্ণকালীন সময়ে বেশি বেশি প্রশ্ন করো না। ফলে, যেসব বিষয়ে আল্লাহ নীরব থেকেছেন, সেখানে আমাদের নিজস্ব বুদ্ধিবৃত্তি ব্যবহারের সুযোগ তৈরি হয়েছে। এটা আমাদের ক্রিটিক্যাল চিন্তার ক্ষেত্রে খুবই শক্তিশালী উৎসাহের জায়গা।
এ পর্যায়ে আমরা ক্রিটিক্যাল চিন্তার একটি ফ্রেমওয়ার্ক বা গঠনকাঠামো দাঁড় করাবো, যা আমাদের ধর্মের প্রতি বিশ্বাসী হওয়ার আবশ্যকীয় উপায়। তাই এখানে আমি যেটা বলতে চাই, তা হচ্ছে ক্রিটিক্যাল চিন্তার নামে আমরা সবকিছুকেই প্রশ্ন করা শুরু করবো না। যেমন-ধরুন আল্লাহর অস্তিত্ব, কুরআনের সত্যতা। আমাদের কিছু কিছু চিন্তক আছেন যারা এই বিষয়গুলোকেও প্রশ্নবিদ্ধ করতে চান, তারা বলেন যে, কুরআন অন্যান্য যে কোনো বইয়ের মতোই একটি বই; আমার মতে এটি একটি গুরুতর সমস্যা। আল্লাহর অস্তিত্ব, কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার মতো বিষয়গুলোকে আমাদের চিন্তার ভিত্তি হিসেবে স্বীকার করেই আমাদের ক্রিটিক্যাল চিন্তা শুরু করতে হবে। যেহেতু কুরআন আমাদেরকে বলে যে, سمعنا و أطعنا “আমরা শুনলাম এবং মেনে নিলাম” তাই আমাদের বুদ্ধি-যৌক্তিকতা ব্যবহার করে আমাদের ‘আক্বল’ এর সীমাবদ্ধতা বুঝতে হবে। তাই কখনো কখনো আমরা শুধুমাত্র ‘আক্বল’/‘রিজন’-কে ব্যবহার করেই কোনো বিষয়ের উপসংহারে পৌঁছাতে পারবোনা, বরং এসব ক্ষেত্রে আমাদেরকে আমাদের ‘ক্বলব’ বা ‘হৃদয়বৃত্তি’কে ব্যবহার করতে হবে।
যেমন-কুরআনে আছে- لهم قلوب لا يفقهون بها “তাদের হৃদয়বৃত্তি আছে, তবুও তারা বুঝে না”। জ্ঞানের উৎস শুধু আমার বুদ্ধিবৃত্তি নয় বরং আমার হৃদয়বৃত্তি বা ক্বলবও। তাই আমি স্পিরিচুয়ালি এটা বুঝতে পারি, যখন কুরআন বলে- ألا بذكر الله تطمئن القلوب “আল্লাহর স্মরণে হৃদয় প্রশান্তি লাভ করে।” আমি বুঝাতে চাচ্ছি, কিছু জ্ঞান আছে যেমন معرفة الله বা আল্লাহর পরিচয়, সেগুলো শুধু যুক্তি দিয়ে প্রমাণ করা যায় না, বরং তা হৃদয়বৃত্তি বা ক্বলবের বিষয়। মানুষের কাছে সত্য পৌঁছানোর ধারণার ক্ষেত্রে এটাই আমার ‘সূচনা বিন্দু ’। তাই আমি এখানে ক্রিটিক্যাল থিংকিং এর যে কাঠামো দাঁড় করাতে চাচ্ছি সেখানে আমি সবকিছু ধ্বংস করে নতুন চিন্তা শুরু করছি, এমন কথা বলতে চাচ্ছিনা।
অনেক সময় মানুষের কথাবার্তা থেকে আমি বুঝতে পারি যে, তারা বলে, আপনি কি করতে চাচ্ছেন ? আপনি কি মডার্নিস্ট যে ইসলামের উৎসসমূহকে প্রশ্নবিদ্ধ করতে চাচ্ছেন ? কিন্তু তাদের এ ধারণা সঠিক নয়। কিন্তু আপনাকে চিন্তার কাঠামো ও কোন জায়গা থেকে আপনি ক্রিটিক্যাল চিন্তা শুরু করবেন সে সম্পর্কে সঠিক ধারণা থাকতে হবে।
এখন একটি স্পষ্ট সিদ্ধান্তে আসা যাক, কোনটা আল্লাহ প্রদত্ত আর কোনটা মানুষের থেকে। প্রথমে আমাদেরকে আয়াতের মূল ইবারত দেখতে হবে এবং তারপর আয়াতের গুরুত্ব বিশ্লেষণ করতে হবে। কারণ সব আয়াত এক রকম নয়, হাদীসের ক্ষেত্রেও একেক হাদীসের মান একেক রকম। কোনটা সহীহ আর কোনটা যঈফ। আমাদেরকে এদের গুরুত্ব বুঝতে হবে।
আমরা মানুষের ড্রেস দেখে মূল্যায়ন করি। কিন্তু মূলনীতি হচ্ছে প্রথমে থাকতে হবে ঈমান। তারপর পোশাক-আশাক।
কুরআনের ইবারত বুঝতে হলে আয়াতের সাথে সাথে আয়াতের ইতিহাস, প্রেক্ষাপট জানা থাকতে হবে। আপনি ইবারত ততক্ষণ বুঝতে পারবেন না, যতক্ষণ না আয়াতের প্রেক্ষাপটের ব্যাপারে সঠিক ধারণা না থাকবে। আয়াতটি কেনো নাযিল হলো, এর সংশ্লিষ্ট ঘটনা কী, এসব জানা থাকতে হবে। অর্থাৎ ওহী এবং পারিপার্শ্বিক বাস্তবতার মধ্যে যোগসূত্র থাকতে হবে। ইবারত, শানে নুযুল, ইতিহাস এগুলো গুরুত্বপূর্ণ। সুতরাং শুরু করার জায়গাটি হলো আমরা মানুষ কর্তৃক গৃহীত প্রতিটি সিদ্ধান্ত যাচাই করবো, প্রশ্ন করবো। এখন প্রশ্ন হলো আমরা কোথা হতে শুরু করবো ?
কারণ যদি আপনি শুধু সমাজবিজ্ঞান নিয়ে পর্যালোচনা করেন এবং এর পরিধি সম্পর্কে আপনার জ্ঞান থাকে, তাহলে আপনি সমাজবিজ্ঞান সম্পর্কে প্রশ্ন করতে পারেন, কিন্তু আপনার মূল পরিভাষাকে নয়, যেমন আপনি আপনার মূল ইসলাম ও বিজ্ঞানে নিয়ে যদি পর্যালোচনা করেন। তবে, শুরু করার জন্য এটা কোনো সঠিক পন্থা নয় বরং শুরু করতে হবে আমাদের নিজেদের মধ্যে থেকে, যেমনটা আমি পূর্বে বলেছি।
- এখন বিষয় হলো আমি কোথা হতে শুরু করবো ?
একটি আলোচনার দিকে যাওয়া যাক, যেটা হচ্ছে মুসলিম আলেম, মুসলিম বুদ্ধিজীবী এবং সকল প্রকার মানব জ্ঞান নিয়ে।
আমাদের গুরুত্বপূর্ণ একটি সমস্যা হলো সংজ্ঞা ও পরিভাষা সম্পর্কে সঠিক ধারণা না থাকা। আমি আরবী থেকে তুর্কিতে রূপান্তরের কথা বলছি না, বা আরবী থেকে ইউরোপীয় ভাষায় রূপান্তরের কথাও বলছি না, বরং আরবী পরিভাষা থেকে আরবী ভাষায়ই ব্যাখ্যা করতে গেলেও সমস্যা তৈরি হতে পারে। আপনি শরীয়াকে কিভাবে ব্যাখ্যা করবেন ? কে করবে ব্যাখ্যা ? যদি আপনার ফকীহ থাকেন, তাহলে তাঁর নির্দিষ্ট বিষয়ে বুঝাপড়া থাকতে হবে। এটা হচ্ছে ইসলামী আইন। যদি আপনি সুফীর কাছে যান, তার রয়েছে একরকম ব্যাখ্যা। যদি কোনো দার্শনিকের কাছে যান, তিনি আলাদা ব্যাখ্যা দিবেন। মুসলিম হিসেবে আমাদের জানতে হবে যে, আমরা আসলে কিভাবে শরীয়াকে ব্যাখ্যা করবো ? শরীয়া শুধুমাত্র একটা গঠন কাঠামো নয় বরং এটা এর চেয়েও গভীর এবং তাৎপর্যপূর্ণ।
সুতরাং আমাদের প্রশ্ন করতে হবে যে, কিভাবে, কে এবং কোথা থেকে শরীয়া ব্যাখ্যা করবো। যখন আপনি ইসলাম নিয়ে কথা বলেন, তখন ইসলামকে কোন হিসেবে ব্যাখ্যা করেন ? কেউ বলে ইসলাম একটি ধর্ম, কেউ বলে সভ্যতা, কেউ বলে জীবন মৃত্যুর ধারণা। আবার ইউরোপীয় ভাষায় ইসলাম বলতে বুঝায় আত্মসমর্পণ। এবার আমি বলি, আপনি কি আরবীতে চিন্তা করেন ? এখন আপনি আরবী ও তুর্কি ভাষায় বুঝার চেষ্টা করেন যে, ইসলামের সঠিক বোঝাপড়া হলো, এর অর্থ আত্মসমর্পণ এবং এভাবেই অন্যান্য ভাষাগুলোতে ইসলাম শব্দের অর্থ করা হয়েছে। ইসলামের সর্বোচ্চ মূল্যবোধ কী ? এটা কি শান্তির পথে ডাকা নয় ? কেননা আল্লাহর নিজেরই একটি গুণবাচক নাম হচ্ছে সালাম বা শান্তি। আর তিনি মানুষকে শান্তির দিকে ও শান্তির জায়গায়ই আহ্বান করেন। সুতরাং ইসলামের অর্থ হচ্ছে, শান্তি। আর এটাকে আমাদের আরো বৃহত্তরভাবে বুঝতে হবে যে, আমরা কিভাবে নিজেদের মধ্যে, অন্যন্য সৃষ্টজীবের সাথে, আল্লাহর দেওয়া শান্তিলাভ করতে পারি এবং একই সাথে আমাদের চূড়ান্ত উদ্দেশ্যের শান্তির জায়গায় পৌঁছাতে পারি ? যদি আমরা ইসলামকে ওরিয়েন্টালিস্টদের করা অনুবাদের আলোকে অনুসরণ করে থাকি, তাহলে আমরা যৌক্তিক কোনো কাজ করছি না, সঠিক চিন্তার আলোকে কাজ করছি না।
আমরা আমাদের জীবনধারা বা ধর্মকে বোঝাপড়া করি আমাদের জীবন ও মৃত্যু উভয়টি বিবেচনায় নিয়ে। এটা গভীর, খুবই গভীর বিষয়। এটাকে শুধু একটা ধর্ম মনে করা যথেষ্ট নয়। আমাদেরকে এর সংজ্ঞায়নে যেতে হবে। এটা খুবই জরুরী। আপনি জিহাদকে কিভাবে সংজ্ঞায়ন করবেন ? খিলাফত বলতে কী বুঝেন ? এই খিলাফতের অর্থ এই নয় যে বর্তমানে সিরিয়ায় যা ঘটছে, ইরাকে যা ঘটছে। বরং এর রয়েছে গভীর ব্যাখ্যা। সৃষ্টিতত্ত্বের সাথে এর রয়েছে গভীর সম্পর্ক। এর সম্পর্ক আমাদের জীবন মৃত্যুর সাথে। এগুলো হচ্ছে মূলত ক্রিটিক্যাল থিংকিং।
এরপর কিছু বিষয়কে নতুনভাবে সংজ্ঞায়ন করতে হবে। নতুন জবাব তৈরি করতে হবে। যেগুলো নিয়ে আমরা প্রতিনিয়ত সমস্যার মুখোমুখি হচ্ছি। যেমন- ‘ইজতিহাদ’। গত ২০০ বছর যাবত আমরা ইজতিহাদ নিয়ে কথা বলেই যাচ্ছি। ইজতিহাদ আমাদেরকে সাহায্য করছে। আমাদের জীবনে কল্যাণ এনে দিয়েছে। আল্লামা ইকবালের মতে, ইজতিহাদ হলো আমাদের মূল চালিকাশক্তি। ভালো কথা, কিন্তু আপনি যদি বর্তমান সময়ের ইজতিহাদ দেখেন, আমরা কি নতুন কোনো ধারণা আনতে পারছি নাকি শুধুমাত্র সময়ের সাথে তাল মেলাচ্ছি ? আমরা বলি ইসলামিক ইকোনমি, ইসলামিক ফিন্যান্স, ইসলামিক, ইসলামিক, ইসলামিক। সবকিছুর শুরুতেই ‘ইসলামিক’ শব্দ প্রয়োগ করে যাচ্ছি বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে চলার জন্য। কিন্তু নিজস্ব উৎকর্ষ সাধন করতে পারছি না, এখানে নিজস্ব জ্ঞানকে প্রয়োগ করতে পারছি না।
আমরা শুধু নিজেদেরকে অন্যদের মত করে ভাবছি। বরং ইজতিহাদ হবে বিশ্বকে বদলে ফেলার কোনো একটি পদ্ধতি। কিন্তু আমরা এর ব্যবহার করছি বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে চলার জন্য। এটি গুরুতর একটি সমস্যা !
- ইজতিহাদ বলতে আমরা কী বুঝি ?
আমি যখন মিসরে পড়াশোনা করছিলাম, তখন শিক্ষকেরা আমাকে ইজতিহাদ বুঝিয়েছে। তারপর আমি বুঝলাম আমাদের বোঝাপড়া এক নয়। আমি ইসলামকে বুঝেছিলাম বিশ্বকে ভালোর দিকে বদলে ফেলার একটি পদ্ধতি হিসেবে। সুতরাং ইজতিহাদ সম্পর্কে আমাদের স্বচ্ছ ধারণা নাই।
এমনকি মাসলাহার ক্ষেত্রেও। ইংরেজিতে মাসলাহা বলতে বুঝায়— Unrestricted Public Interest. মাসলাহা কোনোভাবেই unrestricted কিছু নয় বরং এটা হলো ethical interest (নৈতিক প্রয়োজনীয়তা)। এটি অবশ্যই নৈতিক। আমাদের দরকার কিছু সঠিক নীতি। এটা উন্মুক্ত নয়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে আল্লাহর নীরবতা গুলো এজন্য নয় যে, আমরা যেটা চাই তাই করবো বরং আমাদেরকে বলে দেয়া হয়েছে এমন সব কাজ করার জন্য যা মানবতার জন্য কল্যাণকর। সুতরাং আমাদের এমন একটা উদ্দেশ্যের কথা ভাবতে হবে, যা হবে নৈতিক। এই হলো মাসলাহা। আর মাসালিহুল মুরসালাহ অর্থ Unrestricted Public Interest বিষয়টি এখানে সমস্যাজনক। এরকম হওয়ার কারণ হচ্ছে আমরা কি আমাদের টার্ম বা পরিভাষাগুলো সঠিকভাবে ব্যবহারের প্রচেষ্টা করছি ? না, পর্যাপ্ত চেষ্টা করছি না।
আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো ক্রিটিক্যাল চিন্তার প্রয়োজনীয়তা শুধুমাত্র জ্ঞানের বাহ্যিক বিষয়েই নয় বরং একই সাথে এগুলো অভ্যন্তরীণ, অন্তর্নিহিত বিষয়গুলোর ক্ষেত্রেও। এটা আমাদের জ্ঞানের বিন্যাস, জ্ঞানের শ্রেণিবিভাগ। যদি আপনি কুরআন সুন্নাহর দিকে তাকান, দেখবেন কুরআনের ক্ষেত্রে উলুমুল কুরআন, হাদীসের উসূলে হাদীস, উসূলে ফিকহ, ইলমুত তাসাউফ, ইলমুল কালাম, ইলমুল আখলাক এই সকল প্রকার ইলমের শ্রেণিবিভাগ কোথা থেকে এসেছে? কে করেছে? এটা কি কুরআন থেকে এসেছে ? না। হাদীস থেকে ? না। এটা এসেছে মানুষের নিজস্ব গঠনমূলক চিন্তা থেকে ৷
ইসলামিক জ্ঞান নিয়ে কেনো আমরা কথা বলি ? আমার প্রশ্ন হলো ইসলামিক জ্ঞানের মধ্যে ‘ইসলামিক’ বলতে আসলে কী বোঝায় ? পাকিস্তানে একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে আমি প্রশ্নটি করেছিলাম। তারা যে উত্তর দেয়, তা স্পষ্ট ছিলো না। কোনো কিছুকে আমরা কেনো ‘ইসলামিক’ বলি? সেটা কি তার বিষয়বস্তু ইসলাম সম্বন্ধীয় হওয়ার কারণে? যেমন—কুরআন, সুন্নাহ এগুলো। ইসলামি জ্ঞানের মধ্যে ‘ইসলামিক’ কোনগুলো? গণিত, সামাজিক বিজ্ঞান— এগুলোতে ইসলামহীনতাটা কী, যে আমরা এগুলোর আগে ‘ইসলামিক’ শব্দ ব্যবহার করি?
তারপর আমরা বলি, আমাদের একটি ‘কমপ্রিহেনসিভ এপ্রোচ’ প্রয়োজন। এটা একটা সমস্যা। এরপর যখন আপনি ইসলামিক জ্ঞানকে শ্রেণিবিন্যাস করবেন, তখন মানুষ বলবে, আসলে এটা ইসলামিক জ্ঞান নয়, পবিত্র জ্ঞান। কারণ তাদের বুঝাপড়া শুধু পবিত্র উপাদান নিয়ে ৷ আর তা হলো কুরআন ও হাদীস। এটা আরেকটা সমস্যা। আপনি যখন ফিকহ নিয়ে কথা বলেন, যেটা পুরোটাই মানুষের চিন্তা থেকে আগত, এখন আমার মতামত কি পবিত্র ? আচ্ছা পবিত্র চিন্তার শেষ কোথায় আর মানব চিন্তার শুরু কোথায় – এটাই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। বর্তমানে প্রধান ইসলামিক জ্ঞান হলো— ফিকহ। কেনো? কারণ আমরা হালাল হারাম নিয়ে ডিল করছি। যদি আপনি কোনো শায়েখকে খুঁজেন, তাহলে দেখবেন, তিনি শুধু বলছেন, এটা হারাম, ওটা হালাল।
গোটা আইনি কাঠামোর দর্শন ও এই পুরো প্রক্রিয়ার একটা সামগ্রিক বোঝাপড়াই হওয়া উচিৎ এখানকার মূল কাজ। আমাদের এটা নেই। বরং আমরা যেটা করি, তা হচ্ছে শুধু ‘আইনি’ সিদ্ধান্তটা জানার চেষ্টা করি। ক্লাসিক যুগের আলেমগণ শুরুতেই কোনো মতামত দিতেনা। বলতেন না এটা হারাম, এটা হালাল। বরং তারা সব ব্যাপার গুলো উন্মুক্ত করে দিতো। এ জন্যই বিজ্ঞান, শিল্পকলা বা জ্ঞানের অন্য কোনো শাখা নিয়েই পূর্বে আমাদের কোনো সমস্যা ছিলোনা। জ্ঞান হচ্ছে মুসলমানদের হারানো সম্পদ। এজন্যই আমরা এটা যেখানে পাই, সেখান থেকেই গ্রহণ করি। জ্ঞানের ক্ষেত্রে এখন আমাদের রক্ষণশীল মনোভাবের কারণে, এখনকার সময়ে আমাদের জ্ঞানচর্চার মৌলিক জায়গা গিয়ে দাঁড়িয়েছে শুধুমাত্র কোন বিষয়টি হালাল, কোন বিষয়টি হারাম সেটা জানার জায়গায়। এবং এ বিষগুলোতেও আমরা ক্রিটিক্যাল নই। কেবলমাত্র একটা ফতোয়া পেলেই আমরা খুশি হয়ে যাই। এটা খুবই সমস্যার বিষয়। এ কারণেই জ্ঞানের ক্ষেত্রে আমাদের অগ্রাধিকার কী হওয়া উচিৎ, সেটাই আমরা বুঝতে পারছিনা।
জ্ঞানের শ্রেণিবিন্যাস হলো মূলত ক্ষমতারই রূপায়ন। সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা কার আছে ? আজ মুসলিম বিশ্বের দিকে তাকান, মুসলমানদের নিয়ে কে কথা বলে ? সত্যিকারের কোনো জ্ঞানী-বিশেষজ্ঞ কি আছেন, যিনি মুসলমানদের নিয়ে কথা বলবে?
যদি আপনি চিকিৎসা বিজ্ঞানে ফাতওয়া খুঁজেন, ফাতওয়া কে দিচ্ছে ? সর্বদা যা হয়, একজন শায়েখ। কিন্তু তিনি জ্ঞানের এই শাখা সম্পর্কে কতটুকু জানেন ? আরেকটা বিষয়, আমরা ক্ষমতা নিয়ে কথা বলতে পছন্দ করি না। এটা নিয়ে কথা বলতে হবে। যদি আপনি ক্রিটিক্যাল থিংকিং এ আসতে চান, ক্ষমতা নিয়ে প্রশ্ন করুন। শুধুমাত্র স্বৈরাচারী শাসকদের নিয়ে নয়, সকল প্রকার ধর্মীয় কর্তৃপক্ষকে নিয়ে। কে, কিভাবে, কিসের উপর ভিত্তি করে কথা বলছে, এসব। আপনি পাশ্চাত্যে যাবেন, সেখানে লোকজন এসব জটিলতা নিয়ে প্রশ্ন তোলে।
বর্তমান বিশ্বের নতুন জটিলতা হলো (fragmentation of knowledge) জ্ঞানের বিভাজন। তবে আমাদের বিভিন্ন পর্যায়ে যথেষ্ট দক্ষতাসম্পন্ন লোকজন আছে, কিন্তু জ্ঞানের বিভিন্ন শাখার সাথে তাদের পরিচিতি নেই। জ্ঞানের বিভাজন (Fragmentation of knowledge) আপনাকে কোনো একটা একক বিষয়ে বিস্তারিত জানার ক্ষেত্রে দক্ষ করে তুললেও সামগ্রিক বোঝাপড়ার ক্ষেত্রে এটা খুবই বিক্ষিপ্ত এবং দুর্বল। আজ আমরা সামগ্রিক বোঝাপড়া নিয়ে কথা বলছি অথচ আমাদের নিজস্ব জ্ঞানের শাখাগুলোও সম্পূর্ণরূপে বিক্ষিপ্ত। এটা অনেকটা এরকম, যখন দর্শন নিয়ে কথা বলছেন, তখন কোথাও ভুল করছেন। যখন সুফীবাদ নিয়ে বলেন, তখন তা মূল থেকে বহু দূরে। যখন সমাজবিজ্ঞান নিয়ে কথা বলেন, তখন আসলে এগুলো পবিত্র (Divine) নয়, কেবল নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার।
আমাদের উচিৎ আমাদের নিজস্ব ইতিহাস-ঐতিহ্য নিয়ে কথা বলা। আমাদের ইতিহাসে অনেক সাহসী ওলামা রয়েছেন এবং তারা কিছু বিষয়ে খুবই স্পেসিফিক কিছু প্রশ্ন ও উত্তর নিয়ে এসেছেন। উদাহরণস্বরূপঃ ধর্মত্যগীদের শাস্তি কী হবে—এই বিষয়ে যারা আলোকপাত করেছেন। অষ্টম শতাব্দীতে একজন আলেম বললেন— ধর্মত্যাগীদের মৃত্যুদন্ড দেয়া উচিৎ নয়, কারণ মুহাম্মদ (সা) কখনোই ধর্মত্যাগের জন্য কাউকে মৃত্যুদন্ড দেননি। এখানে তিনি একটি মতামত দিয়েছেন, যেখানে তিনি একাই অসংখ্য আলেমের বিপরীতে দাঁড়িয়েছিলেন। কিন্তু আপনাকে কে বলেছে যে, বেশিরভাগ লোক কোন বিষয়ে একটি মতামত দিলে সেটাই সত্য হবে ? এটা হতে পারে, কেউ একজন একটি মতামত নিয়ে আসলো যা খুবই গভীর এবং তাৎপর্যপূর্ণ, তাহলে এটা সঠিক হতে পারে এবং বাকী সবারটা ভুল হতে পারে। মানুষ এখন সেই আলেম, সুফিয়ান সাওরীকে নিয়ে পুনরায় কথা বলছে যে, তাঁর নীতিটা সঠিকও হতে পারে, কারণ তিনি যা বলেছেন তা সঠিক।
–
বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও এটা হতে পারে, একজনের সঠিক মত অধিকাংশের বিরুদ্ধেও যেতে পারে। এটাই হচ্ছে ক্রিটিক্যাল থিংকিং। একটা মতামত কতজন দিয়েছে, সেটা বাদ দিয়ে চিন্তা করতে হবে মতামত নিয়ে। ইমাম গাজালি আমার খুবই প্রিয় একজন আলেম এবং অনেক মাসআলায় আমি তার অনুসরণ করি। কিন্তু তিনি হলেন তাঁর সময়কার একজন চিন্তাবিদ। তিনি নারী পুরুষের সম্পর্কের ব্যাপারে যা বলেছেন, তা গ্রহনযোগ্য নয়। তিনি মনে করতেন নারী ও পুরুষের সম্পর্ক হচ্ছে— মনিব ও দাসের মতো। যেটা খুব স্বাভাবিকভাবেই সঠিক নয়। সুতরাং এরকম অনেক বিষয়েই আমাদের ক্রিটিক্যালি চিন্তা করতে হবে। আমাদের সমস্ত স্কলারদের ক্ষেত্রেই এটা সত্য, আমরা তাদেরকে সম্মান করি কিন্তু তাদের সব মতামতই যে আমাদের কাছে গৃহীত হবে এমন নয়।এবার যেটা চিন্তা করতে হবে, সেটা হলো,
- মুসলিম হিসেবে আমাদের চিন্তার উৎসগুলো কি কি ?
এটা কি শুধুমাত্র কুরআন ও সুন্নাহ ? আল্লাহর সৃষ্টির মধ্যে কি চিন্তা করার কিছুই নেই ? আমাদের সামগ্রিক বোঝাপড়া এবং আইনি কাঠামোর উৎসগুলো কি কি ? জ্ঞানের বিভিন্ন শাখা থেকে কি গ্রহণ করার কিছু নেই ? অর্থনীতির মধ্যে ? সমাজ বিজ্ঞানের মধ্যে ? রাষ্ট্রবিজ্ঞানের মধ্যে ? আমাদের কি কেবল কুরআন ও হাদিসের মতো জ্ঞানের পবিত্র উৎসগুলোর উপরই নির্ভর করতে হবে ? এটা করতে গিয়ে অন্যান্য জ্ঞানকে আমরা গুরুত্ব দিচ্ছি না। এটা ভুল। শুধুমাত্র চিকিৎসাবিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ে ফতোয়া দিতে গিয়েই আলেমরা এই বিষয়ে একমত হয়েছেন যে— শরীর কিভাবে কাজ করে, তা যেহেতু তাদের জানা নেই, তাই এসব বিষয়ে ফতোয়া দিতে তাদের ডাক্তারের দ্বারস্থ হওয়া প্রয়োজন। তেমনি আমাদের এটাও বুঝতে হবে যে, আল্লাহ তায়ালার জাগতিক সৃষ্টিসম্ভার একটা বইয়ের মত। বিশ্বকে বুঝতে হলে এই বই পড়তে হবে। সুতরাং আমাদের জ্ঞানের উৎস কী হবে— এই বিষয়েও আমাদের প্রশ্ন করতে হবে।
সামনে যারা বসে আছেন, এর মধ্যে যারা রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ছাত্র, মানবিক বিজ্ঞানের ছাত্র, সমাজবিজ্ঞানের ছাত্র, আপনাদের জ্ঞানকে একটা আলোচনায় আনা প্রয়োজন।
এখানে আরেকটি বিষয় গুরুত্বপূর্ণ, তা হচ্ছে— আলেম কারা ? আল্লাহর ঘোষণা, انما يخشى الله من عباده العلماء – বান্দাদের মধ্যে আল্লাহর ব্যাপারে ওলামারাই অধিক সচেতন। আমরা এখানে ‘আলেম’ বলতে এখন শুধুমাত্র ‘ফকীহদের’ বুঝি, বরং এটা অন্যান্য বিষয়ের জ্ঞানীদের প্রযোজ্য হওয়ার কথা। এই আয়াতটি সৃষ্টি ও প্রকৃতির সাথে সংযুক্ত, কোনো বইয়ের সাথে নয়। আর আমাদেরকে এসব বুঝতে হবে অঞ্চলের উপর ভিত্তি করে। উদাহরণস্বরূপ, আপনারা তুরস্কে থাকেন, এই সমাজেই বসবাস করেন। আপনাদের বলতে চাই, সাবধান! আপনারা হচ্ছেন এ অঞ্চলের আলেম। আপনারা তুরস্ক সম্পর্কে জানেন বুঝেন। তাই এমন ফাতওয়া গ্রহণ করবেন না বা কোনো বিষয়ের সমাধান নিবেন না যেটা সৌদি আরব বা অন্য কোনো দেশ থেকে এসেছে। বরং আপনাদের প্রেক্ষাপটটা আপনাদেরই বুঝতে হবে। আপনাদেরকেই আপনাদের অগ্রাধিকারের বিষয়গুলো বুঝতে হবে।
সুতরাং আপনার দায়িত্ব হচ্ছে আপনার অর্জিত জ্ঞানের ব্যাপারে বিশ্বস্ত হওয়া। তুরস্ক সম্পর্কে আপনার চিন্তা অন্য কেউ করতে পারবে না। মক্কা মদীনা বা অন্য কোনো সেরা শহরের লোকেরাও আপনার চাইতে সঠিক চিন্তা করতে পারবে না এই অঞ্চলের ব্যাপারে। কিন্তু এটা করার জন্য আপনাকে আলোচনায় যুক্ত হতে হবে। আপনাকে প্রশ্ন করতে হবে উৎস নিয়ে। বুঝার চেষ্টা করতে হবে, ক্রিটিক্যাল থিংকিং নিয়ে ভাবতে হবে।
আমাদেরকে যথাসম্ভব প্রশ্ন করতে হবে বিভিন্ন জ্ঞান সম্পর্কে, প্রণালী সম্পর্কে এবং অথরিটি নিয়ে প্রশ্ন তুলতে হবে।
বিশ্বের মুসলিমরা বর্তমানে কর্তৃত্ব সংকটে ভূগছে। Crisis of Authority। কারণ আমরা জানিনা কে সিদ্ধান্ত নিচ্ছে, কিভাবে আমাদের রেফারেন্স গুলো দেওয়া হচ্ছে। এই ব্যাপারে মনোযোগ দিতে হবে। আমাদের একটা ধারা আছে, যেখানে একটি অপ্রাতিষ্ঠানিক কর্তৃপক্ষ আছে, যা এসেছে জ্ঞানের শ্রেণিবিন্যাস থেকে। এই ব্যাপারেও প্রশ্ন করতে হবে। আরো প্রশ্ন করতে হবে, ফাতওয়া গুলোর সিদ্ধান্ত কিভাবে গৃহীত হয়, গঠন কাঠামোগুলো কিভাবে তৈরি হয় এবং ইসলামি পরিভাষায় কারা সিদ্ধান্ত দেয়। যদি আপনি ক্ষমতায়ন নিয়ে আলোচনা না করেন, তাহলে রাজনীতিবিদেরা রাষ্ট্রীয় জায়গা থেকে সিদ্ধান্ত দিয়ে দিবে ঘটনা পরম্পরার উপর ভিত্তি করে। তারা মতামতকে বদলে ফেলবে।
আর আলেমগণ বিষয়টাকে পরিবেশের সাথে মানিয়ে নিতে চেষ্টা করেন। কিন্তু গভীর কোনো চিন্তা করার চেষ্টা করেন না। বিশেষ কোনো লক্ষ্যপূরণের চেষ্টা করেন না।
মুসলিমরা ক্ষমতায়ন নিয়ে কথা বলতে পছন্দ করেন না বিশেষত যদি তা ধর্মের ব্যাপারে হয়ে নিয়ে। সৌদি সালাফিগণ বলে থাকেন যে, اولى الامر منكم – যার ফলে ক্ষমতায় যারা থাকে, জনগণ তাদেরকেই অনুসরণ করে। এটাই যথেষ্ট। প্রশ্ন করার দরকার নাই। আর বলে, রাজনীতিতে যাবেন না। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক বিবৃতি হলো “রাজনীতি করবেন না।” কাউকে রাজনীতি করতে নিষেধ করাটাও একটা গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক অবস্থান, এটাও আমাদের বুঝতে হবে।
কিন্তু মুসলিম হিসেবে আমাদের এসব নিয়ে ক্রিটিক্যাল চিন্তা করতে হবে। ধর্মীয় ক্ষমতা, রাজনৈতিক ক্ষমতা, যত প্রকার ক্ষমতা আছে, সবগুলোর ব্যাপারে প্রশ্ন করতে হবে। এমনকি প্রভাবশালী সংস্কৃতি নিয়েও প্রশ্ন করতে হবে। আজ আপনারা তুর্কিরা পাশ্চাত্য দ্বারা প্রভাবিত। যদি এটা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন, তবুও। এখন বলবেন না, না না না আমরা সম্পুর্ণ স্বাধীন। আসুন, এখানকার গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুগুলো নিয়ে পর্যালোচনার চেষ্টা করি। এটা স্বীকার করি এবং ক্রিটিক্যালি চিন্তা করি। প্রভাবশালী ক্ষমতা বা প্রভাবশালী সভ্যতার অর্থ হলো আমাদের সেসব প্রশ্ন করার ক্ষমতা আছে, যেগুলো আমরা জানতে চাই। সুতরাং আপনি কিভাবে নিজেকে মুক্ত রাখতে চাইছেন, সেসব প্রশ্ন করা থেকে।
- আসুন এবার তাত্ত্বিক আলোচনা থেকে বাস্তবায়নের দিকে যাই।
আপনারা জানেন যে, আমি বিশ্ববিদ্যালয়ে একাডেমিক জগতে কাজ করি। আমাদেরকে একটা বিষয় স্পষ্ট হতে হবে, তা হলো সমাজ ও জনগনের সেবায় বর্তমান বিশ্ববিদ্যালয় গুলোর ভূমিকা কী? আমাদের কথা হচ্ছে জনগনের সেবা করা। আপনি হতে পারেন পাবলিক ফিগার কিন্তু আপনাকে মাঠে থাকতে হবে, জনগনের জন্য কাজ করতে হবে। আপনি তাত্ত্বিকভাবে যেগুলো চিন্তা করছেন, সেগুলো বাস্তবায়ন করতে হবে। اللهم نسئلك علما نافعا – হে আল্লাহ আমাদেরকে উপকারী জ্ঞান দান করো। উপকারী জ্ঞানের মাধ্যমেই আমি জনগনের সেবা করতে পারি। এই বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে তুরস্কের জনগণের আগ্রহ পূরণ করতে হবে। আঞ্চলিক পর্যায় থেকে রাজনৈতিক পর্যায় পর্যন্ত।
যে বিশ্ববিদ্যালয় গুলো জনগন নিয়ে চিন্তা করেনা, সেগুলো ইউজলেস, অনর্থক। সেগুলো বন্ধ করে দেয়া হোক। আরেকটি বিষয় হলো, আমরা এ বিষয়গুলো বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে কোথা থেকে শুরু করবো ? আমি প্রায় পঁচিশ বছর যাবত تشجيد এবং Renewal নিয়ে কথা বলে আসছি এবং আজ থেকে ১৫০ বছর পর বিষয় গুলো ক্লিয়ার হবে, এরকম কোনো সম্ভাবনা দেখছি না। আমাদের আরো চিন্তা করতে হবে ইসলামি ধারায় تحقيق المنات বলতে কী বুঝায়। মানে হলো কিভাবে আমাদের মূলনীতিগুলো বাস্তবে প্রমাণ করবো। সুতরাং আপনাকে জানতে হবে প্রেক্ষাপট, জানতে হবে পরিবেশ।
আমাদের স্কুল গুলোতে শুধুমাত্র মুখস্ত করানো হয়, অন্তরে ধারণ করানো হয়। কিন্তু ইসলাম বলছে, যা কিছু মুখস্থ করছে তা বুঝতে হবে। স্কুল গুলোতে প্রশ্ন করার সুযোগ দিতে হবে। মসজিদে জনগণকে প্রশ্ন করার সুযোগ দিতে হবে। এগুলো হচ্ছে বিষয়, যেখান থেকে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার সংস্কার সাধন করতে হবে। আপনার অধিকার আছে প্রশ্ন করার এবং করতে হবে।
আপনি চিকিৎসা বিজ্ঞান নিয়ে পড়েন, সমাজ বিজ্ঞান নিয়ে পড়েন, রাষ্ট্রবিজ্ঞান নিয়ে পড়েন, যা ইচ্ছা তাই পড়েন, যদি মনে করেন এটা দিয়ে কিছু করতে পারবেন, তাহলে এটার অভিষ্ট লক্ষ্য কী তা খুঁজে বের করেন। আপনি যে বিজ্ঞান নিয়ে পড়ে আছেন, সেটার শেষ কী, ফলাফল কী, নিজকে প্রশ্ন করুন। রাজনীতি, অর্থনীতি, শিল্প, সংস্কৃতি এই ক্ষেত্রগুলোতে ইসলামের অবদান বর্তমানে খুবই ভাসাভাসা। চিন্তা করুন, বর্তমানে মানুষের মনন কিভাবে গঠিত হয়ে থাকে। বিনোদন, শিল্প, সংস্কৃতি, কোন ক্ষেত্রে আমাদের অবদান আছে? আমরা এসব নিয়ে কী চিন্তা করছি ? বিকল্প ইসলামী গান, কিছু আরবি শব্দমালা দিয়ে, আল্লাহ রাসূল শব্দের ব্যবহার, এসব দিয়েই আমরা বর্তমানে কাজ করছি। এই জায়গায় আমাদের প্রশ্ন করা, চিন্তা করার কথা। কিন্তু তা আমরা করছি না। এগুলোই হচ্ছে (Amateurism) অপেশাদারিত্ব। এটা কোনো সঠিক পন্থা নয়। এসব ক্ষেত্রে কিভাবে পেশাদার শিল্পী, পেশাদার চিন্তাবিদ, লেখক দাড় করানো যায়, যারা অবদান রাখতে পারবে, এসব চিন্তা করতে হবে। একই কথা অর্থনীতির ক্ষেত্রে। আমাদের আছে ইসলামি অর্থনীতি এবং মূল বিষয় টা হলো আমরা চুড়ান্ত লক্ষ্যবস্তুকে বাদ দিয়ে উপায়গুলোকে ইসলামীকরণ করছি।
আমরা তাদের মত একই রকম টাকা বানাতে চাই কিন্তু হালাল উপায়ে, এটা সঠিক পন্থা না। এটা কেবল পরিবেশের সাথে খাপ খেয়ে চলার মতো। আমি কিছু স্কলারকে বলতে শুনেছি, তারা বলে, ইসলাম হলো Regulated Capitalism. আমাদের সমাধান কি এরকম ? এটা কি বর্তমান বিশ্বে অবদান রাখার কোনো উপায় ? সুতরাং এই ক্রিটিক্যাল থিংকিং যদি কোনো অবদান রাখার জন্য না হয়, তাহলে সেটা একটা সমস্যা। সুতরাং এই আলোচিত সকল বিষয়কে একটি উৎসমূলে নিয়ে আসতে হবে। যেভাবে আমরা বিশ্বকে দেখছি, যেভাবে জ্ঞানকে দেখছি, যেভাবে মানবজাতিকে দেখছি। আমাদের একই সাথে তত্ত্ব এবং বাস্তবতাকে সমন্বয়কারী আলেম দরকার। সব ধরনের আলেমকে এগিয়ে আসতে হবে।
আমি শেষ করতে চাই একটি দর্শন দিয়ে। আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় আরো দার্শনিক ভিন্নতা আনতে হবে। দর্শনটা হলো “কেন”। প্রশ্ন করা। ইসলামে আছে আইন দর্শন, জ্ঞান দর্শন, জ্ঞানতত্ত্ব। সুতরাং মূল ইমেজটা হলো আইন দর্শন ও জীবন দর্শন। যখন আলেম এবং চিন্তাশীলগণ এই আয়াতটি পড়েন, وعلمكم الكتاب والحكمة – আল্লাহ তোমাদেরকে কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দিয়েছেন।
তারা বলেন, হিকমাহ অর্থ সুন্নাহ। এটা সঠিক নয়। এটা কেবল স্বাভাবিক অনুবাদ। হিকমত হলো প্রজ্ঞা। আর প্রজ্ঞা হলো জীবন এবং মৃত্যুর বোঝাপড়া। এটাই হচ্ছে প্রধান দৃষ্টিভঙ্গি। কিতাব পাঠানো হয়েছে প্রজ্ঞা অর্জনের জন্য। আর প্রজ্ঞা হচ্ছে سلامة النفس কে ভালবাসা। سلامة النفس হলো অন্তরের প্রশান্তি। সৃষ্টির সাথে আপনার শান্তি স্থাপন করতে হবে। সৃষ্টিকে সম্মান করতে হবে। সৃষ্টির সাথে, মানুষের সাথে ভালবাসা স্থাপনের ক্ষেত্রে কিভাবে জ্ঞান প্রয়োগ করবেন। আর এটা সহজেই অর্জন করা যায় না। এর বিভিন্ন ধরণ রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ ফিলিস্তিন। আমরা বলি, সেখানে কোনো শান্তি নাই, কোনো ন্যায় বিচার নাই। ন্যায়বিচারের একটি শর্ত হলো নিজের সাথে ন্যায়বিচার করা।
কুরআনে বলা হয়েছে, الهم ظلمنا انفسنا – আমরা নিজেদের উপর যুলুম করেছি। এর মানে হলো আমরা ততক্ষন শান্তি কামনা করতে পারি না যতক্ষন না নিজেরা ন্যায়বিচার করি। আপনি কখনোই শান্তি পাবেন না, যদি দুর্বলদের সাথে অবিচার করেন। সুতরাং সৃষ্টিতত্ত্বের (Cosmology) সাথে শান্তি স্থাপন খুবই জরুরি। সুতরাং শান্তির জন্য প্রয়োজন শিক্ষা, ন্যায়বিচার, স্বাধীনতা। এই সবগুলো নিয়েই আমাদের আগাতে হবে। আর এটাই হচ্ছে জীবনের দর্শন, জ্ঞানের দর্শন, আইনের দর্শন। এটাই হলো ম্যাটাফিজিক্স, যা আমরা প্রায় হারিয়ে ফেলেছি।
আমরা এখন হালাল হারাম বিতর্ক করে ইসলামের মূল্যবোধ কমিয়ে দিচ্ছি। আমার অনুরোধ, এই ক্রিটিক্যাল চিন্তা করতে গিয়ে আবার আধ্যাত্মিকতা বাদ দিয়ে শুধু যুক্তি নির্ভর হয়ে যাবেন না। সুফিবাদে মুরাকাবা মানে ধ্যান সাধনায় আত্মনিয়ন্ত্রণ, এটাকেও ক্রিটিক্যাল চিন্তায় আনতে হবে। নিজেকে যাচাই করতে হবে। প্রথম যেটা করতে হবে, তা হলো কাজের নিয়্যত বিশুদ্ধ করা, যার মাধ্যমে বোঝাপড়া করবেন। আপনার অন্তরের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ আছে কি না, মনের প্রতি, আত্মার প্রতি, শরীরের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ আছে কি না। আত্মযাচাই ব্যাতীত আধ্যাত্মিকতা অর্জন করা যায় না। সুতরাং এটা নিয়ে এগিয়ে আসুন। তবে আধ্যাত্মিকতার বিরুদ্ধে নিখাদ যুক্তি দিয়ে নয়, বরং আধ্যাত্মিকতাকে ক্রিটিক্যাল থিংকিং এর আলোকবর্তীকা হিসেবে গ্রহণ করুন। মানে হলো আমরা ক্রিটিক্যাল কারণ, আমরা এর বোঝাপড়াকে, লক্ষ্যকে, পথকে প্রশ্ন করছি।
সবশেষে, আমাদের নিজেদের ব্যাপারেও আমাদের ক্রিটিক্যালী চিন্তা করতে হবে— আমরা কি কল্যাণের আশায় আল্লাহর ইবাদত করছি ? নাকি সূযোগসন্ধনী হয়ে নিজেদের জন্য অকল্যাণ বয়ে নিয়ে আসছি ? এই চিন্তাটা আমাদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ, কারণ আমাদের কাছে আধ্যাত্মিকতার অর্থই হচ্ছে— আমরা আমাদের জীবনকে অর্থপূর্ণভাবে গড়ে তুলতে পারছি কিনা ! নিজেকে প্রশ্ন করার মধ্য দিয়েই আমার ক্রিটিক্যাল চিন্তা শুরু করতে হবে। আমাকে চিন্তা করতে হবে যে—আমরা দুনিয়াকে বদলে দিতে চাই। কিন্তু এই বদলে দেয়ার জন্য আমি এমন কী করেছি ? দুনিয়াকে বদলে দেয়ার জন্য তো এখানে আমাকে কিছু না কিছু অবদান রাখতেই হবে! বর্তমান সময়ে মুসলিমদের একটি বড় সমস্যা হচ্ছে, আমরা নিজেরা মৌলিক কোন অবদান না রেখে বরং অন্ধভাবে আমরা চাপিয়ে দেওয়া সংস্কৃতি ও সভ্যতাকে অনুসরণ করি। লক্ষ্যার্জনের দিকে দৃষ্টিপাত না করে আমরা শুধমাত্র উপায়গুলোকেই ইসলামীকরণ করার চিন্তা করছি ! তাই আমাদের জন্য ক্রিটিক্যাল চিন্তা হচ্ছে—প্রথমেই উৎস সম্পর্কে জানা অতঃপর বোঝাপড়ার চেষ্টা চালানো, প্রশ্ন করা এবং সবশেষে আমি কী অর্জন করতে চাই তা চিন্তা করা। মানুষের কল্যাণের চিন্তা সবসময়েই আমাদের মাথায় রাখা উচিৎ, কেননা আল্লাহ তা’য়ালা তাকেই সবচেয়ে বেশি পছন্দ করেন— যে ব্যক্তি মানুষের জন্য সবচেয়ে বেশি কল্যাণকর। অন্যরা কী করছে, সেটা নিয়ে চিন্তা করার চাইতে আমরা কী করছি— সেটাই আমাদের বেশি বেশি ভাবা উচিৎ। কেননা আমাদের এখনো নিজেদের নিয়ে করার মতো অনেক কিছুই বাকি।
অনুবাদক : রিয়াজ আহমেদ